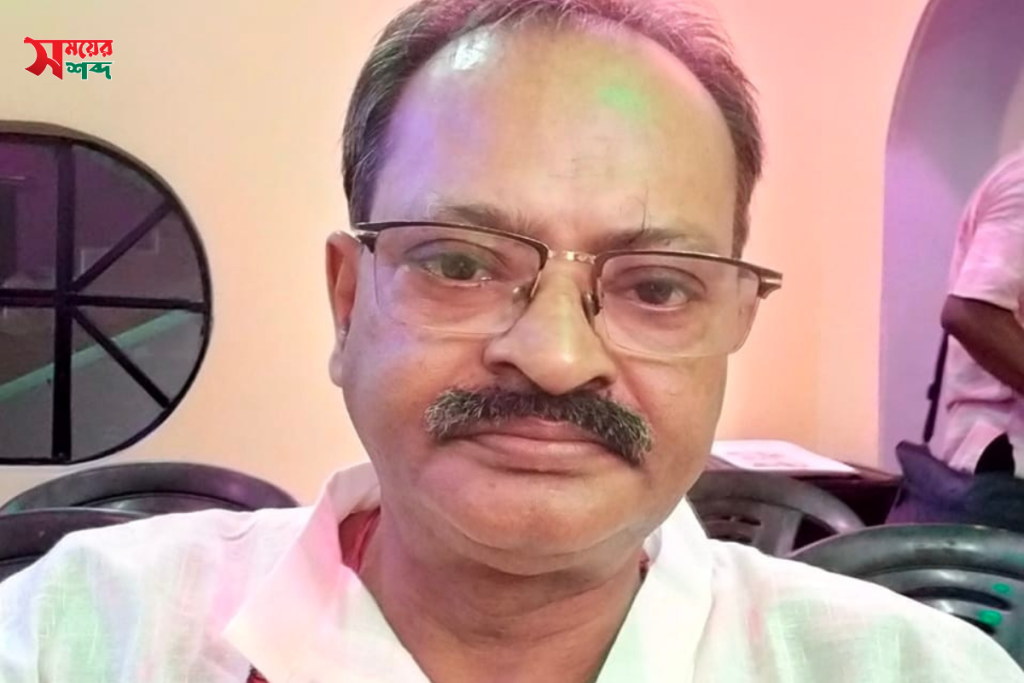শৈলীবিজ্ঞান অর্থাৎ রীতিবিজ্ঞান (stylistics) আমাদের দেশে শিল্পতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিচিত আগন্তুক বলে মনে হলেও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে ‘রীতি’ কথাটি বহুল প্রচলিত। আমরা দেখেছি যে শুধুমাত্র রচনারীতি ও ভাষাভঙ্গির তির্যকতার গুণে কোনো কোনো কবি স্থায়িত্ব লাভ করে সাহিত্যের আসরে। যেমন, সপ্তদশ শতাব্দীর ওড়িয়া কবি উপেন্দ্র ভঞ্জ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র। অতি সাম্প্রতিককালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায়, প্রতীচ্যের অনুসরণে স্টাইলিস্টিকস বা শৈলীবিজ্ঞানের প্রয়োগ শুরু হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ‘স্টাইলিস্টিক্’ শব্দটি সাহিত্যশৈলীর বিজ্ঞান (the science of literary style) অর্থে, বিশেষ্য ও বিশেষণে অভিন্ন রূপ নিয়ে প্রথম ব্যবহার হয়। ১৮৮২ সালে ইংরেজিতে ‘স্টাইলিস্টিক্’ শব্দটির প্রয়োগ শুরু হয়। শৈলী বা স্টাইলের আলোচনায় ইংরেজি সাহিত্যে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের সূত্রপাত ঘটলে প্রাচীন ভাববাদী দর্শনে ও সাহিত্যে প্রকৃষ্ট আঘাত লাগে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডাইড্রেন বলেছিলেন, ভাষা, চিন্তার পোশাক (language is the dress of thought) এবং স্টাইল পোশাকের বিশেষ নির্মিতি (style is the particular cut and fashion of the dress)।
বাকভঙ্গিমাতে শব্দচয়ন একটি বিশেষ লক্ষণ, যা কবি সাহিত্যিকদের স্বাতন্ত্র্য প্রদান করে। বাংলা কাব্যসাহিত্যে জীবনানন্দ দাশ প্রথম শব্দনিচয়ে imageকে এক অনন্যমাত্রায় প্রয়োগ করেছেন। কাব্যে ও সাহিত্যে অনেক শব্দই তার সাধারণ অর্থ পরিত্যাগ করে বাকপ্রতিমা বা ইমেজের সৃষ্টি করে থাকে। আধুনিক কবিতার সমালোচনা প্রসঙ্গে বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক এফ.আর. লাভিস মন্তব্য করেছিলেন, ‘Poetry matters little to the modern world’। কবিতার রাজ্যে পাঠক, আজকের সমাজে অনেক বেশি বিদগ্ধ। একথা আমরা স্বীকার করি যে, আজকের যুগের কবিতা আধুনিক মানবমনের বৈচিত্র্য (variety), জটিলতা (complexity) এবং সুমার্জিত অনুভূতি (refined sensibility) নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে তা সকলের আয়াসসাধ্য নয়। বাংলা কবিতায় ‘খটখটে আধুনিকতা’র প্রকাশ দেখা গেল তিনের দশক থেকে, যখন বোদলেয়ার, পাউন্ড, এলিয়ট, অডেনের অনুসরণে বাংলা কবিতার রাজ্যে পালাবদল এল সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের রচনাতে।
বাংলা কবিতার শৈলীবিজ্ঞান আলোচনা করতে গেলে জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে উপেক্ষা করা যায় না। বর্তমান আলোচনা যদিও কবি অমলেন্দু বিশ্বাসের কবিতার শৈলী বিচার; কিন্তু এ প্রসঙ্গে যাবার আগে পূর্বজ কবি জীবনানন্দ দাশ ও বিনয় মজুমদারের কথা স্বীকার করতে হয়। জীবনানন্দ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় কোনো কোনো শব্দ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অজস্রবার প্রয়োগ করেছেন। যেমন ‘শিশির’ শব্দটি অনেক কবিতাতে বিচিত্র চিত্রকল্প সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। তার প্রকৃত উদাহরণ হল—
১. সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে (বনলতা সেন)
২. … মনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল।
… শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে— (কুড়ি বছর পরে)
৩. অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের
মতো ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা (হাওয়ার রাত)
৪. সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ
ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে। …
… … …
নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরনো শিশির ভেজা গল্প (শিকার)
শাব্দিক কাঠিন্য এক অনন্যতা এনে দেয়। এই শাব্দিক কাঠিন্য অনেক বেশি মায়াময়। যা অমলেন্দু বিশ্বাসের কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে গভীর দর্শন; ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চেতনার সংরাগ। পয়ারের গদ্যশৈলীতে মায়াবী শব্দযোজনা বিশেষতা দান করেছে। কাব্যভাষাকে কখনোই আদর্শ ভাষা বলা যায় না, বলেছিলেন জাঁ মুকারোভস্কি। ইতর, আঞ্চলিক, লৌকিক শব্দকে অনায়াসে কবিতার উপপাদ্য বিষয়ে স্থান দেওয়া যেতে পারে। কবি অমলেন্দু বিশ্বাস এই কাজটি নিপুণতার সঙ্গে করেছেন। মায়াবী শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে ভাষা, অলংকার, ছন্দ, নিসর্গচেতনা, অখণ্ড সৌন্দর্য, ঘোলাটে শব্দ ব্যবহার, আভিধানিক শব্দ এবং প্রচলিত লৌকিক শব্দ প্রয়োগে তাঁর কবিতা অনেক বেশি মোহময়ী করে তুলেছে। আবার যেখানে ধর্ম-দর্শন-আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা রয়েছে, রয়েছে ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক চেতনার সমন্বয়, স্থানিক ব্যঞ্জনা কালোতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ কবি অমলেন্দু বিশ্বাসের কবিতায় বিপ্রতীপরূপ (ইনভার্সন) বা কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার বিপর্যাসও একই কারণে স্থান পায়। অর্থাৎ লেখার জগতেও বক্র কবি ভাষার চেয়ে প্রত্যক্ষ, সংপ্রেষক গদ্য বেশি কার্যকর হয়েছে। যেমন—
যখন কৃত্তিকা সন্ধ্যা ঝুঁকে থেকে দেখছিল
কীর্তনখোলার নীল স্নিগ্ধ প্রতিভাস।
তখনি ঠিক ভেসেল পেরুতে যাবার মুখে
আচমকা দেখা হলো রূপালি আগুন
যেন মোহমুগ্ধ কিশোরী সায়রা বানু।
ঈষৎ কিনার ধরে নদীর বাঁধানো পাড়ে
… … …
কিছুটা অঞ্চল জুড়ে গুপ্তচরের মতন
ছায়ার যামিনী নেমে এলো আমাদের কাছাকাছি।
প্রজনন হেতু জেগে থাকে ইলিশের চোখ
নদীর গহনে। অথচ স্টিমার জল ভাঙলে
সামান্য অরব আলো ছুঁয়ে থাকে, রুয়ে যায়
খরা ছিন্ন সবুজ পাতার অক্ষর কুটিরে।
(সামান্য অরব আলো, শান্ত শ্যাওলা জলে)
কবিতার শৈলীতে আমরা দেখতে পাই গদ্যময় জীবনের কাব্যিকভাষা। কৃত্তিকা সন্ধ্যা, কীর্তনখোলার নীল স্নিগ্ধ প্রতিভাস, রূপালি আগুন, প্রজনন হেতু, ইলিশের চোখ, নদীর গহনে, অরব আলো, খরা ছিন্ন, সবুজ পাতার অক্ষর কুটিরে। কবি অমলেন্দু বিশ্বাস পয়ার ছন্দকে কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে বেছে নিয়েছেন। তাঁর কবিতায় কবির বাস্তব জীবনের কঠিন কঠোর সংগ্রাম রূপ পেয়েছে কাব্যময় ভাষ্য হিসেবে। তাই তাঁর কবিতার ভাষাতে স্থান পেয়েছে কৃত্তিকা সন্ধ্যা, রূপালি আগুন, ইলিশের চোখ প্রভৃতি। এখানে কবির পর্যবেক্ষণ ঋষির মতো। তিনি দিব্য দৃষ্টি দিয়ে জগৎ ও জীবনের সবকিছু যেন দেখতে পান। ইলিশের চোখ তাই কবির মানসিক জগতকে আলোড়িত করে। ভাষা যেন কবির আদর্শ কাব্যিক ভাষা। আবার বাস্তবের সমাহিত আলেখ্যে অবিলোপিতভাবে স্থান করে নেয় কীর্তনখোলার মতো স্থানিক শব্দনিচয়। কখনো কখনো আমাদের বাস্তবতা দুর্বোধ্য মনে হয়; কবির দিব্য দৃষ্টিতে তাও এড়ায় না। চিত্রকল্প রচনাতে যেমন কবি সিদ্ধহস্ত তেমনি প্রকরণের সঙ্গে প্রসঙ্গের মিল-অমিল, অলংকারের পরিমাণ, বাক্যের গড়ন এবং অবয়বজ্ঞান লক্ষ করার মতন। কবিতাটিতে একজন অবজার্ভার যেন স্বয়ং কবি, তিনি দার্শনিক প্রত্যয় ব্যক্ত করছেন, ‘বসে যাও কবি’-র মধ্য দিয়ে। এ জগতে সকল আগন্তুককেই অপেক্ষক তৈরি করার অদম্য বাসনা থাকে আমাদের মধ্যে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা সম্ভব কি?
অপর একটি কবিতায় দেখা যায় কবির অবনত হৃদয়ের শরীরী বাস্তবতার গীতিআলেখ্য রচনার প্রয়াস। নির্মেদী কবিতাদর্শন থেকে সরে এসে আবেগময় মানবজীবনের মূল-সুরকে ব্যক্ত করেন কবি। তিনি বলেন—
ঘুরে ঘুরে চেয়ে দেখি কিছু মাঠে ফলবতী ধান
ঝুঁকে আছে মৃত্তিকার দিকে।
যদিও মৃত্তিকা জানে সম্পূর্ণ পোয়াতী ধান
প্রগাঢ় হরিদ্রা হলে কেটে কেটে কৃষকেরা
তুলে রাখবে নিকানো উঠোনে।
অথচ চাষী বৌ বাইন বানিয়ে রাখে
খোলা আঙিনার এক কোণে
বিশাল মাটির চুলা চেয়ে আছে
হামুখ অপেক্ষা খুলে আগুনের দিকে।
কিছুটা অদূরে অরব নয়নে রয়েছে দাঁড়িয়ে
বহুদিনের শিউলি গাছ! ঝরা ফুল—
কুড়োতে কুড়োতে তুমিও বলেছ কথা
আনত শরমে। দেখি হৈমন্তির নম্রসহচরী চোখে
পরকীয়া কাজলের রং নীল হচ্ছে কৃত্তিকা আকাশে।
(মাটির চুলা, শান্ত শ্যাওলা জলে)
অমিল পয়ার ছন্দে রচিত আপাতদৃষ্টে কবিতাটি। কিন্তু কবিতাটিতে ভাবাবেগের মিল রয়েছে অসাধারণভাবে। কবিতার প্রথম ও শেষ শর্ত কবিতাটির কবিতা হয়ে ওঠা। এদিক থেকে কবি প্রবর অমলেন্দু বিশ্বাস স্রষ্টার আদর্শ মানসপুত্র। আগের কবিতাটি মনকে করে তুলেছে আনন্দিত, যন্ত্রণাদ্র এবং মনকে বেদনায় ভরিয়ে ব্যাকুলতার দিকে অবশ্যম্ভাবীভাবে, গহীনের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। এই কবিতাটি সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, কবি পাঠক হৃদয়কে, ঠেলে দেয় অপার আনন্দে; তাই স্বয়ং স্রষ্টা কবি সৃষ্টিতত্ত্বকে সম্মান করেন, ফলবতী ধান-কে শেষ পর্যন্ত কৃষকপুরুষের হাতে সমর্পণ করেন। বাইন শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে লোকজ সৃষ্টিতত্ত্বকে নির্দেশ করে। মানুষের জীবন শৈলী হয়ে ওঠে কবিতার উপজীব্য বিষয়। ফলবতী ধান, পোয়াতী ধান, বাইন, হামুখ, শিউলি গাছ, ঝরা ফুল, নম্রসহচরী চোখে, পরকীয়া কাজলের রং, কৃত্তিকা আকাশ এসবই কবির সৃষ্ট অমৃত বাকপ্রতিমা। হামুখ যৌনতার নির্দেশক যা কবিতার ভিতরে অমোঘ সত্যকে উদ্ঘাটন করে। কিন্তু কবির মার্জিত রুচির প্রকাশ ঘটে তাঁর শব্দ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। এখানে কবির স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য যা কিনা দুর্লভ বললেই চলে।
কবি অমলেন্দু বিশ্বাস এক গভীর প্রত্যয়ে বাংলার লালিত সংস্কারকে আঁকড়ে ধরেন তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে। প্রাজ্ঞ কবির দার্শনিক অনুধ্যানে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, পরম্পরা অন্বিষ্ট ধরা রয়েছে। এবং পাশাপাশি প্রাক বৈদিক যুগের লোকায়ত, প্রকৃত মানুষ-মানুষীর জীবন শৈলীর কথাও সুন্দরভাবে বহন করে তাকে সীমায়িত পংক্তিতে কবিতার উপজীব্য বিষয় করেছেন। কবিতার শব্দমালিকায় ব্যক্ত হয়েছে কবির শিল্পিত মানসের অভিব্যক্তি। তিনি আধুনিক কবিতা লেখেন মন এবং মনন দিয়ে তাই তাঁর কবিতায় শিকড়ের প্রতি টান অনুভব করেন, ফলত এই কবির কাব্যে প্রকাশ পায় বাস্তব জীবনের কথাভাষ্য। তিনি বলেন—
ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে গেছে গেরস্থ আঙিনা থেকে ঘরে
চালবাটা শাদা শাদা অনেক যোজন লক্ষ্মীর পা।
আমরা দেখি না ঠিক; বুঝেও বুঝি না কোজাগরী—
রাত শুধু একবার আসে গৈরিক ধানের বুকে!
সাজি হাতে যে কিশোরী ভোরকুসুমের ঘ্রাণ-ডাক
ঘরে ঘরে নিয়ে আসে; শিল্পিত আঙুলে এঁকে যায়
মৃন্ময়ী আল্পনা, তাকে ডেকে জিগ্যেস করে কী—
জানা যাবে এত সব সারি সারি যদি লক্ষ্মীর পা
তবে কেন আমার মা চক্ষুজলে ভাসায় সকাল?
(লক্ষ্মীর পা, লক্ষ্মীর পা)
চালবাটা দিয়ে আলপানা দেয় কোজাগরী লক্ষ্মী পূজাতে এই বাংলার গৃহস্থ বাড়িতে বাড়িতে। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান চাক্ষুষ, দর্শনিক, পারক্ষিক সংশ্রয়ে কবি আবদ্ধ। মৃন্ময়ী আল্পনা গ্রাম বাংলার রমনীর সাংসারিক একান্ত সম্পদ। সংসারের মঙ্গল কামনায়, শ্রীবৃদ্ধির জন্য গ্রাম বাংলার নারী সমাজ বিশ্বাসে আলপনা দিয়ে থাকে। কবি কল্পনায় ধরা পরে বাস্তব অভিজ্ঞতা নিঃসৃত প্রজ্ঞা। এবং তা চিত্রকল্পের মাধ্যমে। সুররিয়ালিজম ভোরকুসুমের ঘ্রাণ-ডাক শব্দনিচয়ে ব্যক্ত হয় সুন্দরভাবে। খণ্ডসৌন্দর্য ও অখণ্ডসৌন্দর্যের আবিলতাকে ও উপলব্ধিকে কবি অসাধারণ মুন্সিয়ানার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। শাব্দিক প্রমিতি যেখানে আরব্ধ, সেখানে কবি শব্দলব্ধ চিত্রিতদৃশ্যকেও ভাসিত করে পাঠককুলকে ফাউ রস বিতরণ করতে পারঙ্গম হয়েছেন।
সময়ের গর্ভে বেদনা নিহিত। এখন তো অন্ধকার সময়। কবি বিষাক্ত সময়ের উল্লাসে হতমনা। দুর্বোধ্য দ্বিধাপ্রসূত সম্পর্কের নিরিখে কবি আজ ব্যথিত। রঙচঙে বখাটে শব্দের ভিড়ে ব্যবহৃত কবির শব্দেরা দিশেহারা, মায়াবী কল্পলোকে ভাববাদের প্রেষণা সত্যি আত্মহত্যা করে নিমেষে। তাই কবি বলেন—
কালো মেয়ে এসে ঠেলে দিচ্ছে
সাপের বিবরে। অমারাতে কারা দুপদাপ হেঁটে গ্যালো।
ভোর হতে দেখলাম ছোপ ছোপ রক্ত লেগে আছে রাশিঘাসে।
নিচু স্বরে কারা যেন কথা বলছে আড়াল রেখে।
চেনা যাচ্ছে, অথচ অস্পষ্ট মুখ ও মুখোশ হেঁটে যাচ্ছে
সবুজাভ গ্রাম ফেলে সামুদ্রিক বালিয়ারির গহীন ঘরে।
(ফিসফাস, লক্ষ্মীর পা)
কালো মেয়ে, সাপের বিবরে, অমারাতে, দুপদাপ, ছোপ ছোপ রক্ত, রাশিঘাসে, অস্পষ্ট মুখ, মুখোশ হেঁটে যাচ্ছে, সবুজাভ গ্রাম, সামুদ্রিক বালিয়ারির, গহীন ঘরে প্রভৃতি শব্দে দ্যোতিত হয়েছে এই বাস্তব জীবনের পিছনে অন্য এক জীবনের অনালোচিত অধ্যায়ের অনুষঙ্গ। কবি বিত্তবৈভবে সম্রাট। শাব্দিক সম্পদে রাজাধিরাজ; ধীমান কবি যশোপতি নিসর্গের চিত্রল বর্ণনায়। তাই কবি প্রথম জাগরণে, চেতনসত্তায় ছোপ ছোপ রক্ত লেগে থাকতে দেখেন। মুখ দেখেন তবে তা অস্পষ্ট। বেশি দেখেন মুখোশের ভিড়। কবি এখানে একাকিত্বের যন্ত্রণায় ভোগেন। বিষণ্ণ মনে তাই কবির তৃতীয় সত্তা পর্যবেক্ষণ করে সবুজাভ গ্রাম ফেলে সামুদ্রিক নোনতা হতবসন্তদূতের বালিয়ারির গহীন ঘরে চলে যাবার দৃশ্য।
কবি জীবনানন্দ দাশ ও বিনয় মজুমদারের সার্থক উত্তরসূরী কবি অমলেন্দু বিশ্বাস। পয়ার প্রীতি থেকে আহৃত জীবন দর্শনে ঋদ্ধ কবি মহাজীবনের অন্বেষণে সমাহিত। কবির কবিতায় অধিবাস্তবতাবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি অমোলায়েম সময় সম্পর্কে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলেন–
আমার হাঁটার পথ অপরাহ্ণ আলো
স্তব্ধ স্নানে মেতে উঠলে বোধে জাগে
প্রিয় সান্ধ্যভাষা। এই নীরব ভাষায়
বুনে যাচ্ছি অক্ষরের নতুন সরণি
এ, অনুচ্চারিত শব্দ বোবা পৃষ্ঠা জুড়ে
ভিখিরির যাচ্ঞা হাত; ও ফটিকজল!
(তিন, সান্ধ্যভাষা)
কবিতায় কবি বাকপ্রতিমা সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন। অপরাহ্ণ আলো, স্তব্ধ স্নানে, অক্ষরের নতুন সরণি, বোবা পৃষ্ঠা প্রভৃতি শব্দলতা চিত্ররূপময়তা তৈরি করেছে।
অপর একটি কবিতায় কবি চিরন্তনবানী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন—
আমি ডুবুরীর বেশে
অবগাহনে চেয়েছি একটি দ্যুতিময় প্রবাল।
বরং সে শ্বাসের ভেতর থেকে ছেড়েছিল সাপ
শীতলতার বদলে দিয়েছে উষ্ণ গরল, আর
প্রত্যাশার বুকে হাঙরের দাঁতালো কামড় শেষে
অন্য ডুবুরীকে দিয়েছে আশ্রয়; স্পর্শ শীতলতা।
প্রচণ্ড যুদ্ধের পরে দীঘির ওপারে উঠে, প্রত্যাশার জাল
ফেলে বসে থাকি সারাদিন; ক্ষতস্থানে মাটি চাপি।
(ডুবুরী, ডুবুরী)
এখানে কবি নতশিরে মেনে নিয়েছেন সামাজিক বিধি। বাস্তবজীবনের বাকপ্রতিমা সৃষ্টিতে কবি সিদ্ধহস্ত। উপরের কবিতাটিতে কবি অতিদ্রুত অনেকগুলো সম-বিজাতীয় বিষয় ও ভাবের আমদানি করেছেন: শ্বাসের ভেতর থেকে ছেড়েছিল সাপ, উষ্ণ গরল, হাঙরের, দাঁতালো কামড়, স্পর্শ শীতলতা (tactile–স্পর্শ- বিষয়ক বাকপ্রতিমা এখানে কবি অসামান্য দক্ষতায় লেখনির সাহায্যে প্রকাশ করেছেন।), প্রত্যাশার জাল, ক্ষতস্থানে মাটি চাপি। এক ধরনের সমজাতীয় বিষয় উপস্থাপনার মধ্যেও কবি কবি শেষ পর্যন্ত সমন্বয়ের সূত্র খুঁজে পান।
সাম্প্রতিককালে image এবং imagery (বহু image যখন একত্রিতভাবে পাশাপাশি বসে বিচিত্র ভাব অনুভূতি প্রকাশ করে থাকে) সম্পর্কে নানা আলোচনায় নানা ধরনের image বা বাকপ্রতিমার উপস্থিতিকে স্বীকার করা হয়। যেমন-kinesthetic(গতির অনুভূতি বিষয়ক), ugly beauty( কুৎসিত সৌন্দর্য বিষয়ক), esthetic (নন্দনতত্ত্ব- বিষয়ক), auditory(শ্রবণ -বিষয়ক), tactile(স্পর্শ- বিষয়ক), olfactory(গন্ধ বিষয়ক) প্রভৃতি। কবি অমলেন্দু বিশ্বাস তাঁর কাব্যময় ভুবনে এসমস্ত বাকপ্রতিমা সৃষ্টি করেছেন অসামান্য দক্ষতায়। তাঁর কবিতাকে কাটাচেরা করলে আমরা বিচিত্র ব্যঞ্জনার পাশাপাশি চকিতে অন্যজগতে পৌঁছে যাই।#