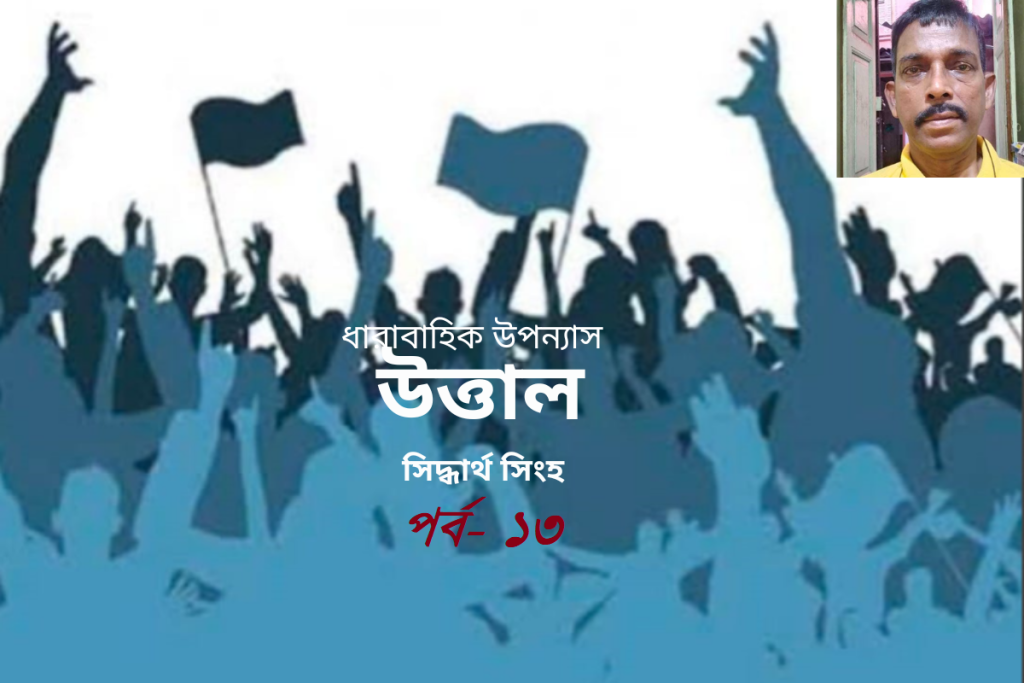।।তেরো।।
এক সময় কারও জমি পছন্দ হলেই, জমিদাররা হয় লেঠেল পাঠিয়ে সে জমি কেড়ে নিত, নয়তো নানা রকম ফন্দিফিকির করে তাকে ফাঁদে ফেলে এমন নাস্তানাবুদ করত যে, জমির মালিক ‘ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি’ বলে, জমিজমা সব ছেড়েছুড়ে পালাত।
ইংরেজদেরও কোনও জায়গা পছন্দ হলে, সেখানে যে-ই থাকুক না কেন, তাকে রাতারাতি উচ্ছেদ করে সেখানে থাবা বসাত।
যুদ্ধের সময়ও সেনাদের ছাউনি করার জন্য কত লোকের কত জমি যে নিয়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই। নিয়ম ছিল, প্রয়োজন মিটে গেলে যার জমি তাকে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা হয়নি। ফলে ও পার বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা লোকেরা সে সব জায়গায় ছাউনি ফেলে থাকতে থাকতে দখল করে নিয়েছিল। গড়ে তুলেছিল কলোনি। পরে তো সে সব জমির পাট্টাও পেয়ে গেছে তারা। সেটা অন্য গল্প। কিন্তু যাদের জমি, সে-ই যে বেহাত হয়েছিল, তাবা কিন্তু আর ফেরত পায়নি।
শুধু এখানে নয়, গোটা পৃথিবীতেই এই একই ছবি। মানুষ সব কিছু করতে পারে, কিন্তু জমি তো সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু কোনও কিছু করতে গেলেই জমির দরকার। তাই জোর করে থাবা বসিয়ে জমি দখল করে। অন্যকে হটিয়ে নিজেরা বসে।
যারা গাড়ির কারখানা করবে বলে জমি দেখতে এসেছে, তারাও নিশ্চয়ই ছলে-বলে-কৌশলে জোর করে তাদের জমি কেড়ে নিতে এসেছে। এক্ষুনি না আটকালে, পরে আর কিচ্ছু করা যাবে না। মুখে মুখে এই খবর রটে যেতেই শুধু ওই গ্রামই নয়, আশপাশে যত গ্রাম ছিল, সেই সব গ্রামের লোকেরা হাতের কাছে যে যা পেয়েছিল, দা, লাঠি, কুড়ুল, কাস্তে নিয়ে ছুটে এসেছিল। ঝামেলা হতেই পারে, আন্দাজ করে প্রচুর পুলিশ নিয়ে এসেছিল ওরা। ভেবেছিল, গ্রামের লোক! বাধা দিতে এলেও, পুলিশ দেখলেই ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু ওরা যখন দেখল, পিলপিল করে গ্রামবাসীরা ছুটে আসছে, আর ওদের সংখ্যার কাছে তাদের সংখ্যাটা নেহাতই নগণ্য। তখন তড়িঘড়ি গাড়ি ঘুরিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ওরা। এটা দেখে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা বললেন, কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো যায় না।
তখনও গ্রামবাসীরা সে ভাবে এককাট্টা হয়নি। সেই প্রথম জমির জন্য সবাই মিলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়া।
আরও পড়ুন: গারো পাহাড়ের চিঠি: ঘোড়া ও রওশন সার্কাস
গ্রামের লোকেরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার আগেই কাজ হাসিল করতে হবে, তাই একশো বছরেরও আগে ১৮৯৪ সালে ইংরেজ আমলে যে ‘ভূমি অধিগ্রহণ আইন’ লাগু করা হয়েছিল, পুঁজিপতিদের সুবিধে করে দেওয়ার জন্য, তার ঠিক একশো বছর পরে, ১৯৯৪ সালে সেটাকেই আরও সংশোধন করা হয়েছিল। যাতে ‘জনস্বার্থ’-র অজুহাত দেখিয়ে যে কোনও জমি অধিগ্রহণ করাটা সরকারের পক্ষে সহজ হয়। আইনসিদ্ধ হয়। সেই আইনটাকেই সরকার এখানে বলবৎ করতে চাইল।
তাতে যদি ছ’হাজার পরিবার-সহ বহু খেত মজুর এবং ভাগচাষি তাদের জীবন-জীবিকা হারিয়ে পথে বসে, তো বসুক। এমনিতেই গ্রামের একটা বড় সংখ্যক চাষিকে আর খাইয়ে-পরিয়ে রাখতে পারছে না চাষবাস। নব্বই দশকের পর থেকে বিশ্বায়ন আর অন্যান্য কারণে কৃষি সে ভাবে আর লাভজনকও নয়। অন্ধ্র থেকে মহারাষ্ট্র, এমনকী যে রাজ্যকে ভারতের শষ্য ভাণ্ডার বলা হয়, সে-ই পঞ্জাব থেকে দাক্ষিণাত্য, সব জায়গা থেকেই খবর আসছে, চাষিরা ঋণে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। এক্ষুনি যদি এ রাজ্যের চাষিদের বিকল্প কোনও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা নাযায়, তা হলে সারা রাজ্যের উপরে কালো ছায়া ঘনিয়ে আসতে বেশি দিন লাগবে না। এ রাজ্যের একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমি সেটা রোধ করতে চাই।
কেউ যদি চাষিদের কাছ থেকে কম টাকা দিয়েও জমি নেয়, তা হলেও ওরা অন্তত প্রাণে বেঁচে যাবে। আর আমরা তো ওদের শুধু উপযুক্ত মূল্যই দিচ্ছি না, তার থেকে অনেক অনেক বেশি দাম দিচ্ছি। তাতেও ওরা রাজি হচ্ছে না কেন?
অকাট্য যুক্তি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের এই জিজ্ঞাস্য ভেবে দেখার মতো। কেন ওরা জমি দিতে চাইছে না? কেন?
এই প্রশ্নের তেমন কোনও জুতসই উত্তর খুঁজে না পেয়ে ভিতরে ভিতরে ছটফট করছিলেন নবীন মাস্টার। তিনি আসামাত্র তেরো নম্বর মারফত মুখে মুখে রটে গিয়েছিল তাঁর আসার খবর। তাই তাদের অভাব, অভিযোগ, সমস্যা জানানোর জন্য গ্রামের লোকেরা দল বেঁধে ভিড় করেছিল তেরো নম্বরের বাড়ির উঠোনে।
কাউকেই উনি চেনেন না। কিন্তু সেই প্রশ্নটা তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তাই প্রথমেই গণেশ, শিবু, রতন, কার্তিক, হাবলুর দিকে ওই প্রশ্নটাই ছুড়ে দিয়েছিলেন তিনি।
গণেশ বলল, জমি বেচে টাকা নিলে, সেই টাকা আমরা রাখতে পারব না। অত টাকা তো কখনও কোনও দিন নাড়াচাড়া করিনি। ফলে বুঝতে পারব না। জলের মতো খরচ হয়ে যাবে। সেই টাকা ফুরিয়ে গেলে খাব কী? জমি থাকলে খাটব, খাব। আমার ছেলের ছেলেরাও খেটে খেতে পারবে। জমি দেব কেন?
নবীন মাস্টার বললেন, কিন্তু আসার সময় যে শুনলাম, অনেকেই নাকি জমি দিয়ে দিচ্ছে…
থাকতে না পেরে গলা চড়াল হাবলু– হ্যাঁ, দিচ্ছে। কিন্তু কারা দিচ্ছে? যাদের সঙ্গে জমির কোনও যোগ নেই, তারাই দিচ্ছে। আমাদের পাড়াতেই তো একজন আছে। যাঁর জমি ছিল, তাঁর নাতির ছেলে এখন মালিক। গত দু’পুরুষের কেউই কোনও দিন ওই জমির দিকে পা-ই মাড়ায়নি। তার জমিটা যে মাঠের ঠিক কোন জায়গায়, সেটাও হয়তো সে বলতে পারবে না। কলকাতার কোথায় যেন থাকে। এখন জমির জন্য সরকার টাকা দিচ্ছে শুনে টাকা নিতে চলে এসেছে। আমরা তো ওদের মতো নই। এখানে জন খেটে খেটে টাকা জমিয়ে অনেক কষ্ট করে জমি কিনেছি। যে দেবে দিক। আমার জমি আমি কিছুতেই দেব না।
শিবু বলল, যারা নিজেরা চাষ করে, তারা প্রায় কেউই জমি দেয়নি। আমাদের গ্রামের দুশো ঘরের মধ্যে কেবল পনেরো ঘর জমি দিয়েছে। জানবেন, যাদের কাছে জমি রাখা হ্যাপা, যারা চাকরি-বাকরি পেয়ে বাইরে থাকে, সপ্তাহে বা মাসান্তে দু’-একবার আসে, তারাই জমি দিচ্ছে।
রতন বলল, ঘড়ার জল কি সারা জীবন থাকবে? আজ টাকা নিলে কাল শেষ। তার পর? আগে যখন টাকা-পয়সা থাকত না, তখন ঘরের চাল ফুটিয়ে, খেতের আলু-লঙ্কা দিয়ে খেয়ে নিতাম। জমি বিক্রির টাকা যে দিন শেষ হবে, সে দিন কী করব?
– জমি থেকে কি তোমাদের তেমন লাভ হয়?
কার্তিক বলল, কী বলেন? আমাদের জমি শুধু জমি না। সোনা। ধানটা কেটে নিলেই আলু। আলু খেতের মধ্যেই কপি, বেগুন, সরষে আর কুমড়ো। একটা ফসলের মধ্যে তিন মাসে আরও চারটে ফসল হয়। একই জমিতে। তার পর পাট, তিল এবং আবার ধান।
গণেশ বলল, চাষে লাভ না হলে আমরা দিয়ে-থুয়ে মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছি কী করে? ঘরদোর বানাচ্ছি কী করে? সংসার চালিয়ে ডাক্তার-বদ্যি করেও দু’-এক বিঘে জমি কিনছি কী করে? লাভ না হলে কি এগুলো করতে পারতাম?
নবীন মাস্টার জিজ্ঞেস করল, মোটামুটি কী রকম লাভ হয়?
গণেশ বলল, সিজিনের সময় ধান চাষ করে বিঘে প্রতি খরচ-খরচা বাদ দিয়ে দেড়-দু’হাজার টাকা লাভ তো থাকেই। তার পরেও আছে অন্যান্য চাষ। শুধু আলু চাষেই প্রতি বিঘেতে তিন মাসে লাভ হয় কম করে সতেরো-আঠেরো হাজার টাকা।
রতন বলল, সবজির মধ্যে সবচেয়ে ভাল হয় ঢ্যাঁড়স। শীতের সময় গাছ করতে লাগে পঁয়তাল্লিশ দিন। তার পর একদিন অন্তর টানা চার-পাঁচ মাস ধরে ট্যাঁড়স তোলা চলে। যার তিন বিঘে জমি আছে, সেও ট্রাক্টর কিনে নেয়।
শিবু বলল, আমাদের গ্রামে এত সবজি চাষ হয় যে, বাইরের লোক এখানে এসে জমির আশপাশে পলিথিন খাটিয়ে রাত কাটায়। ভোররাতে ঝাঁকা ভরে সবজি কিনে নিয়ে কোলে মার্কেট বা হাওড়াতে বেচতে চলে যায়।
কার্তিক বলল, সরকার তো মাত্র দুটো ডিপ টিউবয়েল করে দিয়েছে। লাভ না থাকলে এখানকার চাষিরা কি নিজেদের টাকায় আরও ছাব্বিশটা মিনি টিউবয়েল বসাতে পারত?
আরও পড়ুন: ধারাবাহিক উপন্যাস ‘উত্তাল’ ১২
নবীন মাস্টার এতক্ষণ খেয়াল করেননি, তাঁর কথা শুনে গ্রামের আরও অনেকে একে একে আসতে শুরু করেছেন তেরো নম্বরের দাওয়ায়। এসেই পিছন দিকে বসে পড়ছেন। হঠাৎ তাঁদের মধ্যে থেকে হাড়গোড় বেরোনো কালো মতো একটি লোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার জমি নাই। জন খাটি। বাইরের থিকা প্রতি বছর জন খাটতি এখানে লোক আসে। আমরাও আইছিলাম। এখন এখানেই থাইকা গেছি। কাজের জন্য আমাদের আর কোথাও যাতি হয় না। চাষে লাভ না হইলে জন রাইখা কেউ চাষ করাত?
আরও একজন বললেন, এখানে ঘর বেঁধে আছি। অন্যের জমিতে চাষ করি। গরু-ছাগল আছে। হাঁস-মুরগি পুষছি। মাছ ধরি। খুব ভাল আছি। এখান থেকে যেতে বললেই চলে যাব? শহরে গিয়ে কি ভিক্ষে করব?
তার কথা শেষ হওয়ার আগেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন আর একজন। তিনি বললেন, আমরা আগে বেগমপুরে তাঁতের কাজ করতে যেতাম। সুতো দিয়ে শাড়ি বুনতাম। সকালে বেরিয়ে রাত ন’টা-সাড়ে ন’টায় ফিরতাম। রোজ পঞ্চাশ টাকা করে পেতাম। ছেড়ে দিয়েছি। কারণ, এখানে কাজ করলে তার থিকা বেশি পাই। বিঘেতে বারো বস্তা ধান হলে ভাগচাষি হিসেবে দশ বস্তা আমি পাই। দু’বস্তা জমির মালিক। ঘরে ছ’টা ছাগল, একটা গরু, দুধ বেচে রোজ পঁচিশ-তিরিশ টাকা পাই। মাছও ধরি। খাটতে পারলে অভাব কীসের? কে বলে জমিতে আয় নাই?
তার পাশেই বসে ছিলেন এক ভদ্রমহিলা। গ্রামের বউ মানেই কলাবউয়ের মতো এতখানি ঘোমটা দেওয়া। লাজুক। অচেনা পুরুষের সামনে মুখ তুলে কথা বলতে পারে না। এমন ছবিটাই নবীন মাস্টারের মনের মধ্যে ধরা ছিল। সেটাকে ভেঙে চুরমার করে দিতেই যেন সেই মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে নয়, সটান রুখে দাঁড়িয়ে বললেন, এই জমির আয় থিকাই তো খাইয়া-পইরা পাঁচ-পাঁচটা মাইয়ার বিয়া দিসি। পাকা ঘর করসি। ছ’টা গরু কিনসি। আরও দু’বিঘা জমি কিনসি। আর ওরা বলতাছে কিনা জমিতে আয় নাই, বেইচা দাও। কেন রে বাপু, আমার লাভ হয় কি না, তোদের কাছ থিকা জানতে হইব?
নবীন মাস্টার বুঝতে পারলেন, এরা তেতে আছেন। সামনে মহাবিপদ। তাই এক শামিয়ানার নীচে এসে দাঁড়িয়েছেন জমির মালিক, প্রান্তিক চাষি, বর্গাদার, নথিভুক্ত নয় এমন বর্গাদার, খেতমজুর এবং জনমজুর। যে দেশে বন্যার সময় বাড়িঘর ডুবে গেলে একই গাছের ডালে আশ্রয় নেয় বিষাক্ত সাপ আর অসহায় মানুষ। কেউ কারও ক্ষতি করে না। সে দেশে বিপদের সময় একটা মানুষ আর একটা মানুষের পাশে দাঁড়াবেন না! তাঁরা এককাট্টা হবেন না? হবেনই। কিন্তু এঁদেরকে সঠিক পথ দেখাবে কে? বুদ্ধি দেবে কে? যদি তেমন কেউ হাল ধরেন, পুরো ছবিটাই পালটে যাবে। কিন্তু সেই হালটা ধরবে কে? কে? ভাবতে না ভাবতেই নবীন মাস্টারের মাথার মধ্যে ভিড় করতে লাগল একটার পর একটা মুখ।
চলবে…