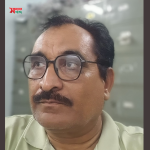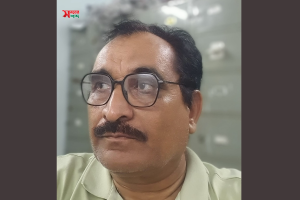মানব প্রজাতির অবিচ্ছ্যে দুটি অংশ নারী ও পুরুষ। একসঙ্গে উভয়ের যাত্রা। একই রোদ বৃষ্টিতে উভয়ের অবগাহন। মানুষ হয়ে ওঠা। সামাজিক মানুষ হয়ে ওঠা। সভ্য মানুষ হয়ে ওঠার সংগ্রাম। উষালগ্নের বেলা ভূমি থেকে ছিল সমভাবে নারী ও পুরুষের অনলস সংগ্রামের সূচনা. এই চলার পথে একদিন দেখা দিল অঘটন। পুরুষ একা অধিকার করে বসল সমাজ-অর্থনীতির মূল দণ্ডটি। ফলে, তারপর থেকে দীর্ঘ যাত্রাপথে পুরুষ ও প্রকৃতির একটি কোরক হল প্রস্ফুটিত। অপরটি আধফোটা থাকল।
কর্মজীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র জুড়ে গড়ে উঠল পুরুষ প্রাধান্য। পুরুষ নিয়ন্ত্রণ। নারীরা কখন, কেমন করে যেন হয়ে পড়ল পিছিয়ে পড়া সঙ্গিনী। সুদূর অতীতের জানা ইতিহাস-কাল থেকে নানাভাবে চলে আসছে পুরুষ-প্রাধান্য। সক্রিয় উদ্যোগী পুরুষের পাশাপাশি নারী হয়ে পড়েছে এক নিষ্ক্রিয় সত্তা-আত্ম সমর্পণে যার অস্তিত্ব, পরনির্ভরতা যার বিধি, পুরুষ সম্পর্কে যার পরিচয়।
আমাদের জানা গোটা ইতিহাসটাই হল পুরুষ প্রাধান্যের ইতিহাস-পিতৃতন্ত্রের ইতিহাস। এর আগে কী ছিল বা ভবিস্যতেই কী হবে- তা নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তার অবকাশ আছে, কিন্তু যা চলছে তা অবয়বে পুরুষতন্ত্র নানাভাবে প্রকাশিত।
সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার যেগুলি মৌল বিষয় অর্থাৎ শিল্প-কৃষি খনি-শক্তি ও পরিবহণ, তার সর্বত্রই নিয়োজিত পুরুষ। তাতে নারীর অংশ গ্রহণ ব্যতিক্রমের মত। বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কীয় মানব মনীষার গুরুত্বপূর্ণ চর্চার ক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থান নগণ্য। ফলে, উৎপাদনের সংগ্রামেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার সংগ্রামের ভিতর দিয়ে মন ও দেহের বিকাশের যে সুযোগ, এতে অংশগ্রহণের ভিতর দিয়ে সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অবস্থানের যে প্রয়োজন তা থেকে নারী সমাজ বঞ্চিত। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রশ্নে-প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা ও সরকারে নারীর অংশগ্রহণ অকিঞ্চিৎকর। আর সমগ্র ক্ষমতার কেন্দ্র পুলিশ- মিলিটারীতে তো নারী সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। ফলে সামাজিক রথ যার হাতে সারথির লাগাম নেই, রক্ষকের অস্ত্র নেই, সরবরাহের দায়িত্ব নেই- তার পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্তরে অবনমিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। নারী তাই এ সমাজে উৎপাদনকারী নয়-ভোগকারী। এই অবস্থার সুযোগেই পুরুষ নারীকে করে রেখেছে অবদমিত।
উৎপাদন ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে যে উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে-মালিক শ্রমিক বা জমিদার-কৃষক, কিংবা রাজনীতিগতভাবে যে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেখানে বলা বাহুল্য নারী পুরুষ ভেদাভেদ বিচার্য বিষয় নয়। কারখানার মালিক কারখানার শ্রমিককে শোষণ করবে। মালিক বা শ্রমিক পুরুষ কি নারী তাতে কোন হেরফের হয় না। শোষক-শোষিতের সম্পর্ক নারী-পুরুর সম্পর্ক নির্ভর নয়। কিন্তু পুরুষতন্ত্র নারীর উপর যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, পুরুষতন্ত্র নারীর যে অবমূল্যায়ন করেছে তা গোটা পুরুষ ও গোটা নারী জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ধনি শ্রেণীর ঘরের নারীর অবস্থান আর গরীব সমাজের ঘরের নারীর অবস্থানের ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ একই চিত্র তুলে ধরে।
পুরুষতন্ত্র নারীকে প্রথমেই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে; ধর্মীয় ভাবে, সামাজিক বিধিনিষেধের মাধ্যমে নারীর একটি বিচিত্র রূপ ও বিচিত্র অবস্থান নির্ধারিত করেছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রচার করা হয়ে এসেছে যে দৈহিক দিক থেকে এবং মস্তিষ্কের দিক থেকে নারী দুর্বল-পুরুষের সমকক্ষ নয়। এই লক্ষ্যে নারীর দৈহিক শক্তি, মানসিক ক্ষমতা ও যৌনজীবনকে পুরুষের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নানারকম ভাবে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে। সবল-দুর্বল, সক্রিয়- নিষ্ক্রিয়, দাতা-গ্রহীতা প্রভৃতি চরিত্রে মানবসমাজের দুটি অংশ পুরুষ ও নারীকে বিভক্ত করে ফেলা হয়েছে।
নারীকে এই ভাবে চিত্রিত করার পুরুষতান্ত্রিক প্রয়াসের দুটি দিক লক্ষ্য করা যার- একটি হল নারীকে অক্ষম, দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় রূপে চিত্রিত করা এবং অন্যটি হল নারীকে ভিন্ন রূপে চিহ্নিত করা। দ্বিতীয় ধারাটি চলেছে ধর্মীয়ভাবে। প্রথম ধারাটি চলেছে সামাজিক ভাবে। সামাজিক ভাবে নারীকে অক্ষম, দুর্বল, নিস্ক্রিয় দেখাবার জন্য এমন কি সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও মনস্তাত্ত্বিক শাখাকে পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে। আর ‘নারী নরকের দ্বার’ প্রমাণ করবার জন্য তো চলে এসেছে যুগ যুগ ধরে এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মের অব্যাহত প্রয়াস।
মানবসমাজ যে একা। পুরুষ-সমাজ নয়- হওয়া সম্ভব নয়, এই বৈজ্ঞানিক অনিবার্যতার কারণে, অপরিহার্য নারীকে পুরুষ এক অভিনব রূপে চিত্রিত করেছে। এই নারী সালঙ্কারা-রূপসী। রূপের স্তুতি আর অলঙ্কারে সজ্জিত করার ভিতর দিয়ে নারীকে স্বতন্ত্রসভাহীন পুরুষপ্রিয়া রূপে গড়ে তোলা হয়েছে। তারই প্রয়োজনে নারীকে কখনও গড়ে তোলা হয়েছে অলঙ্কার-ভূষিতা রূপসী সজ্জায়, কখনও চিত্রিত করা হয়েছে নিবাবরণ সলজ্জ সজ্জায়।
কিন্তু পুরুষ-প্রাধান্যে চাপা পড়ে থাক। নারী সুদূর অতীতে এমন ছিল না। পুরুষতন্ত্রের ওপারে ঠিক কী ছিল তার সুস্পষ্ট ছবি আজ আমাদের সামনে নেই। বিশেষতঃ পুরুষ-রচিত সাহিত্য, ইতিহাস থেকে নারীর সঠিক খবর পাওয়া আরো কঠিন। শোষক শ্রেণীর রাজত্বে তাদের রচিত রচনায় যেমন শোষিতের প্রকৃত ছবি খুঁজে পাওয়া যায় না, পুরুষ-রচিত ইতিহাস, সাহিত্যে তেমনি নারীর প্রকৃত চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেদিনের নারী যে আজকের নারীর মত নিষ্ক্রিয়, আত্মসমর্পণমুখী ছিল না, তারা যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করত তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
এশিয়া মাইনরে তুরস্কের ভূখণ্ডে আনাতোলিয়া বলে একটি জায়গায় বিশ্বের প্রাচীনতম শহর কাটাল হুয়ুক আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে খননকার্য চালিয়ে যে জীবনযাত্রার ছবি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, মেয়েদের ছিল সর্বত্র অবাধ গতিবিধি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। মার্সিন ও হাসিলার- এর খননকার্য থেকেও একই চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সব জায়গায় সযত্বে স্থাপিত কবরে বেশীরভাগ পাওয়া যায় নারীর কঙ্কাল। দেওয়ালের গায়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষিত আছে বহু জায়গায়, নারীর স্তনযুগলের চিত্র ও ভাস্কর্য। বর্বর যাযাবর জাতির আক্রমণে পরাস্ত নারী সম্রাজ্ঞীদের শাসন ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষ এই সমস্ত জায়গায় খুঁজে পাওয়া যায়।
ক্রিটের সভ্যতার অনুসন্ধানে খননকার্য চালিয়ে তখনকার জীবনযাত্রার যে সমস্ত স্বাক্ষর পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় মহিলারা রথ চালনা করছে, শিকার পরিচালনা করছে, বিচার সভায় সভাপতিত্ব করছে, পুরুষের হাত থেকে অর্থ গ্রহণ করছে। অর্থাৎ সামাজিক কাজের প্রধান সমস্ত ক্ষেত্রেই নারী গুরুত্বপূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করছে।
সুমের টিয়ামতকে বলে মৎস্য ন্য অর্থাৎ বিশ্বের স্রষ্টা। সে মানুষকে জীবনের অর্থ শেখাল। শহর গড়তে শেখাল। শেখাল মন্দির গড়তে। সে এসেছিল এগিরাকান অর্থাৎ পারস্য উপসাগর থেকে।
হেলেনিক গ্রীকদের মতে পাঁচটি যুগ অতিক্রম করে এসেছে মানব সভ্যতা। প্রথম যুগ স্বর্ণযুগ- যখন কোন শাসক, দেবতা বা রাজা ছিল না। সে যুগ হারিয়ে গেছে। দ্বিতীয় যুগ: বৌপ্যযুগ- বহু হাজার বছর ধরে চলে এসেছিল এ যুগ। যে সময় পুরুষরা মেয়েদের কথা শুনত, সে একশ বছরের বৃদ্ধ হলেও। তৃতীয় যুগ: প্রাথমিক ব্রোঞ্জ যুগ- যখন ক্রিট সমস্ত এজিয়ানদের এবং পৃথিবীকে শাসন করত। চতুর্থ যুগ: পরবর্তী ব্রোঞ্জ যুগ-এটা হল গ্রীসের বীরদের যুগ এবং পঞ্চম যুগ: লৌহযুগ- ট্রোজান যুদ্ধের পর এই যুগের সূত্রপাত। এই সময় থেকে দেবী, পুজা বন্ধ হয়। দেখা দিল নতুন দেবতা জিয়াস।
বিক্ষিপ্তভাবে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে স্ত্রীজাতির অংশ গ্রহণের অসংখ্য দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় নানাদেশের বিশাল প্রাক্ এবং ঐতিহাসিক কাল জুড়ে। মেয়েদের লাইন ধরে রাজ-ক্ষমতা, অধিকার, আরাধ্য মূর্তিতে দেবীর প্রাধান, স্ত্রীজাতি সম্পর্কে ভয় ও শ্রদ্ধার ভাব প্রভৃতি ঘটনা সারা পৃথিবী জুড়েই অপসৃয়মান হলেও থেকেই দিয়েছে।
ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে, সভ্যতার স্রষ্টা হল হেবল ও কেইন। কেইন হল নারী প্রাধান্যের প্রতীক। হেবাল কথার অর্থ হল, যে জন্ম দেয়। সুমেরদের দেবী টিবির এবং টিবিরা থেকে এই শব্দের উৎপত্তি বলে অনুমান করা হয়। মিশরে সৃষ্টির দেবী আইসিস, সিরিয়াতে টিয়ামাত, গ্রীসে রিয়া, রোমে বোনা ডিয়া প্রভৃতি নারী প্রাধান্যের পরিচায়ক।
পারস্যে সাইরাস রাজা হন সম্রাট এটাইজেস-এর মেয়েকে বিয়ে করে, আর দারায়ুস রাজা হন সাইরাসের মেয়েকে বিয়ে করে। পুত্র রাজা হন নি। রাজা হন দারায়ুসের বিধবা পত্নীর দারায়ুসের মৃত্যুর পর তাঁর আগের স্বামীর পুত্র খেরেখেস। ফোনেশিয়াতে শাসক ছিলেন রানী ভিভো। তিনি কার্থেজ শহর পত্তন করেন। তাঁর মেয়েদের থেকে শাসকের ধারা চলে আসে।
রোমে প্রথম ট্রাইব শাসক হিসাবে দেখতে পাওয়া যায় একজন মহিলাকে। হিব্রু সাহিত্যে সর্বপ্রাচীন গোষ্ঠীর নেত্রীর যে নাম পাওয়া যায় তা নারীর। ক্লডিন কুইনটার ধারা থেকেই রুভিয়ান রাজপরিবাবের সূত্রপাত। কনস্টানটাইন বাজা হন ম্যাক্সিমিয়ানের মেয়েকে বিয়ে করে।
অসিরিয়ার প্রত্নতাত্বিক স্বাক্ষর থেকে দেখা যায় যে রাণী সেবা থেকে রাণী চেনবিয়া পর্যন্ত গোটা পর্বে প্রাধান্য ছিল সম্রাজ্ঞীদের। প্রাক মুসলিম সাহিত্যে মৈয়া বিন্ত আফজারের মত মহিলাকে বারবার স্বামী বদল করতে দেখা যায়।
ক্রিট দ্বীপে এভিয়ানদের মধ্যে নারী প্রাধান্য দিল। প্রুটাক বলেছিলেন- স্পার্টার মেয়েরাই গ্রীসের একমাত্র মহিলা যারা পুরুষের উপর শাসন করত। সুমেরীয় আইন উন নাস্মু, দিপিত ইশতার এবং হাম্বুরাবি কোড থেকে জানা যায় যে ইশথার মন্দিরে পুরুষদের সেবাদাস নিয়োগ করা হত। তাদের এমন কি বেশ্যাদের যত মেয়েদের জন্য দেহদানও করতে হত। এদের সম্পর্কে বলা হত যে ইশথার এদের পুরুষত্বকে নারীত্বে পরিবর্তন করে দিয়েছেন।
মিশরেও মেয়েদের ধারাতে শাসক হবার অনেক উদাহরণ আছে। স্বয়ং ক্লিয়োপেট্রা ভাই থাকতেও রানী হন। হাটশেপসুট দুই ভাই খাকতেও নিজে ফারাও হন। হেরোডোটাস মিশরে মেয়েদের বাণিজ্য দেখাশোনার কাজে নিয়োজিত থাকতে দেখেছিলেন। মিশরের স্ফিংক্স হল পশুর উপর নারী মূর্তি।
ইহুদী পুরাণে রেবেকা, সারা, রাকেল, লিয়া প্রভৃতি হল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উল্লেখযোগ্য মহিলা চরিত্র, যাদের পাশে পুরুষ-চরিত্র আব্রাহাম, আইজাক, র্যাকব নিতান্তই অনুজ্জ্বল।
কুন্তির নাম থেকে পঞ্চ পাণ্ডবকে কৌন্তেয় বলা, প্রৌপদীর নায় থেকে তার পাঁচ পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেনকে দ্রৌপদেয় বলা মাতৃধারার পরিচয় বহনের স্বাক্ষর। উত্তরকুক ও মহেশমতীতে নারীকে আবদ্ধ করার জন্য বিয়ে বলে কিছুর প্রচলন ছিল না, এ কথা মহাভারতে বলা হয়েছে। রামচন্দ্রের মত বীরকেও, সীতাকে লাভ করতে হলে পরীক্ষা দিতে হয়। দ্রৌপদীকে পেতে হলে অবিসংবাদিত বীর অর্জুনকেও প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। কালিদাসকে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করতে গিয়ে পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এসব কিছু নারীর চলে আসা গুরুত্বের টিকে ধাকা প্রথার পরিচায়ক উদাহরণ।
দেবদেবীর নামের ভিতর দেখা যায় অনেক দেশেই দেবীর প্রাধান্য ছিল দীর্ঘদিন এবং প্রধান আরাধ্য ছিল দেবী। এথেনিয়ানদের দেবী এখেন, সাইপ্রিয়ানদের ভেনাস, ক্রিটানদের ভায়ানা, সিসিলিয়ানদের প্রোসারপাইন, মিশরীয়দের আইসিস, ব্যাবিলিয়ানদের ইশথার, ফোনেশিয়ানদের আসটাও বা এ্যাসটোরেখ, এশিয়া মাইনরে সাইবেল, ভারতে আদিবাসীদের দেবী কালী, মনসা প্রভৃতি দেবীর প্রাধান্যের উদাহরণ।
ক্রমশ…