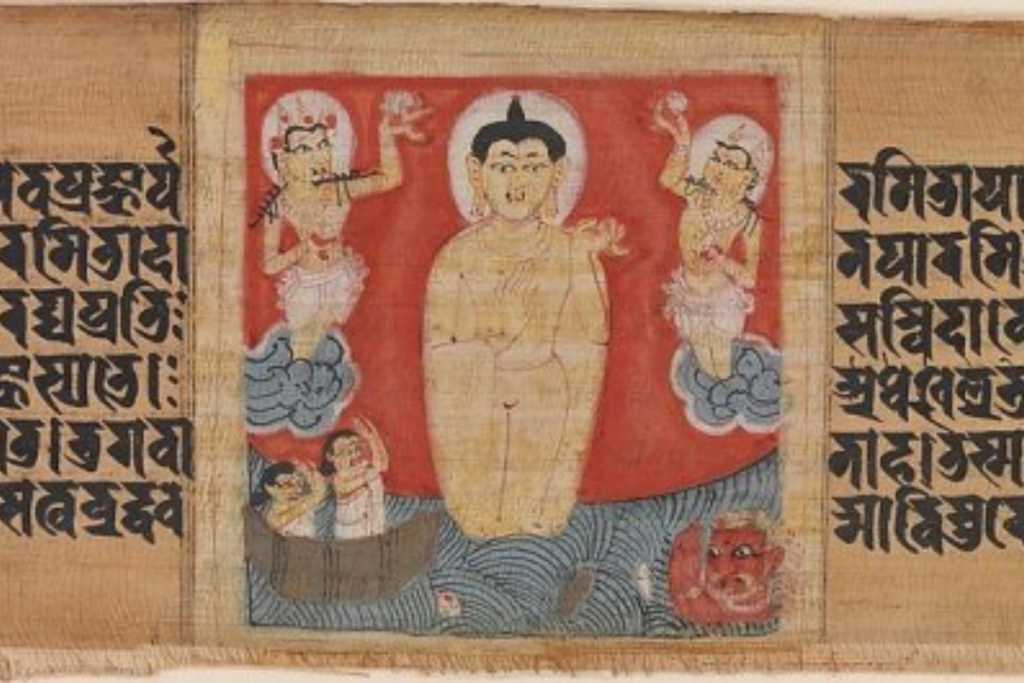বাংলা সাহিত্যে প্রথম কাব্যোসমালোচনা বোধহয় বিজয় গুপ্তেরই। মনসামঙ্গলের কাহিনি কবে নারীসমাজের লৌকিক ব্রতকথা থেকে পুরুষ সমাজের উপভোগ্য কাহিনিতে পরিণত হল, তা বলা কঠিন। বোধহয় হরিদত্তই ছিলেন এই ব্রত পাঁচালির প্রাচীন ও আদিতম রূপকার। তাঁর গ্রন্থের উল্লেখ কেবল বিজয় গুপ্তের পুথিতেই মেলে। পরবর্তীকালে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ময়মনসিংহের দীঘপাইত গ্রাম থেকে একটি ছিন্ন পুথির পাতড়া আবিষ্কার করেন। তার পাঠোদ্ধার করে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, হরিদত্তের লুপ্তপ্রায় পুথির এটি একটি পৃষ্ঠা হতে পারে। দীনেশ্চন্দ্র সেন তাঁর ‘বঙ্গসাহিত্য পরিচয়’-এ ও পরবর্তীকালে আশুতোষ ভট্টাচার্য সংকলিত ‘বাইশা কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা’-তে ওই পৃষ্ঠাটির পাঠ মুদ্রিত হয়েছে। হরিদত্ত ভাগ্যদোষে কানা ছিলেন। বিজয় গুপ্ত তাঁর এই শারীরিক ত্রুটির উল্লেখ করেছেন। সেইসঙ্গে কাব্যের শ্রী ও সৌষ্ঠব এবং কাব্যত্ব যে-সব বিষয়গুলির ওপর নির্ভর করে হরিদত্তের রচনায় তার যথেষ্ট অভাব লক্ষ করেছিলেন পণ্ডিত (মন্য) কবি বিজয় গুপ্ত। তাঁর এই সমালোচনা একটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। কারণ তিনিই প্রথম কবি যিনি কাব্যকে কেবল ভাবের বিকাশ-মাধ্যম হিসেবে দেখেননি, তার প্রকাশ কলার চারুত্ব বিষয়েও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। হরিদত্তের কাব্য বিষয়ে বিজয় গুপ্তের অভিমতটি এইরকম—
সর্ব্বলোকে গীত গাহে না বোঝে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।।
হরিদত্তের গীত যত লোপ্ত পাইল কালে।
যোড়াগাঁথা নাহি কিছু ভাণ্ডে বোলচালে।।
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাহিতে আর গাহে নাহি মিত্রাক্ষর।।
বোঝা গেল, অনুপ্রাস-শূন্যতা, ঘটনার পারম্পর্যহীনতা ও গীতিধর্মিতার অভাবই ‘হরিদত্তের গীত যত ক্ষেপ্ত’ হওয়ার কারণ। কিন্তু তিনি যখন কাব্যাংশের শেষভাগে তাঁর প্রতি মনসার আদেশের কথা উল্লেখ করেন, তখন অনুমান হয়, পূর্বজ কবির কাব্যপ্রতিভা ও কবি-মর্যাদাকে নস্যাৎ করার এটি একটি অপকৌশল মাত্র। তবুও তিনি যে সাহিত্যের মৌল ভাবনা নিয়ে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন একথা ভুললে চলবে না। যে-যুগে কাব্যকালাকে ধর্মেরই অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিবেচনা করত সকলে, সে যুগের বুকে দাঁড়িয়ে এই কবিকেই বলতে শুনি, ‘সর্ব্বলোকে গীত গাহে না বোঝে সাহিত্য’। এ উক্তি সাহিত্যস্রষ্টার ভাবনা পরিধিকে খুব স্পষ্টভাবেই চিহ্নিত করে দেয়।
কাব্যকলার আনুষঙ্গিক ত্রুটি নিয়ে সপ্তদশ শতকের একজন কবিও সমালোচনা করেছিলেন অগ্রজ এক রায়মঙ্গল পালার কাহিনিকারকে। সে অভিযোগ শুধু প্রকাশকলার উপাদান ছন্দ-অলঙ্কার-অনুপ্রাস কেন্দ্রিক ছিল না, সেইসঙ্গে অসন্তোষ জানানো হয়েছিল কাব্যের অসম্পূর্ণতা ও বিষয়ের ভুলভ্রান্তি নিয়েও। অগ্রজ কবির নাম ছিল মাধব আচার্য। তাঁর কাব্যও মেলেনি হরিদত্তের মতো। খুব সম্ভব, কাব্যগত নানা ত্রুটির জন্য জনসমাজে মাধব তেমন আদৃতও হননি। অথচ তাঁর ‘গান’ শুনে মউল্যা-মলঙ্গীরা ‘পরম কৌতুক’ বোধ করছে— এই তথ্য দিয়ে সমালোচক কবি কৃষ্ণরাম দাস বোঝাতে চেয়েছেন যে চাষাদের কোনো সাহিত্যবোধ নেই। ঠিক ‘সাহিত্য’ শব্দটির সরাসরি প্রয়োগ হয়তো করেননি কৃষ্ণরাম, কিন্তু তাঁরও ভাবনার অভিমুখ ছিল বিশুদ্ধ ও ত্রুটিহীন কাব্যরচনার দিকেই। তবে রচনার শেষভাগে দেবতার প্রসঙ্গ এনে পাঠক ও শ্রোতৃসমাজে যে-ভীতি সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছেন তা নিঃসন্দেহে বিজয় গুপ্তের মতোই দুরভিসন্ধিময়, এক সাহিত্যিক প্রকরণ। জোর করে তাঁর লেখার প্রতি অনুরাগী করে তোলার এই চেষ্টায় দেবতার সহায়তা-প্রাপ্তিকে আবশ্যক বলে মনে করেছেন কবি। ফলে তাঁর কাব্যভাষা এখানে যেন আধা-অভিশাপ বাণীর মতো লাগে। ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের মুখ দিয়ে কবি বলাচ্ছেন—
পূর্বে করিল গীত মাধব আচার্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য।।
মশান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা।
চাষা-ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা।
কাকুটি নাকুটি আর করে রঙ্গিভঙ্গি।
পরম কৌতুকে শুনে মউল্যা মলঙ্গি।।
তোমার কবিতা যার মনে নাই লাগে।
সবংশে তাহারে তবে সংহরাবি বাঘে।।
আধুনিক যুগের অলৌকিকতা বিরোধী দেবীপ্রভাবমুক্ত যুক্তিবাদী দৃষ্টি নিয়ে যেমন আমরা আজকাল মধ্যযুগের কাব্যপ্রত্যয় ও প্রকরণ কৌশলকে অবাস্তব ও সত্যবর্জিত বলে ব্যাখ্যা করি। সেকালের অন্তত দু’জন কবিকে পাওয়া যাচ্ছে যাঁদের মানসিকতাটি ছিল এই গোত্রেরই। একই পদ্ধতির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে ক্লান্তিকর একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে অথবা ঘটনার সম্ভাব্যতায় সন্দিহান হয়ে তাঁরা যে এই ধরনের সমালোচনায় আগ্রসর হয়েছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। ‘শ্যামার মঙ্গল’ রচয়িতা রাধাকান্ত মিশ্রের স্পষ্ট অভিযোগ ছিল বহুচর্চিত এই প্রথাটির প্রতি। কবি তাঁর যুগে যে ‘আধুনিক’ ছিলেন তারও নিদর্শন ফুটিয়ে তুলেছেন পূর্ববর্তী রচনাকারদের ‘প্রাচীন কবি’ অভিধায় ভূষিত করে। প্রত্যাদেশ, স্বপ্নাদেশ, বেশবসে পরিবর্তন করে দেবতার দিবালোকে সাক্ষাৎ দর্শন, জিহ্বায় কবিতা লিখে কোনো কবির কবিত্বশক্তি প্রদান ইত্যাদি অতিপরিচিত ও বহু ব্যবহৃত কাব্যকৌশলকে ইনি মৃদুভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। মধ্যযুগে ধর্মই ছিল সমাজ ও ব্যক্তির অন্যতম চালিকাশক্তি। সুতরাং তার আশ্রয় নিয়ে অলৌকিকতার প্রকাশ ঘটানো ছিল অতি স্বাভাবিক ঘটনা। রাধাকান্ত মিশ্র এখানে যেন তারই বিরোধিতা করেছেন নব্যযুক্তিবাদ আমদানি করে। কিন্তু হা হতোস্মি! আসলে তিনিও যে সেই ধর্মভাবনার বাইরে নন, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে পরবর্তী কাব্যরচনাগুলিতে। মানবের প্রাপ্তির সীমার বাইরে দেবতার যে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও নির্বিকার অবস্থান সেই কথাই বলা হয়েছে এখানে। কবি বললেন—
আর এক নিবেদন শুন সর্বজন।
প্রাচীন কবির সম কৈরাছি রচন।।
কেহো কহে মায়ের হয়্যাছে প্রত্যাদেশ।
কেহো কহে দিলা দেখহা ধরি নিজ বেশ।।
কেহো বলে জিহ্বাতে কবিতা দিল লিখি।।
যে পদ ধিয়ান করি না পান বিধাতা।
মানব হইয়া কেহ কেহ হেন কথা।।
কেমনে এমন কথা লইবে হিয়ায়।
কিন্তু সত্য মিথ্যা কিছু কথা নাহি যায়।।
দেখাই যাচ্ছে, উদ্ধৃত শেষ তিনটি চরণে কবির বিশ্বাস মধ্যযুগের ধর্মভাবনারই দাসত্ব করেছে।
সমধর্মী অভিযোগ উত্থাপিত হয়, অষ্টাদশ শতকের কবি রামানন্দ যতির লেখনীতেও। অনেক শিষ্যের অনুরোধে তিনি ‘চণ্ডীমঙ্গল’ লিখতে উৎসাহী হয়েছিলেন। খুব সম্ভব তাঁর কবিখ্যাতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল বহুল প্রচারিত ও ভূয়শী প্রশংসিত কবি মুকুন্দের চণ্ডীকাব্য। কবির যে-জীবনী জানতে পারা গেছে তা থেকে তাঁর শূদ্রকূলে জন্ম বলে মনে হয়। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে বৌদ্ধধর্ম সমগ্র ভারতে একদা ছড়িয়ে পড়েছিল, রামানন্দ তারই ধুয়ো তুলে তাঁর কাব্যে ঘোষণা করেছেন— ‘কলিযুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার’। অর্থহীন দেববিশ্বাসের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও আফশোস প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ‘রামায়ণ’ কাব্যের অনেক স্থানেই। যে-বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁকে এই ধারণায় আসতে বাধ্য করেছিল যে, ‘বাস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ। / নিজ কষ্ট দায় আর লোকমধ্যে লাজ’।। — সেই প্রখর যুক্তিবাদ ও ভৌমদৃষ্টিই মুকুন্দের কাব্যের দোষ নির্ণয়ে সাহায্য করেছেন। ফলে তিনি যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎ চণ্ডীদর্শনের কথা অবিশ্বাসের হাসি হেসে উড়িয়ে দেবেন, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। সমালোচনায় পরিহাস করে তিনি বললেন—
চণ্ডী যদি দেন দেখা তবে কি তা যায় লেখা
পাঁচালীর অমনি রচন।
বুদ্ধি নাই যার ঘটে তারা বলে সত্য বটে।
পথে চণ্ডী দিলা দরশন।।
এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে
চণ্ডী রচে রামানন্দ যতি।।
অনেকের উপরোধ কেহ না করিও ক্রোধ
অনেক শিষ্যের অনুমতি।।
রামানন্দের চণ্ডীমঙ্গলে আখ্যান বর্ণনায় মাঝে মাঝে মুকুন্দের রচনার ওপর কটাক্ষ চোখে পড়ে। কবি এতটাই দাম্ভিক ছিলেন যে, নিজেকে কালিদাসের সমতুল বলে কোথাও কোথাও দাবি করেছেন। সে কারণে ভণিতাতে ‘যতি কালিদাস’ ব্যবহার করেছেন কখনো কখনো।
প্রকৃতপক্ষে, সেকালে আধুনিক সমালোচনা শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়নি, সেকালে কবি-সমালোচকদের জীবনদৃষ্টি ছিল সীমিত পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ, বাংলা সাহিত্যের সেই প্রায়ান্ধকার কালে যে এই ধরনের সমালোচনা পাওয়া গেল, তা কাব্যালোচনার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে কাব্যরূপের যে-আলোচনা আজকের বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির একটি প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়েছে, মধ্যযুগের ক্ষেত্রে সেই বোধ কখনই পাকা হয়ে ওঠেনি। কেননা তখন কবির চোখ ছিল নিজের সৃষ্টির উপরেই সীমাবদ্ধ। বর্তমান কালে ইউরোপীয় কাব্যকলার অনেক প্রগতিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে আমরা পরিচিত বলে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের রসপ্রস্থানকে তেমন আর গুরুত্ব দিই না। কিন্তু একথা আমাদের ভুললে চলবে না, সেকালের কবিরা সংস্কৃতানুসারী কাব্যজিজ্ঞাসার দ্বারা চালিত হয়েই বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, যা আজকের চোখে খানিকটা গতানুগতিক বলে মনে হতে পারে। তবুও আমরা স্বীকার করব, সাহিত্যের ভালো-মন্দ নিয়ে কোনো প্রাচীন কবির এইসব মামুলি প্রশ্নের গুরুত্ব, অনুধাবন করতে সচেষ্ট হব সেই প্রতিভা-দৈন্যের দিনেও কীভাবে এক-কবির কাব্যের জনপ্রিয়তাকে নস্যাৎ করে অপর কবির কাব্য উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠত, অথবা কেমনভাবে ভাবতে অভ্যস্থ ছিলেন ধর্ম-কলের ফাঁদে পড়া অনতি-সচেতন ব্যক্তি-মানুষ। সেইসঙ্গে মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা সমাজ-মানসের ক্রম-পরিবর্তিত ভোগদৃষ্টি কীভাবে সেদিনের আধুনিকতাকে বরণ করে নিচ্ছিল সেটাও হয়ে ওঠে আজকের জিজ্ঞাসু পাঠকের অনুসন্ধানের বিষয়।
সমাপ্ত