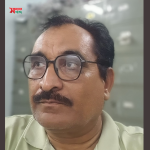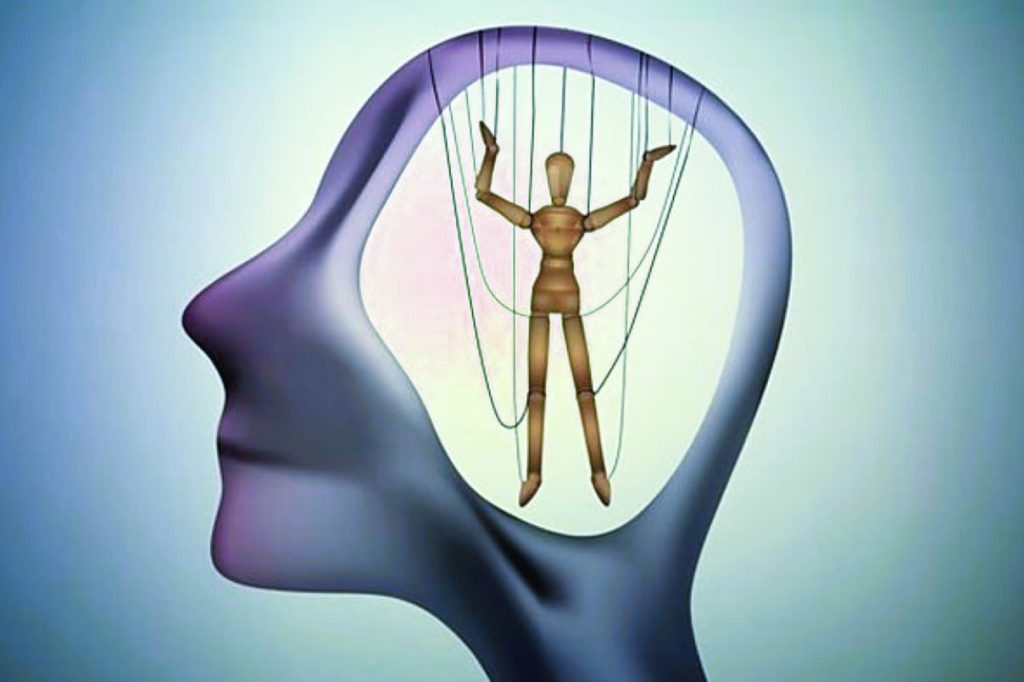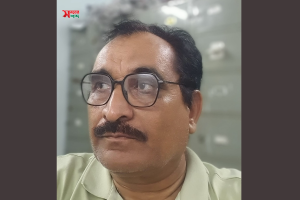সমাজ সাংস্কৃতিক গণিত (Mathematics in the Socio-cultural Environment): সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক যেমন নিবিড় তেমনি গণিতেরও নিকট সম্পর্ক বর্তমান। সমাজে মানুষ অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে নানা ধরনের জীবিকা বেছে নেয়। এবং সেই জীবিকা তার প্রাত্যহিক জীবনেরই একটা অঙ্গ। প্রতিদিনের নানা কাজকর্মে যে প্রতিনিয়ত নিজের অজান্তে কিছু কৌশল, কায়দা-কানুন মেনে চলে, এটা স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়ে থাকে বলে আমরা আলাদা করে অনুভব করি না। সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত ভাবের আদান প্রদান হয়। আর সেই ভাবের আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে তারা তাদের লালিত সংস্কৃতিকে প্রকাশ করে। এই সাংস্কৃতিক প্রকাশও হয়ে তাকে বিশেষ কিছু নিয়ম মেনে বা পদ্ধতি মেনে। এই নিয়ম বা কৌশল মানাটাই ছিল গাণিতিক চেতনার একটি দিক। মানুষ সমাজে বসবাস করে, সমাজের লালিত সংস্কৃতি বহনও করে; আর এই লালিত সংস্কৃতি বা এর ক্ষেত্র বৃহৎ। Culture এর মধ্যে Science-ও এসে পড়ে; গণিত যেখানে বাদ যায় না।
এক এক স্থানের বাস্তুতন্ত্রের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে পরিবেশ। পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে সংস্কৃতির আদান-প্রদানের সম্পর্ক নিবিড়। সেখানেও প্রকৃতির নিয়মেই যেন এক গাণিতিক হিসাব রক্ষিত হয়। মানুষের দৈনন্দিন রোজগার ও তার চাহিদা পূরণ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের যোগান ঠিকঠাক হলে সেই Socio-Cultural Environment সুসমন্বিত হয়। Mathematics যেহেতু সংকেতময় ভাষা তা মানুষের জীবনের ভাব প্রকাশের একটি বিশেষ মাধ্যম। আর গণিতের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। গাণিতিক চেতনা মানুষের কৃত্রিম সৃষ্ট নয়; বরং তা মানসজাত। মানুষ সমাজ-সংস্কৃতি থেকে নানা উপাদান গ্রহণ করে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে। বংশ পরম্পরায় মানুষ তার সংস্কৃতিতে বহন করে চলে। সমাজে লোকাচার, ব্রত, পার্বণ, উৎসব, মেলা থেকে শুরু করে শিল্পকলা, ভাস্কর্য, ইত্যাদিও সর্বক্ষেত্রেই গাণিতিক চেতনাতে কাজ করে থাকে। মানুষ সকল ক্ষেত্রেই গাণিতিক সূক্ষ্ম হিসাবে বিভিন্ন উপাদানের গ্রহণ বর্জন করে নিজেদের অজান্তে, অচেতনে বা অবচেতনে। Socio-Cultural Environment-এ গণিত অবস্থান করে। এখানে প্রতিটি ক্ষেত্র প্রতিটি ক্ষেত্রের দিকে গমন ও প্রতিগমন করে থাকে। Socio-Cultural Environment-এ গাণিতিক চেতনার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বেদে সম্প্রদায় তাদের সংসার লোকজন ও ব্যবসা জিনিসপত্র নিয়ে স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়ায়। তারা বিভিন্ন স্থানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতিরও খাপ খাওয়ায় অসাধারণভাবে। এখানে লক্ষণীয় যে যেখানে তাদের ব্যবসা ভালো হয় সেখানে তারা একটু বেশি সময় অবস্থান করে। আবার যেখানে তাদের ব্যবসা মন্দা দেখা দেয় সেখানে বেশিদিন তারা থাকে না। তাদের ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক ও বংশগত ঐতিহ্য নানা স্থানে বহন করে চলে। এবং তা ক্রমশ সক্রিয় থেকে বিবর্তিত হয় গাণিতিক নিয়ম মেনে। তাই যাযাবর জীবন-বৃত্তি হওয়ায় বেদেদের মধ্যে মিশ্র সংস্কৃতি লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন স্থানের লৌকিক আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার মিলেমিশে তাদের জীবনের সাথে একাকার হয়ে যায়।
নদীকেন্দ্রিক অঞ্চলে নদীকে কেন্দ্র করে মানসিক সংস্কার বিশ্বাস, আচার-আচরণ জন্ম নেয়। তার প্রকাশ পায় লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানে। একটি প্রবাদে বলা আছে—
নদীর ধারে বাস।
ভাবনা বারো মাস ৷৷
এখানে বারো একটি সংখ্যা নির্দেশক। বারোমাস যা কিনা সমগ্র বছরটিকেই বোঝায়। অর্থাৎ যে সমাজ-সংস্কৃতি নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সেখানকার মানুষের জীবন সারা বছর কোনো মতেই মসৃণতাপূর্ণ নয়। বরং সেখানে নানা দুর্ভাবনা মানুষের সামাজিক জীবনকে অতীষ্ট করে তোলে। এখানে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সারাবছরের করুণ অবস্থার কথা বলা হয়। এবং পরিবেশকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বক্তব্যের ভিত্তি। যুক্তি পরম্পরা এখানকার বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বটে।
সমাজে মানুষ বসবাস করে। তারা তাদের মানসিক চেতনাস্তর থেকে নানা ভাবকে বিকশিত করে নানা মাধ্যমে। কখনও গানে, কখনও ছড়ায়, কবিতায়, কথায়, নাচে ও অন্যান্য শিল্পকলায়। এখানে সমাজ, মানুষ ও সংস্কৃতি ত্রিবলয়ের মতো অবস্থান করে। গাণিতিক চেতনাও সংস্কৃতির অন্তর্গত। একটি লৌকিকগানে কীভাবে গাণিতিক চেতনা সুপ্ত হয়ে আছে তা দেখানো হল—
ভাইরে শাল কাঠের ডিঙ্গাখানি কড়ি কাঠের দাঁড়
জমসের আলীর বাইচের তরী গলাত সোনার হার।
ভাইরে সত্তর হাত ডিঙ্গাখানা পঞ্চ হস্ত আড়ে,
পবন কাষ্ঠের নৌকাখানা চলে উজান ধারে।
গানটি একটি নৌকা বাইচের গান। এখানে নৌকার দৈর্ঘ্য হিসাবে বলা হয়েছে সত্তর হাত। যা একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের একক। নৌকার প্রস্থ পাঁচ হাত। অর্থাৎ দীর্ঘ নৌকাটির পরিমাপ যেমন গানে জানিয়ে দেওয়া হল তেমনি ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে, ধর্মের, সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার কথাও জানিয়ে দেওয়া হল— যখন বলা হল নৌকাটি শালকাঠ দিয়ে তৈরি। অতএব বলা চলে Socio-Cultural Environment বা সমাজ-সাংস্কৃতিক গণিতে অর্থনীতি, রাজনীতি, ও জাতিতত্ত্ব জড়িত থাকে। তাই Cultural Environment এক্ষেত্রে বাদ যায় না। এ প্রসঙ্গে বলা বাঞ্ছনীয় যে Cultural Environment এ Aesthetics-এর কথাও এসে পড়ে অনিবার্যভাবে। এখানেও নন্দনতত্ত্বের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে সুসমন্বয় পরিমাণবোধের কথা এসে যায়। তাই অবশেষে বলতে হয় Socio-Cultural Environment-এ Mathematics, Aesthetics, Politics, Economics, Geography ও History এসে পড়ে।
স্বতঃস্ফূর্ত গণিত (Spontaneous Mathematics): গাণিতিক চেতনা মানুষ বংশপরম্পরায় বয়ে নিয়ে চলে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষ তার এই গাণিতিক চেতনাকে নানাভাবে প্রকাশ করে থাকে। এই গণিত শিক্ষা যেহেতু তাদের আপনা আপনি হয়ে থাকে সেই কারণে তার প্রকাশও স্বতঃস্ফূর্ত। একটু নজর দিলেই দেখা যায় রাস্তার বা ফাঁকা স্থানে মাঝে মাঝে যে সকল ম্যাজিসিয়ানরা খেলা দেখায় তাদের অধিকাংশ খেলার স্বতঃস্ফূর্ত গাণিতিক ভাবনার প্রকাশ ঘটে। যে সকল খেলোয়াড়রা লাট্টু ঘোরায় তারা লাটুকে দেহের নানা স্থানে রেখে অসাধারণ নৈপুণ্যে, দক্ষতার সঙ্গে ঘোরাতে থাকে। হাতের তালুতে, কপালে, নাকের উপরে, হাতের কনুই-এর উপর, হাতের আঙুলের উপর ভারসাম্য বজায় রেখে লাট্টুকে দীর্ঘক্ষণ ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে নানা কসরৎ দেখায়। এইভাবে তারা বংশপরম্পরায় ঐতিহ্যকে রক্ষা করে খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। এই লাট্টু ঘোরানোর কৃৎ-কৌশলের মধ্যে স্বতঃ স্ফূর্ত গাণিতিক ভাবনা অন্তর্নিহিত রয়েছে, যা জটিলতম গণিত নির্ভর গতিবিদ্যার ভিত্তি তা ঐ সব খেলোয়াড়রা জানেও না।
আবার সার্কাসে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় খেলোয়াড়রা নানা ধরনের খেলা দেখায়। শিকল তৈরি করার খেলায় একপাশ থেকে অন্যপাশে লাফ দিয়ে একজন খেলোয়াড় অন্যজন খেলোয়াড়ের পা ধরে থাকে। এবং অন্যপ্রান্ত থেকে অপর একজন এসে আবার তার পা ধরে ক্রমশ লম্বা শিকলের চেহারা দেয়। Trapezium খেলার সময় ওইসব খেলোয়াড়রা ভীষণ দক্ষতার সঙ্গে নিখুঁত সময়জ্ঞানের পরিচয় দেয়, যা কিনা সম্পূর্ণ গণিত নির্ভর। এখানে লক্ষণীয় যে খেলোয়াড়রা লাফ দেবার সময় তারা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে লাফ দেয় তা তারা দেখে দেখে বা বংশপরম্পরায় শিখে যায়। এই সব খেলায় যে খেলোয়াড়দের Body Language মেকানিক্স এর জ্ঞান একান্তভাবে জরুরী তা বলা বাহুল্য। সার্কাসের খেলোয়াড় হয়তো মেকানিক্স শব্দটি শোনেইনি। কিন্তু তারা খেলা দেখিয়ে যাচ্ছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম।
বাঁশের, বেতের নানা কাজে যে গাণিতিক চেতনার প্রকাশ দেখা যায় তাও স্বতঃস্ফূর্ত গণিতের নিদর্শন। বাঁশ দিয়ে যখন ঝুড়ি বোনে, বোনা শুরু করে বাঁশের চটা আড়াআড়ি ভাবে দিয়ে। ক্রমশ বেশি চটা দিয়ে ঝুড়ির বহর বাড়ানো হয় এবং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোল করে বোনার পদ্ধতি অনুসরণ করে অবশেষে ঝুড়ির চেহারা পায়।
বেতের ধামা তৈরি করার সময় চারটি বেতের দণ্ড আড়াআড়ি রেখে অন্য একটি বেত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধামাকে বাড়িয়ে তোলা হয়। এইভাবে ধামার চারপাশে বেত ঘুরিয়ে আড়াআড়িভাবে বেত বাড়িয়ে ধামা তৈরির কাজ হয়। বেত দিয়ে অধিবৃত্ত নির্মাণ করে থাকে। এই ধামা তৈরির শিল্পীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপন দক্ষতায় ধামা বুনে চলে বংশপরম্পরায়, যার মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্ত গণিত অন্তর্নিহিত আছে।
জাল বোনে যে সমস্ত জেলে মাঝি ইত্যাদি মানুষ। তারাও বংশপরম্পরায় এই কাজ করে চলেছে। খেপালা জাল বোনার সময় প্রথমে চল্লিশ ঘর মালি নিয়ে বোনা শুরু হয়। ক্রমশ এই ঘর দ্বিগুণ করা হয়। বাড়াতে বাড়াতে ক্রমশ তা একসময় জালের একেবারে সীমান্তে এসে পড়ে। এই জাল বোনার মধ্যেও রয়েছে গাণিতিক হিসাব। সেই হিসাব মেনে ঘর বা ফাশ বাড়ানো হয়। এক্ষেত্রে জেলে বা মাঝিরা কিন্তু কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তাদের বিদ্যাশিক্ষা চর্চা করে না বা গণিতের পাঠ নেয় না। অবলীলায় তারা অনুপাত ও সিরিজ এর মতো গাণিতিক ভাবনা জাল নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে। এই গাণিতিক চিন্তা ও চেতনা স্বতঃস্ফূর্ত।
মৌখিক পদ্ধতি (Oral Mathematics): সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে মৌখিক গণিতের ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ। কারণ গণিত হল সংকেতময় ভাষা, আর সেই সংকেতময় ভাষা সভ্যতার গোড়া থেকে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে ব্যবহার করে আসছে। আকার, ইঙ্গিত প্রভৃতি দিয়ে মানুষ তার মনের ভাবাবেগকে প্রকাশ করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। মানুষ যখন সময় সম্পর্কে সচেতন হল, ক্ষণ, মুহূর্ত, প্রহর, দিন, রাত, ঋতু, বছর, যুগ ইত্যাদি মুখে মুখেই হিসাব করে চলে এসেছে। কারণ লিপি আবিষ্কারের ইতিহাসেরও অনেক আগে থেকে মানুষ সময় সম্পর্কে সচেতন হয়। তারা প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম অর্থাৎ জোয়ার-ভাঁটা, বর্ষা ইত্যাদির সময় যেমন মুখে মুখে হিসাব রাখত তেমনি সংখ্যা (Number) বা গণনা করাও আয়ত্ত করে মুখে মুখে। নানা ধ্বনি দিয়ে নানা সংখ্যাকে প্রকাশ করে এই আদিম স্তরের মানুষই। এমন কি পরবর্তীকালে তারা যখন কৃষি নির্ভর জীবনে প্রবেশ করল তখনও তারা জমির পরিমাপ, পশুর সংখ্যা (বলদ, ষাঁড় ইত্যাদি) উৎপাদিত শস্যের পরিমাণও মুখে মুখে হিসাব রাখত।
আর লোকসমাজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মৌখিক গণিতের এক বড়ো অধ্যায়। লোকসমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে মৌখিক গণিত। বিশেষত মৌখিক সাহিত্যে, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন, হেঁয়ালি, বারমাস্যা, গীতিকা, রূপকথা, মহাকাব্য, লোকসংগীত ইত্যাদিতে।
উদাহরণ হিসাবে বলা যায় আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ময়মনসিংহ গীতিকা’র পালায় অজস্র সংখ্যাবাচক শব্দ, ভাব ব্যবহার হয়েছে। যেমন—
কোথায় তোমার কলসি কইন্যা কোথায় তোমার দড়ি।
তুমি হইবু গহিন গাঙ আমি ডুইব্যা মরি।
এখানে গভীরতা বোঝাতে ‘গহিন’ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। আবার প্রবাদে আছে,
চোরের দশ দিন
গেরস্থের একদিন।
অন্য একটি প্রবাদে,
জাত যায় না ধুলে
স্বভাব যায় না মলে।
এখানে ‘ধুলে’ ও ‘মলে’ শব্দের মধ্য দিয়ে অজস্রবারের ইঙ্গিত করা হয়েছে।
আরো একটি ধাঁধায় আছে,
এক চিলের দুই ঠ্যাং
চারচিলের কয় ঠ্যাং।
চিল একটি পাখি তার দুই ঠ্যাং। আবার চার্চিল একজন ব্যক্তি তাঁরও দুই ঠ্যাং। অথচ ধাঁধাটি শুনে মনে হয় চারটি চিলের আটটি ঠ্যাং।
আরো একটি প্রবাদ স্মরণীয়, তিন মেয়ে যেখানে, কাজির দরবার সেখানে।
পৌষমাসে বাংলায় পৌষ সংক্রান্তির সময় রাত্রে ছেলেমেয়েরা ঘুরে ঘুরে ছড়া কেটে ভিক্ষা করে। এবং সেই ভিক্ষায় সংগৃহীত সামগ্রী দিয়ে পৌষলা পার্বণ উদ্যাপিত হয়। সেখানেও গণিত কীভাবে কাজ করে ভাবলে অবাক হতে হয়। ছেলেমেয়েরা যে ছড়া কেটে ভিক্ষা করে তা হল—
যে দেবে ডালা ডালা
তার হবে সাত গোলা,
যে দেবে বাটা বাটা
তার হবে সাত বেটা
যে দেবে বাটি বাটি
তার হবে সাত বেটি
যে দেবে মুঠো মুঠো
তার হবে হাত ঠুটো।
লোকসংগীতে অসংখ্যা গাণিতিক চেতনার কথা নিবিড়ভাবে মিশে রয়েছে। পরে তা আলোচনা করা হবে। এখানে পাগলা কানাই-এর রচিত একটি দেহতত্ত্বমূলক, আধ্যাত্মিক লোকসংগীতের উদাহরণ দেওয়া হল। গানটি হল—
জাহাজের আট কুঠুরী নয় দরজা
মালকোঠা সোনার
দাঁড়িমাল্লা ছয়জন রিপু জাহাজ চালায় না
জাহাজের কি হবে
পাগলা কানাই বসে এখন তাই ভাবে;
সেদিন জাহাজ হবে কমজোরী ভাই
বান খেয়ে তরী জল নেবে।
দাঁড়ি মাল্লা ছয়জন রিপু সব চলে যাবে’
যেদিন শুকনায় তরী তল্ হবে।
এছাড়া লোকভাষাতে তো অহরহ গাণিতিক চেতনার প্রয়োগ মেলে। যেমন, ‘সাত পাঁচ ভেবে কেঁদো না’, ‘হ্যার বাপের দশ লাঠি, তো মোর বাপেরও দশ লাঠি, মুই ডরাই না কত্তা।’ ‘তোগতো হগল সময়ই কাম লাইগ্যা আছে।’ এখানে বাঙ্গালী উপভাষা-ভাষী অঞ্চলে বসবাসকারী লোকসমাজের মুখের কথ্য ভাষাতে গাণিতিক চেতনা বা মনের এক বিশেষ স্তর প্রকাশ পাচ্ছে যার নান্দনিক গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষাতত্ত্বের আলোকে ইতালিয়ান, নন্দনবিদ Vico-ugly beauty-তে যে অপূর্ব গাণিতিক প্রয়োগ বর্তমান এই লোকভাষা ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সংগ্রহ করলে বোঝা যায়।
চলবে…