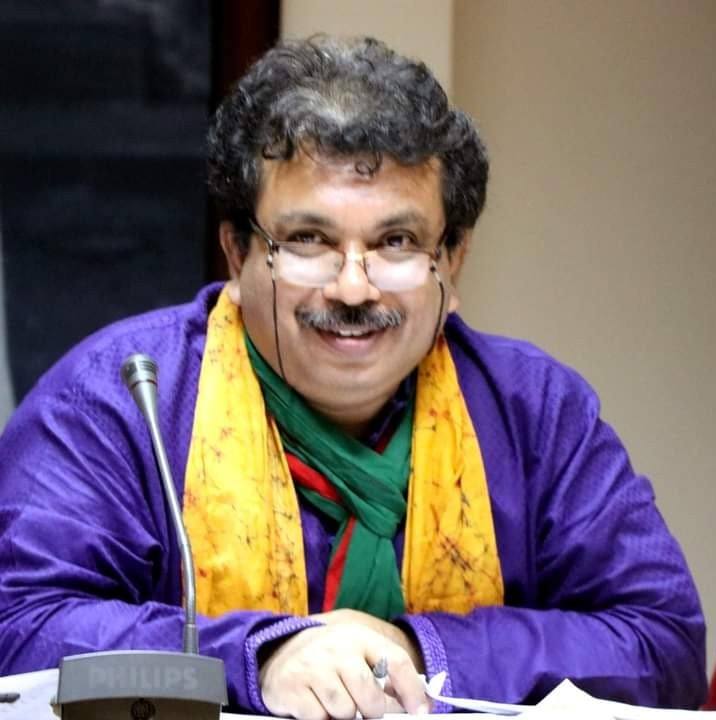“ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ওঁ। অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব যাঁর চরিত্রে দীপ্তিমান হয়ে দেশকে সমুজ্জল করেছিল, যিনি বিধিদত্ত সম্মান পূর্ণভাবে নিজের অন্তরে লাভ করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমরা সেই ক্ষণজন্মা পুরুষকে শ্রদ্ধা করবার শক্তি দ্বারাই তাঁর স্বদেশবাসীরূপে তাঁর গৌরবের অংশ পাবার অধিকার প্রমাণ করতে পারি। যদি না পারি তবে তাতে নিজেদের শোচনীয় হীনতারই পরিচয় হবে।” (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, শনিবারের চিঠি, শনিবারের চিঠি।)
পরাধীন উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ পাশ্চাত্যের রূপ-রস-গন্ধ অনুভব করে ‘আধুনিক’ হয়েছে। শুধু আধুনিক নয়, অনেকের ভাষায় মহাবিপ্লব ‘রেনেসাঁও’। যুক্তির পেছনে পুঁথি টেনে ইতালী, ফ্রান্স-এ সব দেশের বিপ্লবের মহামন্ত্রণাকে যুক্ত করা হয়েছে অভিনব কায়দায়। আবার গোল বেঁধেছে এসবের যাঁরা ঘোর বিরোধী তাঁদের নিয়ে। তাঁরা বিংশ শতকের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে তুলনা করতে গিয়ে উনিশ শতককে এশতকে বসিয়ে দেহ ব্যবচ্ছেদ করে মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। এ দুয়ের টানাহেঁচড়ায় উনিশ শতককে যথার্থ উপলব্ধি করা একটু কষ্টসাধ্য তো বটেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের মানুষ এবং তাঁর ভাবনাগুলো প্রায় সবই সমাজকেন্দ্রিক। সমাজের বৈপরীত্যকে তুলে ধরেছেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ মানুষের মতো, তার সাথে হয়তো পাশ্চাত্যে যুক্তিবোধ প্রধানভাবে লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠে নি। তবে একথা সত্যি, ভারতবর্ষের সমস্যা, ভারতবর্ষের মানুষকে সমাধান করতে হবে তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি দিয়ে। সেখানে ঢালাওভাবে পাশ্চাত্য অনুকরণ এ সমাজ (কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালী সমাজ) মেনে নেবেই বা কেন? যেমন মেনে নেয়নি ইয়ং বেঙ্গলদের। ইয়ং বেঙ্গলরা হয়তো পুরোমাত্রায় পাশ্চাত্য বোধের আধুনিক মানুষ ছিলেন, কিন্তু তারসাথে আমাদের সমাজের সম্পর্ক কোথায়? বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও দর্শন কখনই কোন সমাজ যথার্থভাবে মেনে নেয়নি। আবার আধুনিক বোধের সাথে কখনও সামন্তভাবনা ও সংস্কৃতি টিকে থাকতে পারে না। উনিশ শতকের পরাধীনতা ঠিক একারণেই।
প্রথমেই বলে নেয়া ভাল, বিদ্যাসাগর কোনভাবেই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন, তবে তার ভাবনা দার্শনিক পণ্ডিতের মতো। যে পণ্ডিত সমাজের উপরিকাঠামোর একটু পরিবর্তন চেয়েছলেন। যদিও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বোধকে মেনে নেয়ার মতো শক্তি তখন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের হয়নি। ভারতবর্ষ নানা কারণে দীর্ঘকাল পরাধীন ছিল বাইরে থেকে আগত মুসলমান রাজ্য, সামন্ত প্রভুদের হাতে। বহুকাল ধরে মুসলিম সামন্তরা ক্ষমতায় থাকলেও প্রযুক্তির উন্নতি ঘটায়নি, করে নি আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন। বরং এর পরিবর্তে উন্নয়ন ঘটিয়েছে ভোগ-বিলাসের নানা সরঞ্জাম। অপরদিকে ব্রিটিশরা উন্নত প্রযুক্তি ও পুঁজির মালিক। এর ফলে ব্রিটিশরা অতি সহজে কৌশলে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় মুসলিম রাজা ও জমিদারদের কাছ থেকে। বিজাতীয় দুই সম্প্রদায়ের মূলগত পার্থক্য অবশ্য আছে। মুসলমানরা ক্ষমতা লাভের পর উত্তপ্ত মরুভূমিতে ফিরে যায় নি, কিন্তু ইংরেজরা ক্ষমতাকে ব্যবসাকেন্দ্রিক চিন্তা করতো। আর করতো বলেই এই ভূ-খণ্ডে তারা থাকতে চায় নি। বরং শোষণ, নির্যাতন-লুণ্ঠন করে ফিরে যেতে চেয়েছে স্বদেশে এবং গিয়েছেও।
“ব্রিটিশরা হিন্দুস্তানের উপর যে দুর্দশা চালিয়েছে তা হিন্দুস্তানের আগের সমস্ত দুর্দশার চাইতে মূলগতভাবে পৃথক এবং অনেক বেশি তীব্র।” (উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে মার্কস, এঙ্গেলস, পৃ. ৩৭)।
ক্ষমতা হারানোর ভয়ে মুসলিম সামন্তরা ব্রিটিশদের সাথে আপোষ রফায় আসতে চেয়েছে, কিন্তু পারে নি। অগত্যা তারা নানা সময়ে ব্রিটিশ কোম্পানির সাথে যুদ্ধ করেছে, বিদ্রোহ করেছে। কোন কোন স্থানে এসব বিদ্রোহে নিপীড়িত কৃষকরা যোগ দিলেও কোথাও ঐক্যবদ্ধ রূপ লাভ করে নি বিদ্রোহের। আর তাছাড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাংলার মানুষ এসবে খুব বেশি আগ্রহ বোধ করে নি। তারা এ ব্যাপারটিকে দৈববিধান বলে একপর্যায়ে মেনে নিয়েছে। আর এ সুযোগে ইরেজরা এ দেশকে ব্যবহার করেছে কাঁচামাল ও পণ্যের উৎস হিসেবে। কর ব্যবস্থা আরো কড়াকড়ি করা হয়। ব্রিটিশ নীতির ফলে নতুন জমিদাররা একইভাবে নির্যাতন অব্যাহত রাখে। শোষণের মাত্রা এত বেশি বেড়ে যায় তার একটা উদাহরণ এখঅনে উল্লেখ করা হলো:
“ব্রিটিশ আসার পর ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং এতে প্রায় ১ কোটি লোক প্রাণ হারায়।” (ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন, পৃ. ৪১৪)।
মৃত্যুপথযাত্রী কৃষকরা এসময় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। ১৭৮৩ সালে দিনাজপুরের ইজারাদার দেবীসিংহের বিরুদ্ধে কৃষকরা বিদ্রোহ করে। তারপর থেকে ছোটখাট বিদ্রোহ প্রকটরূপ লাভ করে। বারানসীর বিদ্রোহ, ইঙ্গ-মহীশূরের যুদ্ধ, ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ, এরকম বহু বিদ্রোহ ও যুদ্ধকে মোকাবেলা করে ব্রিটিশ বেনিয়ারা এই ভারতবর্ষকে তাদের উপনিবেশ করতে সমর্থ হয়।
“হিন্দুস্তানের সমস্ত ঘটনা পরম্পরাকে যতই বিচিত্র রকমের জটিল, দ্রুত ও বিধ্বংসকারী বলে মনে হোক না কেন, এই সব কিছু গৃহযুদ্ধ, অভিযান, বিপ্লব, দিগ্বিজয় ও দুর্ভিক্ষ তার উপরিভাগের নিচে নামেনি। কিন্তু ইংলন্ড ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামোটাই ভেঙ্গে দিয়েছে, পুনর্গঠনের কোনো লক্ষণ এখনো অদৃশ্য। পুরনো জগতের অপহ্নতি অথচ নতুন কোনো জগতের এই অপ্রাপ্তির ফলে হিন্দুদের বর্তমান দুর্দশার ওপর এক অদ্ভুত রকমের শোকের আবির্ভাব ঘটে। বৃটেন শাসিত হিন্দুস্তান তার সমস্ত ঐতিহ্য,, তার সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।” (উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে, পৃ. ৩৮)
তবে ১৮৫৭-এ সংঘটিত ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ ব্রিটিশদের হতবাক করে দেয়। এই বিদ্রোহ দমন করতে তাদের বেশ বেগ পেতে হয়। যদিও এই বিদ্রোহ কুসংস্কার দিয়ে আচ্ছন্ন ছিল। দেশীয় সিপাহীদের মনে আশঙ্কা জন্মে ব্রিটিশরা তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করছে। তাদের নিকট যে কার্তুজ বিলি করা হয়, তা ষাঁড় ও শুয়োরের চর্বি দিয়ে মাখানো এবং এটা দাঁত দিয়ে কাটলে ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। আরও উল্লেখ্য যে, এসব বিদ্রোহকে চূড়ান্ত পরিণতিতে নিয়ে যাবার মতো নেতৃত্ব তখনও ভারতবর্ষে তৈরি হয় নি।
তবে এসময় ‘জলসা’ নামক সিপাহীদের একটি সংস্থা গড়ে ওঠে। এই সংস্থা সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ হয় সমগ্র ভারতবর্ষের জাতি, উপজাতি, নানা বর্ণের মানুষকে একত্র করতে। ব্রিটিশ শাসন পাকাপোক্ত হয় প্রধান দুটো কারণে:
এক. ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল কথিত অভিজাত সামন্ত রাজারা। তারা কখনই একত্রে কোন বিদ্রোহ পরিচালনা করে নি।
দুই. বিদ্রোহীদের হাতিয়ার ছিল ইংরেজদের থেকে অনুন্নত। উন্নত প্রযুক্তির কাছে অনুন্নত হাতিয়ার ও অনগ্রসর জাতি টিকে থাকতে পারে না।
সময় থেমে থাকে না। সময়ের দাবি মিটিয়ে সমগ্র জাতি যে আত্মমর্যাদার সাথে দাঁড়াবে, সে সামর্থ্য ও ক্ষমতা কোনটাই ভারতবর্ষের ছিল না। কুসংস্কার আচ্ছন্ন জাতি ধর্মীয় অনুশাসনে পরিচালিত হওয়ার ফলে ভারতীয় জীবন ব্যবস্থায় অধঃপতন নেমে আসে। এই অবস্থায় ভারতবর্ষকে দাঁড়াতে হলে প্রয়োজন শিক্ষার। শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনাই পারে ভারতবর্ষের সকল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে। কলিকাতা কেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থায় উঠতি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ইংরেজি শিক্ষার সাথে পরিচিত হয় এবং একই সাথে জীবনের বোধগুলোও পরিবর্তিত হতে থাকে। এঁরা সরাসরি ব্রিটিশবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ না হলেও কোম্পানি শাসনের সমালোচনা করতে দ্বিধা করে নি। একই সাথে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলন পরিচালনা করেন। বিশ্বকবির ভাষায় ভারত পথিক রামমোহন রায়ের ‘আত্মীয় সভা’ ও ‘ব্রাহ্মসমাজ’ প্রথম অতীত কুসংস্কারের বিরুদ্ধ সামাজিক জনমত গড়ে তোলার পথে কাজ করে। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলা ‘সম্বাদ কৌমুদী’ ও ফারসী ‘মিরাত উল আকবর’– এই ভারতবর্ষের সমাজ জীবনের একটি মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়। ধর্মীয় আদি গ্রন্থ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তিনি এসব আন্দোলন পরিচালনা করেন। তবে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন হেনরী ডিরোজিও ও তাঁর অনুসারী ‘ইয়ং বেঙ্গল’রা। পাশ্চাত্য জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে ‘ইয়ং বেঙ্গল সোসাইটি’র সদস্যরা ধর্ম ও কুসংস্কারকে আক্রমণ করে। এর তীব্রতা যতই থাকুক না কেন ভারতীয় জনগোষ্ঠী এটাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয় নি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রামমোহনের পথ ধরে বাঙালি সমাজকে কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য লেখনী পরিচালনা করেন। বিদ্যাসাগর জানতেন ভারতীয় জাতিকে মুক্তির পথ দেখাতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার। যে শিক্ষার আলোয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জাতি মুক্তির পথ দেখবে।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময়কালে সারা ভারতবর্ষে বহু বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর কোনো লেখায় এ সম্পর্কে সরাসরি কোন মন্তব্য লক্ষ্য করা যায় না। সংস্কৃতিসেবী, সংকৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলে কি তিনি এসবের দিকে দৃষ্টি দেন নি? নাকি অন্য কোন কারণ আছে? বিদ্যাসাগরের চাকুরী ছিল ব্রিটিশদের অধীনে, ফলে সরাসরি তাদের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়া ছিল তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এছাড়া বিদ্যাসাগর আগ্রহ বোধ করেন নি অভিজাত সামন্তীয়দের বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদে। এই প্রতিবাদের পক্ষে আবেগবশতঃ সমর্থন দেওয়া গেলেও যুক্তির নির্মম বিচারে হয়তো সম্ভব নয়। তবে বিদ্যাসাগর বেশিদিন চাকুরি করতে পারেননি ব্রিটিশদের অধীনে, ছাড়তে হয়েছে আটত্রিশ বছর বয়সে। চাকুরি থেকে অবসর নেওয়া সম্পর্কে দুটি ধারণা পাওয়া যায়।
এক, ‘কেউ কেউ বলে থাকেন সিপাহীবিদ্রোহের সময় অধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়াই সংস্কৃত কলেজের সেনানিবাস তৈরী করার প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছিলেন বিদ্যাসাগর।’ (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ১ম খ-, তুলিকলম প্রকাশনী, পৃ. ১০)
দুই. শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্রিটিশদের অর্থাৎ সরকারী কর্তৃপক্ষের সাথে মতভেদের কারণে তিনি চাকুরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নেন।
অবশ্য দুটো মতই অনুমানসাপেক্ষ। স্বেচ্ছা অবসর নেওয়ার সময় অসুস্থ শরীরের কথা নিছক একটা কারণ হলেও তাৎপর্য উপরোক্ত দুটো কারণ যথার্থ বলে মেনে নিতে হয়। বিদ্যাসাগর সঠিকভাবে ব্রিটিশ শাসনকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এদের পারিতোষিক থেকে আর যাই হোক স্বাধীন মত প্রকাশ করা যাবে না। অবহেলিত ভারতবর্ষকে জাগ্রত করাতে হলে প্রয়োজন স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূরীকরণ এবং শিক্ষার বিস্তার পদে পদে লাঞ্ছনা-বঞ্চনার যে দীর্ঘ ইতিহাস তা হলো অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ফসল। এ দুটো থেকে যদি ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকে মুক্তির পথ দেখানো না যায়, তবে এ ভূ-ভাগের মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ কোনদিন পাবে না। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। আর এ কাজটি করতে হলে প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও একই সাথে সামাজিক সংস্কারর সাধন।
শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে প্রয়োজন পাঠ্যপুস্তক। বিদ্যাসাগর জীবনের বৃহৎঅংশ ধরে পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হন। বেতাল পঞ্চবিংশতি, বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় ভাগ), জীবনচরিত, বোধোদয়, শিশু-শিক্ষা চতুর্থ ভাগ, শকুন্তলা, কথামালা, চরিতার্বলী, পদ্যসংগ্রহ (১ম ও ২য় ভাগ) এসব গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকের জন্য তিনি লেখেন। এখানেই তিনি ক্ষান্ত হননি। এগুলো পড়ানোর জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের একটা বিবরণ এখানে উপস্থাপন করা হলো-
এক, ১৮৫৬ সালে দক্ষিণ বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলায় পাঁচটি করে বিদ্যালয় স্থাপন করেন।
দুই, ১৮৫৭-এর নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাসের মধ্যে হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
তিন, শেষ জীবনে সাঁওতালদের এলাকা কার্মাটাঁড়ে বসবাসের সময় তাদের অনাড়ম্বর স্বাভাবিক জীবনে মুগ্ধ হয়ে তাদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
বাঙালি সমাজকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, উচ্চতর জীবন-দর্শনে জাগ্রত করার প্রয়াসে তাঁর কর্মপ্রয়াস এখানে থেমে থাকে নি। গুরুত্ব দিয়েছেন স্ত্রীশিক্ষার উপর। সমাজে নারী পুরুষ যৌথভাবে বসবাস করে। সমাজের নারী সমাজকে অবহেলিত রেখে আর যাই হোক সমাজের পূর্ণ অগ্রগতি সম্ভব নয়। এসব ভাবনা থেকে তিনি ফিরে তাকালেন সমাজের দিকে। অবাক হয়ে দেখলেন বিধবাদের দূরাবস্থা বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের কুফলগুলো। বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য সামাজিক সংস্কারে তিনি এগিয়ে এলেন। “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ গ্রন্থটি বের হলে হিন্দুসমাজে হৈ চৈ পড়ে যায়। গ্রন্থটির কোথাও পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও যুক্তি বোধের উদাহরণ মেলে না। তিনি বোধকরি জানতেন গোঁড়া হিন্দুসমাজকে জাগ্রত করাতে হলে প্রয়োজন ধর্মকে ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে অগ্রগতি সাধন। আর সে কাজটি তিনি যথার্থভাবে করেছেন। গ্রন্থটি বের হলে-
“…এক সপ্তাহের অনধিক কাল মধ্যেই, প্রথম মুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষে পর্যবসিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে উৎসাহিত হইয়া, আমি আর তিন সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করি। তাহারও অধিকাংশই অনধিক দিবসে, বিশেষ ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্বক পরিগৃহীত হয়।” (বিদ্যাসাগার রচনাবলী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৯)
নারীকে আত্মমর্যাদায় সমাসীন করার অভিপ্রায়ে বিধবাবিবাহের পক্ষে তার মত যদিও ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, তথাপি এর শেষাংশে যে বোধ কাজ করেছে তা একজন আধুনিকমনস্ক মানুষের। অবহেলিত নারী সম্প্রদায়ের উন্নতি কল্পে তাঁর এ ভাবনা বিজ্ঞান মনস্ক-
‘তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে।” (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৯)
বিদ্যাসাগরের এইভাব ভাবনার সাথে সামাজিক-অর্থনৈতিক কোন ক্রমধারা বিশ্লেষিত হয়নি। গোঁড়া হিন্দুসমাজ পাশ্চাত্যকে কোনকালেই সেভাবে গ্রহণ করেনি। বরং যুক্তির চেয়ে বিশ্বাস ছিল প্রবল এবং বিশ্বাসের দ্বারা তারা জীবন চালায়। ফলে এই বিশ্বাসকে আঘাত করতে হলে প্রয়োজন ধর্মকে ধর্ম দিয়ে এর মূলে কুঠারাঘাত করা। সে কাজটি বিদ্যাসাগর অত্যন্ত সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করেছেন। সামাজিক সব সমস্যা যে রাষ্ট্র সমাধান করবে তা আশা করা যায় না। রাষ্ট্র যেখানে পরাধীন এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে যখন কোন ঐক্যবদ্ধ রূপ দানা বেঁধে ওঠেনি তখন একজন যুক্তিবাদী সংস্কৃতিসেবী মানুষ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। বিদ্যাসাগরের রচনাব প্রায় সবটুকুই সমাজকে ঘিরেই। তাঁর কর্মক্ষেত্র সমাজ। সমাজ সংস্কারের বাইরে তিনি কোন রাজনৈতিক সভা, সংঘ, গোষ্ঠী সমিতির বৈঠকে যোগ দিতেন না। যদিও এ সভা, সংঘ, গোষ্ঠী গণতান্ত্রিক ও মুক্তির আন্দোলনে প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান। প্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষ অবশ্য এ সব প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের যোগদান না করা সম্পর্কে “তাঁর আকাশস্পর্শী স্বাতন্ত্র্যবোধের” কথা উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগর সে সময় নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান এবং তাঁর প্রচেষ্টায় বিধবা আইন পাশ হয়। ভারতবর্ষের দীর্ঘকালের ইতিহাস মন্ময়তার ইতিহাস, পাশ্চত্যের মত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিধ্বস্ততার কোন রূপ লক্ষ্য করা যায় না। ঐতিহ্যগত দিক থেকে নানা স্রোত মিশে নতুন স্রোতধারা তৈরি হয়েছে এদেশে। সেই স্রোতধারার মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভাষায় ‘বিদ্যাসাগর প্রধান পুরুষ’।
অনেকের ভাষায় বিদ্যাসাগর রাজনীতিবর্জিত সমাজসংস্কারক। কিন্তু তাঁরা হয়তো ভুলতে বসেছেন সমাজকে ঘিরে রাষ্ট্র এবং সমাজের বিধান পরিচালনা কর্মই রাজনীতি। তাই যদি হয় তবে তাঁর ভাবনা প্রচলিত রাজনীতির বাইরে থেকে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে। রাজনীতিতে থাকে দুটো দিক- এক, তত্ত্ব; দুই, প্রয়োগ।
এই অর্থে বিদ্যাসাগর একজন তাত্ত্বিক মানুষ, তাঁর সাধনা আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। সংস্কার সাধিত হয় সমাজের, সমাজ অগ্রগতি লাভ করে মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তার প্রতিফলনে। সেখানে ধার করতে হয় নি পাশ্চাত্যবোধকে। আমাদের যা কিছু সম্পদ, সে সম্পদ থেকে আহরণ করে সমাজকে নতুনভাবে চেনার প্রচেষ্টা বিদ্যাসাগরের। আর যেখানে আমাদের সমাজে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়নি, সামন্তচিন্তা-ভাবনা যার মূল চালিকাশক্তি, সেখানে পাশ্চাত্য ছকে সমাজকে বিচার করা যায় না। করলে বদহজম হবে বৈ কি! আমরা হয়তো ভুলে যাই-
“এই সব শান্ত-সরল গ্রাম-গোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক, প্রাচ্য স্বৈরাচারের তারাই ভিত্তি হয়ে এসেছে চিরকাল, মনুষ্য-মানসকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধিরি মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, তাকে করেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমস্ত কিছু মহিমা ও ঐতিহাসিক কর্মদ্যোতনা।” (উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে, মার্কস, এঙ্গেলস, পৃ. ৪২)
কালমার্কস ভারতবর্ষকে যেভাবে চিনেছেন সেভাবে চেনেননি অনেকেই। কালের ইতিহাসে ভারতীয় জীবন নিষ্ঠুরতা, হত্যাকাণ্ড ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর উপর পরিচালিত হয়েছে। ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ ভারতীয় জীবনব্যবস্থাকে পরিণত করেছে ধর্মীয় প্রথায়। একারণে “যেন না ভুলি যে ছোট ছোট এইসব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদ প্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাহিরের অবস্থার অধীন, স্বয়ং বিকশিত একটি সমাজ ব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে এবং এইভাবে আমদানি রেছে প্রকৃতির পশুবৎ পূজা, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমানরূপী বানর এবং শবলাদেবীরূপী গরুর অর্চনায় ভুলুণ্ঠিত করে অধঃপতনের প্রমাণ দিয়েছে।” (উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে, পৃ. ৪২)
ভারতের জীবন ব্যবস্থা যেখানে এরকম সেখানে কিভাবে তাদের এই প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত জীবনকে মুক্ত করা যায় সেটাই হলো বড় ব্যাপার। বিদ্যাসাগর একজন দার্শনিক মুক্তবুদ্ধির মানুষের মতো সমাজের জঞ্জালগুলো পরিষ্কার করতে চেয়েছেন। কচুরিপানা পূর্ণ পুকুরে যতই মাছের পোনা ছাড়া হোক না কেন তা বিকশিত হতে পারে না। বিদ্যাসাগর সমাজের কুসংস্কার ও জঞ্জালগুলো পরিষ্কার করার জন্য একদিকে যেমন শিক্ষার গুরুত্ব দিয়েছেন, অপরদিকে সামাজিক সংস্কার সাধনে জনমত গঠনে তৎপর হয়েছেন। এই তৎপরতা একজন আধুনিক রাজনৈতিক মানুষের মতো। হয়তো অনেকে বলতে পারেন তিনি কেন ব্রিটিশদের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি। এর বহু জবাব হয়তো আছে। ব্যক্তিগত জীবনে ইংরেজদের সবকিছুর সাথে একমত হতে পারেন নি বলে চাকুরি ছেড়েছেন। কিন্তু তিনি দেখেছেন সমাজকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করাতে হলে ভারতবর্ষের মানুষকে আত্মমর্যাদার সাথে জেগে উঠতে হবে। প্রস্তুতি নিতে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায়। অপরদিকে যাঁরা বিদ্যাসাগরকে বেশি করে আক্রমণ করেছেন তাদের উদ্দেশ্য দার্শনিক কার্ল মার্কসের উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য-
“এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে ইংলন্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংলন্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।” (উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে, পৃ. ৪২)
আর বোধ করি এ সম্পর্কে বেশি কিছু বলার থাকে না। অসাধারণ প্রতিভা ও দার্শনিক প্রত্যয়ে তিনি সমাজকে নিয়ে ভেবেছেন। এ সম্পর্কে ‘নীতিবোধ’ গ্রন্থটির কিছু আলোচনা যেতে পারে। গ্রন্থটিতে দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলনের পাশাপাশি সামাজিক আচরণিক প্রথার চিত্র প্রতিপাদিত হয়েছে। আর সমস্ত প্রবন্ধগুলো সমাজের মধ্যে অবস্থিত মানুষের চরিত্র গঠনমূলক। উপদেশের আশ্রয়ে তিনি একজন সমাজশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম (ক) পশুগণের প্রতি ব্যবহার, (খ) পরিবারের প্রতি ব্যবহার, (গ) প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, (ঘ) পরিশ্রম, (ঙ) স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, (চ) প্রত্যুৎপন্নমতি, (ছ) বিনয়, (জ) নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।
এসব প্রবন্ধগুলো যদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়, তবে বলতে হয় রাজনৈতিক চিন্তার গূঢ়তত্ত্ব অনেক সহজ, সাবলীল ভঙ্গিতে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। ইংরেজ শাসনের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন পাশ্চাত্য জীবনবোধ। পাশ্চাত্য জীবনবোধের সাথে মিলন ঘটিয়েছেন প্রাচ্যের এবং এ দুয়ের মিলনমেলায় ভারতবর্ষ জেগে উঠবে এটাই ছিলো বিদ্যাসাগরের ভাবনা। বিদ্যাসাগর তাঁর ‘চরিতাবলী’ ও ‘জীবনচরিত’ গ্রন্থে যে সমস্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাঁরা তো পাশ্চাত্যের বিখ্যাত ব্যক্তি। বিদ্যাসাগর যে শুধু আমাদের দেশের ঐতিহ্যকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন তা কিন্তু নয়। ধর্মীয় আচার প্রথার বিরুদ্ধে সংস্কৃত গ্রন্থ খুঁজে সামাজিক সংস্কার ব্রতী হয়েছেন, অপরদিকে চরিত্রগঠন ও জীবনবোধ উন্মোচনের জন্যে পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন। এছাড়া তাঁর গল্প, প্রবন্ধ যাই বলি না কেন, তা একান্তই সমাজকেন্দ্রিক। বিদ্যাসাগর একজন আধুনিক মানুষ, তাঁকে বিচার করতে হবে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে। কিন্তু তাঁকে যদি এ যুগে বসিয়ে বিচর করি তা খণ্ডিত একপেশে ছাড়া আর কিছুই হবে না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন নি, কিন্তু তা না করেও তিনি সবকিছুর ঊর্দ্ধে রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান ছিলেন। বিদ্যাসাগরও ঠিক তেমনি, সময়কাল বিবেচনায় রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন সমাজ সংস্কারক একজন আধুনিক মানুষ। কোন ফ্রেমে বন্দী করে বিদ্যাসাগরকে জানা যায় না, চেনা যায় না- সব গণ্ডী ভেদ করে সমাজের জঞ্জালকে সরিয়ে ভারতবর্ষের মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন। সামাজিক সচেতনতার দ্বারা ভারতবর্ষের মানুষ একদিকে যেমন তারা নিজেকে চিনবে, অপরদিকে করণীয় কাজ সম্পর্কে নিজেরাই দিক নির্দেশনা তৈরি করতে সক্ষম হবে। ইতিহাসের ঘটনাবলী সে সাক্ষ্য দেয়। আর তাছাড়া কোন মানুষই শ্রেণি নিরপেক্ষ নন, বিদ্যাসাগরও শ্রেণি চেতনার বাইরে এসে দাঁড়াননি। বরং সেখান থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের দূর্বল দিকগুলোকে উন্মোচিত করেছেন। তিনি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন, পথপ্রদর্শক হতে চান নি।
“দেশহিতৈষণার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর রাজনীতির ভিতটা পাকা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। অপক্ক বাঁশের নড়বড়ে ভিতে নীড়ের দশবিপর্যয়ের কথাটি জানতেন বলেই বিদ্যাসাগরকে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাগণ যখন তাদের দলে যোগদানের জন্যে অনুরোধ জানালেন, তখন তিনি তাদের সরাসরি প্রশ্ন করেন ‘দেশের স্বাধীনতা পেতে গেলে শেষ পর্যন্ত যদি দরকার হয় তারা কি তলোয়ার ধরতে পারবে?’ তাঁর এই প্রশ্নে সকলেই বিব্রত হলে বিদ্যাসাগর মশাই বলেন ‘আমাকে বাদ দিয়েই তোমরা এই কাজে এগোও।’ (শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ, পৃ. ৯২-৯৩) তলোয়ার মানে আত্মবিসর্জন যেমন বোঝায় আবার সংগ্রামী মনোবলও বোঝায়। এই মনোবল যাদের করায়ত্ব নয় তারা কি করে দেশ উদ্ধার করবেন। তাই তো তিনি বলেন ‘বাবুরা কংগ্রেস করছেন, আস্ফালন করছেন, বক্তৃতা করছেন, ভারত উদ্ধার করছেন। দেশের হাজার হাজার লোক অনাহারে মরছে, সেদিকে কারো চোখ নেই। রাজনীতি নিয়ে কি হবে? যে-দেশের লোক দলে দলে না খেয়ে প্রত্যহ মরে যাচ্ছে, সে-দেশে আবার রাজনীতি কি? (ক্ষিতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, ‘নবোদয়, বার্ষিক সাহিত্র পত্রিকা, ১ম বর্ষ (১৩৬২), পৃ. ৭৭) অর্থাৎ বৃক্ষ শীর্ষে জল সিঞ্চন ওঁর পছন্দ ছিল না প্রথমে চেতনা- তারপরে না রাজনীতি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেই পথটা সুগম করে দিয়ে গেছেন বিদ্যাসাগর তাঁর সমগ্র জীবনের কাজ দিয়ে।” (মীজানুর রহমান, সম্পাদক, মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক, বিদ্যাসাগর সংখ্যা)
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে এজন্যে বড়মাপের মানুষ হিসেবে দেখতেন, “সত্যপথের পথিকরূপে সন্ধানীরূপে নবজীবনের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে, ভাবীকালের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে একতালে পা ফেলে আমরা এই কথা বলতে পারব সেইদিনই এই-সকল মহাপুরুষদের স্মৃতি দেশের হৃদয়ের মধ্যে সত্য হয়ে থাকবে। আশা করি সেই শুভদিন অনতিদূরে।’ (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৯)।” মনীষী বিনয় ঘোষ উনিশ শতকের আধুনিক চিন্তার রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সামাজিক শ্রেণির মুখপাত্র হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কীর্তি অতুলনীয়, গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গঠনে তাঁর অবদান বৃহৎ এবং তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।