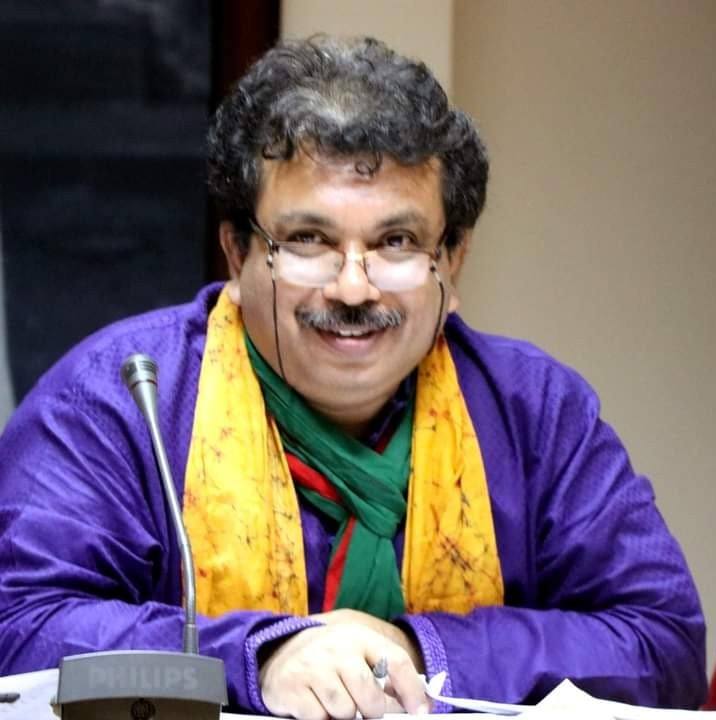বাংলা নববর্ষ উদযাপনের ক্ষেত্রে অর্ন্তবর্তীকালিন সরকারের ব্যাপক তৎপরতার মধ্যে মঙ্গল শোভাযাত্রা নামকরণ পরিবর্তনের ফলে একটা বিরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। রাজনৈতিক সংকট, সাংস্কৃতিক নৈরাজ্যের মধ্যে যা করা হয়েছে তা অনাহুত, অনাকাঙ্খিত। তবুও সংকট অতিক্রম করার প্রক্রিয়া যাই থাকুক না কেন, পয়লা বোশেখের নববর্ষ উদযাপন উৎসব, মঙ্গল শোভাযাত্রা, আনন্দ শোভাযাত্রা বাঙালির উৎসব, যা বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। এই উৎসবের ইতিহাস, ঐতিহ্য আদিকাল থেকে নানাভাবে, বিভিন্ন নাম-বৈচিত্র্যে বহমান হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ উত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতির নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করে।
লক্ষ্য করা যায়, বাংলাদেশে বর্ষবরণের উদ্যমে বাংলার সংস্কৃতি লোকশিল্পরীতিকে সাহচর্য করে জাতীয় সংস্কৃতির বিনির্মাণে নিজস্ব রূপরীতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। উত্তরাধিকারের ঐতিহ্যকে সারথি করে ভৌগোলিক, সামাজিক সংশ্লেষে সংস্কৃতির প্রবাহ জনজীবনে যুগ যুগ ধরে বাহিত হতে থাকে। কালক্রমে জাতি ধর্মের সাথে মিলেমিশে তা সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়। বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষের উৎসব পালিত হয় বৈশাখের প্রথম দিনে, আনন্দযজ্ঞে বৃহৎ জীবনের জয়গানে তা নিবিড় বন্ধন সৃষ্টি করে। বাংলা নববর্ষ বাংলাদেশের এবং বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষীদের বিশেষ ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে । যদিও রীতি পদ্ধতি আচার সংস্কার ও সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, তথাপি মৌলিক ঐতিহ্যকে সাথে নিয়ে পয়লা বৈশাখ বাঙালিদের নব ভাবনার ও প্রেরণার দিন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। জাতি ধর্ম কৃত্য বিভেদকে উর্দ্ধে রেখে একটি সর্বজনীন নববর্ষ উদযাপন বাঙালিদের নিজস্ব সংস্কৃতির স্মারক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যা ক্রমান্বয়ে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বাঙালির উৎসব হিসেবে বিশ্বের প্রায় সর্বত্র পালিত হয়ে থাকে । বিশ্বে বহু জনজাতি কিংবা দেশের নববর্ষ পালনের রীতি বহমান আছে, যা সেইসব দেশের সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও কৃত্যকে লালন করে। বাঙালির অন্যতম প্রধান উৎসব পয়লা বৈশাখ আধুনিক জীবনবোধের মাধ্যমে সংস্কৃতির নব জাগরণ সৃষ্টি করেছে।

ঢাকায় দীর্ঘবছর পয়লা বৈশাখ উদযাপন বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। ’৪৭ সালে ভারত বিভাজনের পর যে পূর্ববাংলা, বর্তমানে বাংলাদেশ তা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা থেকে অনিবার্যভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেই সময়ে পয়লা বৈশাখ পালনের তথ্য ও ইতিহাস শিক্ষাবিদ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, ‘রাজনৈতিক পালাবদলের পটভূমিতে ‘পয়লা বৈশাখ’; একটা পাপশক্তির মুকাবিলায় প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আর আত্মপরিচিতের পতাকা উত্তোলন করে তবে আমাদের এই বৈশাখের যাত্রা শুরু। ইতিহাসের ছাত্র, সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মী জহুর হোসেন চৌধুরীর বয়ানে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি তথ্য এখানে উদ্ধৃত, তা থেকেই বোঝা যাবে। প্রথমত জানাচ্ছেন সমকালের কথা: ‘পাকিস্তান হওয়ার পরই বাঙালি মুসলমানেরা নিজেদের জাতীয় সত্তা সম্বন্ধে তীব্রভাবে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করল পাকিস্তানী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকারী উর্দুভাষী অবাঙালি মুসলমানের দৌরাত্ম্যে।’ তাঁর দ্বিতীয় তথ্য: ‘১৯৫১ সালে (ঢাকায়) ওয়ারি সাত নং হেয়ার স্ট্রিটে কয়েকজন লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, অধ্যাপক মিলে ‘লেখক-শিল্পী মজলিস’ নামে একটি সংগঠন করে রেলওয়ের মাহবুব আলী ইনস্টিটিউটে এদেশে প্রথম পয়লা বৈশাখ সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানে যে লোক সমাগম হয়েছিল তা উদ্যোক্তাদের রীতিমত হতচকিয়ে দেয়। বুঝা গেল ইতিহাস অলক্ষে কাজ করে যাচ্ছে অতঃপর তৃতীয় তথ্যে মন্তব্যে সিদ্ধান্ত যে, ‘১৯৫১ সালের পয়লা বৈশাখ যেন পটভূমি রচনা করে বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির। এই পয়লা বৈশাখ আমাদের প্রথম আন্দাজ ও আত্মবিশ্বাস দেয় আমাদের জাতীয় চেতনার গভীরতা সম্বন্ধে।’’

মহান মুক্তিযুদ্ধ উত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে নববর্ষ পালনের বৃহৎ ও ব্যাপকতা লাভ করে। বিশেষ করে রমনার বটমূলে ছায়ানটের (প্র.১৯৬১) বর্ষবরণ অনুষ্ঠান, ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান, বাংলা একাডেমির কবিতা পাঠের আসর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীদের মঙ্গল শোভাযাত্রাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। তবে চারুকলা অনুষদের বহুবিচিত্র বর্ণিল পশুপাখির অবয়ব, রঙিন মুখোশসহ মঙ্গলশোভাযাত্রা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।
বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আবেদন ও প্রচেষ্টায় জাতিসংঘের সংস্থা ইউনেস্কো ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর মঙ্গলশোভাযাত্রাকে সাংস্কৃতিক হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করে। আজকের পয়লা বৈশাখের মঙ্গলশোভাযাত্রা দেশের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বপথে বাঙালিসহ সকল জনজাতির উৎসব বৈচিত্র্যের আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতির দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।পয়লা বৈশাখে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই উৎসব মুখর পরিবেশে লোকসংগীত, যাত্রাপালা, পুতুল নাচ, সাপখেলা, গ্রামীন খেলায় মেতে ওঠে। কোথাও কোথাও আয়োজন হয় বৈশাখী মেলার। মেলায় লোকশিল্পীদের আলপনায় সমৃদ্ধ শখের হাড়ি, মাটির খেলনা, মুখোশ, ডালা, কাগজের ফুল সহ বিবিধ লোকসামগ্রী পাওয়া যায়। এই সমস্ত লোকসামগ্রীতে গাঁয়ের সরল জীবন, প্রকৃতি, মাছ, পাখি, হাতি, ঘোড়া, লতা, ফুলের আলপনায় নিঁখুত চিত্রের সৌন্দর্য বহন করে। মেলার চত্বরে বিক্রয় হয় মুখরোচক গাঁয়ের মিষ্টি-মিঠাই, বিশেষ করে খাজা-গজা, মুড়ি-মুরকি, চিনি বা গুড়ের তৈরি মাছ, হাতি, ঘোড়া, পাখি আকৃতির মিঠাই উল্লেখযোগ্য। মেলার মাঠে সুসজ্জিত নাগরদোলায় শিশু কিশোররা চড়ে আনন্দ পায়। বৈশাখী মেলার একাল সেকালের মধ্যে প্রভেদ হয়েছে। তবুও দেখা যায়, “গাছের ছায়ায় এবং এর বাইরে সামিয়ানার মতো চাদর বা ক্যানভাসের আচ্ছাদনে সাজানো ছোট ছোট অস্থায়ী দোকান। দোকান সাজানো হতো রকমারি জিনিস দিয়ে। বাঁশি, বেলুন, বিভিন্ন আকারের খেলনা ও পুতুল এর মধ্যে পোড়ামাটির ছোট্র টেরাকোটা পুতুলও থাকতো- প্রধানত টিকালো নাক মাথায় খোঁপা নারীমূর্তি- যেগুলোর দিকে কিশোরীদেও ঝোঁক ছিল সবচাইতে বেশি), রঙিন কাচের চুড়ি, রেশমী ফিতা, চুলের কাঁটা, বিদেশী ছুরি থেকে হরেক রকমের শিশু পণ্যে মেলার চেহারাটাই হয়ে উঠতো জাদুকরী চরিত্রের।

অন্যদিকে গ্রামের কৃষকেরা সাজিয়ে বসতেন কৃষিপণ্য নিয়ে যেমন তরমুজ, খিরা, বাঙ্গি, উচ্ছে-করলা, বেগুন ইত্যাদি শাকসবজিই প্রাধন্য পেতো। আর দোকানিদেও সযত্নে সাজানো বিভিন্ন ধরনের মিঠাই, মিষ্টি, মণ্ডা, লাল পানির সরবত (তাই বলে ‘সুরা’ নয়)। থাকতো গ্রামীণ ললনাদের ব্যবহারের উপযোগী জিনিসপত্র। থাকতো ঘরোয়া ব্যবহারের জিনিসপত্রও, যেমন- কুলা, চালুনি, বেগুন-পিড়ি কিংবা চাষাবদেও সরঞ্জাম বলা যেতে পারে স্টেয়ার পার্টল। এভাবেই পয়লা বৈশাখের মেলা গ্রামাঞ্চলে পেয়ে যেতো সর্বাঙ্গীণ রুপ।
আদিকালে নববর্ষের উৎসবকে আর্তব উৎসব বলা হতো, ইংরেজীতে যাকে Seasonal Festival বলা হয়। সূর্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নে যে ঋতুর পরিবর্তন হতো , তা দেখে আদিকালের গোষ্ঠীভিত্তিক মানুষ উৎসবে মেতে উঠতো । এই নববর্ষ উদযাপনের ধারাবাহিক তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়, ২১ সেপ্টেম্বর শারদীয় বিষ‚ বদিনে প্রাচীন মিসরীয়, ইরানীয়্ ও ফিনিশীয়গণ, ২১ মার্চ বাসন্ত বিষুব-দিনে প্রাচীন ইহুদিগণ, ২৫ ডিসেম্বর সূর্যের দক্ষিণ-অয়নান্ত দিনে ইংল্যান্ডের এংলো-স্যক্সনরা, ২১ ডিসেম্বর সূর্যের দক্ষিণ-অয়নান্ত দিনে প্রাচীন গ্রীক রোমানরা, চান্দ্র বছরের প্রথম মাস, মহররমের প্রথম দিনে প্রাচীন আরবরা। এ ছাড়াও বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায় নববর্ষ উদযাপন করে তাদের ধর্ম ও কৃত্যের অনুষঙ্গে। প্রাচীন ইরানীয়দের মতো ভারতীয় আর্যদের সৌরমাস সমন্বিত চান্দ্রমাসে নববর্ষ পালনের রীতি ছিল। প্রাচীন কালে মানুষ যখন যাযাবর তখন তিথি ভিত্তিক মাস ও বছর গণনা করার প্রচলন ছিল। সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষ প্রবেশ করে কৃষিতে এবং কৃষিকাজ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ফসল চাষ এবং ফলন ফলে থাকে। ফলে চান্দ্র- সৌর বছর ভিত্তিক গণনার রীতি প্রাচীনকালে বিদ্যমান ছিল, এবং হিসেব-নিকেশ করে ফসল ফলানোর প্রচেষ্টা প্রাচীন সভ্য জাতিসম‚হে লক্ষ্য করা যায়। সেই ধারাবাহিকতায় ভারতে তিনদিনব্যাপী দোল উৎসব, ইরানে ছয়দিনব্যাপী নওরোজ উৎসব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে পালিত হয়। তিব্বতীদের লোগসর, খ্রিস্টানদের ক্রিস্টমাস, ভিয়েতনামীদের তেত, ইহুদিদের রুশ হাশানা, শ্যামবাসীদের ত্রাত, মুসলিমদের আশুরা প্রভৃতি নববর্ষ জ্ঞাপক উৎসব বলা হয়। কালে কালে এইসব উৎসবের সাথে ধর্মীয় আচার ও নিষ্ঠা যুক্ত হয়ে উৎসব ভিন্নমাত্রায় পর্যবসিত হয়েছে। আদিকালে নববর্ষ উদযাপন ছিল ঋতু উৎসব। প্রকৃতির রূপ ও বৈচিত্রের সাথে লক্ষ্য রেখে সৃষ্টি হয়েছে মাসের। সে কারণে ভৌগোলিক তারতম্যের জন্য নববর্ষ উৎসব ফসল উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। প্রকৃতির নানা রূপ বৈচিত্রে সংযুক্ত হয় অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব, যা নানা দেশে নানা ভাবে ধর্মের সাথে এই অদৃশ্য শক্তির বিশ্বাস কৃত্যরূপে আর্বিভ‚ত হয়। এই অদৃশ্য শক্তির আনুকল্য পাবার ইচ্ছেই নিবেদনম‚ লোক পূজা অর্চনা, প্রার্থনার তথা ধর্ম পালনের সম্পর্ক যে কোন উৎসবের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। ফলে নববর্ষ উৎসব কালে কালে ধর্মের আচার প্রথা, বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বাহিত হয়েছে, তবে যুগের পরিবর্তনে প্রথা ও উৎসবের বৈশিষ্ট্য নানা মাত্রিকতায় পালিত হচ্ছে।

আদি ভারতে নানাবিধ অব্দের প্রচলন ছিল, তারমধ্যে বিক্রমাব্দ, শকাব্দ বর্তমান অবধি প্রচলিত রয়েছে। প্রাচীন প্রাচ্যে কোন সম্রাটদের প্রচলিত কিছু অব্দের তথ্য পাওয়া গেলেও তার প্রচলন বিলুপ্ত হয়েছে।
আলবেরুনি’র তথ্য অনুযায়ি শ্রীহর্ষাব্দ, বলভাব্দ, গুপ্তাব্দে’র কাল গণনার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। উত্তর ভারতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক গুপ্তাব্দের প্রচলন হয়েছিল, ৩২০–৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাল গণনা করা হতো। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে হর্ষাব্দের প্রচলন করেন। রাজকার্যের সুবিধার্থে কালগণনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । উজ্জয়িনীর রাজা শকদের পরাজিত করে ‘বিক্রমাদিত্য’ নামক নতুন অব্দের প্রচলন করেন। ভারতের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বিক্রমাব্দ ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়। তবে ভারতের প্রায় সর্বত্র শকাব্দকে কালগণনায় ব্যবহার করা হয়। বিখ্যাত জ্যোর্তিবিদ বরাহ মিহিরের (মৃত্যু ৫৮৭খ্রি.) সময়কাল বা পূর্ব থেকেই প্রচলিত শকাব্দের বিভিন্ন নামে অভিহিতি করা হতো। যেমন- শক-কাল, শকভূপ কাল, শাকেন্দ্র কাল, শালিবাহন শক, শকসংবৎ। “উজ্জয়িনীর শক-ক্ষত্রপদের (১৩০-৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) উদ্ভবের সাথে এই শকাব্দের জন্মের যোগ রয়েছে। তাদের দলিলপত্র উৎকীর্ণে রাজ্যাভিষেক ভিত্তিক সনের উল্লেখ রয়েছে কিন্তু সরাসরি শকাব্দ নাম নেই।

শকাব্দের প্ররম্ভ বছর নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। কনৌ’র (konow) মতে এটি ৮৮ খিষ্টপূর্বাব্দ; অর্থাৎ প্রবল প্রতাপশালী মিত্রাদতের মৃত্যুর তারিখ থেকে (যিনি শকদের দর্প খর্ব করেছিলেন) সূচনা হয়। জয়সওয়ালের মতে এর শুরু ১২০ খ্রি.পূ ., হার্জফেল্ড (Herjfeld Rapson)-এর মতে ১১০ খ্রি.পূ., টার (Tarr)- এর মতে ১৫৫ খ্রি.পূ.। অন্যদিকে প্রাচীন শকাব্দের শুরু ১২৯ খ্রি. পূ. বলে মনে করেন ভ্যান লহুইজেন দ্য লিঙ্গউ (Van Lohuzien de leeuw)।”
বাংলায় শকাব্দের প্রচলন থাকলেও কখনো বিক্রমাব্দ ব্যবহৃত হয়নি। পাল আমলে ( ৭৫০-১১৫০ খ্রিস্টাব্দ) কোনো নতুন অব্দের প্রচলন না করলেও রাজ্যভিত্তিক কাল গণনা করতেন বলে জানা যায়।
“সেন রাজারা তাম্র উৎকীর্ণে, শিলালিপিতে ও নানাবিধ প্রশাসনিক কাজকর্মে ‘ রাজ্যাভিষেক বছর’ বছর ব্যবহার করতেন। তবে লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে লক্ষণাব্দ নামে একটি অব্দ স্বল্পকালে প্রচলিত ছিল। বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর প্রকৃত অর্থে সর্ববঙ্গীয় কোনো অব্দ বাংলায় প্রচলিত ছিল না। রাজকীয় কার্যে হিজরী সন ব্যবহৃত হতো। তবে জ্ঞানী-গুণীজন তাঁদের লেখা ও জ্ঞান চর্চায় শকাব্দ ব্যবহার করতেন, আর সাধারণ মানুষ ‘পরিগনাতি’ নামে প্রচলিত একটি অব্দ ব্যবহার করত; হিন্দু রাজত্বেও অবসানের কাল তেকে তা চালু হয় বলে মনে করা হয়।”

বাংলা সনের প্রবর্তনের ইতিহাসে বহু মত বিদ্যমান থাকলেও নিম্নোক্ত মতামতকে ইতিহাসবিদগণ স্বীকৃতি দিয়েছেন।
মুঘল সম্রাট জালালউদ্দিন মোহাম্মদ আকবর ১৫৫৬ সালে ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তখন ভারতবর্ষে নানারকম সন প্রচলিত ছিল, এর কোনটি সৌর, কোনটি চান্দ্র মাসের রীতিতে গণনা করা হতো। ফলে শাহী দরবারের লেনদেনে, খাজনা আদায়ে অসুবিধার সৃষ্টি হতে থাকে। এই অসুবিধা নিরসনের জন্য সম্রাট আকবর নতুন সন প্রবর্তনের আদেশ জারী করেন। তাঁর সিংহাসন আরোহনের হিজরি সন ৯৬৩কে সৌরসেনে পরিবর্তন করে নতুন সনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এই সনই বাংলা সন হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। “সাধারণভাবে বলা হয় যে, দিল্লিতে সম্রাট আকবর কর্তৃক ‘তারিখ ই-ইলাহি’ প্রবর্তিত হলে বঙ্গদেশে এই সূত্র ধরে সূর্যসিদ্ধান্ত ভিত্তিক সৌরবৎসর ব্যবহার শুরু হয়। কাজেই বলা যেতে পারে বাংলা সন হলো একটি সঙ্কর শব্দ যার মূল ভিত্তি ছিল হিজরী সন, কিন্তু গণনা করা হতো সৌরবৎসর ধরে।”
সম্রাট আকবর প্রবর্তিত তারিখ ই-ইলাহি’র আদর্শে বাংলা, উড়িষ্যা, বিহার, দাক্ষিণাত্য, বোম্বাই রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার ফসলি সন প্রবর্তিত হয়েছিল। তবে কেউ কেউ বিষয়টির ভিন্ন মত প্রকাশ করে রাজা শশাঙ্ক এবং হোসেন শাহীর নাম উল্লেখ করেছেন। এই দুটি মতের স্বপক্ষে তথ্যনিষ্ঠ কোন প্রমাণাদি পাওয়া যায়নি বলে গবেষকগণ মনে করেন।
বাংলা সনের সমুদয় বিষয়াদি নিয়ে ভাষাবিদ ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে ১৯৬৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় পণ্ডিত অবিনাশ চন্দ্র, সতীশ চন্দ্র শিরোমণি, তারাপদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক এম এ হামিদ, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ:
১. মুঘল আমলে বাদশাহ আকবরের সময়ে হিজরী সনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে যে বঙ্গাব্দ প্রচলিত আছে, তাহাতে বছর গণনা করতে হবে।
২. ইংরেজি মাস ২৮, ৩০ কিংবা ৩১ দিনে হয়, কিন্তু উপসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলা মাস গণনার সুবিধার জন্য বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত পাঁচ মাসের প্রতিমাস ৩১ দিনে এবং আশ্বিন থেকে চৈত্র পর্যন্ত বাকি সাত মাসের প্রতিমাস ৩০ দিন হিসেবে গণনা করতে হবে।
৩. অতিবর্ষের (লিপ ইয়ার) চৈত্র মাস ৩১ দিনে হবে। ৪ দ্বারা যে সাল বিভাজ্য, তাই অতিবর্ষ বলে পরিগণিত হবে।”
বঙ্গাব্দ কিভাবে গণনা করা যায়, তা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন- ১৫৫৬ আকবরের সিংহাসন আরোহনের সময়কাল ধরে বাংলা সনের গণনা করা যায়। ২০২৪-১৫৫৬= ৪৬৮, এর সাথে ৯৬৩ হিজরী সন যুক্ত করলে হয় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ। এভাবে হিজরী সনকে পরিবর্তন করে বাংলা সনের প্রবর্তন করা হয়েছে।
ভারতে জ্যোতিপদার্থবিদ ড. মেঘনাদ সাহা’র নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালে বর্ষপঞ্জি সংস্কারের সুপারিশ করা হয়। সেই সুপারিশ ছিল শকাব্দের। শকাব্দের বর্ষ শুরু হবে চৈত্র মাসে, শেষ হবে ফাল্গুনে। কিন্তু সনাতনপন্থি পঞ্জিকাকারগণ এই সুপারিশ অগ্রাহ্য করে প্রাচীন ধারাবাহিকতায় পঞ্জিকা প্রণয়ন করে থাকেন।

সম্রাট আকবরের ফসলি সনের আদর্শে বঙ্গাব্দের প্রবর্তিত হলেও বৈশাখের সূচনা কিভাবে হলো, তা নিয়ে অভিন্ন ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় না। তবে লোকজ উৎসব, অনুষ্ঠানের সাথে বৈশাখের সম্পর্ক জনজীবনে বিভিন্নভাবে লক্ষ্য করা যায়। কৃষিভিত্তিক জনজীবনের সাথে ব্রত বা উৎসব পালনের প্রথা ভারতবর্ষে বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশে লৌকিক অনুষ্ঠানের সূচনা বিষুব সংক্রান্তিতে, সমাপ্ত হতো বৈশাখে। বৃটিশ আমলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ওয়াজিরাবাদে বৈশাখী নামে কৃষিভিত্তিক উৎসবের কথা জানা যায়। এই উৎসবে হিন্দু মুসলিম শিখসহ সকলেই অংশ নিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে বৈশাখে অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত, পুণ্যিপুকুর ব্রত, অশ্বত্থ ব্রত, পৃথিবী ব্রত সহ বৃষ্টির মাধ্যমে ফসলের রক্ষায় ব্রত উদযাপিত হয়। বৈশাখ মাসে রাজশাহীর গম্ভীরা, বিভিন্ন অঞ্চলে আমান উৎসবের প্রচলন আছে।
বাংলা সন যেভাবে প্রবর্তিত হয়েছে, তার সাথে ধর্মীয়, লোকজ বিশ্বাস সংযুক্ত হয়ে শাহী দরবারের লেনদেন, খাজনা আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। জমিদারদের প্রথায় খাজনা আদায়ের অনুষ্ঠানকে পুণ্যাহ্ন বলা হয়। সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তনে পয়লা বৈশাখ ব্যবসায়ীদের হালখাতার দিন এবং কালক্রমে বাংলাদেশের নাগরিকের মিলনের দিন, উৎসবের দিন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।
জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সম্প্রীতির দিবস পয়লা বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নববর্ষ প্রবন্ধে প্রত্যাশা প্রার্থনা করেন, অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতে আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব, সায়াহ্ণে যখন বিশ্রামের ঘন্টা বাজিবে তখনো তাহা ঝরিয়া পড়িবে না, তখন সেই অম্লান গৌরব মাল্যখানি আর্শীবাদের সহিত আমাদের পুত্রের ললাটে বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে নির্ভয়চিত্তে সবল হৃদয়ে বিজয়ের পথে প্রেরণ করিব।”
পয়লা বৈশাখের আনন্দ উৎসবে বাঙালির চেতনা সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক । এই বৈশাখী উৎসব বাঙালির সম্প্রীতির উৎসব, জেগে ওঠার উৎসব, নব ভাবনার অভিষেকের উৎসব, মহৎ কাজের দুঃসাধ্য সাধনার উৎসব । বাংলা সংস্কৃতির উৎসব – পয়লা বৈশাখের উৎসব, এ উৎসব শান্তি চেতনাকে বিকশিত করে বিশ্বব্যাপী নবতর ভাবনার উদ্বোধন ঘটাতে পারে।
বাংলাদেশের সর্বত্র নববর্ষ পালনের হৈ-হুল্লোড়, আড্ডা, গান-বাজনার সাথে ভুরিভোজ, ইলিশ পান্তা, ভর্তা সহ উপাদেয় খাবারের সংযোগ ঘটেছে। বিগত কয়েক বছর ইলিশ মাছ নগরের বৈশাখী উৎসবের সাথে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, যদিও কোনকালেই ইলিশ-পান্তা নববর্ষের সাথে সম্পকির্ত ছিল না। সংস্কৃতি যদি বিবর্তনশীল হয়, তবে সে ক্ষেত্রে এই সংযোগ নতুন মাত্রা দিয়েছে। তবে ইলিশ নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতি কোনোভাবেই কাম্য নয়। তবে ইলিশের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশীয় খাবার দিয়ে নগরের পয়লা বৈশাখ উৎসব আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে।

দেশের প্রান্তিক জনপদে বৈশাখের উৎসবে বীরত্বব্যঞ্জক লাঠিখেলা, কাবাডি বা হা-ডু-ডু, গোল্লাছুট, ডাংগুলি, টুষি, কড়ি, চোখবান্দা, বলীখেলাসহ বিবিধ খেলা উৎসাহের সাথে অনুষ্ঠিত হবার তথ্য পাওয়া যায়। পয়লা বৈশাখের উৎসব ও আয়োজন সমকালে বাংলাদেশের শহর গ্রামসহ সর্বত্র ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে পালিত হয়। প্রাচীন কালের সাথে আধুনিক জনজীবনের সেতুবন্ধনে পয়লা বৈশাখের সমাজৈতিহাসিক তাৎপর্য বহন করছে।
বৈশাখের নানা আয়োজনে গীত হয়, তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো–
১. ‘এসো হে বৈশাখ, এসো এসো/ তাপস নিঃশ্বাস বায়ে/ মুমুর্ষুরে দাও ওড়ায়ে/ বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক/ … ‘ মুছে যাক গ্লানি/ ঘুচে যাক জরা/ অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা’ ( রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
২. ‘ ঐ নূতনের কেতন ওড়ে/ কাল বোশেখির ঝড়/ তোরা সব জয়ধ্বনি কর।’ (কাজী নজরুল ইসলাম)
৩. ‘ দুই পরি বালা ধারির গজো বিছাই শীতলপাটি।/ গরমের তাবেল্লায় বেটায় খায় লুটোপুটি।/ গরমর মওছুম আর দুই পরিয়া বালা/ আগিন্ও লাকান রদিও তেজে শরীলো লাগছে জ্বালা।/ পাটিতে হুতিয় বেটায় পাখাদি পাইল্লায়’ (পালা গান, সিলেট গীতিকা)
৪. “ওই এলো বৈশাখ/ খর রোদ্দুর/ হঠাৎ আকাশ মেঘে/ টইটম্বুর;/ নামবে বৃষ্টি আর/ উঠবে কি ঝড়, / থেকে থেকে মেঘ ডাকে/ কাঁপে অন্তর (মহাদেব সাহা)

পয়লা বৈশাখের আয়োজনের ইতিহাসে অসংখ্য অনাহুত ঘটনাবলির দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করেছে বাংলার মানুষ। সেইসব অপতৎপরতা, বিরূপ প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে পয়লা বৈশাখ প্রতিবছর উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশে সরকার কর্তৃক ঘোষিত পয়লা বৈশাখ পালনের নির্দেশনা, প্রণোদনা দিয়েছেন।
কিন্তু মঙ্গলশোভাযাত্রার নামকরণ পরিবর্তন করে আনন্দ শোভাযাত্রা করা হয়েছে। জনসংস্কৃতির উৎসব নিয়ে বিতর্কের মধ্যে পালিত হবে পয়লা বোশেখ। এই উৎসব জাতীয়। রাষ্ট্রের সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তারা উৎসব ভাতা পেয়ে থাকেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কিছু কিছু শিল্প কলকারখানার কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও উৎসব প্রণোদনা পেয়ে থাকেন। ফলে বাংলাদেশের পয়লা বৈশাখ উদযাপন বাঙালি জাতিসত্তা ও রাষ্ট্রসত্তার অবিচ্ছেদ্য উৎসবে পরিণত হয়েছে।
পয়লা বৈশাখের উদযাপনের সাথে আদি ঐতিহ্য, লোকজ সংস্কৃতির সংযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। পয়লা বৈশাখ উদযাপনের সময়কালে কোথাও কোথাও নেতিবাচক ঘটনার তথ্য পাওয়া যায়। এসব বহুবিধ কারণে বাঙালি জাতিরাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার জন্য কতিপয় কার্যক্রমকে সংযোজন করতে হবে। পণ্ডিত প্রবোধচন্দ্র বাগচী ‘দিব্য স্মৃতি’ প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, ‘প্রাচীন শিল্প কলা সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের মনের যোগ ছিন্ন হয়েছে। উপরন্তু ভেদবুদ্ধি এ-ছত্রভঙ্গ জাতিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সুতরাং এই দুর্দিনে আমরা যদি আমাদেও অতীতের উপর শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনতে পারি, প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদেও মনের যোগসূত্র আবার সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত করতে পারি তাহলে আমরা আবার সচেতন হয়ে উঠতে পারব। আমরা আবার একটি আত্মনির্ভরশীল ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হয়ে উঠব।”

বাংলা নববর্ষ উৎসব সকল জনগণের জনসংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। প্রাচ্য ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য পয়লা বৈশাখের উৎসবের মধ্যদিয়ে সমগ্র সমাজকে অখণ্ড তাৎপর্য দান করছে। বহুযুগের ‘আনন্দরূপমৃতম’-এর সম্মিলন জ্ঞান কর্মে কৃত্যে জ্যোতিতে বিশ্বপরিমণ্ডলকে শান্তির মহিমায় গৌরবান্বিত করবে। আর সকল অমানিশা দূরীভূত হয়ে বাংলাদেশের জনপ্রান্তর নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাবে।
“দারুণ অগ্নিবাণে রে হৃদয় তৃষায় হানে রে।।
ভয় নাহি, ভয় নাহি। গগনে রয়েছি চাহি।
জানি ঝঞ্ঝার বেশে দিবে দেখা তুমি এসে
একদা তাপিত প্রাণে রে || (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
তথ্যনির্দেশ:
১. নববর্ষে দেখি বৈশাখের মুখ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, বাংলাদেশের উৎসব: নববর্ষ, বাংলা একাডেমী, মোবারক হোসেন (সম্পাদক প্রথম প্রকাশ পহেলা বৈশাখ ১৪১৫/ ১৪ই এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ২৪৮
২. বৈশাখী নববর্ষ : সেকালে একালে, আহমদ রফিক, নববর্ষ ও বাংলার লোক-সংস্কৃতি, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (সম্পাদনা), সূচীপত্র, ঢাকা, বৈশাখ ১৪১৮/ এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৭৬
৩. বঙ্গাব্দের উৎস সন্ধানে: একটি সমীক্ষা, অজয় রায়, বাংলাদেশের উৎসব: নববর্ষ, মোবারক হোসেন (সম্পাদক), বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ পহেলা বৈশাখ ১৪১৫/ ১৪ই এপ্রিল ২০০৮ পৃ.০৭)
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৮
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৮
৬. বাংলা সন ও পহেলা বৈশাখ, ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ- চৈত্র, ১৩৭৪, সং কামরুল ইসলাম, প্রবন্ধ সংগ্রহ, আজমাইন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ফাল্গুন ১৪২২/ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)
৭. নববর্ষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবন্ধ সংগ্রহ, সময় প্রকাশন, চতুর্থ মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১১, পৃ. ১৬৩
৮. সংগৃহিত।
৯. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, দেশÑবিদেশের সংস্কৃতি, নবার্ক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৯২, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ৭৫
সহায়ক গ্রন্থসমূহ
১. মোবারক হোসেন (সম্পাদক) বাংলাদেশের উৎসব: নববর্ষ, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ পহেলা বৈশাখ ১৪১৫/ ১৪ই এপ্রিল ২০০৮
২. জয়নাল আবেদীন খান, বঙ্গাব্দ, বাংলা সন ইতিাস, উৎপত্তি ও বিকাশ, পাঠক সমাবেশ, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৯/ বৈশাখ ১৪১৬
৩. সন্জীদা খাতুন, সংস্কৃতি-কথা সাহিত্য-কথা. জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১লা বৈশাখ ১৪১১, এপ্রিল ২০০৪
৪. সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০–১৯৮২), অনন্যা, ঢাকা, বইমেলা ২০০১
৫. ড. কাজী মুহম্মদ, বাংলা সন ও পহেলা বৈশাখ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা – মাঘ- চৈত্র, ১৩৭৪
৬. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পুনমুদ্রণ জানুয়ারি ২০১১,
৭. দিলীপ কুমার দত্ত, প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ: উৎসব ও ভবন, প্রকাশক: দিলীপ কুমার দতÍ, ভুবননগর, বোলপুর, প্রথম প্রকাশ ৭ই পৌষ ১৪০৭
৮. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, দেশে বিদেশের সংস্কৃতি, নবার্ক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৯২, সেপ্টেম্বর
১৯৮৫
৯. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (সম্পাদনা), নববর্ষ ও বাংলার লোক-সংস্কৃতি, সূচীপত্র, ঢাকা, বৈশাখ ১৪১৮/ এপ্রিল ২০১১
১০. কামরুল ইসলাম, প্রবন্ধ সংগ্রহ, আজমাইন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ফাল্গুন ১৪২২/ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবন্ধ সমগ্র, সময় প্রকাশন,চতুর্থ মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১১