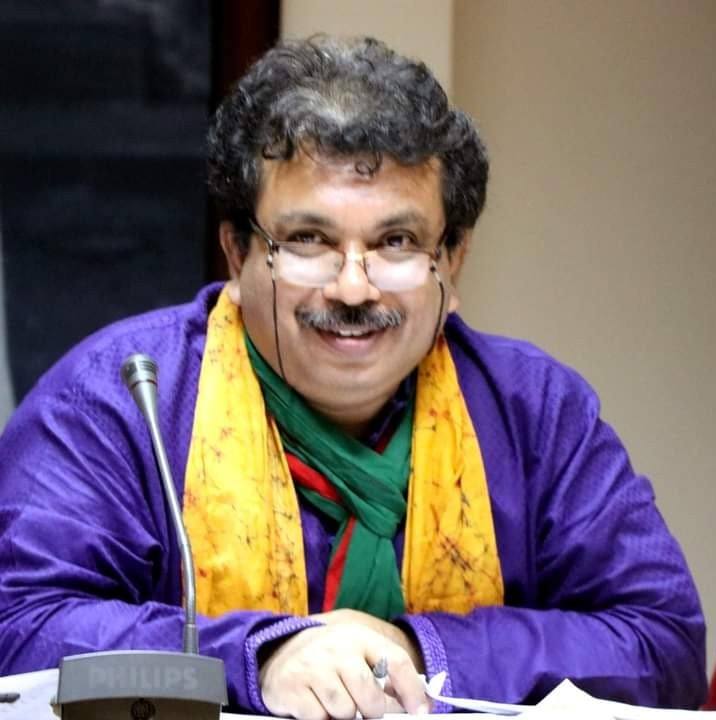আদিকালের শ্রুতি অনুযায়ি গুরুপূর্ণিমার সংস্কৃতি বিশ্বজনপদকে সভ্যতার পথে পরিচালিত করতে উৎসাহিত করে। মানব জীবনের পটভূমি থেকে বিস্তৃত ইতিহাসের কেন্দ্রভূমিতে ধর্ম ওতোপ্রোতোভাবে মিশে আছে। ম্যাক্স মুলার হয়তো একারণে বলতে প্রয়াসী হয়েছেন, ধর্মের ইতিহাসই মানুষের প্রকৃত ইতিহাস। এই ইতিহাসের উপাদন যুগ যুগ ধরে বহমান হয়েছে কৃত্যে, সংস্কৃতিতে। আচার আচরণ, বিশ্বাস আবেগ, রীতিনীতি, প্রথা, জীবন যাপনসহ ভাষা উপাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি করেছে। সেই বন্ধন পরম সত্তার সাথে জীবনপ্রক্রিয়ার মিলনে দর্শনের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় অর্থকে জীবনের সাথে অঙ্গীভূত করে। সনাতন বলে যা আমরা জানি, তার উত্তরাধিকার হিসেবে অপার্থিব অনুভূতি তথা উপলব্ধিকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করতে শেখায়। একথা আমরা বলতে আগ্রহী, ধর্মের অস্তিত্বের সাথে বিজ্ঞানও পরিপূরক অবস্থান সৃষ্টি করে জীবন যাপনে বৈচিত্র্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এই বৈচিত্র্যের অধ্যায়ে ‘ গুরুপূর্ণিমা’ প্রথম প্রথা, যা প্রগতির পথে মহাবিপ্লব বলে মনে করা যেতে পারে। ধর্মের চিরায়ত ঐতিহ্য জ্ঞানশাস্ত্রকে বিকশিত করে। প্রগতির বিশ্লেষণে যত ব্যাখ্যা থাকুক না কেন, ধর্ম দর্শনের সাথে প্রতিতুলনায় অনুসন্ধান ব্যাখ্যা অব্যাহত আছে। তথাপি পরিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কখনোই সম্ভব হয়নি। জ্ঞান প্রযুক্তির নিত্যনতুন আবিষ্কার, ব্যবহার যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, ততই ব্যবহারিক জীবন কাঠামোয় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সাম্রাজ্যের অবসানে রাষ্ট্র কাঠামোর নানারূপ পরিলক্ষিত হলেও মানব জীবনের সংকট প্রতিনিয়ত উচ্চতর সংঘর্ষে রূপ নিয়েছে। ধর্মের সাথে ধর্মের যে হানাহানি পরিলক্ষিত হয়, সেখানে সম্পদ ও ক্ষমতার একচ্ছত্র আধিপত্যকে চিহ্নিত করে। বিজ্ঞান ঐতিহাসিক উপাদানকে তথা তথ্যকে সংগ্রহ করে বাস্তব জগতের সাথে মূল্যায়ন করে। তত্ববিদ্যা ( ontocological), জ্ঞানশাস্ত্র (epistemological) সহ বহ উদ্ভাবনের পথে মানব বিশ্ব অগ্রসর হয়। আদিতে ধর্মের আচার প্রথায় নতুন উদ্ভাবন জ্ঞানকে প্রগতির পথে পরিচালিত করার অভিপ্রায়। কত সহস্র বছর অতিক্রম হলেও ‘গুরুপূর্ণিমা’ বিশ্বে প্রথম প্রগতির বার্তা বহন করে। এমনকি এই শব্দটির সাথে মহাজাগতিক বিপ্লব সূচিত হয়েছে। প্রকৃতির অভাবনীয় সৌন্দর্যের সাথে জ্ঞানবানকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সাথে জ্ঞানচর্চার দ্বার উদঘাটিত হলো। ফলে গুরুপূর্ণিমাই’ বিশ্বমানবের প্রথম বিজয় দিবস বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।
ঐতিহাসিক উপাদানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে কিছু তাৎপর্য উপস্থাপন করলাম। আষাঢ়ের মহাপূর্ণিমায় যমুনার দ্বীপে কালচে বর্ণের দ্বৈপায়ন তথা ব্যাসবেদের আগমন ঘটে। পিতা পরাশরমুণি, মা সত্যবতী। প্রকৃতির কোন অপূর্ব লগ্নে যে ঋষির আগমন ঘটে আদি ভারতে, তিনি পাশ্চাত্যের কোন অববাহিকা থেকে আসেননি। আদি প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান, যাঁর জন্মস্থান ভারতের যমুনানদীর কোন একটি দ্বীপে। রঙেবর্ণে ভাবনায় তিনি হরপ্পা মোহেনজোদারোর সভ্যতার সাথে আর্যভাবনার মহাসম্মিলন ঘটালেন। সনাতন হিন্দুধর্মের হিন্দুশাস্ত্র ‘ বেদ’ এর ব্যবহারিক বিন্যাসকারি, মহাভারত, মহাপুরাণ, উপপুরাণ, বেদান্ত দর্শনের সংকলক, সম্পাদক, রচয়িতা হিসেবে তিনি পরম পূজনীয়, অতি শ্রদ্ধার মহান আসনে অধিষ্ঠিত। তিনি ভারতের মহান শ্রেষ্ঠ আদিগুরু, তিনি বাঙালির আদিজ্ঞানের জনক, তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত।
খ্রিস্টপূর্বে তাঁর জন্ম বলে নানাতথ্য উপাত্তে স্বীকৃত হয়ে আছে। এমনকি মহামুনি শ্রীগৌতমবুদ্ধের পূর্বে জন্মগ্রহণকারি মহাঋষি ব্যাসদেবের আর্বিভাবের মাধ্যমে ঐতিহাসিক সভ্যতার উন্মেষ সৃষ্টি হয়। জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্স মুলারের মতে, খৃ.পূ ১০০০ শতকের পূর্বে; বাল গঙ্গাধর তিলকের মতে খৃপূ ৬০০০ অব্দে; ইয়াকবির মতে খৃপূ৩০০০ অব্দে। বহুতথ্যের দ্বারা একথা বলা যায়, বৈদিক সভ্যতার আর্বিভাব খৃ.পূ ২৫০০-২০০০ অব্দে।
বেদ, বললেই আদি জ্ঞানভান্ডারকে বোঝায়। যার অর্থ জ্ঞান। ‘বিদ্যতে অনেন ইতি বেদঃ– এর অর্থ –” যে শব্দ রাশি দ্বারা মানব জীবনের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সুখ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাই ‘বেদ’।” (বৈদিক সংকলন- ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার) বেদের বিশাল জ্ঞানভান্ডারে মানব জীবনের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নামক চর্তুবর্গের সন্ধান পাওয়া যায়। পৌরাণিক প্রবাদ তথ্যে ব্যাসদেবের আর্বিভাব দ্বাপরযুগে বলে মনে করা হয়। প্রাচীনকালে বেদের সহস্রশাখাকে তিনি চারটি ভাগে বিভক্ত করেন। এবং তিনি তাঁর চারজন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। ঋগবেদ পৈলকে, যর্জুবেদ বৈশ্যম্পায়ন, সামবেদ জৈমিনিকে, অথর্ববেদ সুমন্তকে শিক্ষা দিয়ে জ্ঞানের শাখাকে মানবের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।
আদি এই জ্ঞানভান্ডারের আলোকের উজ্জ্বল প্রভা যত বেশি ছড়িয়ে যেতে শুরু করে, ততই মানবজ্ঞানের সাথে সভ্যতার অবস্থানকে চিহ্নিত করা যায়। আদিতে বিন্যাসের প্রক্রিয়া, ব্যাখ্যার যে ধারা বহমান, তা সত্যিই বিস্ময়। লক্ষ্য করি, বৈদিক সাহিত্য নামক যে ধারাসমূহ সৃষ্টি হয়েছে তার দুটি ভাগ- ১. কর্মকান্ড: মন্ত্র বা সংহিতা ও ব্রাহ্মণ; ২. জ্ঞানকান্ড: আরণ্যক ও উপনিষদ। এসব ব্যাখ্যা নিয়ে এপর্বে আলোচনা মূল লক্ষ্য নয়।
আলোচনা থেকে আমরা কতিপয় দিক উন্মোচিত হয়ে ওঠে, তা হলো জ্ঞানের পথে মানবকে পরিচালিত করা। দ্বিতীয়ত উপনিষদের সাথে সংসদের প্রথম রূপরেখা পাওয়া যায়। √পরি +√সদ– চারদিকে বসা, যাকে পরিষদ বলা হয়। √সম+√সদ- একত্রে বসে আলোচনা করা। আদিতে গুরুর (√উপ) নিকটে ( নি-√সদ) বসতেন। এই সভার নাম ‘উপনিষদ ‘। সংসদ নামক জনসভাগৃহের ধারণা তখন থেকে সূচিত হয়েছে।
মহর্ষি ব্যাসদেব অল্পবয়সে জ্ঞানান্বেষণের জন্য তপস্যারত হতে গৃহত্যাগী হয়ে বদরিকাশ্রমে যান। দীর্ঘ তপস্যায় ফলে তিনি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত দার্শনিক হিসেবে আবির্ভূত হন। মহর্ষি বেদকে শতশাখাযুক্ত ৪ ভাগে বিভক্ত করেন, তাই তাঁকে বেদব্যাস বলা হয়।
আষাঢ়ি পূর্ণিমায় হিন্দু সন্ন্যাসীরা বেদব্যাসকে শ্রেষ্ঠ গুরু হিসেবে ‘ গুরুগীতা’র স্ত্রোত্র পাঠের মাধ্যমে ব্যাসপূজা করেন। এর রচয়িতা তিনি, এবং গুরুদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা।
মহাভারত’ গ্রন্থের ১০০ পর্ব, ১ লাখ শ্লোকের মাধ্যমে তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বান্দে তিনি রচনা করেন। প্রথমে এর নাম ছিল ‘ জয়’। মহর্ষি তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন সহ অন্যান্য মুনিদের শোনান, তখন নাম হয় ‘ভারত’। মুনি সৌতি ১৮ খণ্ডে কাহিনীকে বিভক্ত করে শৌনক ও অন্যান্য মুনিদের শোনান, তখন থেকে এই গ্রন্থের নাম মহাভারত। যা দুই হাজার খ্রি.পূর্বাব্দে। এই কাহিনী ১২০০-৬০০ খ্রি.পূ. ব্রাহ্মী ও সংস্কৃতে লিখিত হয়।
ভারতের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বেদ। মহাভারতে ব্রহ্মাকে বেদের স্রষ্টা বলা হয়। বেদ আদি ঋষিদের গভীর জ্ঞানের প্রকাশ বলে বিবেচনা করা হয়। বেদকে শ্রুতি সাহিত্য বলা হয়, আর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থকে স্মৃতি সাহিত্য বলা হয়।
বেদের ৪ টি ভাগ, ১. ঋগ্বেদ- সূক্তের সমষ্টি, ২. যজুর্বেদ- প্রার্থনা ও যজ্ঞেরর সূত্রবদ্ধের সমষ্টি, ৩. সামবেদ- স্তবসংগীতের সমষ্টি , ৪. অথর্ববেদ- ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রোচ্চারণ ও অলৌকিক অনুষ্ঠানের নিয়মাবলীর সমষ্টি।
মহাকালের ইতিহাসে তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু বলে বিবেচিত। তাঁর জন্মতিথির পূর্ণিমাকে ‘গুরুপূর্ণিমা’ও বলা হয়ে থাকে। আধুনিক বাঙালি রাজা রামমোহন রায় ‘ বেদান্ত গ্রন্থ ও বেদান্ত সার’ নামক ২ টি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। সেখানে স্রষ্টাকে ‘ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম’ হিসেব বেদের শ্লোক অনুবাদ করে বেদকে সর্বজনের নিকট তুলে ধরেন।
মহর্ষি বেদব্যাস সেই সময় ব্যক্তিগত জীবনে বিধবা বিবাহ করেন। তাঁর পুত্রের নাম শুকদেব। কুরুবংশের রাজা বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হলে তাঁর পত্নীদ্বয়কে বিয়ে করেন। অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়। তাঁদের দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম দেন।
তাঁর জন্মতিথিতে বন্দনা..
গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ|
গুরুরেব পরং ব্রহ্মম তস্মৈ শ্রীগুরুরে নমঃ|
ব্যাসদেবকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার এমন সুন্দর অর্থপূর্ণ দিবস বিশ্বে পাওয়া যায় না। তাঁর মাধ্যমে বিশাল জ্ঞানের বহু শাখা সৃষ্টি হয়। ১. শিক্ষা পদ্ধতি; ২. কর্মবিধান; ৩. ব্যাকরণ বিধি – রক্ষার্থং বেদনামধপয়ং ব্যাকরণমিত্যাদি; ৪. অর্থজ্ঞান ; ৫. সুর ছন্দের বিধি — সাতটি ছন্দ হলো গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী; ৬. জ্যোতিষ বিদ্যা বা কাল নির্ণয়– দিন, মাস, ঋতু, তিথি, নক্ষত্র জ্ঞান; ৭. শ্রুতি পাঠ প্রণালী– ১১টি পাঠ প্রণালী আবিষ্কৃত; ৮. সামাজিক পারিবারিক জীবন পদ্ধতি, বিবাহ, পুজা, পার্বণ ইত্যাদি; ৯. বৈদিক দেব-দেবীর ব্যাখ্যা, বিদ্রোহ অতিলৌকিক ঘটনা; ১০. প্রকৃতির প্রবাহ — ঋতু বৈচিত্র্য ; ১১. চিকিৎসা পদ্ধতি ; ১২. যুদ্ধের নীতি পদ্ধতি ; ১৩. ক্রীড়া নৈপুণ্য ; ১৪. অমোঘ বিধান; ১৫. বিশ্বপ্রকৃতির প্রজনন সৃষ্টি ; ১৬. নৃত্যগীত পরিবেশনা পদ্ধতি ; ১৭. স্থাপত্য শিল্প- চিত্রলিপি, গুহাচিত্র, গৃহ, মন্দির ইত্যাদি; ১৮. খাদ্য ও আহারাদি বিষয়ক; ১৯. পরমাত্মা বিষয়ক জ্ঞান – একমেবাদ্বিতীয়ম
বহুবিধ জ্ঞানের দ্বারা মানব জীবনের আলো প্রজ্জ্বলিত করলেন, তিনিই ঋষির ঋষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। এমনই মহাঋষির পুণ্যতীর্থ আমরা বসবাস করছি। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কোনো ধর্মের গন্ডীতে আবদ্ধ হতে পারে না। তিনি সর্বমানবের বিজয়ের উৎস সৃষ্টি করে গেছেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘অথর্ববেদ’কে জনসংঘের সাথে তুলনা করেছেন। ‘ ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ// ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্যং লক্ষীর্বলং বলে’ ঋব সত্য তপস্যা রাষ্ট্র শ্রম ধর্ম কর্ম ভূত ভবিষ্যত বীর্য বল সমস্তই উচ্ছিষ্টে অর্থাৎ উদ্বৃত্তে আছে।… বিশ্বমামনবমনের ভূমিকায়, যারা একে স্বীকার করে তারাই মনুষ্যত্বের পদবীতে এগোতে থাকে। অথর্ববেদ যে-সমস্ত গুণের কথা বলেছেন তার সমস্তই মানবগুণ।… আমাদের ঋতে সত্যে ধর্মে কর্মে সেই বৃহৎ মানবকে আমরা আত্মবিষয়ীকৃত করি। এই কথাটিই উপনিষদ আর-এক রকম করে বলেছেন,
এষস্যে পরমা গতি রেষাস্য পরমা সম্পদ/ এষোহস্য পরমো লোক এষোহস্য আনন্দঃ।”
এখানে উনি এবং এ, দুয়ের কথা। বলছেন, উনি এর পরম গতি, উনি এর পরম সম্পদ, উনি এর পরম আশ্রয়, উনি এর পরম আনন্দ। অর্থাৎ, এর পরিপূর্ণতা তাঁর মধ্যে। উৎকর্ষের পথে এ চলেছে সেই বৃহতের দিকে, এর ঐশ্বর্য সেইখানেই, এর প্রতিষ্ঠা তাঁর মধ্যেই, এর শাশ্বত ধন যা-কিছু সে তাঁতেই।” (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
বিশ্বে এমন ধারণা যিনি মানববিশ্বে দিয়েছেন, তা যুগান্তকারী থেকেও অধিক বলে মনে করি। মানববিশ্বে আদি দেব দেবীর নানা ঘটনা উপঘটনার মধ্যে মানবের জয় ঘোষণা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। মানববিশ্বে দিয়ে গেছেন জ্ঞানভান্ডারের অমূল্য সম্পদ। প্রাচ্যের সকল গণ্ডী পেরিয়ে বিশ্বে ব্যাপৃত হয়েছে। অবিরাবীর্ম এধি- সৃষ্টির এমন বিরাটরূপ তিনি জগতে প্রকাশ করলেন।
আসুন, আদিতে জমগ্রহণকারী বিশ্বশ্রেষ্ঠ ঋষির সম্মানে গুরুপূর্ণিমা উদযাপনের আদি দার্শনিকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি। বিশ্বজ্ঞানের আদি মহাবিপ্লবের জয়গাথা বিশ্বে সকল জনপদকে জানিয়ে দেই।
“সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যসপজঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। সব্বে সত্তা দুকখোপমুঞ্চন্তু। সবে সত্তা মা যথালব্ধ-সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।”
সকল জীব সুখিত হোক, নিঃশত্রু হোক, অবধ্য হোক, সুখী হয়ে কালহরণ করুক। সকল জীব দুঃখ হতে প্রমুক্ত হোক, সকল জীব যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক।।— সেই সঙ্গে এও বলতে পারি, দুঃখ আসে তো আসুক, মৃত্যু হয়তো হোক, ক্ষতি ঘটে তে ঘটুক— মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক, সমস্ত দেশকালকে ধ্বনিত করে বলতে পারুক—: সেহহম। ( রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
গুরুপূর্ণিমার প্রভাব ইতিহাসে দেখা যায় এবং মহামুণিরা কিভাবে অনুসরণ করেছেন দেখা যেতে পারে।
বৌদ্ধ ধর্ম:
মহামুণি বিশ্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক গৌতম বুদ্ধ ২৯ বছর বয়সে আষাঢ়ের পূর্ণিমায় গৃহত্যাগ করেন। ছয় বছর তপস্যার পর মহাবোধি প্রাপ্ত হন। তার একমাস পর এই পূর্ণিমা তিথিতে সারানাথে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যকে প্রথম ‘ধম্ম-চক্কপবত্তন সুক্ত’ ( ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র) উপদেশ দেন। এই শিষ্যরা হলেন- কৌণ্ডিণ্য, বপ্প, ভদ্দীয়, মহানাম, অশ্বজিত।
এই আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা কঠোর সংযম ও সাধনা করে থাকেন। ( এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করব)।
হিন্দু পুরাণ:
আদিযোগী শিব, আদি গুরু এই তিথিতে সপ্তর্ষির সাত জন ঋষিকে মহাজ্ঞান দান করেন। ঋষিরা হলেন- অত্রি, বশিষ্ঠ, পুলহ, অঙ্গীরা, পুলস্থ্য, মরীচি, ক্রতু। বৈদিক যুগ থেকে এই তিথি গুরু- শিষ্যের পরম্পরা হিসেবে পরিগণিত।
জৈন ধর্ম|:
আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে ‘চার্তুমাস’ কঠোর সংযম সাধনার মাস জৈনরা পালন করে থাকেন। মহামুণি মহাবীর গান্ধারের গৌতম স্বামীকে প্রধান শিষ্য হিসেবে এই গুরুপূর্ণিমায় দীক্ষা দেন।
বঙ্গশ্চ তথা বঙ্গ’ ভাবনার জনক বেদব্যাস:
বেদব্যাস মনে করেন, ব্রহ্মই আদিগুরু। স্রষ্টা সর্বপ্রথম সৃষ্টিতে আষাঢ়ি পূর্ণিমায় গুরুরূপে আর্বিভূত হয়েছিলেন।
আজ প্রকৃতির মিলনসেতু চন্দ্রগ্রহণ হবে। সবমিলিয়ে বেদব্যাসের জন্মতিথি, জ্ঞানসাধকের প্রতি যুগ যুগ ধরে পরম পূজনীয় দিন হিসেবে পালিত হবে।
বাঙালির রঙেবর্ণে ভাবনায় বেদব্যাসই ঐতিহ্য, তিনি বাঙালির ‘বঙ্গ’ শব্দটি তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।
“বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চের পাদাঃ” পদটি ঐতরেয় আরণ্যকে পাওয়া যায়। মহাভারতের আদিপর্বে বঙ্গজনপদের উল্লেখ করা হয়েছে, যা ছিল স্বতন্ত্র দেশ। এইসব তথ্য উপাত্তের সাথে পরবর্তীকালে ‘ প্রজ্ঞাপনা’ নামক জৈন উপাঙ্গে বঙ্গজনদের আর্য বলা হয়েছে। বৌদ্ধদের পালিগ্রন্থ মনোরথপুরণি ও অপদানে ‘ বঙ্গান্তপুত্ত’ ও ‘ বঙ্গীশ’ শব্দ পাওয়া যায়।
এনিয়ে সত্যিকার গবেষণা ও পুর্নপাঠ বিবেচনা প্রয়োজন বলে মনে করি । তাহলে প্রচলিত ইতিহাসের জড়ত্ব দূরীভূত হবে।
বঙ্গশ্চ বললে আদি প্রাচ্যতট/ প্রাচ্যের ভৌগোলিক বিশাল ভূবিশ্বকে বোঝায়। আদিতে এই ভূঅঞ্চলে বঙ্গ জনপদ ছিল জ্ঞান শিক্ষা সাধনায় অগ্রসর একটি বৃহৎ জনপদ। আদিগুরু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবই জ্ঞানের মহাদ্বার উদঘাটন করে আদি জ্ঞানের মহাপথিকৃত হয়ে আছেন। তিনি যা করে গেছেন, যা দিয়ে গেছেন তা সকল কালকে অতিক্রম করে প্রতিনিয়ত আবশ্যিকতাকে অবহিত করছে।
আধুনিক প্রাচ্যের জনক রাজা রামমোহন রায়, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকল ব্যাখ্যা তথ্যদিয়ে বিষয়ের উপর গভীর মতামত উপস্থাপন করে গেছেন।
বাঙালিদের গবেষণায় অধিক মনোযোগী হতে হবে, তাহলে বিশ্বের সম্ভাবনাময় ঐতিহ্য আবিষ্কৃত হবে।
গুরুপূর্ণিমা’র পরম শ্রদ্ধাজানাই আদি দার্শনিক দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে। একইসাথে আদি তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাজ্ঞানীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি। বিশ্বের সকল ধর্মপ্রণেতা দার্শনিক চিন্তকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অপূর্ব দিবসটি সকলের হয়ে উঠুক, সর্বনানবের হয়ে উঠুক। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন…
“আলোকেরই মতো মানুষের চৈতন্য মহাবিকিরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে। সেই প্রসারণের দিকে দেখি তার মহৎকে, দেখি মহামানবকে, দেখি যশ্চয়মশ্মিন্ আত্মনি তেজোময়োমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ…”
গুরুপূর্ণিমা’কে সর্বমানবের জয়ধ্বনিতে উচ্চারিত হলে মানব বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা পাবে। বিশ্বে জ্ঞান প্রগতির প্রথম মহাবিপ্লব ‘গুরুপূর্ণিমা’ পুণ্যতিথি ‘জ্ঞানে কর্মে প্রেমে উপলব্ধি করিতে পারি যে, তুমি শান্তনং শিবম্ অদ্বৈতম।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ
মহাঋষি জ্ঞানদ্রষ্টা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবে জন্মতিথিতে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলির অর্ঘ্য অর্পণ করি।
তথ্যনির্দেশ:
১. ধর্ম-দর্শন, ভাষান্তর: সুশীল কুমার চক্রবর্তী। মূলগ্রন্থ” The Philosophy of Religion: Dr. Miali Edward. দ্বিতীয় প্রকাশ জানুআরি ১৯৮৯, পশ্চিমবঙ্গ রাজয় পুস্তক পর্ষদ,কলিকাতা-৭০০০১৩।
২. বৈদিক সংকলন: ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৩. মানুষের ধর্ম: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবন্ধ সমগ্র, আগস্ট ২০০০, সময় প্রকাশন, ঢাকা;
৪. উপনিষদ গ্রন্থাবলী: স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, তৃতীয় পুর্নমুদ্রণ, আগস্ট ২০২০;
৫. বেদান্তসার, বেদান্তগ্রন্থ, তলবকার উপনিষৎ, কঠোপনিষৎ, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, মুণ্ডুকোপনিষৎ;
রামমোহন রচনাবলী, সম্পাদক: প্রসাদরঞ্জন রায়, রামমোহন মিশন, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৫
৬. শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা যথাযথ, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮২
৭. The World Past & Present, Holt, Rinehart and Winston Inc; Orlando-.. Printed by United States of America, 1988
৮. ভারতীয় দর্শন, প্রথম খন্ড, প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত
ব্যানার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা,এপ্রিল ১৯৭১
১০. কবীন্দ্র মহাভারত, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় খন্ড
কল্পনা ভৌমিক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৯
১১. Buddhism- Message of Peace, edited by Renuka Singh, Foundation of SAARC Writers & Literature, New Delhi, 1977;
১২. বাঙালির দর্শন, ড. আমিনুল ইসলাম, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪;
১৩. পৌরাণিক অভিধান, সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত, এম.সি সরকার আ্যান্ড সন্স প্রা. লি. কলকাতা, আশ্বিন ১৪০৬;
১৪. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ (আষাঢ় ১৪২০), অক্ষয় কুমার দত্ত করুণা প্রকাশনী, কলকাতা
১৫. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, দ্বেজ পাবলিশিং, কলকাতা, মাঘ ১৪১৪;
১৬. ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো,১৯৮৯;
১৭. Early India, Romila Thapar, Penguin Books 2015;
১৮. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, প্রথম খন্ড,দ্বিতীয় খন্ড, সুনীল চট্র্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জানুয়ারি ২০১৮