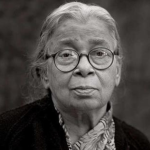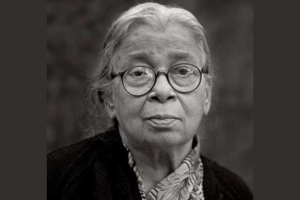একটু বাংলার ইতিহাস দেখা যাক। ১২০৪ খ্রিঃ-১৭৫৭ খ্রিঃ পর্যন্ত বাংলায় মুসলমান শাসন ছিল- যে সময় বাংলায় মধ্যযুগের শুরু। মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের ফলে বঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু পরিবর্তন আসেনি। এর ফলে বঙ্গের সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য, শিল্পকলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ দেশবাসীর জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল।
বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা করেছিলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি। তেরো শতকের শুরুতে তুর্কী বীর ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলমান শাসনের সূচনা করেন। তিনি আফগানিস্তানের গরমশির বা আধুনিক দশত-ই-মার্গের অধিবাসী। ইতিহাসে তিনি বখতিয়ার খলজি নামেই বেশি পরিচিত। তাঁর বংশ পরিচয় সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কি, বংশে খলজি এবং বৃত্তিতে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক।
তখন দুপুর। রাজা লক্ষ্মণ সেন মধ্যাহ্নভোজে ব্যস্ত; প্রাসাদ-রক্ষীরা তখন আরাম আয়েস করছে; নাগরিকগণও নিজেদের প্রাত্যহিক কাজে ব্যস্ত। বখতিয়ার খলজি বণিকের ছদ্মবেশে নগরীর দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছান।রাজা লক্ষ্মণ সেন তাদেরকে অশ্ব ব্যবসায়ী মনে করে নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেন। কিন্তু এ ক্ষুদ্রদল রাজপ্রাসাদের সম্মুখে এসে হঠাৎ তরবারি উন্মুক্ত করে প্রাসাদ রক্ষীদের হত্যা করে। অকস্মাৎ এ আক্রমণে চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়। প্রাসাদ অরক্ষিত রেখে সকলে প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। ইতিমধ্যে বখতিয়ারের দ্বিতীয় দল নগরের মধ্যে এবং তৃতীয় দল তোরণ- দ্বারে এসে উপসি’ত হয়। সমস্ত নগরী তখন প্রায় অবরুদ্ধ। নাগরিকগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত।এ অবস্থায় রাজা লক্ষ্মণ সেন হতাশ হয়ে পড়েন। শত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার কোনো উপায় নাই দেখে তিনি পিছনের দরজা দিয়ে সপরিবারে খালি পায়ে গোপনে নৌকাযোগে পূর্ববঙ্গে মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অল্পকালের মধ্যে বখতিয়ারের পশ্চাৎগামী অবশিষ্ট সৈন্যদলও এসে উপসি’ত হলো।বিনা বাধায় নদিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে আসে।বখতিয়ার খলজির নদিয়া জয়ের সঠিক তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে বর্তমানে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দই নদিয়া জয়ের তারিখ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
এ শাসন প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছরের বেশি স্হায়ী হয়েছিল (১২০১-১৭৫৭ খ্রি:)।রাজ্য জয় করেই বখতিয়ার খলজি ক্ষান্ত ছিলেন না। বিজিত অঞ্চলে তাঁর শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যও তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সংস্কৃতি বিকাশের জন্য তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁর সময় বহু মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল।
আরও পড়ুন: গ্রাম সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ২
অন্যদিকে সুলতান ইলতুৎমিশের আমলেও মধ্য এশিয়া থেকে বহু মুসলিম সুফি ও সৈয়দ তাঁর দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এ সময়- সুফি ও সুধীগণ বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেন। পরে ইওজ খলজির পৃষ্ঠপোষকতায় লখনৌতি মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়।
১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে দেখা গেল, সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের মৃত্যু হয়। বাহরাম খানের বর্মরক্ষক ছিলেন ‘ফখরা’ নামের রাজকর্মচারী। প্রভুর মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ‘ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ’ নাম নিয়ে সোনারগাঁওয়ের ফখরুদ্দিন নিজ নামে মুদ্রা জারি করেছিলেন। তাঁর মুদ্রায় খোদিত তারিখ দেখে ধারণা করা যায়, তিনি ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন- সোনারগাঁও রাজত্ব করেন। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ তাঁর রাজ্যসীমা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিছুটা বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জয় করেন। এবং চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি রাজপথ ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ তৈরি করেছিলেন বলে জানা যায়। ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁও টাঁকশাল থেকে ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহ নামাঙ্কিত মুদ্রা জারি করা হয়।গাজী শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রায় ১৩৫২ খিস্টাব্দ পর্যন-তারিখ পাওয়া যায়।
এর পরবর্তীতে ইলিয়াস শাহ লখনৌতির শাসক হিসেবে বঙ্গ অধিকার করলেও তিনি দুই ভূখণ্ডকে একত্রিত করে বৃহত্তর বাংলার সৃষ্টি করেছিলেন। এ সময় থেকেই বাংলার সকল অঞ্চলের অধিবাসী ‘বাঙালি’ বলে পরিচিত হয়। ইলিয়াস শাহ ‘শাহ-ই বাঙ্গালা’ ও ‘শাহ-ই-বাঙালি’ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।
ইলিয়াস শাহ যে স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর সিকান্দার শাহ সেভাবেই একে আরও শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করতে সক্ষম হন। সুলতান সিকান্দার শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন ‘আজম শাহ’(১৩৯৩-১৪১১ খ্রি:) উপাধি গ্রহণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ একজন ন্যায়বিচারক ছিলেন।রিয়াজ-উস-সালাতীন গ্রন্থে তাঁর ন্যায় বিচারের উজ্জ্বল কাহিনি বর্ণিত আছে। সুপণ্ডিত হিসেবে সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। কবি-সাহিত্যিকগণকে তিনি সমাদর ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কাব্য রসিক ছিলেন এবং নিজেও ফার্সি ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। পারস্যের প্রখ্যাত কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হতো।
মুসলমান শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ বঙ্গের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন।তাঁর রাজত্বাকালেই প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীর ‘ইউছুফ-জুলেখা’ কাব্য রচনা করেন। আজম শাহের রাজত্বকালেই বিখ্যাত সুফী সাধক নূর কুতুব-উল-আলম পান্ডুয়ায় আস্তানা গাড়েন। এই স্থান হতেই তিনি বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম ধর্মের প্রচার করে বেড়াতেন। ফলে পান্ডুয়া ইসলাম শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে ভারতবর্ষে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। ধর্মনিষ্ঠ সুলতানের থেকে তিনি সর্বপ্রকার সাহায্য লাভ করেছিলেন।সুলতান মক্কা ও মদিনাতেও মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণের জন্য অর্থ ব্যয় করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ ছিলেন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম এবং ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতান। তাঁর মৃত্যুর পর হতেই এ বংশের পতন শুরু হয়।
এরপর বাংলাতে হাবসি অরাজকতার সময় কেটেছিল কিছুদিন। তারপর আলাউদ্দিন হুসেন শাহ রাজ্যের কল্যাণের লক্ষে বঙ্গের রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে হাবসীদের প্রভাবমুক্ত করতে যেমন সচেষ্ট ছিলেন, তেমিন রাজধানী পরিবর্তন করে শাসন ব্যবস্থা দৃঢ় করেন। গৌড় রাজ্যের নিকটবর্তী এক জায়গায় তিনি রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন।বঙ্গের সুলতানদের মধ্যে একমাত্র তিনিই পাণ্ডু য়া বা গৌড় ব্যতীত অন্যত্র রাজধানী স্থাপন করেন। হাবসি শাসনকালে গোলযোগ সৃষ্টিকারী আমীর-ওমরাহদের কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়। নীচ বংশজাত অত্যাচারী সকল কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়।তার পরিবর্তে তিনি শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ পদে সৈয়দ, মোঙ্গল, আফগান, হিন্দুদেরকে নিযুক্ত করেন। এ সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে।
আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সময় বাংলার রাজ্যসীমা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। তিনি কামরূপ ও কামতা জয় করেন। উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশও তাঁর করায়ত্ত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশও তাঁর অধিকারে আসে।
তিনি আরাকানীদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন। শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি যথেষ্ট উদ্যম, নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। শাসনকার্য পরিচালনায় ও প্রজাপালনের ক্ষেত্রে তিনি জাতি ও ধর্মের কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেননি।হিন্দু ও মুসলমান-উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের দ্বারা একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা তাঁর লক্ষ্য ছিল। এজন্য একজন গোঁড়া সুন্নি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন হিন্দুকে যোগ্যতা অনুসারে শাসনকার্যে নিয়োগ করেছিলেন। হিন্দুদিগকে উৎসাহিত করার জন্য তিনি তাদেরকে বিভিন্ন উপাধিও প্রদান করতেন। হিন্দুদের প্রতি হুসাইন শাহের এ উদারতা সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য নির্বাহের চিত্র: শ্রীচৈতন্যক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং বাঙালিদের নিজস্ব ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। ইহা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও পরিচয় বহন করে। হুসেন শাহের এ ধর্মীয় উদারতা তাঁর উত্তরাধিকারীদেরও উৎসাহিত করেছিল। তাঁর শান্তিপূর্ণ রাজত্বকালে প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করত।
হুসেন শাহের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনের প্রচেষ্টা তৎকালীন সমাজ-জীবনকেও প্রভাবিত করেছিল।তাঁর শাসনকালেই আবির্ভাব ঘটে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যের। হুসেন শাহ তাঁর প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন এবং তাঁকে ধর্ম প্রচারে সব রকমের সহায়তা করার জন্য কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ দেন। সত্যপীরের আরাধনা হুসেন শাহের শাসনকালের আর একটি উলে- যোগ্য ঘটনা। সত্যপীরের আরাধনা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেএকটি উজ্জ্বল প্রচেষ্টা।
বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশ হুসেন শাহের শাসনকালকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে।হুসেন শাহ যোগ্য কবি ও সাহিত্যিকগণকে উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার প্রদান করতেন।এ যুগের প্রখ্যাত কবি ও লেখকদের মধ্যে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, মালাধর বসু, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস,পরাগল খান ও যশোরাজ খান উল্লেখযোগ্য ছিলেন। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা অসংখ্যখ গ্রন’ রচনা করেন। তাঁদের নিরলস সাহিত্য-কীর্তি বাংলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। এ সময়ে মালাধর বসু ‘শ্রীমদ্ভাগবৎ’ ও ‘পুরাণ’ এবং পরমেশ্বর ‘মহাভারত’ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। আলাউদ্দীন হুসেন শাহ আরবী ও ফার্সী ভাষারও উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।
হুসেন শাহ একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। নিজ ধর্ম ও সুফী সাধকদের প্রতি তাঁর অপরিসীম নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল। তাঁর রাজত্বকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।এ সমস্ত মসজিদের মধ্যে গৌড়ের ‘ছোট সোনা মসজিদ’ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।রাজ্যে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশের জন্য অনেক খানকাহ্ ও মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছিল। পাণ্ডুয়ার মুসলমান সাধক কুতুব-উল-আলমের সমাধি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হুসেন শাহ প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। হুসেন শাহ্ গৌড়ে একটি দুর্গ ও তোরণ, মালদহে একটি বিদ্যালয় ও একটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন। এইসব মসজিদ, মাদ্রাসা, দুর্গ, তোরণ হুসেন শাহের স্থাপত্য প্রীতির পরিচয় বহন করে। তাঁর ২৬ বছরের শাসনকালে বঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অভাবিত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এজন্য তাঁর শাসনকালকে বঙ্গের মুসলমান শাসনের ইতিহাসে ‘স্বর্ণযুগ’ বলা হয়।
বার ভূঁইয়াদের ইতিহাস খুব একটা প্রীতিকর নয়। দিল্লিতে মোগল আধিপত্য বিস্তারের পরেও বাংলার রাজারা বাংলাকে কেন্দ্রের অধীনে সমর্পণ করেননি অধিকাংশ ক্ষেত্রে। রানি দুর্গাবতী এ সময়কার এক বিরলতম মহিলা,যিনি নিজ রাজ্যের মধ্যে কেন্দ্রকে প্রতিহত করতে আমৃত্যু লড়াই করেছেন। অন্যদিকে রাজা গণেশ ও কতিপয় ভূঁইয়াদের বাদ দিলে বাংলাতে ছিল মুসলমানদের শাসন।
আরও পড়ুন: আমার দেখায় বাংলাদেশের মানমন্দির
সম্রাট আকবর সমগ্র বাংলার উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি।বাংলার বড় বড় জমিদাররা মুঘলদের অধীনতা মেনে নেননি। জমিদারগণ তাঁদের নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন।এদের শক্তিশালী সৈন্য ও নৌ-বহর ছিল। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এঁরা একজোট হয়ে মুঘল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বাংলার ইতিহাসে এ জমিদারগণ ‘বার ভূঁইয়া’ নামে পরিচিত। এ ‘বার’ বলতে বারজনের সংখ্যা বুঝায় না। ধারণা করা হয় অনির্দিষ্ট সংখ্যক জমিদারদের বোঝাতেই ‘বার’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।
বাংলার ইতিহাসে বার ভূঁইয়াদের আবির্ভাব ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তীকাল হতে সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে।মুঘলদের বিরুদ্ধে যাঁরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাঁরাই ‘বার ভূঁইয়া’।এছাড়াও বঙ্গদেশে আরও অনেক ছোটখাট জমিদার ছিলেন।তাঁরাও মুঘলদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ান। কিন্ত্ত পরে এঁরা মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। বার ভূঁইয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:
ঈসা খান, মুসা খান( অধিকারী ছিলেন : ঢাকা জেলার অর্ধাংশ, প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা এবং পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলার কিছু অংশ)
চাঁদ রায় ও কেদার রায়(শ্রীপুর, বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ)বাহাদুর গাজীভাওয়ালসোনা গাজীসরাইল(ত্রিপুরার উত্তর সীমায়)ওসমান খানবোকাইনগর(সিলেট)বীর হামিরবিষ্ণুপুর (বাকুড়া)লক্ষ্মণ মাণিক্যভুলুয়া(নোয়াখালি) পরমানন্দ রায়চন্দ্রদ্বীপ(বরিশাল)বিনোদ রায়, মধু রায়চান্দপ্রতাপ(মানিকগঞ্জ)মুকুন্দরাম, সত্রজিৎভূষণা(ফরিদপুর)।
শায়েস্তা খান তাঁর শাসন আমলের বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলীর জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁর সময়ে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য সরাইখানা, রাস্তা ও সেতু নির্মিত হয়েছিল। দেশের অর্থনীতি ও কৃষি ক্ষেত্রে তিনি অভাবিত সমৃদ্ধি আনয়ন করেছিলেন। জনকল্যাণকর শাসনকার্যের জন্য শুধু বাংলায় নহে, সমগ্র ভারতবর্ষেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সময়ে দ্রব্য মূল্য এত সস্তা ছিল যে, টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যেত।
শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। এ আমলে কৃষি কাজের সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। শায়েস্তা খান ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশি বণিকদিগকে উৎসাহিত করতেন।
চলবে…