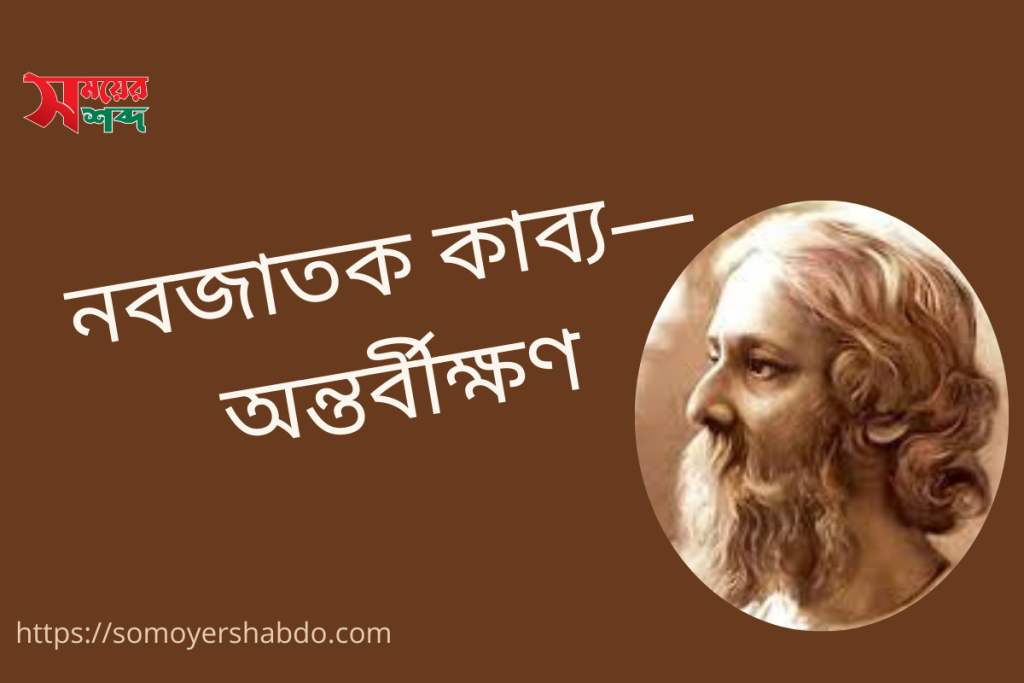রবিজীবনের গোধূলি পর্যায়ে প্রকাশিত হয় ‘নবজাতক’ কাব্য। ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। এবং এই কাব্যে সর্বমোট পয়ত্রিশটি কবিতা রয়েছে। তারমধ্যে ছাব্বিশটি কবিতা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নবজাতকের সূচনায় কবি বলেছেন যে তাঁর “কাব্যের ঋতুপরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায় সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে।… কাব্যে এই যে হাওয়াবদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক” একথা কবি জ্ঞাতসারে মনে করলেও কবি অনুরাগী অমিয় চক্রবর্তীকে বলেছেন—অমিয়চন্দ্র “হয়তো দেখেছিলেন, এরা বসন্তের ফুল নয়; এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে তেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তা হলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা।” কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিকছেন(৩১ মার্চ ১৯৪০), “আমার মুশকিল, আমার দেহ ক্লান্ত, তার চেয়ে ক্লান্ত আমার মন; কেননা মন স্থাণু হয়ে আছে, চলাফেরা বন্ধ—তুমি থাকলে মনের মধ্যে স্রোতের ধারা বয়—তার প্রয়োজন যে কত তা আশেপাশের লোকে বুঝতে পারে না।”
কাব্যের প্রথম কবিতাটি সাময়িকপত্রে প্রথম ছাপা হয় ১৩৪৫ সালের কার্তিকমাসে ‘নবজাতক’ নাম্নী কবতাটি ছাপা হয় পাঠশালা পত্রিকায়। নবজাতক কবিতাটি আশীর্বাদ হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন কবি হেমন্তবালা দেবীর দৌহিত্র কিশোরকান্ত বাগচীকে। প্রথমে কবিতাটির শেষ ছত্র ছিল—
‘নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো এই বুঝি দিল আনি’
পরে এই ছত্রের পরিবর্তন করেন। কবি কাব্যে প্রকাশের সময় লেখেন—
‘নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো বুঝি বা দিতেছে আনি’
‘উদ্বোধন’ কবিতাটি ছাপা হয় শতদল পত্রিকায়, ‘কষ্টিপাথর’ নামে ওই কবিতাটিই প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৪৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। ‘প্রায়শ্চিত্ত’ কবিতাটি প্রবাসী পত্রিকায় ছাপা হয় ১৩৪৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ‘বুদ্ধভক্তি’ কবিতাটি পরিচয় পত্রিকাতে ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন মাসে ছাপা হয়। ‘কেন’ নামের কবিতাটি প্রবাসী পত্রিকাতে ছাপা হয় ১৩৪৫ সালের চৈত্র মাসে। ‘হিন্দুস্থান’ কবিতাটি প্রবাসী পত্রিকায় ছাপা হয় ১৩৪৪ সালের পৌষ মাসের সংখ্যাতে। ‘রাজপুতানা’ কবিতাটি গ্রন্থে প্রকাশের পূর্বে প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৪৫ সালের মাঘ মাসের সংখ্যাতে ছাপা হয়। ‘ভাগ্যরাজ্য’ কবিতাটি পরিচয় পত্রিকায় ১৩৪৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যাতে মুদ্রিত হয়। ‘ভূমিকল্প’ নামের কবিতাটি নাচঘর পত্রিকায় ১৩৪৪ সালের ৩০ চৈত্রতে ছাপা হয়ে বেরোয়। ‘পক্ষী মানব’ কবিতাটি প্রকাশ পায় বিচিত্রা পত্রিকায় ১৩৩৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। ‘রাতের গাড়ি’ নামক কবিতাটি জয়শ্রী পত্রিকাতে ১৩৪৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশ পায়। এর পরের কবিতাটি ১৩৪৫ সালে প্রবাসী পত্রিকাতে শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়; কবিতাটির নাম ‘মৌলানা জিয়াউদ্দীন’ ১৩৪৬ সালের শ্রাবণ মাসের প্রবাসী ‘এপারে-ওপারে’ নামের কবিতাটি মুদ্রিত হয়। ‘মংপু পাহাড়ে’ কবিতাটি পরিচয় পত্রিকাতে ১৩৪৫ সালের শ্রাবণ মাসে ছাপা হয়েছিল। পরে কবিতাটি কাব্যে স্থান পায়। ‘ইসটেশন’ নামের কবিতাটি কবিতা পত্রিকাতে ১৩৪৫ সালেরই আশ্বিন মাসে ছাপা হয়। ১৩৪৭ সালের বৈশাখ সংখ্যার প্রবাসীতে ছাপা হয় ‘জবাবদিহি’ নামের কবিতাটি। ‘প্রবাসী’ নামের কবিতাটি ছাপা হয় ‘জন্মদিন’ নামে প্রবাসী পত্রিকায় (?) ১৩৪৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। ‘জন্মদিন’ কবিতাটি প্রবাসী পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ১৩৪৬ সালের আষাঢ় মাসে। ১৩৪৬ সালের পৌষ সংখ্যায় কবিতা পত্রিকাতে রোমান্টিক কবিতাটি মুদ্রিত হয়। ‘ক্যাণ্ডীয় নাচ’ প্রবাসী পত্রিকাতে ১৩৪৪ সালের শ্রাবণ মাসে ছাপা হয়। তারপরের কবিতা ‘অবর্জিত’ প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৪২ সালে শ্রাবণ মাসে প্রকাশ পায়। কবিতা পত্রিকায় ‘শেষ হিসাব’ নামের কবিতাটি ছাপা হয় ১৩৪৬ সালের আশ্বিন মাসে। ‘জয়ধ্বনি’ কবিতাটি প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৪৬ সালের পৌষ সংখ্যাতে মুদ্রিত হয়। আবার কাব্যের পরবর্তীর কবিতা ‘প্রজাপতি’ কবিতাটি ১৩৪৬ সালের বৈশাখ মাসেই প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৪৫ সালের পৌষ মাসে প্রবাসী পত্রিকায় ‘প্রবীণ’ নামের কবিতাটি ছাপা হয়। প্রবাসী পত্রিকাতে ১৩৪৬ সালের মাঘ মাসে ছাপা হয়েছিল ‘রাত্রি’ নামের কবিতাটি। ‘নবজাতক’ কাব্যের মোট পঁয়ত্রিশটি কবিতার মধ্যে ছাব্বিশটি কবিতাই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। ১৩৪০ সালের চৈত্র মাসে প্রকাশিত নাচঘর পত্রিকা থেকে ১৩৪৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত জয়শ্রী পত্রিকায় এই সাত বছরে মোট ছাব্বিশটি কবিতা প্রকাশিত হয় আটটি সাময়িক পত্রে, পরে ১৩৪৭ সালে আরো নয়টি কবিতা সংযোজিত করে মূল ‘নবজাতক’ কাব্য প্রকাশিত হয়। পাণ্ডুলিপি নির্ভর পাঠভেদের তুলনামূলক আলোচনাতে প্রবেশের আগে কবি স্বয়ং তাঁর নিজের কাব্য ‘নবজাতক’ সম্পর্কে কী বলেছেন তা দেখা যাক তিনি এই কাব্যের প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের উদয়ন বাড়িতে বসে ১৯৪০ সালের ৪ এপ্রিল লিখেছেন—
‘আমার কাব্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু-জোগান নতুন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চারদিকের হাওয়ায়। যারা ভোগ করে এই মধু তারা এই বিশিষ্টতা টের পায় স্বাদে। কোনো কোনো বনের মধু বিগলিত তার মাধুর্যে, তার রঙ হয় রাঙা; কোনো পাহাড়ি মধু দেখি ঘন, আর তাতে রঙের আবেদন নেই, সে শুভ্র; আবার কোনো আরণ্য সঞ্চয়ে একটু তিক্ত স্বাদেরও আভাস থাকে।’ অনন্ত কালের প্রবাহে জীবনের প্রবাহেরও বারংবার ঋতু পরিবর্তিত হয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সৌন্দর্যানুভূতির রূপান্তর ঘটে। ফুল মধুর উৎস, ফলের সম্ভাবনা। সেখানেই তাই মৌমাছি আকৃষ্ট হয়। তারপর ফুলের অনুপস্থিতিতে অন্য স্থানের ফুলের প্রতি মধু ধাবিত হয় ঠিক অনন্ত সৌন্দর্যপিয়াসী মানুষ যেমন রসের সাগরে ভেসে পাড়ি দিয়ে চায় জীবনের সংসার। অন্তিমপর্বে কবির মানস অভিযাত্রাতে অপরূপ মাধুর্যপূর্ণ সৌন্দর্যের সরণিতে সামান্য তিক্ততার অভিব্যক্তিকে সাদরে গ্রহণ করে নেন। তিনি এই মানসযাত্রায় কাল্পনিক কোনো নভোচারী নন, বরং প্রাজ্ঞ ঋষি যইনি জীবনবোধ ও চর্যায় সমৃদ্ধ এবং অগ্নিদহিত এক পবিত্র কাঞ্চনের নির্ভীক বলিষ্ঠ যুব ঋষি। নবজাতক কাব্যটি পড়তে পড়তে প্রকৃতির অপরূপ লাবণ্য এবং অপার্থিব মাধুর্য উপলব্ধি করা যায়। তাই এই কাব্য রচনার সমকালে একটি অসামান্য গান কবি লেখেন গানটি এখানে প্রাসঙ্গিক। গানটি এখানে দেওয়া হল—
আমি শ্রাবণ-আকাশে দিয়েছি পাতি
মম জল-ছলো-ছলো আঁখি মেঘে মেঘে।
বিরহদিগন্ত পারায়ে সারা রাতি অনিমেষে আছে জেগে।।
যে গিয়েছে দেখার বাহিরে আছে তারি উদ্দেশে চাহি রে,
স্বপ্নে উড়িছে তারি কেশরাশি পুরবপবনবেগে।।
শ্যামল তমালবনে
যে পথে সে চলে গিয়েছিল বিদায়গোধূলি-খনে
বেদনা জড়ায়ে আছে তারি ঘাসে, কাঁপে নিশ্বাসে—
সেই বারে বারে ফিরে ফিরে চাওয়া ছায়ায় রয়েছে লেগে।।
পরিণত মনের সুসংহত, সংযত আবেগ বর্ষামঙ্গলের গানটিতে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। নবজাতক কাব্যের ‘প্রবীণ’ কবিতাটি প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৫ এই কাব্যেরই শেষ কবিতা ‘রাত্রি’ প্রকাশ পেয়েছে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ৪৩৫ পৃষ্ঠায়। নবজাতক কবিতাটি শ্রীমান কিশোরকান্ত বাগচীর উদ্দেশে লেখা। কবিতাটি কবি শান্তিনিকেতনে থাকার সময়ে লিখেছেন এখানে উল্লেখ্য যে কাব্যটি কবির জীবনের অন্তিম পর্বের লেখা। এ সময় কবির শরীর ও মন অসুস্থ। সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কবিকে বিমর্ষ করে তুলেছিল। তাই তিনি এই কাব্যের প্রায় প্রতিটি কবিতার মধ্যেই আগামী প্রজন্মের মধ্যে আশার আলো দেখতে পান। কাব্যের প্রথম কবিতায় কবি লিখেছেন—
মানবের শিশু বারে বারে আনে
চির আশ্বাসবাণী
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো
বুঝি-বা দিতেছে আনি।
মানব সভ্যতার গোড়া থেকেই সহজ সত্য সংবেদনশীল সহানুভূতিপূর্ণ মানুষ উপলব্ধি করে এসেছে যে এবং বিশ্বাস করেছে যে শিশুরাই সত্যের সন্ধান, সুন্দরের প্রতীক, তাদের সারল্যের মধ্যে থাকে না কোনো কৃত্রিমতা, তাই চিরকাল গুণীজনেরা, মহৎ হৃদয়ের অধিকারীরা শিশুদের মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে। শিশুদের কল্যাণে প্রকৃত মানুষ ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে তাদের প্রতি যত্নবান হতে চেষ্টা করেছে। তাদের যাতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তাই শিশুদের প্রতি অধিক মনোযোগী; সমাজ সংসারে নারীর ভূমিকা চিরকাল অনপেক্ষণীয়। কারণ শিশুকে তারা প্রথম কোলে তুলে নিয়ে সুর করে করে প্রচলিত গান গেয়ে শুনিয়ে তার ধমনীতে চেতনার সঞ্চার করে দেয়। সেই চেতনাতেই শিশু পরিণত হলে বুঝতে পারে সে মানব সন্তান। তার ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই কর্তব্য। তাই সে এই মহাবিশ্বের অপরূপ রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করে; জানতে চায় অজানাকে। অজানাকে জানতে গিয়েই নিজের অজান্তে আবিষ্কার করে ফেলে জাগতিক নানা সত্যকে রহস্যকে। প্রতিটি সকালই নতুন। নতুন সকাল মানুষকে মুক্তির আলো এনে দেয়। সামনে প্রসারিত পথ এগিয়ে যেতে প্রেরণা যোগায়। শিশুমনের কল্পনাতে গূঢ় রহস্যের অন্তর্জাল ভেদ করতে চায়। কবি একটি গানে সেকথা প্রাঞ্জলভাবে উল্লেখ করেছেন—
অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে,
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে।
বিস্মৃত জন্মের ছায়ালোকে
হারিয়ে যাওয়া বাণীর শোকে
কেঁদে ফেরে পথহারা রাগিণী
কোন বসন্তের মিলনরাতে তারার পানে
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে॥
সকালের মুক্তির আলো বসন্তেরই দ্যোতনা। যা কেবল শিশুরা এনে দিতে পারে। অস্ত্রের বিনিময়ে নয়, ষড়যন্ত্রের শিকার বা জালবুনে নয়, কেবল স্নিগ্ধ হৃদ্যতার মাধ্যমে উদ্বোধন কবিতাটি কাব্যের দ্বিতীয় কবিতা। কবিতাটি কালিম্পং-এ থাকাকালীন লেখা। রচনার কাল হিসাবে উদ্বোধন কবিতাটি কাব্যের দ্বিতীয় কবিতা। সর্বপ্রথম একটি সাময়িক পত্রে প্রকাশ পেয়েছিল। কবিতাটির আকার ছিল কিছুটা সংক্ষিপ্ত। প্রথম প্রকাশিত উদ্বোধন কবিতার পাঠ অনুসারে নিচের চারটি ছত্রের অনুবৃত্তি স্বরূপ নবজাতক-এর মুদ্রিত পাঠে দ্বিতীয় স্তবকে পড়তে হবে—
শুকতারার প্রথম প্রদীপ হাতে
অরুণ-আভাস-জড়ানো ভোরের রাতে
আমি এসেছিনু তোমারে জাগাব বলে
তরুণ আলোর কোলে—
কিন্তু এই কবিতার প্রথম স্তবকে কবি একটি সুষম সৌন্দর্যের কথাও বলেছেন। কবি যেখানে বলেছেন—
এসো এসো সেই নব সৃষ্টির কবি
নবজাগরণ-যুগপ্রভাতের রবি।
গান এনেছিলে নব ছন্দের তালে
তরুণী উষার শিশির স্নানের কালে,
আলো-আঁধারের আনন্দ বিপ্লবে।
এই কবিতাটি গীতবিতানের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হিসাবেও ছাপা হয়েছিল।
নবজাতক কাব্যের তৃতীয় কবিতা শেষদৃষ্টি। কবিতাটি শান্তিনিকেতনের সেঁজুতি বাড়িতে বসে লেখা। রচনার সময় হিসাবে যে তথ্য পাওয়া যায় তা ১২ জানুয়ারি ১৯৪০। দ্বিখণ্ডিত পৃথিবীতে পরাধীন ভারতবর্ষে কবির কাছে জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। তিনি প্রায় ধরতে গেলে বিষাদসিন্ধুতে ডুবে যেতে যেতে সুরের আবেশে ভোগ বিলাসিতা ত্যাগ করেছেন। তারই একটি অপূর্ব চিত্রকল্প আমরা পাই কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে—
যে অতিথিদেহে ভোরবেলাকার
রূপ নিল ভৈরবী,
অস্তরবির দেহলিদুয়ারে
বাঁশিতে আজিকে আঁকিল উহারে
মূলতান রাগে সুরের প্রতিমা
গেরুয়া রঙের ছবি।
কবি আরো তারপরের স্তবকে একটি চিরায়ত, শাশ্বত সত্য যা কেবল কবির পক্ষেই বলা সম্ভব। এবং তা যে এই বাংলার, এই দেশের এই সময়ের পক্ষে মঙ্গলজনক তাও বলেছেন—
নিয়ে সে দুঃখ ধীর আনন্দে
কবি লিখেছেন বিষাদকরুণ শিল্পছন্দে
অগোচর কবি করেছে রচনা
মাধুরী চিরন্তন।
এই মনের মাধুরীই বাঁচার রসদ জোগায় মানুষকে উপলব্ধি করতে কোথায় মানুষ মানুষের জন্য, হৃদয় হৃদয়ের জন্য। একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে তাই মানুষ পড়ে প্রেমের মালা। তাই অখণ্ড ভারতবর্ষে প্রেমের কবি বৈষ্ণব পদাবলির প্রেমের কবি চণ্ডীদাস প্রেমের জয়গান গেয়েছেন। এবং তিনি সমাজের প্রান্তেবাসী পতিত রজনীকেই পূজার স্থানে, মনের মন্দিরে বসিয়েছেন। এছাড়া পৃথিবীর মহাকাব্যের ইতিহাসে ভারতীয় রামায়ণের সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগরী হরফে আদি কবি বাল্মীকিও নিম্ন পতিত মানুষের মধ্যে জন্ম। তিনিও দীর্ঘদিন অকাজ-কুকাজ করে অবশেষে কলম ধরলেন। বাল্মীকি কি লিখতে পারতেন না? না রামায়ণ সমষ্টির রচিত, বাল্মীকি পদাধিকারী কয়েক প্রজন্ম মিলে ওই মহাকাব্য রচনা করেনি তো? সেইদিন যেদিন অন্যের যন্ত্রণা নিজের হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পারলেন। সেইদিন তিনি বলে উঠলেন—
যৎ ক্রৌঞ্চদেকমবধি কামমোহিতম্।
মা নিষাদ শাশ্বতী হয়ং॥
এবং বাল্মীকি রচিত এটিই প্রথম শ্লোক। এই কবিতাতেই একটি অসামান্য পংক্তি যা আমাদের আগামী প্রজন্মকে আমাদের প্রকৃত শিক্ষা দেয়। কবি বলেছেন—
যা গিয়েছে তার অধরারূপের
অলখ পরশখানি
যা রয়েছে তারি তারে বাঁধে সুর,
এই কাব্যের ‘প্রায়শ্চিত্ত’ কবিতাটির রবীন্দ্রভবনের পাণ্ডুলিপির যে পাঠ সংগৃহীত রয়েছে, তার মূল রূপ কেমন ছিল নিচে তা দেওয়া হল—
বহু শত শত বৎসর ব্যাপি
শত শত দনে রাতে
দৈন্যের আর স্পর্ধার সংঘাতে
ধিকি ধিকি করে ব্যাপ্ত হয়েছে
পাপের দহন জ্বালা
সভ্যনামিক পাতালপুরীতে যেখানে যক্ষশালা।
মাঝে মাঝে তারি ঝলক লেগেছে
আতিশয্যের ’পরে,
ভাগ্যের তাহা মহিমা বলিয়া
জেনেছে গর্বভরে
সুখস্বপ্নের নিশীথে উকিল
ভূমিকম্পের রোল
জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে লাগিল
দারুণ দোল।
অহংকারের ফাটিল হর্ম্যচূড়া,
লুণ্ঠিত ধনভাণ্ডার হল গুঁড়া।
বিদীর্ণ হল প্রমোদভবনতল,
তারি গহ্বর ভেদিয়া উঠিল
নাগ নাগিনীর দল।
বিষ-উদগারে দুলিল লক্ষ ফণা,
প্রলয়শ্বাসে ছুটিল অগ্নিকণা।
রক্ত মাতাল যমদূত সবে বীভৎস উৎসবে
ধরণীর বুক চিরিতে লাগিল
অট্টহাস্যরবে।
নিরর্থ হাহাকারে
দিয়ো না দিয়ো না অভিশাপ বিধাতারে।
পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের উ্দদাম বেগে আগে হয়ে যাক ক্ষয়।
অসহ দুঃখে ব্রণের পিণ্ডে বিদীর্ণ হয়ে তার
কলুষপুঞ্জু করে দিক উদগার।
দানবের ভোগে বলি এনেছিল যারা
সেই ভীরুদের দলিত জীবনে উঠুক মৃত্যু ধারা।
মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে কবির জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বল রাশি
লাগুগ তাহাতে লাগুল আগুন
ফেলুক তাহারে গ্রাসি।
ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু কারা
চলে গির্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভালুইতে দেবরায়।
দুর্বলাত্মা মনে জানে ওরা
ভীত প্রার্থনা রবে
শান্তি আনিবে ভবে।
তার বেশি কিছু দিতে নাহি মন, শুধু বাণী কৌশলে
জিনিবে ধরণীতলে।
বহুদিবসের পুঞ্জিত লোভ
বক্ষে রাখিয়া জমা
কেবল শাস্ত্রমন্ত্র পড়িয়া
বিধাতার লবে ক্ষমা।
সবে না দেবতা হেন অপমান
এই ফাঁকি ভক্তির।
যদি এ ভুবনে থাকে কোনো তেজ
কল্যাণ শক্তির—
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নতূন আলোকে
লাগিবে নূতন দেশে।
পাণ্ডুলিপির নিচে লেখা আছে—
বিজয়া দশমী
১৩৪৫
এরপরের কবিতা ‘বুদ্ধভক্তি’। কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল পত্রপুট কাব্যে। কবিতাটির প্রথমে একটি প্রস্তাবনা উল্লিখিত সেটি হল ‘জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধ মন্দিরের পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।’ কবিতাটি কবি ৭ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন লিখেছিলেন। উত্তলিত হিংস্রতার দাবানলে জ্বলতে থাকা অস্থির সময়ে, বিভাজিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে কবির বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এই কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। চীন জাপান যে বৌদ্ধদের প্রভাব সেখানেও প্রতিবেশি দেশগুলির প্রভাবে তারা চিন্তিত হয়ে পড়ে। বিশেষত উপমহাদেশীয় এবং এশিয়া মহাদেশের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে দিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তারপর আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি কবিকে বিমর্ষ, মর্মে বিষম আঘাত করেছিল। তারই প্রতিফলনে কবি আক্ষেপের সঙ্গে এই কবিতায় অত্যন্ত ব্যথাতুর হয়ে লিখলেন—
আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।
আত্মীয় বন্ধন করি দিবে ছিন্ন,
গ্রামপল্লীর রবে ভস্মের চিহ্ন,
হানিবে শূন্য হতে বহ্নি-আঘাত
বিদ্যার নিকেতন হবে ধূলিসাৎ—
বক্ষ ফুলায় বর যাচে
দয়াময় বুদ্ধের কাছে।
তূরী ভেরী বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।
এরপরের কবিতা ‘কেন’। রচিত হয়েছে রবীন্দ্রভবনের সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির তারিখ অনুসারে ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ সালে। উদয়ন বাড়িতে বসে কবি কবিতাটি রচনা করেছেন। কাব্যে যেটি স্থান পেয়েছে সেটি পাঠান্তরিত রূপ। পাঠান্তরিত হয়ে কবিতাটি ১২ অক্টোবর ১৯৩৮ সালে ‘নবজাতক’ কাব্যে গৃহীত হয়েছে। আদি পাঠে কবিতাটিতে ৬৬টি পংক্তি ছিল এবং স্তবক সংখ্যা ছিল চারটি। পাঠান্তরিত হয়ে কাব্যে মুদ্রিত পংক্তি সংখ্যা ৬৮। স্তবক সংখ্যা চারটি রয়েছে।
রবীন্দ্র-ভবনে সংগৃহীত কবিতাটির পাণ্ডুলিপি পাঠ নিম্নে দেওয়া হল—
শুনিলাম জ্যোতিষীর কাছে
তপনের আত্মদান-মহাযজ্ঞ হতে
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় নৈবেদ্যের মতো
এ বিশ্বের মন্দিরমণ্ডপে,
অতি তুচ্ছ অংশ তার
ধরা পড়ে পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র মৎপাত্র তলে।
অবশিষ্ট অমেয় আলোক রশ্মিধারা
আদিম দিগন্ত হতে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে লক্ষ্যহারা দ্যুলোকে দ্যুলোকে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে অপার তিমির-তেপান্তরে
অসংখ্য নক্ষত্র হতে
তেজোদীপ্ত অক্ষৌহিনী
এ কি সর্বত্যাগী অপব্যয়
সর্বগ্রাসী ব্যর্থতার নিঃসীম অতলে।
কিংবা এ কি মহাকাল
এক হাতে দান করে, ফিরে ফিরে নেয় অন্যহাতে।
যুগে যুগে বারংবার হিসাব মেলানো।
প্রকাণ্ড সঞ্চয়ে অপচয়ে?
কিন্তু কেন?
তারপরে চেয়ে দেখি মানুষের চৈতন্যজগতে।
ভেসে চলে কত চিন্তা কত-না কল্পনা, কত পথে
কত দুঃখ সুখ
কত কীর্তি রূপ রসে-তীব্র বেগে
অমরত্বের সন্ধানে উদ্দাম উচ্ছাবে উঠে জেগে
ক্লান্তিহীন চেষ্টা কত।
জ্বেলে ওঠে কোথাও বা বাতি
সংসারের যাত্রাপথে তপস্যার তেজে।
কোথাও বা সভ্যতার চিতাবহ্নিদাহ
নিঃস্বতার ভস্মশেষ রেখে।
লক্ষ লক্ষ ঝরিছে নির্ঝর
নিরুদ্দেশ প্রাণস্রোতে বহু ইচ্ছা বহু স্মৃতি লয়ে।
নিত্য নিত্য এমন কি
অফুরান আত্মহত্যা মানবলোকের?
যুগে যুগান্তরে
মানুষের চিত্ত নিয়ে
মহাকাল কেবলি কি করে দ্যুতখেলা
আপনারি বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে
কিন্তু কেন?
একদিন প্রথম বয়সে
এ প্রশ্নই জেগেছিল মনে।
শুধায়েছি এ বিশ্বের কোন কেন্দ্রস্থলে
মিলিতেছে নিরন্তর
অরণ্যের পর্বতের সমুদ্রের উল্লোলগর্জন,
ঝটিকার বজ্রমন্ত্র
দিবসের রজনীরে মর্মস্থলে
বেদনাবাণীর তারে চেতনার মিশ্রিত ঝংকার,
নিদ্রার মর্মর ধ্বনি,
বসন্তের বরষার ঋতু-সভাঙ্গনে
জীবনের মরণের অবিশ্রাম কীর্তনকল্লোল,
আলোকের নিঃশব্দ চরণধ্বনি
মহাঅন্ধকারে।
বালকের কল্পনায় দেখেছিনু প্রতিধ্বনিলোক
গুপ্ত আছে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরকদরে।
সেথায় বিশ্বের ভাষা চতুর্দিক হতে
নিত্য সম্মিলিত।
সেথা হতে প্রতিধ্বনি নূতন সৃষ্টির ক্ষুধা লয়ে
ফিরে দিকে দিকে।
বহু যুগযুগান্তের বিশ্বনিখিলের ধ্বনিধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে আমাতে নিয়েছে আজি রূপ
নিবিড় সংহত প্রতিধ্বনি।
আমি শুধাইনু পুনরায়—
আবার কি সূত্র তার ছিন্ন হয়ে যাবে,
রূপহারা গতিবেগ
চলি যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্যযাত্রাপথে
ভেঙে ফেলে দিয়ে তার
স্বল্প-আয়ু বেদনার কমণ্ডলু।
কিন্তু কেন।
শান্তিনিকেতন
উদয়ন
১৮।৯।৩৮
১২৫তম রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৯৭, পুনর্মুদ্রণ ১৪০২ সাল। এই রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে নবজাতক কাব্যটি স্থান পেয়েছে। কাব্যের ‘কেন’ কবিতাটির পাঠান্তর নিচে দেওয়া হল-
শুনিলাম জ্যোতিষরা কাছে
তপনের আত্মদান-মহাযজ্ঞ হতে
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয়ে নৈবেদ্যের মতো
এ বিশ্বের মন্দিরমণ্ডপে,
অতি তুচ্ছ অংশ তার ঝরে
ধরা পড়ে পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের পরে
অবশিষ্ট অমেয় আলোকরশ্মিধারা পথহারা
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে লক্ষ্যহারা দ্যুলোকে দ্যুলোকে।
অসংখ্য নক্ষত্র হতে
রশ্মিপ্লাবী নিরন্ত নির্ঝরে।
অবশেষে তাই বলতেই হয় গোধূলি গগনে কবি যেন আগামী কয়েক শত বৎসরের ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারিত করলেন। তিনি যে যুগশ্রষ্ঠা সেকথা এখনো আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। তাই প্রতিদিন প্রভাতে সন্ধ্যায় গুরুদেবেরই আরাধনা করি।
তথ্যসূত্র:
১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ গীতবিতান, গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৭৫, পৃ ৪৬৭
২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃরবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড,বিশ্বভারতী, কলকাতা,১৩৯৭
৩। রবীন্দ্রভবন আর্কাইভস