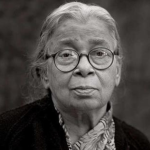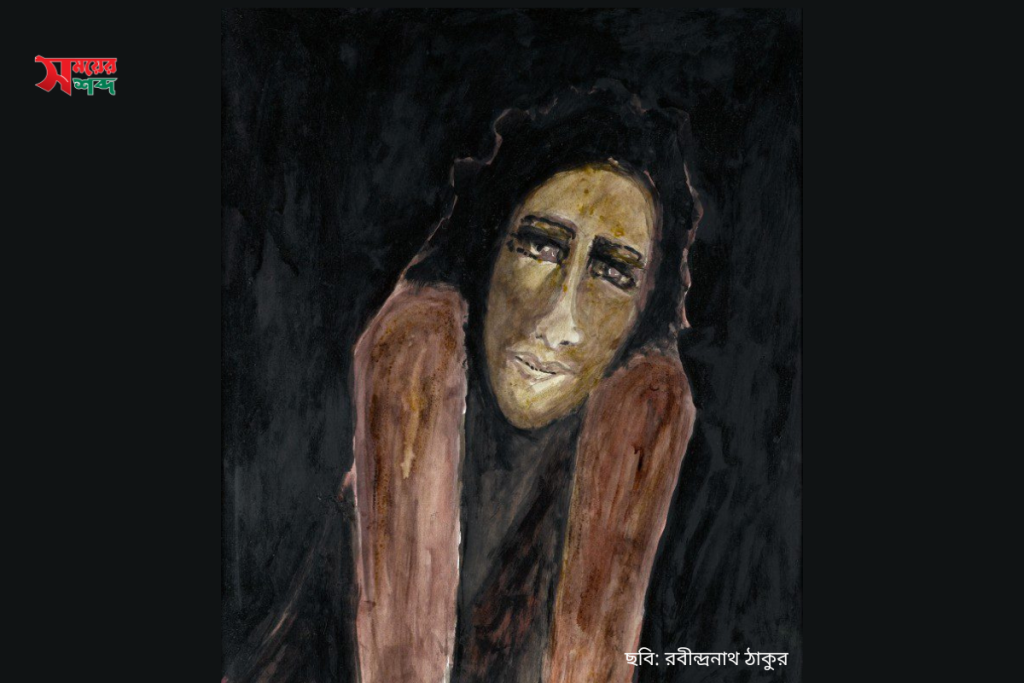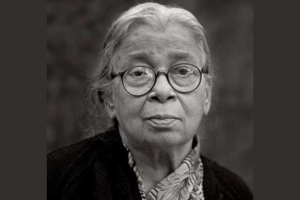দেশ যদি পরাধীন হয় তবে পুরুষও পরাধীন। নারী যদি দ্বিতীয় শ্রেণির হয় তবে তার ক্ষেত্রে সমস্যা আরো। নারীদের সামাজিক অবস্থান ছায়াপাত ঘটিয়েছে রবীন্দ্রনাথের ‘পলাতকা’ কাব্য।
বর্তমান আলোচনায় উঠে এসেছে নারীর ভিন্ন অবস্থানের। অবহেলায় মৃত্যু, বৈধব্য পালন ও পুনর্বিবাহ, কালো মেয়ের চিত্র কিম্বা হারিয়ে যাওয়া মেয়ের ছবি নির্ণয।গভীর অনুসন্ধিৎসু হয়ে কবি গল্পের মতো বলে চলেছেন।
‘পলাতকা’ কাব্যের কবিতাগুলি ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায় প্রকাশিত ১৩২৪ -২৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র বৈশাখের মধ্যে। গ্রন্থাকারে ১৩২৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। প্রথমেই আলোচিত কবিতা, ‘মুক্তি’। কবিতায় মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে সংসার থেকে বিদায় নিচ্ছে একত্রিশ বছরের গৃহবধূ। সে ইবসেনের নোরা নয়, যে নতুন করে ভাবতে শিখবে! মৃত্যু ছাড়া সে-সময়কার বাঙালি মেয়ের মুক্তির অন্য পথ সকলের ছিল না। সে সেই না দেখানো আলোর মুখ।
যতদিন সংসারে ছিল যেন ‘বেঁচে থাকা’টাই ছিল তার ‘রোগ’। কোনো কাজে ভুল হলে কী ‘বিষম কর্মভোগ’ জুটত! সবাই যেটা ভালো বলবে কিংবা মন্দ বলবে, সবটাই মেনে চলতে হতো তাঁকে। হ্যাঁ, ‘নামিয়ে চক্ষু মাথায় ঘোমটা টেনে’ তাঁর উপরে চাপানো সব অপমানভার নীরবে বহন করত, ন’বছর বয়সের বালিকাবধূটি শ্বশুরগৃহের সংসারে প্রবেশ করেছিল, সেই সংসার-যাপন যেন ‘দশের ইচ্ছা বোঝাই-করা’ জীবনটাকে টেনে টেনে। পরবর্তী বাইশ বছর অতিবাহিত। বাইশ বছর ধরে জীবনে শুধু রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা ছিল। বাইরে তাকাবার কোনো অবকাশ তার জোটে না। ‘আমি যে কী’– এ প্রশ্ন তো ওঠেই না। ‘মহাকালের বীণা’– সে জানে না। সাধারণ এক গৃহবধূর জীবনেও বসন্তবাতাস তোলপাড় তুলতে পারে, তার গৃহকর্মে ভুল ঘটাতে পারে, তার বুকেও ‘জন্মান্তরের ব্যথা’ জেগে উঠতে পারে, স্বামী-সন্নিধানের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হতে পারে! কিন্তু সেরকম ঘটে নি।
আর তার স্বামী?
তার বাইরের দুনিয়া আছে। প্রয়োজনের বাইরে তার গৃহজীবনকে পুরুষ গুরুত্ব দেয় নি। আপিস-ফেরত স্বামী বেরিয়ে পড়তেন পাড়ায় কোনো শতরঞ্জ খেলার আসরে। বাঙালি মধ্যবিত্ত সংসারের গৃহবধূদের গৃহকোণেই গড়ে নিতে হয় নিজস্ব পৃথিবী, অর্ধেক পৃথিবী। সেই সংকীর্ণতা থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র মৃত্যু! এ কথা ঠিক, সেই সংকীর্ণতা বিষয়ে সব মেয়েই যে সচেতন হয়, এমন নয়। বরং অধিকাংশ মেয়ে সীমাস্বর্গের রানি হয়ে কৃতার্থই বোধ করে। কবিতার কথক মেয়েটির প্রখর আত্মসচেতনতা তাকে ভূমিকা পালনের তুচ্ছতা থেকে মুক্ত করতে পেরেছিল, বিশ্বচরাচরের সীমাহীনতায় প্রসারিত করতে পেরেছিল নিজেকে। সেই প্রসারণে সে নারী হয়েও ‘মহীয়সী’, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তার বিস্তার, চাঁদের ‘জ্যোৎস্না-বীণা’র সুরে তার সুর মিলে যায়, সন্ধ্যাতারার আলোয় তারই অস্তিত্বের স্বাক্ষর, ফুলফোটার গন্ধে-বর্ণে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে। অথচ তার এই আত্মবোধ একান্ত তারই নিজস্ব, বহিরজীবনের আর কেউ তার খোঁজ রাখে না। সেই জীবনে তার আত্মীয়জনের কাছে সে ‘লক্ষ্মী’ বলে খ্যাত, এর থেকে সংসারে একটি মেয়ের আর কী বা প্রার্থিত হতে পারে!একটি গৃহবধূর এইখানেই তো ‘পরম সার্থকতা’!
জীবনের প্রান্তে এসে, মৃত্যুর প্রতীক্ষায় যখন পৌঁছেছে মেয়েটি, জীবন-মৃত্যু যখন একাকার হয়ে মিলতে চলেছে, তখন তার ‘ভাঁড়ার ঘরের দেয়াল’ যেন ‘ফেনা’র মতো বিলীয়মান, তার সমস্ত সংসার জীবনের উপার্জন তখন অর্থহীন। তখন চরাচর ব্যাপ্ত করে বেজে চলে তার ‘বিয়ের বাঁশি’, তখন দরজায় এসে দাঁড়ায় তার প্রার্থী, তার প্রভু নয়।এভাবেই নারী চৈতন্যের আয়নায় বিম্বিত হয়ে ওঠে কবির ঈশ্বর, মহাবিশ্বে মহাকাশে বিরাজমান সেই বিরাট একটি গৃহবধূর কাছে প্রার্থনা করে তার মধ্যেকার ‘গভীর গোপন’ সুধারস, গ্রহতারার মধ্যে থেকে তুচ্ছ নারীকে পরম মূল্য দিয়ে জেগে থাকে তার দৃষ্টি। তখন তো সমস্ত কিছুই মধুর, বিশ্বসৃষ্টি মধুর, তার নারীসত্তা মধুর আর মৃত্যুও মধুর। সে প্রভু নয়, সে ভিখারি। সেই ভিখারিই জানে, একটি তুচ্ছ মেয়ের ব্যর্থ বাইশ বছর কীভাবে পূর্ণতা পায় কাল-পারাবার উত্তীর্ণ হয়ে? শোক থেকে শ্লোক হয়ে উঠতে পারে চৈতন্যের এই মৃত্যু চেতনার আগের মুহূর্তেই।
সংসার জীবনে হতাশা যা তাকে মুক্তি দেয়নি, দিয়েছে মৃত্যুর আগের মুহূর্তের এক অনুভূতি। সব মেয়ের সেই অনুভূতিও হয় না।
এইখানে তার জীবন অনন্য।
এর আগে প্রকাশিত ‘বলাকা’ কাব্যের ‘হীরামুক্তামানিক্যের ঘটায়’ পূর্ণ অপরূপ তাজমহলের পাশে পালাতকার স্তিমিত লিরিক প্রবাহ কিছুটা ম্লানজ্যোতি, তাই এই কাব্যটি রবীন্দ্রকাব্যধারায় ততটা গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু একটু ধীরভাবে কবিতাগুলি পড়লে বুঝতে পারা যায় যে এই কাব্যনির্ঝরিনীটিতেও বলাকার বাণীই ধ্বনিত হয়েছে। বলাকায় কবি দেখলেন নিরন্তর গতির মধ্যেই রয়েছে বিশ্বের প্রাণশক্তির প্রকৃত প্রকাশ। যৌবনের চলার ছন্দেই লুকিয়ে রয়েছে জীবনের সত্য। মানবজীবনে কোনকিছুই স্থায়ী নয় সবই বন্ধন মুক্তির জন্য ছুটে চলেছে। জীবনের হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, প্রেম, লজ্জা, মান অপমান ইত্যাদি কোন কিছুরই স্থায়ী কোন সত্তা নেই।জীবনের সমস্ত কিছুই অস্থায়ী; পলাতকা।
‘পলাতকা’য় নারী সম্বন্ধে কবির এক নতুন দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। নারী জীবনের এই নতুন আদর্শটি সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন,
‘রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের রচনা ব্যক্তির বন্ধন মোচনের আহ্বানে পূর্ণ।তিনি দেখিয়েছেন জরা, জড়তা, অভ্যাস, সংস্কার, একান্নবর্তী প্রথা-বন্ধনের আর অন্ত নাই, সমস্তই ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে অন্তরায়।এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ব্যক্তিকে, ব্যক্তিসত্তাকে, পূর্ণভাবে বিকশিত হতে তিনি বার বার আহবান করিয়াছেন। এই আহ্বানের একপ্রান্তে ‘মুক্তি’ নামে কবিতাটি; হালদারগোষ্ঠী,স্ত্রীর পত্র, পয়লানম্বর প্রভৃতি অন্যপ্রান্তে; ‘পলাতকা’ কাব্যের নারী নায়িকার দল মাতৃত্ব-প্রেয়সীত্ব-পত্নীত্বের ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়া এক সময়ে বিশুদ্ধ নারীত্বে আসিয়া উপনীত হয়-তখন বুঝিতে পারে ‘আমি নারী, আমি মহীয়সী’।’
“ফাঁকি” কবিতার মূল বিষয় সমাজের প্রচলিত নিয়ম, রীতিনীতি এবং ধারণার বাইরে গিয়ে নিজের জীবনকে নতুন করে বাঁধার চেষ্টা করা। এই কবিতায় বিনুর জীবন, তার অসুস্থতা—।
কবিতার শুরুতেই মাত্র তেইশের বিনু।কবি লেখেন-
‘বিনুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধরল তারে।
ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়ো;
নানা ছাপের জমল শিশি, নানা মাপের কৌটো হল জড়ো।
বছর দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জরজর
তখন বললে, “হাওয়া বদল করো।”
এই সুযোগে বিনু এবার চাপল প্রথম রেলের গাড়ি,
বিয়ের পরে ছাড়ল প্রথম শ্বশুরবাড়ি।’
সমাজের প্রচলিত গণ্ডির বাইরে গিয়ে নিজেকে নতুন করে সন্ধানের চেষ্টা করে বিনু। অসুস্থতা বিনুর একঘেয়ে জীবনকে একটি নতুন দিকে চালিত করে। নতুন জীবনে নতুন অভিজ্ঞতালাভ হয় এবং নতুন মানুষজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। ট্রেন থেকে ঠিক ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসের কুমুর মতো ভিখারি দেখলেই যত্নে দেয় তার সম্বল।
‘রেল-লাইনের ওপার থেকে
কাঙাল যখন ফেরে ভিক্ষা হেঁকে,
বিনু আপন বাক্স খুলে
টাকা সিকে যা হাতে পায় তুলে
কাগজ দিয়ে মুড়ে
দেয় সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে।’
পথের সবকিছুই তার কাছে সুন্দর। কাগজ দিয়ে মুড়ে দেয় অর্থ। স্বামীকে সে নিবিড় করে পায়। যা দেখে তাই তার ভালো লাগে।
‘সবার দুঃখ দূর না হলে পরে
আনন্দ তার আপনারি ভার বইবে কেমন করে।
সংসারের ঐ ভাঙা ঘাটের কিনার হতে
আজ আমাদের ভাসান যেন চিরপ্রেমের স্রোতে,–
তাই যেন আজ দানে ধ্যানে
ভরতে হবে সে যাত্রাটি বিশ্বের কল্যাণে।’
স্বামী জানায়, সংসারের মধ্যে তাদের দেখা ছিল গোপনে। কিন্তু এই বিপুল পৃথিবীর মধ্যে বিনু তার কাছে এসেছে, অসুস্থ হলেও একা। কিন্তু ভেতরের হিসেবী মানুষ মরে যায়নি স্বামীর।বিনুর মতো আবেগ তার জাগেনি। সে নভেল পড়ে। বিনু তাকে অনেক ডাকে কারণ কুলি নারীর মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা দরকার। সাড়া না পেয়ে বলে, এখন তো আপিসের তাড়া নেই। বিনু কুলি নারীর জন্য স্বামীকে পঁচিশ টাকা দিতে বলে। অসুস্থ বিনুকে দুঃখ না দিয়ে সেই কুলি নারীকে ধমকে এক টাকা দেয় এবং বিনুকে মিথ্যে বলে। বিনু মৃত্যুর সময় তাকে বলে,
‘এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ করে।‘
স্বামী পরে আফশোস করে, বিনুর জন্য কুলি নারীকে খোঁজে, রুক্মিণীকে আর পাওয়া যায় না। পঁচিশ টাকার ফাঁকি তাকে কষ্ট দেয়।
কবিতায় আর্থিকভাবে দরিদ্র কুলি নারীকে সমাজ ফাঁকি দেয়।দয়াবতী নারী সহায় হতে চাইলেও তার স্বামী নামক পুরুষতন্ত্র তাকে ফাঁকি দেয়। কুলি নারীর জাতের কারণে তুচ্ছ হয়। আর একটা সাদা চাদর ঢাকা ভদ্রতা মধ্যবিত্ত বিনুর প্রতি থাকলেও আসন্ন মৃত্যু জেনেও বিনুকে ফাঁকি দেওয়া হয়।
এই কবিতায় ‘মুক্তি’ -র মতই বিশ্বপ্রকৃতির চরণতলে এবং মৃত্যুর মুহূর্তে নারী যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়কে পায়। এই কবিতায় সে তাই গভীর পরিতৃপ্ত।
রবীন্দ্রনাথের ‘পলাতকা’ পর্বের কবিতা-গল্পে মুখ্যত সমাজমনস্কতা ও নারীকেন্দ্রিকতার যে প্রকাশ দেখা যায় সবুজপত্র-পর্বের গদ্যগল্পগুলির সঙ্গে তার সাযুজ্য রয়েছে।‘স্ত্রীর পত্র’-গল্প নারীর (শ্রাবণ, ১৩২১) আশ্চর্য বলিষ্ঠ মনের প্রকাশ ঘটেছে।সমসাময়িক কালের ইউরোপের নতুন সামাজিক চেতনা কবি স্বচক্ষে দেখেছিলেন, বুঝেছিলেন এবং কবিচিত্তে তার স্পর্শ লেগেছিল। ‘পলাতকা’ নারীকেন্দ্রিক কবিতা-গল্পের প্রায় সবকটিতেই নারী জীবন সম্বন্ধে কবির এক বিশেষ দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে, নারী জীবনের একটি নতুন আদর্শ তিনি কবিতায় ঘোষণা করেছেন।-আমাদের সমাজে নারীর কোনো মূল্য ছিল না একথা বলা চলে না। কন্যা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে, মা হিসাবে নারীর প্রতি একটি রোমান্টিক দৃষ্টি ও তজ্জনিত প্রীতি এবং শ্রদ্ধাও ছিল, কিন্তু পারিবারিক সম্পর্ক নিরপেক্ষ নারী হিসাবে নারীর মূল্য কিছুই ছিল না, শুধু আমাদের দেশে নয় কোন দেশেই ছিল না। এই নারীর মূল্য অপেক্ষাকৃত বর্তমান যুগের আবিষ্কার, আর্থিক ও সামাজিক বিবর্তনের ফল, ইউরোপের এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে এই ফল, এই আবিষ্কারের সূচনা দেখা দিয়াছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই কিন্তু তাহার প্রকাশ দেখা গেল সে শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থপাদে এবং পূর্ণতার বিকাশ আমরা দেখিলাম মহাযুদ্ধের পর।সে ঢেউ যে আমাদের নিস্তরঙ্গ সমুদ্রতটে আসিয়া লাগিল তাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল ‘স্ত্রীর পত্রে’।
‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পের মৃণাল সম্পর্কে সমালোচকের এই উক্তি যতটা সত্য, পলাতকার নারী নায়িকাদের সম্পর্কেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য।
‘নিষ্কৃতি’ কবিতায় মঞ্জুলিকার জীবনের গল্প, জীবন যন্ত্রণার গল্প- নবজীবনের গল্প। কৌলীন্য প্রথার বলি হয়ে বিধবা মঞ্জুলিকা ভন্ড, স্বার্থপর পিতার সেবায় আত্মোৎসর্গ করে নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ চাওয়া পাওয়াকে ভুলে থাকতেই চেয়েছিল। কিন্তু তার মা’র মৃত্যুর পর বছর না ঘুরতেই পিতা যখন দ্বিতীয় বিবাহ করতে বখরগঞ্জ ছুটলেন, তখন প্রণয়প্রার্থী পুলিনের সাহসী সহযোগিতায় সামাজিক অনুশাসন ছুঁড়ে ফেলে নতুন জীবনে পা রাখে। কবিতায় দুটি দিক- একদিকে পাঁচগুণ বড় পঞ্চননের সঙ্গে বিয়ে কৌলীন্যের জন্য, মঞ্জুলিকার কঠিন বৈধব্য পালন আর বিধবাবিবাহ। কৌলীন্যপ্রথার অন্যতম হাতিয়ার ছিল বহুবিবাহ। বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন অনেক আগেই। কিন্তু মঞ্জুলিকার বাপের মতো মানুষ সমাজে ছিল। আবার তার মা-এর মত প্রতিবাদী সত্তা সমাজে ততদিনে জন্মে গেছে। তিনি বলেন,
“মা কেঁদে কয়,’মঞ্জুলি মোর ওই তো কচি মেয়ে,
ওরই সঙ্গে বিয়ে দেবে, বয়সে ওর চেয়ে
পাঁচগুনো সে বড়।
তাকে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়োসড়ো
এমন বিয়ে ঘটতে দেব নাকো’।”
“বাপ বললে, ‘কান্না তোমার রাখো’,
পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে-
জান না কি মস্ত কুলীন ও যে।
সমাজে তো উঠতে হবে সেটা কি কেউ ভাবো?
ওকে ছাড়লে পাত্র কোথায় পাবো।”
কবিতা লেখার সময়কাল কৌলীন্যপ্রথা সমাজে ছিল রবীন্দ্র নাথ তা দেখিয়েছেন। অনেকদিন আগে কৌলীন্যপ্রথার প্রচলন বল্লাল সেনের হাত ধরে। কিন্তু তারপরও বহুদিন এই প্রথা ছিল। এমনকি বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের একটা কারণ হিসেবে এই প্রথাকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। বহুপরে এই কবিতায় দেখি কৌলীন্য রক্ষা, জাতে ওঠার লোভ থেকেই গেছিল এবং একটা বিরোধী স্বর ছিল, মঞ্জুলিকার মা- সেই স্বরের প্রতিভূ।
কিন্তু পুরুষতন্ত্র যা বলায়, তাই মেনে নিতে হয়।
পঞ্চানন মঞ্জুলিকাকে বিয়ে করে।
‘নিষ্কৃতি’ নামকরণের মধ্যেই রয়েছে মুক্তির দ্যোতনা। প্রেম কিভাবে একটি মেয়েকে সমাজের তথা পিতৃতন্ত্রের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি বা নিষ্কৃতি দিয়েছে, এখানে সেই গল্পই শুনিয়েছেন কবি একান্ত সহজ সরল অলঙ্কারহীন ঘরোয়া ভাষায়।
পঞ্চানন বৃদ্ধ বয়সে যথারীতি দেহ রাখলে তার অল্পবয়সী স্ত্রী বাবার বাড়ি এল। বহুবিবাহ সমাজে আইন সিদ্ধ। বিদ্যাসাগর যে পথ দেখিয়েছেন, বহুপরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্রের বিধবা প্রতিমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সেই ধারাকেই বজায় রেখে গেছেন। এমনকি ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে বিধবা বিবাহ দিতে না পারলেও ‘ত্যাগ’, ‘প্রতিবেশিনী’ গল্প এবং ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে বিধবা বিবাহের চিত্র দেখিয়েছেন। আর তাই তার বিধবা মেয়ে মঞ্জুলিকার মা আবার বিয়ের কথা বলেন। তখন
“বাপ বললেন কঠিন হেসে, ‘তোমরা মায়ে ঝিয়ে
একলগ্নেই বিয়ে কোরো আমার মরার পরে,
সেই কটা দিন থাকো ধৈর্য ধরে।”
এই বলে স্ত্রীর সমস্ত আশায় জল ঢেলে দিয়ে তার “ফের চলল পড়া ইংরেজি সেই প্রেমের উপাখ্যান।” কথার সঙ্গে চরিত্রটির কাজের বৈপরীত্য ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে তার ক্রূর নিষ্ঠুরতাকে সুকৌশলে প্রকাশ করেছেন কবি।বাবা তার নিজের অল্পবয়সী বিধবা মেয়ের কৃচ্ছ্রসাধন দেখে বলেছে –
“গর্ব করি নেকো,
কিন্তু তবু আমার মেয়ে সেটা স্মরণ রেখো।
ব্রহ্মচর্য ব্রত
আমার কাছেই শিক্ষা যে ওর নইলে দেখতে অন্যরকম হত।”
স্ত্রীর মৃত্যুর পর মঞ্জুলিকা বাপের ভার নিলো। নিজে সাধারণ খায় কিন্তু নিষ্ঠুর পিতার খাদ্য তালিকা এইরকম।
’সকাল বেলায় ভাতের পালা, সন্ধ্যাবেলায় রুটি কিংবা লুচি,
ভাতের সঙ্গে মাছের ঘটা
ভাজাভুজি হত পাঁচটা ছটা,
পাঁঠা হত রুটি লুচির সাথে।’
কবি সত্যেন দত্ত ‘দোরোখা একাদশী’ কবিতায় লেখেন,
‘উড়িয়ে লুচি আড়াই দিস্তে দেড় কুড়ি আম সহ
একাদশীর বিধান-দাতা করেন একাদশী,
মুখরোচক এঁর উপবাস,— দমেও ভারী,—অহো!—
পুণ্য ততই বাড়ে যতই এলান্ ভুঁড়ির কশি!
ওদিকে ওই ক্ষীণ মেয়েটি নিত্য একাহারী
একাদশীর বিধান পালন কর্ছে প্রাণে ম’রে,
কণ্ঠাতে প্রাণ ধুঁক্ছে, চোখে সর্ষে-ফুলের সারি,
তৃষ্ণাতে জিভ্ অসাড়্, মালা জপ্ছে ঠাকুর-ঘরে।’
মঞ্জুলিকার মা’র মৃত্যুর পর তার বাবার সেবাযত্নের ভার মঞ্জুলিকার ওপর পড়ার কারণ দেখিয়েছেন কবি –
‘বড়ো ছেলে বাস করে তার স্ত্রী পুত্রদের সঙ্গে বিদেশে পাটনাতে।
দুই মেয়ে তার কেউ থাকে না কাছে,
শ্বশুরবাড়ি আছে।
একটি থাকে ফরিদপুরে
আরেক মেয়ে থাকে আরো দূরে
মাদ্রাজে কোন বিন্ধ্যগিরির পার।
পড়ল মঞ্জুলিকার ‘পরে বাপের সেবাভার।’
মঞ্জুলিকার গৃহকাজের বিবরণ – ‘রৌদ্রে দিয়ে গরম পোশাক আপনি তোলে পাড়ে’, ‘ধোবার বাড়ির ফর্দ টুকে রাখে’। ‘গয়লানী আর মুদির হিসাব রাখতে চেষ্টা করে’, ‘কাসুন্দি তার কোনমতেই হয়না মায়ের মতো’- ইত্যাদি ঘটনা বলে দেয় বাবার সংসার দেখাশোনার মধ্যে কোথাও কোন ফাঁক নেই মঞ্জু লিকার।
মঞ্জুলিকার জীবনে যৌবন-আগমনের পদধ্বনি, প্রেমের অনুভূতি জেগে ওঠে। তার ছবি,
‘আকাশপথে বাণী তারে ডাক দিয়ে যায় আলোর ঝরনা বেয়ে,/রাতের অন্ধকারে/কোন অসীমের রোদন-ভরা বেদন লাগে তারে!/ বাহির হতে তার ঘুচে গেছে সকল অলংকার,/অন্তর তার রাঙিয়ে ওঠে স্তরে স্তরে, /তাই দেখে সে আপনি ভেবে মরে।/কখন কাজের ফাঁকে/জানলা ধরে চুপ করে সে বাইরে চেয়ে থাকে/যেখানে ওই সজনেগাছের ফুলের ঝুরি বেড়ার গায়ে/ রাশি রাশি হাসির ঘায়ে/ আকাশটারে পাগল করে দিবারাতি।’
মঞ্জুলিকার মনের ভাব পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়- ‘রোদন ভরা বেদন’ বাক্যাংশে রোদন ও বেদন- শব্দদ্বয় । ‘বাহির হতে তার ঘুচে গেছে সকল অলংকার’ এই পংক্তি ব্যবহার করে কবি বৈধব্যের বহিরঙ্গীয় বিবর্ণতাকে যেমন স্পষ্ট করেছেন তেমনি এর পরের পংক্তিতে ‘রাঙিয়ে’ শব্দের প্রয়োগে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে ষোল বছরের কিশোরীর প্রেমপূর্ণ টুকটুকে লাল রঙের মনটিকে ইঙ্গিত করেছেন।’ স্তরে স্তরে’ পুনরাবৃত্ত এই পদটি তার মনের আনাচে কানাচে রঙের ছোয়া বুলিয়ে দিয়েছে। শজনে গাছের অজস্র সাদা ফুলকে রাশি রাশি হাসির সঙ্গে তুলনা ও তার দিকে মঞ্জুলির চেয়ে থাকার বর্ণনা মঞ্জুলিকার তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের আনন্দ- পিপাসার স্বরূপটি ফুটিয়ে তোলে,
‘পায়ের শব্দ তারি
মর্মরিত পাতায় পাতায় গিয়েছে সঞ্চারি।
কানে কানে তারি করুণ বাণী,
মৌমাছিদের পাখার গুণ গুণানি।’
সে তার প্রিয়তমের আগমনের পদধ্বনি যেন শুনেছে মর্মর ধ্বনির মাঝে,তার দয়িতের বাণী শুনেছে মৌমাছিদের গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে। তার বয়োধর্ম তাকে প্রেমের পথের সন্ধান দিয়েছে, কিন্তু সমাজধর্ম তাকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করেছে।
সমাজধর্মের নিষ্ঠুরতা আর অন্তরে প্রেমের উন্মেষের এই দুয়ের সঠিক সমন্বয় মঞ্জুলিকা দ্বিধান্বিত। মঞ্জুলিকার প্রেম ও আজন্ম লালিত সংস্কারের দ্বন্দ্ব যে তীব্র অন্তর্দাহ সৃষ্টি করেছে। তাকে পুলিন বিবাহের প্রস্তাব দিলে নিজের পাপ ইচ্ছে পুলিনের চোখে ধরা পড়েছে ভেবে সে বৈধব্যের কৃচ্ছ্রসাধন দ্বিগুণ করে দিয়েছে,
‘মঞ্জুলিকা বাপের সেবায় লাগল দ্বিগুন করে
অষ্টপ্রহর ধরে।
আবশ্যকটা সারা হলে তখন লাগে অনাবশ্যক কাজে
যে বাসনটা মাজা হল আবার সেটা মাজে!
দু’তিন ঘন্টা পর
একবার যে ঘর ঝেড়েছে ফের ঝাড়ে সেই ঘর।
কখন যে স্নান, কখন যে তার আহার,
ঠিক ছিল না তাহার।”
বিধবা মেয়ে থাকতেও স্ত্রীর মৃত্যুর এগারো মাস পেরোতে না পেরোতেই দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তুতি শুরু হল। মেয়ে ,
“দেখলে বাপের নতুন করে সাজ সজ্জা শুরু-
‘হঠাৎ কালো ভ্রমর কৃষ্ণ ভুরু,
পাকাচুল সব কখন হল কটা
চাদরেতে যখন তখন গন্ধ মাখার ঘটা।’
পর পর দুই স্তবকে মঞ্জুলিকার বাবার সংলাপ ও আচরণের মধ্যে যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন কবি, সেই সংলাপ ও বিবরণের ভাষার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে চাপা ব্যঙ্গ। ভাষার আভ্যন্তরীণ এই ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়েছে ভোগী, লোভী, হৃদয়হীন মানুষটির স্বরূপ। স্ত্রী-কন্যাকে প্রতারিত করে নিজে ভোগের রাস্তা থেকে এতটুকু সরেনি চরিত্রটি- যা পিতৃতন্ত্রের নিষ্ঠুরতাকে তীব্র আঘাত করেছে।
মঞ্জুলিকার মা’র মুক্তি ঘটেছে মৃত্যুতে, ‘মুক্তি’ আর ‘ফাঁকি’ কবিতার তেত্রিশ আর তেইশের মেয়েদুটির মতো। কিন্তু মঞ্জুলিকার মুক্তি এসেছে এক জীবনেই, প্রেমের পথে এগিয়ে গিয়ে প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে।বাবা বাখরগঞ্জ থেকে দ্বিতীয় বিবাহ সেরে ঘরে এসে দেখেছেন —
‘ঘরেতে নেই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি পড়ে
পুলিন তাকে বিয়ে করে
গেছে দোঁহে ফারাক্কাবাদ চলে।‘
বাবা যদিও এই বিবাহকে ভালো চোখে দেখেনি, কিন্তু এই কবিতায় আবার রবীন্দ্রনাথ সার্থক একটি বিধবিবিবাহের চিত্র আঁকলেন। রবীন্দ্রনাথ কৌলীন্যপ্রথা নয়, হৃদয় ধর্মকে বড়ো করলেন। আর নিষ্ঠুরতার ইতিহাসকে পাত্তা না দিয়ে মানবতাকে জয়ী করলেন। প্রতাপ ও প্রেমের মধ্যে প্রেমকেই বরণ করে নিলেন। মঞ্জুলিকা তার সেই ভাবনা রূপায়িত করার মঞ্জুলি, মঞ্জরী।
অল্প বয়সে বিধবা নারীর পরিচয় ঘটে ‘পলতাকা’-র, ‘ছিন্নপত্র’ কবিতায়, বিধবা হয়ে বাল্যকালের সখা নায়ককে চিঠি লেখে মনোরমা।
‘শেষ লাইনে নাম লেখা তার ‘মনোরমা’।
আর হল না পড়া,
মনে হল কোন্ বিধবার ভিক্ষাপত্র মিথ্যা কথায় গড়া—
চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে আবার লাগি কাজে।
কিন্তু পড়ল আমার কোলের’ পরে।
অন্যমনে হাতে তুলে
এই কথাটা পড়ল চোখে ‘মনুরে কি গেছ এখন ভুলে’।
মনু? আমার মনোরম? ছেলেবেলার সেই মনু কি এই?
অমনি হঠাৎ এক নিমেষেই
সকল শূন্য ভ’রে
হারিয়ে-যাওয়া বসন্ত মোর বন্যা হয়ে ডুবিয়ে দিল মোরে।
সেই তো আমার অনেক কালের পড়োশিনি,
পায়ে পায়ে বাজাত মল রিনি ঝিনি।
সেই তো আমার এই জনমের ভোর-গগনের তারা
অসীম হতে এসেছে পথহারা;
সেই তো আমার শিশুকালের শিউলিফুলের কোলে
শুভ্র শিশির দোলে;
সেই তো আমার মুগ্ধ চোখের প্রথম আলো,
এই ভুবনের সকল ভালোর প্রথম ভালো।
প্রথমে গুরুত্ব না দিলেও ছিন্ন পত্র উড়ে এসে পড়ে, তাতে লেখা,
ছেঁড়া চিঠির টুকরোয়, যা
‘এসে
কিন্তু এই কবিতায় কেবল ছিন্নপত্র প্রধান, বিধবা সখীর উন্মোচন আছে, ছোটবেলার স্মৃতি আছে কিন্তু এই পর্যন্তই।
‘কালো মেয়ে’ কবিতায় কবিতায় আঁকেন কালো মেয়ের এক টুকরো চিত্র,
‘ মরচে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জানলাখানি;
পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরানী
ঐখানেতে বসে থাকে একা,
শুকনো নদীর ঘাটে যেন বিনা কাজে নৌকোখানি ঠেকা।
বছর বছর করে ক্রমে
বয়স উঠছে জমে।
বর জোটে না, চিন্তিত তার বাপ;’
প্রসঙ্গত মনে আসে রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষণিকা’ কাব্যের কৃষ্ণকলি কবিতার ভ্রমর চোখের কালো মেয়ের কথা। কিন্তু বাস্তবে নেটিভ শাসিত দেশে কালো মেয়ের তেমন কদর ছিল না। আর অদ্ভুতভাবে রবীন্দ্র পরিবারে কালো মেয়েরাই বউ হয়ে আসতো যশোর থেকে। সরোদাদেবী অবশ্য দুধের সর মাখিয়ে বৌদের রূপটান করতেন। পুরাতনী যার লেখক জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, রবীন্দ্রনাথের মেজো বৌঠান।
কবিতায় কালো মেয়ের নাম নন্দরানি। জানলার ধারে স্থির অবস্থান। আর অন্যদিকে বক্তা থাকে মেসে, যাহোক করে পাস করে চাকরির সন্ধান করে। হয়তো এইটা তার নিগূঢ় ইচ্ছে স ঘটে না, ইচ্ছের কথা অস্পষ্ট মনে ঘোরাফেরা করে। পুলিনের মত সে জীবিকা নির্বাহ করে না।তবে সে চলমান।
কবি তার সামনে নারীর সৌন্দর্য দেখতে পান।যেমন লিওপোল্ড সেনঘরের “ব্ল্যাক ওম্যান”-এ, বক্তা নারীকে তার সমস্ত মহিমায় নিজের জন্য ভালোবাসেন, এবং তার প্রেমে, তিনি তার প্রেয়সীর সৌন্দর্য তুলে ধরার জন্য কিছু আকর্ষণীয় চিত্র এবং রূপক ব্যবহার করে। এই কবিতায় কিন্তু পূর্বরাগ ঘটে তাও অসম্পূর্ণ, বাক্যালাপ ঘটে না, ইচ্ছের কথা অস্পষ্ট মনে ঘোরাফেরা করে। পুলিনের মত সে চাকরি করে না, দারিদ্র্য তাকে কলেজের হাফ-ফি করার জন্য প্রিন্সিপালের কাছে ছোটায়। তার জীবনে বাঁশির সুর নন্দরানি। শুধু নন্দরানির হৃদয়খানি চোখের ‘পরে স্পষ্ট আঁকা—দেখে।
‘ও যেন জুঁইফুলের বাগান সন্ধ্যা-ছায়ায় ঢাকা;
একটুখানি চাঁদের রেখা কৃষ্ণপক্ষে স্তব্ধ নিশীথ রাতে
কালো জলের গহন কিনারাতে।’
কালো মেয়ে যেমন বঞ্চিত, নায়কও এই কবিতায় তেমনি বঞ্চিত। অভাব মেসবাসী নায়কের জীবন থেকে আলোকে দূরে সরিয়েছে, নায়িকার সঙ্গে এইখানেই তার মিল। কালো রং নন্দরানির জীবনের আলো বঞ্চিত করেছে। যদিও গরাদ ভাঙ্গা, তবু এই মেয়েটি নায়কের কাছে বাঁশির সুর, আলোর ঠিকানা।
রেনুকা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় সন্তান এবং দ্বিতীয় কন্যা। ২৩ জানুয়ারি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ। মেজ মেয়ে রেনু ওরফে রেণুকার জন্ম। তার বয়স যখন মাত্র দশ বছর, বড়দিদি মাধুরীলতার বিয়ের দেড় মাসের মধ্যেই ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সাথে রেনুকার বিয়ে হয়ে যায়।কিন্ত স্বামী-সংসার শুরু করার আগেই রেনুকা ক্ষয়রোগে(যক্ষ্মা) আক্রান্ত হয়ে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেমবর মাসের মাঝামাঝি সময়েখ্রিস্টাব্দে মারা যায়।প্রিয়কন্যা রেণুকার মৃত্যুতে কবি মানসিক আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেছিলেন।এর আগে চলে গেছেন পত্নী মৃণালিনী। কিন্তু তবু মাধুরীলতা দেবী(বেলা)ছিল। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর রবীন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান মাধুরীলতার জন্ম, তাঁকে ‘বেলা’ বলেই ডাকতেন আদর করে কখনওবা ‘বেলী’ও বলতেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পত্রসাহিত্যে ‘বেলী’ নামের উল্ল্যেখ দেখা যায়।মাধুরীলতা মাত্র পনের বছর বয়সে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয়পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সাথে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী পেশায় ছিলেন আইনজ্ঞ। মাধুরীলতা দেবী নিঃসন্তান ছিলেন এবং ৩১ বছর ৬ মাস বয়সে ১৬ মে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর শ্বশুরালয়ে মৃত্যুবরণ করেন।মধুরীলতার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের খুব একটা সুসম্পর্ক ছিল না। তিনি বেলিকে মৃত্যুর সময় প্রতিদিন দেখতে যেতেন। বেলি চলে গেল অনেক মান অভিমান নিয়ে। কোনো সময় দেখা যায় সে যাচ্ছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে রাঁচি, বাবার কাছে যায় না। বিয়ের পর তাকে লেখা চিঠিতে বেলির মান অভিমানের কথা লেখেন রবীন্দ্রনাথ।
রেনু চলে যাবার পর বেলি ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ ‘পলাতকা’ লিখলেন।
‘হারিয়ে যাওয়া’ কবিতায় ছোট্ট মেয়ে সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে বলে, হারিয়ে গেছি আমি। তার হাতের প্রদীপ নিভে গেছে। সে তার সঙ্গিনীদের ডাক শুনে নিচে নামছিল। তার বাবা ছিল ছাতে। আবার ছাতে ফিরে গিয়ে সারা নক্ষত্রখচিত আকাশকে মনে হয় বেনারসী শাড়ি , তার বামির মতই। কিন্তু সে দীপশিখা বাঁচিয়ে চলছে ধীরে ধীরে। তার শিখা নিভে গেলে আকাশ ভরা ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যেত। বলতো ‘হারিয়ে গেছি আমি’। এই কবিতায় কন্যা শোকের ছবি আঁকেন। মৃত্যুচেতনা ও অর্থহীন জীবন যেন সমানুপাতে বিস্তার করে কবিতার ছায়াশরীরে। কবিতায় হারিয়ে যাওয়া মেয়ে বিশ্ব প্রকৃতির কোলে অবস্থান করে। এই পর্বের আর একটি কবিতায় সরাসরি শোকচিত্র আছে, ‘অবাঞ্ছিত’ দাগা কবিতায়। শৈল মার অবাঞ্ছিত কন্যা, চতুর্থ সন্তান। সহজে তার বিয়ে হয় না। অবশেষে রেঙ্গুনে বিয়ে ঠিক হল। কিন্তু জাহাজডুবির জন্য চিরদিনের নৌকা বেয়ে শৈল চলে গেলো যবনিকা সরিয়ে অন্য লোকে।
‘পলতাকা’র বেশিরভাগ কবিতায় নারী এসেছে, এসেছে নানানভাবে। তাই নাম পলাতকা। হয়তো ব্যক্তি ও সমাজজীবনের আলোকপাত, কাব্যে যন্ত্রণার মুক্তি। কিছু কবিতায় পরাধীন দেশের কথা আছে, আর নারীদের মৃত্যুর সঙ্গে বিশ্বলোকের মাঝে নারী চেতনকে সন্ধান। অথবা বিশ্বলোকে নারীর অবয়ব প্রতিস্থাপন করেছেন তিনি।#