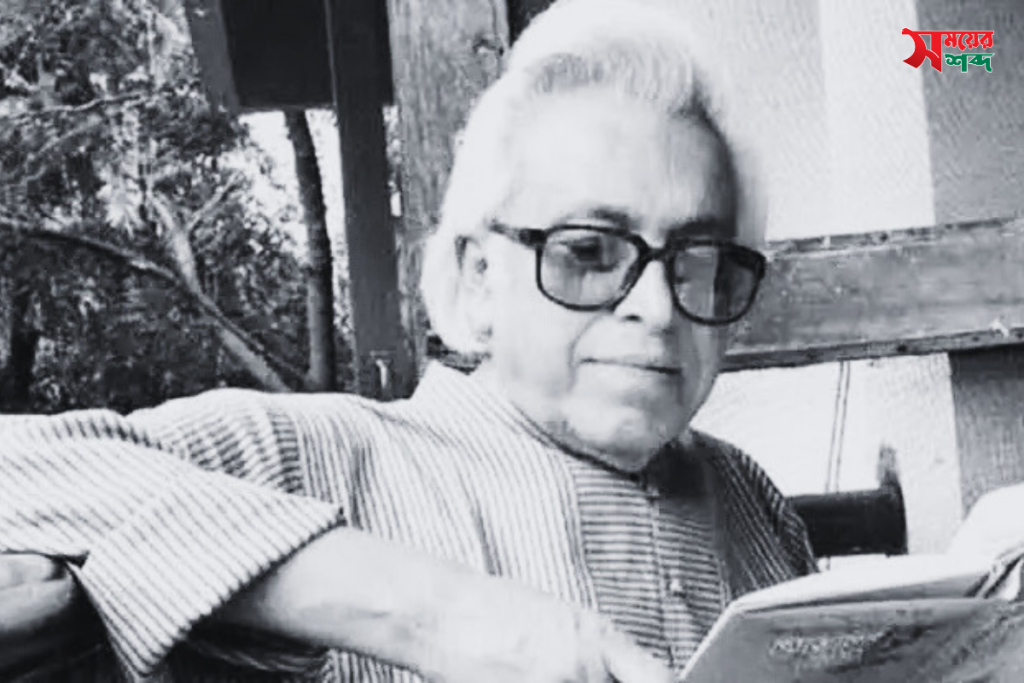আবহমান বাংলা কবিতার উদ্যানে কবি শামসুর রাহমান যেন এক প্রবাদপ্রতিম মালী। তাঁর কবিতা সেই উদ্যানের নানাবর্ণের শোভাময় পুষ্প, যার সুঘ্রাণে আমরা যেমনি আলোকিত হই, আবার অন্যদিকে আলোড়িত হই—রঙের বিভায়। যদিও তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় জীবনানন্দ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটা চোরা প্রভাব প্রবাহিত হয়ে থাকলেও অন্যদিকে নগর সভ্যতার বিবিধ সময়ের বৈষম্য, অসাম্যতা তাঁর সংবেদি বিবেকে দ্রোহের অগ্নি হাত উঠে এসেছে বাবরংবার তার স্বকীয় মেজাজে। আর অন্যদিকে তাঁর অনুকম্পা ও সহানুভূতির নির্মল প্রশস্ত হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কুণ্ঠাহীনভাবে দুঃস্থ মানুষের সেবাকার্যে।
একদম টগবগে যৌবনে পা দিতেই ১৯৪৮ সালে প্রথম কবিতার শুরু। তখন তিনি ১৯-এর দুরন্ত যুবক। সেসময় বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকায় লিখে শুরুতেই নজর কাড়েন কবি, যদিও তাঁর প্রথম কবিতার বই ‘প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যু’ বেরিয়েছিল ১৯৬০ সালে। অধিকন্তু বলা চলে যে, এই প্রথম কাব্যগ্রন্থে কিন্তু শামসুর তাঁর স্বকীয়তার স্বাক্ষর রাখতে পারেননি। অথচ দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘রৌদ্র করোটি’-তে তাঁর স্বরভঙ্গির পরিচয় রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। ভাষাবিজ্ঞানীরা যেভাবে বলেছেন— “যতক্ষণ না মিলছে পাঠকের সাড়া, লেখকের লেখা ততক্ষণই লেখাই নয়।”
অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি কবি শামসুর ১৯৫৮ সালে স্বৈরশাসক আয়ুব খানকে বিদ্রুপ করে লেখেন ‘হাতির শুড়’ নামক কবিতা। ‘সমকাল’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবর রহমান যখন কারাগারে, তখন ‘টেলেমেকাস’ (১৯৬৬-৬৭)। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি গুলিস্তানে একটি মিছিলের সামনে একটি লাঠিতে শহীদ আসাদের রক্তাক্ত শার্ট দিয়ে বানানো পতাকা দেখে মানসিকভাবে মারাত্মক আলোড়িত হন শামসুর এবং তিনি লেখেন ‘আসাদের শার্ট’ কবিতাটি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিবার নিয়ে চলে যান নরসিংদীর পাহাড়তলী গ্রামে। এপ্রিলের প্রথম দিকে তিনি লেখেন যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় আক্রান্ত ও বেদনামথিত কবিতা—‘স্বাধীনতা তুমি’ ও ‘তোমাকে পাবার জন্য হে স্বাধীনতা।”
কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছেন— ‘কবিতা অনেক রকম’। আলাদা হওয়ার পথও এক নয়। এ ব্যাপারে শামসুর রাহমানের ভাবনা কেমন সেদিকে লক্ষ্য করে দেখি—‘কাকে কবিতা বলব, এই প্রশ্নের জবাব নানা মুনি নানা ভাবে দিতে চেষ্টা করেছেন। সেসব সংজ্ঞার ফিরিস্তি পেশ না করে সহজভাবে বলা যেতে পারে, একজন খাঁটি কবি তাঁর অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত অন্তরের নির্যাসটুকু শিল্পিত রূপে কলমের ডগা থেকে কাগজের শূন্য পাতায় লিপিবদ্ধ করলেই কবিতা হয়ে ওঠে। কবিতার বিষয়বস্তু কোনও সীমা পরিসীমা নেই—আনবিক বোমার ভয়াবহতা থেকে শুরু করে ঘাস পর্যন্ত যে-কোনও বিষয় নিয়েই কবিতা হতে পারে। …যে কবি যেমন ইচ্ছে লিখতে পারেন। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে, সেটি যেন কোনক্রমেই অ-কবিতা না হয়।’‘কবিতার দায়’ থেকে তাঁর একটি কবিতার অংশবিশেষ তুলে ধরলে আমাদের মননে একধরণের স্বচ্ছতা ফুটে উঠবে—
আমার কবিতা ভাষা কস্মিনকালেও
বিজ্ঞাপণের ন্যাকা বুলির মতো হবে না, এমন শব্দাবলী
তাতে থাকবে না যাতে বার বার তাক থেকে
নামাতে হয় স্ফীতোদর অভিধান।
কিংবা-
প্রতীকের মুক্ত পথে হেঁটে চলে গেছি আনন্দের মাঠে আর ছড়িয়ে পড়েছি বিশ্বে তোমারই সাহসে।
বোধহয় শামসুর রাহমান জানতেন যে-কবিতা এক আনন্দের মাঠ, আর সেই মাঠে কবি এক কালের রাখাল। জানতেন বলেই হয়তো তিনি খ্যাতির চূড়ায় থেকেও জীবনের শেষ ভাগে প্রভূত লঘু কবিতা লিখলেও জীবনে একটিও বানানো কবিতা লেখেননি। তাঁর কবিতার ভাষায় বিশুদ্ধ সরলতা ছিল, তবে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে কিংবা একেবারেই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মতো শব্দের দুরূহতার দিকে একেবারেই পা বাড়াননি। বালকের চোখ দিয়ে যে সারল্য ও জিজ্ঞাসার দীর্ণমাখা মায়ার আলোকে পাঠক হৃদয় আলোকিত করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কবিতাংশ এখানে তুলে ধরলে আমার বক্তব্যের যথার্থতা মিলে যাবে—
তোমার পাড়ায় আজ বড়ো অন্ধকার; সম্ভবত বাতিটা জ্বালাতে ভুলে গেছে, আমি অভ্যাসবশত কেবলি আলোর কথা বলে ফেলি।
মস্ত উজবুক
এ লোকটা বলে দাও দ্বিধাহীন, ভয় নেই, দেখাবো না মুখ
ভুলেও কস্মিনকালে। তোমরা কি অন্ধকারপ্রিয়,
চলি আমি, এই লণ্ঠনের আলো যে চায় তাকেই পৌঁছে দিও।
(শৈশবের বাতিঅলা আমাকে / বিধ্বস্ত নীলিমা)
কবি তো আলোর কথা বলবেন—এটাই স্বাভাবিক। তমসাচ্ছন্ন অচৈতন্য অবস্থান থেকে চেতনালোকে সুদীপ্তি প্রতিপন্ন করাই তো যে কোন সংবেদি সৃজনশীল মানুষের কাম্য।
কবিতে চিনে নিতে হলে তার বাচনভঙ্গির দিকেই লক্ষ্য দিতে হয়। কীভাবে তিনি নিজস্ব শব্দ সমন্বয় সংঘটিত করছেন, যেখানে ব্যবহারের সুনিপুণ গুণে নতুনত্ব পায় শব্দ; কবি থেকে কবিতে ও কবিতায় বদলে যেতে থাকে তাঁর অর্থবোধকতা। প্রতীক চিত্রকল্পসহ প্রকাশ প্রকরণের বহুরৈখিকতায় নির্মিত হয় কবির নিজস্ব কাব্যভাষা। সেই ভাষাতেই কবি পাঠককে টেনে নেন তাঁর ভাবনাবৃত্তে। তিনবৃত্তের ছন্দে সমান প্রমত্ত হয়ে এখানে লঘু স্বরবৃত্তকে কিভাবে শামসুর ধ্রুপদী মেজাজ তৈরি করেছেন এক্ষণে নীচের উল্লেখিত কবিতা পাঠ করলেই সহজেই অনুমেয় হবে-
ফিরতে হলে বেলাবেলি হাঁটতে হবে
অনেকখানি।
বুক পাঁজরের ঘেরাটোপে ফুচুকি মারে আজব পাখি ।
পক্ষী তুমি সবুর করো,
শ্যামপ্রহরে ডোবার আগে, একটু শুধু
মেওয়া খাবো।
শিরায় শিরায় এখনো তো রক্ত করে
অসভ্যতা।
বাচাল কণা খিস্তি করে হাফগেরস্ত
প্রেমের টানে;
হঠাৎ দেখি চক্ষু টেপে
গন্ধবণিক কালাচাদের মিষ্টি-মিষ্টি
হ্রস্ব পরী।
(ফিরিয়ে নিও ঘাতক কাঁটা / ফিরিয়ে নিও ঘাতক কাঁটা)
কাঠামোগত দিক থেকে নয়, কবির অন্তঃনয়ন কী দেখছে, সেখানেই কবিতার মৌল সৌন্দর্যের বিকিরণ ঘটে। প্রসঙ্গত সনেটের দুটি
পংক্তির কথাই ধরা যাক—
গ্রন্থের অক্ষরদ্বীপে ক্রুশের মতন হেঁটে হেঁটে
পেয়ে গেছি কী উন্মুক্ত অনাক্রমণীয় বাসভূমি।
বলা যেতে পারে যে, উপমা-প্রতীক-রূপকের সুসমন্বয়ে রচিত হয় সার্থক চিত্রকল্প। আলো-আঁধারির উর্ণাজালে রচিত ওপরের দুই পংক্তি চিত্রকল্প হিসেবে শুধু সার্থকই নয়, অনাবিলও বটে। ভাবনা বিস্তারের ঈষৎ সুযোগ করে দেয় পাঠককে। ‘গ্রন্থের অক্ষরদ্বীপ’ এই শব্দবন্ধটি যদি হয় রূপকের উদাহরণ, তাহলে ‘ক্রুশের মতন হেঁটে হেঁটে’ হচ্ছে উপমার অভিমুখ। আসলে এই দুইয়ের সমন্বয়ে শামসুর রাহমান নির্মাণ করেছেন উন্মুক্ত’ চিত্রকল্পের ‘অনাক্রমণীয় বাসভূমি’।
বাংলা কবিতার সুউদ্যানে বিবিধ বর্ণের সুগন্ধিময় প্রেমের কবিতার কুসুম আমরা হৃদয়ে ও মননে তার স্বাদ-গন্ধ-বর্ণসমতে আস্বাদনে বুঁদ হয়ে থেকেছে মানুষ যুগ-যুগান্ত। সেক্ষেত্রে শামসুর রাহমানও ব্যতিক্রম নন। তাঁর ‘কবিতা ও প্রেম’ প্রায় যার কাছে সমার্থক বোধ হয়। তাঁর একটি গদ্যের শিরোনামই হলো—‘প্রেম এবং কবিতা’। সেই গদ্যাংশের স্বাদ আমরা নিতে পারি এখানে— ‘বহুবার প্রেমে পড়েছি, প্রেম আমার জীবনকে বর্ণিল, বৈচিত্রময়, ঐশ্বর্যবান করেছে। কিন্তু আজো আমি প্রেমের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারিনি। চেষ্টাশীল হয়েও কোনো সদুত্তর পাইনি। শুধু বিস্মিত হয়েছি, অভিভূত হয়েছি, পুলকিত হয়েছি, বেদনার্ত হয়েছি।’
প্রসঙ্গত বলা যায় যে, সময়ের সার্থক রূপদানে কবি আপাততুচ্ছ প্রেমের কবিতাকেও দিতে পারেন কালনিরপেক্ষ ধ্রুপদী ব্যঞ্জনা। বাংলা ভাষার অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রেমের কবিতা বলে গণ্য হতে পারে এই কবিতাটি—
যখন তোমার সঙ্গে আমার হলো দেখা
লেকের ধারে সঙ্গোপনে
বিশ্বে তখন মন্দা ভীষণ, রাজায় রাজায়
চলছে লড়াই উলুর বনে।
যখন তোমরা পায়রা-হাতে হাতটা রেখে
ডুবে থাকি স্বর্গ-সুখে,
তখন কোনো গোলটেবিলে দাবার ছকে
শ্বেতপায়রাটা মরছে ধুঁকে
আমরা যখন ঘড়ির দু’টো কাঁটার মতো
মিলি রাতের গভীর যামে,
তখন জানি ইতিহাসের ঘুরছে কাঁটা
পড়ছে বোমা ভিয়েতনামে!
(প্রেমের কবিতা / নিরালোকে দিব্যরথ)
এই মহাবিশ্বে যে কোন সৃজনশীল কবি-শিল্পীদের সান্নিধ্যে এসেছেন বিভিন্ন সময়ে কিছু নারীরা। আবার অন্যদিকে কবিরা প্রেমেও পড়েছেন বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রিয় রমনীর। সেক্ষেত্রেও কবি শামসুর রাহমানের জীবনে ঘটেছে প্রেমসুধাময় অনুভূতির নানা ব্যঞ্জনার অভিব্যক্তি। সেক্ষেত্রে এখন দেখা যাক শামসুর তাঁর একান্ত সাক্ষাৎকারে নারী সম্পর্কে কী কথা বলেছেন—
রাহমান: দেখো, নারী হচ্ছে সৃষ্টিশীল মানুষের প্রেরণা। একটি বেড়ার ঘর তুলতে হলে কিংবা মাচা তৈরি করতে হলেও খুঁটির প্রয়োজন আছে। খুঁটিই কাঠামোটাকে দাঁড় করিয়ে রাখে। সৃষ্টিশীল পুরুষ তার কাজে অদম্য হয়ে উঠতে পারে। এই উৎসাহই কবিতার সূতিকাগার। কিন্তু নারীর মধ্যে যদি কেউ শুধু শারীরিক প্রয়োজন খোঁজে, তা লাম্পট্য ছাড়া আর কিছুই নয়রাহমান : নারী একজন সৃষ্টিশীল পুরুষের সংবেদনশীল মনকে উসকে দেয়। একইভাবে পুরুষও প্রেরণাদায়ক হতে পারে একজন সৃষ্টিশীল নারীর জন্য। আবার বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনরাও এই কাজটি করতে পারেন। আমার অনেক বন্ধু আছেন। সমবয়সী বন্ধু ছাড়াও আছে তোমাদের মতো কিংবা তোমাদের চেয়ে কমবয়সী বন্ধুরা। নারী ছাড়াও এদের কাছ থেকে আমি বিভিন্নভাবে প্রেরণা পাই। তাদের সঙ্গে অভিজ্ঞতার বিনিময় হয়। এইভাবেই একজন সৃষ্টিশীল মানুষ
আধুনিক থাকতে পারেন আজীবন।
এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু প্রেম পর্যায়ের এক ঝলক কবিতার অংশবিশেষ ফের পড়ে নিতে পারি—
১। অথচ আবার প্রেমকে সাজিয়ে বেলাবেলি
মাত্রাবৃত্তে ঘোর অন্যায় করে ফেলি
(কথায় কথায় / টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠো)
২। সারারাত জেগে আমি ফুটিয়েছি শ্বেতপদ্ম এক
অমল অক্ষরবৃত্তে (শ্রুতলিপি / টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠোা)
৩। এভাবে দাঁড়াও যদি দরজার কাছে
তাহলে কী করে বলবো, ‘বিদায় দাও ?’
তোমার দু’চোখ, সোনালি শারীর বলে—
‘হে কবি আমাকে মাত্রাবৃত্তে নাও ।
(কী করে আমরা খণ্ডিত — গৌরব)
৪। দেখেছি সমুদ্রের অস্তরাগে একদা হাওয়ায়
নর্তকী-শিখার মতো সফেদ তরুণ ঘোড়া এক
মেতেছে খেলায়।
উদাহরণস্বরূপ আরো কবিতার অংশবিশেষ তুলে ধরা যেতো, কিন্তু এই স্বল্প পরিসরে বাকসংযমী হতে হলো। কবি শামসুর রাহমানকে যতই নাগরিক কবি বলার একটা প্রয়াস করেছেন কেউ কেউ, আদতে শামসুর মূলত প্রেমের কবি। তাঁর মনোজগৎ ও কবিতাযাপনের ভেতরে আশ্চর্য অন্তর্লীন রোমান্টিকতার ফল্গু স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। একটি বিষয়ে খুব দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, কবি শামসুর তাঁর কাব্যচেতনা ও ভাষাশৈলীর প্রকোষ্ঠে সাবলীল ও সারল্যকে সামনে রেখে কখনো উপমা-রূপক-চিত্রকল্পের মায়াজলে মাত্রাবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত, আবার কখনো শ্বাসাঘাত ছন্দের অব্যর্থ চালে নির্মাণ করেছেন তাঁর কবিতার সাম্রাজ্য। তাঁর সংবাদিকতার পেশা থাকা সত্বেও আসলে তাঁর নেশা কবিতাচর্চা করা ছিল আজীবনের ধর্ম। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে খুব অধিক সংখ্যক পাঠকের হৃদয়ে স্থান করে নিতেই বুঝি এমন সহজিয়া পথে কবিতার অন্দরমহলকে সারল্যতার প্রাধান্য দিতে গিয়ে কখনো কখনো কিছু কবিতা বড্ড লঘু, তারল্যে মূর্ত হয়েছে। তবুও তাঁর সময়কে সুনিবিড়ভাবে ছুঁয়ে কবি সময়োত্তীর্ণের দিকে অভিযাত্রা করেছেন।
কেলমাত্র প্রেম চেতনায় বিধৃত নয়, কবি শামসুরের জীবনচর্যা ও কবিতাযাপনের ভেতরে অধিকতর দুঃস্থ মানুষ ও সমাজ-রাজনীতি অসাম্যতা, বৈষম্যতার বিরুদ্ধে তাঁর সংবেদি বিবেক সব সময় তাঁর দ্রোহ হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মানবতার জয়গানে। ধ্বংসের কিনারে বসেও তিনি স্বপ্ন দেখেছেন সুদিনের। বিপন্ন মানুষকে জুগিয়েছেন ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস। নিম্নোক্ত কবিতায় দেখি তাঁর প্রতিফলন—
আকাশের নীলিমা এখনো
হয়নি ফেরারি, শুদ্ধচারী গাছপালা
আজো সবুজের
পতাকা ওড়ায়, ভরা নদী
কোমর বাঁকায় তন্বী বেদেনীর মতো।
এ পবিত্র মাটি ছেড়ে কখনো কোথাও
পরাজিত সৈনিকের মতো
সুধাংশু যাবে না।
(সুধাংশু যাবে না / ধ্বংসের কিনারে বসে)
শামসুর রাহমান বাঙালির জাতিগত এই ভাষা সাবলীল রপ্ত করেছিলেন। সেই অন্তঃশীল ভাষা তিনি খুবই সুদক্ষভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর কবিতায়। সেই সূত্রেই সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে মিথ করে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা বর্তেছিল তাঁর লিখনশৈলীতে। এখন সেইসব উল্লেখযোগ্য কবিতার অংশবিশেষ তুলে ধরে দেখে নেওয়া যাক—
১। ঝাঁকা-মুটে, ভিখিরি, শ্রমিক, ছাত্র, সমাজসেবিকা,
শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবী, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক,
নিপুণ ক্যামেরাম্যন, ফিরিঅলা, গোয়েন্দা, কেরানি,
সমস্ত দোকান-পাট, প্রেক্ষাগৃহ, ট্রাফিক পুলিশ,
ধাবমান রিকশা, ট্যাক্সি, অতিকায় ডবল ডেকার,
কোমল ভ্যানিটি ব্যাগ, আর ঐতিহাসিক কামান,
প্যান্ডেল, টেলিভিশন, ল্যাম্পপোস্ট, রেস্তোরাঁ, দপ্তর
যাচ্ছে ভেসে, যাচ্ছে ভেসে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরে।
হায়, আজ একি মন্ত্র জপলেন মৌলানা ভাসানী !
বল্লমের মতো ঝলসে ওঠে তার হাত বার বার,
অতি দ্রুত স্ফীত হয়, স্ফীত হয়, মৌলানার সফেদ পাঞ্জাবি,
যেন তিনি ধবধবে একটি পাঞ্জাবি দিয়ে সব
বিক্ষিপ্ত বে-আব্রু লাশ কী ব্যাকুল ঢেকে দিতে চান।
(সফেদ পাঞ্জাবি / দুঃসময়ে মুেখোমুখি)
২। স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা—
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত স্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।
(স্বাধীনতা তুমি / বন্দী শিবির থেকে)
৩। রক্তিম কাদায় ক্রল করতে করতে হাঁটু আর কনুই আহত, অবসন্ন;
বিশ শতকের প্রায় অস্তিম গোধূলি পান ক’রে
ক্ষয়ের ভাটিতে ভেসে যাচ্ছি ক্রমাগত বুঁদ হয়ে, নিরুপায়।
(হ্যাঙওভার /শূন্যতায় তুমি শোকসভা)
৪। আসাদের শার্ট
গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিম্বা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায়, নীলিমায় ।
বোন তার ভায়ের অম্লান শার্টে দিয়েছে লাগিয়ে
নক্ষত্রের মতো কিছু বোতাম কখনো
হৃদয়ের সোনালি তন্তুর সূক্ষ্মতায় ;
বর্ষীয়সী জননী সে-শাট
উঠোনের রৌদ্রে দিয়েছেন মেলে কতদিন স্নেহের বিন্যাসে।
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।
আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্ৰ মানবিক।
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।
প্রসঙ্গত তাঁর কবিবুদ্ধি যাচাইয়ের নিরিখে ‘শ্রেষ্ট কবিতা”-র ভূমিকাটুকু এখানে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন বলে মনে হয়—
প্রায় পঁচিশ বছর ধরে বাগদেবীর পেছনে পেছনে ছুটে চলেছি। কখনো তিনি আমাকে নিয়ে যান স্নিগ্ধ উপত্যকায়, প্রাচীন উদ্যানে, ঝরণাতলায়, সূর্যোদয়ের ঝলমল টিলায়, কখনো বা তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে পৌঁছে যাই চোরাবালিতে। ….কবিতা লেখার সময়, কোনো এক রহস্যময় কারণে, আমি শুনতে পাই চাবুকের তুখোর শব্দ, কোনো নারীর আর্তনাদ; বাগান ঘেরা একতলা বাড়ি, একটি মুখচ্ছবি, তুঁত গাছের ডালের কম্পন, ধিকিয়ে চলা ঘোড়ার গাড়ি, ঘুমন্ত সহিস ভেসে ওঠে দৃষ্টিপথে বার বার। কিছুতেই এগুলি দূরে সরিয়ে দিতে পারিনা। যা-কিছু মানুষের প্রিয়-অপ্রিয়, যা-কিছু জড়িয়ে মানব নিয়তির সঙ্গে, সে সবকিছু আকর্ষণ করে আমাকে। …এসবের বন্দনাই কি আমার কবিতা?
প্রকৃতপক্ষে তাঁর ওই উপরি উল্লিখিত আত্মকথনের অংশটুকুর প্রতিফলন তাঁর সমগ্র কবিতাবলীতে বন্দিত ও নন্দিত রূপে আজও প্রবহমান পাঠক হৃদয় সলিলে। পরিশেষে তাঁর একটি সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ উপস্থাপন করে আমরা দেখে নিতে পারি তিনি তাঁর কবিতার বীক্ষা ও দর্শন কীভাবে ভেবেছেন-
“ধারা-পরম্পরার মধ্যেই কবিতার অগ্রসরমানতা। সেই সঙ্গে চিররহস্যময়তা। রহস্যের পেছনে সত্যসন্ধের মতো ছুটে বেড়ানোতেই কবির আনন্দ। শব্দের পেছনেও কবিতা হচ্ছে রহস্যের খেলা।”
তথ্যসূত্র:
১। আমরা একসঙ্গে হেঁটেছিলাম // আবু হাসান শাহরিয়ার
২। শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা