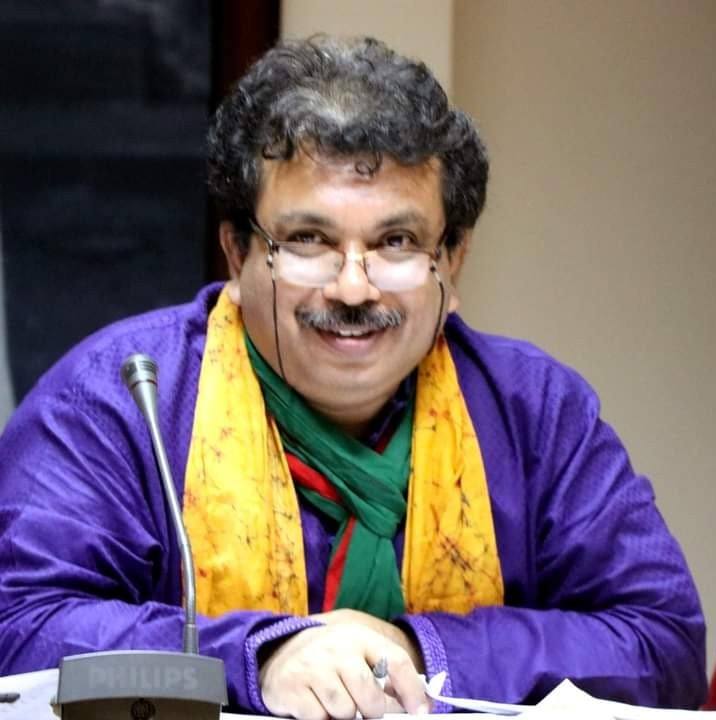উপনিবেশবাদের বৃটিশ আধিপত্যে ভারতবর্ষের জীবন ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, আর্থিক বাণিজ্য নীতি, উৎপাদন ব্যবস্থাসহ সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়ে যায়। প্রাচ্যের সামন্তীয় জীবন ব্যবস্থায় বহুকাল যাবত ধর্মের ভেদাভেদ, জাতিভেদ প্রকটতর হয়ে সামাজিক বৈষম্য, পীড়ন, শোষণ অব্যাহত ছিলো। ভারতবর্ষে বৃটিশ আধিপত্যের ক্ষমতার বলপ্রয়োগের মধ্যেই পাশ্চাত্যের নবজাগরণের প্রবাহ সমাজে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। কুসংস্কারে বিপন্ন প্রাচ্য সমাজের আত্মশক্তি ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হিসেবে জনমনের বিশ্বাস সর্বস্তরে বিরাজিত ছিলো। সামন্ত রাজা জমিদার ভূস্বামীদের সামাজিক জোটের নিকট সাধারণ মানুষের জীবন অসহায় ছিলো। ভোগ বিলাসে মত্ত কূপমণ্ডুক সম্রাট, তার অধঃস্তন রাজা নবাব সামন্তরা পুরো প্রাচ্যকে অশিক্ষা-কুশিক্ষার মধ্যে রেখে সাধারণ জনগণকে শোষণের হাতিয়ার করে রাখে। পাশ্চত্যে পরিবর্তনের যেসব আয়োজন ছিলো, তা থেকে যোজন দূরে অবস্থান প্রাচ্য জনপদের। বৃটিশ উপনিবেশিকতার ভয়াল আয়োজনের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। নতুন এক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হতে থাকে। যারা বৃটিশ অনুগত হয়েও পাশ্চাত্য বোধের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে উনিশ শতকের ভারতে অন্ধকারের ভেতর আলোকায়ন করতে থাকে। সাহিত্য সৃজনশীলতায় ব্যাপক পরিবর্তনের কালপর্বে প্রাচ্যের যুগমানস হয়ে উঠলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (২৫ জানুয়ারি ১৮২৪- ২৯ জুন ১৮৭৩)। উনিশ শতকের পাশ্চাত্য নব জাগরণের প্রাচুর্যের দ্যুতিতে উদ্ভাসিত শক্তিশালী সাহিত্যিক হিসেবে সমকালেও তিনি প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন। বলা যেতে পারে, প্রাচ্যে উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সময়কালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, জীবনবোধের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নতুর অধ্যায় বিনির্মাণ করেছেন। ইউরোপের নবজাগরণলব্ধ প্রজ্ঞার দ্বারা তাঁর মানস চেতনা সজীব, বিস্ময়কর সৃষ্টিশীল। বিশেষ করে উনিশ শতকের নবজাগরণের ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায় এবং ডিরোজি’র ইয়ং বেঙ্গলের ভাবধারায় তাঁর সাধনা ও বাসনায় বিশ্বজাগৃতিবোধ প্রবলতর হয়ে ওঠে। প্রাচ্যের আদি শিল্প সাহিত্য, বিশেষ করে পুরাণ ইতিহাস, রামায়ণ মহাভারত উপাখ্যানের উপাদানকে নবরূপে পাশ্চাত্য আদর্শে সৃষ্টি করার অসামান্য কৃতিত্বের দেখিয়েছেন। হোমারের ওডিসি ও ইলিয়াদ, ভার্জিলের ইনিদ, দান্তের ডিভাইন কমেডি, মিল্টনের প্যারাডাইস লস্টের নির্মাণ কৌশল এবং গ্রীক পুরাণের ঐতিহ্য কবিকে প্রভাবান্বিত করে। এই জীবনবোধ নবযুগের। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্যই কবির জীবন উপলব্ধির পরিপূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।
“গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; ঊরি, দাসে দেহ পদছায়া।
– তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিব পান সুধা নিরবধি।
(মেঘনাদ বধ)
মধুসূদন দত্তের প্রভাব ভারতের অসমিয়া, হিন্দী, মারাঠা, তেলেগু, কন্নড়, মৈথিলী, মণিপুরী সাহিত্যে প্রসারিত হয়েছে। ভিন্ন প্রদেশে মধুসূদন’ প্রবন্ধে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য গবেষণার মাধ্যমে উল্লেখ করেন, মধুসূদন দত্তের কাব্য আঙ্গিকে অসমিয়া কবি রমাকান্ত চৌধুরীর মহাকাব্য ‘ অভিমন্যু বধ’, কবি ভোলানাথ দাসের ‘সীতাহরণ কাব্য (১৯০২, তবে ১৮৭৮ সালে আসাম বিলাসিনীতে প্রথম প্রকাশিত), ওড়িয়ার কবি রাধাকান্ত রায় ‘ মহাযাত্রা (১৮৯৬) কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। তেলেগু ও কন্নড় ভাষার গুরজাডা বেংকট আপ্পারাও ও মঞ্জেশ্বর গোবিন্দ পাই দক্ষিণ ভারতীয় কবিতায় আদি প্রাস বা মিল বর্জন করেন। এছাড়াও অনূদিত হয়েছে, মারাঠা কবি মাধবানুজ মেঘনাদ বধ, বীরঙ্গনা কাব্য; হিন্দী কবি মৈথিলীশরণ ‘মধুপ’ নামে বীরঙ্গনা ও মেঘনাদ রধ’ কাব্য; মৈথিলী ভাষায় গৌরীশঙ্কর ঝাঁ ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্য। মাইকেলের প্রভাবান্বিত কবি ভারতের বিনায়ক দামোদর সাভারকর ‘মহারাষ্ট্রভাট’ ছদ্মনামে ‘গোম-ক (১৯২৪) মহাকাব্য রচনা করেন। মনিপুরী ভাষায় মাইকেলের সৃষ্টিকর্ম মেঘনাদ বধ, অন্যান্য কবিতা অনুবাদ করেন নবদ্বীপচন্দ্র সিংহ, লৌরেমবম ইবোয়াইমা সিংহ, অশাংবম মীনকেতন সিংহ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মাধ্যমে সাহিত্যের যে নবযুগ তা সমকালেও প্রাচ্যের সকল ভাষার কবি লেখক শিল্পীর চেতনাবোধের নবতর উন্মেষ হতে পারে। সংস্কৃত, প্রাচীন ঈরানীয়, গ্রীক, লাতিন, গথিক, আইরিশ ভাষার সংমিশ্রণ, সংস্কৃতির জনজাতিভিত্তিক ঐতিহ্য নিয়ে ভারতবর্ষে বহু জাতির সাথে বিভিন্ন ভাষার মিলনের ফলে প্রাচ্য সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। সেই জ্ঞানবোধ ছিল মাইকেলে মধুসূদন দত্তের।
মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনের নানা পর্যায়ে বিচিত্র জীবন প্রবাহ বিস্ময়কর। ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতায় বসবাস তের বছর বয়স থেকেই এবং সেই সময়ের সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক, প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ উনিশ শতকের বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কলকাতায় নাগরিক সমাজের আকাঙ্খা কবিকে বিলাত যাবার বাসনা সৃষ্টি করে। ১৮৪৩ সালে ৯ ফেব্রুয়ারি সনাতন ধর্ম পরিত্যাগের মতো দুঃসাহস দেখিয়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। দীক্ষা দাতা পাদ্রী ডিলট্রি তাঁকে “মাইকেল” নামকরণ করেন। তখন থেকেই তিনি “মাইকেল মধুসূদন দত্ত” নামে পরিচিতি লাভ করেন। এই ধর্মান্তর এবং পরবর্তী জীবনপ্রবাহ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত হতে সাহায্য করে। গ্রিক, লাতিন, সংস্কৃতসহ বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় মধুসূদনকে আরেক মধুসূদনে রূপান্তর ঘটায়। সংস্কারমুক্ত আধুনিক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বিদ্যোৎসাহিনী সভায় (বাংলা ২ ফাল্গুন ১৮৭২) কবিকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করে রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করে। সেইসময় মধুসূদন দত্ত তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ‘স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম। কিন্তু আমার মতো ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে এদেশের তাদৃশ কোনো অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়। তবে গুণানুরাগীর আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য সহৃদয়তা।’ কবির বিনয় যাই থাকুক কবি নিজের সৃজনশীলতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।
রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘রত্নাবলী’ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করার মধ্যদিয়ে নাটক লেখায় উৎসাহিত হন। ১৮৫৮খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘শর্মিষ্ঠা’ প্রথম মৌলিক নাটক এবং ১৮৫৯ সালে ৩রা সেপ্টেম্বও নাটকটি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হয়। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে দুটি প্রহসন- ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ এবং ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’; পূর্ণাঙ্গ নাটক ‘পদ্মাবতী'(১৮৬০) নাটক প্রকাশিত হয়। এই নাটকেই তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যগ্রন্থ ‘তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০)’ কাব্য, মহাকাব্য ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ (১৮৬১) , ‘ব্রজাঙ্গনা’ কাব্য (১৮৬১), ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক (১৮৬১), ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্য (১৮৬২)। চতুর্দশপদী কবিতা (১৮৬৬), ১৮৭১ সালে মহাকবি হোমারের ‘ইলিয়ড’ মহাকাব্যের অবলম্বনে ‘হেকটর বধ’ প্রকাশিত হয়।
মধুসূদন দত্তের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি মেঘনাদ বধ, যা গ্রীক আদর্শে রচিত মহাকাব্য। সংস্কৃত সাহিত্যের উপাখ্যান, রচনাশৈলী ইউরোপীয়, অলংকারশাস্ত্র গ্রীক – মেঘনাদ বধ মহাকাব্যে সৌন্দর্য ও অসাধারণ দীপ্তি প্রদান করেছে। নারীশক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে প্রমীলা।
১. কি কহিলি! বাসন্তী? পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
২. রোষে লাজ ভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা! কিরীটছটা কবরী-উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী-শিরে
ইন্দ্রচাপ
৩. প্রমোদ উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি বিরহে কাতরা যুবতী।
মধুসূদন দত্তের অসাম্প্রদায়িক, উদার, বিশ্বপ্রসারী দৃষ্টিতে অভিভূত হতে হয়। মুসলিম উপাখ্যান মহরমের ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের করুণ পরিণতি নিয়ে মহাকাব্যো উপজীব্য হতে পারে, সেই বিষয়ে রাজনারায়ণ বসুকে পত্রে লিখেছেন। ইংরেজিতে লেখা পত্রের অনুবাদ –
“আমরা এই মাত্র মহরমের বাজনা শুনে এলাম। আমি তোমাকে বলছি ভারতবর্ষে মুসলমানদের মধ্যে যদি কোন বড় কবির জন্ম হতো তাহলে তিনি হোসেন ও তাঁর বড় ভাই এর মৃত্যুর উপর একটি মহাকাব্য রচনা করতেন এবং এরমধ্যে তিনি তার সমগ্র জাতির আবেগের একটি চমৎকার রূপ দিতে পারতেন। তুমি কি বিশ্বাস লেখার জন্য আমাদের এ-ধরনের কোন বিষয় নেই।” (মোবাশ্বর আলী, মধুসূদনের বিশ্ব)।
মাইকেল মধুসুদন দত্ত সমকালেও প্রাসঙ্গিক এবং অপরিহার্য। তাঁর সৃষ্টিশীল ক্ষমতায় মূল্যবোধের নবতর অভিক্ষেপ, সমন্বয়ের যুগমানস ও আধুনিক জীবনবোধের দূরসঞ্চারী সম্ভাবনা প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয়বার ঢাকায় আসেন। ঢাকার পোগোজ স্কুলে ঢাকাবাসীর পক্ষে সর্ম্বধনার উত্তরে তিনি একটি কবিতা পাঠ করেন।
“নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ব্ব-বঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।
পীড়ায় দুর্ব্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে ( বিধির বিধানে)
তব কওে, হে সুন্দরি! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারে, মহৎ যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে?
দ্বৈপায়ন হৃদতলে কুরুকুলপতি?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে,
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি!”
এই অনুষ্ঠানের একটি বিবরণ ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
“শ্রীযুক্ত মাইকেল দত্ত ঢাকায় গেলে সেখানকার জন কয়েক যুবক তাহাকে একখানি অ্যাড্রেস দেন। তখন একজন বক্তৃতাকালীন বলেন যে, “আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা প্রভৃতি দ্বারা আমরা যেমন মহা গৌরবান্বিত হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমরা ভারি দুঃখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল।” মাইকেল মধুসূদন ইহার উত্তরে বলেন “আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোন ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক একখানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যে (মনি) বলবৎ হয় অমনি আর্শিতে মুখ দেখি। আরো আমি শুদ্ধ বাঙ্গালি নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর।”
(মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবন-প্রসঙ্গ, মধৃসূদন কাব্য গ্রন্থাবলী, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ১৯৭০, পৃ. ২৫-২৬।)
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দ্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রাচ্যের যুগমানস হিসেবে সমকালের পটভূমিতে অনন্য ভাস্বর হয়ে থাকবেন। বৃটিশ উপনিবেশের প্রবল প্রতাপের মধ্যে সামাজিক জাগরণের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তির পথকে প্রশস্ত ও শক্তিশালী করেছেন। একটি অধঃপতিত সমাজে রূপান্তরণের প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। প্রাচ্যের নাগরিক সমাজের মধ্যে বিশ্ব সাহিত্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কীর্তিসমূহ অনন্যসাধারণ হিসেবে সবসময় জ্যোর্তিময় হয়ে থাকবে।#