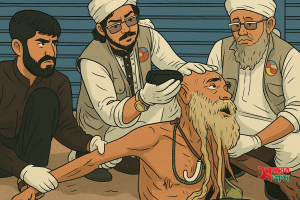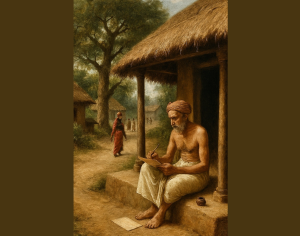আইরিস নাট্যকার জন মিলিংটন সিঞ্জের ‘রাডারস টু দ্য সী‘ (১৯০৪ ) নামের এক প্রখ্যাত একাঙ্কিকায় পশ্চিম আয়ারল্যাণ্ডের আরান দ্বীপপুঞ্জের এক ধীবর পরিবারের বিষাদমথিত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মিখাইল শলোখভের চার খণ্ডে বিধৃত ‘য়্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দ্য ডন‘ (১৯১৮-১৯৪০) নদীবলয়িত জীবনভিত্তিক এক মহৎ উপন্যাস।
বাংলা কথাসাহিত্যে নদীপ্রসঙ্গ বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে চিত্রায়িত হয়েছে। কিন্তু ১৯৩৬ সালের পূর্বেকার উপন্যাসে নদীর ভূমিকা অনেকাংশে আলংকারিক এবং প্রসাধনিক।নদীভিত্তিক বৃত্তিজীবন,নদীর উদ্দামতা ও ঔদাসীন্য, নদীর ধ্বংস এবং সৃষ্টিলীলা বা সামগ্রিকভাবে নদীনির্ভরতা মূল কাহিনি ও চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে নি। এই আত্মীকরনের সূত্রপাত করলেন মাত্র আটচল্লিশ বছরের নিঃশ্বাসী জীবনের অধিকারী (১৯০৮-১৯৫৬) এক নিঃসঙ্গ সাহিত্যপথিক যাঁর নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গ্রন্থিত উপন্যাসটির নাম ‘পদ্মানদীর মাঝি’। পিতার কর্মসূত্রে ভিন্নধর্মী পরিবেশে তাঁর পরিচিতি ঘটে সেই সব প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে যাঁদের য়্যান্তনিও গ্রামশি তাঁর ‘কারাগারের নোটবই’তে সুবলতের্নো বা সাব-অলটার্ন বলেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর অতুলন পর্যবেক্ষণ শক্তি।কথাশিল্পী ও প্রাবন্ধিক সন্তোষকুমার ঘোষের ভাষায় ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আসল ব্যাপার তাঁর নিজের চোখ, একেবারে জ্বলজ্বলে ড্যাবডেবে চোখ, বোধ হয় রঞ্জন-রশ্মিও ছিল। এই প্রথম লক্ষিত হল উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর যাপনচিত্র স্থানিক আচার, সংস্কার, আর্থিক অবস্থিতির সঙ্গে নদীর প্রবহমানতা, তার খেয়ালি চরিত্রের একাত্মতা।
বুদ্ধদেব বসু তাঁর An Acre of Green Grass গ্রন্থে মানিক সাহিত্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ‘We found in him both the rythm and the impulsion of energy, a dramatic, impersonal almost intangible style in his novel of East Bengal boatmen the most beautiful use of dialect of our literature.‘ প্রাবন্ধিক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর‘ গ্রন্থে মানিক উপন্যাসকে যে তিনটি পর্বে বিভাজিত করেছেন তাতে ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ প্রথম পর্বের উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তখনও মার্ক্সীয় বস্তুবাদে মানিকের প্রথাগত দীক্ষা হয় নি।
কী এবং কেন এই দুই প্রশ্নই তাঁকে লিখনের ব্যাপারে বারেবারে আলোড়িত করেছে। ‘যে জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি বুঝেছি সেই জীবনটাই সাহিত্যে কীভাবে কতখানি রূপায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে সেটাও সাহিত্যিককে স্পষ্টভাবে জানতে ও বুঝতে হবে। নইলে নতুন সৃশটির প্রেরণাও জাগবে না, পথও মুক্ত হবে না’।(লেখকের কথা)।
‘সন্ধ্যার সময় জাহাজঘাটায় দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে নৌকার আলো ওগুলি। সমস্ত রাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সংকেতের মতো সঞ্চালিত হয়। –শেষ রাতে ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি ওঠে। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ। লন্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে। মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মতো দেখায়।’
‘কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতেছিল দেবীগঞ্জের মেইল দেড়েক উজানে।
আরও দু’মাইল উজানে পদ্মার ধারে কেতুপুর গ্রাম।’
এভাবেই একটি আস্ত নদী, সর্বনাশা পদ্মা নদী প্রবেশ করেছে বাংলা সাহিত্যের অন্দরমহলে। উপন্যাসটির একটি প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে প্রমত্তা পদ্মা।
পদ্মানদীকেন্দ্রিক ধীবরদের জীবনযাত্রা তিনি কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই নদীবক্ষে ইলিশ মাছ ধরা, চালান দেওয়া, ব্যবসাদার ফড়েদের অত্যাচার, অর্থনৈতিক অ-স্বাধীনতা ব্যাপক দারিদ্র্য এবং বঞ্চনার এক অনাপোশী চিত্র অঙ্কন করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পদ্মার খেয়ালি চরিত্র। গোষ্ঠীগত যাপনচিত্র দিয়ে শুরু হলেও উপন্যাসটি মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। নায়ক কুবের এক অবহেলিত প্রান্তিক সমাজের প্রতিনিধি। ‘গরিবের মধ্যে সে গরিব। ছোটোলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটোলোক। ‘তৃতীয় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কুবের প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামী কিন্তু শান্ত সাংসারিক পরিমণ্ডলে বিরাজমান। ঘরে আছে স্ত্রী মালা, দুই ছেলে, এক মেয়ে, বিধবা পিসি। মালা রূপবতী স্নেহপ্রবণা। সে স্বামীর খোঁজখবর নেয়। রূপকথার গল্প শুনিয়ে স্বামী সন্তান ও শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখে।জেলেপাড়ায় যা দুর্লভ। তার দুটি দোষ–একটি হল তার পঙ্গুত্ব, অন্যটি হল ‘সে হাসতে জানে না। ‘ঊর্মিলা’ এবং ‘পত্রলেখা’ যেমন কাব্যে উপেক্ষিতা মালাও তেমনি এই উপন্যাসে উপেক্ষিত চরিত্র।
এই প্রেক্ষাপটে চতুর্থ পরিচ্ছেদে নাট্ট্যমঞ্চে কপিলার আবির্ভাব। ‘সেবার বড়ো বর্ষা হয়েছিল’। মালার অনুরোধে কুবের যায় চড়কডাঙ্গায় তার শ্বশুরের জলমগ্ন গ্রামে। কোথাও একহাত শুকনো জমি নেই। কুবের ভাইবোনসহ কপিলাকে কেতুপুরে নিয়ে আসে। কপিলা মালার বোন। স্বামী পরিত্যক্তা। সে পদ্মার মতোই প্রমত্তা। সে পরিহাস মুখরা উচ্ছ্বাস প্রবণা লীলা বিভঙ্গে পটিয়সী। ‘পালং শাকের মতো দেহলাবণ্য তার। অবাধ্য কঞ্চির মতো তার বসার ভঙ্গি। কেতুপুরে বাসকালে সে কুবেরকে নৌকায় তামাক পৌঁছে দেয় আর জিজ্ঞেস করে, ‘আমারে নিবা মাঝি লগে”।বেগুনি রঙের শাড়িখানি পরিয়া চুলে চপচপে তেল দিয়া সে শুধু কুবেরের মনোরঞ্জন করে না, কুবেরের সেবাযত্নও করে সে। না চাইতেই পা ধোয়ার জল পায় সে।পান্তাভাতের কাঁসিটির জন্য তাকে আর হাঁকাহাঁকি করতে হয় না। দীন মলিন শয্যাটি পরিপাটি।কখনও সে কুবেরের গোঁফ ধরিয়া টান মারিয়া, কোনোদিন চিমটি কাটিয়া হাসি চাপিয়া চোখের পলকে উধাও হইয়া যায়।কপিলা যেন কুবেরের স্বপ্নসম্ভবা। কিন্তু তার মানসিক দোলাচলের জন্য কপিলা ব্যঙ্গচ্ছলে মাঝেমাঝেই বলে, ‘আরে পুরুষ’। ‘চুলে চপচপে তেল’ দেওয়ার অনুষঙ্গটি উপন্যাসে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে।কুবেরের বঞ্চিত জীবনের রুক্ষ মরুবেলায় কপিলা যেন সরস মরুদ্যান– এটাই বোধ হয় এর প্রতীকী ব্যঞ্জনা।
আশ্বিনের ঝড়ে বিপর্যস্ত মাঝিরা ফিরে আসার সময় পথে কুবেরের সঙ্গে দেখা হলে কপিলা উচ্চরবে কেঁদে ওঠে। বলে, ‘ফিরা আইছ মাঝি, মুখ রাখছেন–ঠাহুর আমার মুখ রাখছেন–আমি না মানত কইর্যা থুইছি পাঁচ পহার হরির লুট দিমু। ‘ঝড়ে ঘরের চাল চাপা পড়ে কুবেরকন্যা গোপির পা ফুলে উঠেছে। পূজা এসে গেলে কপিলার ভাই অধর সবাইকে নিয়ে যেতে চাইলেও কপিলা গোপির বিপদের দোহাই দিয়ে থেকে যায়। এ কি শুধু গোপির সেবাযত্নের জন্য অথবা কুবেরের সঙ্গলিপ্সায়! বাবুদের বাড়ি পূজা দেখে ফেরার পথে কর্মচারী শীতল তার আঁচলে প্রসাদ বেঁধে দেওয়াতে কুবের ঈর্ষাহত হয়ে ওঠে। কুবের তাকে জড়িয়ে ধরলে সে করুণ কন্ঠে বলে, ‘মনডা ভাল না মাঝি, ছাড়বা না? মনডা কাতর বড়ো।’
মন কাতর ক্যান রে কপিলা?
সোয়ামিকে মনে পড়ে মাঝি।
স্বামী পরিত্যক্তা কপিলার এও আরেক রূপ। এ কি কুবেরের পৌরুষ জাগ্রত করবার ছলনা অথবা অবৈধ প্রেমের জন্য বিবেক দংশন?’ কে জানে কি আছে কপিলার মনে। ‘প্রেমবঞ্চিতা এই রমণী হয়তো বহিরঙ্গিন উচ্ছলতার আড়ালে গভীর অন্তরবেদনা প্রশমিত করতে চাইছে।
‘রমণীর মন কে বা জানে।’
ছেলেমেয়েদের নিয়ে কুবের শ্বশুরবাড়ি যায় দোল উৎসব উপলক্ষ্যে। সেখানে আবার কপিলার অন্য রূপ।
‘আমারে রঙ দিলা না মাঝি’?
‘পাঁক দিমু কপিলা, রঙ ত নাই’।
দূর অ! রঙ নাই পাঁক দিবার চায়! দিও না মাঝি,পাঁক দিও না কইলাম।’ পা পিছলাইয়া কপিলা কাদা মাখিয়া জলে গড়াইয়া পড়ে।গাগরি ভাসিয়া যায় জলে।
‘ধরো মাঝি, কলস ধরো’। বলে, ‘আমারে ধরো ক্যান কলস ধরো’।
‘ভীত চোখে চারিদিকে চাহিয়া কলসির মতো আলগোছে– কপিলা ভাসিয়া থাকে, তেমনই ত্রাসের ভঙ্গিতে– স্তন দুটি ভাসে আর ডোবে’। পুকুর থেকে ভরা কলসির জল খানিকটা উছলাইয় পড়ে। কুবেরের প্রতি পূর্ণপ্রেমের অমল অমৃত সিঞ্চনের প্রতীক কি এটি? হোক না সে অবৈধ প্রণয়।
উপন্যাসটিতে হোসেন মিয়া একটি জটিল চরিত্র। সে গীতিকার গায়ক নিপুণ নাবিক দক্ষ শোষক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ। সে নোয়াখালির দিকে একটি অরণ্য অধ্যুষিত দ্বীপ কিনেছে। সেটিকে বাসযোগ্য করে তোলার জন্য প্রজননক্ষম নারীপুরুষের প্রয়োজন। সেজন্য সে কুবেরের ঘরে চোরাই জিনিস রেখে যায়। এবং পরিকল্পনামাফিক পুলিশি তল্লাসী।হয় ময়না দ্বীপ নয়তো কারাগার। রাত গভীর। একাকিনী কপিলা আসে নদীঘাটে কুবেরকে সাবধান করার জন্যে। তার নারীসত্তা প্রার্থিত পুরুষের বিপদ আশঙ্কায় আকুল। ‘কুবেরের বক্ষের আশ্রয়ে কাঁদিতে থাকে সে।’ শেষ মুহূর্তে হোসেন মিয়ার চাতুর্যে কুবের যখন ময়নাদীপে যেতে সম্মত হয়, কপিলা তাকে চুপি চুপি বলে, ‘না গেলা মাঝি, জেল খাটো।’ কিন্তু কুবেরকে হোসেন মিয়ার চক্রান্তে যেতেই হবে। দ্বিধাকম্পিত কপিলা শেষ পর্যন্ত কুবেরকে ত্যাগ করার দৃঢ়তা দেখাতে পারে নি। ছইয়ের একান্তে সে কুবেরকে বলে, ‘আমারে নিবা মাঝি লগে?” কূল থেকে অকূলে পাড়ি।প্রমত্তা পদ্মা থেকে অনিশ্চিত অভিসারে মহাসমুদ্রে যাত্রা।
একুশ বছর পরে প্রকাশিত (১৯৫৭) সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ আর একটি সমুদ্রবিস্তারী নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস। এখানে নদীকে ব্যবহার করা হয়েছে মাছমারাদের নির্মম নিয়তি রূপে। কেতুপুরে ধীবর জীবনের ম্লান স্থবিরতার বিপ্রতীপে প্রাথমিক পর্যায়ে এই উপন্যাসে শুধু গতির বিভঙ্গ। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নৌকার বহর শুধু আসছে—ধলতিতা, তেতুঁলিয়া, বীরপুর, ইটিণ্ডে, টাকি, হাসনাবাদ,বসিরহাট, ন্যাজাট, ব্যারাকপুর নৌকার সারি। শুধু আসছে আসছে। চলার ছন্দে কালপ্রবাহের ব্যঞ্জনা, বেগের আবেগ, জীবনের বহমানতা। মানিকের মতো সমরেশেরও বোধ হয় রঞ্জন রশ্মি চোখ ছিল। মানিকের মতো তিনিও অন্ত্যেবাসী মানুষদের দুঃখবেদনার অংশীদার হয়েছেন লেখকজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে।
গঙ্গাবক্ষে মাছমারাদের দলে থাকে জেলে, কৈবর্ত, নিকিরী, চুনুরী, মালো সবাই। উপন্যাসের নায়ক বিলাস—তেঁতুলতলার ‘তেঁতলে বিলাস’। মানিক যেমন কুবেরদের কথোপকথনে স্থানিক ভাষা ব্যবহার করেছেন সমরেশও গঙ্গার কাহিনি বিন্যাসে মাছমারাদের কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসটির প্রথমাংশে যেন তথ্যভিত্তিক দলিল চিত্র পরিবেশিত হয়েছে। ‘আসছে, সবাই আসছে এদিকে। দিনেরাতে আসছে–একে একে সারি, পাশাপাশি।’ ভাষার ছন্দে বেজে ওঠে জলের অবিরাম প্রবহমানতা। ছোটো ছোটো শব্দবন্ধে যে তরঙ্গ সৃষ্ট হয়েছে তাতে মাছমারাদের জীবনের, নদীতে ভাসমান জীবনের গতিময়তা পরিস্ফুট। একটি ঘনসন্নিবিষ্ট গোষ্ঠীজীবনের আঙ্গিকে উপন্যাসের সূচনা হলেও পরে বিশিষ্ট চরিত্রদের ঘিরে আবর্তিত হয়েছে মাছমারাদের জীবনের জোয়ারভাঁটা। ব্যক্তি আর নৈর্বেক্তিকের সহাবস্থানে পরিব্যাপ্ত হয়েছে এক দুঃখগাথা। মাঝে মাঝে মৃত্যুচেতনা পাঠককে হতবুদ্ধি করে দেয়। সাঁইদার নিবারণ, তার ভাই পাঁচু এবং ঠাণ্ডারামের বীভৎস মৃত্যু আমাদের অনন্ত বিষণ্ণতার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। কিন্তু তা অতিক্রম করে বিলাসের সমুদ্রযাত্রা এক বলিষ্ঠ জীবনবোধের দ্যোতক। এই বাস্তব চিত্রায়ন সম্ভব হয়েছে সমরেশের অভিজ্ঞতার সুবাদে। যেন বি.টি রোডের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চটকল মজুরদের বস্তি পাশ কাটিয়ে তিনি গঙ্গায় এসে পড়লেন।
বিভিন্ন মিথ বা পুরাণকথাকে সমরেশ মাছমারাদের জীবন আবর্তে বারে বারে ব্যবহার করেছেন। নিষ্ঠুর বাস্তবতার মধ্যে বিবিধ পুরাণ কাহিনি বা লোককথা তাদের কাছে জীবনের উৎস, বেঁচে থাকার আধার। ‘পদ্মানদীর মাঝি’র ধীবরদের মতো ‘গঙ্গা’র মাছমারাদের জীবনও মহাজনের কাছে দায়বদ্ধ। কিন্তু আর্থিক অ-স্বাধীনতা, প্রতিকূল প্রকৃতি, জীবনের রূঢ়তা সবকিছু অতিক্রম করে লক্ষিত হয় বহমান চলিষ্ণুতা, সর্বপ্রাণবাদ।
উপন্যাসটির উজ্জ্বলতম নারীচরিত্র ‘হিমি’। সে দামিনী ফড়েনির নাতনি। সে আসে। হাসে। পাড় থেকে নেমে আসে নৌকার কাছে—যতটা না মাছ নেবার জন্যে, তার চেয়ে বিলাসের দুর্বার আকর্ষণে। গায়ে জামা নেই, একখানি শাড়ি পরে এসেছে। গাঢ় নীল সমুদ্রের মতো।তার ওপরে ছড়ানো সাদা রঙের ফুল যেন সোনার মতো খড়কে মাছ সোনা ছিটিয়ে দিয়েছে। জোয়ার, ভাটা,টোটা, সাঁওটা প্রভৃতি নদীকেন্দ্রিক অনুষঙ্গ বিভিন্ন চরিত্রায়নে প্রতীকী মাত্রা সংযোজন করেছে। ‘হিমির শাড়ির জলে ঢেউ কেটে চলে ময়ূরপঙ্খী। পূবের বাতাস টানে আঁচল ধরে। ‘কিন্তু অমন চোখে তাকিয়ে কী দেখে দুজনে দুজনকে। পলক পড়ে না। যেন দুটিতে কতকালের চেনা। যেন ছাড়াছাড়ি হয়েছিল অকস্মাৎ। হারিয়ে গিয়েছিল।ভাটার জলে মাঝি ভাসে আর পলিমাটির পিছনে দাঁড়িয়ে সেই মেয়ে। চোখে চোখ রেখে বলে, ‘যেন চেনা চেনা লাগে, তুমি কি সেই মাঝি’? হিমির রূপবর্ণ্না প্রসঙ্গে লেখক বলছেন–‘শরীরখান অকূল হয় নি, কূলের মুখে এসে থমকে আছে। বর্ষা এলে ভাসবে অকূল পাথারে’। চলতে গিয়ে হিমি পা পিছলে পড়েছে। পা হড়কায় তবু সে হাসে। পশ্চিম আকাশের কালো মেঘের তলা দিয়ে একটু সিঁদুরে মেঘের আলো এসে পড়েছে হিমির একভাঁজ শাড়িতে খোঁপাটি চকচক করছে। কূলের মুখে এসে থমকে থাকা এই হিমি সহজেই পাঠকমন আকৃষ্ট করে।
বহু জীবনযুদ্ধের সেনানী দার্শনিক পাঁচুকাকা মনে করে–‘বিলাসের সাঁওটা ডাক ছেড়েছে মনের মধ্যে। ‘সস্নেহে বলে ওঠে, ‘ও যে মাছমারা সেকথা ভুলে যাচ্ছে। ডাকিনীর মায়া লেগেছে ওর। ‘কখনো শাপান্ত করে, ‘মরবি, মরবি শোরের –লাতি।’ কিন্তু পিরিতি না মানে শাসন। কুবের কপিলার সম্পর্কের বিস্তার ঘটেছে ঊর্মিমুখর পদ্মার বুকে বা কেতুপুরে গার্হস্থ্য পরিমণ্ডলে। তেমনি বিলাস-হিমির প্রেমগাথাও রচিত হয়েছে গঙ্গাতীরে। হিমির সে অর্থে কোন পিছুটান ছিল না।
প্রাবন্ধিক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাগুক্ত গ্রন্থে ‘গঙ্গা’ উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘হিমি বইখানির সর্বাপেক্ষা দুর্বল অংশ। তার ভালোবাসায় মধ্যবিত্ত নায়িকার ধাঁচ এসে পড়ায় বিলাসের সমুদ্রযাত্রার ফলশ্রুতি গৃহীত হয় নি। শ্রদ্ধেয় প্রাবন্ধিকের এই মন্তব্যের যথাযথ মান্যতা দিয়েও বলা যায়, বিলাসের সংগ্রামী বলিষ্ঠতার সঙ্গে হিমির জীবনতৃষ্ণা যুক্ত না হলে বহমান জীবনধারার সামগ্রিক চিত্রটি বাস্তবায়িত হয়ে উঠতো না উপন্যাসে। পাঁচুর বাস্তববুদ্ধি আর দার্শনিক বিষণ্ণতার মাঝে হিমির উজ্জ্বল উপস্থিতি না থাকলে বিলাসের মতো কালনাগ সদৃশ চরিত্রের ব্যাপ্তি পরিস্ফুটিত হত না।তার প্রতিবাদী চরিত্র হয়তো আরো বিদ্ধংসী হয়ে উঠতো।
বিলাসকে হিমি বলে ‘ঢপ’ আর বিলাস তাকে ডাকে ‘মহারানী’ বলে। আজ হিমি সেজেছে তাজা ইলিশকাটা গাঢ় রঙের মতো লাল রঙের শাড়ি পরে। পায়ে দিয়েছে আলতা। কপালে দিয়েছে ছোট টিপ। খোপা বাঁধা মাথার চুল তৈলচর্চিত। কপিলার এত সাজ পোশাকের বহর ছিল না। তবে সেও কুবেরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চপচপে করে মাথায় তেল মাখতো। যারা পমেটম, ফেসিয়ালের নাগাল পায় না সেই অন্ত্যেবাসী রমণীরা অধিক মাত্রায় চুলে তেল দিয়ে নিজেকে সাজাতে ভালবাসে বোধ হয়। আদিবাসী রমণীরাও উৎসবের দিনে করঞ্জার তেলে কেশবিন্যাস করে মাদলের তালে তালে নৃত্যবিভঙ্গে মেতে ওঠেন।
হিমি বিলাসের প্রেমে কোন অবৈধতা ছিল না বলে দুজনে দুজনের কাছে অকপট। গঙ্গার কলুষনাশিনী মিথকে লেখক তাদের অতীত জীবনের মালিন্য দূর করতে ব্যবহার করেছেন। বিলাস অমর্ত্যর বউ এর সঙ্গে তার চকিত শারীরিক সম্পর্কের কথা স্বীকার করে বলে, ‘বড়ো পাপ বয়ে বেড়াচ্ছি আমি, তুমি আমার পাপ ধুয়ে দাও। ‘হিমির অতীত জীবনের পঙ্কিল কাহিনি শুনে বিলাস বলে, ‘আমরা ধোয়ামোছা করে নিই জীবনটা’। লেখকের ‘টানাপোড়েন’ উপন্যাসে যেমন বলা হয়েছে ‘জীবন বুনাকর চল’, এ সেই জীবন বুননের কথা– বলিষ্ঠ জীবনবাদের কথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,অন্তর্গত চরিত্রের পাপবোধ ও অনুতাপ এবং তজ্জনিত স্বীকারোক্তি আধুনিক উপন্যাসের একটী স্বীকৃত পদ্ধতি। এই ধারার সূচনা দস্তয়ভস্কির ‘ক্রাইম এণ্ড পানিশমেন্ট’ উপন্যাসে।
একথা ঠিক যে হিমির চরিত্রে কিছুটা রোমান্টিকতা আছে। কিন্তু প্রেমে রোম্যান্টিকতা না থাকলে তো সে তো নেহাৎই জৈবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।কপিলার দৈনন্দিন পরিবেশ আর হিমির যাপিত জীবনের পরিস্থিতি ভিন্নতর। কেতুপুর ও সংলগ্ন অঞ্চলের বাসিন্দা কপিলার উচ্চারণ ও আচরণে গ্রামীণ সারল্য পরিলক্ষিত হয় কিন্তু হিমি গঞ্জবাসিনী। নিম্নবর্গীয় হলেও তার আচরণ কিছুটা পরিশীলিত হতে বাধ্য। লেখক সেজন্য সচেতনভাবে হিমির সংলাপে মাছমারাদের ভাষা ব্যবহার করেন নি। তার আচরণেও আছে কিছুটা নাগরিক আভাস। অন্তরঙ্গ মুহূর্তেও হিমি বিলাস শালীনতার সীমা অতিক্রম করে নি।
কুবের কপিলার সম্পর্ক এবং বিলাস হিমির সম্পর্ক চিত্রায়ণে মধ্যবিত্ত পরিসরের বাইরে দুই প্রান্তিক যুগলকে নিয়ে রোমান্টিক সম্পর্কের বাতাবরণ সৃষ্ট হয়েছে। ‘আমি হৃদয়ের কথা বলিবারে চাই’। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোয়ীয় মানসকিতাকে ‘রোমান্টিক ন্যাকামি’ বলে অভিহিত করেছিলেন, কিন্তু ‘পদ্মা নদীর মাঝি’তে সেই রোম্যান্টিক আবেষ্টন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। হিমি-বিলাস সম্পর্ক তো আদ্যন্ত রোম্যান্টিক। ‘হিমি সারা দেহ চেপে রইল বিলাসের বলিষ্ঠ দুটি জঙ্ঘায়। বিলাস যেন আদিম মানব। সে জামা খুলে ফেলেছে। চাঁদের আলো পিছলে পড়েছে সারা গায়ে। হিমি আরো ঘন হয়ে এল বিলাসের। বিলাস বলে উঠলো, ‘মহারানী ঝড়ের ভয় করে না কি’? হিমি মুখ লুকিয়ে বলল,’হ্যাঁ গো’। কূল আর অকূল একাকার হয়ে গেল। দোলের দিন দুপুরে পুকুরে কপিলার স্নানদৃশ্য অথবা সন্ধেবেলা বাবুদের বাড়িতে পুজো দেখে ফেরার পথে কুবেরের সঙ্গে কপিলার ঘনিষ্ঠতায় এক আদিমতার আভাস মেলে। কপিলা যেমন অবাধ্য বাঁশের কঞ্চির মতো, পালং শাকের মতো সতেজ তার দেহবল্লরী, হিমিরও তেমনি গড়নটি ছিপছিপে। বয়স বাইশ চব্বিশ হবে–ছেউটি ছেউটি। তবে হিমির চারিত্রিক গভীরতা কপিলার চাইতে বেশি মনে হয়।
বিলাসের প্রশস্ত বুক নীলাম্বুরি অন্ধকারের মতো মহাসমুদ্র। বিলাস সমুদ্রযাত্রায় যাবে শুনে সেই বুকে ভেসে পড়ে হিমি।বলে, সমুদ্রের টান লেগেছে আমারো। আমি এখানে থাকব কেমন করে?
তুমি যাবে মহারানী? অকূলে ভাসবে আমার সঙ্গে?
সেই যে আমার বড়ো সাধ, নইলে থাকবো কোথায় গো?
কিন্তু স্থলবাসিনী অকূলে ভেসে যেতে বড় ভয়। শেষ মুহূর্তে সে নৌকা থেকে নেমে পড়ে।বিদায়বেলায় বেলায় বিলাস বলে, ‘জোয়ারের আগনা্য় আসব তোমার কাছে,চলন্তায় যাব অকূলে,তখন যেন তোমার দেখা পাই।’ হিমি ফিসফিস করে বলতে থাকে ,’তাই, তাই, তাই গো। তাই থাকব আমি, তোমার পথ চেয়ে থাকব।’ কূল আর অকূলের দান্দ্বিকতায় হিমি এখানে চারিত্র মাধুর্যে উজ্জ্বল।
হোসেন মিয়ার স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে কপিলা কূল থেকে অকূলে ভাসতে পেরেছিল। কুবেরকে হারাবার দ্বিধাচিত্ততা ছিল বলে তাকে শেষ মুহূর্তে বলতে হয়েছিল, না গেলা, মাঝি’। কিন্তু হোসেন মিয়া শ্বাপদসঙ্কুল জনবসতিহীন ময়নাদ্বীপে কপিলাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় কুবেরকে। কপিলার গোপন বাসনা চরিতার্থ হয়েছে বটে, কিন্তু হোসেন মিয়া ছিল তার নিয়ন্ত্রক। কিন্তু স্বাধীনচেতা হিমি নিজেই নিজের নিয়ন্তা। এখানেই তার চারিত্রিক দৃঢ়তা। অকূলে যাত্রার অনিশ্চয়তা কূলবাসিনী হিমির বিচ্ছেদের পটভূমি তৈরি করেছে। পদ্মালালিত কপিলার সমুদ্রযাত্রার ভয় নেই, তাই কুবেরে সঙ্গে ‘প্রেমের জোয়ারে’ ভাসতেও তার আপত্তি নেই।
দুটি কালজয়ী নদীবলয়িত উপন্যাসে এই দুই নারীচরিত্র উপন্যাস দুটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে তাই নয়,দুজনেই বাংলা কথাসাহিত্যে নিজস্ব দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে আছে। উপন্যাস দুটি যেমন আঞ্চলিকতার সীমা অতিক্রম করে বিশ্বসাহিত্য সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে, এই চরিত্র দুটিও নিজ বলয়ের বাইরে এসে নিজেদেরকে আপন আপন বিশিষ্টতায় উন্মোচিত করেছে।♦