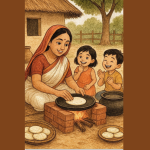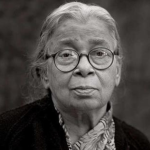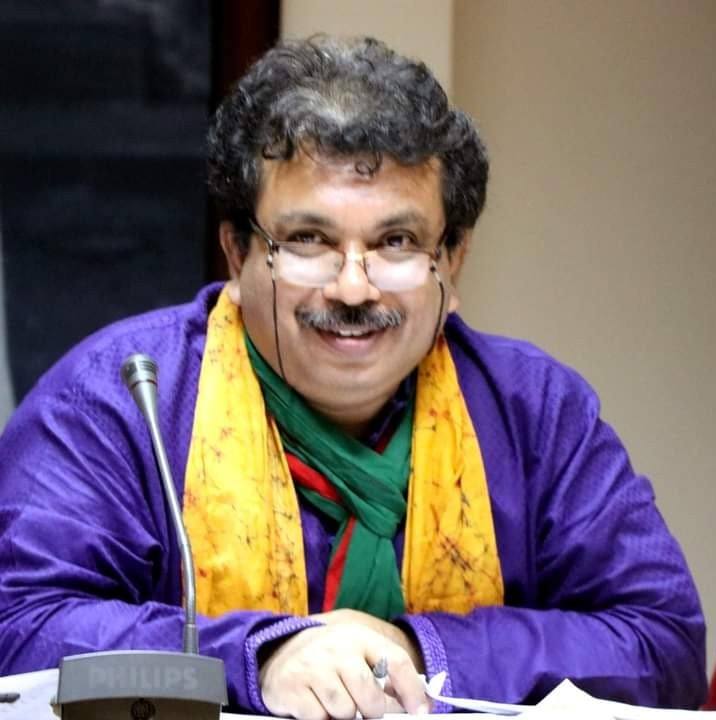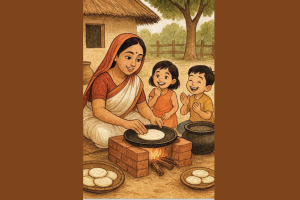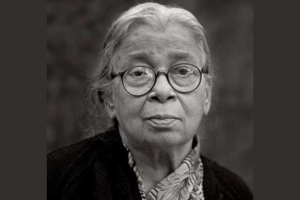বিশ্ব জনপদের সংস্কৃতিতে নৃত্যগীতের ধারা অতি প্রাচীন কাল থেকে শক্তিশালী রূপে বাহিত হয়েছে। প্রাচীন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে নৃত্যের সাথে সামাজিক জীবন, ধর্মীয় কৃত্য, কিংবদন্তী পৌরাণিক কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্র, নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে নৃত্যশাস্ত্র বিষয়ক আলোচনা পাই। নৃত্যের সাথে বিশ্বের প্রত্যেক দেশের বিশেষ কাঠামো, আঙ্গিক সৃষ্টি হয়ে আছে। ভাষা কাঠামো সৃষ্টির পূর্বে ইশারা, অঙ্গের কলাকৌশল নৃত্যের আদিভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর নৃত্যের সাথে সকল মানুষের সংযোগ অনবদ্য আনন্দ ও মানবিকতার হয়ে থাকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীদের নৃত্যে উৎসাহিত করা এবং শিক্ষার সাথে নৃত্যকে সম্পৃক্ত করেছেন। লক্ষ্য করা যায়, কবিগুরু শিক্ষার অনুষঙ্গে সংগীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, নাট্যচর্চাকে পাঠ্যক্রমে যুক্ত করে আনন্দদায়ক শিক্ষাব্যবস্থার ধারা সৃষ্টি করেন। মহৎ আনন্দসৃষ্টির মাধ্যমে মানবিক সমাজ গড়ে তোলা ও নৃত্যের গৌরব মর্যাদার সাথে বিশ্বে তুলে ধরার প্রয়াসে নৃত্যকলাকে তিনি শিক্ষার অনুষঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে বাংলা নৃত্যকলা ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাসে ‘নবযুগ’ সৃষ্টি করেছে। আধুনিক যুগে নৃত্যচর্চার একাডেমিক রূপরেখাটি ১৯২০ সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী থেকে সূচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত নৃত্যকলার ধারাটিকে ‘রবীন্দ্র-নৃত্যবিদ্যা’ বলা যেতে পারে। বাংলা নৃত্যকলার নিরীক্ষা, পর্যালোচনা, সংযোগ-সংশ্লেষ ও বিনির্মাণের মাধ্যমে বঙ্গীয় গৌড়ীয় অঞ্চলের নৃত্যধারার একটি পরিপূর্ণ রূপ ‘রবীন্দ্র নৃত্যবিদ্যা’। যার সাথে প্রাচ্য পাশ্চত্যের নৃত্য ধারার নিরীক্ষা থাকলেও প্রাচ্যনৃত্যরীতি ও অখণ্ড চেতনার সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়েছে।
বিশ্ব নৃত্য দিবস, ইউনেস্কো ঘোষিত তারিখ ২৯ এপ্রিল প্রতিবছর পালিত হয়ে থাকে। প্রখ্যাত ফরাসী ব্যালেট নৃত্যশিল্পী জঁ জর্স নভেরির (২৯. ০৪. ১৭২৭– ১৯. ১০. ১৮১০) জন্ম তারিখকে ১৯৯২ সালে ইউনেস্কো বিশ্বনৃত্য দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আর এই স্বীকৃতির পেছনে Dance Committee of the International Theatre Institute এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্ব নৃত্য দিবসের মূল লক্ষ্য-
1. To Promote all dance forms throughout the World.
2. To make people aware of the value of all the dance forms.
3. To bring attention of governments, leaders and get support to the dance community to promote their art work.
বিশ্বের দেশে দেশে নৃত্য দিবসের প্রতিপাদ্য বাস্তবায়িত হবে সেটাই প্রত্যাশা করি । প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন নৃত্য প্রসঙ্গে বলেন, ”We dance for laughter, We dance for tears, We dance for madness, We dance for fears, We dance for hopes, We dance for screams. We are the dancer, We create the dreams.”
আদি ভারতের শাস্ত্রীয় রীতির সাথে প্রচলিত প্রাকৃত জনপদের বিভিন্ন নৃত্য আঙ্গিকের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরদেশের নৃত্যের আঙ্গিককে সুর, তাল, লয়ের মাধ্যমে আধুনিক নৃত্যকলার রূপটি গড়ে উঠেছে । কবিগুরুর ‘বাল্মিকী প্রতিভা(১৮৮১), কালমৃগয়া (১৮৮২), মায়ার খেলা (১৮৮৮) গীতিনাট্যের অভিনয় কৌশল, সুরের সাথে নৃত্যের পরোক্ষ অনুভব সৃষ্টি হয়েছিল। যা শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার পর প্রকৃত নৃত্য আন্দোলনে পরিণত হয়। কবিগুরু বাংলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নব অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। এই বিস্তৃত বিশাল রবীন্দ্র নৃত্যবিদ্যার সাথে বিশ্ববোধের প্রকাশ উদ্ভাসিত হয়েছে।
আদি ভারতে ‘ভাব, রাগ ও তাল’– এই তিনের সমন্বয়ে নৃত্যকলার অনুশীলন ও বিবর্তনের রূপ পাওয়া যায়। প্রাচীন কালের সামবেদকে সংগীত ও মন্ত্রের বেদ বলা হয়। খৃ পূ ১২০০-১০০০ সময়কালে গ্রন্থিত বলে মনে করা হয়। ১৮৭৫ টি মন্ত্র এই বেদে সন্নিবেশিত আছে। ঋগবেদের তথ্যে জানা যায়, আদিকালে ৩২৯ জন ঋষি, ২৮ জন ঋষিকা ছিলেন। প্রাচীন ভারতবর্ষকে ঋষিদের পুণ্যভূমি বলা হয়। প্রাচ্যঋষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বেদের সংকলন ও বিন্যাস করেছেন। যা কাল পরম্পরায় স্বীকৃত হয়ে আছে। বেদে গায়ত্রী, বৃহতী, অণুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ, উষ্ণিক, জগতী ইত্যাদি ছন্দের নাম উল্লেখ আছে। সামবেদের নবম খণ্ডের ১৯৮ মন্ত্রে দেখা যায়, সাম গায়কেরা (সামগান গায়কেরা) বৃহৎ অন্তরিক্ষে নিবাসী সূর্যরশ্মিসমূহ থেকে আহূত বৈদ্যুতিক জ্যোতিঃ রূপ ধন দান করেন; (= বাজী) অন্নবল ও বাকের অধিকর্তা ইন্দ্র, (সেই বৈদ্যুতিক জ্যোতি থেকে সৃষ্ট) অন্নবল ও বাকদান করুন। (বেদ সমগ্র-ড. অলোক কুমার সেন)।’ বেদের মধ্যে গীত, নৃত্যের বিষয়টি পণ্ডিতগণ নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।
আদি সভ্যতা হরপ্পা, মহেঞ্জদরোর ইতিহাসে নৃত্যের প্রচলন ছিল। প্রাচ্য ভাবধারায় নৃত্যগীতের দেবতা নটরাজ অর্থাৎ শিব। নটরাজের ২টি নৃত্য- তান্ডব, লাস্য। নটরাজের মূতি, ভাস্কর্য বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। বিশ্বের বৃহৎ পদার্থবিদ্যার গবেষণাগার সুইজারল্যান্ডের CERN এর সামনে নটরাজের মূর্তি (২মিটার লম্বা, ২০০৪ সালের ১৮ জুন) স্থাপিত আছে। পদার্থবিদ ফ্রিৎজো কাপ্রা নটরাজ প্রসঙ্গে বলেন, শিবের নৃত্য অতি পারমাণবিক বিষয়। যা সকল অস্তিত্বের ভিত্তি, আর সকল প্রাকৃতিক বিষয়ের ইতিও বোঝায়। তিনি আরও বলেন, শিবই বুঝিয়ে দেন, বিশ্বের কোন সৃষ্টিই স্থিতিশীল নয় এবং সবসময় পরিবর্তনশীল, আর আপেক্ষিকও বটে।’ বিশ্বে নৃত্যের ইতিহাসের সাথে জীবন-জীবিকা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে আছে।
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘নটীর পূজা’য় অভিনয় করার পর নটরাজের ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছিলেন। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবের জন্য লিখলেন ‘নটরাজ -ঋতুরঙ্গশালা’। ‘ষড়ঋতুর আনন্দরূপ বর্ণনা, নট-নটী তরুলতার বন্দনা।
নটরাজের মুক্তিতত্ত্ব “আমি নটরাজের চেলা/ চিত্তাকাশে দেখছি খেলা/ বাঁধন খোলার শিখছি সাধন/ মহাকালের বিপুল নাচে।- ;
উদ্বোধন —
“মন্দিরার মন্দ্র তব বক্ষে আজি বাজে, নটরাজ’
নৃত্যমদে মত্ত করে, ভাঙে চিন্তা, ভাঙে শঙ্কা লাজ,
তুচ্ছ করে সম্মানের অভিমান, চিত্ত টেনে আনে
বিশ্বের প্রাঙ্গনতলে তব নৃত্যছন্দের সন্ধানে।…..
নটরাজ, আমি তব
কবিশিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লব।”
তারপর লিখলেন,
নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।”
১৯০১ সালে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন । নাম দেন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম। কবি উল্লেখ করছেন, ‘শিলাইদহে পদ্মাতীরে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিভৃতে বাস করতুম। একটা সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে সেখান থেকে এলেম শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে’। – (আশ্রমের রূপ ও বিকাশ)। এই আশ্রম হয়ে উঠলো কবির সকল নিরীক্ষার কেন্দ্র। ” সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রার যোগ” সাধনের উদ্দেশ্যে ‘ বিশ্বভারতী” নাম দিলেন। যার লক্ষ্য দুটি, ” এক, ভারতবর্ষকে জানা। দুই, বিশ্বের জ্ঞান- জগতের সাথে যুক্ত হওয়া।” ( উমা দাশগুপ্ত, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন)।
১৯১৮ সালে বিশ্বভারতীর কাজ শুরু হয়। তারপূর্বে তিনি তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখেছিলেন,” শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে–ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে– স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসচে– ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্চে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।’
বিশ্বভারতীর নানারকম উৎসব, পর্ব, অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পন্ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কবিগুরু নৃত্য বিষয়ক বিভিন্ন নিরীক্ষা, অনুশীলনের ব্যবস্থা করেন। নৃত্যের জন্য কোচিন রাজা ভেলায়ূমের নিকট পত্র দেন। সেখান থেকে রাজা কল্যাণী আম্মা নামক নর্তকী দেবদাসীকে পাঠান। এরপর সেখানে পাঠান, স্বরম, কইকুট্রিকলি, কলামুল্লি, মেননকে।
১৯১১ সালে বৈশাখে ‘রাজা’ নাটকে কবিগুরু ঠাকুরদা চরিত্রে নৃত্য অভিনয় করেন। ১৯১৪ সালে অচলায়তন, ১৯১৫ সালে শান্তিনিকেতন ও ১৯১৬ সালে কলকাতায় ফাল্গুনী’ নাটকে অন্ধবাউলের ভূমিকায় কবিগুরুর নৃত্য বিশেষ স্বকীয়তায় পায়।
১৯১৯ সালের ৫-৬ নভেম্বর কবিগুরু সিলেটে পরিভ্রমণ করেন। ৬ নভেম্বর শহরের সম্মিলন স্থলে প্রায় দেড় ঘন্টা বক্তৃতা প্রদান করেন। যা পরে প্রবাসীতে ‘বাঙালির সাধনা’ নামে প্রকাশিত হয়। এই দিনে সিলেটের নিকটে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীতে গিয়ে তিনি ‘রাখাল নৃত্য’ দেখেন। আর কলাগাছের তোরণ, মঙ্গলঘট, আমপাতার শোভনে অভিভূত হন। সন্ধ্যায় ফাদার টমাসের বাংলোয় মনিপুরীর ইমাগো দেবী ও শিল্পীরা ‘রাসলীলা গীতি ও নৃত্য’ তুলে ধরেন । যা কবির মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে। মনিপুরী নৃত্যের অনুশীলনের জন্য প্রথমে সিলেট থেকে অল্প সময়ের জন্য ২ জন নৃত্য শিক্ষককে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যান। তাঁদের চলে যাবার পর কবিগুরু শান্তিনিকেতনের জন্য ত্রিপুরার রাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যকে চিঠি দেন। ত্রিপুরা রাজা ১৯২০ সালে বুদ্ধিমন্ত সিংহ, পরে নবকুমার সিংহ, বৈকুণ্ঠ সিংহকে শান্তিনিকেতনে পাঠান। ১৯২৬ সালে সর্বপ্রথম ‘নটীর পূজা’য় মণিপুরী নৃত্য আঙ্গিক অনুসরণ করা হয়। শান্তিনিকেতনে ১৯২৪ সালে গুজরাতি গবরা শেখানো হয়। সিঁউড়ির ‘রায়বেশেঁ’ নৃত্যের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন।
নৃত্য বিষয়ে কবিগুরুর নানা অভিমত ‘ জাভা-যাত্রীর পত্র’ এ পাওয়া যায়। জাভা দ্বীপে সুরবায়া, সুরকর্তায় নৃত্যের পোশাক তুলনা, ‘ নাচের তালে দুটি অল্প বয়সের মেয়ে এসে মেজের উপর পাশাপাশি বসল। বড়ো সুন্দর ছবি। সাজে সজ্জায় চমৎকার সুছন্দ। সোনায়-খচিত মুকুট মাথায়, গলায় সোনার হারে অর্ধচন্দ্রাকার হাঁসুলি, মণিবন্ধে সোনার সর্পকু-লী বালা, বাহুতে এরকম বাজুবন্দ–তাকে এরা বলে কীলকবাহু। কাঁধ ও দুই বাহু অনাবৃত, বুক থকে কোমর পর্যন্ত সোনায়-সবুজে-মেলানো আঁট কাঁচুলি; কোমরবন্দ থেকে দুই ধারার বস্ত্রাঞ্চল কোঁচার মতো সামনে দুলছে। কোমর থেকে পা পর্যন্ত শাড়ির মতো বস্ত্রবেষ্টনী, সুন্দর বর্তিকশিল্পে বিচিত্র; দেখবামাত্রই মনে হয়, অজন্তার ছবিটি। এমনতর বাহুল্যবর্জিত সুপরিচ্ছন্ন সামঞ্জস্য আমি কখনো দেখি নি। আমাদের নর্তকী বাইজীদের আঁটপায়জামার উপর অত্যন্ত জবড়জঙ্গ কাপড়ের অসৌষ্ঠবতা চিরদিন আমাকে ভারি কুশ্রী লেগেছে! তাদের প্রচুর গয়না ঘাগরা ওড়না ও অত্যন্ত ভারী দেহ মিলিয়ে প্রথমেই মনে হয়, সাজানো একটা মস্ত বোঝা। তার পরে মাঝে মাঝে বাটা থেকে পান খাওয়া, অনুবর্তীদের সঙ্গে কথা কওয়া, ভুরু ও চোখের নানাপ্রকার ভঙ্গিমা ধিক্কারজনক বলে বোধ হয়– নীতির দিক থেকে নয়, রীতির দিক থেকে। আমরা দেখলুম, এই দুটি বালিকার তনু দেহকে সম্পূর্ণ অধিকার করে অশরীরী নাচেরই আর্বিভাব। বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য, বচনকে পেয়ে বসেছে বচনাতীত।”
“এদের সংগীতকে বলা যেতে পারে স্বরনৃত্য, এদের অভিনয়কে বলা যায় রূপনাট্য। ভারতবর্ষ থেকে নটরাজ এসে একদিন এখানে মন্দিরে পূজা পেয়েছিলেন, তিনি এদের যে-বর দিয়েছেন সে হচ্ছে তাঁর নাচটি– আর, আমাদের জন্যে কি কেবল তাঁর শ্মশানভস্মই রইল।’ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৭
কবিগুরু শান্তিনিকেতনে মণিপুরী গানের সুর ও লয়ে শাপমোচন, ঋতুরঙ্গ, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, মায়ার খেলা’য় আরোপ করেন। ১৯৩১ সালে নৃত্যগুরু সোনায়িক সিংহ রাজকুমার, ১৯৩৫ সালে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের নৃত্যগুরু নীলেশ্বর মুখার্জী যোগ দেন। এভাবেই বিশ্বভারতীর শিক্ষার্থীরা নৃত্যে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। যা ভারতবর্ষের মূলসুর ও নৃত্য আঙ্গিক মিলেমিশে নতুন নৃত্য আঙ্গিক সৃষ্টি করেছে। প্রাচ্য প্রতীচ্যের বহু নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শান্তিনিকেতনে নৃত্যধারার নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করেছে। কবিগুরু এই নৃত্য আঙ্গিকের কোন নামকরণ করেননি। অনেকে রবীন্দ্র নৃত্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে এই নৃত্য বিষয়ক ধারাই রবীন্দ্র নৃত্যবিদ্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ঋতু উৎসবে পরিবেশিত নৃত্যে বিশেষ রীতি ও আঙ্গিকের প্রকাশ হয়েছে । বর্ষবরণ, বর্ষামঙ্গল, ধর্মচক্র (বুদ্ধপূর্ণিমা), বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, পৌষমেলা, মাঘোৎসব, বসন্তোৎসব, খৃস্টোৎসব, গান্ধীপুণ্যাহ, রবীন্দ্রজন্মোৎসব ইত্যাদি উৎসবে নৃত্য গীতের স্বতন্ত্র রীতি রূপ, যা কবিগুরুর নৃত্যবিদ্যা হিসেবে বিশ্বের নৃত্য আঙ্গিকে শক্তিশালী সংযোজন বলা যায়।
কবিগুরুর সংগীতে নৃত্যের তাল লয় অভূতপূর্ব দ্যোতনা সৃষ্টি করে। এই আঙ্গিক কখনো কাথিয়াবাড়ীর চাষীর মেয়ের মন্দিরা নিয়ে, কখনো প্রকৃতির অনুষঙ্গে, দক্ষিণ ভারতের লোকনৃত্যে, মারাঠি পদ অনুসারে, কখনো বাউলের নাচে, কখনো কীর্তন রীতিতে, কখনো পাশ্চাত্যের আঙ্গিকে, যা মিলে মিশে স্বতন্ত্র আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে।
শান্তিনিকেতনে নৃত্যচর্চা নিয়ে শান্তিদেব ঘোষের কতিপয় আলোচনা তুলে ধরা হলো, যা কবিগুরুর নৃত্যবিদ্যা বিষয়ক ধারা ও ভাবনা বলা হয়।
১. ” শান্তিনিকেতনে গুজরাতের গরবা নাচের প্রবর্তন করেন বিশ্বভারতীর ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভকিলের পত্নী। এই যুগে ভকিল-পত্নী ১৫-১৬ জন ছাত্রীকে গরবা নাচ শেখান।… সেই গান ক’টি হলো– ‘ যদি বারণ কর তবে গাহিব না’, ‘মোর বীণা ওঠে’, ‘কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে।’
২. ‘ ফাল্গুনীতে বাউল হয়ে অনেকগুলি গানে তিনি নাচের ছন্দ ফুটিয়েছিলেন। গানের সঙ্গে দল বেঁধে আনন্দে নাচত ঐ-সকল নাটকে (শারদোৎসব, অচলায়তন, ফাল্গুনী)।
৩. ‘নটীর পূজা’য় মণিপুরী নাচের সম্ভাবনায় উৎসাহিত হয়ে ১৯২৭ সালে গুরুদেব ‘নটরাজ’ গীত-কাব্যের আসর বসালেন দোল-পূর্ণিমার রাত্রে।… এইবারে প্রথম মণিপুরী নৃত্যাভিনয়-ধারা এই গীত-কাব্যে প্রধান অংশগ্রহণ করল।’
৪. কলকাতায় তামিলের দেশের নৃত্যাভিনয়ের রীতি ‘ঋতুরঙ্গে’ পরিবেশন করে দক্ষিণী ছাত্র।
৫. “১৯৩০এর মার্চ মাসে গুরুদেব তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূসহ বিলেতে রওনা হলেন। ইংলন্ডের ডেভনশায়ারে তাঁর ভক্ত মিঃ এলমহার্স্ট-প্রতিষ্ঠিত ‘ডার্টিংহান হল’ বিদ্যালয়ে তাঁরা কিছুদিন বাস করেন। সেখানে তাঁরা ইধষষবঃ নাচ শেখেন। প্রতিমা দেবী এই বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা নৃত্য-পরিচালকের ইধষষবঃ নৃত্য পরিকল্পনা, প্রতিদিনের কাজ ও ইধষষবঃ রচনার করণ-কৌশল অনুশীলন করেন।”
৬. “‘নবীনে’ মণিপুরী নাচের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাংলার বাউল, রাইবেশে ও ইউরোপের হাঙ্গেরী দেশের লোকনৃত্য ছিল আরো একটি প্রধান বিশেষত্ব¡। এই-সব নৃত্যপদ্ধতিকে নানা গানে খুব ভালোভাবেই খাপ খাওয়ানো হয়েছিল।”
৭. শান্তিনিকেতনে জার্মানি, হাঙ্গেরি, রাশিয়ার নৃত্য পদ্ধতির চর্চা তুলে ধরা হয়েছে।
৮. “ব্যালে-তে নাচ গড়ে ওঠে সবসময় যণÍ্র-সংগীতের সাহায্যে। কিন্তু এখানে নাচ আবৃত্তিকথা ও গানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। ইউরোপীয় নৃত্য-পদ্ধতি ও দেশী নাচের ঢঙ উভয়েই পাশাপাশি এতে কাজ করেছে।”
৯. “১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে রচিত ‘চিত্রাঙ্গদা’ ‘শ্যামা’ ও পরবর্তীকাললের ‘চ-ালিকা’ নৃত্যনাট্যের মূলে ঐ একই ইতিহাস জড়িত। প্রত্যেকবার একই নামের ব্যালে-আদর্শে পরিকল্পিত নৃত্যাভিনয়কে পরিপূর্ণ গীতনাটকে রূপান্তরিত করে তবে নিশ্চিন্ত হন।”
১০. “গুরুদেব একদিকে প্রাচীন আদর্শে ভারতীয় নৃত্যে যুগ-প্রবর্তক, অপর দিকে তিনি সকলের চেয়ে অতি আধুনিক।”
(রবীন্দ্রসংগীত- শান্তিদেব ঘোষ)
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যরীতির নৃত্যবিদ্যা প্রাচীন ভারত, ইউরোপীয় রীতির সাথে নতুন ধারার নৃত্য-পদ্ধতি প্রর্বতিত হয়েছে। তিনি যে শান্তিনিকেতনকে সর্বজাতিক মিলনকেন্দ্রের কথা ভেবেছিলেন, তা বাঙালির সংস্কৃতি পুর্নগঠনের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী হয়েছে। আদি ঐতিহ্যের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করে বাঙালির সাধনায় তা এক অনন্য গৌরবের অধ্যায় সৃষ্টি করে। সমগ্র বাস্তবতায় কবিগুরুর নৃত্য যেন ভারতবর্ষের সাথে বাঙালির সামগ্রিক প্রকাশ ঘটিয়েছে।
কবিগুরুর ভাষায় বলতে হয়, ‘বাঙালির যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, শাশ্বত, যা সর্বমানবের বেদীমূলে উৎসর্গ করবার উপযুক্ত, তাই আমাদের বর্তমানকাল রেখে দিয়ে যাবে ভাবীকালের উত্তরাধিকাররূপে।’ কবিগুরুরর নৃত্যবিদ্যা সম্পর্কে এই কথাটি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য।#