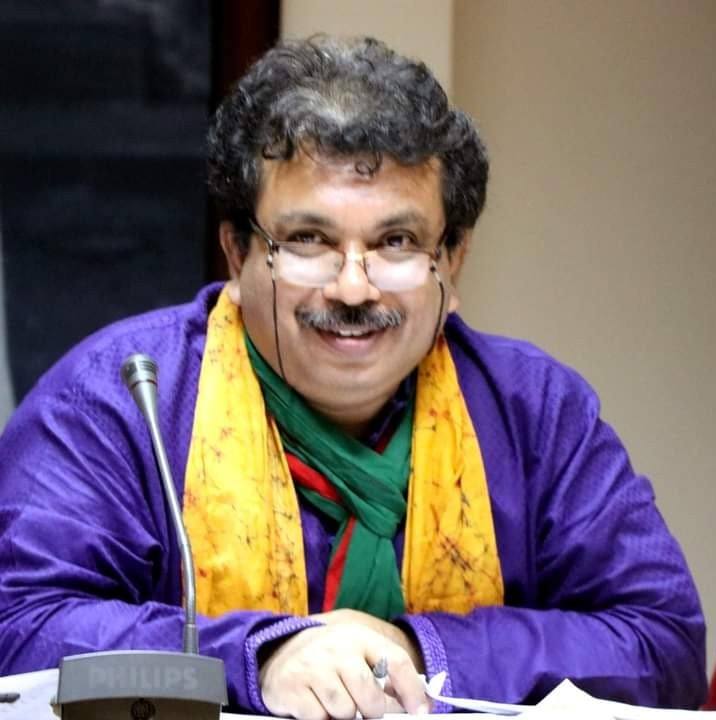“একবার ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে দেখুন- এমন একদিন এসেছিল, যখন বাঙ্গালী হিন্দুর আঁধার ঘরে আলোক এসে উঁকি মারলে, তখন তাঁরা চোখ খুললেন; পরে পাখির কলরব শুনে বুঝতে পারলেন, “আর রাত্রি নাই ভোর হইয়াছে” তখন তাঁরা অলস শয্যা ত্যাগ ক’রে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু হিন্দু উঠে যাবেন কোথায়? – এটা করলে জাতি যায়, সেটা খেলে জাতি যায়; সুতরাং তাঁরা দলে-দলে খ্রীষ্টান হতে আরম্ভ করলেন- ক্রমে বন্দ্রোপাধ্যায় নাম বদলে “ ব্যানার্জ্জী” হলেন, আর সরকার হলেন, “সিরকা”। সেই ঘোর সঙ্কটের সময়ে রাজা রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি সমাজ-হিতৈষী লোকেরা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রবর্ত্তন ক’রে হিন্দুকে সবংশে খ্রীস্টান হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। তখন তাঁদের নিজের স্কুল, কলেজ হ’ল, – তাঁদের ছেলেমেয়েরা আর খ্রীস্টানের স্কুলে পড়তে যায় না।। তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রক্ষা পেলেন।
অপর দিকে মোসলেম সমাজ যখন “ঝোঁপড়ী মে শুয়ে মহলের খাব” দেখছিলেন, সেই সময়ে আলোক এসে মোসলেমের ঝোঁপড়ীর ভাঙ্গা চালের ভিতরও উঁকি মারলে। তখন তাঁরা আর কেবল “ পন্দেনামা” আর “শাহনামা” পাঠ করেই তৃপ্ত থাকতে পারলেন না, – তাঁরা ছুটলেন হিন্দু আর খ্রীস্টানের স্কুলে। তাঁরা কিন্তু নিজেদের স্কুল কলেজ কিছুই করলেন না। তারা খ্রীষ্টানের কলেজের লেখা-পড়া শিখে দিব্যি সাহেব হয়ে গেলেন, – বলেন বিলাতি বুলি; চাকরকে বলেন বেহারা, আর মুটিকে বলেন কুলী।”
(ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ, বেগম রোকেয়া)
বেগম রোকেয়ার (১৮৮০-১৯৩২) ভাবনার জগৎ সংস্কার মুক্ত যুক্তিবোধের দ্বারা স্বমহিমায় উদভাসিত হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর লেখায় দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ‘মানববাদ ও যুক্তিবাদ’ উঠে এসেছে। পনের শতকের পর থেকে পাশ্চাত্যের আদি দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটলের ভাবনার পুর্নজন্ম দিয়ে ইতালিসহ ইউরোপে নতুন ভাবপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে প্রাচীন শিল্পকলা, দর্শন, সাহিত্যসহ বিদ্যাচর্চার নবদিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে। প্রাচীন সভ্যতার পুনর্জাগরণে পাশ্চাত্যের যে প্রবাহ তার জ্যোতি এসেছিলো ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে এবং ইউরোপীয় প-িতদের গবেষণার নানা আয়োজনে। লক্ষ্য করা যায়, ১৭৮৪ সালের জানুয়ারিতে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই সোসাইটির মাধ্যমে প্রাচ্য বিদ্যা, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ভূগোল, প্রত্ন সহ নানাবিধ গবেষণা অব্যাহত থাকে। ১৮০০ সালে স্থাপিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। কোম্পানির ও ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়ে পাশ্চাত্যের পন্ডিত উইলিয়ম জোন্স, জেমস প্রিন্সেপ প্রমুখ ভারতের সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম, প্রাকৃতিক সম্পদ, আর্য়ুবেদ, প্রত্ন নিদর্শনসহ বিবিধ আবিষ্কারে মনোযোগী হন। এইসময় বাঙালি বা ভারতীয় কোন পণ্ডিত তাঁদের গবেষণা কর্মে, সোসাইটিতে সভ্য ছিলেন না। কিন্তু সেই সময় বহুভাষাবিদ রামমোহন রায়ের আর্বিভাবের ফলে যুগান্তকারী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তিনিই ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র অনুবাদ, পত্র পত্রিকা প্রকাশ, হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান ধর্মের মূল বাণীতে সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি, শিক্ষা, সতীদাহ প্রথা বিলোপ, নাগরিক অধিকার, যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভিত্তি স্থাপন করেন। পাশ্চাত্যের ভাবনায় সমাজ সংস্করণে মাধ্যমে ভারতবর্ষে নবজাগরণে রাজা রামমোহন রায় অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। পাশ্চাত্য বোধ, দর্শন, চিন্তার প্রতিফলনে বিশ্বব্যাপি যে জাগরণ, সেই জাগরণকে তিনি ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন । সামাজিক সংস্কার, ধর্ম সংস্কার, নারীর শিক্ষা, অধিকার প্রতিষ্ঠা, কুসংস্কার প্রতিরোধে তাঁর যুগান্তকারী পদক্ষেপের যে বিশাল বিস্তৃত ধারা বাহিত হয়েছিলো, সেই নব জাগরণের ধারার মহান মনীষী ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখের অবদান স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিশেষ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃজনশীলতা, কর্মপন্থা, ভাবাদর্শ শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বে নব জাগরণের বৃহৎ পথ সৃষ্টি করেছে। কবিগুরুর বিশাল ব্যাপ্তির সময়কালে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের জীবনকাল অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর আয়ুষ্কালে “প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্তই অল্প, মাত্র পাঁচটি: ‘মতিচূর (প্রথম খণ্ড, ১৯০৪), ‘ Sultana’s Dream (১৯০৮), ‘মতিচূর’ (দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২২), ‘পদ্মরাগ’ (১৯২৪) এবং ‘ অবরোধ-বাসিনী’ (১৯৩১)। সাহিত্যকর্মের বাইরে তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি কাজ- ১৯০৯ সালে ‘সাথাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল’ প্রতিষ্ঠা আর ‘আনজুমানে-খাওয়াতীন ইসলাম’ নামে একটি সংগঠনের স্থাপনা। বাংলা ও ইংরেজি রচনা, স্কুল প্রতিষ্ঠা, নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা-বেগম রোকেয়ার এই সমস্ত কর্মকা-ের লক্ষ্য ছিল নারীর জাগরণ, পুরুষের সমান নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা।” (নতুন সংস্করণের ভূমিকা, রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ফাল্গুন ১৪০৫/মার্চ ১৯৯৯)
বেগম রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্যের বিস্তৃত গবেষণা লক্ষ্যযোগ্য হয়নি। তবে বাংলা একাডেমির নতুন সংস্করণে অগ্রন্থিত গ্রন্থাবলী, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা, অসংখ্য পত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। সেইসব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বেগম রোকেয়ার সৃষ্টি সাধনা ও কর্ম সাধনা উনিশ শতকের পাশ্চাত্য বোধের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সমাজের কুসংস্কার রোধে, শিক্ষার বিস্তার, সামাজিক ভাবনায় তাঁর সমস্ত সৃষ্টিসম্ভার অনন্য সামাজিক জাগরণের প্রতিফলন সৃষ্টি করে। সমাজে পিছিয়ে পড়া মুসলিম নারী জাগরণের অব্যাহত প্রচেষ্টায় তিনি সমাজকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে তৎকালীন ভারতীয় সমাজের চালচিত্র উঠে এসেছে।
কোন কোন সমালোচক বলতে প্রয়াসী হয়েছেন, রবীন্দ্র যুগে তাঁর আর্বিভাব হলেও গুরুদেবের সাহচর্যে তিনি পৌঁছাতে পারেননি। রবীন্দ্র সাহিত্যের সাথে আদৌ কি তিনি পরিচিত ছিলেন? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিলো কিনা জানা যায় না। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য কর্মের সাথে তাঁর পরিচয় ও চর্চা ছিলো। বেগম রোকেয়ার বিভিন্ন লেখায় সেইসব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।
“আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, ভারতবর্ষ হেন দেশে যদি সকলে চক্ষু হইতে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের আবরণ উন্মোচন করিয়া ন্যায়চক্ষে দৃষ্টিপাত করতঃ চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে “ আমরা প্রকৃতপক্ষে একই প্রভুর উপাসনা বিভিন্ন প্রণালীতে করিতেছি- একই প্রভুকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ও ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকিতেছি।”
“পুরাও পুরাও মনস্কাম,-
কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম
জগতের ভাষাহীন ভাষা?’ –
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
“সকলে তাঁরে ডাকে,
আমি যাঁরে ডাকি,-
রাঙ্গা রবি নিয়া বুকে ঊষা ডাকে সোণামুখে
শ্যাম ছটা মাখি।”-
মানকুমারী দেবী
(মতিচূর: দ্বিতীয় খণ্ড)
বিভিন্ন ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনায় তাঁর দৃষ্টির উদারতা বিস্ময়কর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রবীন্দ্র ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে দেখা যায়- “ বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন-ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্য ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে- স্বস্থানে সকলেরই মাহত্ম্য সে দেখিতে পায়।
ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃস্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে লড়াই করিয়া মরিবে না- এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে।”
কবিগুরুর ভাবনার প্রতিফলন বেগম রোকেয়ার লেখায় পাওয়া যায়- “অন্যান্য দেশেও বিভিন্ন ধর্ম্ম এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবিশ্বাসী লোক আছে, কিন্তু ভারতবর্ষ এই আদর্শের অদ্বিতীয় দেশ- ইহার তুলনা এ ভারত নিজেই। এ দেশে এত স্বতন্ত্র ধর্ম্ম এবং এত পৃথক বিশ্বাসের লোক বাস করে যে, মনে হয় যেন ভারতবর্ষে সমস্ত ধর্ম্ম-মত-সমূহের প্রদর্শনী ক্ষেত্র। এবং এই দেশ সেই স্থান, যেখানে পরস্পরের একতা, মিত্রতা এবং সহানুভূতির মধ্যে ধর্ম্মেও সেই আদর্শ- যাহাকে আমি ইতঃপূর্ব্বে বাঞ্ছনীয় বলিয়াছি – পাওয়া যাইতে পারে।
একের দুঃখে অপরে দুঃখিত হইবে-সমুদয় ভারতবাসী একই জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে। অধিকিন্তু জগতের বড় বড় শক্তিপুঞ্জ ভারতসন্তানকে একজাতি বলিয়া জানিবে।” (মতিচূর: দ্বিতীয় খণ্ড)
বেগম রোকেয়ার প্রখর দৃষ্টিভঙ্গি রেনেসার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সমাজে পশ্চাৎপদ নারীর জাগরণের জন্য শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীকে ‘ভগিনী’ সম্বোধন করে প্রবন্ধ, অনুবাদসহ বিভিন্ন সাহিত্য সৃজনে, বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন। ‘নারী-সৃষ্টি’ একটি পৌরাণিক উপাখ্যানের অনুবাদ। গল্পের অনুবাদের মূল লক্ষ্য নারী সচেতনতা সৃষ্টি।
নারী সমাজের জাগরণের পাশাপাশি বঙ্গভূমির উন্নতির বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধে লিখেছেন। সেখানেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। “আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, – তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়াছেন, “ধান্য তার বসুন্ধরা যার।” তাই ত অভাগা চাষা কে? সে কেবল “ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরিবে,” হাল বহন করিবে, আর পাট উৎপাদন করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে, “মরাই-ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, উঠান ভরা মুরগী ছিল,” এ কথার অর্থ কি? ইহা কি শুধুই কবির কল্পনা? না, কবির কল্পনা নহে, কাব্য উপন্যাসও নহে, সত্য কথা। পূর্ব্বে ওসব ছিল, এখন নাই। আরে! এখন যে আমরা সভ্য হইয়াছি! ইহাই কি সভ্যতা? সভ্যতা কি করিবে, ইউরোপের মহাযুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, তা বঙ্গীয় কৃষকের কথা কি?
আমি উপযুক্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না, কারণ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ ত এই সাত বৎসরের ঘটনা। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কি চাষার অবস্থা ভাল ছিল?”
বেগম রোকেয়া কৃষকদের অবস্থার নানা চিত্র, উদাহরণ সহযোগে তাদের দূরাবস্থা তুলে ধরেছেন।
“এ কঠোর মহীতে
চাষা এসেছে শুধু সহিতে;
আর মরমের ব্যথা লুকায়ে মরমে
জঠর-অনলে দহিতে।”
তিনি সভ্যতার টানাপোড়নে দূরাবস্থার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইংরেজদের আগমনের আগে গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলো। কৃষক রমণীরা চরকায় সূতা কেটে কাপড় তৈরি, এণ্ডি রেশমের পোকা প্রতিপালন, টেকো হাতে সূতা কাটাসহ বস্ত্র শিল্পে অনন্য অবদান রেখেছে। “সেকালে রমণীগণ হাসিয়া খেলিয়া বস্ত্র-সমস্যা পূরণ করিত। সুতরাং তখন চাষা অন্নবস্ত্রের কাঙাল ছিল না” তিনি প্রতিকারের উপায় চিহ্ণিত করে কার্যকর পদক্ষেপের জন্য আহবান জানিয়েছেন।
“সুখের বিষয়, সম্প্রতি পল্লীগ্রামের দুর্গতির প্রতি দেশবন্ধু নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কেবল দৃষ্টিপাতই যথেষ্ট নহে; চাষার দুক্ষু যাতে দূর হয়, সেজন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিতে হইবে। আবার সেই “মরাই-ভরা ধান, ঢাকা মসলিন” ইত্যাদি লাভ করিবার একমাত্র উপায় দেশী শিল্প- বিশেষতঃ নারী শিল্পসমূহের পুনরূদ্ধার।” (চাষার দুক্ষু, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ)
বিস্মিত হতে হয়, বেগম রোকেয়া সমাজের গভীরে দূরবস্থা চিহ্নিত করে তার সমাধানে পরামর্শ দিয়েছেন। সেসব প্রবন্ধসমূহ হচ্ছে- এণ্ডি শিল্প, সিসিম ফাঁক, দজ্জাল, নারী-পূজা, কূপম-ুকের হিমালয় দর্শন, রসনা পূজা, ঈদ-সম্মিলন, আশা-জ্যোতিঃ, কাটা মুণ্ড কথা কয়, রাঙ ও সোনা, বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতিতে সভানেত্রীর ভাষণ, লুকানো রতন, রানী ভিখারিনী, উন্নতির পথে, বেগম তরজীর সাথে সাক্ষাৎ ( উর্দ্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ), সুবেহ্ সাদেক, ৭০০ স্কুলের দেশে, ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম, হজ্বের ময়দানে, বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল (সফল স্বপ্ন), গুঁলিস্তা, কৌতুক-কণা, নারীর অধিকার ইত্যাদি। এসব প্রবন্ধে সমাজের অসংলগ্ন বিষয়াদি উঠে এসেছে। আশ্বর্য হতে হয়, তিনি এসব প্রবন্ধে বহু লোক সংস্কৃতির উপাদান, উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। মুসলিম নারীর জাগরণের সাথে সকল নারীর জাগরণ, সমাজ সংস্কার, সমাজের বৈপরীত্য, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশ্ব সংকটের কথা বলেছেন।
‘পদ্মরাগ’ উপন্যাসের নিবেদন অংশে সমাজ বীক্ষণের যে দৃষ্টি, তা নব জাগরণের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করা যেতে পারে। “ ধর্ম্ম একটী ত্রিতল অট্রালিকার ন্যায়। নীচের তলে অনেক কামরা, হিন্দু- ব্রাহ্মণ, শুদ্র ইত্যাদি বিভিন্ন শাখা; মুসলমান,- শিয়া, সুন্নী, হানাফী, সাফী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়; ঐরূপ খ্রীস্টান,- রোমান-ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, ইত্যাদি। তাহার উপর ত্রিতলে উঠিয়া দেখ,- একটী কক্ষ মাত্র, কামরা বিভাগ নাই, অর্থাৎ মুসলমান, হিন্দু, কিছুই নাই- সকলে একপ্রকার মানুষ এবং উপাস্য কেবল এক আল্লাহ। সুক্ষ্মভাবে ধরিতে গেলে কিছুই থাকে না- সব ‘নাই’ হইয়া কেবল আল্লাহ থাকেন।”
এইতো একেশ্বরবাদের ভাবনা। একমেবাদ্বিতীয়াম।
বেগম রোকেয়া সমাজ সংস্কারকের মতো একদিকে লিখেছেন, অপরদিকে সেসবের প্রতিষ্ঠা দেবার প্রত্যাশায় বিদ্যালয়, সংগঠন গড়ে তুলেছেন। স্বল্প সময়ের জীবনে ‘ মতিচূর’ ১ম ও ২য় খণ্ড, ‘Sultana’s Dream, ‘পদ্মরাগ, অবরোধ-বাসিনী, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ, কবিতা, পত্রাবলী, ছোটগল্প, রস-রচনাসহ সকল সৃষ্টিকর্মে যুক্তিনিষ্ঠ প্রাঞ্জল ভাষায় রাষ্ট্র, সমাজে ন্যায্য অধিকার প্রবর্তনের বক্তব্য ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে নারীর মর্যাদা, সমতার লক্ষ্যে নারী সমাজের জাগরণে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাচ্যে নারীর অধিকার নিয়ে ইংরেজিতে লেখা, ১৯০৮ সালে প্রকাশিত ‘Sultana’s Dream, বাংলায় লেখিকাকৃত অনুবাদ, ‘সুলতানার স্বপ্ন’, একটি ব্যঙ্গরসাত্মক সৃষ্টিকর্ম। “ রোকেয়ার ‘Sultana’s Dream- এ স্বাধীন স্বনির্ভর নারী-সমাজের যে রম্য fantastic কল্পচ্ছবি ধ্যানদৃষ্টিতে তুলে ধরা হয়েছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে পরবর্তীকালে Anthony M. Luovic-র লেখা Lysistra, or Woman’s Future and Future Woman পুস্তকের প্রতিপাদ্য ভবিষ্যৎ নারীজীবনের দৃশ্যাবলী। তা থেকেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রোকেয়া ছিলেন সুদূরদষ্টির অধিকারিণী।” (গ্রন্থ-পরিচয়, মাঘ, ১৩২৮, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, রোকেয়া রচনাবলী)
২. বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা কবি খনা, তাঁর লেখা মুখে মুখে কাল অতিক্রম করেছে খনার বচন হিসেবে। দ্বিতীয় কবি রামী বা রজকিনী, তৃতীয় মাধবী, চতুর্থ কিশোরগঞ্জের চন্দ্রাবতীকে মনে করা হয়। এভাবে যদি দেখি নারী লেখক সমাজের শক্তিশালী একটি ধারা আছে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় সে ধারা শক্তিশালী হয়ে দেদীপ্যমান। সেসব ধারায় কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) , স্বণর্কুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩), প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৪) ….এরকম বহু নারী কবি সাহিত্যিক ইতিহাসে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তবে বেগম রোকেয়াকে (১৮৮০-১৯৩২) নারী জাগরণের ক্ষেত্রে পথিকৃত বলা হয়।
বিশ্বের ইতিহাসে দেখা যায়, আদি ভূখ- ভারতের ‘ বঙ্গ-রাঢ়-পুণ্ড্র-গৌড়’ কোমে কিংবা ‘পুন্ড্রু-গৌড়-তাম্রলিপ্তি-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল’ ইত্যাদি অখণ্ড ভৌগোলিক সীমায় বৈদিক যুগের প্রবাহ দীপ্যমান আছে। আদি প্রাচ্যে ৩০ জন ঋষি নারীর কথা জানা যায়। বহুকাল সময় প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধর্মের আগমন, বহু শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা, রাষ্ট্র, সমাজের উদ্ভব ঘটে। যার পরিচালনায় ছিলেন পুরুষরা। আর নারীদের গৃহকর্ম, সন্তান উৎপাদনের জন্য দাসতুল্য করে রাখা হয়। এমনকি, যুদ্ধের পর বিজিতদের দ্বারা নারীরা সর্বোচ্চ পীড়নের শিকার হন। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নারীর বিষয়ে ফরাসী দার্শনিক জঁ জ্যাক রূশো তাঁর এমিলি (১৭৬২) গ্রন্থে নারীর সমানাধিকার সমর্থন করেন। ‘ Man is born free but everywhere he is in chains. মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, কিন্তু সমাজ তাকে শৃঙ্খলিত করে।’ বিশেষ করে ‘লা কস্তা সোসিয়েল’ গ্রন্থে ‘জনতার অধিকার রয়েছে বিপ্লবের দ্বারা রাজতন্ত্রের পতন ঘটানো’ মর্মবাণী, যা অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নারীদের উৎসাহিত করে। এই উদ্দীপনা ফরাসী বিপ্লবের ( ১৭৮৯-১৭৯৯) মূল প্রতিপাদ্য-, Liberte, E’galite, Fraternite’, ou la mort; স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ব অথবা মৃত্যু। ‘ফরাসীর পউলিন লিয়ন (২৮ সেপ্টেম্বর ১৭৬৮– ৫ অক্টোবর ১৮৩৮) এবং থেরওয়ান দ্য মেরিকুয়ো (১৩ আগস্ট ১৭৬২–৯ জুন ১৮১৭), তারা নারীর পূর্ণ অধিকার নিয়ে আন্দোলন করেন। ১৭৯২ সালের ৬ মার্চ ৩১৯ নারীর স্বাক্ষর নিয়ে জাতীয় সভায় আবেদন পত্র দেয়া হয়। যার মূলকথা ছিল-নারী অনুশীলন, প্যারিস রক্ষার জন্য নারী রক্ষী বাহিনী গঠন। সেই আবেদন বাতিল করা হলেও নারীরা থেমে থাকেননি। ১৭৯২ সালে নারীনেত্রী মেরিকুয়ো নারী সৈন্যবাহিনী গঠনের আহবান জানান। তারা গড়ে তোলেন ১৭৯৩ সালে ১০ মে Society of Revolutionary Republican Woman সংগঠন। এই সংগঠনের মাধ্যমে খাদ্য শস্যের অবৈধ মজুত ও মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ, নারীর পূর্ণ অধিকার নিয়ে আন্দোলন এবং সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হন। ১৭৯৩ সালের ৩০ অক্টোবর সংগঠনকে সরকার বিলুপ্ত করে। সকলকে ভৎর্সনা, তিরস্কার, প্রকাশ্যে আঘাত করা হয়। আর মেরিকুয়োকে আজীবন কারাগারে আটকে রাখা হয়। ইতিহাসের এই মহান নারী বিপ্লবীর কারাগারে নির্যাতন, মানসিক পীড়নে অকাল মৃত্যু হয়েছিল।
কলকাতায় নারী সমাজের মুক্তির পথে রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবাদের অবস্থা উন্নয়নে বিধবা বিবাহের পুর্নবিবাহের আইন পাশ হয়। নারী শিক্ষার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বিশ্বব্যাপী নারী জাগরণের জন্য নারী, পুরুষ লেখকরা এগিয়ে আসেন। রূশ লেখক আলেক্সজান্দার পুশকিন (৬ জুন ১৭৯৯–১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭) নারীর সমতা নিয়ে লেখেন। বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের নিউইয়র্কে কারখানার নারী শ্রমিকদের বিক্ষোভ বিশ্বকে নাড়া দেয়। ব্রিটিশ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল ১৮৬১ সালে লেখেন এবং তা প্রকাশ করেন ১৮৬৯ সালে ‘দ্য সাবজেকশন অব উইমেন’ নামে। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ভোটাধিকার প্রাপ্তি ঘটে নিউজিলান্ডে ১৮৯৩ সালে, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় ১৮৯৫, অস্ট্রেলিয়ায় ১৯০২। তবুও বিশ্বের বহু দেশে নারীর সমতা, অধিকার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা পায়নি। আর এই সময় জার্মানির সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন ( ৫ মে ১৮৫৭–২০জুন ১৯৩৩)-এর নেতৃত্বে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ সালে নিউইয়র্কে ঘটে যায় ঐতিহাসিক নারী সম্মেলন। সেখানে মজুরি বৈষম্য, কাজের অমানবিক পরিবেশ বিলোপ, কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করার দাবী উত্থাপিত হয়। ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে ১৭ টি দেশের ১০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা দেন। ১৯১৪ সাল থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ ৮ মার্চ নারীদিবস হিসেবে পালন করে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র গৃহিত হয়।
ভারতে ১৯২৭ সালে পুণেতে অনুষ্ঠিত হয় All India Women Conference. তবে তার আগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে বাঙালি নারী লেখক, সংগঠক স্বর্ণকুমারী দেবীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল যোগ দেন। ১৯৩৫ সালে ক্যালকাটা কাউন্সিল হাউসে বেগম রোকেয়ার উত্তরসূরী শামসুন নাহার মাহমুদ ( ১৯০৮-১৯৬৪)-এর নেতৃত্বে ভোটাধিকারের প্রস্তাব দেয়া হয়। বহুদেশে নারীর মর্যাদা, ভোটাধিকার প্রয়োগ বিভিন্ন সময়ে হলেও ভারতে ১৯৩৬ সালে, যুক্তরাজ্যে ১৯১৮, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০, কানাডায় ১৯১৭, নরওয়ে ১৯১৩, স্পেনে ১৯৩১, ফ্রান্সে ১৯৪৪, ইতালিতে ১৯৪৬, লাতিন আমেরিকায় ১৯৪০ দশকে দেয়া হয়। মুসলিম দেশ সৌদি আরবে নারীরা ২০১৫ সালে পৌরসভায় ভোটাধিকার পায়। এ এক দীর্ঘ ইতিহাস। ১৯৭৫ সালের পর থেকে জাতিসংঘের দেশসমূহ বিশ্ব নারীদিবস পালন করছে। বিশ্বে যুগ যুগ ধরে মানব শান্তি, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পুরুষ ও নারীর সম অধিকার অপরিহার্য। বেগম রোকেয়া সেই কাজটি দক্ষতার সাথে করেছেন।
পৃথিবীর নারী আন্দোলন ও জাগরণের সাথে বাংলায় বেগম রোকেয়ার অবদান সমান্তরাল এবং শক্তিশালী। জীবনের নানা প্রতিকূলতায় সাহসের সাথে তিনি কর্মনিবেশ করেছেন। তাঁরই উদ্ধৃতি-
জীবন এমন ভ্রম কে জানিত রে?
“ছিন্ন তুষারের প্রায় বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়
তাপদগ্ধ জীবনের ঝহ্ঝা বায়ু প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত,
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দূর্গ প্রকারে।”
(রোকেয়া রচনাবলী, ৪৯১ পৃ.)
জীবনের সংগ্রামে তাঁর দৃঢ়তা অকল্পনীয়-
“শৈশবে বাপের আদর পাইনি, বিবাহিত জীবনে কেবল স্বামীর রোগের সেবা করেছি। প্রত্যহ থরইন পরীক্ষা করেছি। পথ্য রেঁধেছি, ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি। দুবার মা হয়েছিলুম- তাদেরও প্রাণ ভরে কোলে নিতে পারিনি। একজন ৫ মাস বয়সে, অপরটি ৪ মাস বয়সে চলে গেছে। আর এই ২২ বৎসর যাবত বৈধব্যের আগুনে পুড়ছি। —আমি আমার ব্যর্থ জীবন নিয়ে হেসে খেলে দিন গুনছি। (রো.র, পৃ. ৪৯২)
বিভিন্ন লেখায় লোক সংস্কৃতির প্রচলিত উপাদানের মাধ্যমে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে,-
“মানুষের জীবন দুঃখ ও সংগ্রামে ভরা, তারই মধ্যে দুই এক দিন একটু হাসি খুশি পাওয়া যায়. তাহাই গণিমত ( যথেষ্ট)। বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম:
“হেসে লও, দু’দিন বই ত নয়
আছে তো জীবন ভরা দুঃখ।’
ঘাটশীলা আমাকে যেন তাহাই বলিতেছে:
“হেঁটে লও, দু’দিন বই ত নয়,-
আছে ত কলকাতার বন্দী-খানা।”
(রো,র. পৃ. ৪৯৭)
উনিশ শতকের নবজাগরণের ধারার অনন্য উত্তরাধিকার হিসেবে বেগম রোকেয়াকে পরিগণিত করা হয়। বিশ শতকের সূচনায়, ১৯০২ সালে ‘নবপ্রভা’ নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম লেখা ‘পিপাসা’ প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ সালে কমলা মাতমিয়া নাথান ও সরোজিনী নাইডু’র যৌথ সম্পাদনায় মাদ্রাজের Indian Ladies Magazine পত্রিকায় Sultana’s Dream প্রকাশিত হলে সমাজ সচেতন নারী লেখক হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৮ সালে কলকাতায় গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত ‘Sultana’s Dream’ কলকাতার সুধী সমাজের বিশেষ সমাদর লাভ করে। ১৯০৯ সালে স্বামী প্রয়াত হলে তিনি কিছুদিন ভাগলপুরে স্কুল প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। বহুবিধ কারণে ১৯১০ সালে ভাগলপুর থেকে কলকাতায় এসে বসবাস এবং ১৯১১ সালে কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের’ কার্যক্রম শুরু করেন।
১৯১৬ সালে নারী সমাজের কল্যাণে “আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম’ নামক মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর আমৃত্যু বলিষ্ঠতার সাথে সমাজ সংস্কার, নারী জাগরণ, বিশেষ করে মুসলিম নারীর সচেতনতা সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন, তারমধ্যে- ১৯২৫ সালের ২৬-২৮ ডিসেম্বর, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীতে ‘অল ইন্ডিয়া মহামেডন এডুকেশনাল কনফারেন্সে; ১৯২৭ সালের ১৯ ফ্রেব্রুয়ারি কলকাতায় বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনের চতুর্থ দিবসের অধিবেশনে সভানেত্রী হিসেবে, ১৯৩১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে‘ Educational Ideals for the Indian Girls’ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯৩২ সালের ৮ ডিসেম্বর রাত ১১টায় লেখেন ‘নারীর অধিকার এবং ৯ ডিসেম্বর সকালে সূর্যের আলোর সাথে সাথে তিনি ইহজগত ত্যাগ করেন। মহাপ্রয়াণ হলেও তিনি নবজাগরণের জ্যোতিঃ দ্যুতিতে চির অমর অক্ষয় হয়ে থাকবেন। আর তাঁরই আশা জাগরিত করবে বঙ্গবাসীকে-
জাগো বঙ্গবাসী!
দেখ, কে দুয়ারে
অতি ধীরে ধীরে করে করাঘাত।
ঐ শুন শুন! কেবা তোমাদের
সুমধুর স্বরে বলে: সুপ্রভাত!”
অলস রজনী
এবে পোহাইল
আশার আলোকে হাসে দিননাথ।
শিশির-সিক্ত
কুসুম তুলিয়ে
ডালা ভরে নিয়ে এসেছে “সওগাত”।
(সওগাত, রো.র. পৃ. ৪৫৮)