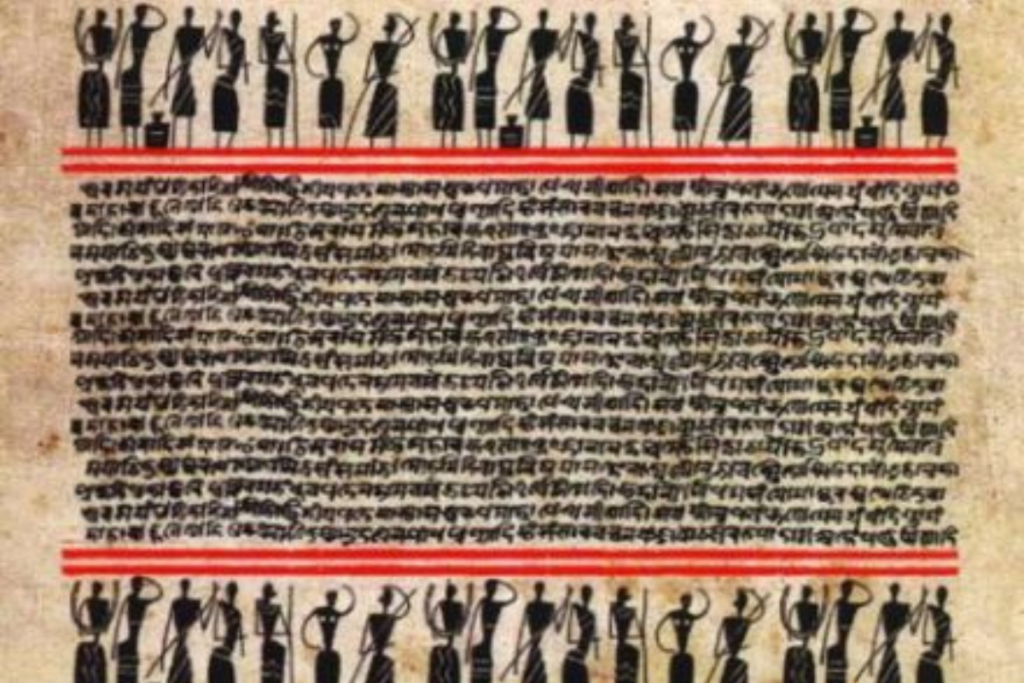দ্বাদশ শতকীয় কবি জয়দেবের কাব্যের ভাব, রস, শব্দঝংকার ও অলংকার নৈপুণ্য পরবর্তীকালের অনেক বৈষ্ণব কবির কাছে অনুসরণীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল। চৈতন্য-পূর্ব যুগে জয়দেব-প্রভাবিত শক্তিমান কবি ছিলেন বিদ্যাপতি। তিনি বাঙালি নন, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বঙ্গসাহিত্যে বিদ্যাপতির স্থান রয়ে গেছে অপ্রতিদ্বন্ধ্বী। মিথিলার রাজা শিবসিংহ তাঁর এই কলানিপুণ সভাকবিকে যে ‘অভিনব জয়দেব’ নামে প্রশংসা করেছিলেন ও ভূসম্পত্তিদানে পুরস্কৃত করেছিলেন তা যথেষ্ট কারণবহ ছিল। মূলত মিলনের কবি, বসন্ত ঋতুর কবি হিসেবে বিদ্যাপতির খ্যাতি। তাঁর লেখা ব্রজবুলির পদ চৈতন্যোত্তর কালের কবিদের খুবই আকৃষ্ট করে। তাঁর সার্থক অনুসরণকারী ছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। বিদ্যাপতির কয়েকটি পদের সম্পূর্ণতা বিধান করেছিলেন ইনি এবং এঁর নির্মিত অংশ মূল পদের সঙ্গে এমনই সঙ্গতিবিধান করেছিল যে পৃথক ভণিতা থাকায় গোবিন্দাদাসের রচনা বলে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। সেই গোবিন্দদাস যেভাবে তাঁর গুরুস্থানীয় বিদ্যাপতিকে বন্দনা জানিয়েছেন একটি পদে তা অতুলনীয়। তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন বিদ্যাপতির সুরভিত কাব্যবাণীর, মধুররসসিক্ত ভাবসম্পদের। শ্রবণসুখকর বিদ্যাপতির পদ যে গোবিন্দদাসকে বিমোহিত করে বৈষ্ণব পদরচনায় প্রণোদিত করেছিল, সে কথাও কবি স্বীকার করেছেন ওই বন্দনা-গীতে। তারই খণ্ডাংশ এখানে উদ্ধৃত করি—
কবি-পতি বিদ্যাপতি মতিমাসে।
লাখ গীতে জগ- চীত চোরায়ল
গোবিন্দ গোরি-সরস-রস-গানে।।
ভুবনে আছয়ে যত ভারতি-বাণী।
তাকর সার সার পদ সঞ্চয়ে
বান্ধল গীত কতহুঁ পরিমাণি।।…
যত যত রসপাদ করলাহি বন্ধে।
কোটি হুঁ কোটি শ্রবণ যব পাইয়ে
শুনইতে আনন্দে লাগয়ে বন্দে।।
একইভাবে অনুবর্তীদের দ্বারা বন্দিত হয়েছেন গোবিন্দদাস কবিরাজও। চৈতন্যোত্তর পর্বের ইনি শ্রেষ্ঠ কবি। ভাবের গভীরতায়, শব্দযোজনার পারিপাট্যে, ছন্দের বৈচিত্র্যে ইনি তাঁর সমকালের ও পরবর্তীকালের কবিদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। শব্দবৈভবে গোবিন্দদাস মহাধনী, আর অভিসারের পদে রাজাধিরাজ। মঞ্জরী ভাবের পদ রচনায় তিনি অনন্য। তাঁর পদে যেন শ্রুত হয় কোকিলের পঞ্চম তাল, ফুটে ওঠে বীণায় গুরুনাদধ্বনি। তাঁকে কেউ কেউ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের পূর্বপিতামহ বলেও প্রশংসা করেছেন, কেননা, বাংলা গীতিকবিতার ছন্দোবৈচিত্র্য ও রচনাবিন্যাস কৌশল নাকি তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর সরস কবিত্বে ও পদঝংকারে মুগ্ধ বল্লভ দাস, নরহরি চক্রবর্তীর মতো অনুজ কবিরা। তাঁকে যে বাঙালি রসিক পাঠক ‘দ্বিতীয় বিদ্যাপতি’ বলে সম্বোধন করে, সে অভিধার সূচনা ঘটিয়েছিলেন বল্লভদাস। গোবিন্দদাসের কাব্য সমালোচনা করে ইনি লিখেছিলেন—
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বন্দিত কবিসমাজ
কাব্যরস অমৃতের খনি।
বাগদেবী যাঁহার দ্বারে, দাসী ভাবে সদা ফিরে
অলৌকিক কবি শিরোমণি।।
ব্রজের মাধুরী লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।।
আর কবি নরহরি চক্রবর্তী প্রশংসা করে জানালেন এই কবি বৈদগ্ধ্যে ও সূক্ষ্মানুভূতির বিশ্বস্ত রূপকার। গোবিন্দদাসের আবেদন প্রথমে মস্তিষ্কে ও অন্তিমে হৃদয়ে—
পরম বিচিত্র কাব্য বিন্যাস কি রচব
সুকৌশল নহু অবগাহ।
তিখিন বাণ সম বেধই হিয় শির ঘুমই
রসিকগণ শুনই উচ্ছাহ।।
বিদ্যাপতির মতো চৈতন্য-পূর্বকালের আর এক শক্তিমান ও জনপ্রিয় বৈষ্ণব পদকর্তা হলেন চণ্ডীদাস। রবীন্দ্রনাথের মতে, তিনি ‘সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি’। এই প্রসাদ গুণে তিনি প্রাচীন কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিদ্যাপতির মতো তিনি বহিরঙ্গের মণ্ডনকলাকে প্রাধান্য দেননি, বরং তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভাবের অতলান্তিক গভীরতা। প্রেমের কঠোর সাধনা তাঁর রাধা চরিত্রে দৃশ্যমান। প্রাণ অপেক্ষা প্রেম তাঁর কাছে মহার্ঘ। সেই প্রেম অবিনাশী ও কামগন্ধহীন। বাঙালির হৃদয়ের ভাষায় তাঁর পদগুলি সংরচিত। সে কারণে তিনি বাংলার প্রাণের কবি হয়ে উঠেছেন। চণ্ডীদাসের পদগুলিতে আত্মানুভূতির চূড়ান্ত প্রকাশ। এঁর পদসমূহের একটি রসতাত্ত্বিক বিচার করেছেন আর একজন পদকর্তা। তিনি কানুরাম দাস। এক অনুজ কবির চোখে আর এক পূর্বজ কবির কৃতিত্ব কীভাবে ধরা পড়েছে তা কানুরামের ত্রিপদীতে স্পষ্ট। চণ্ডীদাসের শিল্পীসত্তার এমন চুলচেরা বিশ্লেষণ সম্ভবত মধ্যযুগের আর কোনো কবিই করেননি। কানুরাম লিখেছেন—
কবিকুলে রবি চণ্ডীদাস কবি
ভাবুকে ভাবুক মনি।
রসিকে রসিক প্রেমিকে প্রেমিক
সাধকে সাধক গনি।।
উজ্জ্বল কবিত্ব ভাষার লালিত্য
ভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে মুখে ভাষা ফুটে
উভয়ে অধীন যেন।।
সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল
প্রসাদ গুণেতে ভরা।
যেই পশে কানে সেই লাগে প্রাণে
শুনামাত্র আত্মহারা।।
আরও পড়ুন: মধ্যযুগের বাংলা কাব্য: মধ্যযুগের কবিদের চোখে ২
বিদ্যাপতির যেমন অনুকর্তা ছিলেন গোবিন্দদাস, তেমনি চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য হলেন জ্ঞানদাস। রূপানুরাগের পদে জ্ঞানদাস অনন্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘সৌন্দর্যই তাঁহার আহ্বান গান’। শব্দের তথ্যসীমাকে অতিক্রম করে কীভাবে সৌন্দর্য স্বরূপের মধ্যে প্রবেশ করতে হয় সেই রহস্য জানতেন জ্ঞানদাস। চণ্ডীদাসের রাধা যেখানে যৌবনে যোগিনী, সেখানে জ্ঞানদাসের রাধা হলেন ভাবময়ী। কবি ছিলেন বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যে প্রকৃত লিরিক প্রতিভার অধিকারী। গাঢ় গভীর অনুভূতি জ্ঞানদাসের পদগুলির মহান ঐশ্বর্য। সেই অনুভূতিকে সংহত ও তীব্র আকারে প্রকাশ করতেই তাঁর শৈল্পিক চরিতার্থতা। রূপ ও রসের সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন ঘটেছে তাঁর পদে। পরবর্তীকালের কবি রাধাবল্লভ জ্ঞানদাসের পদাবলি আস্বাদন করে তাই লিখেছিলেন—
ধন্য ধন্য কবি জ্ঞানদাস।
এ গৌড় মণ্ডলে যার মহিমা প্রকাশ।।
সুধামাখা যার পদাবলী।
শ্রবণে প্রবেশমাত্র মন যায় গলি।।
কবিত্ব-সরণী মাঝে যার।
রসিক সরাল সদা দেয় ও সাঁতার।।
প্রশংসাবাচক সমালোচনা পর্বের ছেদ টানি সপ্তদশ শতকের শেষে আবির্ভূত কবি নরোত্তম দাস (ঠাকুর) সম্পর্কে বল্লভ দাসের অনুকূল্য মন্তব্য দিয়ে। নরোত্তম পদকর্তা ও সুকণ্ঠ কীর্তনীয়া ছিলেন। কীর্তন গানের গরানহাটি রীতির প্রবর্তক বলে কথিত। খেতুরি মহোৎসবের তিনিই মূল উদ্যোক্তা। বল্লভদাসের লেখনীতে নরোত্তম প্রশস্তি এইরকম—
রচিলা অসংখ্য পদ হৈয়া ভাবে গদ গদ
কবিত্বের সম্পদ সে সব।
যেবা শুনে যেবা পড়ে আর যেবা গান করে
সেই জানে পদের গৌরব।।
আরও পড়ুন: ভালবাসার মানুষ টনি মরিসন ৩
এবার আসা যাক প্রতিবাদী সমালোচনার কথায়। কেউ কেউ এমনটাই মনে করেন যে, সমালোচনা মানেই বিরুদ্ধতা তথা ধ্বংসাত্মক আলোচনা। অথচ শব্দটির মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে সমদর্শিতার ব্যঞ্জনা— সম+ আলোচনা, অর্থাৎ নিরপেক্ষ হয়ে দোষ-গুণ নির্ধারণই প্রকৃত সমালোচনা। যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ গ্রন্থে ‘নূতন গ্রন্থের সমালোচনা’ শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, ‘গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক যে সুখলাভ বা যে জ্ঞান লাভ করিবেন তাহা অধিকতর স্পষ্টীকৃত বা তাহার বৃদ্ধি করা, গ্রন্থকার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন সেখানে ভ্রম সংশোধন করা, যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা সাধারণের নিকট প্রতীয়মান করা— এইগুলি সমালোচনার উদ্দেশ্য’। এজন্য সমালোচনায় যেমন থাকা উচিত রসের পরিচয় উদ্ঘাটনের প্রয়াস, তেমনি তার তুল্যমূল্য বিচারও। পশ্চিমি সাহিত্যতত্ত্ব সমালোচকের ভুমিকাকে তিনভাবে দেখা হয়েছে, তিনি হবেন বিবৃতিকার, উপস্থাপক ও ব্যাখ্যাপ্রদানকারী। জর্জ ওয়াটসন নামে একজন সাহিত্যবেত্তা সমালোচনা-প্রকৃতিকে তিনিটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। সেগুলি যথাক্রমে— তাত্ত্বিক(Theoritical, বিচারমূলক (Legislative), ও বর্ণনাত্মক (Descriptive)। এছাড়া সমালোচনার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিগত নানা বৈচিত্র্য আছে; যেমন প্রকরণিক, সংরূপাত্মক, ঐতিহাসিক, জীবনীভিত্তিক, আপ্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক, প্রত্নতাত্ত্বিক ইত্যাদি। কখনো কখনো একই সমালোচক তাঁর জীবনের দুই পর্বে দুই ধরনের মানদণ্ডের কথা বলেছেন। যেমন টি এস এলিয়ট। তিনি প্রথম দিকে বলেছিলেন যে, কাব্যের ব্যাখ্যা এবং রুচির সংশোধনই হল সমালোচনার আসল কাজ। কিন্তু তেত্রিশ বছর পর তিনি আগের ধারণা থেকে সরে এসে জানালেন, কাব্যোপভোগ ও কাব্যোপলব্ধিই হল প্রকৃত সমালোচনা। অন্যদিকে, সমালোচককে যে নির্মোহ হতে হয়। নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে রচনার মধ্যেকার শ্রেষ্ঠত্বকে আবিষ্কার করতে হয়— এমন নিদান হেঁকেছিলেন ম্যাথু আর্নল্ড। নিছক নেতিবাচকতা কোনো সমালোচকের কৃত্য হতে পারে না। অথচ তেমন ব্যাপারই লক্ষ করা গেছে মধ্যযুগের বাংলার কয়েকজন কবির সমালোচনায়। এইসব প্রতিকূল সমালোচনাকে এককথায় পূর্বজ কবির অপবাদ বা নিন্দা বলে অভিহিত করা চলে এবং এগুলির পিছনে কিছু সুষ্পষ্ট কারণও ছিল। সত্যসত্যই কাব্যমূল্যে যেসব সাহিত্য হীন, তাদের কপালে তো কটুবর্ষণই ভবিতব্য। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ঈর্ষাও কাজ করেছে। আবার কেউ কেউ নিজের রচনাকে গৌরবান্বিত করতে অগ্রজ কবির রচনাকে তুলোধোনা করে ছেড়েছেন। সেক্ষত্রে কোনো কোনো কবির আবার সেকালের ধর্মভীরু মানুষের ধর্মভীতিকে কাজে লাগিয়েছেন। কবিদের দেবতা ব্যবহারের নানা অভিমুখ আলোচনা করলে ষ্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কোনো কোনো কবি যুগের চাহিদা, অসুখ ও প্রাণ-প্রবাহের প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামেশ্বর ভট্টচার্য্যের মধ্যে কিছুটা এবং কৃষ্ণরাম দাস ও ভারতচন্দ্রের মধ্যে পুরোটাই এই বোধ পাকা হয়ে উঠেছিল মনে হয়। একই সঙ্গে এটাও অনুমান করি যে, যতই মধ্যযুগের নিশান্ধকার অপসৃত হচ্ছিল, ততই মানুষের মন আধুনিক, যুক্তিবাদী, কৌশলী ও ধর্মবিষয়ে সংশয়ী হয়ে উঠেছিল। হয়তো এই কারণেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রায় শেষ দিকে বেশি পরিমাণ প্রতিবাদী সমালোচনার সাক্ষাৎ লাভ করি আমরা। এইসব কবিরা যে-যুগ মানসিকতায় বিচরণ করেছিলেন, তার নিরিখে পূর্বেকার সাহিত্যভাবনা যে কতটা আলৌকিকতা মণ্ডিত, প্রথানুগ ও কার্যকারণহীন তা সেদিনও তাঁদের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে কম-বেশি ধরা পড়ে গিয়েছিল। এ কারণে এ ধরনের সমালোচনা শুধু সাহিত্যের নান্দনিক তুল্যমূল্যেরই বিচার নয়, একই সঙ্গে কবির জীবনবোধ ও কালের প্রকৃতবোধেরও পরিমাণক। এভাবেই হয়তো একটা সৃষ্টি অন্য সৃষ্টির থেকে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে, বানিয়ে তোলে দু’কালের মধ্যে অদৃশ্য দেওয়াল। কবিদের আধুনিকতা এভবেই চিহ্নিত হয়। শুধু সন তারিখের দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তনেই নয়।
এ কথার অর্থ তাই নয় যে, যাঁরা কাব্য সমালোচনা করেছিলেন তাঁরা সবাই আধুনিক ধ্যান-ধারণার অধিকারী কিংবা তাঁরা মধ্যযুগের মানসিকতার সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কাব্যজগতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁরা সময়ের অভিজ্ঞানে সরে যেতে পারেননি। সাহিত্যগুণ-শূন্য বলে যে-কটূ মন্তব্য বিজয়গুপ্ত হরিদত্তের রচনা সম্পর্কে করেছিলেন, তাঁর ‘পদ্মপুরাণ’ পরবর্তী কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের নিরিখে সেই একই অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারে। তেমনি অলৌকিকতার প্রসঙ্গ তুলে রামানন্দ যতি মুকুন্দের কাব্যকে সমালোচনা করলেও তাঁর চণ্ডীমঙ্গলেও আমরা কম অবাস্তব বিষয় পাই না। আবার কৃষ্ণরাম দাস তাঁর কাব্যের সুপ্রচারের জন্য পূর্বজ মাধবাচার্যের লেখাকে শুধু ‘চাষাভোলানো গীত’ বলে ব্যঙ্গই করলেন না ভীরু পাঠকের মনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকা দেবভীতিকেও কাজে লাগালেন কল্পনার অলৌকিক বাঘ তৈরি করে। আসলে এসবই ছিল মধ্যযুগীয় সীমাবদ্ধ ভাবনার বৃত্তে কবিদের এলোপাথারি পরিভ্রমণ। তবুও এসব সমালোচনার গুরুত্ব আছে, মূল্য আছে সাহিত্যের ইতিহাসের পালাবদলের অধ্যায়ের প্রেক্ষাপটে। কবিরা যে চলমান স্রোতধারায় আত্মসত্তাকে পুরোপুরি সঁপে দেননি, আন্ততপক্ষে সচেতন প্রয়াসে ফিরে তাকাবার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ, এগুলো তারই প্রমাণ, যা নিশ্চিতভাবে অভিনন্দনযোগ্য। পাঠকের সাহিত্যবোধকে তৃপ্ত করার জন্য, সমকালীন সমাজ-বাস্তবকে চিত্রিত করার জন্য, এই যে নিছক প্রতিবাদী কাব্যরচনার ঢঙ, তা সাহিত্যরচনার ইতিহাসকেও নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করে তোলে।
বাংলা সাহিত্যে প্রথম কাব্যোসমালোচনা বোধহয় বিজয় গুপ্তেরই। মনসামঙ্গলের কাহিনি কবে নারীসমাজের লৌকিক ব্রতকথা থেকে পুরুষ সমাজের উপভোগ্য কাহিনিতে পরিণত হল, তা বলা কঠিন। বোধহয় হরিদত্তই ছিলেন এই ব্রত পাঁচালির প্রাচীন ও আদিতম রূপকার। তাঁর গ্রন্থের উল্লেখ কেবল বিজয় গুপ্তের পুথিতেই মেলে। পরবর্তীকালে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ময়মনসিংহের দীঘপাইত গ্রাম থেকে একটি ছিন্ন পুথির পাতড়া আবিষ্কার করেন। তার পাঠোদ্ধার করে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, হরিদত্তের লুপ্তপ্রায় পুথির এটি একটি পৃষ্ঠা হতে পারে। দীনেশ্চন্দ্র সেন তাঁর ‘বঙ্গসাহিত্য পরিচয়’-এ ও পরবর্তীকালে আশুতোষ ভট্টাচার্য সংকলিত ‘বাইশা কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা’-তে ওই পৃষ্ঠাটির পাঠ মুদ্রিত হয়েছে। হরিদত্ত ভাগ্যদোষে কানা ছিলেন। বিজয় গুপ্ত তাঁর এই শারীরিক ত্রুটির উল্লেখ করেছেন। সেইসঙ্গে কাব্যের শ্রী ও সৌষ্ঠব এবং কাব্যত্ব যে-সব বিষয়গুলির ওপর নির্ভর করে হরিদত্তের রচনায় তার যথেষ্ট অভাব লক্ষ করেছিলেন পণ্ডিত (মন্য) কবি বিজয় গুপ্ত। তাঁর এই সমালোচনা একটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। কারণ তিনিই প্রথম কবি যিনি কাব্যকে কেবল ভাবের বিকাশ-মাধ্যম হিসেবে দেখেননি, তার প্রকাশ কলার চারুত্ব বিষয়েও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। হরিদত্তের কাব্য বিষয়ে বিজয় গুপ্তের অভিমতটি এইরকম—
সর্ব্বলোকে গীত গাহে না বোঝে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।।
হরিদত্তের গীত যত লোপ্ত পাইল কালে।
যোড়াগাঁথা নাহি কিছু ভাণ্ডে বোলচালে।।
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাহিতে আর গাহে নাহি মিত্রাক্ষর।।
বোঝা গেল, অনুপ্রাস-শূন্যতা, ঘটনার পারম্পর্যহীনতা ও গীতিধর্মিতার অভাবই ‘হরিদত্তের গীত যত ক্ষেপ্ত’ হওয়ার কারণ। কিন্তু তিনি যখন কাব্যাংশের শেষভাগে তাঁর প্রতি মনসার আদেশের কথা উল্লেখ করেন, তখন অনুমান হয়, পূর্বজ কবির কাব্যপ্রতিভা ও কবি-মর্যাদাকে নস্যাৎ করার এটি একটি অপকৌশল মাত্র। তবুও তিনি যে সাহিত্যের মৌল ভাবনা নিয়ে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন একথা ভুললে চলবে না। যে-যুগে কাব্যকালাকে ধর্মেরই অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিবেচনা করত সকলে, সে যুগের বুকে দাঁড়িয়ে এই কবিকেই বলতে শুনি, ‘সর্ব্বলোকে গীত গাহে না বোঝে সাহিত্য’। এ উক্তি সাহিত্যস্রষ্টার ভাবনা পরিধিকে খুব স্পষ্টভাবেই চিহ্নিত করে দেয়।
চলবে…