বাংলা কবিতার মতো বৈচিত্র্য বিশ্ব সাহিত্যেও আছে কিনা জানি না, তবে বিশ্ব সাহিত্যের প্রেরণা নিয়ে বাঙালি কবিরা যথেষ্টই সমৃদ্ধ এবং ভিন্নতর পথের দিশারি হয়ে উঠেছেন তা বলাই বাহুল্য। মধুসূদনের যুগ থেকে এই কাব্য সাধনার পথ প্রশস্ত হয়ে চলেছে। কল্লোল, কালি-কলম, কৃত্তিবাস, পরিচয়, কবিতা, হাওয়া ৪৯ এমনকি কবিসম্মেলন প্রভৃতি পত্রিকাগুলিও নানা সময়ে কাব্য-সাহিত্যের জগতে নানা বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটিয়েছে। এগুলি ছাড়াও অসংখ্য লিটিল ম্যাগাজিনে নির্ভর করে বহু কবি-সাহিত্যিক তৈরি হয়েছেন এবং আজও হয়ে চলেছেন। নয় এর দশকে বাংলা কবিতায় একটি নতুন ধারার সূচনা হয়েছিল। কবিরা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কবিতা শুধু আবেগের নয়—কবিতা এক মেধাবী উত্তরণও। কবিতা একমুখীও নয়—তা বহুমুখী,বহু অসামঞ্জস্যের সমন্বয়। কোথাও পরস্পর বিরোধী চেতনার সংঘাতও। পর্বমাত্রা ভেঙে নিছক গদ্যে, বিষয়হীনতায় এবং এক ধরনের শাব্দিক প্রজ্ঞায় এর চলন উপলব্ধি করা যায়। কবিতার গঠনে যেমন বিদ্রোহ, কবিতার ভাবের ক্ষেত্রেও বিদ্রোহ উঠে আসে। গতানুগতিকতাকে পরিহার করে কবিরা নতুন পথের সন্ধানী হয়ে ওঠেন। সেক্ষেত্রে না-কবিতা, কবিতিকা, অধুনান্তিক কবিতা এবং সর্বোপরি কবির ব্যক্তিপরিচয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পায়। সনাতন কবিতা পাঠকের কাছে তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি এক নতুনতর পথের সন্ধান দেয়। সেই নয়-এর দশক থেকে কবিতার পথে ঘুরতে ঘুরতে আমরা আরও দুই দশক অতিক্রম করেছি। কবিতা চর্চাও শহর গ্রামের বিভেদ দূর করে দিয়েছে।প্রবীণ কবি তরুণ কবির ফারাকও মুছে দিয়েছে। প্রকাশনার জগতেও এসেছে বিপ্লব। এরকমই পরিস্থিতিতে কয়েকজন কবির কাব্য প্রতিভার নিরীক্ষণ করার সময় হয়তো এটাই।কয়েকটি বিষয় লক্ষ করার মতো—

১.
উপলব্ধির জগৎ নির্মাণ
কবিদের উপলব্ধির জগৎও বিস্ময়কর। আত্মরসায়নের নিবিড় সংযোগ থেকেই উন্মোচিত হয় তার ক্ষরণ, যা বিমূর্ত শূন্যতারই বাতাবরণ বলা যায়। আপাত বিশৃঙ্খলা, যুক্তিহীন, স্বয়ংক্রিয় আত্মগত কোনো উৎস।সেখান থেকেই উপলব্ধির জাগরণ ঘটানো যদি সম্ভব হয়, তাহলেই প্রবীণ কবি ব্রতী মুখোপাধ্যায়ের কবিতার কাছে আমরা গিয়ে বসতে পারি। জীবনের সংরাগ আর অভিভব মেশানো এক শূন্যতার দরজায় উপলব্ধির নকশাগুলি মেলে দিতে পারি। বিমূর্ত চেতনায় চালিত হতে হতেই এক রূপজ অবয়বের কাছে আমাদের ভাবনা প্রক্রিয়ার নির্মাণ সাধিত হতে থাকে। জার্মানির হামবুর্গে বসবাসকারী ভারতীয় কবি-লেখক সঙ্গীতজ্ঞ ও ধ্যান শিক্ষক অমোঘ স্বামী The Home: A Haiku নামে একটি হাইকুতে লিখেছিলেন-
“From void’s womb they bloom,
Cosmic dance of fleeting forms,
Stars return to dusk.”
(Amogh Swamy, On My Way To Infinity: A Seeker’s Poetic Pilgrimage)
অর্থাৎ শূন্যের গর্ভ থেকে তারা প্রস্ফুটিত হয়,
ক্ষণস্থায়ী রূপের মহাজাগতিক নৃত্য,
তারারা সন্ধ্যায় ফিরে আসে।
“শূন্য
সেই ঠাঁই অনন্ত সারাক্ষণ গর্ভ যন্ত্রণায়,
সেইখানে শতখানেক কুঠুরির মন,
একান্ত আরশিও, লক্ষরঙা ভুবন ডাঙার ছায়া ধরে,
ধরে আপ্রাণ প্রাণ পিঞ্জরও নয়দুয়ারির”
এখানেই বাসনাকষ্টগুলি জোনাকি হয়।
স্বয়ংক্রিয় কবির বিক্ষিপ্ত সঞ্চার ঘটে। যাকে কবি বলেছেন: “শূন্যের ঘরে অবাধ্য পাগলামি/ব্যথাঝলমল”। ব্যথাও রঙিন হয়ে উঠলে কবিতা তখন ভেতর ও বাহিরেও সাম্রাজ্য বিস্তার করতে থাকে। সৌন্দর্যের এপাশ-ওপাশ আলোয় উদ্ভাসিত করতে থাকে। মঙ্গল আরতির আয়োজনে তার আনুষ্ঠানিক জাগরণ ঘটতে পারে। আর সেই কারণেই কবি ভালোবাসার ঘোষণার সঙ্গে কবিতার ঘোষণাকেও মিলিয়ে দেন:
“বুকের ভিতর নিয়ে আমি কবিতা লিখব
বুকের উপর নিয়ে আমি কবিতা লিখব
আকাশ ধুয়ে রোদ নেমেছে কবিতা লিখব
তোমার মুখে রোদ পড়েছে কবিতা লিখব
শাঁখ বাজাও ধূপ জ্বালাও দুয়ারে নেই খিল
তিলের ঠোঁটে একটি-দুটি শব্দ দানের দিন”
কবিতা এভাবেই এসেছে কবির কাছে। ‘তুমি’ ও ‘তোমার’ সঙ্গে তুমুল প্রকৃতিও এসে বসতি স্থাপন করেছে। ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষণও জুড়ে গেছে। শরীরের সঙ্গে কোথাও অশরীরী। বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষ্যের মিলনও শব্দের মাপকে দীর্ঘ করেছে। শিসের সঙ্গে নীরবতাও এবং দাহর সঙ্গে ব্যথাও বেজে উঠেছে। তাঁর কবিতায় আমরা প্রেম চিনতে পারি, প্রেমের ভুবন চিনতে পারি, মুক্তকচ্ছ শব্দের কারিগরকেও চিনতে পারি। কাব্যকলার নিয়ম বহির্ভূত চলনে চলার তৌফিকও রপ্ত করতে পারি। গল্প না-গল্পের ঘ্রাণে উজ্জীবিত হতে পারি। চোখ তখন দৃষ্টির প্রলম্বিত আধার হয়ে যায়। সময়ের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকে না। রহস্য চারিপাশেই সাজাতে থাকে ক্রিয়া। কবি তখন লিখতে পারেন:
‘সন্ধেহাওয়ায় উড়ে আসা শিরীষগল্প’
‘মধুজোছনায় অশ্রু যেই মিলিয়ে দিলাম কাজল’
‘নাভিতলের অফুরান যন্ত্রণারা প্রজাপতিরং’, ‘মাখনঠোঁটের কামড়’ থেকে ‘রজনীর গন্ধ ঠোঁট ছুঁয়ে নীল রঙের আগুন’ এবং ‘তার ভেতর একটুখানি ছাতিমফুলের আর পারি না’ নঞর্থক শিস। অথবা ‘তার ভেতর একটুখানি ঝালরদোলানো ব্যথা’ এভাবেই শিকড় ছড়ানো অনুভূতির মন্থন আর বিমূর্ত চিত্রকল্পের গভীর অন্বয় । কানাডিয়ান-আমেরিকান জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞানী,মনোভাষাবিদ, জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক এবং জনবুদ্ধিজীবী স্টিভেন আর্থার পিঙ্কার তাঁর গ্রন্থে বলেছেন:
“If we dig even deeper to the roots of words, we unearth physical metaphors for still more abstract concepts.”
(Steven Pinker, The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature)
অর্থাৎ যদি আমরা শব্দের শিকড়ের আরও গভীরে খনন করি, তাহলে আমরা আরও বিমূর্ত ধারণার জন্য শারীরিক রূপক খুঁজে পাই। ব্রতী মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় এই physical metaphors-এরই ছড়াছড়ি বেশি।
তিনটি কাব্য:
১) লং লিভ মনখারাপ! লং লিভ!(জানুয়ারি ২০২০)
২) মাটির নিচে জলের বেহালা বাজছে (২০১৮)
৩) দেয়ালদিনের কবিতা (এপ্রিল ২০১৭)
সময়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলেও, সময়ের উচ্চারণকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেও আত্মস্থিত এক উপলব্ধির প্রজ্ঞায় শারীরিক রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন শব্দে শব্দে প্রায় প্রতিটি কবিতাটিতেই। তাই মাঠ, বাড়িঘর, সন্ধ্যেবেলা, রোদ, মেঘ-বজ্র, হলুদঠোঁট পাখি, ব্যথা, রাষ্ট্র, আগুন, আমলাশোল, চাঁদ, ভারতবর্ষ তাঁর কবিতায় বারবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বিমূর্ত শূন্যতায় মূর্ত হয়েছে উপলব্ধির ক্ষরণ। কোনো কবিতার আলাদা নামকরণ প্রয়োজন হয়নি। প্রবহমান এক চক্র নির্বিকল্পবোধের সীমানায় অসীম হয়ে উঠেছে। কোন্ কাব্যের কোন্ কবিতা আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। নিজস্ব ঘরানাতেই কবিকে চেনা যাবে।পড়তে পড়তে সেই স্রোতেই অবগাহন করি বারবার:
“নিজের কোনো আলো নেই আমার,অন্ধকার নেই
না-ফুরনো শীত বুকের ভেতর
পথে পথে দীপবাহক, থামে না,ফেরি করে সূর্যের আলো,
আনন্দের গুঁড়ো ভাসে
আকাশে
প্রাচীন মঞ্চ জানে, আকাশের নিরিকল্প মাঠ সব জানে
আসতে না আসতেই সরে যায় প্লাবনের বেনজির নদী, মৌন ও একা,
শুকনো পাপড়ি পুরাতন অশ্রুরেখার কথা তুলতে চায়
নিজের কোনো আলো নেই আমার, অন্ধকার নেই”
পড়তে পড়তেই শুনতে পাই মাটির নিচে কেমন করে জলের বেহালা বাজছে।সময়ের পতাকা উড়ছে, বুকের ক্ষতগুলি বড় হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় অন্ধকার মানবিক চৈতন্যের চিতা সাজাচ্ছে। সভ্যতার সিঁড়িগুলি ভেঙে ফেলছে রাষ্ট্র শাসনের নামে। কান্না ও রক্ত একসঙ্গে বয়ে চলেছে আমাদের মানবিক পাহাড়ে। ভালোবাসার ফুল কখন ফুটবে তবে? এক অস্থিরতা যাপনের মধ্যে আমাদের রাস্তাগুলি ক্রমশ বেঁকে যাচ্ছে। অসহনীয় নৈঃশব্দ্যে আমাদের স্পন্দন থেমে আছে।
‘দেয়াল দিনের কবিতা’ বিপন্নতার বহুমাত্রিক প্রজ্ঞায় উঠে আসা মুহূর্ত গুচ্ছ আলাদা আলাদা নামকরণে খণ্ডিত হলেও উৎসমূলের সামঞ্জস্যে একীভূত চেতনার পরিচয়ে উদ্দীপ্ত। মানবিক অন্বেষণ জারি রেখেই কবির পথে নামা।প্রেমই তাঁর ব্যবসার মূলধন। শব্দই তাঁর ভাষা। উপলব্ধিই তাঁর প্রজ্ঞার নির্মিতি। অন্ধকার অনিশ্চয়তায় ভরা যাত্রাপথ:
“নক্ষত্রের ভরসায় প্রদীপ জ্বলছে না
আগুন পিঠে, বিছানা পুড়বে
অশরীরী উৎসবের রাত”
এই রাত প্রতিকূলতায় ভরা। রক্তের ছিটে লাগে গাছের পাতায় পাতায়। কে কোথায় খুন হয় কেউ জানে না। তবু কবি পাপে অথবা পুণ্যে থাকেন না। ভালোবাসায় থাকেন। এখনো ‘তুমি’ বলে ডাকেন। মাটির নিচেও জল থাকে না। চোখেও জল থাকে না।তখন নিজের রক্ত নিজেই পান করে অসময়ের দেশে ‘জান কাহিল রাত্রির চরে’ এসে দাঁড়ান। নিজের ছাল নিজেই ছাড়ান। নুন ছিটিয়ে কেমন কষ্ট!কষ্ট বোঝেন। ছিন্ন সময়, ভাঙা স্বপ্ন, বৃষ্টির রাত সবই শত্রু-শত্রু। কাতর করেছে অকাতরে। অন্ধ চোখে তবুও ‘সূর্যপ্রচোদিত’ ‘জাদুদীপন’। বিদীর্ণ সত্তা সঞ্চয় করে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ। কবিতাযাপন সময়যাপনের সমান্তরালে এক বিষাদদ্রাঘিমা টেনে দেয়। আমরা তখন খুঁজে পাই দেয়ালদিন। পাঠকের কাছে বাংলা কবিতার এক নতুন উচ্চারণ, এক নতুন অভিজ্ঞতার পথপরিক্রমায় ব্রতী মুখোপাধ্যায় নিজেকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন।

২.
জীবনপর্যটকের মন্ত্রিত ডায়েরি
কবি অমিত চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘জলকে ছুঁয়ো না এখানে’ হাতে নিয়ে দু একটা পৃষ্ঠা খুলতেই মধ্যবিত্ত রক্ত ছলকে উঠল। রোমান্সের বারুদগুলি ফুটতে লাগল। ভাঙা সাইকেলে চেন পড়ুক, তবু ভালো;ব্রেকটা লুজ্ হোক, তবু ভালো; তবু সেই টঙ্ থেকে রাতের গ্রাম যে মোহময়ী তা চোখের সামনে ভেসে উঠল। রাস্তা যতদূর যাবে যাক—তা ধানক্ষেত, ডাললেক, চিল্কায়ও হতে পারে। সবই তো সাধ্যের মধ্যে এসে যায়। সব কিছুই অসঙ্কোচ। “শেষ অবধি রাস্তা ফুরোয় স্টেশনে”। লাস্ট ট্রেন চলে গেলে টিকিট ঘরে লকডাউন। তা কোথায় যাবেন কবি?
অবশেষে মাতাল হবেন। চোরের মতন ফিরতে ফিরতে ডিফেন্স পার্টির গার্ডের কাছে ‘ পুরনো বর’, ‘সেজেগুজে বাবু’, ‘ফিটফাট স্বামী’। একরাতের জন্যই ‘যদিদং হৃদয়ং তব’ মন্ত্র পাঠ। প্রৌঢ় পাগলামো স্মৃতির দোকান খুলে দিতে দিতে যেন হেসে উঠল।
জীবনে কত গল্প জন্ম নিয়েছে, গল্পগুলি মরে যায়নি, কবিতার কাছে রাস্তা চেয়েছে, কবিতার কাছে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। ছেঁড়া পদ্যের বাস্কেটবলে ম্যাজিক জনসন অথবা সুনিপুণ মাইকেল জর্ডন হয়ে ফিরে এসেছে। রক্তচোষা শব্দের স্তোত্র। যে শব্দ বিসর্জনের ট্র্যাশে শূন্যতা ধরে আছে ট্রফির মতন। গ্রাম নক্ষত্র আকাশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে অন্ধকারে নিঃসাড়,যুদ্ধ ঘোষণায় কল্পনায় একে একে খেলা দেখে গেছে। আর ভেবেছে :
“আসলেই আধভাঙা এই স্বপ্ন, যার মানে
আধখানা গড়াও, এইভাবে সে দিন শুরু করে
একটা শিশুর মতো ঢেঁকিকলে চড়ে,
আজ এই প্রান্তে, কাল ওই,
অথচ কখনোই কালক্রমে নয়,
সর্বদাই আলম্ব থেকে দূরে।“
জীবনের এলোমেলো ধূসরতা স্বপ্ন-মেদুরতাকে আত্মস্থ করেই কবি অগ্রসর হয়েছেন। স্মৃতিগুলি রংবেরঙের নুড়িপাথর। ফেরিগানে আজানে ছোপানো হয়েছে ঝিঙেফুলে। বারবার কবি ‘তুমি’ নামে এক সর্বনামের কাছে ফিরে গেছেন। আসলে এই ‘তুমি’-ই প্রেম। তুমি ধাক্কা দেয়, প্রশ্ন করে, উত্তরও চায়, কিন্তু কবি তাঁর নিজস্ব গতিতেই ধাবমান। আকাঙ্ক্ষাহীন হয়েও আকাঙ্ক্ষার দরজা খোলেন। প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েও নিরুত্তর থাকেন। কবি বলেছেন:
“এ পরীক্ষায় জানি প্রশ্ন অঢেল, উত্তর অগোছালো,
তাই শেষ অবধি একটা মিশ্ররাগ জন্মায়, একটা ওয়াল্টজ,
আস্তে পা ফেলা, নিরীক্ষণ, কিন্তু থামা চলা, থামা চলার
একটা অনুরাগ ছন্দ।”
সমগ্র কাব্যটি এই অনুরাগ ছন্দের আবর্তনেই বিবর্তিত। কবিতাগুলি আবহমান প্রেমিকের দৈবঅনুজ্ঞায় নির্মিত স্মৃতিসৌধ। জীবনপর্যটকের মন্ত্রিত ডায়েরি। নারীমুখের ইলাস্ট্রেশনে কাঙ্ক্ষিত বিজ্ঞপ্তি হয়ে উঠেছে। ভাষার সঙ্গে চিত্রকল্প, অনুভূতির সঙ্গে বিবৃতির ঘরকন্নার এমন সাযুজ্য পারিপাট্য দান করেছে যে কবিকে প্রেমিকসত্তারই অব্যর্থ শক্তি এনে দিয়েছে। তাই তিনি যত বড় কবি, তার থেকে অধিক প্রেমিক। তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে যায় ভার্জিলের কথা:
“Love conquers all things; let us too surrender to Love.”
অর্থাৎ প্রেম সব কিছু জয় করে; আসুন আমরাও প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ করি। প্রেমিক হৃদয়কে স্বপ্নে ও শূন্যতায় চালিত করি। জলকে মুদ্রিত প্রেমসত্তারই মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা জল সমুদ্র রচনা করে। শব্দ রচনা করে প্রেম।
ম্যানচেস্টার মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির রাইটিং স্কুলের অধ্যাপক এবং সৃজনশীল পরিচালক ও কবি ক্যারল অ্যান ডাফি বলেছেন:”You can find poetry in your everyday life, your memory, in what people say on the bus, in the news, or just what’s in your heart.” অর্থাৎ তুমি তোমার দৈনন্দিন জীবনে কবিতা খুঁজে পেতে পার, তোমার স্মৃতিতে, বাসে মানুষ কী বলে, খবরে, বা তোমার হৃদয়ে যা আছে। সুতরাং কবিতা আত্মযাপনের, আত্মদহনের, আত্মমগ্নতার ভাষা থেকেই বেরিয়ে আসে। সেখানে নিজস্ব বৃত্তেই ঘুরে আসে ছায়ারা। একান্ত উপলব্ধিগুলি নির্মাণ করে চলে তাদের জগৎ। সেই কথাই বলতে চাইলেন আমেরিকা প্রবাসী কবি অমিত চক্রবর্তী:
“এও এক ধরনের যুদ্ধ। নিউরনগুলিকে জিতে নেওয়ার।
আমাকে ওরা মনভবনে পাঠাবার সব ঠিকঠাক করেছিল,
কারণ আমি জানালা দিয়ে একবার হিংসা দেখে ফেলেছিলাম।
তারপর ওরা যখন আমাকে নিতে এল,
আমি গল্প বলা শুরু করলাম—অদ্ভুত সব দেহভৃৎ বা জীবজন্তুর গল্প,
লোমহর্ষক,স্নায়ুপীড়া দেওয়া, অসংগতি, ঘূর্ণি, আর রঙ্গ-অন্তরঙ্গের…”
উদ্ধৃত অংশটি পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায় আত্মক্ষরণের সেই স্নায়ুযুদ্ধ প্রবৃত্তিমুখীন জীবনের বিচ্যুতি, আবেগ, অসংগতি এবং রঙ্গ-অন্তরঙ্গের অভিমুখ কতখানি মর্মান্তিক ও অনপনেয়। এখান থেকেই শুরু হয়েছে ৪৫টি উপপাদ্যের ক্ষেত্রভূমি যা প্রমাণ সমীক্ষণের বহু ঊর্ধ্বে চেতনার বৃহত্তর আন্দোলিত ক্রিয়ায়। কাব্যের নামও দিয়েছেন ‘ভুলটা ছিল উপপাদ্যে, প্রমাণেতে নয়'(প্রথম প্রকাশ ২০২৩)।
কবিতা তার পট পরিবর্তন করেছে, আনুভূমিক টান থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে এক গূঢ়তর পথ অন্বেষণে। স্বাভাবিক আলো, দৃশ্য, ক্রিয়া ও প্রকাশের ভেতর থেকে সরে গিয়ে সংক্ষিপ্ত দ্যুতিময় টুকরো টুকরো না-গল্পের ভেতর আমাদের উপস্থিত করেছে। তাই সমগ্র কাব্যটিতে গল্প ভেঙে গেছে, জীবনের কতগুলি ঢেউ আর নকশাকে একত্রিত করেছেন, সেগুলিতেই অনুভূতির দৃশ্য তৈরি হয়েছে। আদি-মধ্য-অন্ত বলেও কিছু নেই। বিশেষণ ও ক্রিয়ার প্রচলিত ব্যবহারও নেই। প্রচলিত বিশ্বাস, ইতিহাস, বিজ্ঞান, যুক্তি মানবতাকেও তিনি আশ্রয় করেননি। এক মুক্তিপ্রয়াসী চেতনার অভিক্ষেপ সন্নিবিষ্ট প্রজ্ঞার বিক্ষিপ্ত প্রকাশ সাবলীল গতিতে অগ্রসর হয়েছে। তাই কবিতাংশগুলির নামকরণের প্রয়োজন হয়নি। কবি লিখেছেন:
“কল্পনাকে ঝুরো করে ফেলে গুঁড়ো গুঁড়ো চুর
নির্ঝর মাঞ্জায় মাখে নিষ্ঠুর আকুতি প্রাণ
অন্য ছাঁচে সুধা পান, আহুতি দর্পণ।”
লক্ষ্য করার বিষয় কবিতায় তিনি সামঞ্জস্য বা চিরাচরিত রীতির অনুসারী হতে চাননি। তাই শব্দার্থ ধরেও অগ্রসর হননি। দৃশ্যপট ‘সূর্যাস্ত আঁকা’ লিখেও বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন ‘বিষণ্ণ ইঞ্জিনিয়ার’, ‘মরচেপড়া রূপসী’, ‘দুর্বলতার আতর’,’দুপুরের জুঁই’,’বৈষ্ণব অহংকার’, ‘ছায়ার বঁড়শি’ ইত্যাদি। বিশেষ্যও যৌগিক হয়ে উঠেছে ‘অশ্বউটগাধা’-এর এভাবে ব্যবহারে। সর্বনাম ‘তুমি’ এবং ‘ছেলেটি’ উল্লেখ থাকলেও একটা ইঙ্গিতময় সত্তার ধারক হয়ে উঠেছে, যা কখনো নিজস্ব অবয়ব। শুধু ক্রিয়ায় দেখা দিয়েছে ‘ট্রাপিজ জাম্প’ এবং ‘ইচ্ছেগুলো নিয়ে কাঁদি’র মতো বোধ। প্রচলিত জীবনধারার মোক্ষম চালগুলি টুকরো টুকরো সংলাপে বিবৃতির পর্যায় থেকে উঠে এসেছে। তাই সেখানে কিছুটা স্বাভাবিক ও সামাজিক প্রকাশ দেখতে পাই। যেমন কবি লিখেছেন:
‘এপাড়ায় কবে আসছেন?’
‘কবিতা এসো তো আমার সুজন মাঝি’
‘এ জিনিস অমৃত,
রোজ সকালে খাও বয়স কমবে’
‘সোনারপুর লোকালের মেয়ে’
‘অরণি কাঠের গল্প’
‘রেসের মাঠে পাওয়া সমাধানের ভেলকি’
‘একটা লোক কিন্তু ফের আমার কথা ভাবছে’
কিন্তু এইসব বিবরণ, বিবৃতি, সংবাদ সবকিছুর মধ্যেই একটা vision-এরই অন্তরাল তৈরি করেন। যা স্বাভাবিকতাকেও ভিন্নতার নিরিখ দান করে। বোধের বহু ব্যাপ্তি সম্মোহনের দিকে ধাবিত করে। তখনই লিখতে পারেন:
“আমার হাতে পোষমানা সাপ
তোমার হাতে উদ্ধত।”
তখন প্রকৃত দৃশ্য পাল্টে যায়, লক্ষ্য পাল্টে যায়। ঠোক্কর খাওয়া ঝড়, হোঁচট খাওয়া ঝড়, ভেলভেট ঘাসের ওপর হেঁটে যাওয়া ফ্রকপরা বালিকারা আমাদের মর্মরিত করে। চেতনার দৃষ্টিকে প্রখর করে তোলে। ‘গোপন ছেঁড়া’ লিখে রাখা লম্বা হাতা কনুই অবধি ব্লাউজকে তখন বুঝতে পারি। দৃশ্যের অতীত অদৃশ্য তাড়না আমাদের তাড়িত করে। পাবলো পিকাসো তাই লিখেছিলেন:
“If I paint a wild horse, you might not see the horse… but surely you will see the wildness!”
অর্থাৎ
আমি যদি একটি বন্য ঘোড়া আঁকতাম,তুমি ঘোড়াটি দেখতে পেতে না… তবে তুমি অবশ্যই বন্যতা দেখতে পেতে!
এই বন্যতাকেই উপপাদ্যের নিয়তি করে তুলেছেন কবি যা কখনোই প্রমাণের কাছে পাওয়া যাবে না।

৩.
ইতিহাসের জীবন্ত কণ্ঠস্বর
২০১০-এ বেরোনো বিশ্বজিৎ মাইতির ‘বারো হাত কাঁকুড়ের দেশ’ এক ভিন্নতর কাব্য প্রয়াস বলা চলে। প্রচলিত রীতিতে ছন্দোবদ্ধ কবিতা লিখে তিনি মাত্ করতে চাননি। বরং ছন্দময় জীবনের ছন্দোহীন রূপটিকেই তিনি দেখাতে চেয়েছেন। তাই একুশটি গদ্য কবিতায় সময় ও স্বদেশ, ইতিহাস ও জীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, রাজনীতি ও মৃত্যু-সংঘাতের ছবিগুলি তুলে ধরেও এক বিদ্রূপাত্মক বিদ্রোহের ভেতর অন্তঃক্ষরণের তীব্র দহনকে ভাষা দিয়েছেন। মর্মস্পর্শী বেদনার অভিঘাত আমাদের সহ্য করেই তাঁর কবিতার কাছে যেতে হয়। শুনতে হয় কষ্ট-দীর্ণ হাহাকারের কণ্ঠস্বর।দেখতে হয় ছিন্ন-বিছিন্ন চিত্রলিপির ভেতর মানবসভ্যতার ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা ও জিঘাংসা। কত মৃত্যুময় জীবনযুদ্ধের বিভীষিকা গ্রাস করেছিল, সেই সময়ের সন্তান হিসেবেই কবি নিজেকেও দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। সেই সময়েরই প্রতিটি মুহূর্ত যাপনের উদ্বেগকে, মানুষের দীর্ঘশ্বাস ও মৃত্যুকে, রাজনৈতিক চক্রান্ত কে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন কবিতায়।
সেই সময়ের ইতিহাসটি এই রকম—
২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে হুগলী জেলার সিঙ্গুরে টাটাদের গাড়ি কারখানার বিরুদ্ধে ২৬ দিন ধরে অনশন করেন সেই সময়ের বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই তখন চরম গণ্ডগোল চলছে। বামফ্রন্টের নেতৃত্বাধীন সরকার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চাইছেন শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে। সিঙ্গুরে টাটাগোষ্ঠী এসেছে গাড়িকারখানা গড়তে। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামেও বৃহৎ পেট্রোরসায়ন হাবের পরিকল্পনা চলছে। ইন্দোনেশিয়ার সালিম গ্রুপ ওই হাব এবং বিশেষ শিল্পাঞ্চল গড়তে আগ্রহী। এই উদ্দেশ্যেই সংযোগের জন্য বিরাট চওড়া রাস্তা এবং হুগলী নদীর ওপরে নতুন সেতুও নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে।
এই সময়েই একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় নন্দীগ্রামে পেট্রোরসায়ন হাবের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হবে।
এর বিরুদ্ধেই তখন শুরু হয় বিক্ষোভ।শুধু কৃষকেরাই নয়, সরকার পক্ষের লোকজনও বিক্ষোভে সামিল হয়। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা, জামিয়াত উলেমা এ হিন্দ। পরে যুক্ত হয় মাওবাদীরাও। পীড়ন-দমনে আন্দোলন বন্ধ করা যায় না। অনেক জায়গায় রাস্তা কেটে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নও করা হয়। নন্দীগ্রাম ছেড়ে বহু সিপিআইএম কর্মী ও তাদের পরিবারগুলি পালাতে বাধ্য হয়।
প্রায় তিনমাস এভাবেই বিচ্ছিন্ন ছিল নন্দীগ্রাম। মার্চের প্রথম থেকেই প্রচার চলছিল পুলিশ অপারেশন হবে। তারিখও আন্দাজ করেছিল ১৪-ই মার্চ। অসংখ্য পুলিশও এলাকায় টহল শুরু করেছিল।
সেই সময়ের বিভিন্ন সংবাদপত্রগুলি থেকে জানা যায় কীর্তন-শাঁখের আওয়াজের মধ্যেই চলতে থাকে গোলাগুলি। সড়ক অবরোধ, হাঙ্গামার মাঝেই দেখা যায় জায়গায় জায়গায় ছড়ানো-ছেটানো
শত শত চটি-চপ্পল, রক্তের দাগ। জানালায় ও বাড়ির দেওয়ালে গুলির দাগ। সিপিআইএমের দুর্নীতি, অত্যাচার, দমন-পীড়নে সবাই এককাট্টা হয়ে পড়ে। পুলিশের গুলিতে ১৪ জন কৃষক নিহত এবং অসংখ্য আহত হয়। পুরো এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে ভূমিউচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। এই জমি বাঁচাও আন্দোলন এবং পুলিশের হাতে গ্রামবাসীদের মৃত্যু কবি নিজেই দেখেছেন। সবই তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে। সমগ্র কাব্যজুড়ে তার মরমী প্রকাশ একটি জীবন্ত ইতিহাসের কণ্ঠস্বর হয়ে বেজে উঠেছে। যা ইতিহাসে লেখা থাকে না, যা সংবাদপত্রগুলিতেও উল্লেখ করা হয় না, তা কবিতায় কবি লিখলেন। শান্ত পরিবেশ কিভাবে অস্থির হয়ে উঠল, কিভাবে নিরীহ মানুষেরাও সরকার বিরোধী আন্দোলনে সামিল হল, মেয়েদের সম্ভম আর জীবন রক্ষার্থে কিভাবে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই পরিচয় দিতেই কবি ‘সংস্কৃতি’ নামক কবিতায় লিখেছেন:
“সারারাত শোনা যেতে লাগল ফুর্তি, হইহাল্লার শব্দ
দেখা যেতে লাগল মশালের আলো
নদীর সমতল, পাহাড়ের ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে
ক্রমশ জঙ্গলের ভেতর ঢুকে যেতে লাগলাম আমরা।”
দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে নিরীহ মানুষও ঘুরে দাঁড়াতে শেখে। নিজেদের রক্ষা করতেই বিদ্রোহী হয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একদিকে দারিদ্র্য, কর্মহীনতা, মনুষ্যেতর জীবনযাত্রার জন্ম দিতে থাকে। অপর দিকে আগ্রাসী মনোভাব সেই চিত্রও কবি দেখতে পান:
“ছবিগুলি ভেসে ওঠে—ছবিগুলি কোথা ভেসে যায়! শালিখ ও গাঙচিলের দল ভয়ে ভয়ে উড়ে যায় চুনিবুড়ির উপর দিয়ে। বোমা ও গুলির শব্দে সন্ত্রস্ত গ্রাম জেগে থাকে। একটি ময়ূরী তার সঙ্গীটির ফেরার আশায় রাত জাগে।”
প্রাণীজগতের এই আতঙ্ক আসলে মনুষ্য জগতেরই আতঙ্কের স্বরূপ। জনজীবন কতটা ভয়চকিত ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল তারই চিত্র কবিতায়। প্রাণীজগতের শত্রু-মিত্র, খাদ্য-খাদক যেমন সম্পর্ক থাকে, মনুষ্যজগতেও শাসক-প্রজা, স্বপক্ষ ও বিরোধী পক্ষ, অস্ত্রধারী ও অস্ত্রহীনের সম্পর্ক থাকে। ধর্মের দোহাই দিয়ে শোষণ ও শাসনের বিকল্প তৈরি হয়। সেই ছদ্মবেশের অন্তরাল থেকেই কবির বোধ সদা জাগ্রত:
“এরকম একটি দৃশ্যের ভিতর ময়ূর ও সাপকে ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে দিতে চাইছে কেউ কেউ, যাতে এই যুদ্ধটাও ধর্মযুদ্ধের একটি এপিসোড হিসেবে গণ্য হতে পারে পরবর্তীকালের গবেষকদের কাছে।কিন্তু পোষা ময়ূরের পায়ের ঘুঙুর বেজে উঠছে সাপকে ঠুকরে দেওয়ার মুহূর্তে। তাছাড়া ধর্মপুত্তুরদের পা মাটিতে না পড়াই শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু মার্চের রোদ্দুরে তাদের পা, এমনকী ছায়াও পড়ছে মাটিতে।”- এই ‘যুদ্ধসংবাদ’ কবিতার শেষ অংশে ছদ্মবেশী কুচক্রী ভেকধারী ধর্মপুত্তুরদের আসল রূপও কবি উন্মোচন করেছেন যা রিপোর্টাররাও জানেন না। ‘হননপট’ লিখতে গিয়ে শাঁখের আওয়াজের সঙ্গে থ্রি-নট-থ্রি-র গুলিবর্ষণ। কবি চেতনাপ্রবাহ গুলি-খাওয়া মৃত অথবা অর্ধমৃত মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করলে উপলব্ধি করেন:
“মর্গে শুয়ে আছি, মৃতের মতো চোখ বন্ধ করে, তলপেটে গুলি, রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে— ক্যামেরার লেন্স জুম করে এই দৃশ্য তুলছে উন্নয়নশীল দেশের চিত্রসাংবাদিকরা।”
এরকমই মৃত্যুর বর্ণনা প্রসঙ্গ বারবার ফিরে এসেছে। অত্যাচারিত হতে নারী, শিশু-কিশোরী কেউ বাদ যায়নি। বেপরোয়া ধর্ষণও চলেছে। রাজনীতির সমর্থকেরা অত্যাচারীদের দলে যোগ দিয়েছে। প্রশাসনের সহায়তায় তারাও সাহস পেয়েছে। রোমহর্ষক বর্ণনা যেন বারবার আর্তনাদ আর রক্তে ভিজে গেছে:
“ধরা-পড়া দশজন ভাড়াটে ধর্ষণকারী ও বন্দুকবাজের দায়, সরকারি হিসাবে চোদ্দোজনের মৃত্যুর দায়, অসংখ্য নিখোঁজের দায়, লাশ গায়েবের দায় এবং ঘরছাড়াদের দায় নিতে হয় তাঁকেই— মস্তিষ্কে যিনি প্যারাসাইট ঢুকিয়েছেন।”
আরো রোমহর্ষক বর্ণনায় কবি লিখেছেন:
“ধূপের ধোঁয়ায় উদ্বেলিত বাতাস,শঙ্খ ধ্বনিতে উচ্ছ্বসিত চতুর্দিক, কীর্তনের গানে মাতোয়ারা পরিমণ্ডল। সুবদির বুড়া গৌরাঙ্গের রূপ দর্শনে মুগ্ধ জনগণ। এসবের মধ্যেই টিয়ারগ্যাসের সেল ফাটে, ছত্রখান শিশু ও মহিলা, কিশোর ও যুবাজন। অনবরত গুলি চলে থ্রি-নট-থ্রি আর পাইপ গান থেকে।
নাড়িভুঁড়ি ছেতরে পড়ে থাকে শিশু, যোনিতে লোহার রডের খোঁচা খায় যুবতি, ঘাটের পাটে ধর্ষিতা হয় মহিলা ও কিশোরী— শিশুদের দু-পা ধরে চিরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়।শ্যামা, গাঙশালিখ, টিয়া ও কাকের দল শকুনের দ্বারা বিতাড়িত।”
এই শকুন বলতে কবি স্বার্থপর শোষক পীড়নকারীকেই বুঝিয়েছেন। এরা সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মানুষ হত্যায় নেমে পড়েছে। এদের নিষ্ঠুরতা সীমাহীন। ১৪ই মার্চের সেই আর্তনাদ এবং সেই সোনাচূড়া গ্রামের বিভীষিকাময় ঘটনা যা স্মরণ করলে আজও শিউরে উঠি । নীতি নৈতিকতাহীন মানুষের অসামাজিকতা অসভ্যতা কতটা নিম্নমুখী হলে তবেই পশুকেও হার মানায় একথা কবি জানেন। তাই এই অসহ্য অমানবিকতা, ছলনাময় প্রবঞ্চনাকে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতেই বর্ণনা করেছেন:
“শুয়োরেরা প্রজাপতি সেজে
ফুলে ফুলে মধু খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে,
ছৌনাচের মুখোশে সীতা সেজেছেন যিনি
তিনি আসলে হাড্ডাকাড্ডা এক জোয়ান,”
এই ভড়ং আর চালাকি সর্বত্রই। শুয়োর যেমন প্রজাপতি হয় না, হাড্ডাকাড্ডাও সীতা হয় না। দুটিই বিভৎসতার পরিচয়। আর এক শ্রেণির মানুষ অনাহারক্লিষ্ট এবং অত্যাচারে ভিটে ছাড়া হয়ে মুকুন্দ চক্রবর্তীর মতোই ‘অভয়ামঙ্গল’ লিখে চলেছেন। ছোটোআঙারিয়ার পাশের গাঁয়েই তাদের ঘর। দীর্ঘদিন তারা ঘরছাড়া।
কত দুঃখ ও বঞ্চনার কথা, মৃত্যু ও হতাশার কথা কাব্যটিতে লেখা হয়েছে। ধর্ষিতা কিশোরী যেন লুন্ঠিত বোঁটা ছাড়া শিউলি। অথবা অশুভ কাকের ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়া ভাইয়ের দেহ। কোথায় পলিমাটি যে সুন্দর জন্মাবে? আত্মবিশ্বাস জন্মাবে? সাধনা ও প্রেমের বৃক্ষে ফুল ফল ফলবে?
কবি লিখেছেন:
“কণ্ঠনালীতে টান পড়ে বড়ো
শরীরে আমার পলিমাটি খুঁজি
পলিমাটি নেই…”
সময়ের এই বিপন্নরূপ অদ্ভুতভাবে বিক্রিয়া করে কবির মানসিকতায়। এক অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। জীবনের সংরাগও মুছে যায়। তখন জাদুবাস্তবের কাছে কবি আশ্রয় চান। অসম্ভবকে সম্ভবের তালিকায় তুলে আনেন। কুমারীর গর্ভে তখন শ্বেত হস্তিটির আগমন টের পান।জঙ্গলের নীল শাড়ির টুকরোকে পাখি হয়ে উড়ে যেতে দেখেন। মতিভ্রমের স্বপ্ন-মায়াপরবশ এভাবেই বাঁচতে শেখায়।
কাব্যের নামকরণেই কবি সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের চাবুক হেনেছেন। ‘বারো হাত কাঁকুড়ের দেশ’ যা রূপকথার গল্পের নামকরণ হতে পারে, কেননা তার ‘তেরো হাত বিচি’ সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে যায়। অর্থাৎ যতটা আড়ম্বর ও আয়োজন তা অন্তঃসারশূন্য, কথার বুজরুকি মাত্র। ভেতরে ভেতরে রক্তাক্ত, হাহাকার, দিশাহীন হননবৃত্তির অন্ধকার। সেই কারুণ্য ও নিঃস্বতাকেই এভাবে বর্ণনা করেছেন ‘জীবনবিদ্যা’য়:
“বারো হাত কাঁকুড়ের দেশে
একদিন আমি থাকব না
জেগে থাকবে বুড়ো লোকটির হাতের তকলি
ভুরু কুঁচকে তাকানো বউটির পায়ের গোছ
লম্বা চুল পানঅলা যুবকের পাশে
কাজের মেয়েটির সস্তা ক্রিম-মাখা মুখের আলো”
ক্ষুধার্ত, ভিক্ষুক, দেহপসারিনি,মাস্তান, সস্তা মেয়ের রূপ এই বর্ণনার মধ্যেই উঠে আসে। কবির ব্যঙ্গের তীব্রতা আরো টের পাই ‘শান্তিসংগীতে’। অশান্তির আতিশয্যে ভড়ং সর্বস্ব বারফাট্টাই বিচিরা অর্থাৎ লোকদেখানো বড়াইকারীরা দেশের কল্যাণবাণী প্রচার করবে।কবি তাই লিখেছেন:
“বারো হাত কাঁকুড়ের দেশে
তেরো হাত বিচিরা সর্বদা
অখিলের শান্তিসংগীতে মাতোয়ারা,
সোনালি ঝালরে মোড়া গাধা
সেই অবসরে স্মিত হেসে
মহিলামহলে ঢুকে পড়ে
বারো হাত কাঁকুড়ের দেশে
তেরো হাত বিচিরের বারফাট্টাই দেখে
মুগ্ধ হয় জনগণ।”
এখানে ধর্মব্যবসায়ী থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রপরিচালক সবাইকেই কবি ‘তেরো হাত বিচি’ বলতে চেয়েছেন।
কাব্যটিতে কবির ভালোবাসার গ্রাম, অঞ্চলও ইতিহাসের ধারক । কবিতাগুলিতে সর্বত্রই এক মরমী স্পর্শ ছড়িয়ে আছে। গ্রাম যেন সভ্যতারই এক পরাজিত নায়িকা। রাজনৈতিক চক্রান্তকারীরা গ্রামকেও ধর্ষণ করে চলেছে। ঘাতক হয়ে হত্যা করে চলেছে নির্মমভাবে। যে হাসিমুখ, খেয়াঘাট, ভোরের দৃশ্য, চায়ের দোকান, ফুলুরি ভাজার গন্ধ নিয়ে সকাল হত— সেই সকাল এখন রক্তাক্ত, পোড়া গন্ধে পাল্টে গেছে। তবুও কবি গ্রামকে দেখেন আর চারিপাশে প্রসারিত করে নিজেকে ছড়িয়ে দেন:
“আমাদের ছোটো গাঁয়ে
পাশ দিয়ে বয়ে চলে নদী
সামনে প্রসারিত প্রান্তর
গাঁয়ের ভেতর ছোটো ছোটো ঘর
আমাদের ভাঙাবেড়া আমাদের সোনাচূড়া
আমাদের অধিকারীপাড়া
আমাদের গোকুলনগর।”
পাড়াগাঁর চালচিত্র, প্রচলিত রীতি-নীতির পরিচয়, কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষের পরিচয় যেমন আছে, তেমনি মানুষের প্রচলিত সংস্কার ও সমালোচনারও পরিচয় আছে। রোমান্সের রহস্যময় চালচলনও:
“পাঁচ সিকার ছাগল এক হাজার টাকার
বাগান নষ্ট করছে অবলীলায়
মুরগির ছানা দেখে ভয় পাচ্ছে শিশুটি
নতুন বউ ভাসুরকে দেখেও ঘোমটা দিল না
আমাদের গায়ে এইসব ঘটনায় তর্কবিতর্ক-
চুলোচুলি-ঠাট্টামশকরা-ফিসফিস খুব চলে
আমাদের গাঁয়ে রাত্রির নদীটি জ্যোৎস্নায় রহস্যময়ী
তার তীরে মুগ্ধতায় হাতে হাত যুবক-যুবতি।”
সাদাসিধে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার এই অকপট উচ্চারণ যখন শিল্পের কারখানা স্থাপনের নামে জমি অধিগ্রহণের কারণে পাল্টে যায় তখনই নেমে আসে আতঙ্ক। পাঁচসেলের টর্চের আলোর সাথে ক্রুদ্ধ শাসানি, থ্রি-নট-থ্রি-র গুলি ছুটে আসে। শিশু হত্যা ও বাদ যায় না। প্রথম বর্ষের কলেজ ছাত্রীও লাশ হয়ে যায়। এই ইতিহাস বাংলার মানুষ জানে।
একটি কাব্যগ্রন্থ একটি সময়ের ইতিহাস, একটি আর্তনাদ আর রক্তাক্ত মৃত্যুর ইতিহাস নিয়ে লেখা হয়েছিল। পরাধীন দেশে মেদিনীপুরই সারা বাংলার হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল। জমি আন্দোলন, মানসম্ভ্রম, জীবন রক্ষার আন্দোলনেও মেদিনীপুরই রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। তাই এই কাব্যখানি সেই সময়েরই উচ্চারণে মুদ্রিত, মানুষের হাহাকারে দীর্ঘশ্বাসে পূর্ণ। এই ইতিহাস কখনোই ভুলতে পারবে না।
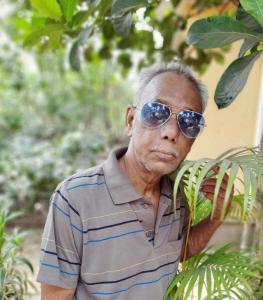
৪.
অস্তিত্ব সঞ্চার
প্রচলিত কাব্যধারার সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান করছেন কবি পিনাকীরঞ্জন সামন্ত (জন্ম:জানুয়ারি ১৯৪৭)। সনাতন বাংলা কবিতা পাঠকের কাছে তিনি কতটা গ্রহণীয় হবেন সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। তবে এটুকুই বলা যায় বাংলা কবিতা তাঁর হাতে এক ভিন্ন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। শুধুমাত্র পোস্টমডার্ন ধারণার মধ্যে তিনি যেমন বিচরণ করতে চাননি, তেমনি একমুখী বিষয়ভিত্তিক কাব্য রচনাতেও আবদ্ধ থাকেননি। সব ধারণাকেই নস্যাৎ করে একটি নিজস্ব পথের সন্ধান করেছেন আর এক্ষেত্রে তিনি যে সফল হয়েছেন তা বলাই বাহুল্য।
মোট সাতটি কাব্যগ্রন্থ: ‘উপদ্রুত হাওয়ার পালক’, ‘পুরনো ধারাপাত’, ‘বাইপাস সার্জারি’, ‘আলাদা শ্রীমতী যখন’, ‘এক অর্বাচীনের উপাখ্যান’, ‘কেন আমি অঙ্কে শূন্য পেয়েছিলাম’ এবং ‘আল্টিমেটাম নীলপায়রা’ থেকে বাছাই কবিতা নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ‘নির্বাচিত কবিতা'(প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০২২)। কাব্যের প্রাককথনে কবি উল্লেখ করেছেন: “আমি কবি হওয়ার লক্ষ্যে কোনোদিন কবিতা লিখিনি। বরং বলা ভালো, কবিতা আমাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে লিখিয়ে নিয়েছে।” এই লিখিয়ে নেওয়া ব্যাপারটিতে একটি প্রাকৃতিক স্বয়ংক্রিয়তা আছে, ঘর্মাক্ত হয়ে মাথা খাটানোর ব্যাপার নেই। তিরিশ বছর ধরে লেখালিখির এই ফসল তাঁর জীবনেরই ভাঙাগড়ার যে বিক্রিয়া তা বলা চলে।
‘আল্টিমেটাম নীলপায়রা’ কাব্যের ‘কবিতার সংজ্ঞা’ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:
“০×০=০=কবিতা। সুতরাং কবিতার কোনো বেসিক সংজ্ঞা হতে পারে না।”
সূর্য একটা বিন্দু হলে বৃত্তাকারে তার চারিপাশে সব গ্রহগুলিই ঘুরছে। পৃথিবীও ঘুরছে। আর পৃথিবীতে আমরা মানুষ। হাসি কান্না সুখ দুঃখ এবং প্রকৃতি। যদিও প্রকৃতি=মা। কিন্তু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যে শূন্য তা কবি জানিয়ে দিয়েছেন। ‘এক অর্বাচীনের উপাখ্যান’ কাব্যে ‘কবিতার প্রতিধ্বনি’তে লিখেছেন:
“আমি কোনো কবিতা লিখছি না। ধ্বনি সমন্বয়ে কিছু কিছু প্রতিধ্বনি হতে পারে।”
এই প্রতিধ্বনি আসলে শূন্যবাদেরই। যার সঙ্গে সবকিছুর গুণ করলে শূন্যই ফিরে আসে। তাই সব খেলার ভিতরে, সব জীবনের ভিতরে, সব বিবর্তনের ভিতরে কখনো শ্রীকান্ত, কখনো রবীন্দ্রনাথের বন্ধু, কখনো রবীন্দ্রনাথের উপেন হয়ে কবি ঘুরপাক খান। এক তরঙ্গকে ধারণ করেই লিখে চলেন:
“এ জীবন এলোমেলো,যত মত তত পথে
পথের নিশানা করি পিঁপড়ের স্রোতে।”
এইভাবেই এলোমেলো জীবনের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেন। কখনো বৃদ্ধ বয়সের কিসও শূন্যতার আকাশে উড়িয়ে দেন। শূন্যতা সহজ অর্থে মৃত্যুরই ঘন্টাধ্বনি। ‘কবিতা’ শব্দটির বিনির্মাণ এভাবে করেন: ‘কবিতা’র ‘ক’ কলকাতার, ‘তা’ লিটল ম্যাগাজিনের, ‘বি’ উচ্চারণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইংরেজির Bee হয়ে যায়। কবিতা তখন মৌমাছি হয়ে ফুড়ুৎ হয়ে যায়।
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছায়াগুলি কবিতায় উঠে আসে। পাল্টে যাওয়া শ্রীমতীকেও দেখতে পাই। প্রকৃতির রোদ ও দিন কবির প্রিয়জন, প্রিয় ভাই। শীত-গ্রীষ্ম স্মৃতির স্ফটিক। মাতা ও পিতা শ্রাবণের মেঘ। বৃষ্টি তো প্রিয়তমা, প্রিয় সহচরী। এসবের মধ্যেই কবির লুকোচুরি খেলা। পরাবাস্তবের অলৌকিক বাহার দেখতে দেখতে ক্ষুধার্ত সময়ের বাজনাও শোনেন। নিজের শ্বাসকষ্টজনিত হাঁপানির গল্পও কবিতায় মিশে যায়। ইতিহাস চেতনার ভেতরও প্রাচীন সভ্যতায় কবি পৌঁছে যান। মানবিকতা থেকে ঈশ্বরের দূরত্ব মাপতে চান। ক্ষুন্নিবৃত্তির মানুষের করুণ কাহিনি হয়ে ওঠেন। বাঁক আর উপবাঁকে দাঁড়িয়ে থাকা দৈনন্দিন জীবনের টুকরো খবর হয়ে ওঠেন। পকেটকেই নিজের প্রেমিকা হিসেবে চিহ্নিত করেন। অদ্ভুত তাঁর আত্মবোধের এই পকেট। প্রতিটি অনুভবের রঙে পিছনের দরজা খুলে দেন। হ্যাঁ সূচক স্বাদের মধ্যে না সূচক শরীরের গন্ধ স্থাপন করেন। প্রশ্নগুলি বাস্তব থেকে এলেও উত্তরগুলি জিরো অবাস্তবের। মানুষের খোঁজ মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। কী খোঁজে মানুষ নিজেই জানে না, সারা জীবনে তা খুঁজেও পায় না।
কখনো মেটাফিজিক্সের প্রভাবে সচরাচর দেখা বিষয়গুলিও পাল্টে যেতে থাকে। দৃশ্যের মাঝখানে এক বোধের দেখা পাওয়া যায়। এই বোধ কখনো কখনো তীব্র হয়ে ওঠে। এক একটি গল্পের জন্ম দেয়। গল্পগুলি কখনো কখনো মর্মভেদী দরদিয়ার কম্পনে কাঁপায়। কখনো ব্যঙ্গের চাবুক নিয়ে দাঁড়ায়। ঠোঁটকাটা বঁড়শির মতো শব্দের টোপ গিলে ফেলি। মনে মনে রক্তাক্ত হই। ‘পুরনো ধারাপাতে’ তিনি লিখেছেন:
“বাসস্ট্যান্ডের ওপারে আবার সর্বসুখ।
শিশু গাছের নীচে নন্দীবাবুর চায়ের দোকান, সেখানে
গাছের নীচে বেশ কিছু মাথা—মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।
নীচে গরম সিঙ্গাড়ার কড়াই, সকাল থেকে সন্ধে।
যুবতী সিঙ্গাড়ারা, তাক করে চোখ মারে
একে ওকে ইশারায় কথা বলে।
কী প্রবল উচ্ছ্বাস ঐ গরম তেলের।”
তখন রাস্তার ওপারে শূন্যতার মায়া কেটে নিজের অস্তিত্ব ফিরে পান কবি শিশু গাছের মধ্যে দিয়ে। অন্ধকার, ঋতুমতী বর্ষা ও যুবতী সব নিয়েই শূন্যতার পৃথিবী কবির। “এক ফর্মার হাসিতে তোমার শরীরে নির্ভেজাল একগুচ্ছ চুল” এটুকুই সাজাতে চেয়েছেন এক ফর্মার জীবনে। তাই কাটোয়া ভ্রমণও একটি কবিতা হয়ে উঠেছে।যোগ এবং ধ্যানের শিক্ষক, ব্রেথওয়ার্ক ফ্যাসিলিটেটর, মানবতার আধ্যাত্মিক জাগরণে নিবেদিত, বোধিসত্ত্ব দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত জোসেফ পি. কফম্যান তাঁর একটি গ্রন্থে লিখেছেন:
“You are not limited to this body, to this mind, or to this reality—you are a limitless ocean of Consciousness, imbued with infinite potential. You are existence itself.”
(Joseph P. Kauffman, The Answer Is YOU: A Guide to Mental, Emotional, and Spiritual Freedom)
অর্থাৎ আপনি এই দেহে, এই মনের মধ্যে বা এই বাস্তবতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নন—আপনি অসীম সম্ভাবনায় আচ্ছন্ন চেতনার সীমাহীন সমুদ্র। আপনি নিজেই অস্তিত্ব। এই অস্তিত্ব হয়ে ওঠার মধ্যেই আধ্যাত্মিক মুক্তির দেখা পেয়েছেন। পিনাকীরঞ্জন সামন্তও সেই মুক্তিকেই ধারণ করেছেন কবিতায়। তাই প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছাতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র আলোড়নও সামুদ্রিক তরঙ্গের অভিরূপ হয়ে উঠেছে। ইথার তরঙ্গে শব্দকলি ধীমানের মতোই উপলব্ধির সীমানা উন্মোচিত করেছে। ঘটনা-সুন্দরী প্রবাহ-বাসরে পৃথিবী হয়ে জেগেছে। আল্টিমেটাম নীলপায়রা দূর আকাশের নীল হয়ে উড়ে গেছে। মহাকাল মহাকাশ ইলেকট্রন প্রোটন পজিট্রন এন্ড দেন উত্তরণ যেখানে হরিদাসকেও ‘পিনাকীরঞ্জন’ করে তুলেছে। রবীন্দ্রসেতু-বিদ্যাসাগর সেতু অ্যালজেব্রার ফরমূলাকে ছাড়িয়ে মহাকালের স্রোতস্বিনীর স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। এদের দুজনকেই শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়েছেন। এই সেই অস্তিত্ব যা অনন্তের দিশারী, অসীমের প্রজ্ঞায় নিয়ম বহির্ভূত অবস্থানে স্বয়ংক্রিয়।

৫.
প্রবহমান জীবনের প্রত্যয়ভূমি রচনা
শূন্য দশকের যে ক’জন কবিকে আমরা আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারি তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সোমনাথ বেনিয়া। ‘উক্তি শ্রীবাস্তব'(২০২০) কাব্য গ্রন্থটিতে তিনি অ্যাবসার্ডবাদ এবং অ্যাবস্ট্রাক্টবাদের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। যার ফলে বিশৃংখল জীবনের দিশেহারা ক্ষুব্ধ হতাশ নিরুপায় অন্তর্জীবনের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর এই ভাবনার সঙ্গে আলবার্ট কামু, স্যামুয়েল বেকেটের ছায়াও লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে ফরাসি নাটক ‘ওয়েটিং ফর গোডো’ এবং আয়োনেস্কোর ‘রাইনোসেরা’ ও ‘দ্য চেয়ারস্’ নাটকের উদ্ভট দৃশ্যগুলি কবিতার পংক্তি বিন্যাসে প্রভাব বিস্তার করেছে। তেমনি বিমূর্তবাদে কবির ব্যক্তি অনুভূতির কণ্ঠস্বরটিই বড় হয়ে ওঠে। সেখানেই তাঁর উপলব্ধিই সত্য। তাই ভি. ই. শোয়াব বলেছেন বলেছেন: “Abstracts, mostly Nonsense art, my friend Jake calls it. But it’s not really nonsense, it’s just—other people paint what they see. I paint what I feel. Maybe it’s confusing, swapping one sense for another, but there’s beauty in the transmutation.”
(V.E. Schwab, The Invisible Life of Addie LaRue)
অর্থাৎ বিমূর্ত, বেশিরভাগই ননসেন্স আর্ট, আমার বন্ধু জেক এটাকে বলে। কিন্তু এটা আসলেই আজেবাজে কিছু নয়, এটা ঠিক—অন্য লোকেরা যা দেখে তাই আঁকে। আমি যা অনুভব করি তা আঁকি। হতে পারে এটি বিভ্রান্তিকর, একটি ইন্দ্রিয়কে অন্যটির জন্য অদলবদল করে, তবে রূপান্তরের মধ্যে সৌন্দর্য রয়েছে।
ননসেন্স আর্ট এই গ্রন্থের কবিতাকেও মনে হতে পারে। মনে হতে পারে বিভ্রান্তিকর,অসামঞ্জস্য, অসঙ্গতিপূর্ণ, এলোমেলো ও বিচ্ছিরি। কখনো তা নগ্ন বাস্তবের মুখাপেক্ষী হতে চেয়েছে।
কাব্যের নামকরণে ‘উক্তি’ শব্দটি প্রয়োগ করে বাস্তবের সঙ্গে ‘শ্রী’ যোগ করেছেন। এই উক্তি আসলে কবির কথন প্রক্রিয়া, অপরদিকে তা নাটকীয় সংলাপের প্রেক্ষণ। বাস্তবের আগে ‘শ্রী’ যোগ করার একমাত্র কারণ হল, তিনি নিজেই সেই বাস্তবের স্রষ্টা। যে বাস্তবকে সবাই চর্মচক্ষে দেখতে পায় না, তা অন্তরালেই থেকে যায়। অথবা যে বাস্তবতাকে কবিই বিনির্মাণ করেন অথবা দেখাতে চান। এই ধারার কাব্য সৃষ্টিকে বলে কিউবিজম। যে সৃষ্টিতে প্রশ্রয় পেল উদ্ভট ও বিমূর্ততা। মানবমনের জটিল স্তরগুলিকে প্রকাশ করতে চাইলেন এর মাধ্যমে। প্যারিসের কিউবিস্ট কবি ম্যাক্স জ্যাকব একটি রচনায় লিখলেন:
“Cubism is … a picture for its own sake.
Literary Cubism does the same thing in literature, using reality merely as a means and not as an end.”
(Max Jacob, The Cubist Poets in Paris: An Anthology)
অর্থাৎ কিউবিজম হল… নিজের স্বার্থে একটি ছবি।
সাহিত্য কিউবিজম সাহিত্যে একই কাজ করে, বাস্তবতাকে নিছক একটি উপায় হিসাবে ব্যবহার করে এবং শেষ হিসাবে নয়।
সুতরাং কিউবিজম পাঠক ও কবির মধ্যে একটি সেতু গড়ে তুলতে চায় যার দ্বারা শিল্পীর সৃষ্ট জগতে পৌঁছানো যায়।
শ্রীবাস্তব উক্তিগুলিতে কবির সৃষ্ট বাস্তবতার স্বরূপগুলিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক।
১) “উক্তি, একদিন মুছে যাওয়ার গল্প শোনাবে
ফিসফিস করে নয়, বরং অসহ্য চিৎকারে”
২) “উক্তি, উইঢিবিকে শালগ্রাম শিলা ভেবো
দেখবে স্পর্শ কতটা আদিম ভালোবাসার প্রচ্ছদে!”
৩) “উক্তি, ঘুমের দেশে ট্যাবলেট হৃদয়ের সাথে কী কথা বলে
প্রিয় সম্বোধনে কোষে জল জমে, শ্যাওলা পড়ে…
তোমার পিছলে যাওয়া পাণ্ডুলিপি রাখা আছে ছায়াপথে”
৪) “দৃষ্টির সাথে দৃশ্যের গেরিলা যুদ্ধ বাঁধে, ফিনফিনে আলো
নেশাতুর অবকাশে তোমার টাইটেল নিয়ে আলোচনা
এক অদ্ভুত রকমের সংগঠনের সামনে দাঁড়ায় নেটিজেন
উক্তি শ্রীবাস্তব বলে কাটাতে চেয়েছি সম্পর্কের
হ্যালুসিনেশনপর্ব”
৫) “উক্তি, বিষাদ আমার কাছে বিষ
নীলকন্ঠ হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই
কল্কের মধুতে, ধুতরার বীজে পুনর্জন্মের খসড়া রাখতে চাই না”
৬) “ওরা শ্রীবাস্তবের কথা জানে না, জানে না
কোটেশনের ভিতর অতিরিক্ত নিশ্বাস ভয়েস চেঞ্জ চায়…”
৭) “পথ হারালেও পথ থাকে, চেনা নাও হতে পারে
উক্তি বোঝে কচুবনের চেতনা জোনাকির আলো
জ্যোৎস্নার আলোয় সার্বিক বৃদ্ধি তার শেয়ারবাজার”
৮) “উক্তি একটি পাসওয়ার্ড
আবার অ্যাট দ্যা রেট অব ইয়াহু ডট কমেও আছে
মনের সহজাত ভুলে যাওয়া স্বভাবকে যা দিয়ে রাখি”
৯) “উক্তি হাই তুললে ভোরের কুয়াশা ইনফ্যাচুয়েশন
তখন সূর্যের উঠি-উঠি ভাব আকাশের মেমো নম্বর
কে নড়ে ওঠে মৃত স্বপ্নের জঠর ছিঁড়ে”
১০) “উক্তি মাঝেমধ্যে নো পার্কিং জোন
ভিতরে স্তূপাকৃতি বিষাদের চূড়া ভিতরে ডাম্প হতে থাকে
এই আগামীর আনমনা বৃষ্টি আগে থেকে অনির্ণেয়
তবে ভিজতে খারাপ লাগে না
মন আসলে অনুভূতির বাজার, যে যেমনটা কেনাকাটা করে
কিছু অনুভূতি এক্সট্রা উপপাদ্য, আনসলভড থেকে যায়
এরপরও লেটার মার্কের কাছাকাছি পৌঁছে-
”অতিরিক্ত একটি দিনের কামনায় ব্যাকুল”
একান্ত নিজস্ব অনুভূতি যার বহুমুখী অভিজ্ঞা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের দেখারও যা অগোচর, আমাদের ভাবনারও যা অগম্য, আমাদের প্রকাশেরও যা সীমাবদ্ধ—কবি তাকে গুরুত্ব দিলেন। বাহ্য রূপের অন্তরাল ভেদ করলে ভেতরে প্রবেশ করতে পারি। সেই অভিনব কৌণিক পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। আবিষ্কার করতে চাইলেন আত্মদ্রাঘিমার বিস্তৃত জগৎ। যা আমাদের কাছে অবাস্তব, জটিল, কখনো অপার্থিব অতিচেতনার বিষয় হয়ে উঠল। তবে তা মননশীলতায়, উপলব্ধির প্রাখর্যে, প্রসঙ্গচ্যুতির অবিন্যস্ত কার্যকলাপে উপলব্ধির সত্যের কাছেই দায়বদ্ধ হল। জীবনযাপনের নানা স্তরগুলি বাস্তবতাকে গ্রহণ করেই এক অন্তঃস্থিত শূন্যতাকেও ধারণ করল। ফলে চেনা জগতের মাঝেও অচেনা জগতের পদধ্বনি শোনা গেল। কবি সহজেই লিখতে পারলেন:”শূন্যস্থান হাতড়াতে-হাতড়াতে নিজের মুখে নিজের আঙুলের রক্ত দেখেছি”। খুঁটে খুঁটে উক্তিকে জপের মালায় রেখেছেন। অজ্ঞাতসারে দিনযাত্রার ইশতেহার কবির। পাশবালিশ সরে গেলে বিছানার চাদরেই নিবিড় সহবাস। বহুগামী পতিতার কোষে কামনার রিক্ত অস্থায়ী নিষিদ্ধজল। সব “গন্তব্য শেষে স্বর্গের আশ্চর্য বায়োপিক।” ৮০ পৃষ্ঠার বই। আলাদা করে কোনো কবিতার শিরোনাম ব্যবহার করতে হয়নি। প্রবহমান জীবনের প্রত্যয়ভূমি রচনা করতে উক্তি শ্রীবাস্তবের আয়োজন বাংলা সাহিত্যে একটি নব সংযোজন বলেই মনে হল।
পাবলো পিকাসো বলেছেন: “The fact that for a long time Cubism has not been understood and that even today there are people who cannot see anything in it means nothing. I do not read English, an English book is a blank book to me. This does not mean that the English language does not exist. Why should I blame anyone but myself if I cannot understand what I know nothing about?” -Pablo Picasso.
অর্থাৎ সত্য এই যে দীর্ঘকাল ধরে কিউবিজম বোঝা যায়নি এবং আজও এমন লোক রয়েছে যারা এর মধ্যে কিছু দেখতে পায় না, তার মানে কিছুই নয়। আমি ইংরেজি পড়ি না, একটি ইংরেজি বই আমার কাছে একটি খালি বই। এর মানে এই নয় যে ইংরেজি ভাষার অস্তিত্ব নেই। আমি যে বিষয়ে কিছুই জানি না তা বুঝতে না পারলে নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ করব কেন?
এই কবিতাগুলি সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। যদি আমরা না বুঝতে পারি, যদি এর ভিতর প্রবেশ না করতে পারি, যদি কিউবিজম বিষয়ে আমাদের ধারনা না থাকে, তবে সোমনাথ বেনিয়াকে আমরা দোষারোপ করব কেন? তাঁর একটা উপলব্ধির জগৎ আছে, তাঁর জগতের একটা সত্য আছে এটা আমাদেরকে মানতেই হবে। তিনি যা ভাবতে পারেন, তিনি যা বলতে পারেন, তিনি যা লিখতে পারেন—তাইতো শ্রীবাস্তব!

৬.
শূন্যবাদী কবির নিজস্ব জগৎ
দীর্ঘদিন কবিতাচর্চা করেও খুব বেশি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ করেননি এমনই একজন কবি মৃণাল মোদক। গতানুগতিক কবিতা চর্চার ধারায় তিনি নিজেকে সামিলও করতে চাননি, সর্বদা নিজস্ব একটি পথেরই অনুসন্ধান করেছেন। ৭০ দশকে যাত্রা শুরু করে আজ পর্যন্ত কবিতা নিয়েই তাঁর নিজস্ব জগতের ঠিকানা খুঁজেছেন। বাংলা ভাষার যে ক’জন কবিকে আলাদা করে ভাববার অবকাশ আছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবি মৃণাল মোদক। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর কাব্য ‘শব্দ বৃত্ত অক্ষর’ (২০২১) পাঠের পর আমার সামান্য প্রতিক্রিয়াটুকু না জানিয়ে পারলাম না।
কবি মৃণাল মোদক বিষয়কে কবিতা করেননি কবি, বরং কবিতাকেই বিষয় করে তুলেছেন। তাই তাঁর কবিতায় বিষয় খুঁজে পাই না, অথচ শূন্যবাদের নির্বিকল্প এক চেতনা প্রতিটি মুহূর্ত যাপনের প্রতিধ্বনি তুলেছে। তখন কবিতাকেই তিনি মোক্ষম করে তুলেছেন দৃশ্যকল্পের সচলতায়, আর সময়কেই নাবিক করে তুলেছেন। এই সময়েরই উপস্থাপনায় ‘নশ্বর কাহিনির নৌকা নিরুদ্দেশ অভিঘাতে একা’ বহমান হয়েছে। শূন্যবাদের ব্যাপ্তি ‘কিছুই না থাকার ভিতর পালক প্রহরে’ জারিত হয়েছে। কবিতা সেই শূন্যের-ই মগ্নতায় উদ্ভাসিত:
“গায়ে তার ছায়ার চাদর
গাছ মাটি শিকড়ে অস্পষ্ট অধরা
ধরে আছে শূন্য কয়েক টুকরো।”
সমগ্রতার মধ্যেও শূন্যতা যা এম্পটিনেসের প্রজ্ঞা থেকে উত্থিত। যাকে শব্দ অক্ষর ও ছন্দে ধরা যায় না। হওয়া কিংবা না- হওয়ার মধ্যেও তার হিসেব পাওয়া যায় না। তাকে বোঝাতে কবি তিনটি বিশেষণেই একটি পংক্তি নির্মাণ করেছেন: ‘অমর্ত্য অসীম আদিগন্ত’। তিনটি বিশেষণেই আছে অপরিমাপযোগ্য বিস্ময় ও চির কৌতূহল। কিন্তু কবির নিজের শিকড় কোথায়?
নিজের মধ্যেও যখন টান দিলেন, তখন দেখলেন সেখানেও কোনো স্থিরতা নেই। অমর্ত্য অসীমের সঙ্গেই মিলিত প্রান্তহীন একা হয়ে রয়ে গেছেন। সেই এক সত্তা যার রূপ নেই, কেবল ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময় জাগরণ। কাব্যের নাম ‘শব্দ বৃত্ত অক্ষর’ কবিতাতেই লিখলেন:
“টান দিতেই প্রান্তহীন একা, ছেঁড়া সুতো শিহরন
না আঁকা শূন্য, পরাবৃত্ত সমার্থক।
থর থর ভাঙে নামগন্ধহীন ল্যান্ডস্কেপ
কোষকলা কৌশলে কতনা ফ্ল্যাশব্যাক।।
অতঃপর যবনিকা, শব্দ বৃত্ত অক্ষর
পাণ্ডুলিপি পালকে একেকটি প্রচ্ছদ।”
‘না আঁকা শূন্য’, ‘পরাবৃত্ত সমার্থক’, ‘নাম গন্ধহীন ল্যান্ডস্কেপ’ ‘কৌশলের ফ্ল্যাশব্যাক’ তারপর যবনিকা এবং পাণ্ডুলিপির আয়োজনে পালকের এক একটি প্রচ্ছদ। শব্দ ও চিত্রকল্পের প্রতীকী ব্যবহারে বিষয়ও এখানে দাঁড়াতে পায়নি। তাই শূন্যতাও অদৃশ্য, বৃত্তও পরাবৃত্ত। অবচেতনের স্বয়ংক্রিয়তায় অ্যাবসার্ড হয়ে উঠেছে। শুধু শব্দের ব্যবহারই কতখানি মারাত্মক হতে পারে তা জানতে পারি কবির উপলব্ধিতে।
বিখ্যাত মার্কিন কবি এমিলি ডিকিনসন(১৮৩০-১৮৮৬) লিখেছেন :
“If I read a book and it makes my whole body so cold no fire can warm me, I know that is poetry. If I feel physically as if the top of my head were taken off, I know that is poetry. These are the only ways I know it. Is there any other way?”
(Emily Dickinson, Selected Letters)
অর্থাৎ আমি যদি একটি বই পড়ি এবং এটি আমার সমস্ত শরীরকে এত ঠান্ডা করে দেয় যে কোনো আগুন আমাকে গরম করতে পারে না, আমি জানি এটিই কবিতা। যদি আমি শারীরিকভাবে অনুভব করি যে আমার মাথার উপরের অংশটি খুলে ফেলা হয়েছে, আমি জানি এটি কবিতা। এই আমি এটা জানি একমাত্র উপায়। অন্য কোনো উপায় আছে কি?
এমিলি ডিকিনসনের মতোই মৃণাল মোদকের কবিতাও উপলব্ধির ভেতর শূন্যতার নিরাবয়ব প্রচ্ছদ এঁকে চলে, অভিঘাতে কম্পন তোলে, স্পর্শের উষ্ণতায় অবগাহন করায়। কবিতা হয় শুধু ভেতরের ধ্বনিময় ক্ষরণের অনির্বৃত্ত একপর্যায়। সেখানে:
“শিকড় জুড়ে শুধুই সঞ্চরণ,প্রজ্ঞাপালক,
না চেনা বৃত্তান্ত, মূলরোম আলো
মাটি মেঘ-বৃষ্টির প্রণম্য আগুন।”
মৃত্যু-মেধা-মননের মন্ত্রে অন্তঃস্থিত এই আলো আঁধারের চক্রে দুর্বার হয়ে ওঠে। কান্নার সেতু থেকে নৌকা নদীর নতজানু, জলরং কোষ, বুনন সাদা বৃক্ষের ব্যাকরণ সবই অনুধাবিত। পথহারা বাক্যের ড্যাস এবং না-মরা মৃত্যু ও লিপি ইতিহাস ক্রমান্বয়ে ঝাপটাতে থাকে, বাতিল কাগজের ব্যর্থ এক বৃত্তে। ক্লান্ত করোটি, মায়া রং নৌকা, ধুলো জীবনের পাণ্ডুলিপি, মগ্ন চেতনার বর্ণমালা সবই উন্মুখ নিবেদনে এক একটি নির্মাণ করে চলে অনন্তের সত্তার রহস্য। কবিতায় বিশৃংখলা দেখা দেয়। স্বয়ংক্রিয় অভিমুখে কবিসত্তা প্রাসঙ্গিকতা পাল্টে নেয়। বহুমুখী প্রয়োগ কুশলতায় বিক্ষিপ্ত, সংশয়-আশ্রিত, দ্বান্দ্বিক পীড়ায় আক্রান্ত হন। তাই ‘যেন’, ‘মনে হয়’, ‘কিংবা’, ‘হয়তো’ অব্যয়গুলিরও ভূরিভূরি ব্যবহার হয়। কাব্যের শেষ কবিতায় এসেও কবি পাঠকের কাছে ধরা পড়ে যান:
“হয়তো কোথাও একটা শুরু কিংবা না শুরু
তল অতল অনন্ত গভীর একাকার একসা
দেখি কেঁপে ওঠা ওলট পালট ছবি সব
ছিঁড়ে উড়ে জুড়ে যায়, দৃশ্য ছেঁড়া পরস্পর আড়ালে।
কিংবা নাভিস্নানের নিজস্ব নিয়মেই তৈরি হয় ভূমিকা
অক্ষর আগুনের সিলেবাস, যত গল্প আকাশের।
অতঃপর ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশ বৃত্ত থেকে পরাবৃত্তে
এক একটি স্ফুলিঙ্গ, যুগ যুগান্তের অখণ্ড সত্তা।”
পুনরাধুনিক পর্যায়ের মধ্যেই কবি প্রবেশ করেছেন । যুগের হতাশা ও ক্লান্তির সীমাহীন প্রাচুর্যে এক বিচ্ছিন্নতার নিরবধি ছোবলে বিপন্ন বোধ করেছেন। তাই অ্যাবসার্ড কবিতা বা শূন্যতাবাদী কবিতার আলোকে এই কবিতাগুলিও প্রভাবিত।এরকমই একজন কবি পাবলো সাবোরিওর কবিতায় এরকমই বিচ্ছিন্নতার বিমূর্ত গ্রাস দেখতে পাই। ‘এবং এর শূন্য'(And The Emptiness Of)নামে একটি কবিতার কিছুটা অংশে তিনি লিখেছেন:
“mystery is a heavy mist
pounded on our eyes
love sits
with cold legs
and the emptiness of the sand
those fingers
to carve in the skin of this earth
the folded name;
the forgotten
labyrinth of him.”
“রহস্য
আমাদের চোখের উপর একটি ভারী কুয়াশা ধাক্কা
ভালবাসা শীতল পা
এবং বালির শূন্যতা নিয়ে বসে থাকে
সেই আঙ্গুলগুলো
এই পৃথিবীর চামড়ায় খোদাই করা
নাম ভাঁজ;
তার ভুলে যাওয়া
গোলকধাঁধা।”
কবি মৃণাল মোদকও কাব্যটি শেষ করেছেন: তাত্ত্বিক কাহিনির আয়নায়—না-বিষাদ, না-আলো—না-পাওয়া মগ্নতায় নির্নিমেষ, সরল-জটিল এক নির্মোহ স্তব্ধতায়। অর্থাৎ কবির বাস্তবতা তাঁর হৃদয়ের অন্তর্গত অথবা মস্তিষ্ক শূন্যতার গভীরে অন্ধকারে, অথবা আলো-অন্ধকারে স্বয়ংক্রিয় অভিযাপনের ক্রিয়ায়। যেখানে যুক্তিও শিথিল হয়ে গেছে। উপলব্ধির সত্যতাই ইঙ্গিতের বুদবুদ হয়ে উঠেছে। সিলেবাস তৈরি করেছে অস্পষ্ট অক্ষরের আবরণে। উচ্চারণে এসেছে মগ্নতা। বাক্য গঠনে শব্দে এসেছে বিচ্ছিন্নতা। দৃশ্যে ও অদৃশ্যে ভাঙচুর ঘটেছে। কবি একাকিত্বের আশ্চর্য সহবাসে ডুবে গেছেন।
বাংলা কবিতার এই বহুমুখী ব্যাপ্তি দীর্ঘতর পথ পরিক্রমা করে চলেছে। দশক বিচারে যেমন কবিকে বন্দি করে রাখা যায়নি, তেমনি প্রতিনিয়ত বাঁকবদলের মধ্য দিয়ে তাঁর যাত্রাকেও একই ধারায় চিহ্নিত করা যায়নি। তবে বাংলা কবিতায় গতানুগতিক কবিতা চর্চার কবির সংখ্যাও কম নয়। তবে ভিন্ন পথের কবিদের পাঠক যে নেহাত কম এবং কবিও যে অনালোচিত থেকে যান তা এখানে আলোচিত কবিদের তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে। আরও বহু কবি আছেন যাঁদেরকে ব্যতিক্রমী হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্তীতে কোনো এক সময় তাঁদের কথাও বলতে হবে আমাদের।#










