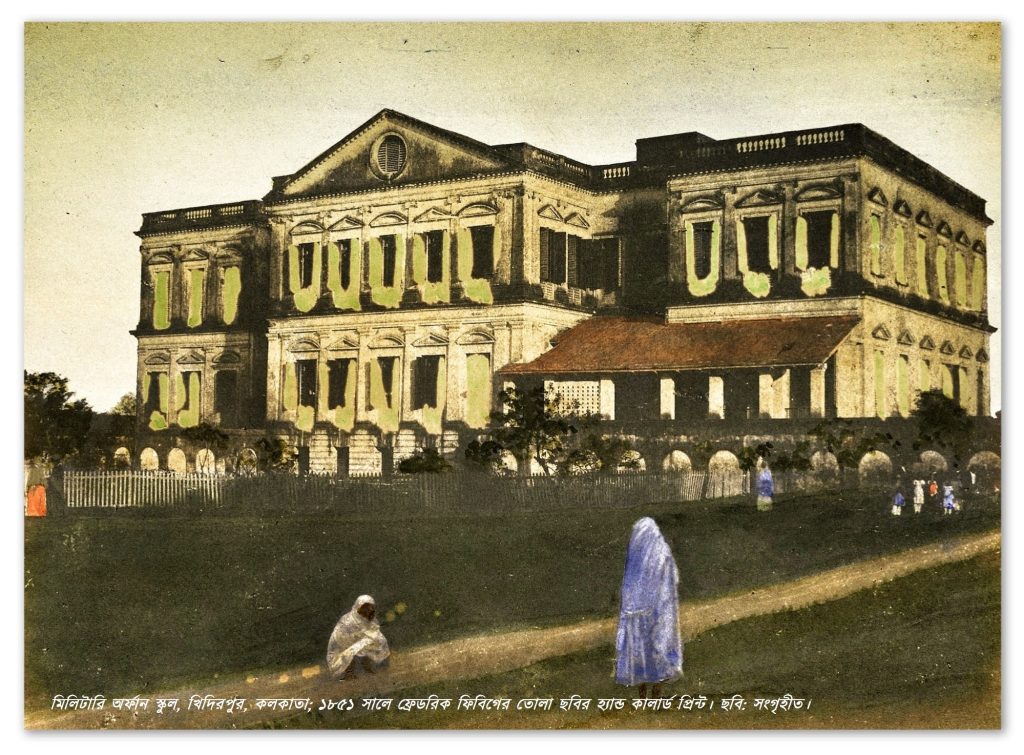বেনিয়া-শাসনের প্রথম যুগে বঙ্গদেশে ইংরেজি-শিক্ষা বিস্তারের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা কোম্পানির শাসকদের ছিল না। ১৭৫৭ সালের পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁরা ভারতের মাটিতে নিজেদের অবস্থানকে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট ছিলেন। তখন বঙ্গদেশে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত আদালতের কাজের সুবিধার জন্য পণ্ডিত-মৌলভীদের নিয়োগ করতে হত বলে তাঁরা বাংলায় সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা-চর্চায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানির রাজনৈতিক স্বার্থে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গোঁড়া ধর্মাবলম্বীদের সন্তোষ-বিধানার্থে প্রাচ্য-শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। ১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলার মুসলমান সমাজের অভিজাত-শ্রেণীর আস্থাভাজন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হেস্টিংসের কাছে মুসলমান ছাত্রদের আরবি ও ফারসি ভাষায় উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করবার আবেদন করেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, তিনিও সেই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তাই সুযোগ পাওয়া মাত্র কালবিলম্ব না করে তিনি সেই বছরেরই অক্টোবর মাসে বাংলার অভিজাত ঘরের মুসলমান ছাত্রদের ইসলামিক শিক্ষাদানের জন্য কলকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। সেখানে ছাত্রদের আকৃষ্ট করবার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। সেখানে প্রাচীন আরবি ও ফারসি রীতি অনুসারে কোরানীয় ধর্মতত্ত্ব, পাটীগণিত, তর্কশাস্ত্র ও ব্যাকরণ পড়ানো হত; এবং একজন মৌলভী সেই প্রতিষ্ঠানটির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এরপরে মুসলমানদের মতোই হিন্দু-সম্প্রদায়কে খুশি করবার জন্য লর্ড হেস্টিংসের সমর্থনে ও জোনাথান ডানকানের উদ্যোগে বেনারসে ১৭৯১ সালে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। মনুর বিধানানুসারে সেখানে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হত এবং বৈদ্যশাস্ত্রের অধ্যাপকরা ছাড়া সেখানকার অন্যান্য অধ্যাপকেরা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তবে তখন শুধুমাত্র বেনারসে নয়, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সংস্কৃতজ্ঞ কোলব্রুক সাহেব কোম্পানি সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিলেন। ঐভাবেই তখন কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে হেস্টিংসের আনুকূল্যে একটি ‘প্রাচ্য’ গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল এবং সেই গোষ্ঠীটি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে বঙ্গদেশের শিক্ষা-কাঠামো নির্মাণে নিজেদের প্রভাব-বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিল। (আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা, কুমুদকুমার ভট্টাচার্য, পৃ- ২৪) প্রকৃত পক্ষে প্রাচ্য শিক্ষা-চর্চার জন্য সেই দুটি কলেজ স্থাপন করা ছাড়া ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্য কোনো ধরণের শিক্ষানীতি সেই সময়ে ছিল না। তখন সাম্রাজ্য-শোষণের স্বার্থে – “তদানীন্তন রাজপুরুষগণ হিন্দু ও মুসলমানগণের প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি হস্তার্পণ করিতে অতীব কুন্ঠিত ছিলেন।” (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ- ৭০) অতীতে সেই একই কারণেই বৃটেনে চার্লস গ্রান্ট ও উইলিয়ম উইলবার ফোর্সের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয়দের খৃষ্টান করবার আগে বিজয়ী জাতির ভাষা ইংরেজির মাধ্যমে ইউরোপীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত করবার জন্য অবৈতনিক ইংরেজী-স্কুল স্থাপন করবার পরামর্শ দিয়ে চার্লস গ্রান্ট যখন ১৭৯২ সালে তাঁর ‘Observations’ নামক পুস্তিকাটি (পুরো নাম – ‘Observations on the state of society among the Asiatic subjects of Great Britain, particularly with respect to their morals and on the means of improving them’) লিখেছিলেন, এবং গ্রান্টের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উইলবার ফোর্স যখন ভারতীয়দের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং ধর্মচেতনা ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতির জন্য সরাসরি ইংল্যাণ্ড থেকে একদল শিক্ষক ও মিশনারি ভারতে পাঠাবার জন্য বৃটিশ-পার্লামেন্টে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তখন তাঁদের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতের ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের মনে আঘাত হানবার জন্য কোম্পানির কর্তারা অনিচ্ছুক ছিলেন বলেই কোম্পানির ১৭৯৩ সালের সনদে ভারতের শিক্ষা-বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তখন বাংলা তথা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য একদিকে যেমন কোম্পানি-সরকারের আনুকূল্যে ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা-চর্চায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি লর্ড ওয়েলেসলীর উদ্যোগে কোম্পানির তরুণ ইউরোপীয় কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নিতান্ত সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও সেই কলেজটি কিন্তু খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকে বাংলা গদ্য-বিকাশের প্রথমপর্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ইংরেজদের ‘প্রাচ্য’-গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক লর্ড মিন্টো ১৮১১ সালের ৬ই মার্চ তারিখের ‘মিনিট’-এ ভারতে প্রাচ্য শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহের অভাব দেখা দেওয়ার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছিলেন যে, তখন ভারতীয়দের মধ্যে প্রাচ্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আলোচনা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছিল, এবং সেটার ফলে শেষপর্যন্ত ভারতের প্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থগুলি ক্রমেই বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছিল। মিন্টো জানিয়েছিলেন যে, ইংরেজ সরকার যদি সে বিষয়ে অবিলম্বে কোন সাহায্য না করে, তাহলে পাঠ্যগ্রন্থ ও উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার সমাপ্তি ঘটবে। (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ: ৭৫-৭৬) তাই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, নদীয়ার নবদ্বীপে ও ত্রিহুতের অন্তর্গত ভাউর নামক জায়গায় সংস্কৃত কলেজ এবং ভাগলপুর ও জৌনপুরে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়োজন রয়েছে। মিন্টোর সেই প্রস্তাবে অবিলম্বে কোনো ফল না হলেও কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী ঊনিশ শতকের ভারতের শিক্ষা-সমস্যার প্রতি আর উদাসীন থাকতে পারেননি, এবং এর ফলে কোম্পানির ১৮১৩ সালের সনদে (Charter Act) ৪৩নং ধারায় ভারতে শিক্ষার প্রসারের জন্য একলক্ষ টাকা বরাদ্দ করে বলা হয়েছিল, “প্রত্যেক বৎসরে ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা স্বতন্ত্র রাখতে হবে এবং তা ভারতের শিক্ষিত অধিবাসীদের উৎসাহদান, সাহিত্যের উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবন এবং ভারতের বৃটিশ-শাসিত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের জন্য ব্যয় করা হবে।” (Mother Tongue & Equality of Opportunity in Education, B. S. Goel & S. K. Saini, P- 10) কোম্পানির সনদ-আইনের শিক্ষা-বিষয়ক এই ধারাটি দ্ব্যর্থবোধক ও গভীর হতাশাব্যঞ্জক ছিল। কারণ, কোম্পানি কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র সমাজের অভিজাতশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্পর্কেই চিন্তা করেছিলেন। সনদে উল্লেখিত – ‘শিক্ষিত ব্যক্তিদের উৎসাহদান’ ও ‘বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন’ – এই বাক্যাংশ দুটিকে একত্রে পাঠ করলে এই সত্যিটাই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে, তখন যাঁরা অর্থ ও বর্ণকৌলীন্যের জোরে সুদূর বৈদিক যুগ থেকে শিক্ষাকে নিজেদের শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তাঁদের জন্যই কোম্পানী-সরকারের যত মাথাব্যথা ছিল; কিন্তু যাঁরা কোনোদিনই শিক্ষার অধিকার পাননি, তাঁরা বঞ্চিত হয়েই থেকে গিয়েছিলেন। তাঁদেরকে শিক্ষিত করবার বিষয় নিয়ে দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত করা হয়নি; শুধু শিক্ষার ধরন ও ভাষা-মাধ্যম নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। সনদ-আইনে উপরোক্ত দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করবার ফলে সেই টাকা কি ধরনের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে, এবং বাস্তবে শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম কি হবে – সেসব নিয়ে তখন প্রবল মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল।
ঊনিশ শতকের বঙ্গদেশে থাকা খৃষ্টান মিশনারীদের একাংশের উদ্যোগে মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাদান করবার ব্যাপক প্রয়াস শুরু হয়েছিল। বাংলায় থাকা ইংরেজ-ছাত্রদের জন্য উইলিয়ম কেরির উৎসাহে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকেরা যখন বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন, শ্রীরামপুরের মিশনারীরা (১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল) তখন কেরির অধিনায়কত্বে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষা বিস্তারের সর্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেটাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। তখন তাঁরা একদিকে যেমন আঞ্চলিক ভাষার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ও আধুনিক শিক্ষাদানের পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি মাতৃভাষায় পুস্তক প্রকাশ করবার জন্য ১৮০০ সালে বাংলা হরফের ছাপাখানাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আধুনিক জ্ঞানের আলো দেশীয় সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো বিদেশী ভাষার মাধ্যমে সেকাজ সম্ভব নয় – এই অভিমত ব্যক্ত করে ডাঃ জোশুয়া মার্শম্যান ইংল্যাণ্ডের মিশনারী কর্তৃপক্ষের কাছে ‘মিনিট’ পাঠিয়েছিলেন এবং সেই ‘মিনিট’-এ ব্যক্ত অভিমতের উপরে ভিত্তি করেই ১৮১৬ সালে তিনি – ‘Hints relative to the Native Schools together with the outline of an institution for their expansion and management’ – নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। ভারতবর্ষ তথা বাংলায় আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে সেই ‘মিনিট’ ও পুস্তিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১৩ সালে কোম্পানির সনদ-আইন গৃহীত হওয়ার পরে ভারতে আধুনিক শিক্ষা-প্রসারের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সর্বপ্রথম মার্শম্যানই তাঁর সেই ‘মিনিট’-এ উপস্থিত করেছিলেন। সেখানে জনশিক্ষার জন্য যেসব সুপারিশ করা হয়েছিল, সেগুলির অনেকগুলিই পরবর্তীকালে ১৮৫৬ সালে ‘উডের ডেসপ্যাচ’ আইনে গ্রহণ করা হয়েছিল। অবশ্য মার্শম্যানের সেই পরিকল্পনার পিছনে মাতৃভাষার মাধ্যমে বঙ্গদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য থাকলেও তাঁর সেই ‘মিনিট’-এর ঐতিহাসিক মূল্যকে কিন্তু কোনোভাবেই অস্বীকার করা চলে না। কারণ, ঊনিশ শতকের বাংলার কৃষিজীবী মানুষের স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা সেই সর্বপ্রথম তাঁর ‘মিনিট’-এ উপস্থিত করা হয়েছিল। নিজের ‘Hints’ নামক পুস্তিকায় মার্শম্যান বঙ্গদেশে ইংরেজিভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করবার জন্য সেকালের কিছু ব্যক্তির চেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করে লিখেছিলেন, “প্রথমেই একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে হলে তাঁদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমেই করতে হবে। ভারতবর্ষের অথবা যেকোনো দেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষার অথবা ইংরেজিভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করলে সেটা প্রতারণামূলক কাজ করা হবে।” সুতরাং তাঁর মতে – “এমনভাবে শিক্ষার মাধ্যম নির্বাচন করা উচিত যাতে দেশের মানুষ পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে সুখী হতে পারেন।” (History of Serampore Mission, J. C. Marshman, Vol. I, P- 63) তাই তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন যে, ভারতের মানুষের জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, এবং সেটা মাতৃভাষার মাধ্যমেই সার্থক হতে পারে; বিদেশী ভাষার মাধ্যমে নয়। সেই সময়কার প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের জন্য তিনি সরল অঙ্ক, মাতৃভাষার ব্যাকরণ ও বিশুদ্ধ বানান শেখবার বিষয়ের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন; এবং উচ্চশিক্ষার জন্য ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই পরামর্শ তখন অরণ্য রোদনে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। ঊনিশ শতকের বাংলার ‘নবজাগরণের’ নায়কেরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের জন্যই মার্শম্যানের সেই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেননি। তাঁরা কলকাতায় ও কলকাতার আশেপাশে বিভিন্ন নগরে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা-প্রসারের জন্য বিভিন্ন ইংরেজি-স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং কলেজ-স্থাপনে অগ্রণী হয়েছিলেন। বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল ১৮১৪ সালে কুড়ি হাজার টাকা দান করেছিলেন। ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি তারিখে রামমোহন-গোষ্ঠীর ‘আত্মীয়সভা’ ও রাধাকান্ত-গোষ্ঠীর ‘ধর্মসভা’র অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের সম্মিলিত চেষ্টায় কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যেকার ধর্মগত বিভেদ কিংবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ধর্মীয় গোঁড়ামী – নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ পূরণ করবার জন্য সেই কলেজ স্থাপনের পথে কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮১৬ সালের ১৪ই মে তারিখে কলকাতায় যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সভার বিবরণ দিতে গিয়ে ওই সভার আহ্বায়ক – তৎকালীন কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডোয়ার্ড হাইড ইস্ট, ১৮ই মে তারিখে বিচারপতি হ্যারিংটনকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, “এই সভার একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, নানা জাতির লোক – যাঁহারা একত্রে বসিয়া ভোজন করিবেন না – তাঁহারাও তাঁহাদের শিশুদের একত্রে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার জন্য এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন।” (বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ- ১২২) দশজন ইউরোপীয় ও ঊনিশজন দেশীয় ধনী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলীতে – ‘আত্মীয়সভা’ ও ‘ধর্মসভা’ – উভয় সভারই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা ছিলেন। হিন্দু কলেজের পরিচালকমন্ডলীতে থাকা দেশীয় ব্যক্তিরা ছিলেন – চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রঘুমণি বিদ্যাভূষণ, গোপীমোহন ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রামতনু মল্লিক, অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল দে, রাজা রামচাঁদ রায়, রামগোপাল মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক, চৈতন্যচরণ শেঠ, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, রামরতন মল্লিক ও কালীশঙ্কর ঘোষাল। তখন হিন্দু কলেজ-স্থাপনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করে বলা হয়েছিল, “বিশিষ্ট হিন্দু-পরিবারের সন্তানদের ইউরোপ ও এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়সমূহ ইংরেজিভাষায় ও ভারতীয় ভাষাসমূহের মাধ্যমে শিক্ষাদান করাই হল এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।” (হিন্দু কলেজের ইতিহাস, সুপর্ণা ঘোষ ও অশোকলাল ঘোষ, দেশ, ১৩তম সংখ্যা, ৪১তম বর্ষ, ২৬শে জানুয়ারি ১৯৭৪ সাল, পৃ- ১০৯৬) তাই সেকালের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রায় সকলেই ধনিক-পরিবারের সন্তান ছিলেন। ইংরেজিভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে তাঁরা অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তখনকার হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র লিখেছিলেন, “সমস্ত দিক থেকেই আমরা নিরাপদ। সাহিত্য ও বিজ্ঞানে আমরা ক্রমেই উন্নতি করছি এবং যতদিন আমরা বৃটিশ-পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করব ততদিন উন্নতি করতেই থাকব।” (The Days of John Company, Edited by A. Dasgupta, P- 68)
১৮২২ সালে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রামমোহন রায় তাঁর নিজের ব্যয়ে কলকাতার হেদুয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অ্যাংলো হিন্দু স্কুল স্থাপন করেছিলেন। সেখানেও শুধুমাত্র তখনকার বিত্তশালী ও সম্ভ্রান্তবংশীয় ঘরের সন্তানেরাই অধ্যয়ন করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথও সেই স্কুলেই পড়াশোনা করেছিলেন। ১৮২৭ সালে রেভারেণ্ড অ্যাডাম রামমোহনের সেই বিদ্যালয় সম্পর্কে লিখেছিলেন, “এই বিদ্যালয়ে দু’জন শিক্ষক আছেন; তাঁদের একজনকে মাসিক ১৫০ টাকা ও অন্যজনকে মাসিক ৭০ টাকা মাইনে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে ৬০ থেকে ৮০জন হিন্দু বালক ইংরেজিভাষায় শিক্ষালাভ করে।” (রাজা রামমোহন, ঋষি দাস, পৃ- ১২৪) তাছাড়া রামমোহন রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফকে কলকাতায় ‘জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউসন’ নামের একটি ইংরেজি ভাষার বিদ্যালয় স্থাপনের কাজেও সাহায্য করেছিলেন। রামমোহন রায় বঙ্গদেশে ইংরেজিভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের একজন প্রভাবশালী সমর্থক ছিলেন। (History of Indian Social and Political Ideas, B. B. Majumdar, P- 71) সুতরাং ঊনিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকে বঙ্গদেশে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, তৎকালীন বিত্তবান জমিদার ও মধ্যশ্রেণী ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণীর পক্ষে সেটার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। ফলে বাংলার রায়ত-কৃষকের ঘরের সন্তানেরা বা সাধারণ ঘরের সন্তানেরা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, এবং তাঁরা চির-অন্ধকারেই থেকে গিয়েছিলেন।। তখনকার বিত্তশালী শ্রেণীর আগ্রহে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বঙ্গদেশে যখন ইংরেজিভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটছিল, তখনো পর্যন্ত বৃটিশ সরকার ভারতের শিক্ষা-বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেনি। ১৮১৬ সালের আগে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে শিক্ষাবিষয়ে কোনো ধরণের ঐকমত্য ছিল না। তখন তাঁরা মূলতঃ দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন – তাঁদের মধ্যে একদল আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ইত্যাদি প্রাচ্যভাষার মাধ্যমে ভারতে উচ্চতর প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন; এবং অন্যদল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ভারতে ইউরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিক্ষার সপক্ষে ছিলেন। তাঁদের মধ্যেকার সেই অন্তর্বিরোধকে কোম্পানির সনদ-আইন আরো তীব্রতর করে তুলেছিল। সেই আইনে – ‘শিক্ষিত অধিবাসীদের উৎসাহদান’, ‘সাহিত্যের উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবন’, ‘বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন ও বিস্তার’ – ইত্যাদি দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহৃত হওয়ার ফলে উপরোক্ত উভয় পক্ষই নিজের নিজের মতানুযায়ী সেই আইনকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে প্রাচ্যপন্থীরাই তখন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। ১৮২৩ সালের ১৭ই জুলাই তারিখে একটি সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে দশজন ইউরোপীয় সদস্য নিয়ে ‘General Committee of Public Instruction’ নামের একটি কমিটি গঠন করে তাঁদের হাতে বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল। সেই কমিটির বিভিন্ন পদে ও সদস্যরূপে যাঁরা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা হলেন – জে. এইচ. হ্যারিংটন: সভাপতি; জে. পি. লারকিন্স; ডাব্লিউ. বি. মার্টিন; ডাব্লিউ. বি. বেলি; এইচ. সেক্সপীয়ার; এইচ. ম্যাকেঞ্জী; এইচ. টি. প্রিন্সেপ; জে. সি. সি. সাদারল্যাণ্ড; এ. স্টার্লিং এবং এইচ. এইচ. উইলসন: সম্পাদক। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ১৮৩৪ সালে লর্ড বেরিংটন মেকলে সেই কমিটির সভাপতিরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। (আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা, কুমুদকুমার ভট্টাচার্য, পৃ- ২৮)
জেনারেল কমিটির সদস্যদের মধ্যে প্রাচ্যভাষা ও প্রাচ্যশিক্ষার বিষয়ে ভিন্নমত থাকলেও পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের বিষয়ে কোন ধরণের মতবিরোধ ছিল না। তাছাড়া সেই উভয় গোষ্ঠীই মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিরোধী ছিলেন। ১৮২৩ সালের একটি সরকারি নির্দেশনামার মাধ্যমে জেনারেল কমিটিকে দেশীয় ব্যক্তিদের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল। তখন ওই কমিটির মধ্যে প্রাচ্যপন্থী সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার ফলে প্রাচ্য-শিক্ষানুরাগী উইলসন ও প্রিন্সেপের নেতৃত্বে ক্ল্যাসিক্যাল অর্থাৎ সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষার মাধ্যমে প্রাচ্য-কলাবিদ্যা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। বৃটিশ-পার্লামেন্ট কর্তৃক ভারতের শিক্ষাখাতে বাৎসরিক বরাদ্দ একলক্ষ টাকা হিসাবে তিন বছরের (১৮২১-১৮২৩ সাল) তিনলক্ষ টাকার মধ্যে প্রাপ্ত ২,৬৬, ৪০০ টাকা তাঁরা সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয় করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। উইলসন ও প্রিন্সেপ সংস্কৃত ও আরবি ভাষার মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-চর্চায় যত্নশীল হয়েছিলেন। সেই কাজের জন্য প্রথমে তাঁরা কলকাতার মাদ্রাসা ও কাশীর সংস্কৃত কলেজের সংস্কারসাধন করেছিলেন, এবং এরপরে তাঁরা কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ও তাঁদেরই উদ্যোগে কলকাতায় ১৮২৪ সালে সেই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক বহু ইংরেজি-গ্রন্থ তাঁরা সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় প্রকাশ করিয়েছিলেন। তাছাড়া, তাঁদেরই উদ্যোগে প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবি-গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু ঐভাবে প্রাচ্যভাষায় বিদ্যাদানের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় এবং ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের প্রতি জেনারেল কমিটির অনীহা – দেশীয় ভূস্বামী-বণিক-ধনিকশ্রেণীকে তাঁদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ফলে তাঁরা রামমোহনের রায়ের নেতৃত্বে জেনারেল কমিটির প্রাচ্য-বিদ্যাদান ও ভাষানীতির-বিরোধিতায় আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কোম্পানির শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য, শিক্ষার ভাষামাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা-বিস্তারের পদ্ধতি প্রভৃতি প্রশ্ন নিয়ে ঊনিশ শতকের কলকাতায় সেই শিক্ষা-আন্দোলনটি গড়ে উঠেছিল। সেই শিক্ষা-আন্দোলনে শিক্ষার জন্য ভাষার মাধ্যমের প্রশ্নটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্জন করেছিল। সেই প্রশ্নের ফলে তখন তিনটি মতের সৃষ্টি হয়েছিল। লর্ড বেন্টিঙ্ক, লর্ড মেকলে, রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ, রাজা রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ প্রমুখ এবং সমকালীন খৃষ্টান মিশনারীদের একাংশ ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে ছিলেন। হেস্টিংস, জোনাথান, কোলব্রুক, মিন্টো, উইলসন, প্রিন্সেপ প্রমুখ ইউরোপীয় রাজকর্মচারীরা সংস্কৃত ও আরবি ভাষার সপক্ষে ছিলেন। মনরো, এলফিনস্টোন, কেরি, মার্শম্যান, অ্যাডাম, ডিরোজিও প্রমুখ সমেত তৃতীয় দলটি মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু প্রথম দুটি দলের তুলনায় তৃতীয় দলটি দুর্বল হওয়ার ফলে তখন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-বিস্তারের দাবিটি উপেক্ষিত হয়েছিল। বলাই বাহুল্য যে, রামমোহন যদি সেই দাবি সমর্থন করতেন, তাহলে তৎকালীন গ্রামবাংলা আধুনিক ভাবধারায় উদ্দীপ্ত হয়ে সামন্ত-শৃঙ্খলকে ভেঙে ফেলতে সমর্থ হত। তবে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রচলনের ব্যাপারে উক্ত তিন দলের মধ্যে কিন্তু কোনো ধরণের মতপার্থক্য ছিল না। সেকালের দেশীয় ভূস্বামীশ্রেণীর দুই গোষ্ঠী, অর্থাৎ রামমোহন-দ্বারকানাথের ‘আত্মীয়সভা’ এবং রাধাকান্ত-ভবানীচরণের ‘ধর্মসভা’র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই ইংরেজিভাষায় ইউরোপীয় বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়গুলি অধ্যয়নের পক্ষপাতী ছিলেন। ওই উভয় গোষ্ঠীর কাছেই ইংরেজি-শেখার অর্থ ছিল – চাকরি, অর্থ ও সামাজিক সম্মানলাভ। “ইংরাজি বিদ্যা দেশে প্রচলিত হইবা মাত্র লোকে দেখিতে পাইল যে, ইংরাজেরা সমুদ্রপার হইতে নানাবিধ অদ্ভুত সামগ্রী আনিয়াছেন, তার মধ্যে এও একটা অত্যন্ত অপরূপ সামগ্রী। অতি সহজে এ একটা পেট ভরিবার উপায়। এই বিদ্যার উপার্জনে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ কড়ি খরচ করিতে হয় বটে; কিন্তু তারপর ইহা বেচিয়া বা ইহার বিনিময়ে বা ইহার নামে যথেষ্ট কড়ি ঘরে আইসে। অর্থোপার্জনের যত পন্থা দেশের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে এইটাই সবচেয়ে সহজ পন্থা হইল। ইহাতে অধিক মূলধনের দরকার হয় না। ইহাতে অধিক ব্যবসায় বুদ্ধি আবশ্যক হয় না, এবং সবচেয়ে সুবিধা – ইহাতে দেউলিয়া হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না।” (রামেন্দ্র-রচনাসংগ্রহ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল সম্পাদিত, পৃ- ৪৯৮) তাই বঙ্গদেশে ইংরেজিভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের দাবি করে রামমোহন রায় ১৮২৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে লর্ড আমহার্স্টকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, “যদি ইংরাজ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ রাখা উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে প্রাচীন স্কুলমেনদিগের অসার বিদ্যার পরিবর্তে বেকনের প্রবর্তিত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত হইতে না দিলেই হইত, কারণ প্রাচীন জ্ঞানই অজ্ঞতাকে বাহাল রাখিত। সেইরূপ এদেশীয়দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখা যদি গভর্ণমেন্টের আকাঙ্ক্ষা ও নীতি হয়, তাহা হইলে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় তাহার উৎকৃষ্টতর উপায় আর নাই। তৎপরিবর্তে এদেশীয়দিগের উন্নতি বিধান যখন গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা বিষয়ে উন্নত ও উদার রীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যদ্দ্বারা অপরাপর বিষয়ের সহিত, গণিত, জড় ও জীব-বিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীরস্থান-বিদ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে অর্থ এখন প্রস্তাবিত কার্য্যে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইউরোপে শিক্ষিত কতিপয় প্রতিভাশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে ও ইংরাজী শিক্ষার জন্য একটি কালেজ স্থাপন করিলে ও তৎসঙ্গে পুস্তকালয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রাদি, প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল দিলেই পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।” (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ- ৮২)
সেই সময়কার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রধানেরা, অর্থাৎ ‘ধর্মসভা’র নেতারাও নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে বঙ্গদেশে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের প্রচেষ্টাকে সোচ্চারে সমর্থন করেছিলেন। আর সেই কারণে অর্থকরী বিদ্যা-উপার্জনের আবশ্যকতাকেও তাঁরা শাস্ত্রসিদ্ধ বলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ‘ধর্মসভা’র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘কলিকাতা কমলালয়’ গ্রন্থে লিখেছিলেন, “অতএব অর্থকরী বিদ্যোপার্জনের আবশ্যকতা আছে তাহা শাস্ত্রসিদ্ধি বটে এবং যখন যিনি দেশাধিপতি হয়েন তখন তাহাদিগের বিদ্যাভ্যাস না করিলে কি প্রকারে রাজকৰ্ম্ম নির্ব্বাহ হয় ইহাতে আমার মতে কোন দোষ দেখি না।” (কলিকাতা কমলালয়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ- ১২) সমকালীন তিলক-শোভিত হিন্দু পণ্ডিতেরা ও হ্যাট-কোট-প্যান্ট পরিহিত কালো চামড়ার দিশি সাহেবেরাও অর্থকে পরমার্থ বলে মনে করেছিলেন; এবং সেই কারণে মাতৃভাষাকে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়ার ব্যবস্থায় তাঁরা সকলেই একমত ছিলেন। তাঁদের কাছে ইংরেজি ভাষা রাজার ভাষা, আর বাংলাভাষা লেংটি-পরা মানুষের লাঙলের ভাষা ছিল। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলা যেতে পারে, প্রাক-বঙ্কিমযুগে – “বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্বর জ্ঞান করিতেন।” (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩তম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ- ৮৯২) শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগে বঙ্গদেশে ইংরেজি ভাষায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসার নয়, শ্বেতাঙ্গ-সরকার যাতে প্রাচ্য-শিক্ষাদানের নীতি পরিত্যাগ করে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করে সনদ-আইনে বরাদ্দ বার্ষিক একলক্ষ টাকা ব্যয় করে, সেই কারণে রামমোহন তাঁর পূর্বোক্ত চিঠিতে লর্ড আমহার্স্টের কাছে আবেদন জানিয়ে লিখেছিলেন, “আমরা অবগত হয়েছি যে, ইংলণ্ডের সরকার ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষার জন্য বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করেছিলেন। আমরা নিশ্চিতভাবে আশা করেছিলাম যে গণিত, জড় ও জীব-বিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীর-স্থান-বিদ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষাদানের কাজে প্রতিভাধর ব্যক্তি ও শিক্ষাবিদকে এদেশে নিয়োগের জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হবে; কারণ বিজ্ঞান বিষয়সমূহে উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা ইউরোপীয় জাতিসমূহ পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অধিবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে।” (The English Works of Raja Rammohun Roy, Edited by K. D. Nag & D. Burman, Part IV, P- 3) কিন্তু ইউরোপীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য রামমোহন দাবি করলেও তখন প্রাচ্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য জেনারেল কমিটির উদ্যোগে ১৮২৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কলকাতায় মাদ্রাসার জন্য নতুন গৃহ নির্মাণ করা শুরু হয়েছিল, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং কিছুদিন পরেই ইংরেজিভাষার শিক্ষাকে কলেজের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যদিও তখন সেই অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল, তবে তা সত্ত্বেও শিক্ষাখাতে বরাদ্দ টাকার অধিকাংশ প্রাচ্য শিক্ষার উন্নয়নেই ব্যয় করা হয়েছিল। অথচ বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য জেনারেল কমিটির কাছে কয়েকটি শিক্ষা-প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। মাতৃভাষায় আধুনিক শিক্ষার কাঠামো গড়ে তোলার জন্য জন. পি. শেক্সপীয়ার কর্তৃক ১৮১৩ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে উপস্থাপিত প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, প্রথম স্তরে প্রত্যেকটি থানা এলাকায় একটি বাংলা স্কুল, দ্বিতীয় স্তরে প্রত্যেকটি জেলার সদর-শহরে দুটি করে বাংলা স্কুল এবং প্রাদেশিক আদালত অবস্থিত রয়েছে এমন ছ’টি বড় শহরে ছ’টি বাংলা স্কুল স্থাপন করা হোক। ১৮২৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরি কর্তৃক লিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, দরিদ্রশ্রেণীর জন্য জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং দেশীয় ব্যক্তিদের মাতৃভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞান-শিক্ষা দেওয়া হোক। এখানে লক্ষ্যণীয় যে – মার্শম্যান, জন. পি. শেক্সপীয়ার, কেরি, ডিরোজিও প্রমুখরা তখন মাতৃভাষায় আধুনিক শিক্ষাদানের দাবি করলেও আমহার্স্টের কাছে লিখিত পূর্বোক্ত চিঠিতে রাজা রামমোহন রায় কিন্তু সেই দাবি উত্থাপন করেননি। অর্থাৎ তিনি দেশের মাটির পরিবর্তে বিদেশে নির্মিত টবে ফুল ফোটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডিরোজিওর শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা বাংলারই মাটির রসে সিক্ত ছিল।
একজন শিক্ষক হিসাবে ডিরোজিও সমকালীন বঙ্গদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। ১৮২৬ সালে প্রকাশিত ‘Education in India’ নামক প্রবন্ধে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর লব্ধ জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনার রূপরেখা পাওয়া যায়। তাতে ‘Indian Magazine’ পত্রিকায় প্রকাশিত শিক্ষা-বিষয়ক একটি প্রবন্ধের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ডিরোজিও বলেছিলেন যে, লেখক উক্ত প্রবন্ধে দেশীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা (‘The necessity and benefit of Local Education’) সঠিকভাবে দেখালেও ভারতে ইউরোপীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (‘necessity of a European Education’) রয়েছে; এবং লেখক পক্ষপাতহীন মনোভাব নিয়েই দেশীয় শিক্ষার বিষয়টি বিচারকালে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন (‘the subject of Local Education has been very dispassionately and ably treated by the writer’)। অর্থাৎ ডিরোজির মনে করতেন যে, বঙ্গদেশের মাটিতে ইউরোপীয় জ্ঞানের বীজ রোপণের লক্ষ্য নিয়েই দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত। (রামমোহন-ডিরোজিও: মূল্যায়ন, কুমুদকুমার ভট্টাচার্য, ২য় সংস্করণ, পৃ- ৬১) তবে তখন শুধু ডিরোজিও নন, তাঁর ছাত্ররাও নিজেদের শিক্ষকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাদানের দাবির সমর্থনে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। সেই কারণেই ১৮৩৮ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত ‘সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা’র অধিবেশনে ডিরোজিওর প্রস্তাবিত দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার রূপরেখাকে বিস্তৃত করে ডিরোজিওর শিষ্য উদয়চন্দ্র আঢ্য দেশীয় ব্যক্তিদের জন্য মাতৃভাষা-চর্চা ও সেটার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত যে প্রস্তাবটি পাঠ করেছিলেন, তাতে – ‘যাহাতে স্বদেশীয় ভাষায় বাঙ্গালিদিগের সুশিক্ষা হয়’ – সেই উদ্দেশ্যে উক্ত লেখক তথ্য-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের ফলেই ইউরোপীয়দের অগ্রগতি ঘটেছিল এবং সেই সময়কার প্রত্যেক দেশেই মাতৃভাষায় আধুনিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু সমকালে বঙ্গদেশে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা – “বাঙ্গালা ভাষায় কোনো প্রয়োজন নিষ্পাদন হইতে পারিবেক না ইহা ভিন্ন মনে অন্য কদাচ স্থান দেন না।” (রামমোহন-ডিরোজিও: মূল্যায়ন, কুমুদকুমার ভট্টাচার্য, ২য় সংস্করণ, পৃ: ৬১-৬২)
বঙ্গদেশে ইংরেজি ভাষায় ইউরোপীয় শিক্ষাদানের প্রস্তাবের উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেকলে বলেছিলেন, “আমাদের এখন এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যাঁরা আমাদের হবে এবং আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোককে শাসন করছি সেই শাসিতদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানকারী হবে। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা হবে রক্তে রঙে ভারতীয়, আর রুচিতে, মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।” (A Student’s History of Education in India: 1800-1965, S. Nurullah & J. P. Naik, P- 86) অর্থাৎ, বাঙালী জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর জগতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো মহৎ পরিকল্পনা নয়, শুধু ঔপনিবেশিক স্বার্থেই একদল হ্যাট-কোট-প্যান্ট পরিহিত দেশীয় – “ইংরেজ-ভক্ত কেরাণী-দোভাষী সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এদেশে ইংরেজি-শিক্ষার প্রস্তাবনা। মেকলে এমন একদল শাসক সমর্থক দেশীয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যাঁরা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক অটুট রাখবেন। তাই ইউরোপের ‘এলিট’ সমাজ দেশীয় ‘এলিট’ তৈরি করায় মনোনিবেশ করলেন। তাঁরা সম্ভাবনাময় কিশোরদের বেছে নিলেন। উত্তপ্ত লোহাকে যেমন পিটিয়ে নিজের মনোমত জিনিস তৈরি করা হয় তেমনি তাদেরকে পশ্চিমী সংস্কৃতিতে দীক্ষা দেওয়া হল।” (বাংলার নবজাগৃতি, বিনয় ঘোষ, পৃ- ১৫২) মেকলের নিকটাত্মীয় চার্লস ট্রেভেলিয়ানও একই প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, “আমাদের সংরক্ষণে থাকলেই তাঁদের দেশের উন্নয়ন ঘটতে পারে – একথা জানেন বলেই শিক্ষিত ব্যক্তিরা আমাদের অনুরক্ত থাকবেন।” (বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, বিনয় ঘোষ, পৃ- ১৯৮) তাছাড়া তাঁর মতে, “এই ইংরেজি ছাঁচে গড়ে-ওঠা মানুষগুলো স্বাধীন কোন দেশীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনায় ভীত সন্ত্রস্ত। কারণ যে বিদেশী শিক্ষা তাঁদের শাসকের কাছ থেকে সুযোগ, অর্থপ্রতিষ্ঠা এনে দিচ্ছে সেই বিদেশী শিক্ষাই ভবিষ্যতে জনগণের শত্রু হিসাবে তাঁদের চিহ্নিত করে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।” (অনুষ্টুপ, চতুর্থ সংখ্যা, সপ্তম বর্ষ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ- ৭৫) মেকলের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ তারিখে শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজি ভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে একটি ঘোষণায় বলেছিলেন, “সরকার নির্দেশ দিচ্ছে যে, শিক্ষা-সংস্কারের জন্য জেনারেল কমিটিকে প্রদত্ত সমগ্র অর্থ দেশীয় ব্যক্তিদের ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে এবং সরকার কমিটিকে অনুরোধ করছে যে, তারা যেন অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের একটি পরিকল্পনা তৈরি করে সরকারের কাছে পেশ করে।” (A Student’s History of Education in India: 1800-1965, S. Nurullah & J. P. Naik, P- 64) তাঁর সেই ঘোষণার ফলে সেকালের বাংলার জমিদার-মধ্যশ্রেণী উল্লসিত হয়েছিলেন। এরপরে প্রিন্স দ্বারকানাথ লর্ড ব্রুহামকে একটি পত্রে লিখেছিলেন যে, এর ফলে বঙ্গদেশের স্কুলসমূহ – “দেশের অসামরিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য কোম্পানির শাসনবিভাগের নিম্নতর স্তরে বেশ কয়েকজন সুদক্ষ করণিককে পাঠাতে সমর্থ হয়েছে। এরাই হল সরকারের কার্যসিদ্ধির সর্বোৎকৃষ্ট উপায় ও হাতিয়ার।” (দ্বারকানাথ ঠাকুর: বিস্মৃত পথিকৃৎ, কৃষ্ণ কৃপালনী, পৃ- ২৩২) ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বঙ্গদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি করবার পিছনে ঊনিশ শতকের বাংলার জমিদার-মধ্যশ্রেণীর যে স্বদেশ-হিতৈষণার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, সেকথা দ্বারকানাথের উপরোক্ত বক্তব্যেই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।
তখন শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক স্বার্থে একদল শিক্ষিত তল্পিবাহক তৈরি করবার জন্য ইংরেজি-শিক্ষাকে বিত্তশালী ভূস্বামী ও ধনিক-বণিকসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল; ফলে দেশের জনসমাজের বৃহত্তম অংশ কৃষক-সাধারণ অজ্ঞতার অন্ধকারে থেকে গিয়েছিলেন। সেই কারণে সৈয়দ শাহেদুল্লাহ বলেছিলেন, “কিন্তু সর্বসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার কথা কেউ ভাবতে পারেননি। ধর্ম প্রচারই বা কতদূর দূরান্তরগামী ছিল? রামমোহন এমনকি মহর্ষিও তাঁদের পাল্কী-বেহারাকে ‘ব্রাহ্মসমাজে’ নেবার বা ব্রাহ্ম করার কথা ভাবতেন কি? সুতরাং তাঁদের ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর কথা ভাববার প্রশ্নই ওঠে না।” (জনশিক্ষার প্রতিবন্ধক, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, নন্দন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, পৃ- ৫৬৪) নিজেদের ভূসম্পত্তির ক্রমবৃদ্ধি ও নিরাপত্তার স্বার্থে সেকালের ভূস্বামী-মধ্যস্বত্বাধিকারীশ্রেণী যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে উচ্ছেদ করবার দাবি উত্থাপন করেননি, তেমনি রায়ত-কৃষকের সন্তানকে তাঁরা সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলবার জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণও করেননি, এবং পরবর্তীকালে তাঁরাই বাংলার গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের বিরোধিতা করেছিলেন।
ঊনিশ শতকের বাংলার নায়কদের ইংরেজি-শিক্ষার আন্দোলন মূলতঃ সেকালের দেশীয় বণিক-জমিদারদের আত্মবিস্তার ও আত্মসংহতির আন্দোলন ছিল। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার কৃষকেরা যেমন নিজেদের জমির মালিকানা হারিয়ে ফেলেছিলেন, তেমনি ইংরেজি ভাষায় আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে ১৮৩৫ সালে তাঁরা নিজেদের মুখের ভাষায় শিক্ষাগ্রহণের অধিকারও শেষপর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলেন।#