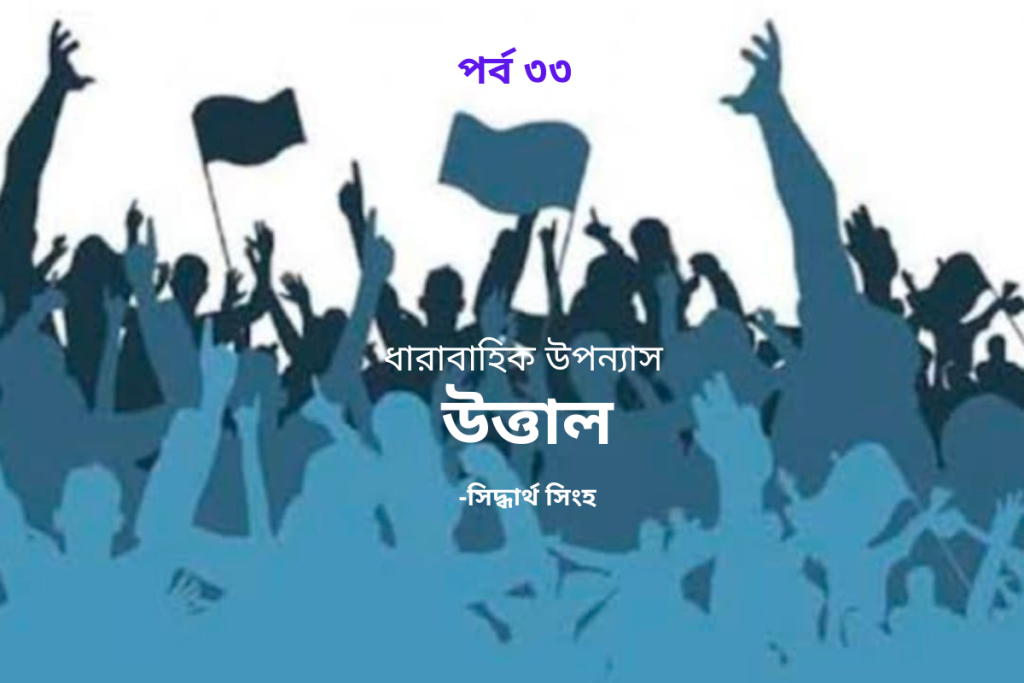।। পর্ব – ৩৩।।
পায়ে গুলি লাগতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কেশপুরের উত্তম পাল, ওরফে শম্ভু। সেটা দেখে ওর কাকিমা তাপসী পাল ভয়ে ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছু ফিরে কোনও রকমে ওকে তুলতে যেতেই কোথা থেকে দু’-তিন জন পুলিশ ছুটে এসে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারতে লাগল তাঁকে। একজন পুলিশ বলল, মাতঙ্গিনী হাজরা হবি? তোকে শালি আজ মেরেই ফেলব। দেখি কে বাঁচায়…
অন্য একজন পুলিশ ছিল পাশে। সেই পুলিশটির দিকে তাকিয়ে সে বলল, এমনি এমনি মারবি? তার আগে একবার চেখে দেখবি না? উত্তম তখন কাতরাতে কাতরাতে কাতর গলায় জল চাইছে। তখন অন্য আর একটা পুলিশ ওর মুখে এক দলা থুতু ছিটিয়ে দিল।
কালীচরণপুরের বাসন্তী করও দৌড়ে পালাচ্ছিল। একটা ছেলে, সে পুলিশ না সি পি এমের ক্যাডার বোঝা গেল না। কারণ, তার গায়ে পুলিশের পোশাক। কিন্তু পায়ে স্যান্ডেল। সে দৌড়ে এসে পিছন দিক থেকে বাসন্তীকে জাপটে ধরে ফেলল। পুলিশদের গাড়ি যাতে গ্রামে ঢুকতে না পারে, সে জন্য ক’দিন আগে গ্রামবাসীরা যে রাস্তাটা বেশ খানিকটা গভীর করে কেটে রেখেছিল, মারতে মারতে টেনেহিঁচড়ে সেই গর্তে নিয়ে ফেলে দিল। একজন পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে সেখানে নেমে, বুট দিয়ে থেঁতলে দিতে লাগল তাঁকে। বাসন্তী তখন যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। তাঁর আর্তনাদে, এখানে পুলিশ আছে টের পেয়ে, অন্য মেয়েরা যাতে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে না পড়ে, কিংবা অন্যত্র পালিয়ে না যায়, সে জন্য অন্য একটা পুলিশ ওঁর কান্না থামাতে কোমর থেকে রিভলভার বার করে সরাসরি কপাল লক্ষ করে ট্রিগার টিপে দিল।
একই ভাবে গুলি খেয়ে রাস্তায় পড়ে গেল পঞ্চানন দাস। কিছুটা দূরে পায়ে গুলি খেয়ে রক্তের মধ্যে ছটফট করতে লাগল মণি রানা। যেতে যেতে এক গ্রামবাসী ওদের দু’জনকে তুলতে যেতেই কোথা থেকে একটা গুলি এসে বিঁধল তার বুকে।
একের পর এক মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল গড়চক্রবেড়িয়ার মঞ্জুয়ারা বিবি, অশোক জানা, সুধীর গিরি, ইমাদুল খান। ৭ নম্বর জলপাইয়ের কাজল ঘোড়াই, লক্ষ্মীরানি বর্মন, লালিবালা দাস, সেখ ফুসি আলম, শ্যামলী মান্না, জাপানি মান্না। সোনাচূড়ার সুকান্ত মণ্ডল, নীলিমা দাস, রেনুকা মাইতি, নারায়ণ পাইক, তাপসী দাস, অঞ্জনা বেরা, লক্ষ্মীরানি রায়। কালীচরণপুরের মিনতি দাস, কমললতা দাস, মন্টু মণ্ডল, পরীক্ষিত মাইতি, অভিজিৎ গিরি। গোকুলনগরের রণজিৎ মাঝি, সলিল দাস অধিকারী, স্বর্ণময়ী দাস, কাঞ্চন মাল। অধিকারীপাড়ার জানকী অধিকারী। নন্দীগ্রামের সেখ সুলতান। সাউদখালির তুষার জানা, পুষ্প ধাপার, আরতি দাস, সুমিত্র জানা। গাংড়ার অপর্ণা প্রধান, জ্যোৎস্না মণ্ডল, রানু পাল, জগদীশ মণ্ডল, শ্রাবণী দাস, রামকৃষ্ণ দাস, হৈমবতী হালদার, মঞ্জু মান্না। কেশপুরের প্রণতি মাইতি, বনশ্রী আচার্য। আরও কত জায়গার কত গ্রামবাসী যে ধুপধাপ পড়ে গেল, তার হিসেব নেই।
গুলি কারও মাথায়, কারও হাঁটুতে, কারও থাইয়ে, কারও কনুইয়ে, কারও হাতে, কারও পায়ে, কারও পিঠে, কারও জানুতে, কারও বুকের খাঁচায়, কারও চোখে, কারও নাকে, কারও স্তনে, কারও পেটে, আবার কারও কাঁধে।
গুলি যেমন চলছে। তার পাশাপাশি চলছে অকথ্য অত্যাচার। পুলিশ আর ক্যাডার বাহিনীর হাত থেকে বাঁচার জন্য একটা বউ ছুটে পালাচ্ছিলেন, দু’জন পুলিশ ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেলল। তাঁর মাথা দেওয়ালে ঠেসে ধরে লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি মারতে লাগল একজন। অন্য জন হঠাৎ তাকে থামতে বলে, ওই বউটার একটা পা ধরে টান মেরে উপরে তুলে যৌনাঙ্গে লাথি মারতে লাগল। মার খেতে খেতে তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। পাশ দিয়ে যেতে থাকা তিন জন পুলিশ ওই অবস্থাতেই তাঁকে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।
কোনও কোনও মেয়েকে তিন-চার জন পুলিশ মিলে মাঠে ফেলে লাঠি দিয়ে মারতে লাগল। শাড়ি খুলে নিতে লাগল। কেউ কেউ সেই সব মেয়েদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যাঁদের দেখতে ততটা ভাল নয়, তাঁদের সঙ্গে আঁচড়া-আঁচড়ি বা কামড়া-কামড়ি না করলেও, অন্য পুলিশ বা ক্যাডাররা তাঁদের মাঠের মধ্যে চিৎ করে ফেলে, হাত-পা চেপে ধরে যৌনাঙ্গের মধ্যে লাঠি ঢুকিয়ে মোচড় দিতে লাগল।
ভয়ে তিন জন মেয়ে ছুটে গিয়ে একটা পানের বরজের ভিতরে লুকোল। তাদের একজনের হাতে গুলি লেগেছিল। মুখে শাড়ির আঁচল ঠেসে ধরেও সে তার কান্না চাপা দিতে পারছিল না। সেই গোঙানির শব্দ শুনে একটা পুলিশ ছুটে এসে, লতাপাতার বেড়ার জন্য কাউকে দেখতে না পেয়ে বন্দুকের নল দিয়ে, বরজের ভিতরে এমন ভাবে গুঁতো মারতে লাগল যে, একজনের প্রস্রাবের দ্বার ভেদ করে ঢুকে গেল বেয়নট। সে বুক ফাটা আর্তনাদ করে উঠতেই, অন্য কাউকে ধরার জন্য ইতিউতি ছুটতে থাকা অন্তত দশ-বারো জন পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপরে।
ঠিক তখনই কিছুটা দূরে একটা মেয়েকে দৌড়ে পালাতে দেখে ছ’-সাত জন পুলিশ ধেয়ে গেল সে দিকে। কম করেও চার-পাঁচ জন চড়াও হল তার উপরে। সে সময় হঠাৎ একটা কিশোরীকে একটা প্রকাণ্ড বটগাছের আড়ালে ভয়ে গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে থাকতে দেখে বাকিরা তার দিকে ছুট দিতেই দু’জন পুলিশ তার শাড়ি-ব্লাউজ টান মেরে মেরে খুলতে লাগল।
গোটা গ্রামের পুরুষরা তখন গ্রাম ছাড়া। ভূমি উচ্ছেদ রক্ষা কমিটির এক সদস্যের বাড়িতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল সাদা পোশাক পরা দশ-বারো জন লোক। সে বাড়ির কর্তাকে না পেয়ে, তার বড় ছেলেটাকে যে যেমন ভাবে পারল মারতে লাগল। সেটা দেখে তার মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের পায়ে আছড়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাবুগো, তোমরা যা বলবে, আমরা তাই করব। আমাদের ছেড়ে দাও।
তখন ছেলেটিকে উঠোনের একটা নারকেল গাছের সঙ্গে বেঁধে ছেলেটার মায়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল একজন। ছেলের সামনেই বিবস্ত্র করতে লাগল মাকে। বাকিরা ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে বাড়িটার এ ঘরে ও ঘরে। টেনে টেনে বার করে এনেছে ওই মহিলার কুড়ি বছরের বিবাহিত মেয়ে আর বারো বছরের ছোট্ট কিশোরীটিকে। উঠোনে যখন ছেলের সামনেই মায়ের ওপরে পাশবিক অত্যাচার হচ্ছে, তখন মেয়ে দু’টিকে প্রায় কোলপাঁজা করে তুলে কয়েক জন ক্যাডার গোয়ালঘরে নিয়ে ঢুকল। প্রবল ধস্তাধস্তির পর বড় মেয়েটিকে দু’জন আর ছোট মেয়েটিকে একজন ক্যাডার ধর্ষণ করল।
শুধু ওই বাড়িতেই নয়, এর পর পুলিশ আর সি পি এমের ক্যাডাররা গ্রামের পুরুষদের খোঁজে বাড়ি বাড়ি ঢুকে তল্লাশি শুরু করল। কাজল মাঝি নামে এক গৃহবধূকে পর পর চার জন ধর্ষণ করল। বেরিয়ে আসার সময় রাধারানি নামের এক মহিলার যোনিতে লোহার রড ঢুকিয়ে দিল একজন ক্যাডার।
একটা বছর বারো ছেলের সামনে তার মাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে এক দল লোক ধর্ষণ করে শাসিয়ে গেল, থানা-পুলিশ যা ইচ্ছে করতে পারিস। জানবি, কেউ আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না।
শ্রাবন্তী দাস অধিকারীর যৌনাঙ্গেও লাঠি ঢুকিয়ে দিল একজন ক্যাডার। আট মাসের গর্ভবতী একুশ বছরের নিকাশি দাসকে পুকুরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল পুলিশ। গর্ভেই মারা গেল তার সন্তান। সালেমা বিবিকে মাটিতে ফেলে তলপেটে বুট দিয়ে ভয়ংকর ভাবে পিষে দিল এক ক্যাডার। নূরজাহান বিবির জননেন্দ্রিয় বন্দুকের বাঁট দিয়ে খুঁচিয়ে দিল অন্য আর একজন।
ও দিকে মাঠের মধ্যে তখন বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলোকেও পুলিশ আর সি পি এমের ক্যাডার বাহিনী ছাড়ছে না। হয় গুলি করে মারছে, নয় পেটে কুকরি ঢুকিয়ে নাড়িভুঁড়ি বার করে দিচ্ছে। সারা শরীর রক্তে ভাসতে থাকা সাত-আট বছরের একটা ছেলে, ছুটে পালাতে থাকা এক মহিলার পা আঁকড়ে ধরে কাতর গলায় বলতে লাগল, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।
মুখে কাপড় বাঁধা লোকগুলো ছুটে এসে মেয়েটিকে ধরে ফেলল। আর, আরও অনেক বাচ্চার মতো ওই ছেলেটার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলে তলোয়ারের এক কোপে নামিয়ে দিল তার মাথা।
যে সব পুলিশ এবং ক্যাডার এই অপারেশনে নেমেছে, তারা সবাই যেন ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে আসা এক-একটা চেঙ্গিস খান। যে ঘোড়ার পিঠে যেতে যেতে বর্শা ছুড়ে মায়ের কোল থেকে গেঁথে নিত ছোট্ট শিশু। তার পর উল্লাস করতে করতে ধুলো উড়িয়ে চলে যেত। এরা যেন তারই উত্তরসূরি। যেতে যেতে রাস্তার মধ্যে পড়ে থাকা মৃত বা অর্ধমৃত শিশু দেখলেই, দু’পা ধরে টান মেরে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। যাতে এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে লোক শিউড়ে ওঠে। কিশোর-কিশোরীদের মুণ্ডু কেটে বস্তায় ভরে পুকুরে ফেলে দিতে লাগল। কিছু লাশ তড়িঘড়ি পুঁতে দিল মাটিতে। বেশ কিছু দেহ গাড়ি করে, জিপে করে, নৌকোয় করে ভাসিয়ে দিল জলে।
শুধু খুন, জখম, ধর্ষণই নয়, তার পাশাপাশি চলল ঘরে ঘরে লুঠপাট। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল আগে থেকে ঠিক করে রাখা জমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির লোকজনদের ঘরবাড়ি, ধানের গোলা। আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল কান্নার রোল।
এ দিন এই ঘটনার পরে সরকার নিজে থেকেই ঘোষণা করল, উভয় পক্ষের গুলি চালনায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মারা গেছেন ১৪ জন। তাঁদের নাম এবং বয়স হল– ইমদাদুল খাঁ (২০), গোবিন্দ দাস (৩০), সুপ্রিয়া জানা (৪০), রাজা সেখ ইমদাদুল (২০), রতন দাস (৩০), বাসন্তী কর (৬২), পুষ্পেন্দু মণ্ডল (২৭), জয়দেব দাস (২৪), বাদলকুমার মণ্ডল (৪৫), প্রলয় গিরি (২৫), রাখাল গিরি (৩২), পঞ্চানন দাস (৪৫), শম্ভু পাল (৩০), এ ছাড়াও একজন মারা গেছেন। যার পরিচয় এখনও জানা যায়নি। আনুমানিক বয়স ৩২ বছর। এদের প্রত্যেকেরই পোস্টমর্টেম করা হয়েছে তমলুক হাসপাতালে।
এই তালিকা দেখে সবাই অবাক। সরকার যে বলল, উভয় পক্ষের লোক মারা গেছে! কিন্তু যে নামগুলো তারা প্রকাশ করেছে, তাঁরা যে সবাই এই গ্রামের এবং এই গ্রামেরই আশপাশের লোক। তা হলে ওই পক্ষের নাম কোথায়!
এই তালিকার সঙ্গে সরকার আরও জানাল, এ দিন আহত হয়েছেন ১৬২ জন। নিখোঁজ ৩ জন। ওই রিপোর্ট শুনে গ্রামবাসীরা বললেন, নিখোঁজ নয়, ওদেরকে মেরে, ওদের লাশ গুম করে দিয়েছে পুলিশ।
কেউ কেউ বলল, পুলিশ নয়, পুলিশ এত নিষ্ঠুর হতে পারে না। তারাও তো আমার আপনার মতো ঘর থেকেই এসেছে। তাদেরও তো মা আছে। বোন আছে। সন্তান আছে। কিন্তু ইতিহাস ঘাঁটলে বোঝা যাবে, এটা সি পি এমেরই কাজ। দেশ ভাগের পর ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলা থেকে যে-সব শরণার্থী ভারতে এসেছিল, তারা কোথাও স্থায়ী শিকড় গাঁড়তে পারেনি। ১৯৫৯ সালে তাদের দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানকার পাথুরে জমিতে তারা কিছুই ফসল ফলাতে পারছিল না। তাই বারবার পশ্চিমবঙ্গে আসতে চাইছিল। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের জলা জমিতে। জলা জমি পেলে তাদের আর কিচ্ছু চাই না। জীবনটা তারা কিছু না কিছু করে ঠিকই কাটিয়ে দিতে পারবে।
ওদের ওই মনোভাব দেখে সি পি এমেরই হাইকম্যান্ড জ্যোতি বসু ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি ভিলাইতে গিয়ে, সতীশ মণ্ডল, রঙ্গনাথ গোলদার, রাইচরণ বাড়ৈ, কালী বসু-সহ অন্যান্য উদ্বাস্তু নেতাদের কথা দিয়ে এসেছিলেন, সি পি এম ক্ষমতায় এলে তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যাবেন। সুন্দরবনে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবি পূরণ করবেন।
এমনকী, ১৯৭৭ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গে যখন বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হল, সে মাসেরই ২১ তারিখে জ্যোতি বসুর সভাপতিত্বে বামপন্থী দলগুলো সমবেত ভাবে কলকাতায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সব দায়িত্ব কেন্দ্রীয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার যৌথ ভাবে নেবে।
অথচ ১৯৭৮ সালে সেই জ্যোতি বসুই যখন মুখ্যমন্ত্রীর মসনদে বসলেন, একদম ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে উলটো গান গাইতে শুরু করলেন। ভুক্তভোগীরা আরও একবার বুঝতে পারলেন, বিরোধী দলে থাকার সময় কাজ উদ্ধারের জন্য বড় বড় নেতারা অনেক গাল ভরা কথা বলেন, অগাধ প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু নিজে দায়িত্বে এলেই সব ফক্কা। তখন সব কিছু বেমালুম ভুলে যান। হলও তাই। জ্যোতি বসু বললেন, পশ্চিমবঙ্গে জন সংখ্যার চাপ এখন এত বেশি যে, এখানে দণ্ডকারণ্যের একজন উদ্বাস্তুরও পুনর্বাসন সম্ভব নয়।
তার আগেই যেহেতু বামপন্থী নেতাদের আশ্বাস পেয়েছেন, তাই দণ্ডকারণ্যের মানা ক্যাম্পের সবচেয়ে বড় উদ্বাস্তু সংগঠন ‘মানা উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি’র এক প্রতিনিধি দল হাসনাবাদ থেকে লঞ্চে করে মে মাসে গোসাবা থানার মরিচচকে যান। সেই একশো পঁচিশ বর্গমাইল বিরাট চরের উলটো দিকে গজিয়ে ওঠা একটা দ্বীপে একশো বছরেরও পুরনো একটা গ্রাম আছে। সেখানকার মানুষ জন তাঁদের বললেন, এখানে পাঁচ ফুটের বেশি উঁচু কখনও জোয়ার আসে না। আমরা যদি পাঁচ ফুট উঁচু বাঁধ দিয়ে, নোনা জল ঠেকিয়ে একশো বছর ধরে এখানে চাষ করতে পারি, তোমরা পারবে না কেন? তোমরা তো পূর্ববঙ্গের মানুষ। আমাদের মতোই জলে-জলে বড় হয়েছ। আর কিছু না পারো, মাছ ধরতে তো পারবে? এখানে প্রচুর মাছ। ধরে শেষ করতে পারবে না। আর তার থেকেও বড় কথা, এই দ্বীপটা এত বড় যে, শুধু এই দ্বীপেই তোমাদের মানা ক্যাম্পের ওই ষোলো হাজার পরিবারের জায়গা হয়ে যাবে। তোমরা সবাই আবার আগের মতো একসঙ্গে থাকতে পারবে। আর তোমাদের দেখাদেখি যদি অন্য কোথাও থেকে বিশ-পঁচিশ কেন, যদি ত্রিশ হাজার মানুষও আসে, এই সুন্দরবনের দত্ত পাসুরেই তাদের জায়গা হয়ে যাবে।
তাঁদের কথা মতো ১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে দণ্ডকারণ্য, বিশেষ করে মালকানগিরি থেকে যখন উদ্বাস্তুরা দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করেছে, দীর্ঘ জল-পথ পাড়ি দিয়ে আঠারো এপ্রিল, প্রায় দশ হাজার উদ্বাস্তু পরিবার যখন কুমিরমারি পার হয়ে মরিচঝাঁপিতে গিয়ে পৌঁছেছে, তখন রাজ্য সরকারের কাছে সি পি আই (এম)-এর রাজ্য কমিটি আবেদন জানাল, দণ্ডকারণ্য থেকে যে-সব উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসেছে, দরকার হলে বল প্রয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাদের হটিয়ে দিন।
তাদের আবেদন মতো ওদের তাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকার যে শুধু ওই উদ্বাস্তুদের পাশ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল, তাই-ই নয়, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশনের মতো আরও যত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উদ্বাস্তুদের মধ্যে চাল, ডাল, তেল, কখনও সখনও খিচুরি, বাচ্চাদের জন্য পাউডার দুধ, ওষুধপত্র, জামাকাপড় বিলি করে, স্বাস্থ্যশিবির করে ওদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য। তাদেরকেও হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য করল। সহায়-সম্বলহীন গুটিকতক পরিবার, যারা মাছ ধরে বা কাঠের জিনিস তৈরি করে কিংবা বিড়ি বানিয়ে অথবা ছোট আকারে পাউরুটি কারখানা চালিয়ে, নয়তো অন্য কোনও ভাবে জীবিকার সংস্থান করছিল, সেটাও রাতারাতি বন্ধ হয়ে গেল সরকারি নিষেধাজ্ঞায়।
কিন্তু দু’বেলা তো দু’মুঠো খেতে হবে, তাই প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে রাতের অন্ধকারে কেউ কেউ মাছ ধরার জন্য নদীতে যেত। সেটা টের পেয়ে সরকারও ভেড়ি কেটে, পুলিশ আর বন বিভাগের লঞ্চ লেলিয়ে, ওই সব উদ্বাস্তুদের মৃত্যু হতে পারে জেনেও, ওদের নৌকোগুলোকে মাঝনদীতে ভেঙে দিতে লাগল।
তাতেও ওরা দমছে না। গেঁড়ি-গুগলি, লতাপাতা, কলাগাছের থোড় সেদ্ধ করে খেয়েও তারা ঠিক দিন কাটিয়ে দিচ্ছে দেখে ১৯৭৮ সালের ১৯ আগস্ট কুড়িখানা লঞ্চ আর বিশাল পুলিশ বাহিনী দিয়ে একেবারে সামরিক কায়দায় নদীপথ অবরোধ করল রাজ্য সরকার।
তাতেও মড়া পোড়াবার কোনও ধোঁয়া ওই দ্বীপ থেকে উঠছে না। নদীর পাড়ে কেউ কোনও মৃতদেহকে করব দিতে আসছে না। তার মানে ওরা বেঁচে আছে। এটা বুঝতে পেরে, ৬ সেপ্টেম্বর ওই সব লঞ্চ দিয়ে পুরো দ্বীপটিকে চুপিসাড়ে ঘিরে ফেলল পুলিশ। দূর-দূরান্ত থেকে অতি কষ্টে, ঘুরপথে লুকিয়ে-চুরিয়ে নিয়ে আসা রসদ, জ্বালানি কাঠ ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বোঝাই করা উদ্বাস্তুদের ২০০টি নৌকো আচমকা হানা দিয়ে পুলিশরা ডুবিয়ে দিল।
তাতেও ওরা মরছে না কেন! নিশ্চয়ই গভীর রাতে, নদী সাঁতরে কিংবা চোরের মতো ছোট ছোট নৌকো করে গিয়ে অন্য কোনও দ্বীপ থেকে ওষুধপত্র, বাচ্চাদের খাবারদাবার ওরা নিয়ে আসছে! এই সন্দেহবশতই ১৯৭৯ সালের ২৪ জানুয়ারি পুরো মরিচঝাঁপি দ্বীপটি বিশেষ পুলিশ বাহিনী দিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হল।
এই দ্বীপটাতে উদ্বাস্তুরা ছাড়া আর কোনও মানুষ বাস করত না। কারণ, ওখানে কিছুই পাওয়া যেত না। এমনকী পানীয় জলটুকুও না। কুমিরমারি বা আশপাশের অন্যান্য দ্বীপ থেকে ওরা পানীয় জল, খাবারদাবার, ওষুধপত্র, পাউরুটি আর বিড়ি কারখানার কাঁচা মালপত্র নিয়ে আসত। রাজ্য সরকার পুলিশ দিয়ে মরিচঝাঁপি ঘিরে ফেলে সে-সবও বন্ধ করে দিল। যাতে অনাহারে, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে বিনা চিকিৎসায় ওরা মারা যায়।
সে সময় উদ্বাস্তুদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া কংগ্রেসের প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী, সুনীতি চট্টরাজ, অরুণ মৈত্র, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তো বটেই, এমনকী কোনও সাংবাদিককেও সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আটকে দেওয়া হয়েছিল বহু আগেই। না হলে, ওখান থেকে ওদের উচ্ছেদ করার জন্য টানা বেশ কিছু দিন ধরে পুলিশ যে বর্বরোচিত আচরণ করেছিল, তা জানাজানি হয়ে যেত।
কী না করেছে ওরা? নারী ধর্ষণ থেকে শুরু করে গণহত্যা। কাউকে গুলি করে মেরেছে, তো কাউকে কুপিয়ে মেরেছে। ছোটখাটো কেস দিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়ার নাম করে লঞ্চে এনে, হাত-পা বেঁধে নদীতে ফেলে দিয়েছে। কিছুই বাদ দেয়নি ওরা। তবু নিজেরা সব দিক সামলে উঠতে পারত না। তাই উদ্বাস্তুরা যখন কুড়ানখালি নদী পেরিয়ে কুমিরমারি দ্বীপে জল আনতে যেত, তখন লোকসমেত ডিঙি ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ডিঙি পিছু সারেংদের হাজার টাকা করে পুরস্কার দিত। আর পুলিশ-ক্যাডারদের জন্য সে সময় বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছিল, কে কত নৃশংস ভাবে এবং কত কম সময়ের মধ্যে কত জনকে মারতে পারে, তার উপর ঢালাও পুরস্কার।
১৯৭৯ সালের ১৬ মে, যে দিন মরিচঝাঁপি অপারেশন শেষ হল, তার ঠিক একদিন কি দু’দিন পর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রধান সংগঠক অশোক চৌধুরী হ্যামিলটনগঞ্জের একটা ভটভটি নিয়ে কুড়ানখালি নদী দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মাঝি বলে উঠলেন, সামনের দিকে এখন আর যাওয়া যাবে না।
উনি বললেন, কেন?
মাঝি বললেন, সামনের দিকে তাকান।
উনি তাকাতেই চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল তাঁর। তিনি দেখলেন, এক ঝাঁক ছোট-বড় কুমির কতকগুলো মৃতদেহ নিয়ে খাবলাখাবলি করছে। মারামারি করছে।
অশোকবাবুর বুঝতে অসুবিধে হল না, মৃতদেহগুলো কাদের এবং কোথেকে এসেছে।
যারা এত নৃশংস হতে পারে, ভোটে জেতার জন্য মুখে এক কথা বলে, আর জেতার পরেই অনায়াসে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যেতে পারে, তারা সব পারে।
আরও পড়ুন: ধারাবাহিক উপন্যাস ‘উত্তাল’ (বত্রিশ)
সময় এবং স্থানের ব্যবধান হলেও, নন্দীগ্রামের এই বর্বরোচিত কার্যকলাপ আসলে মরিচঝাঁপিরই একটা মডেল। যে মডেলে ১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল সি পি এমের ফিল্ডমার্শাল শচীন সেনের নেতৃত্বে সকাল সাতটা থেকে একই সঙ্গে কসবা, বালিগঞ্জ, বিজন সেতু, বন্ডেল গেটে ঘটানো হয়েছিল আনন্দমার্গী-নিধনযজ্ঞ।
‘চোর চোর’ বলে আনন্দমার্গীর সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের ধাওয়া করে, পিছন থেকে ইট-পাটকেল ছুড়ে, আহত করে, তাঁদের ধরে ফেলার পর বেধড়ক লাঠি পেটা করে, রড মেরে, আধ মড়া করে তাঁদের গায়ে পেট্রল আর কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। পথচারীদের বিভ্রান্ত করার জন্য রটিয়ে দিয়েছিল, ওরা ছেলেধরা। আসলে, ভারতে আনন্দমার্গীদের সংগঠন তৈরি হওয়ার পর, বিশেষ করে পুরুলিয়ায় আশ্রম গড়ে ওঠার সময় থেকেই শাসক দল ওদের বাড়বাড়ন্ত দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। ওদেরকে প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করেছিল। কারণ, একটি সঙ্ঘ, যেটা রীতিমত ক্যাডার বেসড, যেটা শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের মধ্যেই নয়, সারা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তারা নিশ্চয়ই পরবর্তিকালে রাজনীতিতে আসবে। রাজনীতি করবে।
তার ওপর শাসক দলের রেগে যাওয়ার আরও একটা কারণ হল, মার্ক্সবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি এবং অমানবিক দিকগুলো নিয়ে ওই সঙ্ঘেরই মূল হোতা, আচার্য মন্ত্রেশ্বরানন্দ অবধূত দুটো বই লিখেছিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে কোনও যুক্তি খাড়া করতে না পেরে, প্রমোদ দাশগুপ্ত ১৯৭৯ সালের ১০ জুলাই সি পি এমের দলীয় মুখপত্র ‘গণশক্তি’তে লিখেছিলেন, আনন্দমার্গীরা হল সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক, বিচ্ছিন্নতাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। জনগণের ঐক্য বিনাশকারী বিপদ। পার্টি কমরেটদের জন্য আলাদা একটি পুস্তিকাও লেখেন তিনি। যার নাম ‘এই বিপদ রুখতে হবে’। গোটা বইটির মূল বক্তব্য ছিল– যে ভাবেই হোক, আনন্দমার্গীদের ধাপে ধাপে খতম করতে হবে। তাই প্রতিটি লোকাল কমিটি মারফত ক্যাডারদের মাধ্যমে পাড়ায় পাড়ায়, বাড়িতে বাড়িতে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, আনন্দমার্গীরা সি আই এ-র চর।
সি পি এমের নেতারা ভেবেছিলেন, যেহেতু আনন্দমার্গীদের সংগঠন একশো বিরাশিটা দেশে ছড়িয়ে আছে, ফলে এই সংগঠনে বিদেশি টাকার ছড়াছড়ি। অর্থাৎ এখানে বিদেশের হাত আছে বললেই, সহজেই সবাই সেটা বিশ্বাস করবে। আর এটা বিশ্বাস করতে শুরু করলেই সাধারণ লোকেরা ওদের সন্দেহের চোখে দেখবে এবং ওদের পাশ থেকে সরে দাঁড়াবে।
কিন্তু শাসক দলের পক্ষ থেকে একের পর এক এ রকম মারাত্মক অভিযোগ করলেও, এ দেশের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর কিন্তু অনেক খোঁজখবর, অনুসন্ধান করে সাফ জানিয়ে দিল, এই অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই।
তাই শুধু লেখালিখি করে নয়, সমস্ত চেষ্টা যখন বিফলে গেল, তখন পার্টির অ্যাকশন স্কোয়ার্ডের লিডার বাবলু চক্রবর্তী, ওরফে মিচকে বাবলুকে দায়িত্ব দিয়ে ১৯৮২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, শনিবার, বিকেল পাঁচটার সময় পিকনিক পার্কের আনন্দ আরতি ইনস্টিটিউট হলে ডাক দেওয়া হল– ‘আনন্দমার্গের সন্ত্রাস সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে নাগরিক কনভেনশন’। সেটার আহ্বায়ক ছিলেন অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী, সংসদ সদস্য সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিধানসভার সদস্য ড. শুভঙ্কর চক্রবর্তী, আবৃত্তিকার রজত বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যাডভোকেট অরুণ মিত্র, কান্তি গাঙ্গুলি, সমীর পুততুণ্ড, বিজয়নগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জগদীশ সরকার-সহ মোট আটানব্বই জন।
তো, সেই ঘরোয়া মিটিংয়েই ৩০ এপ্রিলের বীভৎস নরহত্যার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়ে গেল।
যারা পূর্ব পরিকল্পনা করে একসঙ্গে সতেরো জন সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীকে এই ভাবে পুড়িয়ে মারতে পারে, তারা কী না করতে পারে! যে রাজ্যে এমন পৈশাচিক কাণ্ড ঘটে, সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ করে কী ভাবে বিশ্রামের অজুহাত দিয়ে দিন কতকের জন্য শৈল-শহরের সফরসূচি ঘোষণা করেন, বোঝা যায় না।
যে জবাব দেওয়ার ভয়ে জ্যোতি বসু তড়িঘড়ি শহর ছাড়তে চেয়েছিলেন, তিনি কিন্তু তার থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না। বাগডোগরাগামী বিমানে ওঠার আগেই সাংবাদিকরা তাঁকে ছেঁকে ধরলেন। প্রশ্ন করলেন, আনন্দমার্গী হত্যা সম্পর্কে।
কী উত্তর দেবেন বুঝতে না পেরে তিনি নির্বিকার ভাবে বলে ফেললেন, এমন ঘটনা তো কতই ঘটে।
সবাই তাজ্জব হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল বানতলার সেই ঘটনা। আনন্দমার্গীদের খতম-ছকের মতোই একই পদ্ধতিতে ওই সমাজসেবীদেরও ছেলেধরা বলে তাড়া করা হয়েছিল। গাড়ির চালক আর কয়েক জন নরনারীকে প্রচণ্ড মারধর করার পর অনীতা দেওয়ানকে ঝোপের আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে পর পর ধর্ষণ করেছিল কয়েক জন। তার পর তাঁকে হত্যা করে, পাটভাঙা শাড়ি-ব্লাউজ পরিয়ে দিয়েছিল। তাঁর ওপর এতটাই পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছিল যে, পোস্টমর্টেমের সময়, তাঁর ক্ষত-বিক্ষত ও থেঁতলানো গোপনাঙ্গ দেখে এক মহিলা-ডাক্তার মূর্ছা গিয়েছিলেন।
অথচ এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জ্যোতি বসু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলেছিলেন, এ রকম ঘটনা তো হতেই পারে।
যে-রাজ্যে ধর্ষণ হলে মুখ্যমন্ত্রী ভাবলেশহীন ভাবে এমন মন্তব্য করতে পরেন, নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নৃশংস ভাবে খুন করার ছক কষতে পারেন, জীবিত লোকদের চিরতরে লোপাট করে দিতে পারেন, সে রাজ্যের দলীয় কর্মীরা যে লাগামছাড়া হয়ে উঠবে, এটা আর নতুন কথা কী!
তবু ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে ওই ঘটনার পর, প্রশাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, ওই দিনই দুপুরবেলায় কলেজ স্কোয়ার থেকে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এবং প্ররোচনাহীন এক বিশাল মিছিল বেরোয়। ব্যানার এবং স্লোগানবিহীন সেই মিছিলে হাঁটেন মহাশ্বেতা দেবী, শঙ্খ ঘোষ, তরুণ সান্যাল, অপর্ণা সেন, জয় গোস্বামী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শুভাপ্রসন্ন, যোগেন চৌধুরী, গৌতম ঘোষ, শাঁওলী মিত্র, মনোজ মিত্র, পূর্ণদাস বাউল, মমতাশঙ্কর। কে ছিলেন না সেই মিছিলে? কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, গায়ক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, ছাত্র সবাই। বাদ যাননি গৃহবধূ, শিশু-কিশোর, প্রতিবন্ধীরাও।
সেই মিছিল যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, পথচলতি সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সেই মিছিলে পা মিলিয়েছিল।
পর দিন ১৫ মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় বেরোল– পুলিশ-জনতা সংঘর্ষে গুলিবৃষ্টি, নিহত ১৪।
বর্তমান-এ আলাদা আলাদা খবরের শিরোনাম হল– নন্দীগ্রামে পুলিশের গণহত্যা / ছক কষেই এগিয়েছিল পুলিশ। নির্বিচারে গুলি, নিহত অন্তত ২৫।
সংবাদ প্রতিদিন-এ বেরোল– নন্দীগ্রামে পুলিশের তাণ্ডবে হত অন্তত ২২, জখম ৫০। লাল বাংলা রক্তে লাল। কাল বাংলা বনধ, সরব রাজ্যপালও। যেন কাশ্মীরের জঙ্গিদমন অভিযান।
একদিন-এ বেরোল– বাংলা বনধ, ক্রদ্ধ শরিকরা, ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল, পিছোল উচ্চমাধ্যমিক/রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নন্দীগ্রামে। রণক্ষেত্র নন্দীগ্রাম।
আলাদা বক্স করে বেরোল নন্দীগ্রাম অপারেশনের সময়সূচি– বেলা ১১টা দু’দিক দিয়ে সাঁড়াশি অভিযান শুরু।
সাড়ে ১১টা ভাঙাবেড়ায় গুলি চালানো শুরু।
১২টা ভাঙাবেড়া ব্রিজের পাশে ইটের পাঁজা দখল। বিকেল সাড়ে ৪টেয় সোনাচূড়া দখল করল পুলিশ।
দৈনিক স্টেটসম্যান-এ বেরোল– নন্দীগ্রামে জালিয়ানওয়ালাবাগ / পুলিশ-ক্যাডারদের নির্বিচার গুলি, নিহত ৩১ । অবাধে লুঠপাট। স্বজনের খোঁজে দিশেহারা নন্দীগ্রাম।
এই একই ধরনের খবর বেরোল দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, দ্য টেলিগ্রাফ, দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায়। শুধু এ দেশের বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি বা অন্যান্য ভাষাভাষি পত্রপত্রিকা বা টিভির নিউজ চ্যানেলগুলোতেই নয়, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমই অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশন করল এই খবর।
স্বয়ং রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গাঁধী বললেন, ‘নন্দীগ্রামে আজকের ঘটনা আমার কাছে হাড়-হিম করা আতঙ্কের বার্তা বয়ে এনেছে। এই বিপুল রক্তক্ষয় কি এড়ানো যেত না? এই বলপ্রয়োগে কী জনস্বার্থ রক্ষা হল? দেশবিরোধী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ হলে এক কথা। কিন্তু যাঁরা বলপ্রয়োগের শিকার, তাঁরা সেই দলে পড়েন না। আমি এই পদে যে শপথ নিয়েছি, তাতে নিছক ক্ষোভ ও উষ্মা প্রকাশ করেই থেমে থাকতে পারি না। আমি বিশ্বাস করি, এই আতঙ্কের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সরকার তা নিশ্চিত করবে।’
অথচ মহাকরণ ও দলীয় স্তর থেকে সাফাই গাওয়া হল, আত্মরক্ষার্থে বাধ্য হয়ে পুলিশ গুলি চালিয়েছে।
এ দিন রাতেই এক জনসভায় দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা রাগে-শোকে-হতাশায় ভিয়েতনামের সেই বিখ্যাত স্লোগানের একটু অদলবদল করে উচ্চারণ করল– ‘আমার নাম তোমার নাম, নন্দীগ্রাম নন্দীগ্রাম।’ শুধু এ দেশই নয়, নড়েচড়ে বসল গোটা পৃথিবীর সচেতন মানুষ। তদন্ত করার জন্য নন্দীগ্রামে হাজির হল সি বি আই টিম। ১৭ মার্চ, নন্দীগ্রাম সংলগ্ন সি পি এম নিয়ন্ত্রিত খেজুরির জননী ইটভাঁটা থেকে দলীয় ঝান্ডা ও অস্ত্রসস্ত্র-সহ শাসক দলের দশ জন ক্যাডারকে গ্রেফতার করলেন তাঁরা।
১৪ মার্চের সেই ভয়াবহ দিনে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়া নন্দীগ্রামের পাঁচ মহিলা– কাজল গায়েন, লালি মণ্ডল, সুস্মিতা দাস, গীতাবালা গায়েন এবং খুকুরানি দাস, পাঁচ দিনের মাথায়, ১৮ মার্চ গ্রামে ফিরে এল। ওরা বলল, ওই দিন পুলিশ আর ক্যাডার বাহিনীর হামলার সময় ওরা নাকি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে জেলিংহামের জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছিল। টানা চার দিন খাওয়াদাওয়া তো দূরের কথা, খাওয়ার জলটুকুও তাদের জোটেনি। শরীরের এমন অবস্থা যে, তখনই তাদের হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়।
নন্দীগ্রামের এই ভয়াবহ কর্মকাণ্ডের মূল হোতা ছিল সি পি এমের স্থানীয় নেতা বাদল গাড়ু, সুদর্শন গাড়ু, অনুকূল শীট-সহ আরও অনেকে। সি পি এম যা করে, মাথার উপর যত বড় নেতাই থাক না কেন, তা স্থানীয় ক্যাডারদের দিয়েই করে। যে-ভাবে ১৯৬৯ সালে বামফ্রন্টের আমলে রাজারহাট বিধানসভার বিধায়ক, কাম কৃষক নেতা রবীন মণ্ডলের নেতৃত্বে সি পি এমের পোষা গুন্ডা-বাহিনী চিন্তা সিংহের ভেড়ি দখলের মধ্যে দিয়ে পত্তন করেছিল ভেড়ি-রাজ। সেটাকে আটকাতে এখনকার সল্টলেকের সেক্টর ফাইভ-এর পাশের মহিষবাথানের ভেড়ি মালিকরা সতর্ক হয়ে যান। আরও বেশি করে পাহারাদার, রাত-পাহারাদার রাখতে শুরু করেন। জোট বাঁধতে থাকেন। তাঁদের মধ্যমণি হয়ে ওঠেন অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু ভেড়ি মালিক শঙ্কর মণ্ডল। জাঁদরেল এক নেতার অঙ্গুলি হেলনে এক রাতে তাঁকেও খুন করে দেয় সি পি এমের লোকেরা। তিনি মারা যেতেই তাঁর ভেড়িটি চলে যায় জল-মাফিয়াদের হাতে। ১৯৮৫ সালে খাসমহলের খাসের ভেড়ি দখল হয়ে যায়। তখন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর শ্যালক বিজন নাগ সেই ভেড়িতে আই এফ বি-র তত্ত্বাবধানে মধুমিতা কনস্ট্রাকশন লিমিটেড নামে রাতারাতি একটি কোম্পানি খুলে গলদা চিংড়ির চাষ শুরু করেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে খাসের ভেড়িতে এত দিন ধরে কাজ করতে থাকা শ্রমিকদের বিনা নোটিশে ছাঁটাই করে দেন। শুরু করেন বাছাই করা মস্তান বাহিনীদের নিয়ে ভেড়ি সাম্রাজ্য।
তাঁরই উৎসাহে ও সাহায্যে স্থানীয় বিধায়ক রবীন মণ্ডল, বিধাননগরের কাউন্সিলর তপন তালুকদার, জেলা নেতা অমিতাভ নন্দী সুপরিকল্পিত ভাবে একটার পর একটা ভেড়ি দখল করে নেন। আতঙ্কগ্রস্ত ভেড়ি মালিকদের হয়ে ভেড়ি মালিক অ্যাসোসিয়েশনের নেতা প্রেমতোষ ঘোষ, সুকুমার মিত্ররা এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে গেলে, তিনি কিন্তু তাঁদের সঙ্গে দেখাই করেননি।
যাদের এই রকম অতীত, তারাই তো এ সব করতে পারে। করেও। ফলে ১৪ মার্চের ও রকম একটা জঘন্য এবং অমানবিক ঘটনার জেরে সারা রাজ্য যখন উত্তপ্ত, তখন ওই জ্যোতি বসুর উত্তরসূরি, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কিন্তু কোনও ভুল করেননি। যেই বুঝতে পেরেছেন, তিনি কী ভুল করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দুঃখের সঙ্গে তিনি বলেছেন, আমি বুঝতে পারেনি এমনটা হবে।
পরে এই মর্মান্তিক ঘটনার কারণে পদত্যাগ করা নাট্যশিল্পীদের সঙ্গে একটি একান্ত বৈঠকে তিনি জানালেন, খবরটা পাওয়া মাত্র তিনিও মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করার কথা ভেবেছিলেন। এবং ওই বৈঠকের কিছুক্ষণ পরেই অন্য আর একটি ছাত্র জমায়েতে তিনি ঘোষণা করলেন, এর দায় আমি মাথা পেতে নিলাম। আমি কথা দিলাম, নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব হবে না। না, আমরা নন্দীগ্রামে যাব না। কোনও দিন যাব না।
চলবে…