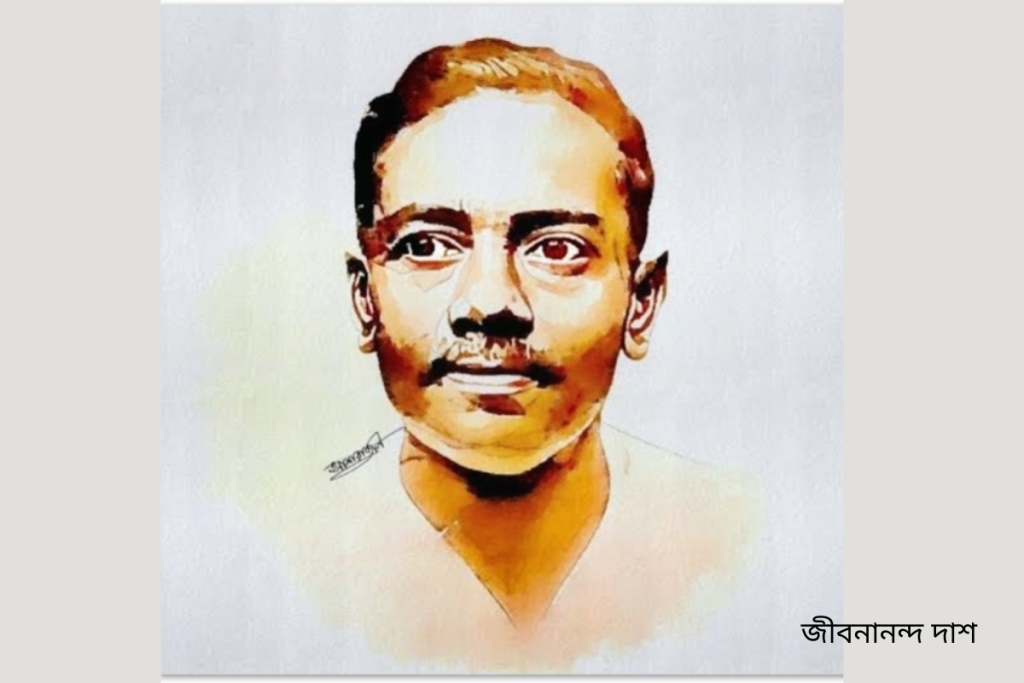কবিতায় ‘অশ্লীলতার’ অভিযোগে কলকাতার সিটি কলেজ থেকে চাকরিচ্যুত হওয়ার পরেও জীবনানন্দ কলকাতাতেই থেকে গিয়েছিলেন এবং এখানে ওখানে চাকরির চেষ্টা করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এরপরে বছর খানেক ধরে তিনি কোথাও কোনো চাকরি পাননি। সেই সময়ে নিজের হাতখরচ ও প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ের খরচ চালানোর জন্য তিনি সামান্য দু’-একটা টিউশনি করতেন মাত্র। তারপরে ১৯২৯ সালের কোন একসময়ে তিনি খুলনা জেলার বাগেরহাট কলেজে ইংরেজি অধ্যাপকের একটা কাজ পেয়েছিলেন। জীবনানন্দের জীবনীকারদের মতে খুব সম্ভবতঃ খবরের কাগজে এবিষয়ে কোন বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেই তিনি এই কাজটি জোগাড় করেছিলেন। যদিও তাঁর এই চাকরিটি অস্থায়ী ছিল কিনা—সেবিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না, তবে জীবনানন্দ মাত্র মাস তিনেক এই চাকরিটি করেছিলেন বলে জানা যায়। এবিষয়ে তাঁর ভাই অশোকানন্দ দাশের মত ছিল যে, বাগেরহাট কলেজে ভাল না লাগবার কারণেই তিনি এই চাকরিটি শেষপর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন।
বাগেরহাট কলেজের চাকরিটি ছেড়ে দেওয়ার পরে জীবনানন্দ পুনরায় কলকাতার তাঁর সেই পুরোনো আস্তানা—প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে ফিরে এসেছিলেন এবং আবার নতুন চাকরির চেষ্টা করতে শুরু করেছিলেন ও কলকাতার খরচ চালাবার জন্য পুনরায় কিছু টিউশনি ধরেছিলেন। তবে সেই সময়ে অবশ্য জীবনানন্দের বাড়িতে কোন টাকা না দিলেও চলত। কারণ—জীবনানন্দের ছোটভাই অশোকানন্দ তখন চাকরিতে ঢুকে গিয়েছিলেন, এবং এর সাথে জীবনানন্দের পিতার মাস্টারি তো ছিলই। সেই সময়ে জীবনানন্দ মাঝে মাঝেই বরিশালের বাড়িতে যেতেন এবং সেখানে কিছুদিন করে কাটিয়ে আসতেন। এভাবেই তখন একবার বরিশালে যাওয়ার পরে সেখানে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তর ভাইপো সুকুমার দত্তর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। সুকুমার দত্ত তখন দিল্লীতে একটা উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। সেই সাক্ষাতে জীবনানন্দের কাজ নেই শুনে তিনি ফিরে দিল্লী গিয়ে সেখানকার রামযশ কলেজে তাঁকে একটা অধ্যাপনার চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন। যদিও জীবনানন্দ সাধারণতঃ বাংলা ছেড়ে বাইরে কোথাও কাজের জন্য যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু তবুও তখন একপ্রকার বাধ্য হয়েও নিজের একান্ত অনিচ্ছাতেই তিনি সেকাজের জন্য দিল্লী গিয়েছিলেন। সেবারে ১৯২৯ সালের শেষের দিকে জীবনানন্দ রামযশ কলেজে কাজে যোগ গিয়েছিলেন এবং ১৯৩০ সালের মে মাস পর্যন্ত সেখানে চাকরি করেছিলেন। এরপরে মে মাসে দিল্লী থেকে দেশে বিবাহ করবার জন্য ফিরে এসে তিনি আর কখনো দিল্লীতে ফিরে যাননি। কিন্তু বিবাহ করবার পরেই জীবনানন্দ বেকার হয়ে পড়েছিলেন বলে তাঁর জীবনীমূলক গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায়। তাঁর জীবনীকারদের মতে—হয় তিনি বিবাহের পরে দিল্লীতে আর ফিরে না গিয়ে সেই চাকরিটি ছেড়ে দিয়েছিলেন, আর নয়তো তিনি বিবাহ করতে এসে দেরি করে ফেলবার জন্য তাঁর সেই চাকরিটি চলে গিয়েছিল। তবে জীবনানন্দের সেই চাকরিটি যে একেবারে নিছক অস্থায়ী কিছু ছিল না—সেকথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কারণ—ওই চাকরিটি যদি অস্থায়ী হত, তাহলে সেই চাকরিতেই নিজেকে বহাল অধ্যাপক পরিচয় দিয়ে তিনি বিবাহ করতে যেতেন না। আবার এমনও হতে পারে যে, তাঁর সেই চাকরিটি হয়ত প্রথমে অস্থায়ী ছিল, কিন্তু পরে তাঁকে সেই পদে স্থায়ী করা হবে—এমন কোন আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। হয়ত সেই সাহস বা বিশ্বাসের উপরে ভর করেই জীবনানন্দ তখন বিবাহ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত যে কোনো কারণেই হোক—সেই কলেজ কর্তৃপক্ষ সেই পদে তাঁকে আর স্থায়ী করেননি।
কিন্তু জীবনানন্দের সিটি কলেজের চাকরি চলে যাওয়া থেকে শুরু করে রামযশ কলেজের চাকরি ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত—এই দু’বছরে, অর্থাৎ—১৩৩৫ ও ৩৬ বঙ্গাব্দে তাঁর কবিতা রচনা ও প্রকাশ করবার ক্ষেত্রে আদৌ কোন ভাটা পড়েনি। উক্ত সময়ে তিনি বেকার থাকুন বা সাময়িকভাবে অস্থায়ী চাকরিরত থাকুন—উভয় অবস্থাতেই তিনি সবসময়েই সমানে লিখে গিয়েছিলেন এবং নিজের সেই লেখাগুলি বিভিন্ন কাগজে প্রকাশও করেছিলেন। ১৩৩৫ ও ৩৬ বঙ্গাব্দে শুধুমাত্র ‘প্রগতি’ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর যে কবিতাগুলির সন্ধান এখনও পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, সেই তালিকা নিম্নরূপ—
প্রগতি—১৩৩৫ বঙ্গাব্দ
(মাস→কবিতার শিরোনাম)
বৈশাখ→১৩৩৩,
আষাঢ়→সহজ,
ভাদ্র→পরস্পর,
অগ্রহায়ণ→জীবন,
পৌষ ও মাঘ (একত্রে)→স্বপ্নের হাতে।
প্রগতি—১৩৩৬ বঙ্গাব্দ
আষাঢ়→পুরোহিত,
ভাদ্র→বোধ,
আশ্বিন→আজ,
কার্তিক→অবসরের গান।
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে ১৩৩৫ ও ৩৬ বঙ্গাব্দের যে প্রগতি পত্রিকাগুলি সংরক্ষিত রয়েছে, সেগুলির মধ্যে উক্ত দু’বছরেরই শ্রাবণ সংখ্যার সন্ধান পাওয়া যায় না, এছাড়া সেখানে পত্রিকাটির কোন বাৎসরিক সূচীপত্রও সংরক্ষিত নেই। সুতরাং সেই দু’বছরের শ্রাবণ মাসেও উক্ত পত্রিকাটিতে জীবনানন্দের কোনো কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা—সেকথা বলা সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখিত প্রগতিতে প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে শুধুমাত্র ‘আজ’ শিরোনামের কবিতাটি বাদ দিয়ে অন্য সব কবিতাগুলিই জীবনানন্দ তাঁর গ্রন্থভুক্ত করে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ একথাও জানিয়ে রাখা যাক যে, জীবনানন্দের ‘আজ’ কবিতাটি আসলে ৩২০ লাইনের একটি দীর্ঘ কবিতা। একইসাথে একথাও উল্লেখ্য যে, প্রগতি পত্রিকায় প্রকাশিত জীবনানন্দের এই ‘আজ’ কবিতাটি সুদীর্ঘ হলেও ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ‘কালি-কলম’ পত্রিকাতেও জীবনানন্দ ‘আজ’ নামের আরেকটি সুন্দর ও ছোট্ট প্রেমের কবিতা প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু সেটিও তিনি কোন গ্রন্থভুক্ত করে যাননি।
১৩৩৫ ও ৩৬ বঙ্গাব্দের প্রগতি এবং কালি-কলম পত্রিকা ছাড়াও সমকালীন অন্যান্য পত্রিকাতেও তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত তো হয়েছিলই, এমনকি মাসের পর মাসও কবিতা বেরিয়েছিল। যেমন—‘ধূপছায়া’ পত্রিকার ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় তাঁর—‘প্রেম’—শিরোনামের কবিতাটি, এবং একই পত্রিকার সেই বছরেরই আশ্বিন সংখ্যায়—‘মাঠের গল্প’ ও কার্তিক সংখ্যায়—‘আমরা’— শিরোনামের কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া ওই একই বছরের কার্তিক মাসেই কালি-কলম পত্রিকায়—‘ফসলের দিনে’—শিরোনামে জীবনানন্দের আরও একটি সুন্দর প্রেমের কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু পূর্বোক্ত ‘আমরা’ এবং ‘ফসলের দিনে’—এই দুটি দীর্ঘ কবিতাও জীবনানন্দ তাঁর কোনো গ্রন্থভুক্ত করে যাননি।
এরপরে বরিশালের বি. এম. কলেজে স্থায়ী অধ্যাপকের কাজ পেয়ে জীবনানন্দ তখন অর্থের দিক দিয়ে কিছুটা হলেও নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন। অতীতে এই কলেজেরই এক ছাত্র—আবুল কালাম শামসুদ্দীন—তখনকার জীবনানন্দ সম্বন্ধে লিখেছিলেন—
“তাঁকে প্রথম দেখি যখন আমরা আই. এ. ক্লাসের ছাত্র। বরিশালের ব্রহ্মমোহন কলেজে ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন তিনি। শ্যাম রঙের স্বাস্থ্যবান পুরুষ। চল্লিশোত্তর বয়স তখন। পরনে ধুতি, পাঞ্জাবী, পাম্প-সু। কাঁধে পাট করে রাখা চাদর, হাতে একটি কি দুটি বই। মুখ তাঁর সর্বদা ভারী গম্ভীর; চোখে আশ্চর্য চাঞ্চল্য ও তীক্ষ্ণতা। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতেন। … শিক্ষকতায় তিনি সর্বজন-প্রিয় হতে পারেননি। এ অতৃপ্তি তাঁর মনে অবশ্য ছিল। তাঁর কবিতা অন্যান্য অধ্যাপক মহলে উপহাসের খোরাক জুগিয়েছে দেখেছি।”
বি. এম. কলেজে জীবনানন্দ কেন সর্বজন-প্রিয় একজন অধ্যাপক হয়ে উঠতে পারেননি, সে সম্বন্ধে তৎকালীন বি. এম. কলেজে জীবনানন্দেরই এক সহকর্মী অধ্যাপক—হেরম্ব চক্রবর্তী—অতীতে নিজের স্মৃতিচারণে জানিয়েছিলেন—
“কলেজে দেখেছি, আই. এ. ও বি. এ. ক্লাসের যে বইগুলো অত্যন্ত নিরস ও কঠিন, যে বই পড়ে ছাত্ররা কোনওরূপ আনন্দ পাবে না, সেই সব বই-ই বেছে বেছে জীবনানন্দবাবুকে পড়াতে দেওয়া হ’ত। অন্য সহজ ও সরস বইগুলো তাঁর বিভাগের অন্য অধ্যাপকরা পড়াতেন। ঐ রকম একটা বইও তাঁকে পড়াবার জন্য দেওয়া হ’ত না।”
একইসাথে তিনি একথাও স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে বি. এম. কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকরা তখন তাঁকে খুবই উপহাস করতেন এবং তিনিও তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। তবে জীবনানন্দকে নিয়ে তাঁদের সেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুধুমাত্র মুখেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ওই কলেজের অনেকেই তখন তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা তো লিখেছিলেনই, একইসাথে সেই কবিতাগুলি বিভিন্ন কাগজে প্রকাশ করেও তাঁর উপরে আক্রমণ চালিয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, ওই সময়ে কর্মক্ষেত্রের বাইরে ‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকার তাঁকে তীব্র আক্রমণ ও গালিগালাজ, এবং একইসাথে কলেজেও সহকর্মীদের একই ধরণের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও আক্রমণ—জীবনানন্দের মত একজন কবি ও ভাবুক মানুষের জন্য নিজের মানসিক অবস্থা স্থির রেখে চলবার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার হয়ে পড়েছিল। তবে জীবনানন্দ অত্যন্ত স্থির ও সহিষ্ণু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলেই তখন সম্ভবতঃ সেসব সহ্য করে চলতে পেরেছিলেন।
জীবনানন্দ বরাবরই তাঁর কবিতার সমালোচনায় খুবই আঘাত পেতেন। কিন্তু তবুও ওই কলেজে তাঁর কবিতা নিয়ে বিদ্রূপকারীরা যেহেতু তাঁর সহকর্মী ছিলেন, এবং তাঁদের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে তিনি বাধ্য ছিলেন—তাই সবসময়েই তিনি তাঁদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকে নিজের স্বভাব সুলভ হাসি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন, আর কলেজে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করাটা যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতেন। বি. এম. কলেজে জীবনানন্দের অধ্যাপক জীবনের কথা বলতে গিয়ে সেখানে তাঁর সহকর্মী থাকা অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তী পরবর্তী সময়ে তাঁর—‘জীবনানন্দকে যেমন দেখেছি’—প্রবন্ধে লিখেছিলেন—
“আজ মনে পড়ে যে ‘নীল জলে সিঙি মাছ’ নামে এক ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশ করে তাঁকে আক্রমণ করেছিলাম। প্রথমে তাঁর চোখে ফুটে উঠল একটা সলজ্জ, অপ্রতিভ কাতর ভঙ্গি। তারপর মুহূর্তেই উৎকট হাস্যের একটা দমকা এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল বিদ্রূপের ধূম্ররাশি। সেই বিদ্রূপযজ্ঞের হোতা ছিলেন অধ্যাপক নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়। … জীবনানন্দবাবু তাঁর কবিত্বের বিরূপ সমালোচনায় বড় ব্যথিত হতেন। বেত্রাহত বালকের মুখে যে করুণ অসহায়তা, তাই দিয়েই তিনি বিরুদ্ধবাদীকে নিরস্ত করতেন। শনিবারের চিঠির গাল খেয়ে তিনি রুষ্ট হতেন কিনা জানি না। কিন্তু কৌতূহলী হয়ে উঠতেন খুব। পত্রিকাখানি এসেছে শুনলে আমার কাছে আসতেন, বন্ধনীর মধ্যে ‘জীবানন্দ নহে’ পড়তেন। তারপর অনন্যসুলভ সেই উপহাসটি উপহার দিয়ে নীরবে উঠে যেতেন। তাঁর কবিত্বের স্বপ্নাবরণ যেন কিছুতেই ছিন্ন হ’ত না। … মাঠের পাশের বাঁকা পথ ধরে কলেজের পিছন দিক দিয়ে কলেজে যেতেন, ক্লাসে শান্ত, গম্ভীর ভঙ্গিতে পড়াতেন; অবসরকালে কষ্টি পাথরের মূর্তিটির মতো বিশ্রামকক্ষের কোণে বসে থাকতেন।”
যাই হোক, বরিশালের ব্রহ্মমোহন কলেজে একজন অধ্যাপক হিসাবে ‘সর্বজনপ্রিয়’ হতে না পারলেও, জীবনানন্দ নিজে তখন কি পরিমাণে পড়াশোনা করতেন, এবং বাইরে থেকে তাঁকে অমিশুক ও অসামাজিক বলে মনে হলেও, বাস্তবে তিনি যে কতটা সহজ, সরল ও মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন—সেকথা পরিচয় এই কলেজেই তাঁর ছাত্র থাকা আবুল কালাম শামসুদ্দীনের একটি লেখা থেকে জানতে পারা যায়। তিনি লিখেছিলেন—
“বাড়ি তাঁর (জীবনানন্দের) একটা মেয়ে স্কুলের কম্পাউন্ডের মধ্যে। খুব সম্ভবত সে স্কুলটা তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাংলো ধরনের বাড়ি, উপরে শণের চাল। বেড়া অর্ধেক ইঁট আর অর্ধেক বাঁশের। কিন্তু ভিতরে সাহিত্য পাঠকের কাছে আশ্চর্য এক জগৎ—বই, বই আর বই। বাংলার, বাংলার বাইরের অসংখ্য পত্রিকা। সবই সযত্নে গুছিয়ে রাখা—দেখেই মনে হয় বার বার পড়া। একধারে একটা ছোট টেবিল। হয়তো তাঁর লেখার।
… সেদিন তাঁর বাড়িতে না গেলে জীবনানন্দবাবু ‘অসামাজিক মানুষ’ এই ধারণা করেই চিরদিন দূরে থেকে যেতাম। সে ধারণা অচিরেই ভেঙে গেল। অমন রাসভারী চেহারার ভিতরে একটা সহজ সরল শিশুর মন খুঁজে পেয়ে আমরা চমৎকৃত হয়ে গেলুম।”
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শামসুদ্দীন যখন উক্ত কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন থেকেই তিনি সাহিত্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে তাঁর নিজের কথায়—
“আমরা তখন লেখায় মক্স করছি। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ কত কী?”
আর সেই ছাত্রজীবন থেকেই শামসুদ্দীনের সাহিত্যচর্চার প্রতি একটা নেশা তৈরি হয়েছিল ছিল বলেই সেই সময়ে তিনি নিজের বাড়িতে মাঝে মাঝেই একটা করে সাহিত্যের সভা বা আড্ডা বসাতেন। জীবনানন্দ শামসুদ্দীনের আমন্ত্রণে তাঁর বাড়ির সেই আড্ডাতেও যোগ দিতেন। এপ্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শামসুদ্দীন লিখেছিলেন—
“আমাদের ছোট টিনের ঘরে দোতলায় তাঁকে সাহিত্যের আড্ডাতেও পেয়েছি। একদিন সেই আড্ডায় অচিন্ত্যকুমারকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন বলে মনে হয়।”
যদিও শামসুদ্দীন বলেছিলেন যে, বরিশালে জীবনানন্দের বাড়িটি সম্ভবতঃ জীবনানন্দের পিতার প্রতিষ্ঠিত একটা মেয়েদের স্কুলের কম্পাউন্ডের মধ্যেই ছিল, কিন্তু তাঁর জীবনীকারদের মতে—জীবনানন্দের সেই বাড়িটি মেয়েদের স্কুলের কম্পাউন্ডের মধ্যে নয়, বরং জীবনানন্দের বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যেই মেয়েদের সেই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে সেই স্কুলটি অল্প কিছুদিনের জন্যই সেখানে ছিল এবং সেটি আসলে ছোট ছোট মেয়েদের স্কুল ছিল। যদিও জীবনানন্দের এক পিসিমা সেই স্কুলটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তবে ওই স্কুল তৈরি করবার ব্যাপারে অবশ্য জীবনানন্দের পিতারও সাহায্য ছিল। জীবনানন্দের সেই পিসিমা চিরকুমারী ছিলেন। নিজের প্রথম জীবনে তিনি সেখানেই স্থানীয় মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন, পরবর্তী সময়ে শিক্ষকতার কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পরে নিজের শেষ বয়সে কিছুদিনের জন্য নিজের বাড়িতে তিনি ছোট ছোট মেয়েদের একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
জীবনানন্দ বরিশালের বি. এম. কলেজে ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন বলে জানা যায়। সেই সময়ে ওই কলেজে চাকরি পাওয়ার ফলে তাঁর যেমন আর্থিক সচ্ছলতা হয়েছিল, তেমনি তিনি নিজের বাড়িতে সপরিবারে থাকবার জন্য কিছুটা মানসিক শান্তিও পেয়েছিলেন। আর সেই সময়ের মধ্যেই, ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর একমাত্র পুত্র সমরানন্দেরও জন্ম হয়েছিল। তাই বাইরের মানুষ তখন তাঁর কবিতা নিয়ে যতই বিদ্রূপ করুক না কেন, তিনি কিন্তু ওই কলেজে অধ্যাপক থাকবার সময়েও প্রচুর কবিতা লিখেছিলেন এবং সমকালীন বহু পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশও করেছিলেন।
জীবনানন্দ যে বছর বি. এম. কলেজে অধ্যাপকের চাকরি পেয়েছিলেন, ঠিক সেই বছরই, অর্থাৎ—১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বা ১৩৪২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে বুদ্ধদেব বসু তাঁর ত্রৈমাসিক ‘কবিতা’ পত্রিকাটি প্রকাশিত করতে শুরু করেছিলেন। জীবনানন্দ তখন শুধুমাত্র কবিতা পত্রিকাতেই কিভাবে তাঁর কবিতাগুলি প্রকাশ করেছিলেন, নিচে প্রথম দু’বছরে প্রকাশিত কবিতা পত্রিকা থেকে সেটার একটা হিসাব তুলে ধরা হল—
১৩৪২ বঙ্গাব্দ—১ম বর্ষ
১ম সংখ্যা, আশ্বিন→মৃত্যুর আগে;
২য় সংখ্যা, পৌষ→বনলতা সেন, কুড়ি বছর পরে, মৃত মাংস, ঘাস;
৩য় সংখ্যা, চৈত্র→হওয়ার রাত, আমি যদি হতাম, হয় চিল;
৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ়→শঙ্খমালা, বুনো হাঁস।
১৩৪৩ বঙ্গাব্দ–২য় বর্ষ
১ম সংখ্যা, আশ্বিন→নগ্ন নির্জন হাত, শিকার, বলিল অশ্বত্থ নেই, নদী, হাজার বছর শুধু খেলা করে;
২য় সংখ্যা, পৌষ→সিন্ধু সারস, রাত্রি মাখা ঘাসে (পরে পরিবর্তিত নাম–নিরালোক), স্বপ্ন, হরিণেরা;
৩য় সংখ্যা, চৈত্র→শ্রাবণ রাত, বিড়াল;
৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ়→আদিম দেবতারা, মুহূর্ত।
উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, তখন তিনি কবিতা পত্রিকার কোনো কোন সংখ্যায় চার-পাঁচটা পর্যন্ত কবিতাও প্রকাশ করেছিলেন। তবে এই তালিকার কবিতাগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি অবশ্য ১৩৪২ বঙ্গাব্দের বা ১৯৩৫ সালের আগেই তিনি লিখেছিলেন। যাই হোক, এথেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, জীবনানন্দ বি. এম. কলেজে অধ্যাপনা করবার সময়ে দীর্ঘদিন এভাবে কম-বেশি হিসাবে বহু কবিতাই বুদ্ধদেব বসুর পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া সমকালীন অন্যান্য পত্রিকায় তো তিনি লিখেছিলেনই।
কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপনাকালে জীবনানন্দ যেমন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরা পালক’ প্রকাশ করেছিলেন, তেমনি বরিশালের বি. এম. কলেজে অধ্যাপনাকালেই তিনি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ—‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ এবং তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ—‘বনলতা সেন’ প্রকাশ করেছিলেন।#