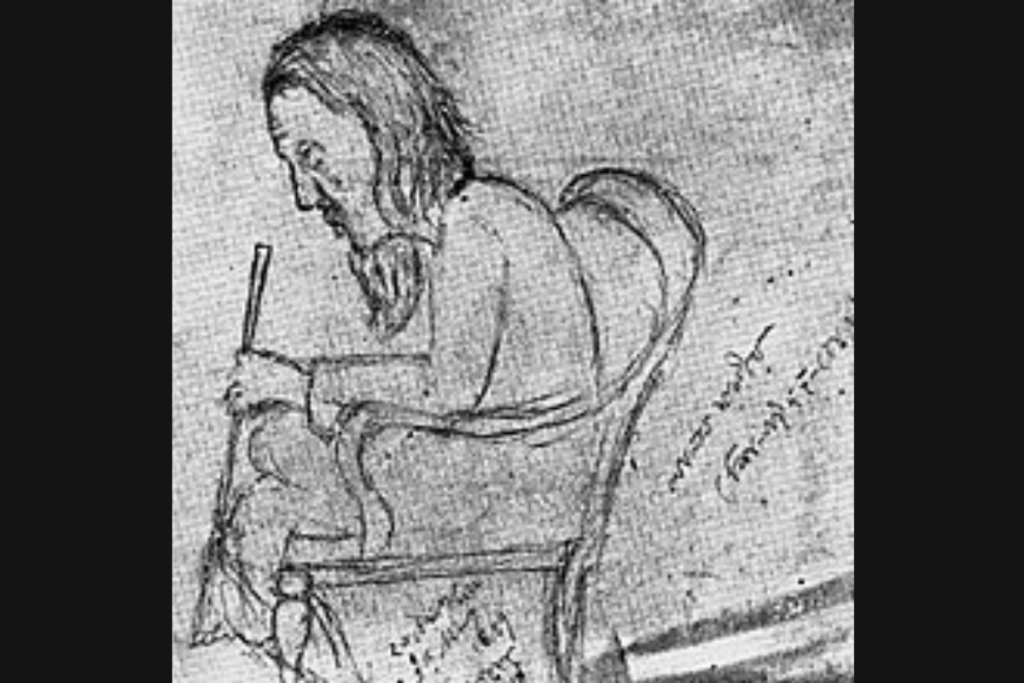লালন ফকিরের জন্মসাল সম্পর্কে আজও কেউ নিঃসন্দেহ নেন। তবুও সাধারণভাবে তাঁর জীবনকাহিনী নিয়ে মানুষ যতটা পরিচিত রয়েছেন, সেটা এরকম—
লালন এক হিন্দু বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি মহাব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তাঁর আত্মীয়স্বজনরা তাঁকে পরিত্যাগ করেন। সেই সময়ে এক মুসলমান রমণী কর্তৃক তিনি শুশ্রূষা পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে লালন ফকির ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেন। নিজের জাত সম্পর্কে তাঁকে কোন প্রশ্ন করা হলে তিনি উদাসীনভাবে তাকিয়ে থাকতেন ও ঠোঁটের কোণে এক রহস্যময় হাসি আনতেন। হয়ত নিজের বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত জীবনে তিনি জাতের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাইতেন না। আর এভাবেই নিজের জীবদ্দশা ও মৃত্যুর পরে তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির এক মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।
তবে তাঁর মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে সকলেই নিঃসন্দেহ। ১৮৯০ সালের ১৭ই অক্টোবর বা ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১লা কার্তিক তারিখে কুষ্টিয়ার উপকণ্ঠে ছেঁউরিয়ার আখড়ায় লালন ফকির দেহত্যাগ করেছিলেন। সমকালীন পাক্ষিক ‘হিতকরী’ পত্রিকার একটি বিশেষ সম্পাদকীয় নিবন্ধে তাঁর সেই মৃত্যুসংবাদ ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল। মীর মোশাররফ হোসেন—যাঁকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষার একজন শক্তিশালী লেখক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে—তিনি উক্ত পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন; তবে সম্পাদক হিসেবে পত্রিকাটিতে কারো নাম প্রকাশিত হত না। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১৫ই কার্তিক তারিখে উক্ত পত্রিকার প্রথমভাগের ১৩তম সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে লালনের মৃত্যু নিয়ে যে সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছিল, সেটা নিম্নরূপ ছিল—
“লালন ফকির ১১৬ বছর বয়সে গত ১৭ অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।”
যদিও হিতকরী পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে লালনের বয়সকে একশো ষোলো বছর বলে স্বীকার করে নিয়ে বর্তমানের অনেক লালন গবেষক ১৭৭৪ সালকে তাঁর জন্মসাল বলে চিহ্নিত করে থাকেন, কিন্তু তবুও এবিষয়ে যেহেতু কোনো প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিল এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, সেহেতু এই সালটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভব নয়।
এটা গেল বর্তমানে লালন সম্পর্কে বিতর্কের একটি দিক। কিন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে তাঁকে নিয়ে যে নতুন বিতর্কটি দেখা দিয়েছে, সেটা হল যে—তিনি জন্মগতভাবে কোন সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন? হিন্দু নাকি মুসলমান? এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়ার কারণ হল যে, সাম্প্রতিক অতীতে পূর্ববঙ্গের বেশ কিছু গবেষক দাবি করেছিলেন যে, লালন নাকি জন্মগতভাবেই মুসলিম ছিলেন। এপ্রসঙ্গে আলোকপাত করবার জন্য প্রথমেই আবুল আহসান চৌধুরীর লেখা ‘লালনচর্চার ইতিহাস’ নামক গ্রন্থটির দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। উক্ত গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যানুসারে লালনের জীবদ্দশাতেই ১৮৭২ সালের আগস্ট মাসের ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ পত্রিকায় ‘জাতি’ শিরোনামের একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে লালনের ধর্মমত সম্পর্কে নিম্নের মন্তব্যটি করা হয়েছিল—
“লালন শা নামে এক কায়স্থ আর এক ধর্ম আবিষ্কার করিয়াছে। হিন্দু মুসলমান সকলেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। তিন চার বৎসরের মধ্যেই এই সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল হইয়াছে। ইহারা যে জাতিভেদ স্বীকার করেন না, সে কথা বলা বাহুল্য।”
যদিও এই নিবন্ধের রচয়িতা হিসেবে পত্রিকাটিতে কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবুও অনেকে অনুমান করে থাকেন যে, পত্রিকাটির সম্পাদকই এই নিবন্ধটির রচয়িতা ছিলেন। সেযুগের পূর্ববঙ্গের কুষ্টিয়ার প্রসিদ্ধ সাংবাদিক হরিনাথ মজুমদার, যিনি বাংলার ইতিহাসে ‘কাঙাল হরিনাথ’ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ—তিনিই তখন পূর্বোক্ত গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায় যে, তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৩৩ সালে এবং মৃত্যু হয়েছিল ১৮৯৬ সালে। তিনি লালনের একজন বন্ধু এবং সমর্থক ছিলেন। ১২৯২ বঙ্গাব্দে কাঙাল হরিনাথের লেখা ‘ব্রহ্মাণ্ড বেদ’ নামের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, যেটির প্রথম সংখ্যায় লালন সম্পর্কে বলা হয়েছিল—
“হৃদয় নির্মলা হইলে ভগবানের ভাব প্রস্ফুটিত হয়, ইঁহারই নাম তাঁহার আকার, প্রকাশ, আবির্ভাব, দর্শন প্রভৃতি শব্দে সাধক ও ভক্তগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন। ভগবত ভক্ত ব্যতীত এই প্রকার দর্শন আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। লালন ফকির নামে জনৈক ভক্ত এই সম্বন্ধে যে একটি গান প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম—
‘কে বোঝে সাঁইয়ের লীলাখেলা
দেখিয়া সব পুঁথির পালা।’ …”
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এটিই লালনের জীবদ্দশায় তাঁকে নিয়ে প্রথম কোন মুদ্রিত লেখা ছিল। তবে কাঙাল হরিনাথও লালনের জন্মসাল বংশ ইত্যাদি নিয়ে তেমন কোন নাড়াচাড়া করেননি, হয়ত এবিষয়ে তেমন কোন প্রশ্নও তাঁর মনে উত্থাপিত হয়নি। বরং তিনি লালনকে অনুসরণ করে বেশ কিছু গান লিখেছিলেন বলে জানা যায়, এবং ফকির চাঁদ ভণিতায় তাঁর লেখা সেই গানগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। আর সেই গানগুলি থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, তাঁর ভাবাদর্শে লালনের স্থান কতটা উঁচুতে ছিল।
যাই হোক, লালনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার যে বর্ণনা ‘হিতকারী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেটা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, লালন মনে প্রাণে একজন মানবতাবাদী ছিলেন। এপ্রসঙ্গে উক্ত পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—
“মৃত্যুকালে কোনো সম্প্রদায়ের মতানুসারে তাঁহার অন্তিমকার্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছু লাগে নাই। গঙ্গাজল হরে রাম নামও দরকার নাই। তাঁহারই উপদেশানুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না।”
হিতকারীর এই সংবাদ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, নিজের শেষ কাজ কেমনভাবে হবে, সেবিষয়ে লালন আগে থাকতেই সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন; এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর অনুগামী ভক্তরা সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। লালন গবেষকদের মতে—আসলে লালন তৎকালীন প্রান্তিক সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন বলেই সম্ভবতঃ এমন করা সম্ভব হয়েছিল। যদি তিনি সেযুগের তথাকথিত উচ্চবর্গীয় সমাজের মানুষ হতেন, তাহলে হয়ত তাঁর সেই নির্দেশ অমান্য করবার সম্ভাবনা থাকত, এবং সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে তাঁর শিষ্য এবং অনুচরেরা মহাসাড়ম্বরে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করে কোনো একটি ধর্মের প্রতীকস্বরূপ অহংকারের ধ্বজা উড়িয়ে দিতেন।
লালনের মৃত্যুর পরে তাঁকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গে একটি বাউলচর্চার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং ছেঁউরিয়ার আখড়ায় তাঁর একটি সমাধি সৌধও স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু অনেকের মতে সেক্ষেত্রেও তখন একটি সূক্ষ্ম স্বার্থবুদ্ধি কাজ করেছিল। এপ্রসঙ্গে আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর ‘লালন শাহ’ গ্রন্থে জানিয়েছিলেন—
“ছেঁউরিয়া মৌজায় লালন ভক্ত মলন শাহ কারিকর লালন ফকিরকে প্রায় সাড়ে ১৬ বিঘা জমি দান করেন। এই দানকৃত জমির প্রায় অর্ধাংশে লালনের আখড়া গড়ে ওঠে। স্থানীয় কারিকর শ্রেণীর ভক্তবৃন্দ লালনের বসবাস ও সাধনার জন্য এই আখড়ার চতুর্দিকে বারান্দা যুক্ত একটি পূর্ব দুয়ারি চারচালা বড়ো খড়ের ঘর তৈরি করে দেন। লালন পরে, যেখানে এখন তাঁর সমাধি আছে, সেখানে একটি গোলাকৃতি বড়ো খড়ের ঘর তৈরি করে বাস করতে থাকেন। এই ঘরেই তাঁর ভজন সাধন চলত। মৃত্যুর পর এখানেই তিনি সমাধিস্থ হন।”
কিন্তু লালনের মৃত্যুর পরেই তাঁর শিষ্যদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে, বিশেষতঃ তাঁর সমাধি সৌধটি নিয়ে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। একথার দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে লালন শিষ্য মনিরুদ্দিন শাহের সকাতর আবেদনপত্রটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেটার দিকে নজর দিলেই বুঝতে পারা যায় যে, লালনের উত্তরাধিকার নিয়ে তখন তাঁদের মধ্যে কি ধরণের ঝগড়ার সৃষ্টি হয়েছিল। মনিরুদ্দিন শাহ লালনের সমাধিতে একটি পাকাবাড়ি তৈরি করবার আবেদন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—
“আজ এই দরখাস্ত দ্বারা আবেদন করিতেছি যে, আমার পরমারাধ্য গুরু লালন শাহ ছায়েবের সমাধি পাকা ইমারত করাইবার অনুমতি হুজুরের সরকার হইতে পাইয়াছিলাম। হুজুর বিলাত হইতে আসিয়া শ্রীযুক্ত মাননীয় নগেন্দ্রবাবু মহাশয়ের প্রতি ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সমাধিস্থানে গমন পূর্বক দৈর্ঘ্য প্রস্থের পরিমাপ করিয়া আসিয়া ছিলেন এবং এসটিমেট প্রস্তুত করাইয়া লইয়া ছিলেন। দুর্ব্বৎসর দেখিয়া শিলাইদহের কাছারির কর্মচারী মহাশয়দিগেরা কয়েক মাসের জন্য সমাধি পাকা করানোর বিষয়ে স্থাগিত রাখিয়াছেন।”
কিন্তু ইতিমধ্যে লালনের অপর দুই শিষ্য—ভোলাই এবং শীতল শাহ—মাটির কাদা দিয়ে গাঁথনি করে সেখানে একটি ঘর তৈরি করে ফেলেছিলেন। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে বজ্রপাতের ফলে লালন শাহের সেই সমাধি সৌধের দক্ষিণ দিকের অংশটি একেবার ভেঙে গিয়েছিল। এরপরে ১৯৪৯ সালে লালন শাহ আখড়া কমিটির পক্ষ থেকে সেই ভেঙে পড়া সৌধটি পুনরায় নতুন করে তৈরি করবার চেষ্টা করা হলেও টাকার অভাবে শেষপর্যন্ত সেই প্রয়াস আর সফল হতে পারেনি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম হয়ে গিয়েছিল এবং তখনও পর্যন্ত সেখানকার সরকার লালন শাহ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কোন আগ্রহ দেখায় নি। এরফলে পরবর্তী একদশক, অর্থাৎ—১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত লালনের সমাধির দিকে কারো নজর না পড়বার ফলে সেটি অনাদৃত ও অবহেলিত অবস্থাতেই থেকে গিয়েছিল। এরপরে মোহিনী মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার পদে কর্মরত দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী লালনের সমাধিস্থলটি সংস্কার করবার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়াসে তখনকার দিনের হিসেবে প্রায় আট হাজার টাকা খরচ করে সেখানে একটি সৌধ নির্মাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। সেবারে তাঁর ব্যবস্থাপনায় নতুন বাড়ি তৈরি হবে বলে আগেকার সৌধটি একেবারে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে দেবীপ্রসাদ শেষপর্যন্ত তাঁর সেই স্বপ্নকে সফল করতে পারেননি। এপ্রসঙ্গে পৃথ্বীরাজ সেন তাঁর ‘লালন ফকির: জীবন ও সাধনা’ গ্রন্থে জানিয়েছিলেন—
“কী সেই কারণ, সে সম্পর্কে যথেষ্ট অনুসন্ধান করা হয়েছে। কিন্তু আমরা সেই রহস্য এখনও উদঘাটন করতে পারিনি। হয়তো স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কেউ কেউ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। এর অন্তরাল কি সাম্প্রদায়িকতার ছায়া ছিল? অবশ্য এসব আমাদের অনুমান—ঐতিহাসিক সত্য জানা সম্ভব নয়।”
কিন্তু এরপরেই একপ্রকার হঠাৎ করেই লালনের সমাধিস্থল নিয়ে পরিবেশ এবং আবহাওয়া পুরোপুরি বদলে গিয়েছিল; এবং ১৯৬৩ সালে মুহম্মদ মনসুর উদ্দিনের প্রস্তাবে সেখানে লালন শাহের সুদৃশ্য সৌধ এবং মাজার গড়ে উঠেছিল ও লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্রের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারও তখন সেবিষয়ে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেছিল। সরকারের গণ পূর্ত বিভাগের বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ এম. এ. হাই–এর করে দেওয়া নকশা অনুসারেই তখন সেখানে লালনের বিশাল সমাধিক্ষেত্রটি গড়ে উঠেছিল। পৃথ্বীরাজ সেনের বক্তব্যে—
“এই সমাধি ক্ষেত্রটি দেখলে দিল্লির মুসলমান সাধক হজরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মকবরার কথা মনে পড়ে যায়। অনেকে বলে থাকেন, এভাবেই পাকিস্তান সরকার লালন ফকিরের ইসলামিকরণের কাজ শুরু করে দেয়।”
অতীতে এপ্রসঙ্গে বিশিষ্ট লালন গবেষক এ. এইচ. এম. ইমামউদ্দিন তাঁর ‘বাউল মতবাদ ও ইসলাম’ গ্রন্থে যে মন্তব্যটি করেছিলেন, সেটাও এখানে অবশ্য উল্লেখ্য। তিনি লিখেছিলেন—
“কতিপয় লালন ভক্ত সুধী ব্যক্তির চেষ্টার বিলুপ্ত প্রায় লালন শাহের আখড়া নবজীবন লাভ করিল, গড়িয়া উঠিল লালন স্মৃতিসৌধ। আখড়া পরিণত হইল মাজার শরীফে এবং লালন শাহ উন্নীত হইলেন মহাসুফী সাধক পদে।”
তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ করে পৃথ্বীরাজ সেন জানিয়েছিলেন—
“মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য আঙ্গিক থেকে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন, লালন লোক সাহিত্য কেন্দ্র স্থাপন করা বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের পক্ষে এক সসম্মানীয় প্রয়াস। তবে আজ পর্যন্ত এই লোকসাহিত্য কেন্দ্রের তরফে সৃষ্টিশীল কোনো গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়নি শুধুমাত্র মাঝে মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের নামবদল হয়েছে। ১৯৬৩ সালের লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র ১৯৭৬ সাল থেকে লালন অ্যাকাডেমি নামে পরিচিত। কিন্তু এখানে লালন গীতির একটি নির্ভরযোগ্য সংকলন কি থাকতে পারত না? কেন প্রকাশিত হয়নি লালনের ঘটনাবহুল জীবনের ইতিবৃত্ত?”
ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী সমাজের অনেকেই লালন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন এবং লালনের হিন্দু উৎস সম্পর্কে সন্দেহপ্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ‘হিতকারী’ পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে জানতে পারা যায় যে, লালন জন্মগতভাবে হিন্দু পরিবারের সন্তানই ছিলেন। অন্যদিকে লালনচর্চার ইতিহাসের কালপঞ্জী থেকে জানা যায় যে, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে বসন্ত কুমার পাল প্রথমে সেযুগের বিখ্যাত ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় লালন ফকিরের পরিচিতি লিখেছিলেন, এবং পরে ১৩৬২ বঙ্গাব্দে তিনি লালনের জীবন অবলম্বনে ‘মহাত্মা লালন ফকির’ নামের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ লিখেছিলেন। অতীতে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মতিলাল দাস, মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন প্রমুখ লালন গবেষকরা বসন্ত কুমার পাল লিখিত লালনের সেই জীবন বিবরণকেই সত্যি বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এছাড়া তাঁরা সকলেই জানিয়েছিলেন যে, যে লালন আসলে ভাঁড়ারা, অর্থাৎ—কুষ্টিয়ার মানুষ ও জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন, কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় তিনি শেষপর্যন্ত জাতি বিশ্বাসহীন একজন গৌণধর্মী ফকিরে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরেই হঠাৎ করে একদল নতুন লালন গবেষক একথা প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছিলেন যে, লালন নাকি জন্মসূত্রেই মুসলমান ছিলেন! তখন তাঁদের সেই অপপ্রয়াস লক্ষ্য করে ব্যথিত চিত্তে মনসুরউদ্দিন ১৩৭১ বঙ্গাব্দে লিখেছিলেন—
“ইদানিং এখানে দেখা যাইতেছে অনেকেই প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া লালন শাহকে জন্মকাল হইতে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতেছেন ও লালন শাহের জন্মস্থান যশোহরে বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার, সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল ইঁহারা সকলেই তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন।”
এরপরে মনসুরউদ্দিনের লেখা সেই প্রতিবাদ প্রবন্ধটি পড়ে তরুণ লালন গবেষক লুৎফর রহমান ১৯৮৪ সালে তাঁর ‘লালন জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থে যে ক’টি প্রশ্ন তুলেছিলেন, সেগুলির মধ্যে একটি নিম্নরূপ ছিল—
“প্রাণান্ত পরিশ্রম করলেই কি কোনো মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায়? লালন শাহ জন্মগতভাব মুসলিম সন্তান, একথা তিনি স্বীকার না করলেও সত্য। লালনের জন্মস্থান যে ভাঁড়ারা নয়, যশোর জেলার হরিশপুরে—সেকথাও সত্য। তার প্রমাণ দুদ্দুশাহের বর্ণনায়, মরহুম আবদুল ওয়ালি লিখিত প্রবন্ধে। এসব তথ্য বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রমাণের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই।”
আর লুৎফর রহমানের গ্রন্থটি বিশ্লেষণ করে পৃথ্বীরাজ সেন তাঁর ‘লালন ফকির: জীবন ও সাধনা’ গ্রন্থে যে তথ্যগুলি উপস্থাপিত করেছিলেন, সেগুলির কিছুটা নিম্নরূপ—
“লুৎফর রহমান যে দুদ্দু শাহের কথা বলেছেন, তাঁর কী পরিচয়। তাঁকে আমরা লালন পরবর্তী এক শক্তিশালী গীতিকার হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। লুৎফর রহমান তাঁর লেখা একটি কলমী পুঁথি নিজ প্রয়াসে মুদ্রিত করেন। অনেক গবেষক এই পুঁথিটিকে জাল বলে মনে করেন।
আবদুল ওয়ালি কে ছিলেন? তিনি ছিলেন ইংরেজ আমলে যশোরের শৈলকুপার সাব রেজিস্ট্রার। ৩০ নভেম্বর ১৮৯৮ সালে তিনি বোম্বাইয়ের অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটিতে একটি ভাষণ দেন। এই ভাষণের বিষয় ছিল, বাংলার ফকির সম্প্রদায়ের কিছু অপ্রচলিত প্রথা। এই প্রবন্ধটি পরে ১৯০০ সালে পঞ্চম খণ্ডের চতুর্থ সংখ্যায় সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটির মাধ্যমে আবদুল ওয়ালি বলেছেন যে, লালন এবং তাঁর গুরু সিরাজ সাঁই যশোর জেলার হরিশপুরের মানুষ। তবে লালনকে তিনি ‘নোন অ্যাজ কায়স্থ’ বলে একটি সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ যশোর জেলার মানুষ হওয়া সত্ত্বেও লালন জন্মসূত্রে হিন্দু—এই কথা স্বীকার করেছেন আবদুল ওয়ালি।”
কিন্তু এখানে যে প্রশ্নটি থেকে যায়, সেটা হল যে, হঠাৎ করে লালন ফকিরকে ইসলামীকরণ করবার প্রচেষ্টা কেন শুরু হয়েছিল? অতীতের অনেকেই এপ্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমান দ্বিজাতি সমস্যার কথা টেনে এনেছিলেন। তাঁদের মতে দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় হীনমন্যতা শিকার হয়েছিলেন; এবং তাঁদের এজাতীয় মনোভাবের অন্তরালে তখন অনেকগুলি সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণ বর্তমান ছিল। সেকালের পূর্ববঙ্গের বেশিরভাগ ভূমিখণ্ডই হিন্দু জমিদারদের অধীনে ছিল। সেইসব উচ্চ বংশীয় হিন্দু জমিদারেরা নানাভাবে নিম্নবর্গীয় হিন্দু এবং মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করতেন; কখনো তাঁদের দিকে সুনজরে তো দেখতেনই না, বরং লেঠেল এবং পাইক বরকন্দাজ দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করতেন। এরফলে তাঁদের প্রতি বৈরীতার ভাবের জন্ম হয়েছিল, এবং তখনকার সেই অবস্থায় মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুমাত্রকেই তাঁদের জাতশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলেছিলেন।
পৃথ্বীরাজ সেন জানিয়েছিলেন—
“হয়তো এই সব বিষয়গুলিকে আলাদাভাবে বিচার বিবেচনা করা উচিত। ভাবতে অবাক লাগে, লালনের মহাপ্রয়াণের দীর্ঘকাল পরেও তাঁকে মুসলমান বলে গণ্য করার স্বপক্ষে কোনো দলিল দস্তাবেজে তুলে ধরা হয়নি। গবেষকরাও এ বিষয়ে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব ছিলেন। ১৮৯০ সাল অর্থাৎ লালনের মৃত্যুবর্ষ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এই বিষয়টি নিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলে কোনো চর্চা হয়নি। লালন যে মুসলমান, একথা প্রথম বলেছিলেন মুহম্মদ আবু তালিব। ১৯৬৮ সালে তাঁর প্রকাশিত ‘লালন পরিচিতি’ বইতে তিনি জানিয়েছেন—
‘বর্তমান লেখকই সর্বপ্রথমে লালনের সত্য জীবনের প্রতি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তিনিই সর্ব প্রথমে লালনকে যশোহর জেলারে হরিশপুর নিবাসী এবং জন্মগতভাবে মুসলিম সন্তান হিসাবে দাবি করেন। ১৩৬০ সালের (১৯৫৩ ঈসায়ীর আগস্ট) ভাদ্র সংখ্যা মাহেনাও পত্রিকায় তিনি সমস্ত প্রচলিত ধারণার প্রতিবাদ করে বলেন—আনুমানিক ১১৭৩ (১৭৬৬ ইংরাজি) সালে যশোহর জেলার অধীন হরিনাথকুঞ্জ থানার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামের এক খোনকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন লালন শাহ।’
লালন কি সত্যি খোনকার বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের মতো এক বিশিষ্ট প্রবন্ধকার ১৩০২ বঙ্গাব্দে কুষ্টিয়ার কুমারখালি অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন উৎসাহী গবেষক। বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই বিষয়ে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা লিপিবদ্ধ হয় ভারতী পত্রিকায়। তিনি লিখেছেন—
‘লালনের ধর্মমত অতি সরল ও উদার ছিল। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না, হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন ও শিষ্যদিগের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সকল জাতিকেই গ্রহণ করিতেন। লালন হিন্দু নাম, শা উপাধি মুসলমান জাতীয়—সুতরাং অনেকেই তাঁহাকে জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিত। তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে স্বপ্রণীত নিম্নলিখিত গানটি শুনাইতেন—
‘সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে
লালন ভাবে, জাতির কী রূপ দেখলাম না এ নজরে।’
লালন কেন তাঁর জাতের কথা সর্বসমক্ষে ঘোষণা করতেন না? এর অন্তরালে হয়তো অনেকগুলি কারণ আছে। প্রসঙ্গত আমরা লালনের বিশেষ পরিচিত কাঙাল হরিনাথের কথা বলব। হিতকরী পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তিনি লিখেছেন—
‘লালন নিজের কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, অথচ সকল ধর্মের লোকই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আচার-ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত। বৈষ্ণব ধর্মের মত পোষণ করিত দেখিয়া হিন্দু ইঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওড়াইত।’
লালনের চরিত্রের এই উদার নির্ভীকতা আমাদের অবাক করে দেয়। সব অর্থে তিনি ছিলেন প্রগতিশীল মানবতাবাদী। নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সাহস এবং সামর্থ ছিল তাঁর জন্মগত। এখানে একটি প্রশ্ন করা যেতে পারে, তাহল, যদি জন্মগতভাবে লালন মুসলমান হতেন, তাহলে সর্বসমক্ষে তা গোপন করবেন কেন? কেউ কেউ বলে থাকেন, তিনি ইসলামী আচার ত্যাগ করে অনুভববাদী মারফতি ফকির হয়ে অবস্থান করছিলেন। এই জাতীয় অনেক ফকির পূর্ব বাংলায় আসেন। তাঁরা কিন্তু তাঁদের জন্ম পরিচয়ের কথা সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন। এর জন্য তাঁরা মৌলবাদীদের হাতে বারবার লাঞ্ছিত ও অবহেলিত হয়েছেন, তবুও সত্যকে গোপন করেন নি।
লালনের সমসাময়িক ভাবসাধক গীতিকার পাগলা কানাইয়ের মৃত্যু হলে তাঁর শোক মিছিলে মৌলবীরা যোগ দেন নি। লালন বোধহয় এসব খবর জানতেন। তিনি বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর কোনো ধর্মমতে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হবে না।
কুষ্টিয়াবাসী মুসলমান এ. এইচ. এম. ইমামউদ্দিন তাঁর ‘বাউল মতবাদ ও ইসলাম’ বইতে লালনের জন্ম—পরিচয় সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন—
‘ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে
তার কাছে জাতের বিচার নাই।’
এই আলোচনায় একথা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, লালন জাতিতে বিশ্বাস করিতেন না। ছেঁউড়িয়ার যে পল্লীতে তিনি বাসা বাঁধিয়া ছিলেন, তাহার অধিকাংশ মোমিন সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। তিনি এক মুসলমান মেয়েকে নিকাহ করিয়া ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি মুসলমান, একথা প্রকাশ করিতে তাঁহার ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। তবুও তিনি জাতিত্বের পরিচয় প্রকাশ করেন নাই, তাহা হইলে কি লালন তাঁর জাতিত্বের আসল পরিচয় গোপন করিয়াছিলেন?
এই বক্তব্যের শেষ শব্দ ক’টি যথেষ্ট রহস্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতবাহী। এর থেকেই হয়তো ওই গবেষক বলতে চেয়েছিলেন যে, জন্মগতভাবে লালন ছিলেন হিন্দু।
ইমামউদ্দিন সাহেব আর একটি ভালো প্রশ্ন করেছেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, ‘লালন জীবিতকালে যে জাতের গণ্ডিতে আবদ্ধ হইতে চাহেন নাই, এখান তাঁহাকে জাতের সীমারেখায় আবদ্ধ করিলে কি তাঁহার উপর অন্যায় ও অবিচার জুলুম করা হইবে না?’
এ প্রশ্ন শুধু নির্মোহী গবেষক ইমামউদ্দিনের নয় আরও অনেক সত্যান্বেষী গবেষক বারবার এই প্রশ্ন করেছেন। এমনকি বাংলাদেশের গবেষকরা পর্যন্ত এব্যাপারে পারস্পরিক বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন। একদল সত্যান্বেষক চাইছেন, লালনের জাত বিচার করার অপচেষ্টা থেকে দূরে থাকতে। অন্য আর একদল গবেষক সরকারি অর্থানুকূল্যে গবেষণা করে লালনের পূর্ব পরিচয় জানতে আগ্রহী। তাঁরা সমবেতভাবে এই কথা সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেছেন যে, লালন জন্মগতভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বী।
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আজও লালন ফকিরের কোনো তথ্যানুসারী জীবনপঞ্জী রচনা করা সম্ভব হয় নি। নিজের পূর্ব জীবন সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ মৌলাবলম্বন করতেন। হয়তো সেখানে ছিল দারুণ জ্বালা। তাই তিনি এই জীবনের কথা স্মরণ করতে চাইতেন না। এর ফলে প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছেও লালনের পূর্ব জীবনের ইতিহাস ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।
অনুমান সম্বল বেশ কিছু গুজব লালনের নামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আমরা জানি বাঙালিরা আবেগপ্রবণ এক হুজুগে জাতি, এই স্বভাব আজও আমরা সযত্নে বহন করে চলেছি। যে কোনো মানুষকে কেন্দ্র করে যে মিথ বা কষ্টকল্পনা গড়ে ওঠে, আমরা সেদিকেই বেশি আকর্ষণ বোধ করি। রহস্য প্রহেলিকা সরিয়ে সত্যসূর্যের সন্ধান করতে চাই না। লালনের কথা একই কথা প্রযোজ্য।”
লালন জন্মগতভাবে হিন্দু নাকি মুসলমান ছিলেন, সে প্রসঙ্গে পৃথিরাজ সেনসহ একাধিক গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ সমেত বিভিন্ন আলোচনা পাওয়া যায়, এবিষয়ে আগ্রহীরা সেসব পড়ে নিজেদের অনুসন্ধিৎসা মিটিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে এপ্রবন্ধের পরিশেষে যে কথা বলবার সেটা হল যে, লালন জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন নাকি মুসলমান ছিলেন—এ বিতর্ক একেবারেই অবাঞ্চিত ও অবাস্তব। বরং একথা বললেই সবথেকে ভালো হয় যে, তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির এক জ্বলন্ত ঐতিহাসিক প্রতীক। সেখান থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে, তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমতকে অগ্রাহ্য করে, তাঁকে ইসলামীকরণ করবার অপচেষ্টা করলে—তিনি যে কত বড়ো মাপের একজন সাধক ছিলেন, মানবতাবাদী মহান দরদী হিসাবে পৃথিবীতে এসেছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনে চলবার পথে তাঁকে যে কত রক্তাক্ত অধ্যায় অতিক্রম করতে হয়েছিল, কিন্তু সেসব সত্ত্বেও তিনি কখনো হতোদ্যম হননি বা ভেঙে পড়েননি—এসব উজ্জ্বল দিকচিহ্নগুলি অনাদৃত ও অবহেলিত থেকে যাবে, যা শেষপর্যন্ত ইতিহাসেরই ক্ষতি করবে। তাই লালন শাহকে লালন শাহ থাকতে দেওয়াই সকলের জন্য মঙ্গলের।#