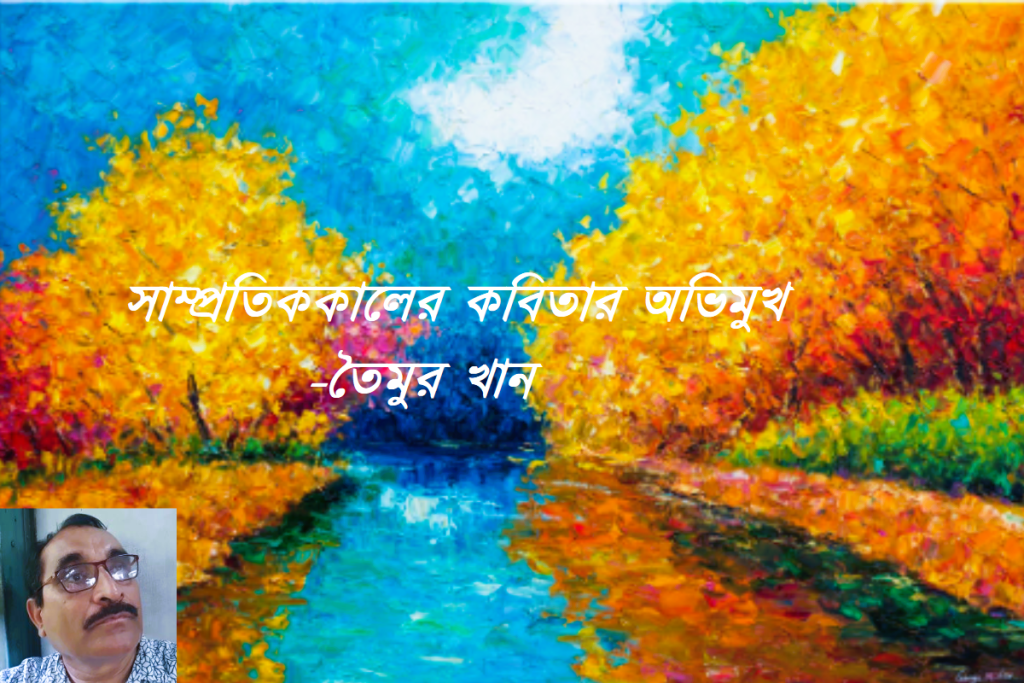সাম্প্রতিককালে পত্রপত্রিকায় অধিকাংশ কবিরাই যেসব কবিতা লিখছেন, তাতে বহুমুখী কাব্যধারার পরিচয় ফুটে উঠছে। হাংরি বা শ্রুতি আন্দোলন বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে অনেকখানি জায়গা দখল করে আছে। কিন্তু তারপরেও বাংলা সাহিত্য থেমে থাকেনি। বাংলা কবিতাকে আমরা অনেকেই বিদেশি সাহিত্যের বা শিল্পের প্রভাবান্বিত বলে থাকি। একথা অস্বীকার করা যায় না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, মেঘনাদ বধ ইত্যাদি যতগুলোই কাব্য রচনা করেছেন প্রায় সবগুলোতেই বিদেশি প্রভাব আছে। তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দও বাংলা ভাষায় পুরোপুরি নতুন ছন্দ। যদিও তা পয়ার, কিন্তু দেশীয় আধারে বিদেশীয় প্রবাহ। কবিতার নতুন দিগন্তে এটিও একটি চূড়ান্ত পদক্ষেপ।
সাম্প্রতিককালের কবিতায় কবিরা মডার্ন বা পোস্টমডার্ন ধারাকে অনুসরণ করেও ব্যক্তিভেদে তাতে নিজস্বতা আরোপ করে চলেছেন। কবিতা নিয়ে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে যে, অনেক সনাতন পাঠকই এই কবিতায় প্রবেশ করতে পারছেন না। কিন্তু প্রকৃত একজন অনুসন্ধানী তথা কৌতূহলী পাঠক এ বিষয়ে তাঁর ভাবনার দরজা নিঃসন্দেহে খুলে রেখেছেন। সংখ্যায় কম হলেও তাই প্রত্যেক কবিরই পাঠক আছেন। এমনও কিছু পাঠক আছেন যাঁরা কবিতার গভীরে প্রবেশ করতে চান। তাঁরা বোঝেন কবি ও কবিতার ক্রম পরিবর্তন অর্থাৎ বাঁকবদল।
কবিতা কোনও সূত্রে বা ফর্মে আবদ্ধ নয়। কবিতার ব্যাকরণ মেনেও কবিতা কেউ লেখেন না। কবিতার ছন্দ কবির মনেই তৈরি হয়ে যায়। এমনকী মাত্রা গণনা, পর্ব ও পর্বান্তর, অন্ত্যমিল-অনুপ্রাসও মন থেকেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসে। কষ্টকল্পিত ব্যাপার তা একেবারেই থাকে না। কবি শব্দচয়ন ও সঠিক প্রক্ষেপণ করে দেন মাত্র। কবিতাকে বহুমুখী বৈচিত্রের সমন্বয়ে যাঁরা বিনির্মাণ করে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মলয় রায়চৌধুরী। দীর্ঘদিন কবিতার পথে থেকে কবিতায় সর্বদা বাঁকবদল করে চলেছেন। তাই তাঁর কবিতা যখনই পাঠ করা যাক, তখনই নতুন বলে মনে হয়। তিনি কিউবিজম, ফবিজম, সুররিয়ালিজম এবং হাল আমলের পোস্টমডার্নিজম সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করেছিলেন। পরীক্ষিত বাস্তবতাকেই গ্রহণ করে আত্মসত্তার বিনির্মাণে তিনি কবিতায় শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তাই তাঁর বাস্তবতাকে উলঙ্গ মনে হলেও অশ্লীল মনে হয় না। কেননা পরিপূর্ণভাবে তাকে তুলে ধরতে চান। মানবজীবনের যে ক্রিয়াগুলি গোপনে বা আড়ালে সম্পন্ন হয়, সেসবকেও তিনি গোপন করতে চান না। তাঁর ‘নিজস্ব ঈশ্বর’ই তাঁকে চালিত করে। যা প্রচলিত মূল্যবোধ তার প্রতি সর্বদা থাকে একটি চ্যালেঞ্জ। সনাতন ঘরানার সব অবলম্বনই তিনি ভেঙে দেন। কবিতাই হয়ে ওঠে ব্যক্তিসত্তার জাগরণের চূড়ান্ত ধর্ম। উদাহরণ হিসেবে সাম্প্রতিকের লেখা একটি কবিতা:
“মাথা কেটে পাঠাচ্ছি যত্ন করে রেখো
মুখ দেখে ভালোবেসে বলেছিলে, “চলুন পালাই”
ভিতু বলে সাহস যোগাতে পারিনি সেই দিন, তাই
নিজের মাথা কেটে পাঠালুম, আজকে ভ্যালেনটাইনের দিন
ভালো করে গিফ্টপ্যাক করা আছে, “ভালোবাসি” লেখা কার্ডসহ
সব পাবে যা-যা চেয়েছিলে, ঘাম-লালা-অশ্রুজল, ফাটাফুটো ঠোঁট
তুমি ঝড় তুলেছিলে, বিদ্যুৎ খেলিয়েছিলে, জাহাজ ভাসিয়েছিলে
তার সব চিহ্ণ পাবে কাটা মাথাটায়, চুলে শ্যাম্পু করে পাঠিয়েছি
উলঙ্গ দেখার আতঙ্কে ভুগতে হবে না
গৌড়ীয় লবণাক্ত লিঙ্গ কোনো স্কোপ আর নেই
চোখ খোলা আছে, তোমাকে দেখার জন্য সব সময়, আইড্রপ দিও
গিফ্টপ্যাক আলতো করে খুলো, মুখ হাঁ-করাই আছে
আমার পছন্দের ননভেজ, সন্ধ্যায় সিঙ্গল মল্ট খাওয়াতে ভুলো না
মাথাকে কোলেতে রেখে কথা বোলো, গিটার বাজিয়ে গান গেও
ছ’মাস অন্তর ফেশিয়াল করিয়ে দিও, চন্দনের পাউডার মাখিও
ভোর বেলা উঠে আর ঘুমোতে যাবার আগে চুমু খেও ঠোঁটে
রাত হলে দু’চোখের পাতা বন্ধ করে দিও, জানো তো আলোতে ঘুমোতে পারি না
কানে কানে বোলো আজও উন্মাদের মতো ভালোবাসো
মাথা কেটে পাঠালুম, প্রাপ্তি জানিও, মোবাইল নং কার্ডে লেখা আছে।”
এই কবিতা পড়ার পর আমাদের নির্বাক হয়ে যেতে হয়। অতীতে এবং বর্তমানে আর কোনও প্রেমিক-কবি কি এরকম কবিতা লিখেছেন? একবারও কি আমাদের অশ্লীল বলে মনে হয় এই দুটি পংক্তি?
“উলঙ্গ দেখার আতঙ্কে ভুগতে হবে না
গৌড়ীয় লবণাক্ত লিঙ্গ কোনো স্কোপ আর নেই।”
কবিতায় কথ্যভাষার উচ্চারণে তিনি যে বাস্তবতা নির্মাণ করেন তা অনেক সময়ই নিষ্ঠুর বাস্তব। কিউবিজম এবং সুরিয়ালিজম এর প্রভাবে তা সংঘটিত হতে পারে। এই দুটি শিল্প আন্দোলনই ফ্রান্সে উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। মানুষ তার চর্মচক্ষুতে কোনও বস্তুর সম্পূর্ণ রূপকে দেখতে পায় না। যা দেখে তা খণ্ডিত। কিউবিজম ধারণায় বস্তুর সম্পূর্ণ রূপকে দেখার প্রচেষ্টা হল। অর্থাৎ বস্তুর ভেতর-বাহির উঠে এল সেই শিল্পে। অনেক সময় তার নির্মাণ কিম্ভূতকিমাকার হলেও মনন ধর্মীতায় তাকে উপলব্ধি করা সহজ হল। কবি শিল্পীরা এই বাস্তবতাকে দেখতে গিয়ে প্রতিস্থাপন করলেন আরেক বাস্তবতা। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে মানব মনের জটিল স্তরের রূপায়ণ ঘটল। চেনা জগতের সঙ্গে কখনো অচেনা জগতেরও দর্শন হল। কবিতার এই ‘মাথা কেটে পাঠানো’ আত্মসত্তার মেধাবী উত্তরণে এই কিউবিক চেতনাই একটি কার্যকরী পন্থা বলে বিবেচিত হল।
কিউবিজম এবং সুরিয়ালিজম দুই ধারার প্রভাবই সাম্প্রতিক এর কবিতায় খুব বেশি প্রশ্রয় পায় এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্যে যে কিউবিজম্ (Cubism) আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল, সেই পথকেই বর্তমানে অনুসরণ করছেন কবিগণ। কিউবিজম শিল্পীর সৃষ্ট জগৎ ও প্রকৃতিই প্রধান লক্ষ্য। শিল্পীই তাঁর বাস্তবতা ও রহস্যের গোলকধাঁধা সৃষ্টি করেন। পাল সেজান এই প্রসঙ্গে বলেছেন : “Art is a harmony parallel with nature.”(Paul Cezanne, Cezanne. Mont Sainte Victoire) অর্থাৎ শিল্পও প্রকৃতির সমান্তরালভাবে গড়ে উঠবে। সেইসঙ্গে সুরিয়ালিজমে অবচেতন মনের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটল। যুক্তির নিয়ন্ত্রণকে অনেকটাই শিথিল করে দিল। স্রষ্টাদের সামনে অপরিমেয় সম্ভাবনার জগৎ খুলে গেল। সুরিয়ালিজমে ‘অবচেতন মন এবং যুক্তিশীলতা’ বিমুক্ত চিন্তন প্রক্রিয়াকে রূপায়িত করতে চাওয়ার ফলে পরাবাস্তববাদী কবিতা বাক্যবন্ধে বিশৃংখল, প্রসঙ্গচ্যুতি, ক্রমহীনতা, স্বপ্নালু, তমসাচ্ছন্ন এবং অদ্ভুত প্রতীকের সহাবস্থানে এবং অসম্পৃক্ত ইমেজের সমন্বয়ে গড়ে উঠল। কখনো কখনো তা আধিভৌতিক ব্যাপারও হয়ে উঠল। অটোমেটিক রাইটিং হিসেবে কবিরা অবচেতন মনের প্রভাবকেও অস্বীকার করলেন না। প্রাজ্ঞ কবি নিখিলকুমার সরকারের ‘নানা রঙের হাইফেন’ কাব্যটিতে এই প্রভাব আছে। সেখানে তিনটি পংক্তি এমনই:
“আমি বাঘ
আমি মানুষ
আমি বাঘমানুষ”
বাঘ খণ্ড সত্তা, মানুষও খণ্ড সত্তা; আমরা মানুষ হিসেবে কবিকে চিনি, কিন্তু বাঘ হিসেবে চিনি না। কিউবিক চেতনায় এই বাঘকে দেখালেন। ‘বাঘমানুষ’ তখন পরাবাস্তবের রূপ পেল। এই কবির আরেকটি কবিতার অংশ এরকম:
“বয়ঃসন্ধির জ্যোৎস্নায় ভেসে যেতে যেতে
নিষিদ্ধ জানালায় চোখ পড়তেই দেখে ফেলেছিল
অলোকসামান্য দৃশ্যটি : চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে…”
বয়ঃসন্ধির জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া, নিষিদ্ধ জানালায় চোখ পড়া, চাঁদের গায়ে চাঁদ লাগা সুরিয়ালিজমেই সম্ভব। আর এই বাস্তবতা নির্মাণ কিউবিজমকেই কবি মেনে চলেন।
এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন কবির কবিতাংশ উদ্ধৃত করা হল:
১) শ্যামলকান্তি দাশ:
“চোখ ফুঁড়ে ফুঁড়ে যেদিন উঠবে গাছ
বুক খামচিয়ে যেদিন গজাবে পাতা
মাথা গুঁড়ো গুঁড়ো যেদিন উড়বে ছাই
দেখো তো আমার উদ্ভাস কতখানি!”
২) অমিতাভ মৈত্র:
“আর একবার যদি তিপ্পান্ন মিনিট পাই
আমি আদিগন্ত অন্ধকার এই মরুভূমির অনেক নিচে
ছোট্ট আর মিষ্টি জলের কুয়োয় বদলে দেব তোমাকে
গভীর স্তব্ধতার ভেতর আমার না-দেখা ছুঁয়ে তখন
তোমার স্পন্দন উঠে আসবে
জল-যক্ষের মতো”
৩) মুরারি সিংহ
“অলৌকিক ঝর্নাজলে ঘর বেঁধে আছি
সর্বাঙ্গ দিয়ে স্পর্শ করছি ঢেউ ও গ্যালপিং
এক টুকরো আয়নায় দেখছি রোদ ও ছায়ার খেলা
ঋতুফুলের বিস্ফোরণে দেখছি প্রজাপতিদের ওড়াউড়ি
ঝিঁঝিঁপোকাদের হাতে অহরহ
অনাবিল খুন হয়ে যায় দিনলিপি
নারীর রোদ্দুর পতাকা ধরে দাঁড়িয়ে আছে
জীবনের মাঝখানে
ঝিলমিল ঝলমল ঝমঝম”
৪) গোলাম রসুল:
“আমার গোড়ালিতে পৃথিবী
আমি তখন উড়ে চলা বালক
জাঙাল যেভাবে চুমো খায় নদীর বুকে
আর নিঃসঙ্গ সারস এসে বসে
জল নেমে গেল
ব্যথা উঠে যাচ্ছে সিঁড়ির মতো
দুপুরের ওপরে
দিগন্তের একটি নিশ্চুপ বাড়ি
চুনের চেয়েও সাদা
মহামারির কাল
গলিপথে লুকিয়ে থাকা মহাদেশ
প্রত্যক্ষ একটি স্বর্গ”
৫) অনুপম মুখোপাধ্যা:
“বাতাসকে যেখানে ডাকি বাতাস সেখানে রাখে না। খুব
আনইজি দাঁড়িয়ে থাকি আমি।
কোথায় ঠেস দেবো? বলো, কোথায়?
ওর আদর আমার আদর হয়ে উঠছে। তোমরা
কি ভাবছো ও আমাকে ফেলে দেবে চুষে?
একটা দেওয়াল খুঁজে দেবে? অবশ্য আমার
দরকার নেই খুব।
ফেটেই যাই শেষে… দুহাত”
৬) নিয়াজুল হক:
“প্যাঁচা কাঠ হয়ে গেল
প্যাঁচা পাথর হয়ে গেল
প্যাঁচা মাটি হয়ে গেল
প্যাঁচা
ইট, কাঠ, পাথর হয়ে গেলে
মহামানব হয়ে যায়
মহামানব তো রামকৃষ্ণ
রসগোল্লার রস নিংড়ে নিয়ে
একবার মুখে ফেলে দিয়ে দেখুন
কে রামকৃষ্ণ”
৭) বিজয় সিংহ:
“রাত্রির শহর রজনীর তিনতলা আলো
যা যৌনের দীর্ঘতম হাত ছড়িয়ে রেখেছে
হারামি চাঁদের হয়ে তুমিও কম্পনে শোও
কম্পনের রতিপাঠে তারাচিহ্নে বুক ঢেকে রাখ”
৮) সৈয়দ কওসর জামাল:
“কোনো উৎসবই আর সূচিত হবে না রূপের মূর্ছনায়
পাখির বিষাদঘন চোখ দিয়ে আমি চেয়েছি আকাশে
তাকে বলি, বরং তুমিই নেমে এসো মাথার ওপরে
ছুঁয়ে দেখি মেঘ, কতদিন আর এই আত্মঘাতী আর্তনাদ
বয়ে বেড়াবে হাওয়া, অসময়ে বৃষ্টিকে পারি না ফেরাতে
স্মৃতিহারানোর এই এক মুগ্ধবোধ সরল প্রকরণ
আত্মবিস্মরণের এই কাল খুব কি মৃত্যুর কাছাকাছি…”
৯) শঙ্খশুভ্র পাত্র:
“সমুদ্র হাওয়ায় আজও মিশে আছে অন্ধকার স্মৃতি…
ছন্দের বারান্দা জানে : পাশাপাশি, হেঁটে যাওয়া ঘোর
সহাস্য মঞ্জীর, বিভা, কে যে কার, ছুঁয়ে আছে দোর
জগৎ জানে না — শুধু মনে পড়ে পুরনো সে-চিঠি
নিঝুম সাঁকোর মতো চুপচাপ, স্তব্ধ বালিয়াড়ি
অমুদ্রিত কথাগুলি হু হু করে সমুদ্র ফেনায়
প্রতিটি চরণে ঢেউ— বেজে ওঠে নিজ মূর্ছনায়
লবনাক্ত প্রেম, ওই ফিরে যাওয়া ভাব, আর আড়ি”
প্রতিটি কবিতা অংশেই কবিগণ স্ব স্ব মহিমার পরিচয় দিয়েছেন। যে বাস্তবতা তাঁদের কবিতায় উঠে এসেছে, তা নিজস্ব সৃষ্টিরই অনবদ্য এক একটি ঘরানা। কিউবিজম বা সুরিয়ালিজম এর প্রয়োগ ঘটলেও তার ভিন্নতাও চোখে পড়ার মতো। যেকোনো শিল্প আন্দোলনই সূচনা পর্ব থেকে বিস্তার ও প্রয়োগ পর্বে এসে বাঁকবদল করতে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই শিল্প আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিল্পকে নিজস্ব চালেই আত্মনিষ্ঠ কথনের বুননে এক সংলাপধর্মী ব্যাকরণহীন পথে নিয়ে যেতে। কিউবিজমএর মূলকথা : “Maybe Cubism started this way. Memory re-arranging a face.”(Mary Rakow, The Memory Room।”
সম্ভবত কিউবিজম এভাবেই শুরু করেছে, স্মৃতিকে সম্মুখে পুনরায় স্থাপিত করার জন্য। উদ্ধৃত কবিতাংশগুলিতে স্মৃতির পুনরুত্থান ঘটেছে, তেমনি ভাবনাও মুক্তি পেয়েছে। ছন্দের ভেতর দিয়েও কবিরা তাঁদের ভাবকে এই মুক্তির সোপানে পৌঁছে দিয়েছেন। শঙ্খশুভ্র পাত্র সনেটের মধ্য দিয়ে তার প্রয়োগ ঘটিয়ে দেখিয়েছেন। সমুদ্র হাওয়ার প্রেক্ষাপটকে ব্যবহার করেছেন তাঁর স্মৃতির আশ্রয় হিসেবে। চিঠি সমুদ্র ফেনার মতোই ব্যাপ্তিময় হয়ে উঠেছে। ছন্দ থাকলেও চরণে চরণে ঢেউও আছে। ফেনা ঢেউ ঘোর প্রভৃতি শব্দগুলি পরাবাস্তবেরই আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। সৈয়দ কওসর জামাল আত্মবিস্মরণ থেকে ফিরতে চেয়েছেন। পাখির বিষাদঘন চোখ তাঁর চোখেও নেমে এসেছে। মেঘের আত্মঘাতী আর্তনাদকে নিজেরই আর্তনাদ মনে হয়েছে। বিজয় সিংহের রজনীর তিনতলা আলো যৌনের দীর্ঘতম হাত হয়ে হারামি চাঁদের কম্পন উপলব্ধি করিয়েছে। কম্পনের রতিপাঠে তারাচিহ্নে বুক ঢেকে থাকার দৃশ্য হয়ে উঠেছে। নিয়াজুল হক এর বোধে প্যাঁচার কাঠ মাটি পাথর হওয়ার পর মহামানব হয়ে যাওয়াও কিউবিজম এর চূড়ান্ত রূপ। অনুপম মুখোপাধ্যায় শূন্যতার ভেতর তার আত্মসত্তার অভিক্ষেপকে বাতাস ও দেওয়ালে স্থিত করতে চান। কিন্তু দুই হাতই দুর্মর হয়ে ওঠে। গোলাম রসুলকে উড়ে চলা বালক হিসেবেই গতিময়তাকে ধারণ করতে দেখি। নিঃসঙ্গ পরিবেশে ‘ব্যথা’ সিঁড়ির মতো প্রতিটি ধাপ রচনা করে। দিগন্তের নিশ্চুপ বাড়ি এবং গলিপথের স্বর্গ কবির যাত্রার অভিমুখ হয়ে ওঠে। মুরারই সিংহকেও অলৌকিক ঝরনার জলে ঘর বাঁধতে দেখা যায়। আয়নায় রোদ-ছায়ার খেলা থেকে ঋতুফুলের বিস্ফোরণে প্রজাপতির ওড়াওড়ি, ঝিঁঝিঁপোকাদের হাতে দিনলিপির খুন এবং নারীর রোদ্দুর পতাকা পরাবাস্তবেরই দৃশ্য হয়ে ওঠে। অমিতাভ মৈত্রের কবিতায় মরুভূমির নিচে গভীরে জল-যক্ষের ধারণা আমাদের সচকিত করে। শ্যামলকান্তি দাশ নিজের উদ্ভাসের ব্যাপ্তি উদ্ভিদ ও পত্র-পল্লবে বিন্যস্ত করেন। অবচেতন মনের স্বয়ংক্রিয়তা চেতন মন থেকেই বিচ্ছুরিত হয়েছে। মগ্ন চৈতন্যের ভাঙাগড়াকে চেতনায় ঠাঁই দিয়েছেন।
সাম্প্রতিকের কবিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়: প্রত্যেকেই একাধিক দৃষ্টিকোণ আরোপ করেছেন কবিরা তাঁদের সৃষ্টিক্ষেত্রে। কখনো কখনো বিষয়কে ভেঙে, জ্যামিতিক আকারের উপর জুড়ে দিয়ে ইচ্ছেমতো রূপ পাল্টে দিয়েছেন । অসংখ্য দৃশ্যপট, ক্রিয়া সংযোগ, অলংকারহীন আবেগহীন বিজ্ঞান ও গণিতের ভেতর ভাবনাকে চালিত করেছেন:
“Cubism is … a picture for its own sake.
Literary Cubism does the same thing in literature, using reality merely as a means and not as an end.”
-Max Jacob, The Cubist Poets in Paris: An Anthology
একথা ভুললে চলবে না, নিজের স্বার্থের কথা ভেবেই শিল্পীরা সাহিত্যেও কিউবিজমকে নিয়ে আসেন। একইভাবে বাস্তবতাটিকে কেবল একটি উপায় হিসাবে ব্যবহার করেন,শেষকথা হিসাবে নয়।#