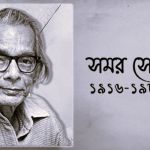ঐতিহাসিকদের মতে শিরোনামের চারটি পার্বণই সংশয়বিবহিতভাবে শস্য উৎসব-ভিত্তিক ধর্মধারার সঙ্গে সম্পর্কিত। উর্বরতা-কেন্দ্রিক ধর্মধারার ক্ষেত্রে নারী ও ধরিত্রী সমার্থবোধক বলে গণ্য হওয়ার ফলে, সুদূর অতীতে যেসব সংস্কার সৃষ্টি হয়েছিল, অম্বুবাচী সেগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখনীয়। নতুন বর্ষার মুখপাতে পৃথিবী যখন প্রথম সিক্ত হয়ে ওঠে, তখন পৃথিবীকে প্রথম ঋতুমতী নারীরূপে গণ্য করবার আদিম সংস্কারই অম্বুবাচী পার্বণের উৎস। ঋতুর ঠিক পরবর্তী দিনগুলি যেমন নারীর পক্ষে সন্তান-ধারণের জন্য প্রশস্ততম বলে মনে করা হয়, ঠিক তেমনভাবেই অতীতে অম্বুবাচীর পরবর্তী সময়টাকে ফসল ফলানোর জন্য সবথেকে শ্রেয়কাল বলে মনে করা হয়েছিল। উড়িষ্যা রাজ্যে এই পার্বণটিকে পরিষ্কারভাবে – ‘রজোৎসব’ – বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আসামের কামাখ্যা মন্দিরেও এই উপলক্ষ্যে দেবীর ঋতুকাল সমাগত বলে মনে করে প্রতিবছর উৎসব পালন করা হয়। সূর্যের দক্ষিণায়ণের দিন থেকে শুরু করে তিনদিন (আষাঢ় মাসের ৭ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে এর শুরু) পর্যন্ত এই পার্বণের পালনকাল। এই ক’টি দিন জমিতে লাঙ্গল দেওয়া বা বীজ বোনা ঠিক সেই কারণেই নিষিদ্ধ, যে কারণে ঋতুকালে নারীর পুরুষ-সংসর্গ নিষিদ্ধ। (ভাষাতাত্ত্বিকরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, পুরুষবাচক শব্দ ‘লিঙ্গ’ এবং কৃষিযন্ত্র ‘লাঙ্গল’ – একই উৎসজাত।) এই ‘সংযম’ পালন করবার সূত্র ধরেই পরে উপবাস এবং অরন্ধনের প্রথা আরোপিত হয়েছিল। বিধবার ক্ষেত্রে এই ‘সংযম’ পালনটা সেই সামাজিক-মানসিকতা থেকেই এসেছে, যেটার আরেক অভিব্যক্তি একাদশী পালনের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তবে অতীতে অম্বুবাচীর মূল উপলক্ষ্যের সঙ্গে এসবের বিন্দুমাত্র কোনো সম্পর্ক ছিল না। বরং আসাম ও উড়িষ্যায় (সেখানে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি থেকে তিনদিন এই পার্বণ পালিত হয়) এই ক’দিন উৎসবের আবহাওয়াই থাকে।
প্রাচীনকাল থেকে নতুন ফসল ওঠবার সময়ে যে কতগুলি কৃষিকেন্দ্রিক উৎসব প্রচলিত ছিল, সেগুলির মধ্যে, অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চলে ইতুব্রত এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। ইতু হল ‘ঋতু’-র স্খলিত উচ্চারণজাত রূপ। যদিও কেউ কেউ ইতুপুজোকে সূর্য-উপাসনা বলে থাকেন, তবুও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের ছাত্র মাত্রেই এই পার্বণের রীতি ও উপচারগুলিকে বিশ্লেষণ করে ইতুকে মাতৃকাদেবী রূপেই গণ্য করেন বলে দেখা যায়। ঘটের গায়ে পুতলি আঁকা এবং ভিতরে শস্যদানা ও তৃণগুচ্ছ রাখা – একই সঙ্গে মাতৃপ্রতীক আর প্রতীকী শস্যক্ষেত্রের (জেমস ফ্রেজার সারা পৃথিবীর শস্য-উৎসবেই এই একই ধরনের রীতি এবং উপচার দেখে এটিকে ‘গার্ডেন অব অ্যাডোনিস’ নাম দিয়েছিলেন) স্বরূপ। কার্তিক সংক্রান্তি থেকে শুরু করে অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তি পর্যন্ত – ফসলী ঋতুর ভরাভরন্ত সময়কাল অবধি প্রতি রবিবার যেহেতু ঐ ঘটপুজা করা হয়, সেহেতু রবি তথা সূর্যই ইতু – এমন একটা ধারণা হয়েছে। ফার্টিলিটি কাল্টের সঙ্গে সূর্যের একটা যোগসূত্র রয়েছেই। কিন্তু সেটা বলে ইতুই যে সূর্য, এমন কিন্তু নয়। সূর্য ওরফে বৈদিক ‘মিত্র’ দেবতা উচ্চারণের অপভ্রংশে ‘ইতু’ হয়ে গিয়েছেন, এমন ভাবনাও নেহাৎই দূরান্বয়ী। অগ্রহায়ণ মাসের শেষে ফসল ঘরে উঠে গেলে ইতুর ঘট ভাসিয়ে দেওয়ার রীতি, এই পার্বণটির মাতৃকারূপকেই বেশি করে সূচিত করে।
ইতুপুজো এবং নবান্ন উৎসব একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়, এমনকি এগুলির চরিত্রও যে মূলতঃ একই – সেটা ‘নবান্ন’ নামটি থেকেই প্রকাশ পায়। এই উপলক্ষ্যে নতুন আমন ধান ওঠবার পরে সেটার থেকে পাওয়া চাল নিজেরা খাওয়ার আগে পিতৃপুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে রন্ধনশেষে নিবেদন করবার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এদিক থেকে দেখলে এটি মহালয়ায়ই সমধর্মী একটি পার্বণ। মনে করা হয় যে, পিতৃপুরুষ কাকের রূপ ধরে এসে ‘নবান্’-এর অংশ গ্রহণ করে যান; এই কাক রূপধারী পূর্বপুরুষের কল্পনা নিঃসন্দেহে এক ধরনের টোটেম ভাবনা। এই উৎসবে শাঁখ বাজিয়ে পূর্বপুরুষের আত্মাকে আহ্বান করবার প্রথা চালু রয়েছে। নতুন ধান, নতুন গুড় এবং দুধ – নবান্নে নিবেদিত খাদ্যের প্রধান উপকরণ। নবান্ন উৎসব পালনের ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ বা তিথি নেই; ক্ষেতের ফসল গোলাজাত করবার সময়ে যেকোনো দিনই এই উৎসব পালন করা যেতে পারে, যদিও পাঁজির বিধান অনুসারে কোন শুভদিন দেখেই মেয়েরা নবান্ন মাখেন। এইসময়ে তৈরি করা খাদ্যটিকে সাধারণভাবে মেয়েরা খুবই পবিত্র বলে মনে করে থাকেন, এবং এটির মধ্যে তাঁরা খানিকটা দৈবীগুণও কল্পনা করে থাকেন। সেই কারণে স্নান সেরে শুচিস্নিগ্ধ অবস্থায় নবান্ন স্পর্শ করবার লৌকিক বিধান রয়েছে। বিশেষ বিশেষ শারীরিক অবস্থায়, ঐ দৈবীপবিত্রতা আরোপ করবার কারণে নবান্ন স্পর্শ করবার ট্যাবুও (নিষেধাত্মক ধর্মীয় সংস্কার) প্রচলিত রয়েছে। তবে অন্য কেউ হাতে তুলে দিলে সেটাকে নিজের জন্য গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই। স্পষ্টতঃই নবান্নকে খাদ্য-দেবতারূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। পূর্বপুরুষের আত্মা কাকরূপে নবান্ন গ্রহণ করে গেলে বাকি খাদ্যটা তাঁদের প্রসাদরূপেই গণ্য হয়। পিতৃপুরুষের আত্মা সেখানে দেবকল্প। এখানে যে ব্যাপারটা আকর্ষণীয় সেটা হল – নবান্ন একই সঙ্গে দেবতার প্রসাদ এবং দেবতা-কল্প। এই ধরনের সংস্কারের বিমিশ্রণ কিন্তু নিতান্তই দুর্লভ।
নবান্নে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের অংশটুকু ছাড়া অনুষ্ঠানের বাকিটুকুর সবই প্রায় মেয়েদের করণীয়। এই শ্রাদ্ধও সচরাচর পুরোহিত ছাড়াই করা হয়ে থাকে; মহালয়ার তর্পণের সঙ্গে এদিক থেকেও নবান্নের ভাবসাযুজ্য রয়েছে। সারা বছর ধরে শস্যকে কেন্দ্র করে যত রকমের উপলক্ষ্য বাঙালী হিন্দুর সংসারে আবির্ভূত হয়, সেগুলোর মধ্যে নবান্নের একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে – যেটার অনুষঙ্গ ধরে এর কিছু পরেই আরেকটি পার্বণ উপস্থিত হয়, সেটা হল – পৌষপার্বণ।
ক্ষেত থেকে নতুন শস্য ঘরে উঠবার পরে আনন্দোৎসব করবার রেওয়াজ বিশ্বজনীন এবং সেটার বয়সও প্রায় কয়েক হাজার বছর। কৃষির উদ্ভবের পর থেকেই এই শস্য-উৎসবের ধারা পৃথিবীর সমস্ত দেশে এবং সমাজে প্রচলিত হয়েছে। বাঙালীর পৌষ-সংক্রান্তি উৎসব সেই বিশ্বজনীন ঐতিহ্যেরই ধারাবাহী। এই একই তিথিতে দক্ষিণভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সেখানকার অন্নোৎসব – ‘পোঙ্গল’ – পালিত হয়। এই দিনই আসামের মাঘ-বিহু উৎসবেরও মুখবন্ধ ঘটে। গুজরাটে একই দিনে শস্যোৎসব পালনের অনুষঙ্গ হিসেবে সূর্য পূজার দ্যোতকস্বরূপ ঘুড়ি উড়িয়ে আনন্দ করবার রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এই বিশেষ দিনটিতেই কেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে – মূলতঃ যে যে জায়গার প্রধান খাদ্যই হল ভাত – আনন্দ উৎসবের প্রথার প্রচলন হয়েছে?
খুব সম্ভবতঃ গুজরাটি রীতির মধ্যেই উৎসবটির ঐতিহাসিক সূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বর্তমান সময়ে সূর্যের উত্তরায়ণ মাঘের শেষ সপ্তাহে ঘটলেও হাজার দু’য়েক বছর আগে সেই তারিখটি কিন্তু পৌষের শেষেই ছিল। সেই প্রাচীন আমল থেকেই কালচক্রের পরিবর্তনের পটভূমিতে এই উৎসব সম্ভবতঃ সেইসব অঞ্চলে পালিত হতে শুরু হয়েছিল, যেখানে আমন ধান ফলে এবং ততদিনে গোলায় উঠে যায়। সূর্যের ঐ কক্ষ-পরিবর্তনের উপলক্ষ্যে তার উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদনের প্রতীক ছিল ঘুড়ি ওড়ানো; প্রাচীন বিশ্বাস-অনুযায়ী যা মানুষের ভক্তির অর্ঘ্যকে সূর্যের কাছে পৌঁছে দেয়। সূর্যের সঙ্গে শস্যের সম্পর্কের কথা সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ভেবে এসেছে। এই উত্তরায়ণ ওরফে মকরসংক্রান্তির উপলক্ষ্যেই গঙ্গাসাগরের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানকার কপিলমুনির পৌরাণিক গল্পের ভিত্তি যেটাই হোক না কেন – মকরবাহিনী গঙ্গাকে শিবের জটা থেকে মুক্ত করে ঐ তিথিতে ভগীরথ পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন – প্রাচীন হিন্দুরা এমন কল্পনা করেই পুরাণ-বৃত্তান্ত তৈরি করেছিলেন। ‘মকর’ নামটির ভাবানুষঙ্গেই যে এই ভাবনার উদ্ভব হয়েছে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই তারিখে পূর্ববঙ্গে বাস্তপূজার যে প্রথা প্রচলিত রয়েছে, সেখানে (মকরের বিকল্প হিসেবে) মাটির কুমিব বলি দেওয়ার রীতিও সম্ভবতঃ এই আদিম ভাবনার সূত্রবাহী।
তবে শুধু কুমিরই বা কেন? বরিশাল অঞ্চলে এই পৌষপার্বণের দিন গৃহদেবতা তথা বাস্তুদেবের পূজা উপলক্ষ্যে ব্যাঘ্রবাহিনী কুলাই দেবীর আরাধনার সময়ে দুটি করে মাটির কুমিরের সঙ্গে একটি বাঘের মূর্তিও দেখতে পাওয়া যায়। অতীতের কোন একসময়ে ছেলেরা সেখানে দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাঘের এবং ধান তোলার বিষয়ে বিভিন্ন ছড়া কেটে খাবার জোগাড় করতেন। পশ্চিম বাংলাতেও কিছু-কিছু এলাকায় একইভাবে পোষলা উৎসবের শেষদিনে কুলুই ঠাকুরের পুজোয় ঐ একই রকমের বাঘ ও ধান-সম্পৃক্ত ছড়া আওড়ানোর প্রথা চালু রয়েছে। ময়মনসিংহ জেলায় এই ছড়ার আঞ্চলিক নাম হল – ‘বাঘাইয়ের বয়াৎ’। নদীয়া জেলাতে অনুরূপ ছড়া ও গানকে – ‘হোলবোল’ কিংবা ‘হলুই গান’ – বলা হয়ে থাকে। এই ধরনের প্রথা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলেও প্রচলিত রয়েছে। রংপুরের ব্যাঘ্রবাহন জোড়া দেবতা ‘সোনা-উপো’ বা সোনা রায়-রূপা রায়েরও এই পৌষালী সংক্রান্তিতে পুজো উপলক্ষ্যে বাঘের তুষ্টিবাচক কথাবার্তা বলে ছড়া কাটা হয়ে থাকে। কিন্তু শস্য উৎসবের সঙ্গে পশুর এবং পশুর দেবতার এই যোগাযোগটা সারা বাংলা জুড়ে কেন যে হয়েছে, সেটা ইতিহাসের দিক থেকে একটা আকর্ষণীয় প্রশ্ন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফসল কাটবার সময়ে সেখানকার কৃষকদের আদিম সংস্কার অনুযায়ী শস্যগুচ্ছকে নানাধরনের পশুরূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে। সেই প্রথা না হয় কোন আদিমতর সংস্কারকে (অতীতে প্রথমে পশুই মানুষের খাদ্য ছিল, এখন ফসল খাদ্য – সুতরাং পশু ও ফসল সমার্থক) অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছে; কিন্তু বাংলায়? বাঘ বা কুমির তো কোনকালেই মানুষের খাদ্য ছিল না, পৃথিবীর সর্বত্রই সেগুলি খাদক হিসেবে পরিচিত। তাহলে? এই হেঁয়ালির উত্তর একটি বাংলা প্রবাদে পাওয়া যায় – ‘মাঘের শীতে বাধে পালায়’। আসলে ফসলী ঋতু মানুষকে অন্ন দিলেও, নিরাপত্তা দিতে পারেনি। সুতরাং, সাপ বাদে অতীতের গ্রাম-বাংলার মানুষের অন্য যে দুটি প্রধান শত্রু ছিল – বাঘ ও কুমির – সেগুলির এবং সেগুলির অধিষ্ঠাতা দেবতাদের তুষ্টি সাধন করবার জন্যই এইসব প্রথার অভ্যুদয় হয়েছিল। অতীতের কোন একসময়ে দল বেঁধে হইচই করে বনভোজন এবং ছড়া-গানের মাধ্যমে বাঘ তাড়ানোটাও হয়ত একটা উদ্দেশ্য ছিল। মাঘের প্রাক্কালে বাঘ পালিয়ে যাবে – এটাই হয়ত সেকালের মানুষের কামনা ছিল। দল বেঁধে ফসল কাটবার পটভূমিতে বাঘ গহীন বনে চলে যাচ্ছে – এমন ছবি মহেঞ্জোদড়োর সীলমোহরের গায়েও খোদাই অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। অতীতের সেই ঐতিহ্যের অনুসরণই ওই আদি-অস্ট্রিক-দ্রাবিড়দের (যাঁরা ধানের সঞ্জাত খাদ্য খেতেন) বংশাবতংস বাঙালীদের মধ্যে আজও প্রবহমান রয়েছে। বাস্তুপুজো উপলক্ষ্যে মাটির কুমির বলি দেওয়াটা, অর্থাৎ হিংস্র পশুকে বধ করে নিরাপদে থাকবার জন্য দেবতার কাছে আশ্রয় নেওয়া – মানুষের আদিমতর ভাবনার ধারাবাহী।
এটা গেল পৌষ সংক্রান্তির বিচিত্র ধরণের উৎসবের একটি দিকের কথা। এই উৎসবের অন্য দিকটির বৈচিত্র্যও কিন্তু কম নয়। পিঠে-পুলি-পায়েস ইত্যাদি অধুনা দুর্লভ খাবারগুলি তৈরি এবং বিতরণ করাও এই পৌষালী উৎসবেরই একটা অঙ্গ। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় মকর সংক্রান্তির আগেরদিন ক্ষেত থেকে আমনধানের কেটে নিয়ে আসা গুছিগুলিকে মেয়েরা পূজো করেন, যেটার নাম হল – আওনি-বাঁওনি (আমনী-বাঁধনি)। গ্রাম বাংলায় প্রচলিত এই ধরণের আরেকটি উৎসব হল পৌষ-আগলানো। তাতে সর্বত্র আলপনা এঁকে গোবরের নাড়ু আর চালের গুঁড়ো পুজো করে সারারাত ধরে সেগুলোকে বিনিদ্রভাবে পাহারা দেওয়ার প্রথাও বিচিত্র প্রাচীন সংস্কারজাত। দুপুরবেলা কুনকের মধ্যে ধান ও ধানের ছড়া ভরে পূজো করে ধান্যলক্ষ্মীর বন্দনা করাটা পূর্ববঙ্গের একটা বিরাট অংশ জুড়ে প্রচলিত রয়েছে। এই একইদিনে তুষ-তুষলি ব্রত উদযাপনও করা হয়ে থাকে। শস্য উৎসব এবং সূর্যবন্দনা – এটির মধ্যে একত্রিত রয়েছে। রাঢ় বাংলার সুবিস্তীর্ণ এলাকায় প্রচলিত টুসু বা তুষু দেবীর পূজাও এই তিথিতেই সাঙ্গ হয়। যদিও টুসুকে পুরোপুরি শস্যদেবী বলা যাবে কিনা – সেটা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে শস্যসম্ভারকে উপলক্ষ করেই যে টুসু পরব, এবং পৌষ সংক্রান্তিতেই যে সেটার সমাপ্তি ঘটে, এ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা মোটেও অসঙ্গত নয় যে, গোটা বঙ্গভূমি জুড়েই এই দিন যে শস্যকেন্দ্রিত উৎসব নানাভাবে পালিত হয়, এটাও সেটারই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। টুসুর সরা, আওনি-বাঁওনির এবং ধান্য লক্ষ্মীর কুনক, পৌষ-আগলানোর চালগুঁড়ো-গোবরের নাড়ু – এগুলো সবই সমান দ্যোতনা বহন করে। ফসল ক্ষেতের এই প্রতীকগুলি সংস্কৃতিবিজ্ঞানে গ্রীক শস্য-দেবতা ‘অ্যাডোনিসের বাগান’ বলেই পরিচিত।#