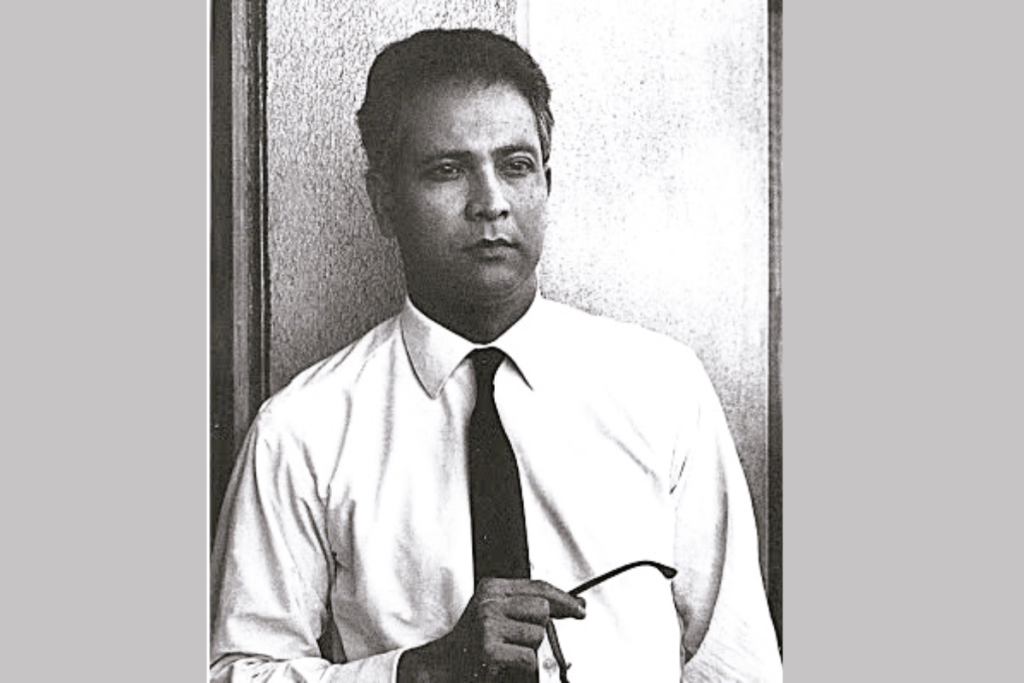অনেক সমালোচকই চাঁদের অমাবস্যা উপন্যাসটিকে অস্তিত্ববাদী উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। হ্যাঁ, অস্তিত্ববাদের পক্ষে যায় এমন অনেক যুক্তি খাড়া করা চলে উপন্যাসটিকে ঘিরে। এটি ফ্রান্সে বসে লেখা। এটি রচনার বছর দুয়েক আগে সার্ত্র-এর অস্তিত্ববাদী উপন্যাস লা নজে (মূল ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৯৩৮-এ) ইংরেজিতে বেরিয়ে গেছে। তাছাড়া তাঁর অস্তিত্ববাদী দার্শনিক গ্রন্থ বিইং এ্যান্ড নাথিংনেস (মূল ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৯৪৩-এ) ইংরেজি অনুবাদে বেরোয় ১৯৫৬ সালে। দু’টো গ্রন্থই যদি ওয়ালীউল্লাহ্’র পড়া হয়ে থাকে তবু বলতে হবে চাঁদের অমাবস্যা আসলে যুবক শিক্ষককেন্দ্রিক উপন্যাস হলেও এতে রয়েছে তারও অধিক বাস্তবতার প্রতিফলন। উপন্যাসটি এক অর্থে রচয়িতার প্রথম উপন্যাসের সম্প্রসারণ। যে-গ্রামে ষাট বছর আগে মজিদের দেখা মিলেছিল সেরকম এক গ্রামেই দেখা মেলে হত্যাকারী কাদেরের। এই ষাট বছরে পরিবর্তন যে হয় নি তা নয়। মহব্বতনগরে যুবক আক্কাস স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। এ-গ্রামে মক্তবের পাশাপাশি রয়েছে স্কুলও। মজিদের ক্ষমতার বাহন ধর্ম এবং তার প্রকাশ মাজার। চাঁদের অমাবস্যা’য় দাদাসাহেব এবং কাদেরেরও ক্ষমতার বাহন ধর্ম এবং সে-ক্ষমতার প্রতীক বড়বাড়ি। অর্থাৎ কালের ব্যবধানে মাজার হয়ে গেছে বড়বাড়ি নামক প্রতিষ্ঠান। ধর্মপ্রবল মজিদকে দেখা গেছে পীড়ক-নির্যাতকের ভূমিকায়। এখানে কাদের সাবলীল হত্যাকারী। দাদাসাহেব চরিত্রটির ধর্মপ্রাবল্যের পরিচয় ইতঃপূর্বে ম্যালকম এক্স প্রসঙ্গে লক্ষ করা গেছে। কিন্ত তার তৎপরতা ব্যাপকতর। ঔপন্যাসিক তারও বিবরণ দিয়েছেন। নিজের পরিবারের চৌহদ্দিতে দাদাসাহেবের নির্দেশ ধর্মীয় রীতিনীতির মত অবশ্যপালনীয়- যেমন, খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের আগে আবশ্যিকভাবে সৃষ্টিকর্তার নামোচ্চারণ, পরিবারের সকল সদস্যের নামাজ-পড়া বাধ্যতামূলক- “তারপর ঈমানের অর্থ, কোরান-পাঠ ও হাদিস-সুন্নার প্রয়োজনীয়তা, তস্বি-পড়ার উপকারিতা, নফল নামাজের কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন।” ‘ঝানু মোল্লামৌলবীদের’ চাইতেও তাঁর ধর্মীয় সাফল্য অধিক। মোটকথা দাদাসাহেবের মধ্যে আমরা ঝিকিয়ে উঠতে দেখি আমাদের লালসালু’র অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত মজিদকে। দাদাসাহেব তাঁর অন্তঃপুরে ছোটখাট একটি ধর্মসম্মত ব্যবস্থার কায়েমকারী। এটিরই বৃহত্তর ছায়াপাত আমরা লক্ষ করবো পূর্ববঙ্গের সমকালীন ইতিহাসে। ১৯৪৮ সালে জিন্নাহ সাহেবের উর্দু ভাষা চাপানোর প্রচেষ্টা, ১৯৪৯-এ ভাষা-সংস্কার তৎপরতার উদ্যোগ, ১৯৫২-ও ভাষা আন্দোলন প্রভৃতি পর্বে পূর্ববাংলার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাচারিতার ঘটনাপ্রবাহকে সমান্তরালে দেখলে দাদাসাহেবের জবরদস্তির ঔপন্যাসিক চিত্রের প্রতীকী বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যাবে। সেই বাস্তবতা আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারি হলে এবং চাঁদের অমাবস্যা প্রকাশকালে পাকিস্তানে সামরিক শাসনাধ্যায় তুঙ্গস্পর্শী। সেই তুঙ্গতা ওয়ালীউল্লাহ্’র তৃতীয় উপন্যাসে আরও সর্পিল-অষ্টাবক্র। এই দ্বিতীয় উপন্যাসজুড়ে পূর্বাপর বিরাজমান এক থমথমে পরিবেশ। একটি হত্যাকাণ্ড, হত্যাকাণ্ডের অপরাধীর মুক্ত-স্বাধীন চলাফেরা, শাস্তি না-হওয়ার অপরাধবোধ, নিরাপত্তাহীনতা, অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা এইসব সমকালীন জীবনপ্রণালীরই সমান্তরাল নির্মাণ।
আরও পড়ুন: ইতিহাসের বাস্তব এবং লেখকের বাস্তব: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ৩
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’র চাঁদের অমাবস্যা উপন্যাসের নায়ককে সার্ত্র-এর লা নজে উপন্যাসের নায়কের আদলে বিবেচনা করার পক্ষে ততটা যুক্তি থাকে না। বরং পরবর্তী কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে সার্ত্র্-এর লা নজে’র নায়ক আঁতোয়াঁ রক্যতাঁ’র সাদৃশ্য সত্ত্বেও অন্তিমে আরেফ আলী, মুহাম্মদ মুস্তফা দু’জনের কাউকেই সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদী ঘরানার নায়ক বলা যাবে না। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’র বিশ্বসাহিত্যের পাঠ-পঠন তাঁর মানসগঠনে অনেকখানি ভূমিকা রাখলেও কোনো বিশেষ আঙ্গিক বা দর্শনে তাঁর নির্ভরশীলতা লক্ষণীয় নয়। লা নজে-তে নায়ক আঁতোয়াঁ রক্যতাঁ’র মার্কুইস দ্য রোয়েবোঁ-র জীবনেতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্যে তার বুভিয়ে-বসবাস, পরবর্তীতে ইতিহাসের পরিবর্তে তার উপন্যাস-রচনার পরিকল্পনা, তার ব্যক্তিগত জীবনের অবসাদ-বিষাদ, পরিপার্শ্বের সঙ্গে তার বিচ্ছিন্নতার বোধ প্রভৃতি যে-নাগরিক পটভূমিতে একের পর এক ঘটে যেতে থাকে তার সঙ্গে চাঁদের অমাবস্যা-র বিষয় বা পরিণতির সাদৃশ্য অনুপস্থিত। আঁতোয়াঁ’র বিবমিষাবোধের সঙ্গে কাজেই আরেফ আলীর (চাঁদের অমাবস্যা) কিংবা মুহাম্মদ মুস্তফা’র (কাঁদো নদী কাঁদো) অস্বস্তি-অস্থিরতার প্রতিতুলনা চলে না। চাঁদের অমাবস্যা উপন্যাসের নায়ক আরেফ আলীকে ঔপন্যাসিক হয়তো নামের পরিবর্তে বিশেষণ বা সর্বনামেই (যুবক শিক্ষক) অধিক পছন্দ করেন । যেটা সার্ত্র-এর লা নজে উপন্যাসের চরিত্র ওগিয়ের পি-র ‘স্বশিক্ষিত’ পরিচিতির সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু এটুকু সাদৃশ্যকে আত্যন্তিক পর্যায়ে টেনে নেওয়া মুশকিল। চাঁদের অমাবস্যা উপন্যাসে একদিকে প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যুবক শিক্ষকের সত্য প্রকাশের চেষ্টা এবং অন্যদিকে ক্ষমতাদর্পী ব্যক্তি, অবদমিত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের চরমতা। এই দু’টি ধারাই উপন্যাসটির অভিমুখ। আমরা দেখেছি ষাট বছরের ব্যবধানেও একটি জনপদের জীবনসংস্কৃতি প্রায় অপরিবর্তনীয় রয়ে যায়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’র প্রতিটি উপন্যাসে কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব সূক্ষ্ম ও খুঁটিনাটিভাবে চিত্রিত কিন্তু ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে তিনি ধরবার চেষ্টা করেছেন সমগ্র ব্যবস্থাটাকে, সমগ্র পরিস্থিতিকে। আর, সেটি তিনি করেছেন সুপরিকল্পনার সঙ্গে, অবিমিশ্র ধারাবাহিকতার সঙ্গে। ইতিহাস ও কালচেতনাকে বিকৃতির হাত থেকে সযত্নে রক্ষা করে একটি দেশ ও একটি জাতির সামগ্রিক জীবনচেতনার মধ্যে থাকা অসঙ্গতি, অসম্পূর্ণতা, বিকাশহীনতার লক্ষণগুলো সৃজনশীল এষণায় বিশ্লেষিত হয় তাঁর সাহিত্যে। যুবক শিক্ষকের চোখ দিয়ে ঔপন্যাসিকই দেখেছেন তাঁর সমকালকে যে-সমকাল বস্তুত লালসালু বাহিত হয়ে আসা। লালসালু উপন্যাসে গ্রামটির পরিচালন বা নিয়ন্ত্রণের অধিকর্তা ছিল গ্রামসমাজ। গ্রামসমাজের নিয়ন্ত্রণকে আবার অলিখিতভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে পরিণত করেছে মজিদ। ষাট বছর পরে চাঁদের অমাবস্যা’য় পরিচালন-নিয়ন্ত্রণের কর্তা যুগপৎ গ্রামসমাজ এবং রাষ্ট্র। গ্রামসমাজটির কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতীক বড়বাড়ি। বড়বাড়ির ক্ষমতার প্রতিনিধিত্বকারী দাদাসাহেব এবং কাদের। রাষ্ট্র বলে একটা জিনিসের অস্তিত্ব থাকলেও সেটা যে ঠিক কার জন্যে তা কারও জানা নেই। তবে সেটা যে একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয় তা যুবক শিক্ষকের চাইতে ভাল আর কেউ জানে না। চাঁদের অমাবস্যা’র রাষ্ট্র আসলে মজিদ এবং তার উত্তরপুরুষ দাদাসাহেব এবং কাদেরের কল্যাণে নিয়োজিত। আর, ১৯৫০ সালের ভূমি আইনে যাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয় রাষ্ট্র তাদেরও স্বার্থসংরক্ষণকারী। তারা খালেক ব্যাপারীদের (লালসালু) উত্তরসুরী। যদিও যুবক শিক্ষক হত্যাকারী কাদেরের স্বরূপ উন্মোচন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, একই সঙ্গে এটাও তার জানা ছিল কাদেরকে রক্ষা করবে রাষ্ট্রই। কেননা, সে তার একমাত্র সম্বল টিনের স্যুটকেসটি আগেই সঙ্গে নেয়। সমাজও তার পক্ষে, রাষ্ট্রব্যবস্থাও তার পক্ষে। আরেফ আলীর পক্ষে গ্রাম ত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প থাকে না। ষাট বছর আগে শিক্ষিত যুবক আক্কাসের শিক্ষা জ্ঞান এসবের কোনো মূল্য ছিল না সমাজের নিকটে। ষাট বছর পরে এসে যুবক শিক্ষকের শিক্ষার কোনো মূল্য নেই সমাজ ও রাষ্ট্রের নিকটে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’র দু’টি উপন্যাসই পরিণতি পায় হতাশার নিমজ্জনে। লালসালু’তে চরম নেতির মধ্যে মাজারের গায়ে জমিলার পদস্পর্শের প্রতীকটি অনেকটা ঔপন্যাসিকের দূরতম আশাবাদের প্রকাশ। চাঁদের অমাবস্যা’য় শ্রেণিস্বার্থসংরক্ষণকারী রাষ্ট্রের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ এবং সর্বময় হতাশার মধ্যে ব্যক্তি আরেফ আলীর আত্মদায়মুক্তির বিষয়টাই গুরুত্বপূর্ণ। এখনও পর্যন্ত সমাজ এবং রাষ্ট্রের কোথাও উল্লেখ করবার মত জোরালো কোনো আশার দেখা পান নি ঔপন্যাসিক।
আরও পড়ুন: দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের কবি সুকান্ত
ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’র জীবনদর্শনকে হতাশা ও দুঃখবাদ বলে অভিহিত করবার জন্যে তাঁর তৃতীয় উপন্যাস কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮) পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা না করলেও চলতো। তৃতীয় উপন্যাস পাঠান্তে দেখবো, তাঁর ঔপন্যাসিক জীবন এবং নয়া ঔপনিবেশিক পূর্ববাংলার জীবন প্রায় সমবয়সী। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা যে নতুন আশা বা স্বপ্ন জাগায় তা যে আসলে দুঃস্বপ্নের নামান্তর সেটা অন্তত ১৯৬৪ সাল (চাঁদের অমাবস্যা’র প্রকাশকাল) পর্যন্ত অসত্য নয়। ১৯৬৮-তে এসে আমরা এই বিশ্বাসে বদ্ধমূল হই, ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাস্তবজীবনে কতটা আশাবাদী ছিলেন সে-বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, তিনটি উপন্যাসের সামগ্রিকতায় তাঁর জীবনচেতনায় আশাবাদ প্রচণ্ডভাবে অনুপস্থিত। যে-আশা ১৯৪৮ সালে ঝলকমাত্র আভাময় হয় (লালসালু উপন্যাসে) সেটির পুরোপুরি মৃত্যু ঘটে আরেফ আলীর অবরুদ্ধ জনপদ ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনায়। যে-গ্রাম আরেফ আলী ছেড়ে যায় সেটির হয়তো একটা অন্য নাম থাকতে পারে, কিন্তু সে-গ্রামকে ডাকা যেতে পারে মহব্বতনগর নামেই। কিন্তু কথা হলো, হত্যাকাণ্ডের ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন অপরাধবোধের ক্লিন্ন বৃত্ত সেই গ্রাম ছেড়ে কোথায় গেল আরেফ আলী। যে-গ্রামই সে যাক সেখানেই রয়েছে একটি করে বড়বাড়ি এবং একজন করে দাদাসাহেব বা কাদের। ধরা যাক, কোনো গ্রামেই গেল না আরেফ, গেল সে এক ছোট্ট মফস্বল শহরে যে-শহরের নাম কুমুরডাঙ্গা। সেখানেই এসে একদিন ছোট হাকিমের পদে যোগদান করে গ্রাম থেকে আসা এক যুবক মুহাম্মদ মুস্তফা। একদিন সেই যুবক মুস্তফা আত্মহত্যা করে চিরবিদায় নেয় পৃথিবী থেকে। আর, তার এই আত্মহত্যার সঙ্গে সঙ্গে চিরমৃত্যু ঘটে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’র আশাবাদেরও।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আশাবাদী লেখক ছিলেন না কিন্তু তিনি ভবিষ্যতের পাঠকের জন্যে রেখে যান এমন সাহিত্যিক নির্মাণ যেটির অভিজ্ঞতালব্ধ পাঠক ভাববেন, যখন চারপাশ ক্রমাগত বিবিধ আঁধারাচ্ছন্নতায় ছেয়ে যেতে থাকে তখন মিথ্যে আশার স্তোক দিয়ে একজন ঔপন্যাসিক সেই বাস্তবতাকে আড়াল করতে পারেন না। ‘উইজার্ড অব ওজ’ নয়, তাঁকে হতে হয় ‘উইজার্ড অব রিয়েলিটি’। তাই দেখবো, নির্যাতন-নিপীড়নের বাস্তবতা পেরিয়ে হত্যা-অপমৃত্যু হয়ে আত্মহত্যার বিনাশী পরিণতিতে পৌঁছাবার পরে যে-গল্পের শুরু সেই শুরুর বিন্দুতে সব মৃত ও অতীত হয়ে গেছে। জীবনের গল্প শোনানো হয় মৃত্যু ও হতাশার কিনারায় বসে। কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাসের আরম্ভের জীবনপ্রবাহ বস্তুত মৃত্যুনদীর ঢেউ- আমাদের জানা হয়, সকল স্তব্ধতারই সূচনা আসলে স্পন্দনের মধ্য দিয়ে। বহুস্তরা জীবনের স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার কাহিনি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’র কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাস। অনেক সমালোচক এটিকে ‘স্ট্রিম অব কনশাসনেস’ বা ‘চেতনাপ্রবাহ’-রীতির উপন্যাস হিসেবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু কেবল চেতনাপ্রবাহ নয় ওয়ালীউল্লাহ্’র এই তৃতীয় উপন্যাসেও লক্ষ্য করা যাবে বিবিধ উৎসের অনুপ্রেরণা। সমালোচক শিবনারায়ণ রায় তাঁর একটি প্রবন্ধে (‘বিবেকী ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’) কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাসটিকে সমকালীন পূর্ববাংলার জীবনসচেতন উপন্যাস বলে অভিহিত করেন। রায়ের মন্তব্যটি অত্যন্ত যৌক্তিক। সাহিত্যজীবনের প্রথম থেকেই দৈশিক-জাতিগত চেতনার স্পন্দন ওয়ালীউল্লাহ্-মানসে বর্তমান। ব্যক্তিক নির্ভরতার আঙ্গিকে সমষ্টিগতকে ধরবার তাঁর নিজস্বতা পূর্বাপর স্বাতন্ত্র্যচহ্নিত। মজিদ, আরেফ আলী এবং মুহাম্মদ মুস্তফা এই তিন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা তারই দৃষ্টান্ত। বিচক্ষণ সমালোচক শিবনারায়ণ রায়ের দৃষ্টি এড়ায় নি, একটি বিকাশমান জনপদের জীবন-বহমানতা বৈরিতাপ্রবণ বিরুদ্ধতার ফলে যে অনিশ্চয়তার বদ্ধ ডোবায় মুখ থুবড়ে পড়ে তারই বৃত্তান্ত উপন্যাসটি।
আরও পড়ুন: পিটসবার্গে কবি বুদ্ধদেব বসু
চেতনাপ্রবাহ রীতির আঙ্গিকে উপস্থাপিত উপন্যাসের তিনটি প্রধান ধারা। একটি ধারায় গ্রামে অতিবাহিত মুহাম্মদ মুস্তফা’র শৈশব ও বেড়ে ওঠার কাহিনি যেটির বর্ণনকারী তারই চাচাত ভাই। আরেকটি ধারায় মফস্বল শহর কুমুরডাঙ্গার জীবনপ্রবাহের বিবরণ যেটির বর্ণনাকারী স্টিমারঘাটের কেরানি তবারক ভুঁইয়া। তৃতীয় আরেকটি ধারায় থাকে কুমুরডাঙ্গায় ছোট হাকিম পদে যোগদান করা মুহাম্মদ মুস্তফা’র একেবারে ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলোর পর্যবেক্ষক যাকে কথকই বলা যাবে, হয়তো তাঁর মধ্যে পরোক্ষে আমরা ঔপন্যাসিককে পাবো। মিখাইল বাখতিন কথিত হেটেরোগ্লসিয়া’র এক অনুপম দৃষ্টান্ত কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাস। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য শব্দটির পরিভাষা করেছেন ‘অনেকার্থদ্যোতনা’। এটিকে বহুস্বরতা বলেও চিহ্নিত করা যায়। বিভিন্ন প্রক্ষেপণের রশ্মিপাতে বাস্তবতার ছায়া-প্রচ্ছায়ার আভাসে পটভূমির ব্যাখ্যা এখানে চলমান। তার ভেতর দিয়েই দৃষ্টিকোণ, দর্শন, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির ওঠানামা। উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয় স্থান-কাল-পাত্রভেদে ঔপন্যাসিকের সত্তাবিন্যাস চেতনার বিচিত্র প্রবহমানতায়। কখনও প্রধান হয় হতাশার আবর্তে পড়া সংকটাপন্ন কুমুরডাঙ্গার বর্তমান, কখনও মুহাম্মদ মুস্তফা’র দুঃস্বপ্নতাড়িত শৈশব ও বেড়ে ওঠা, কখনও-বা কুমুরডাঙ্গার বিভিন্ন পেশার সমস্যাপীড়িত মানুষের কথকতা। উপন্যাসটিকে চেতনাপ্রবাহ রীতির বলা হলেও এতে একই সঙ্গে কাজ করেছে একাধিক উৎসের ঔপন্যাসিক অনুপ্রেরণা। উপন্যাসটির আঙ্গিকের ক্ষেত্রে চেতনাপ্রবাহের কথা সর্বজনবিদিত। প্রসঙ্গক্রমে ভার্জিনিয়া উল্ফ্, ডরোথি রিচার্ডসন, জেমস্ জয়েস কিংবা স্যামুয়েল বেকেটের কথা ওঠে। সার্ত্র-এর লা নজে উপন্যাসের সঙ্গে যুগপৎ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের দিকটিও মনে রাখতে হয়। সার্ত্র-এর নায়ক আঁতোয়াঁ প্যারিস ছেড়ে বুভিয়ে’তে যায় এবং বুভিয়ে-ই উপন্যাসটির মুখ্য পর্যটনক্ষেত্র। সার্ত্র-এর উপন্যাসের বুভিয়ে এবং কাঁদো নদী কাঁদো’র কুমুরডাঙ্গা তুলনীয়। বুভিয়ে’তে গিয়েই অন্তর্গত বিচ্ছিন্নতার বোধ, বিবমিষা এবং প্রায় অসুস্থতা অনুভব করে আঁতোয়াঁ। মুহাম্মদ মুস্তফা’র জীবনেও নেতিকর বিচ্ছিন্নতা, অসুস্থতা-অস্থিরতা প্রভৃতি সত্তাপ্রতিকূল অনুভূতির দেখা দেয় কুমুরডাঙ্গায় অবিস্থিতির পর থেকে। বলা যায় দু’টি উপন্যাসের দু’টি অপরিচিত জায়গায় সত্তার পরীক্ষা চলে দু’জন নায়কের। সার্ত্র এবং ওয়ালীউল্লাহ্’র উপন্যাসের মধ্যে সাদৃশ্য বলতে এটুকুই। কিন্তু আঁতোয়াঁ এবং মুস্তফা’র অস্তিত্বের বোধ, প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি বিপ্রতীপ পারস্পরিকতাচিহ্নিত। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত আঁতোয়াঁ’র শুরুটাই বিয়োগাত্মক অনুভবের হতাশা দিয়ে। শুধু তা-ই নয়, সে জানতে পারে তার একসময়কার প্রেমিকা এ্যানি অর্থের বিনিময়ে অন্যের রক্ষিতা এবং বিত্তবান লোকেদের সে শয্যাশঙ্গী। বিবমিষায় আক্রান্ত আঁতোয়াঁ বমি করতে থাকে আর ভাবে বুভিয়ে হলো একটা নরক এবং বুভিয়েবাসীরা সবাই শুয়োর। লক্ষ্য করার বিষয় ‘বু’ শব্দের মানে হলো আবর্জনা। অর্থাৎ ‘বুভিয়ে’ শব্দের পূর্বনির্দিষ্ট ঔপন্যাসিক নামকরণের মধ্যেই নায়কের অসুস্থতার বীজটি পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে, কুমুরডাঙ্গায় ছোট হাকিমের পদে যোগদান করতে যাওয়া মুহাম্মদ মুস্তফা’র মধ্যে ছিল সংযুক্তির বোধ। যদিও তার ছিল একটা অসুখী-অবদমিত শৈশবাভিজ্ঞতা। তার দুর্বৃত্তস্বভাব পিতার অপচ্ছায়ায় বেড়ে ওঠাটা মুস্তফা’র অসুখের একটা বড় কারণ। পিতার উপপত্নী পোষা, গ্রামের লোকেদের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, মিথ্যে মামলায় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা এসব নিরানন্দকর অভিজ্ঞতার চাপ মুস্তফার মন থেকে মুছে দেয় স্বপ্নের আলতো আভাসটুকুও। দুর্বৃত্তস্বভাব পিতা খেদমতুল্লাহ’ অন্য এক দুর্বৃত্ত কালুগাজির হাতে খুনের ঘটনা মুস্তফাকে করে দুঃস্বপ্নতাড়িত। কুমুরডাঙ্গা ছিল মুস্তফা’র ভারাক্রান্ত জীবন ও তার ভবিতব্যের মাঝখানকার বিভাজনরেখা। যদিও কুমুরডাঙ্গা কোনো স্বপ্নদায়ী ভুবন নয়। কুমুরডাঙ্গায় জীবনের একটা পর্বকে স্থিতিতে নিয়ে যাওয়ার প্রবল স্পৃহা মুস্তফাকে যোগায় প্রেরণা। বিবাহের সিদ্ধান্ত তার সেই নতুন পর্বের প্রবেশদ্বার। তারপরেই ঘটতে থাকে একের পর এক ঘটনা (বা দুর্ঘটনা)। এসবের অন্তিম পরিণামে মুস্তফা’র স্বপ্নাকাক্সক্ষা দুমড়েমুচড়ে যায়। পরিপার্শ্বের বাস্তবের প্রকৃত নখদাঁতকে প্রকটিত দেখে মুস্তফা অনুভব করে, কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা আরও যন্ত্রণা আরও দুর্ভোগ ও আরও নিপীড়নের শিকার। এবং তার নিরানন্দকর দুঃস্বপ্নের শৈশব ও বর্তমানের বিপন্ন কুমুরঙাঙ্গা এক অবিচ্ছিন্ন অমঙ্গলসত্তা হয়ে প্রগাঢ়-অমোচনীয় কালি লেপে দেয় তার ভবিতব্যের প্রচ্ছদপটে। জীবনের কোথাও কোনো আশার আলোকণা দেখতে পায় না মুস্তফা। বুভিয়েতে যতই বিবমিষা হোক আঁতোয়াঁর উপন্যাসের শেষদিকে আমরা দেখি, কৃষ্ণাঙ্গ গায়িকার সেই গানটি (যে-গান রিফ্রেন হয়ে উপন্যাসে দেখা দেয় আঁতোয়াঁর মনোভুবনে।) এক ধরনের আশ্বাস বয়ে আনছে। আঁতোয়াঁ ভাবছে, ইতিহাস নয় সে লিখবে মার্কুইস দ্য রোয়েবনকে নিয়ে উপন্যাস যে-উপন্যাস হবে লোহার মত দৃঢ়, যে-উপন্যাস মানুষকে লজ্জা দেবে, নিজেদের সত্তা নিয়ে তারা হবে লজ্জিত। সবশেষে বুভিয়ে নগরীতে পরদিনের বৃষ্টির সম্ভাব্যতা জানিয়ে শেষ হয় উপন্যাস। কুমুরডাঙ্গায় ঘটে সম্পূর্ণ উল্টো ঘটনা। একটা বিকাশমান জীবনের স্বপ্ন নিয়ে সেখানে প্রবেশ করা যুবক মুস্তফা শুধু কুমুরডাঙ্গাই নয়, প্রস্থান করে জীবনের চৌহদ্দি থেকেই- আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে, তা-ও আত্মহত্যা করে সে কুমুরডাঙ্গায় নয়, নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়ে, যেখান থেকে সে এসেছিল। আত্মহত্যা করে মুস্তফা সেই ডোবায় যেখানে আত্মহত্যা করেছিল তারই ফুফাতো বোন খোদেজা।
আরও পড়ুন: কৃষ্ণাকামিনী দাসী
বস্তুত কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাসে সংঘটিত মুহাম্মদ মুস্তফা’র আত্মহত্যার ঘটনাটিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’র সামগ্রিক জীবনদৃষ্টি ও ঔপন্যাসিক দর্শনের নিরিখে দেখলে এটির মর্মার্থ পরিষ্ফুট হতে পারে। অনেক সমালোচকের ধারণা, এই আত্মহত্যার ঘটনাটি আচমকা, অপ্রত্যাশিত এমনকি আরোপিত। কিন্তু সাহিত্যজীবনের প্রথম উপন্যাস থেকে তাঁর এই তৃতীয় বা শেষ উপন্যাস পর্যন্ত পরম্পরাগতভাবে বিবেচনা করে এবং সেই সঙ্গে তাঁর সমকালীন বাস্তবতাকে সমান্তরালে স্থাপন করে দেখলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’র নায়কের আত্মহত্যার কারণ খুঁজে পাওয়া দুরূহ নয়। মুহাম্মদ মুস্তফার জন্ম ও বেড়ে ওঠা মূলত চাঁদের অমাবস্যা’র ছায়ায়। এ-সত্য আবিষ্কারেও খুব উদ্ভাবনীশক্তির প্রয়োজন পড়ে না, মুস্তফা ১৯৪৭-এর জাতক। উপন্যাস রচনার কাল ১৯৬৬/৬৭ সাল এবং উপন্যাসান্তগর্ত কালও একই। সেসময়টাতে ২০/২১ বছর বয়সে গ্র্যাজুয়েটধারী শিক্ষিত যুবকেরা সরকারি চাকুরিতে যোগদান করতো। সে-হিসেবে কুমুরডাঙ্গায় ছোট হাকিমের পদে সদ্য যোগদান করা মুস্তফা’র বয়স ২০/২১। গ্রামের বড়বাড়ির দাদাসাহেবের অনুজ কাদেরের হাতে করিম মাঝির স্ত্রীর খুনের ঘটনার (চাঁদের অমাবস্যা) আগেই কিন্তু মুস্তফা’র জীবনে আরও একটি হত্যাকাণ্ডের অভিজ্ঞতা ঘটে যায়। সেটি হলো তার নিজেরই পিতা খেদমতুল্লাহ্-হত্যাকাণ্ড। পিতার অসৎ-দুর্বৃত্ত স্বভাব, মায়ের অসম্মান-অমর্যাদা, পিতার হত্যাকাণ্ড এইসব পারিবারিক-সামাজিক অনাচারের মধ্যে বেড়ে ওঠা মুস্তফা’র বৃহত্তর পরিমণ্ডলের অভিজ্ঞতাও সুখকর নয় বরং আটপ্রাহরিক মানসিক অস্বস্তির কারণ। শিবনারায়ণ রায় চিহ্নিত স্টিমারঘাট থেকে কোম্পানির ঘাট সরিয়ে নেওয়ার চিত্রটিকে পূর্ববাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের (সামরিক স্বৈরাচার) শোষণ-নির্যাতনমূলক আচরণের প্রতীক হিসেবে ধরলে কুমুরডাঙ্গা অনিবার্যভাবে পূর্ববাংলার রূপকে দাঁড়ায়। কুমুরডাঙ্গার রুদ্ধতা, বিকাশহীনতা, ক্রমাধোগতির সাক্ষী মুস্তফা। ১৯৫৮ সালে জারিকৃত সামরিক শাসন তখন তুঙ্গে। এরিমধ্যে ১৯৬৫ সালে বেধে যায় ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত যুদ্ধ। সে-যুদ্ধে এককালে ভীরু বলে পাকিস্তানি শাসক কর্তৃক অপবাদ দেওয়া বাঙালি বৈমানিকদের বেছে-বেছে ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে পাঠানো হতে থাকে। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বাধিকারচেতনা-উদ্দীপ্ত বাঙালির ৬-দফা ঘোষিত হলেও সামরিক শাসনের কাঠিন্য-কালাকানুনের প্রতিরোধে বাঙালি কোণঠাসা। ১৯৬৭ সালে পূর্ববাংলায় চেপে বসে নতুন যাঁতা। রেডিও-টেলিভিশন ইত্যাদি প্রচার-মাধ্যমে নিষিদ্ধ হয় রবীন্দ্র সঙ্গীত। ১৯৬১ সালে সামরিক শাসনামলেই বাঙালি প্রভূত প্রতিকূলতার শ্যেণ চক্ষু উজিয়ে উদযাপন করেছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীর উপলক্ষ। কিন্তু রবীন্দ্র-নিষিদ্ধের ঘটনায় বাঙালি সত্যিকার অর্থেই হতচকিত হয়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, রবীন্দ্রসাহিত্য-সংস্কৃতির যাবতীয় চর্চার সামনে তুলে দেওয়া হয় বাধার প্রাচীর। এরকম নিরানন্দকর মানসিক যাতনাময় পরিস্থিতিতে কুমুরডাঙ্গার স্টিমারঘাট সরিয়ে নেওয়াটা যেন এক মহাবিপর্যয়। মুস্তফা’র ব্যক্তিগত জীবন এবং কুমুরডাঙ্গাবাসীদের সামষ্টিক জীবন উভয়ই আক্রান্ত হয় বিপন্নতায়। প্রথমবার যাত্রার মুহূর্তে জ¦রের কবলে পড়া মুস্তফা’র বিবাহযাত্রায় বিঘœ ঘটে এবং পরের বার ঘাট বন্ধ হয়ে গেলে মুস্তফার মনে জেগে ওঠে এক গাঢ় অমঙ্গলবোধ। এরিমধ্যে তার বিবাহের সংবাদ গ্রামে পৌঁছালে তাদেরই বাড়িতে আশ্রিত পিতৃহীন ফুফাতো বোন খোদেজা আত্মহত্যা করে। খোদেজার মৃত্যু মুস্তফাকে ভেতরে ভেতরে অপরাধী করে তোলে। কেননা, সে বা খোদেজা কেউই পরস্পর পরস্পরকে কখনও বিয়ের চিন্তা মনে ঠাঁই না দিলেও পরিবারের সবাই ধরেই নিয়েছিল অভিভাবকদের ইচ্ছে অনুযায়ী একদিন নিজের পায়ে দাঁড়ানো মুহাম্মদ মুস্তফার সঙ্গেই বিয়ে হবে খোদেজার। একই সঙ্গে তাকে সহ্য করে যেতে হয় অধিবাসীদের দুর্ভোগ ও কষ্টের দিনযাপন। লক্ষণীয়, স্টিমারঘাট বন্ধের বিষয়টিকে কুমুরডাঙ্গাবাসীদের মনে হয় গভীর চক্রান্তÑ তাদেরকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তিলে-তিলে ধ্বংস করবার এক সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র। কুমুরডাঙ্গা মফস্বল এবং একই সঙ্গে দ্বীপও। ফলে, যোগাযোগ ও আসা-যাওয়ার সূত্র-ছিন্ন কুমুরডাঙ্গায় নামে মহাজাগতিক দুর্যোগ। তারা দেখতে পায় তাদের সামনে ধ্বংস ও বিপন্ন হয়ে যাওয়াটাই একমাত্র গন্তব্য। কুমুরডাঙ্গার এ-পরিস্থিতি সন্দেহাতীতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি নয়া ঔপনিবেশিক শাসনকবলিত পূর্ববাংলার চিত্র। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন পূর্ববাংলায় সৃষ্টি করে এক ভয়াবহ অন্ধকার যুগ। এটা ঔপন্যাসিকরেই পর্যবেক্ষণ- লিখেছেন তিনি- “যে-টুকু অবশিষ্ট ছিলো তা-ও শেষ হয়েছে এবং কুমুরডাঙ্গা এবার যেন মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তন করেছে।” ‘মধ্যযুগ’ মানে আলো-আশাহীনতার যুগ। তবে, এ-কথাটা আর কিছুদিন পরের বাস্তবতায় উচ্চারিত হতো কিনা সে-প্রশ্ন উত্থাপনযোগ্য। উপন্যাসটির রচনাকাল এক চরম নেতিময় যুগের প্রেক্ষাপটে। কিন্তু সেটি যদি ১৯৬৮ সালের আগে না হয়ে ১৯৬৯ সালের পরে হতো তাহলে পরিস্থিতি দাঁড়াতো সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি অনুমান এবং কল্পনানির্ভর হলেও আমাদের ধারণা, মুহাম্মদ মুস্তাফা’র মনোজগতে একটা নতুন চিন্তা একটা নতুন চেতনার আভাস জাগতো। কেননা, ‘আজি এ-প্রভাতে রবির কর’-এর মত এক চরাচরব্যাপী বিস্ফারণে পূর্ববাংলায় সৃষ্টি হয় অভূতপূর্ব গণজোয়ার। গণআন্দোলনের তরঙ্গ আছড়ে পড়া কুমুরডাঙ্গার মানুষ নিশ্চয়ই তখন নিজেদের বাসভূমিতে ‘মধ্যযুগ’-এর পরিবর্তে লক্ষ করতো এক নবযুগের আসন্নতা। এরকম দৃষ্টিউন্মোচক-প্রাণসঞ্চারী জাগরণের সামনে মুহাম্মদ মুস্তফা’র মনের অন্তর্গত ঊষরতা নিশ্চয়ই খানিকটা হলেও পেতো আর্দ্রতার স্পর্শ। ফলে, আত্মধ্বংসের মত বিনাশী গন্তব্যের অভিমুখ হয়তোবা বেছে নিতো না সে। কিন্তু ১৯৬৮-র পূর্বে এক ধারাবাহিক ধ্বসের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলা পৌঁছায় এক মুমূর্ষাবস্থার দ্বারপ্রান্তে। সে-বাস্তবতা অর্থনীতির ছাত্র সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’র চাইতে ভাল আর কারও জানার কথা নয়। ফলে, কাঁদো নদী কাঁদো-তে স্টিমারঘাট বন্ধের প্রতীকটি শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানি অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক শোষণের প্রখর প্রতিকল্প হয়ে দাঁড়ায়। গাণিতিক-পরিসংখ্যানগত বিচারেও আমাদের পক্ষে উপন্যাসের বা কুমুরডাঙ্গার বা পূর্ববাংলার বাস্তবতাটির অনুধাবন সম্ভব। ধরা যাক, দুই পাকিস্তানে বিভাজিত দেশ স্বাধীন হলো ১৯৪৭ সালে। তাহলে ১৯৪৮ থেকেই শুরু হয় বিকাশমান দুই দেশের দু’টি জাতির অর্থনৈতিক যাত্রা। কিন্তু অর্থনীতির প্রাণপঙ্ক যে-বাজেট সেটির নিয়ন্ত্রণ থাকে পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে। সেই বাজেট-চরিত্র বিশ্লেষণ করলে তখনকার অর্থনৈতিক বাস্তবতার চিত্রটি স্পষ্ট হবে। ১৯৫০-৫৫ কালপরিধিতে পূর্ববাংলায় ব্যয়িত হয় ৪৬.৪% পরিমাণ অর্থ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৫৩.৬%। ১৯৫৫-৬০ কালপরিধিতে পূর্ববাংলায় ব্যয়িত হয় ৩১.৭% পরিমাণ অর্থ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৬৮.৩%। ১৯৬০-৬৫ কালপরিধিতে পূর্ববাংলায় ব্যয়িত হয় ৪১.৮% পরিমাণ অর্থ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৫৮.২%। ১৯৬৫-৭০ কালপরিধিতে পূর্ববাংলায় ব্যয়িত অর্থ ৪১.২% পরিমাণ অর্থ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৫৮.৮%। পরিসংখ্যানটির শাব্দিক অনুবাদ হলো, পূর্ববাংলার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক শোষণ। আর সেই বৈষম্যের পরিণতিতে পশ্চিম পাকিস্তান এগোয় উন্নয়নের প্রধান সড়ক ধরে। রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, ভবন, সেতু, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি দৃশ্যমানতায় ভরে উঠতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত অঞ্চল আর বিপরীতে ঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়া কুমুরডাঙ্গা তথা পূর্ববাংলার মানুষেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান, কখন আবার ঘাট চালু হবে। এরই সৃজনশীল অনুবাদে দেখবো, কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাসে কুমুরডাঙ্গার ক্রমঃ-শীর্ণবিশীর্ণতার সমান্তরালে শোনা যেতে থাকে নদীর কান্না যে-কান্না প্রথমে শুনতে পায় স্কুলশিক্ষয়িত্রী সাকিনা, তারপর একে-একে সংক্রমণের মত প্রায় সব অধিবাসী। ১৯৬৯ যে একটি বিপুল ধাক্কা সেটি বেঁচে থাকলে নিঃসন্দেহে অনুভব করতো মুহাম্মদ মুস্তাফা। কেননা, সে-ধাক্কা টের পেয়েছিল খোদ পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরাচার-ই। যেজন্যে ১৯৭০ সালে প্রথম বারের মত বাজেটে পূর্ববাংলার জন্যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় ৫৫% এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে ৪৫%। হ্যাঁ, স্পষ্টই ব্যতিক্রম আর সেই ব্যতিক্রমটি ছিল এক ধরনের রাষ্ট্রীয় উৎকোচ- বলেছেন খোদ পাকিস্তানি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হাসান গার্দেজি এবং পাকিস্তানি সাংবাদিক অক্সফোর্ড বিশ^বিদ্যালয়ের চাত্র সংসদের সাবেক সভাপতি তারিক আলীসহ আরও অনেকেই। কিন্তু সেটা ছিল বড় বিলম্বের ফল। এমন উৎকোচের আয়োজন সত্ত্বেও ঠেকিয়ে রাখা যায় নি কুমুরডাঙ্গাবাসীদের মানে পূর্ববাংলার মানুষকে তথা বাঙালিকে। পরবর্তী ইতিহাস লড়াই রক্তাক্ত যুদ্ধ এবং রক্তনদী সাঁতরানো বিজয়ের সোনালি সূর্যের উদয়। দুর্ভাগ্য, সেই সূর্যোদয়ের জন্যে মুহাম্মদ মুস্তফা’র বেঁচে থাকা হয় না। আত্মহত্যা না-করে বেঁচে থাকলে একটু হলেও যে আশাবাদে উদ্রিক্ত হতো মুহাম্মদ মুস্তফা তার প্রমাণ স্বয়ং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-ই। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনায় দারুণ অনুপ্রেরণা অনুভব করেন তিনি যেটা তাঁর জীবনী থেকে জানা যায়। তাছাড়া ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি প্যারিসে বসে সেখানকার গণমাধ্যম এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষে জনসংযোগের ভূমিকায় নামেন। চাপা স্বভাবের মানুষ ওয়ালীউল্লাহ্ হয়ে ওঠেন সাংগঠনিক মানুষ। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের সঙ্গে রাখেন যোগাযোগ। প্যারিস থেকে সংগৃহীত অর্থ পাঠান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সহায়তায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য স্বয়ং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’রও। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে দেশ স্বাধীন হওয়ার মাসদু’য়েক আগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন বিদেশের মাটিতে।#