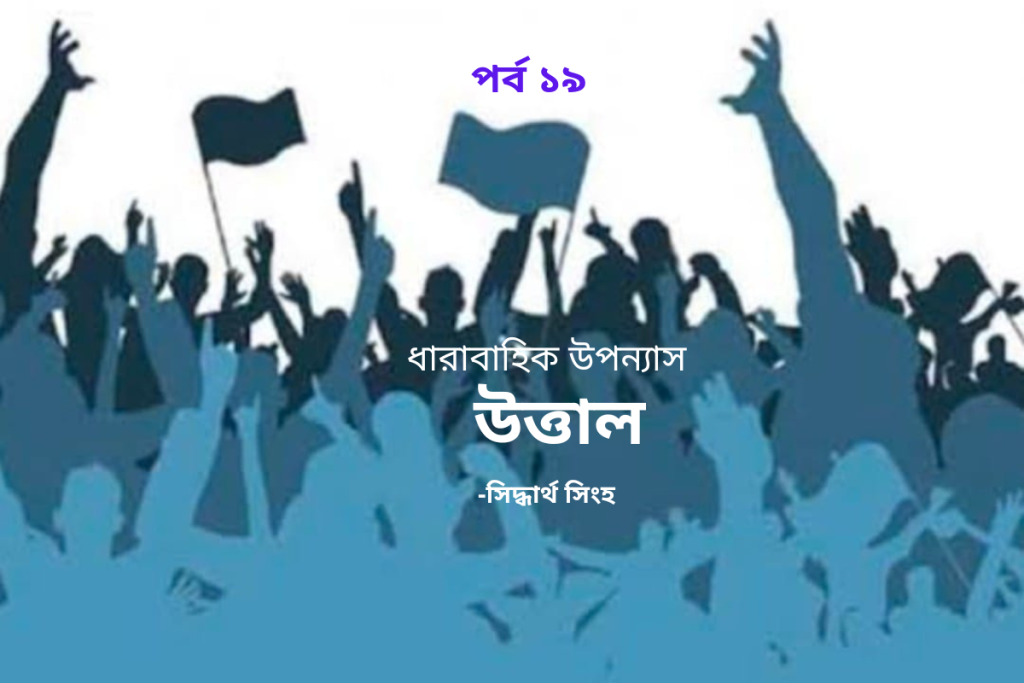।।পর্ব – উনিশ।।
শুভাপ্রসন্ন, চৈতালী ঘোষ, প্রসূন ভৌমিক, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের পথ দেখিয়ে বেড়াবেড়ির পূর্বপাড়ায় নিয়ে এলেন এই গ্রামেরই দীর্ঘ দিনের বাসিন্দা হরিচরণ। আসার পথে তাঁর মুখেই ওঁরা শুনলেন, দোবাঁদি বা রুইদাসপাড়ার তুলনায় এই পূর্বপাড়াটা একটু বর্ধিষ্ণু। এখানে একশো পঞ্চান্ন থেকে একশো ষাট ঘর মানুষ বাস করেন। তার মধ্যে এক ঘর কেবল তফসিলি, বাকিরা মাহিষ্য। গ্রামসভার নাম খাসেরভেড়ি। বেড়াবেড়ি পঞ্চায়েতটা সি পি এমের। এই গ্রামসভায় একমাত্র একজনই তৃণমূল সদস্য। তাঁর নাম দুধকুমার ধাড়া। গ্রামে কয়েক ঘর ভূমিহীন ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেরই কম-বেশি নিজস্ব জমি আছে। ভাগ চাষি হিসেবে নথিভুক্ত বা রেকর্ডেড বর্গাদার মাত্র এক ঘর। তাঁরা এর মধ্যেই এই আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে এগিয়ে এসেছেন এবং তাঁরা আগাম বলেও দিয়েছেন, সরকার তাঁদের যত প্রলোভনই দেখাক না কেন, তাঁরা কিছুতেই টলবেন না।
শুধু তাঁরা নন, এখানে আসার পর থেকেই যাঁরা বংশপরম্পরায় এত দিন ধরে সি পি এম করে এসেছেন, সি পি এমের রাজত্বে জন্মেছেন, সি পি এমের রাজত্বেই পড়াশোনা করেছেন, সি পি এমের রাজত্বেই বিয়ে করেছেন, বাবা-মা হয়েছেন এবং যাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁদের মৃত্যুও হবে এই বাম জমানাতেই, তাঁদেরও কেউ কেউ এই জমি রক্ষার আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। যদিও তার মধ্যেই যাঁরা শাসক দলের একেবারে অন্ধ ভক্ত, যাঁরা নিজেদের ভাল-মন্দটুকুও ঠিক মতো বোঝেন না, বুঝতেও চান না, পার্টির দাদারা যা বোঝান, তাই বেদবাক্য মনে করেন। তাঁরা কিন্তু অনড় অবিচল। প্রথম থেকেই কেতাবি ভাষায় বলতে শুরু করেছেন, দেশের উন্নতির জন্য বা রাজ্যের শিল্পায়ন ঘটাতে সরকার যে পদক্ষেপ নেবে, আমাদের তাতে পূর্ণ সমর্থন আছে। শুধু চাষের জমি কেন, সরকার যদি বাস্ত জমিও চায়, আমরা তা আনন্দের সঙ্গেই দিয়ে দেব। শুধু নিজে খাব, নিজে পরব, নিজে ভাল থাকব করলে হয় না, দেশের জন্যও একটু ভাবতে হয়। কোনও বড় কাজের জন্য অনেক ছোট ছোট ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। যাঁরা স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন, তাঁরা কি কম করেছিলেন? কী না করেছেন তাঁরা? শুধু তাঁরা নন, তাঁদের বউ-মেয়েরা তো তাঁদের শেষ সম্বল, গায়ের গয়নাগুলো পর্যন্ত খুলে দিয়েছিলেন দেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করার জন্য। আর আমরা এটুকু দিতে পারব না! তা ছাড়া সরকার তো আর বিনে পয়সায় আমাদের জমি নিচ্ছে না। নিতে হলে, জমির যা দাম, তার থেকে বেশিই দেবে। তা হলে আমরা সরকারের এই কর্মযজ্ঞে সাথ দেব না কেন?
এই কথাগুলো যাঁরা বলছিলেন, তাঁদের মধ্যে যেমন অনেক গরিব মানুষ আছেন, তেমনি আছেন অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পরিবারও।
এখানকার লোকজনদের কারওরই পাট্টা জমি নয়, সবারই নিজস্ব বাস্তুজমি। তার দলিল বা পরচা আছে। পৈতৃক জমি ছাড়াও চাষবাস থেকে আয় করেও অনেকে কিছু কিছু জমি কিনেছেন। গত দশ-পনেরো বছরে এখানে খুব দ্রুত উন্নতি হয়েছে। গোটা গ্রাম ঘুরলেও চার-পাঁচটার বেশি কাঁচা বাড়ি দেখতে পাওয়া যাবে না। সবই পাকা বাড়ি। কোনও কোনও বাড়ি আবার দোতলা। স্থানীয় লোকেদের দাবি, তাঁদের যাবতীয় উন্নতি হয়েছে চাষাবাদ করেই। কারণ, তাঁরা যা ফলান, সংসারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রেখেও প্রচুর ধান, আলু, পাট, শাক-সবজি বিক্রি করতে পারেন। এবং তা থেকে যথেষ্ট কাঁচা টাকাও তাঁরা আয় করেন।
আরও পড়ুন: ধারাবাহিক উপন্যাস উত্তাল ১৮
হাঁটতে হাঁটতে হরিচরণই বললেন, সরকার জমি নিয়ে নিলে, গ্রামের তিন-চারটে পরিবারের গায়ে তেমন কোনও আঁচ পড়বে না ঠিকই, কারণ, তাঁদের পরিবারের ছেলেরা কেউ কাজ করেন পোস্ট অফিসে। কেউ মাস্টারি করেন স্কুলে। আর তা না হলে কাজ করেন রেলের ওয়ার্কশপে। কিন্তু একদম পথে বসে যাবেন গ্রামের বাকি লোকেরা। ইতিমধ্যেই জমি হারানোর আতঙ্কে, বিকল্প আয়ের কথা ভেবে বড়দের পাশাপাশি প্রায় প্রতিটি পরিবারের অল্পবয়সি ছেলেরাও কাজের জন্য গ্রামের বাইরে যেতে শুরু করে দিয়েছে।
রাস্তাঘাট অত্যন্ত ভাল হয়ে যাওয়ায় এবং নতুন নতুন অনেক রুট চালু হওয়ায় এখান থেকে কলকাতায় যাতায়াত করাটা যেহেতু অনেক সহজ হয়ে গেছে, তাই চাষের কাজের পাশাপাশি, দু’পয়সা বাড়তি রোজগারের জন্য এখানকার ছেলেরা কলকাতায় গিয়ে হয় কাঠের কাজ করছে, না হলে ইলেকট্রিকের কাজে হাত পাকাচ্ছে। কেউ কেউ বিভিন্ন ফ্ল্যাটবাড়ি বা আবাসনে পাহারাদারের কাজও করছে। করছে রংমিস্ত্রির কাজও। কিন্তু কে কী করছে, সেটা কেউই কাউকে বলছে না।
সে না বলুক। কিন্তু গ্রামের বাইরে বেরিয়েছে দেখেই তো ওরা ক্রমাগত স্বচ্ছল থেকে স্বচ্ছলতর হচ্ছে। ভালমন্দ খাচ্ছে। দামি দামি জামাকাপড় পরছে। সংসারে বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে। তা হলে আমরাই বা পড়ে থাকব কেন? এটা ভেবেই হয়তো ওঁদের দেখাদেখি গ্রামের অন্যদের মধ্যেও কলকাতায় কাজ করতে যাওয়ার প্রবণতা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।
তবে সব থেকে বিপাকে পড়েছেন বয়স্ক লোকেরা। যাঁদের বয়স ষাট থেকে পঁয়ষট্টি। জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই তাঁরা কাটিয়েছেন গ্রামের ভিতরে। গ্রামের বাইরে সে ভাবে কখনও পা-ও রাখেননি। ফলে এই বয়সেও মাঠের কাজে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে পারলেও, শহরে গিয়ে কিছু করা তো দূরের কথা, শহরে যাওয়ার জন্য বাসে-টামে ওঠাটাও তাঁদের কাছে একটা ভয়ানক আতঙ্কের ব্যাপার।
এখানে প্রত্যেক বাড়িতেই গরু আছে। জাত অনুযায়ী এক-একটা গরু পাঁচ-ছ’কেজি থেকে আট-দশ কেজি দুধ দেয়। নিজেরা ফেলিয়ে-ছড়িয়ে খেয়েও যতটা দুধ বাঁচে, দশ টাকা কেজি দরে সেই দুধ বিক্রি করেও গরুর খোরাকি, ওষুধপত্র-সহ যাবতীয় খরচ-খরচা উঠে তো আসেই, উপরন্তু দু’পয়সা হাতেও থাকে। কিন্তু জমি নেওয়ার জন্য সরকার যে ভাবে উঠেপড়ে লেগেছে, এ সব বোধহয় আর বেশি দিন চলবে না। কারখানা করার জন্য জমি চলে গেলে ধান চাষ বন্ধ হয়ে যাবে। পাওয়া যাবে না গরুর খাওয়ার বিচালিও। উধাও হয়ে যাবে গরু চরাবার জায়গাও। তখন সবাই গরু বেচতে শুরু করে দেবেন। আর সবাই-ই যদি গরু বেচতে চান, কিনবেন কে? সুতরাং তখন গরুর দামও হুহু করে নেমে যাবে। হয়তো বিনে পয়সায় দিলেও খোরাকি জোগাড় করার ভয়ে কেউই নিতে চাইবেন না। তাই ভয়াবহ সেই দিনের কথা ভেবে অনেকেই আগেভাগে গরু বেচতে শুরু করে দিয়েছেন।
আরও পড়ুন: আমৃত্যু সংগ্রামী যোদ্ধা শহীদ সেরনিয়াবাত
টাটাদের পছন্দ করা জায়গার মধ্যে এই গ্রামের বেশির ভাগ লোকেরই জমি পড়েছে। কারও কারও সব জমি না পড়লেও কিছু না কিছু তো পড়েছেই। পড়েছে ভাগচাষের জমিও। সেখানে কাউকেই ঘেঁষতে দিচ্ছে না পুলিশ এবং ক্যাডার-বাহিনী। তার বাইরে যাঁদের দু’-চার কাঠা জমি পড়ে আছে, অনেকে সেখানে সবজি চাষ করছেন। পাটও লাগাচ্ছেন কেউ কেউ। গ্রামের অবস্থাপূর্ণ পরিবারের লোকেরা পাটকাঠি দিয়েই জ্বালানির কাজ করেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা পাট লাগাতে পারেননি, তাঁরা তো আর এত দিনের অভ্যাস একদিনের মধ্যে পালটাতে পারবেন না, তাঁদের পাঠকাটি লাগবেই। তাঁদের কাছে বিক্রি করা যাবে, এই আশায়।
শুভাপ্রসন্নদের দলটাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা হরিচরণ যে মাঠে এনে বসতে দিলেন, সেটা খামারের মাঠ। উনি বলেছিলেন, অন্যান্য বছর এখানে গোলা ভরা ধান থাকে। সব সময় লোকজনে গমগম করে। বস্তায় ভরে ভরে ভ্যানরিকশায় করে বাজারে নিয়ে যাওয়া হয় বিক্রির জন্য। সম্বৎসর বাড়িতে খাওয়ার জন্য চাল করতে পাঠানো হয় ধানভানার কলে। কারণ, এখন আর কোনও বাড়িতেই সেই আদ্যিকালের মতো ঢেঁকিতে ধান ভানা হয় না।
কিন্তু শুভাপ্রসন্নরা দেখলেন, ধান কোথায়? এ তো একেবারে ফাঁকা ময়দান। আর সেই ময়দানে এই মধ্যদুপুরেও তাঁদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। তা ছাড়াও দূর দূর থেকে এখানে যাঁরা কাজ করতে আসেন, আছেন সেই সব মেয়ে-বউরাও।
একজন মহিলাকে দেখে গুটিগুটি পায়ে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন এ পি ডি আর-এর দেবব্রত। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম কি?
উনি বললেন, লক্ষ্মী মণ্ডল।
ফের প্রশ্ন করলেন তিনি, কোথায় থাকেন?
উনি বললেন, আমি এখানে থাকি না। ঝাঁপানডাঙা থেকে আসি।
– ঝাঁপানডাঙা? সেটা আবার কোথায়?
– বর্ধমান জেলায়।
চমকে উঠলেন দেবব্রত। বর্ধমান থেকে!
– এখন তো অনেক কমে গেছে। আগে প্রত্যেক দিন বর্ধমানের বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রচুর মানুষ এখানে মজুর খাটতে আসত। এখন আমরা মাত্র ক’জনে এসে ঠেকেছি।
– কত দিন ধরে আসছেন?
– তা প্রায় ষোলো-সতেরো বছর তো হবেই।
– এখানে কী ধরনের কাজ করতেন?
– বিভিন্ন রকমের কাজ। ধান রোয়া থেকে শুরু করে ধান তোলা। যখন যেমন কাজ থাকত, তেমন। সব কাজই করতাম। আবার দরকার পড়লে শুধু মাঠের কাজই না, ঘরের কাজও করতাম।
– কোথায় কাজ করতেন?
– একটা বাড়িতে।
– রোজই আসতেন?
– হ্যাঁ, রোজই। ঝড় হোক জল হোক, কাজ হোক না হোক, রোজ আসতাম। কিন্তু চাষ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়…
– এখন কী করেন?
– সক্কালবেলায় এসে গ্রামের মধ্যে ঘোরাঘুরি করি। যে যা বলে করি দিই।
– রোজ কাজ পান?
– না না, এখন আর রোজ কাজ মেলে না। চাষই নাই, তো কাজ!
– তবু রোজ আসেন?
– হ্যাঁ। শুয়ে-বসে থাকলি তো আমাদের চলবে না। বেরুতে হবে।
– যে দিন কাজ পান না, সে দিন তো আপনার এখানে আসা লস।
– অত লাভ লোকসান দেখলি চলে? কাজ পাব না ভেবে যদি বাড়িতে বসে থাকি, চলবে? হয়তো দেখা যাবে, ওই দিনই মেলা কাজ ছিল। অত হিসেব করে চললি আমাদের হবে না। আমাদের গতর খাটিয়ে খেতি হয়।
– যে দিন কাজ পান না, সে দিন ক’টা অবধি এখানে থাকেন?
– দুপুর অবধি তো থাকিই।
– আর খাওয়াদাওয়া?
– সেটা এখানে কারও না কারও বাড়িতে ঠিক হয়ে যায়।
– কাজ না করলেও?
– হ্যাঁ, আমাকে চেনে তো… জানে। কেউ কেউ তো নিজে থিকাই বলে, কোথাও কিছু না পাইলি আজ দুপুরে আমাদের এখানে খাইয়া নিয়ো। ফলে, খাওয়ান নিয়ে আমার কোনও চিন্তা নাই।
ওঁরা কথা বলছিলেন। পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন হরিচরণ। তিনি হঠাৎ ওঁদের কথার মাঝখানে বলে উঠলেন, কিছু দিন আগেও সক্কালবেলায় বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রত্যেক দিন কয়েকশো লোক কামারকুণ্ডু স্টেশনে নেমে এই সব গ্রামে ছড়িয়ে পড়ত। কোথাও না কোথাও ঠিক কাজ পেয়ে যেত। এ দিকে না পেলে ডানকুনির দিকেও চলে যেত। কেউই খালি হাতে ফিরত না।
ক’হাত দূরেই আর একজন খেতমজুরের সঙ্গে কথা বলছিলেন শুভাপ্রসন্ন। তাঁর নাম কেশব বালা। তিনি আসেন বর্ধমানের চাঁচাই থেকে। মশাগ্রামের পরের স্টেশন। তিনি জানালেন, ধান কাটার মরসুমে আমরা এক-একদিন প্রায় দু’-তিনশো লোক এখানে কাজ করতাম। এখন মোটে চার-পাঁচ জন আসি। আমার নিজের কোনও জমি নাই। ভাগেও করি না। বরাবরই চাষের কাজে মজুর খাটি। ধান-আলুর মরশুমে বর্ধমানের দিকে কাজ থাকে। তাই ওই সময়ে আমি এখানে খুব একটা আসি না। পাটের সিজিনেই বেশি আসি। কিন্তু যারা পাট চাষ করত, তাদের বেশির ভাগ জমিই তো টাটাদের মোটর গাড়ি কারখানার মধ্যে পড়ে গেছে। ফলে এ বছর পাট চাষ হয়নি বললেই চলে। এর পরে যে কী হবে, বুঝতে পারছি না।
শুভাপ্রসন্ন বললেন, আচ্ছা, তোমরা যেমন ও দিক থেকে এ দিকে কাজ করতে আসো। এ দিককার লোকও কি ও দিকে যায়?
কেশব বললেন, না না, এ দিককার লোক অন্য কোথাও যায় না। অন্য জায়গার লোকই বরং এখানে আসে। এ দিকেই তো চাষবাসটা ভাল। সারা বছরই কিছু না কিছু চাষ হয়।
আরও পড়ুন: শ্রীমতি বর্ষা
বেড়াবেড়ির এই পূর্বপাড়ায় একটাই তফসিলি জাতির ঘর। তাঁরা তিন ভাই। তার মধ্যে সীতারাম মাঝি একজন। তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন চৈতালী ঘোষ। তাঁরা তিন ভাই মিলে আট বিঘে জমি ভাগে চাষ করতেন। অনথিভুক্ত ভাগচাষি সীতারাম নিজে চাষ করতেন তিন বিঘায়। বোরো এবং আমন, দু’ধরনের চাষই। মাঝখানে আলু, পটল, সরষে, কুমড়ো, কপিও বাদ দিতেন না। খুব ভাল ভাবে খেয়ে-পরে সংসার চলে যেত। এ ছাড়াও তাঁর একটা দমকল আছে। মানে পাম্পসেট। সেচের কাজে ভাড়া খাটাতেন। ঘণ্টায় চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা ভাড়া। সব খরচ-খরচা বাদ দিয়েও ঘণ্টা পিছু কুড়ি-পঁচিশ টাকা আয় হত। সেই টাকা জমিয়ে ব্যাঙ্কে কিছু সঞ্চয়ও করেছিলেন। ভেবেছিলেন, আরও একটা পাম্পসেট কিনবেন। কিন্তু সরকারের নয়া নীতিতে চাষবাস শিকেয় ওঠায়, যে পাম্পসেটটা আছে, সেটাই এখন ভাড়া হচ্ছে না। ফলে নতুন কেনার কোনও প্রশ্নই নেই।
চৈতালী তাঁকে বললেন, তা হলে আপনার আয় কমে গেছে বলুন…
সীতারাম বললেন, সে তো গেছেই। এ বার অল্প কিছু জমিতে ট্যাঁড়স করেছি। কিছু দিন কাজ হবে। তার পরে যে কী হবে ফানি না।
– ঘরে ক’জন লোক?
– আমরা স্বামী-স্ত্রী ছাড়াও দুই মেয়ে আছে।
– তারা কী করে?
– ওরা পড়াশোনা করে।
– কীসে পড়ে?
– বড়টা ক্লাস নাইনে আর ছোটটা ফাইভে।
– তা হলে এখন কী করবেন?
– সেটাই তো ভাবছি। ওদের পড়াশোনার খরচ, খাওয়াদাওয়া, আত্মীয়-কুটুম্ব আসা-যাওয়া, রোগবালাই হলে তার চিকিৎসা করা– সবই তো করতে হবে। কী ভাবে যে সামাল দেব বুঝতেই পারছি না।
ওঁদের থেকে ক’হাত দূরে তখন প্রসূন ভৌমিককে ঘিরে একটা জটলা। তাঁর কাছে স্থানীয় আর এক বাসিন্দা হড়বড় করে বলে চলেছেন, টাটা প্রকল্পের জন্য যে জায়গাটা অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, সেখানে সেচের জন্য ডিপ টিউবয়েল আছে তিনটে। মিনি টিউবয়েল সাঁইতিরিশটা। ওরা জমি নিয়ে নিলে তো ওগুলো ওদের মধ্যে পড়ে যাবে। আমরা ব্যবহার করতে পারব না। ফলে ওই প্রকল্পের বাইরে যে চাষের জমি পড়ে থাকবে, জলের অভাবে সেখানেও কিন্তু চাষ মার খাবে। আসলে সেচের ব্যবস্থা ভাল বলেই এখানে চাষবাসের এত উন্নতি হয়েছিল। তা ছাড়া আটাত্তরের পর থেকে এখানে আজ পর্যন্ত কোনও বন্যা হয়নি।
– কেন?
– কারণ, এই বাঁধ। এই বাঁধের ফলে শুধু বন্যাই আটকায়নি, আমাদের চাষেরও অনেক সুবিধে হয়েছে।
– কী রকম?
– বৃষ্টির সময় নদীতে জলের চাপ বেড়ে গেলে বাঁধের লোকেরা লকগেটের কপাট ফেলে দেয়। ফলে উপর দিয়ে বয়ে যায়। ওই বাড়তি জল জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই জল পেয়ে ধানগাছগুলিও তরতর করে বেড়ে ওঠে। আমাদের আলাদা করে আর সেচের ব্যবস্থা করতে হয় না। কিন্তু চাষের জমি যদি ওরা নিয়ে নেয়, তা হলে তো কারখানা করার সঙ্গে সঙ্গে জমিটাকেও ওরা কংক্রিট করে ফেলবে। আর তার ফলে লকগেটের কপাট ফেলে দিলে বাড়তি জল টেনে নেওয়ার মতো কাঁচা-জমি না থাকায়, যে-জল একদিন আমাদের চোখে-মুখে হাসি ফুটিয়েছিল, সেই জলই আমাদের দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের ঘরবাড়ি সব ভাসিয়ে দেবে। আবার বন্যার কবলে পড়ব আমরা।
গ্রামবাসীরা যে যা বলছিলেন, প্রসূন সেগুলোকে ছোট্ট একটা নোট বইয়ে টুকে নিচ্ছিলেন। ওই গ্রামবাসী একটানা কথা বলতে বলতে একটু দম নিতেই তার ফাঁকে ঢুকে পড়লেন আর একজন।
তিনি অভিযোগ করলেন, কিছু দিন যাবৎ দেখছি, ওই জমিতে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে, সে জন্য পাহারাদার রাখা হয়েছে। রাতে সেটা আরও জোরদার করা হয়। সারা রাত ওখানে হ্যালোজেন জ্বালিয়ে রাখে। সেই আলো প্রকল্পের বাইরের জমিতেও এসে পড়ে। আর তার ফলে আশপাশের জমিতে যে ট্যাঁড়স গাছ লাগানো হয়েছে, সেগুলোতে তেমন ফলন হচ্ছে না।
– কেন?
– সারা রাত আলো জ্বললে এমনিতেই ফসলের ক্ষতি হয়।
– তাই নাকি?
– হ্যাঁ। কারণ, মানুষের যেমন রাত্রিবেলায় ঘুমের দরকার হয়, তেমনি গাছেদেরও বিশ্রামের প্রয়োজন হয়।
– তাই? অবাক হয়ে গেলেন প্রসূন। আলো জ্বললে গাছেদের অসুবিধে হয়!
– হবে না? অত পাওয়ারের আলো। ওদের কি অভ্যাস আছে? রাত্রিবেলায় আপনার চোখের সামনে যদি সামান্য একটা পাঁচশো ওয়াটের লাইটও জ্বালিয়ে রাখি, আপনি কি ঘুমোতে পারবেন?
প্রসূনের মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, না।
– তা হলে? আর ওদের সামনে ইয়া বড় বড় এক-একটা আগুনের গোলার মতো হ্যালোজেন জ্বালিয়ে রাখা হচ্ছে। ওই প্রখর আলোর জন্য তো ওদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে। আর তার জের গিয়ে পড়ছে ওদের শরীরের ওপর। ফলনের উপর।
আর একজন স্থানীয় বাসিন্দা বললেন, সাধারণত কোথাও কারখানা হলে দূষণের ফলে শুধু কারখানার ঘেরা জমিই নয়, তার আশপাশের চাষের জমিও নষ্ট হয়ে যায়। এই তো, দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ও পাশে, মহিষটিকরিতে একটা পিচ কারখানা আছে। শীতকালে যখন হাওয়া দেয়, এত দূর থেকেও একটা বিচ্ছিরি গন্ধ ভেসে আসে। নাক রাখা যায় না।
প্রসূনের সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে যে চার-পাঁচ জনের একটা জটলা ওঁদের কথাবার্তা শুনছিলেন, তাঁদের মধ্যে এই গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকও ছিলেন। তিনি বললেন, শুধু গন্ধ না। ওই গন্ধের ভিতরে একটা ঝাঁঝালো গ্যাসও আছে। তাকালে চোখ জ্বালা করে। এমনকী কোনও কোনও বাচ্চার তো শ্বাসকষ্ট অবধি হয়। আর তার ফলে ওদের পড়াশোনারও অনেক অসুবিধে হচ্ছে।
একে একে আরও অনেকের সঙ্গেই কথা বললেন প্রসূন। স্থানীয় বাসিন্দা রামরতন বললেন, এখানকার মেয়েরা সাধারণত ঘরের কাজই করেন। কেউ মাঠে যান না। বাড়িতে কোনও পুরুষমানুষ না থাকলে কিংবা হাতের কাছে তেমন কাউকে না পেলে, খুব প্রয়োজনের সময় মাঠ থেকে হয়তো ধান কিংবা হঠাৎ বাড়িতে জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে একটু আধটু খড়বিচুলি বয়ে আনেন শুধু। আর চাষের কাজে মুনিশ এলে তাঁদের জলখাবার দিতে যান। কখনও সখনও মুনিশদের দুপুরের খাবারেরও ব্যবস্থা করেন মাঠে। ব্যস, বাড়ির বাইরে কাজ বলতে শুধু এইটুকুই। এ সব নিয়েই তাঁরা ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু এই জমি চলে গেলে পুরুষদের পাশাপাশি এঁরাও যে একদম বেকার হয়ে যাবেন।
আর এক গ্রামবাসী এগিয়ে এসে বললেন, যাঁদের বাড়িতে এ সবের বালাই নেই, তাঁদের বাড়ির অল্পবয়সি মেয়ে-বউরা আগে থেকেই কেউ কেউ ঠোঙা বানানোর কাজ করতেন। এখন অনেকেই সেই কাজের সঙ্গে সঙ্গে টিপের কাজও করছেন। টিপের কাজ মানে টিপের ওপর সূক্ষ্ম কারুকাজ করা। এক-একটা টিপের পাতায় দশ-বারোটা করে টিপ থাকে। এ রকম এক ডজন টিপের পাতায় কাজ করতে পারলেই নগদ তিন টাকা।
আরও পড়ুন: শুধু বাঁশি
যাঁরা ধর্মতলা থেকে ম্যাটাডর ভাড়া করে দল বেঁধে আঁধারগ্রামে এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই কারও না কারও সঙ্গে কথা বলে জেনে নিচ্ছেন এখানকার মূল সমস্যা থেকে একেবারে খুব ছোট ছোট সমস্যাও। কেউ উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন তো কেউ চটের উপরে বসেই কথা বলছেন। দেবব্রতর বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্থানীয় গৃহবধূ পারমিতা দাস। উনি বললেন, আগে আমাদের ঘরে ধান ছিল। ধান সেদ্ধ করা ছিল। মুড়ি ভাজা ছিল। ওগুলো সব আমরা নিজেরাই করতাম। তাতে কোনও কষ্ট ছিল না। কাজ করলে শরীর ভাল থাকে। কিন্তু সত্যি সত্যিই যদি আমাদের জমি চলে যায় তা হলে আমরা কী করব! এই দুশ্চিন্তাটাই আমাদের এখন কুরে কুরে খাচ্ছে। আমরা একদম ভাল নেই। আমাদের মনও ভাল নেই।
কথা বলতে বলতে হঠাৎ গলার স্বর ধরে এল তাঁর। কেমন যেন কান্না ভেজা গলা। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলার দিকে চোখ তুলে তাকালেন দেবব্রত। দেখলেন, তাঁর চোখের কোনায় চিকচিক করছে জল।
চলবে…