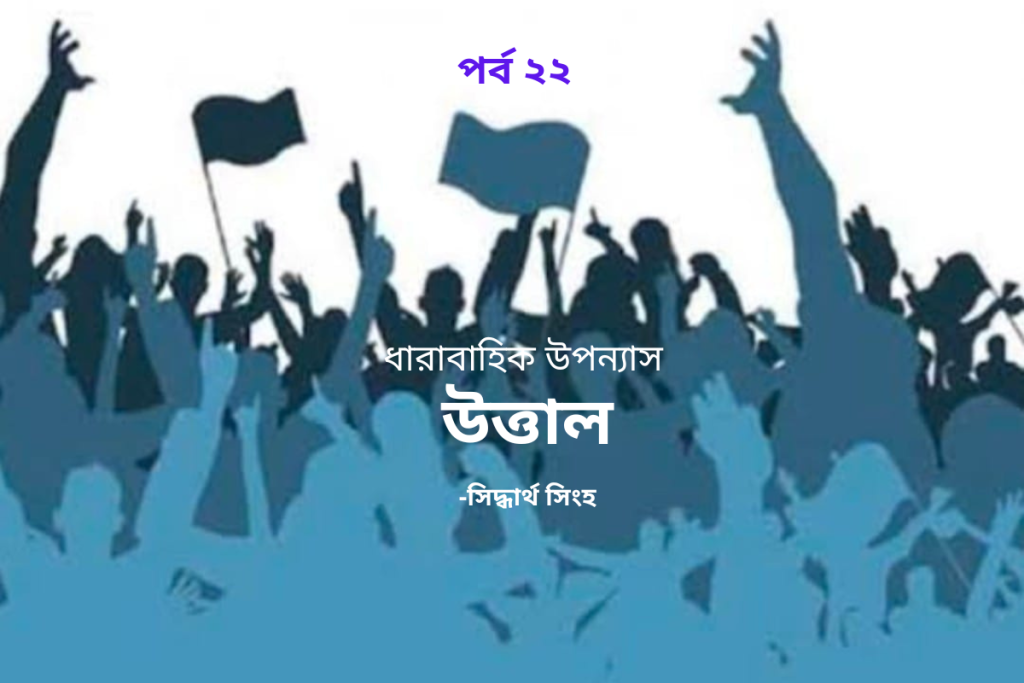।।পর্ব – বাইশ।।
হাতে অফুরন্ত টাকা আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকলে মানুষকে খুব সহজেই দমিয়ে রাখা যায়। যা ইচ্ছে করা যায়। তাদের অবহেলার কারণে মানুষের কোনও রোগ হলেও এবং সেটা প্রমাণিত হলেও সেই রোগকে অস্বীকার করা যায়, বলা যায় এই জন্য নয়, ওই জন্য হয়েছে। কিন্তু পশুদের হলে?
সেটাও শুরু হয়ে গেল মিনামাটায়। বিড়ালেরা হঠাৎ হঠাৎ বিকারগ্রস্থ হয়ে দলে দলে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করতে লাগল। সমুদ্রের বুকে উড়তে উড়তে, বৃন্ত থেকে ঝরে পড়া ফুলের মতো টুপটাপ খসে পড়তে লাগল ঝাঁক ঝাঁক পাখি।
কেন এমন হচ্ছে! রাষ্ট্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, তাদের বিরাগভাজন হয়ে, নিপ্পনের দেওয়া নানান টোপের হাতছানি উপেক্ষা করে, গোছা গোছা উপঢৌকনের প্রলোভন দু’হাতে ঠেলে সরিয়ে ফের কুমামোতো বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই গবেষকেরা এ বার জানালেন, যে-সব বিড়ালেরা ওই সমুদ্রের মাছ খেয়েছে কিংবা শরীর খারাপ লাগলেই অনেক সময় বিড়ালেরা নিজে থেকেই এক ধরনের ঘাস খায়… যে-বিড়ালগুলো সমুদ্র উপকূলবর্তী জমি থেকে ওই ঘাস খেয়েছে, তাদেরই এই দশা হয়েছে। ওই একই ভাবে, যে-পাখিগুলো সমুদ্রের কাছাকাছি জমির শষ্যখেত থেকে শষ্যদানা খেয়েছে, তারাই আকাশের বুকে উড়তে উড়তে মুহূর্তের মধ্যে চলৎশক্তিহীন হয়ে টপাটপ সমুদ্র পড়েছে।
এই রিপোর্ট ছড়িয়ে পড়তেই গোটা দেশ আবার গর্জে উঠল। শুরু হল মিটিং, মিছিল, আলোচনা সভা। মুখে কালো কাপড় বেঁধে নিঃশব্দে প্রতিবাদ, পদযাত্রা। শুধু নেতা-নেত্রীই নন, দেশের সাধারণ মানুষেরাও অথৈ জলে পড়া, অসহায় মৎস্যজীবীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন।
আন্দোলন যখন উত্তাল হয়ে উঠেছে, জাপান সরকার তখনও উদাসীন। এক্কেবারে নীরব। আক্রান্তদের জন্য কোনও রকম ক্ষতিপূরণ ঘোষণা তো করেইনি, নিপ্পন কেসসোর উপরেও জারি করেনি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের কোনও ফরমান। ফলে নিপ্পন যেমন চলছিল, সেই একই ভাবে পুরোদস্তুর উৎপাদন চালিয়ে যেতে লাগল। আর সেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে, কেউ যাতে বাধা দিতে না পারে, কোম্পানির সামনে অবস্থান-ধর্মঘট করতে না পারে, বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে, কোম্পানির চার দিকে কাতারে কাতারে রাইফেলধারী পুলিশ মোতায়েন করে দিল প্রশাসন। ফলে বহাল তবিয়তে নির্বিঘ্নে ওটা চলতেই থাকল। বন্ধ হল না সমুদ্রের জলে পড়া তাদের কোম্পানির বর্জ্য পদার্থও। উলটে ওই রোগের প্রকোপ যাতে আর না বাড়ে, সে জন্য ওই কুমামোতো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের রিপোর্ট মেনে নিয়ে মৎস্যজীবীদের উপরে জাপান সরকার লাগু করল অভিনব নিষেধাজ্ঞা– সমুদ্রে কেউ মাছ ধরতে যাবেন না। উপায়ন্ত না পেয়ে যদি কেউ যানও, ভুল করেও কিন্তু ওই সমুদ্রের মাছ কিংবা অন্য কোনও প্রাণী খাবেন না।
আরও পড়ুন: ধারাবাহিক উপন্যাস ‘উত্তাল’ ২১
সরকারি এই নির্দেশ জারি হতে না হতেই শুধু ওই এলাকারই নয়, দুর-দূরান্তের লোকেরাও সমুদ্রিক মাছ আর সামুদ্রিক জীব খাওয়া বন্ধ করে দিল। ফলে মৎস্যজীবীরা হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে মাঝ-সমুদ্র থেকে মাছ ধরে আনলেও,সেগুলো আর বিক্রি হচ্ছিল না। হঠাৎ করেই গোটা মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এক বিরাট সঙ্কটের মুখে পড়ল।
দেশের প্রথম সারির কিছু বুদ্ধিজীবী সে সময় ওঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। গান গেয়ে, ছবি এঁকে, নাটক করে, যতটা পারা যায় টাকা তুলে তাঁদের সাহায্য করতে লাগলেন। কিন্তু এ ধরনের কোনও প্রচেষ্টা পৃথিবীর কোনও দেশেই অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না। ও দেশেও চলল না। প্রথম দিকে খুব তোড়জোড় করে শুরু হলেও অল্প কিছু দিন পরেই আস্তে আস্তে তা থিতিয়ে পড়ল।
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আওয়াজ উঠল, ওঁদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যাঁরা মারা গেছেন এবং যাঁরা ওই রোগের শিকার হয়েছেন, তাঁদেরও। কত টাকা দিতে হবে, তা নির্ধারণ করতে হবে তাঁদের সঙ্গে বসে কিংবা সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনকে নিয়ে কোনও কমিটি গঠন করে। কোম্পানি ইচ্ছে মতো যৎসামান্য টাকা দিতে চাইলে তা বরদাস্ত করা হবে না।
আলোচনায় বসে ঠিক করতে হলে ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সহজেই তা অনুমান করে, খুব কমে ওই সমস্যাটাকে মিটিয়ে ফেলার জন্য কোম্পানির কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিল, যাঁকে যেমন পারবেন, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, হাতে কিছু নগদ টাকা গুঁজে দিয়ে তাঁদের মুখ বন্ধ করবেন।
আর এটা করতে গিয়েই কোম্পানি দেখল, বাহ্, দারুণ তো! প্রশাসনকে কাজে লাগিয়েও ওরা যা করতে পারেনি, বিরোধী নেতাদের সোনাবাছা করেও ওরা যা কিছুতেই করে উঠতে পারছিল না, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ বাবদ সরাসরি ‘নগদ টাকা’র সামান্য একটা চালেই কিন্তু তারা তা অনায়াসেই করতে পারল। একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ল সারা দেশ জুড়ে উত্তাল হয়ে ওঠা আন্দোলন।
যাঁরা টাকা নিচ্ছেন আর যাঁরা আরও বেশি টাকা পাওয়ার আশায় নিচ্ছেন না, তাঁদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল দ্বন্দ্ব। রেষারেষি। ভুল বোঝাবুঝি। তৈরি হয়ে গেল দুটো দল। ওঁরা এটাই চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন গোটা দেশ জুড়ে যে আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে সরকারকে, সেই আন্দোলনটাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে।
পরে কোম্পানির মতিগতি কী হবে, আদৌ কিছু দেবে কি না, তার চেয়ে অনেক ভাল এখন যা গরমাগরম পাওয়া যায়, সেটা নিয়ে সরে পড়া। সেই টাকা নিয়ে কেউ কেউ মাছ ধরা ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন অন্য কোনও গ্রামে। কেউ কেউ ওখানকারই কোনও কারখানায় কাজে লেগে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ আবার খুলে বসেছিলেন চায়ের দোকান, প্রকাশ্য রাস্তার ধারে সাজিয়ে নিয়ে বসেছিলেন মনোহারির পশরা। বাঁচার জন্য যে যাঁর মতো বদলে নিয়েছিলেন নিজেদের পেশা।
আর, যাঁদের জন্য আন্দোলন, যাঁদের নিয়ে আন্দোলন, তাঁরা টাকা নিয়ে একে একে সরে পড়তেই আন্দোলনটাও কমজোরি হতে লাগল। এবং এক সময় একেবারেই ঠান্ডা হয়ে গেল। এর ফলে যাঁরা নানান রাজনৈতিক নেতাদের আশ্বাসে, আরও বেশি টাকা পাওয়ার স্বপ্নে তখন টাকা নেননি, দেখা গেছে, উনিশশো তিরানব্বই সালেও, তাঁরা একটি পয়সাও পাননি। অনেকেই টাকার জন্য দিন গুনতে গুনতে মারা গেছেন। আর যাঁরা বেঁচে আছেন, খুনখুনে বয়সেও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আশায় বুক বেঁধে পথ চেয়ে আছেন। তাঁদের সংখ্যা তখনও নয় নয় করেও অন্তত চল্লিশ হাজার।
পরবর্তিকালে পৃথিবীর আর যেখানেই ওই জাতীয় কারখানার আশপাশে ওই রকম উপসর্গ বা রোগ দেখা দিয়েছে, লোকজন তাকে চিহ্নিত করেছে ‘মিনামাটা রোগ’ নামে। কোনও অঞ্চলের নামে কোনও রোগের নামকরণ সম্ভবত সে-ই প্রথম।
ব্রাজিলেও গড়ে উঠেছিল– ক্যুবটাও। যাকে বলা হত– কেমিক্যাল ক্যাপিটাল অব ব্রাজিল। যা মাত্র ক’দশকের মধ্যেই ওই অঞ্চলটাকে পরিণত করেছিল একেবারে মৃত্যু উপত্যকায়।
আরও পড়ুন: রাসসুন্দরী দেবী
ওই সব দেখেশুনে অনেক দিন আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের নিজেদের দেশে ওই ধরনের রাসায়নিক শিল্পের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করেছিল। তারা বলছিল, তাদের দেশে যে-কোনও কেমিক্যাল অনায়াসে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু বেশ কিছু নির্ধারিত কেমিক্যাল, তাদের দেশের মাটিতে উৎপাদন করা যাবে না। যদিও অন্য বেশ কয়েকটি উন্নত দেশ রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য তাদের দেশে ছাড়পত্র দিয়েছে। অবশ্য তার পাশাপাশি তারা বেশ কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন যে শুধু নিষিদ্ধই করেছে বা কিছু কিছু যৌগর উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করছে, তা-ই নয়, যেগুলো উৎপাদন করার অনুমতি দিয়েছে, সেই সব শিল্প থেকে নির্গত বর্জ্যে বিষাক্ত উপাদানের পরিমাণের ওপরও রাখছে কড়া নজরদারি। তাই সব মিলিয়ে উন্নত দেশগুলোর বেশির ভাগ দেশেই কেমিক্যাল শিল্পটাকে টিকিয়ে রাখা ব্যবসায়ীদের কাছে এখন একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
কারণ, নিরাপদ আর নিরাপত্তার হাজার একটা নিয়মকানুন মেনে ওই সব কেমিক্যাল উৎপাদন করা যে একেবারেই অসম্ভব, তা নয়। কিন্তু ওগুলো নিয়ম অনুযায়ী ঠিকঠাক মতো করতে গেলে তা হবে প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। সে খরচ এতটাই বেশি যে, ওই সব দ্রব্যের এমনিতে যা দাম হয়, ওই সতর্কতামূলক পদ্ধতিতে তৈরি করতে গেলে তার দাম পড়ে যাবে অন্তত তার একশো গুণ। ফলে যে দেশের লোকের হাতে বিপুল টাকা আছে, তাঁরাও ওই দ্রব্যটি আদৌ ব্যবহার করবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।
তাই বেশ কয়েক দশক ধরেই আন্তর্জাতিক বৃহৎ বাণিজ্য সংস্থাগুলো নজর দিয়েছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দিকে। যে দেশের লোকেরা অতটা স্বাস্থ্য সচেতন নন এবং যেখানে দূষণ নিয়ে কারও কোনও মাথা ব্যথা নেই। না-সরকারের। না-জনগণের। আর যা রাতারাতি পালটে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনাও নেই। তারা জানে, সেই সব দেশের রাজনৈতিক মাথাদের কিনে এবং জনসাধারণকে সেখানে চাকরির লোভ দেখিয়ে খুব সহজেই এই ধরনের কারখানা গড়ে তোলা যায়। আর একবার কারখানা গড়ে উঠলেই, তাদের গায়ে কোনও আঁচড় পড়বে না। সেখানকার জমি, জল আর নামমাত্র শ্রমে উৎপাদিত হতে থাকবে ওই সব কেমিক্যাল। তারা শুধু পুঁজি, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আর কাঁচামাল সরবরাহ করবে। আর উৎপাদন হওয়ার পরে ওই সব দেশ থেকেই সরাসরি তা চালান হয়ে যাবে আন্তর্জাতিক বাজারে। ধনী দেশগুলোতে। এমনকী তাদের দেশেও। যারা নিজেদের দেশ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন এবং পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে একেবারে মরিয়া।
নবীন মাস্টার কী করে যেন খবর পেয়েছিলেন, সে রকমই একটি কেমিক্যাল কোম্পানি গড়ে তোলার জন্য খুব ভাল একটা অফার পেয়েছে এই রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছেন, তাঁরা ‘কেমিক্যাল হাব’ গড়তে চলেছেন।
‘কেমিক্যাল হাব’ শব্দটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো কারণে। প্রথমত, এটা শুনতে বেশ ভারী। গাল ভরা নাম। দ্বিতীয়ত, নতুন এই শব্দটার মধ্যে একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করে মূল বিষয়টাকে সবার কাছ থেকে খুব সহজেই আড়াল করা যায়। ‘কেমিক্যাল’ শব্দটা পরিচিত। সকলেই প্রায় জানেন। আর ‘হাব’ কথাটাও অল্পবিস্তর অনেকেই জানেন। কিন্তু ওই পৃথক পৃথক শব্দ দু’টি জুড়ে যে শব্দটি তৈরি করা হয়েছে, সেটার মানে কিন্তু বেশিরভাগ লোকই জানেন না। ‘কেমিক্যাল হাব’ মানে কী? ওটা কি খায়? না, মাথায় মাখে? ওটা আসলে কী? কোথায় তৈরি হচ্ছে ওটা? তাও জানতে পারলেন না কেউ। কেউ শুনলেন, কেমিক্যাল হাব হবে নয়াচরে। কেউ শুনলেন, হলদিয়ায়। আবার কেউ শুনলেন, একেবারে অন্য একটি জায়গার নাম। কিন্তু কোথায় হবে কেউ জানেন না।
সেটা জানার জন্যই নবীন মাস্টার হাজির হয়েছেন হলদিয়ায়। তাঁর সঙ্গে আঁধারগ্রামের সেই তেরো নম্বর।
চলবে…