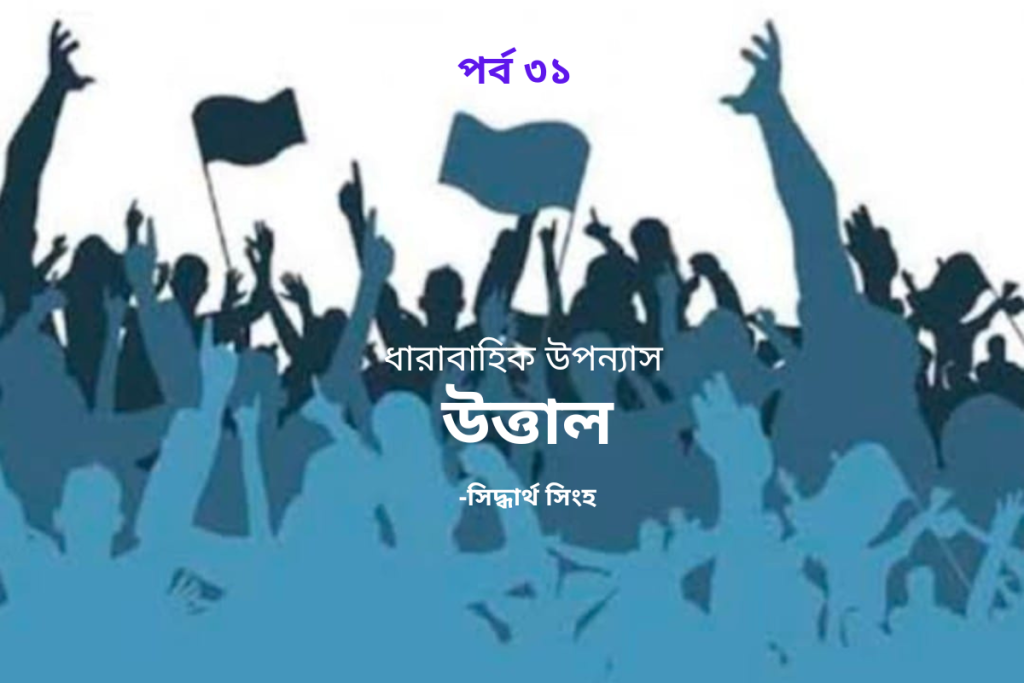।। পর্ব – ৩১।।
আঁধারগ্রামে কী কী ঘটছে, খবরের কাগজ, টিভি আর ফোনের মাধ্যমে খুঁটিনাটি সবই জানতে পারছিল তেরো নম্বর। জানতে পেরেছিল, ২০০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর সাদ্দামের জন্য নীরবতা পালন। ১৪৪ ধারা বাড়ানোর প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিকে চিঠি পাঠানো। পর দিন সারা গ্রাম জুড়ে মিছিল। ২০০৭-এর ১ জানুয়ারি আঁধারগ্রাম দিবস পালন। একই সঙ্গে কৃষক দিবস পালন। এবং তার পর থেকে এক এক দিন এক একটি দলের আঁধারগ্রাম যাত্রা। মানিক দাসের বাড়িতে হামলা। কিন্তু তার পক্ষে তখন তার জন্মভিটেয় যাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। কারণ, নবীন মাস্টারের সঙ্গে সে-ই যে সে হলদিয়ায় এসেছিল, কেমিক্যাল হাব করার নামে ইন্দোনেশিয়ার বহুজাতিক শিল্প সংস্থা সালিম গোষ্ঠীর হাতে ঠিক কোন জায়গাটা সরকার তুলে দিচ্ছে, তা জানার জন্য, তার পর সেই নিয়ে নানা কাজে জড়িয়ে পড়ায় তার আর আঁধারগ্রামে যাওয়া হয়নি। ওরা ঠিক করেছিল, কেমিক্যাল হাব করার জন্য সরকার যদি সত্যিই ওদের জমি দেয়, তা হলে যে ভাবেই হোক, ওই মারণ কারখানা যাতে শুধু ওখানে কেন, এ রাজ্যের কোথাও ওরা তৈরি করতে না পারে, সে জন্য যা যা করার, তারা করবে। তাই তারা নাওয়া-খাওয়া ভুলে আগাম জনমত গড়ে তোলার জন্য এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, আঁধারগ্রামে ও রকম কাণ্ড ঘটছে জানতে পেরেও তারা সেখানে যেতে পারেনি।
একজনের বাড়িতে ঘরোয়া মিটিং করে ফেরার পথে তেরো নম্বর বলেছিল, আঁধারগ্রাম এখন উত্তাল। এ সময় ওদের পাশে না থাকলে কী থেকে কী ঘটবে, কিচ্ছু বলা যায় না।
নবীন মাস্টার তখন ওকে বুঝিয়েছিলেন, কেউ যদি কাউকে ক্রমাগত মেরে যায়, তা হলে যে মার খাচ্ছে, তাকে বারবার বাঁচানোর চেয়ে, তাকে একা একা লড়তে শেখানোটা অনেক বেশি জরুরি কাজ। সেটা তুমি ইতিমধ্যেই করে ফেলেছ। ওখানে আর কেউ একা নয়, সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে লড়ছে। আজ না হোক কাল, ওরা ঠিক জিতবেই। এটা আমার কথা না। এটা ইতিহাস বলছে। কিন্তু যে অঘটন এখানে ঘটতে চলেছে, সেটা যদি সতিই ঘটে, তা হলে এ রাজ্যে মহাবিপর্যয় ঘটে যাবে। অসংখ্য মানুষ তিলে তিলে মারা যাবে।
আসলে এই সরকার সরাসরি মুখে না বললেও, তাদের হাবভাব বলছে, ভাল কথায় জমি দিলে দাও, না হলে কেড়ে নেব। এলাকা ঘিরে মানুষের ‘লাইফ হেল’ করে দেব।
বোঝাই যাচ্ছিল না, সরকার ঠিক কী করতে চাইছে। এ বিষয়ে এলাকার লোকজনও ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে। এখানে লক্ষণীয়, অধিগ্রহণের জন্য চিহ্নিত জমির মালিক এবং সেই জমির আশপাশের লোকজনদের নিয়ে কিন্তু কোনও জনশুনানির ব্যবস্থা করা হয়নি। যা এই ধরনের শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে প্রায় বাধ্যতামূলক। ওখানে কী কী জিনিস উৎপাদন হবে, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রের ওপর তার সম্ভাব্য প্রভাব কী, দুর্ঘটনা ঘটার কোনও সম্ভাবনা আছে কি না, থাকলে তা কতটা মারাত্মক, কিছুই জানানো হয়নি। এ ছাড়া স্থানীয় মানুষকে সচেতন করা, প্রকল্পটি সম্পর্কে অবহিত করা, এমন একটা শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠলে এলাকার লোকজনদের কী কী উপকার হবে, বিনিময়ে তাদের কতটা খেসারত দিতে হবে– সে সব কিছুই জানায়নি এই সরকার।
এই ধরনের বিপজ্জনক শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো আশপাশের মানুষকে জানানো যে কতটা প্রয়োজন, তা বোঝার জন্য ভূপালের ‘ইউনিয়ন কার্বাইড’ কারখানার মর্মান্তিক দুর্ঘটনাই যথেষ্ট।
ভূপালের মানুষ জানতেনই না, শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে, একটা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায়, কীটনাশক তৈরির একটা করাখানা এমন বিপজ্জনক ভাবে আছে। জানতেন না, ওখানে কী কী তৈরি হয়। জানতেন না, এর আগেও এই কারখানায় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় শ্রমিক মৃত্যুর ইতিহাস। জানতেন না, দুর্ঘটনা ঘটলে ঠিক কী কী করণীয়। পরে ওখানকার আক্রান্তরা জেনেছেন, গ্যাস লিক করে ঘটা ওই দুর্ঘটনাটির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা যদি এমনিই কয়েক বার চোখে জলের ঝাপটা দিতেন, তা হলেই শতকরা অন্তত আশি ভাগ মানুষ নিজেদের চোখ বাঁচাতে পারতেন। জেনেছেন, কিন্তু অনেক পরে। ততক্ষণে তাঁদের বেশির ভাগ লোকেরই চোখের দফারফা হয়ে গেছে।
তাই আজকে যে কোনও শিল্প স্থাপনেরই অপরিহার্য অঙ্গ এলাকার মানুষকে প্রকল্পটি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানানো। সমস্ত উন্নত দেশে এটা বাধ্যতামূলক। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সবের ধারই ধারে না। ফলে যে ভাবেই হোক এটা আমাদের আটকাতেই হবে। তার আগে জানতে হবে, হাব করার জন্য ওরা ঠিক কোন জায়গাটাকে চিহ্নিত করেছে।
বেশি দিন লাগেনি, ওখানে যাওয়ার মাত্র ক’দিনের মধ্যেই বিভিন্ন সূত্র থেকে ওরা জেনে গিয়েছিল, সুতাহাটে ৪৫টি, হলদিয়ায় ৩০টি, মহিষাদলে ৪০টি, নন্দকুমারে ৭টি, কাঁথি হরিপুরে ৪০টি, বারুইপুরে ৩৫টি, মগরাহাটে ১২৩টি, ফলতায় ২৭টি, রায়চকে ২০টি, ভাঙড়ে ২০টি, নন্দগ্রামে ৩৮টি গ্রামের মতো হলদিয়ার খুব কাছে, হলদি নদীর ও পারে, গাছে গাছে ছাওয়া মনোরম জায়গা– খেজুরির ৫টি গ্রামও অধিগ্রহণের জন্য চিহ্নিত করেছে সরকার। সব মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার একরেরও বেশি জমি শিল্পায়ন ও উন্নয়নের নামে পুঁজিপতিদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিতে চায় ওরা। এতে যে দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবী মানুষ একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে, তা বুঝতে পেরেও, তাদের হাত এতটুকু কাঁপছে না। শোনা যাচ্ছে, এর মধ্যে আশি হাজার একর জমিই তুলে দেওয়া হবে শুধু সালিম গোষ্ঠীর হাতে।
ইতিমধ্যেই হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরকারি লোকজনদের প্রাথমিক আলোচনাও হয়ে গেছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের ২৭টি মৌজা এবং হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা সীমানার বাইরে খেজুরি ব্লকের সাহেবনগর মৌজার জে এল নম্বর ৪৭ এবং ৪৮ নম্বরের জমিতে গড়ে তোলা হবে কেমিক্যাল হাব, একটা জাহাজ মেরামতি ও জাহাজ নির্মাণ কারখানা। এ ছাড়াও রয়েছে বন্দর উন্নয়ন করার প্রকল্প। তাই জমি অধিগ্রহণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার উঠেপড়ে লেগেছে। এটা জানতে পেরেই নবীন মাস্টার এবং তেরো নম্বর আর কালবিলম্ব করেনি। সোজা চলে গেছে নন্দীগ্রামে। তার আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের ২০০৪-এর রিপোর্ট থেকে ওরা জেনে নিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের এক নম্বর ব্লকের আয়তন ১৮১.৮৪ বর্গ কিলোমিটার। সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত আছে দশটি। মোট মৌজার সংখ্যা নিরানব্বই। জন সংখ্যা ১,৭৪,৬৬৫। ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র একটা। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র দুটো। একটি মহম্মদপুরে আর একটি মহেশপুরে। প্রাথমিক বিদ্যালয় একশো বাইশটি। আর শুধু কৃষিজমিই আছে ১২,৮০০ হেক্টর।
এ সব জানার পর এর কাছ থেকে ওর কাছ থেকে, এই দফতর থেকে ওই দফতর থেকে, একে তাকে ধরে, কোনও রকমে ওরা জেনে নিয়েছে প্রস্তাবিত সেজ এলাকায় নন্দীগ্রামের ৩৮টি মৌজার ১৯,১৯৬.৩৯ একর জমি সরকারের তরফ থেকে অধিগ্রহণ করার কথা। যদি সত্যিই অধিগ্রহণ করা হয়, তা হলে পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে এখান থেকে উঠে যেতে হবে এত দিন ধরে বসবাস করা অন্তত পনেরো হাজার পরিবারকে। অর্থাৎ কমপক্ষে প্রায় সত্তর হাজার মানুষকে। ভেঙে ফেলতে হবে ১২৭টি প্রাথমিক, ৪টি মাধ্যমিক ও ৩টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়াও ৩টি মাদ্রাসা। ধূলিসাৎ করে দিতে হবে ১১২টি মন্দির, ৪২টি মসজিদ, অনেকগুলো কবরস্থান, শ্মশান, অগুনতি ঘরবাড়ি আর দোকানপাট।
ওখানকার লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে ওরা জেনেছে, নন্দীগ্রামের জন সংখ্যার প্রায় শতকরা সত্তর জনই হয় প্রান্তিক চাষি নয়তো খেত মজুর। কিন্তু তাঁদের বেশির ভাগেরই কোনও পাট্টা নেই। তবু জানপ্রাণ লড়িয়ে তাঁরা চাষ করেন। ওখানে মূলত আমন ধানটাই বেশি হয়। ধান ছাড়াও রয়েছে পর পর অসংখ্য পানের বরজ। সার সার নারকেল বাগান। শাক-সবজির খেতও প্রচুর। আর হলদি নদীর পার ধরে যে পাঁচ-ছ’হাজার মানুষের বাস, তাঁদের একমাত্র জীবিকা– মাছ ধরা।
তাঁদের কথা ভেবে তেরো নম্বরের বুক হুহু করে উঠল। এঁদের যদি এখান থেকে সব কিছু ছেড়েছুড়ে চলে যেতে হয়, তা হলে তাঁরা খাবে কী? করবেই বা কী? তাঁদের সঙ্গে কথা বলে ও বুঝেছে, চাষ ছাড়া তাঁরা আর অন্য কোনও কিছুই করতে জানে না। সরকার তাঁদের জমি নিয়ে নিলে তার বিনিময়ে তাঁরা পাবেই বা কী? আদৌ কিছু পাবে কী?
সরকারের জমি অধিগ্রহণ আইনে ক্ষতিপূরণের কথা বলা আছে ঠিকই, সেই আইন অনুযায়ী জমির মালিক, নথিভুক্ত বর্গাদার এবং জবরদখলকারীরাও কিছু টাকা পাবেন। কিন্তু ওই জমির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এলাকার বা বাইরে থেকে আসা খেতমজুর, মালবহনকারী, ভ্যানচালক, কুটিরশিল্পী, হাঁস-মুরগি-ছাগল-গরু প্রতিপালন যাঁদের পেশা, তাঁরা কিছুই পাবেন না। আর যাঁরা ক্ষতিপূরণ পাবেন, তাঁরাও খুব একটা লাভবান হবেন না। কারণ, বিকল্প জীবিকার সন্ধান করার আগেই, সংসার চালাতে গিয়ে তাঁদের মুষ্টিমেয় সেই টাকা খরচ হয়ে যাবে। ফলে তাঁরা বেশির ভাগই কার্যত ছিন্নমূল জীবিকাচ্যুততে পরিণত হবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জমি অধিগ্রহণ হলে জমির মালিকদের জীবিকার অধিকারের ওপরেও পরোক্ষ ভাবে নেমে আসে হস্তক্ষেপ। তা ছাড়া তাঁদের আগের অভিজ্ঞতাও যে অত্যন্ত খারাপ।
তাঁদের মুখেই তেরো নম্বর আর নবীন মাস্টার শুনেছে, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে-পরেই, মানে, ১৯৭৬-‘৭৭ সালে গ্যাংড়াচর মৌজার বাস্তু আর কৃষিজমি মিলিয়ে মোট ২৫৬ একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল। বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানিকে দিয়েছিল ‘জেলিংহাম’ প্রজেক্ট গড়ে তোলার জন্য। মহাধুমধাম করে সেটা শুরুও করেছিল তারা। কিন্তু মাত্র দশ বছর বাদেই কোনও কারণ না দেখিয়েই মালিকপক্ষ সেটা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু যাঁরা জমি দিয়েছিলেন, এই তিরিশ বছর পার হয়ে যাওয়ার পরেও সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁরা তো ওই কারখানায় কোনও কাজ পানইনি, পাননি কোনও পুনর্বাসনও। যাঁরা ভেবেছিলেন, ওই কারখানা গড়ে উঠলে, তার আশপাশে গড়ে উঠবে আরও অনেক অনুসারী শিল্প, অন্তত বেশ কিছু মানুষ করে-কম্মে খেতে পারবেন, তাঁদের সেই আশায় ছাই চাপা পড়ে গিয়েছিল। এমনকী বারো বছর আগে হলদি নদীতে বাঁধ দেওয়ার জন্য নদীর পার বরাবর যে বিপুল জমি প্রায় জোর করে সরকার কেড়ে নিয়েছিল, তারও কোনও ক্ষতিপূরণ আজও পাননি ওখানকার চাষিরা।
আর পড়ুন: ধারাবাহিক উপন্যাস ‘উত্তাল’ (ত্রিশ)
শুধু কি ওঁরাই ক্ষতিপূরণ পাননি? নাকি, ওঁদের মতো এই রাজ্যের আরও অনেকেই সমান ভুক্তভোগী? অনুসন্ধান করতে গিয়ে নবীন মাস্টার যেমন জেনেছেন, তেরো নম্বরও এত দিনে তাঁর সঙ্গে থেকে থেকে, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে জেনে গেছে, শুধু আঁধারগ্রাম বা নন্দীগ্রামেই নয়, যেখানেই জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, সেখানেই এই একই ছবি। কোনও প্রতিশ্রুতিই সরকার কোথাও পালন করেনি। চাকরি নিয়ে, ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে, এই দেব, সেই দেব, গাল-ভরা নানা কথা বলে, শুধু টালবাহানাই করে গেছে। আর সেটা নিয়ে হইচই হলেই ওটা থেকে চোখ সরাতে অন্য আর একটা ঘটনা তৈরি করেছে এই সরকার। সর্বত্র প্রতারণা করেছে এরা। যেমন করেছে রাজারহাটে।
রাজারহাটের জমি নেওয়ার সময় প্রতি কাঠা জমির জন্য সরকারের তরফ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ চাষিদের দেওয়া হয়েছিল তেরো হাজার ছ’শো পঞ্চাশ টাকা। অথচ সরকার সেই জমি বিক্রি করেছিল কাঠা পিছু এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা করে। বর্ধমানের নবহাটে বাস টার্মিনাস প্রকল্পে ১০ টাকা বর্গফুট দরে জমি অধিগ্রহণ করে, সেটা ‘উন্নয়ন ও নির্মাণে’ প্রায় ৬০০ টাকা প্রতি বর্গফুটে খরচ দেখানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তা বিক্রি করা হয়েছে ৩০০০ টাকা প্রতি বর্গফুট। ১০ টাকা দরে কিনে, যতই বাড়িয়ে বলুক, ওদের হিসেব অনুযায়ী সরকার খরচ করেছে আরও ৬০০ টাকা যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই, তা হলেও প্রতি বর্গফুটে সরকার লাভ করেছে কম পক্ষে ২৩৯০ টাকা। শোনা গেছে, আঁধারগ্রামের ১০০০ একর জমির জন্য প্রায় ৩১৪ কোটি টাকা অর্থাৎ বিঘা পিছু দশ লাখেরও কিছু বেশি টাকা দেবে টাটারা। কিন্তু সরকারি ঘোষণা মতো চাষিরা পাবেন বিঘা পিছু মাত্র দু’লাখ টাকা। মানে, মাঝখান থেকে সরকার খেয়ে নেবে বিঘা পিছু আট লাখ টাকা। কেন? কেন জমির মালিকদের এই ভাবে ঠকানো হবে? তখন না হলেও, পরে কি আরও কিছু টাকা দিয়ে তাঁদের পুষিয়ে দেওয়া যেত না? রাজারহাটে তো এখন ঝকঝকে তকতকে টাউনশিপ তৈরি হয়েছে। কিন্তু যাঁদের জমি নিয়ে ওই টাউনশিপ গড়ে উঠেছে, তাঁরা এখন কোথায়!
রায়চকেও তাই। সরকারি সহায়তায় জলের দরে একের পর এক জমি কিনে এক শিল্পপতি তো সেখানে বহুতল আবাসন তৈরি করছেন। যাঁরা শাড়ির সঙ্গে রং মিলিয়ে নিত্যনতুন গাড়ি কেনেন, এ রকম বহু বিখ্যাত ধনী পরিবার সেখানে শুধুমাত্র আনন্দফুর্তি করার জন্য বাগানবাড়ি বানাচ্ছেন। আর যাঁরা সেখানকার ভূমিপুত্র, সরকারের চাপের মুখে পড়ে সামান্য ক’টা টাকায় জমি বেচে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই টাকায় তাঁদের এক বেলাও ঠিক মতো খাবার জোটে না। তাঁদের কেউ কেউ এখন শহরের উপকণ্ঠে কোনও কারখানায় ‘অনভিজ্ঞ মজুর’ হিসেবে সাপ্তাহিক মজুরিতে কাজ করছেন। আবার কেউ কেউ নিজেদের জমিতেই বাবুদের বাগানের মালি হিসেবে কিংবা মাস মাইনের দারোয়ান হিসেবে কাজ করছেন। আর বাকিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। যেমন বহু মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন খড়াপুর, ভাঙড়, উলুবেড়িয়া কিংবা উত্তরবঙ্গের নানান জেলা থেকে।
কোথায় যাবেন তাঁরা? ক’জায়গায় ছুটবেন? সব জায়গায় যে একই ছবি। সেই চা-বাগানের খবর এখন আর ক’জন রাখেন? উন্নয়নের নামে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া সেখানকার শ্রমিকরা এখন এই প্রবল শীতের মধ্যে ঝুপড়ির অন্ধকারে বাস করছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বউ-ছেলেমেয়েদের মুখে দুটো ভাত তুলে দিতে না পেরে, প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের জন্য সকাল বিকেল সরকারি কর্তাদের টেবিলে টেবিলে হত্যে দিয়ে, না পেয়ে অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।
এই তো কিছু দিন আগে উলুবেড়িয়ায় সস্তায় মোটর সাইকেল তৈরি করার জন্য সালিম গোষ্ঠীকে জমি দিয়েছিল সরকার। বলেছিল, বহু লোকের চাকরি হবে। কিন্তু আসলে কী হয়েছে সেখানে? না, কিচ্ছু না। উলটে, যাঁরা ওই জমিতে সোনা ফলাতেন, সেই সব কৃষকরাই ওই সব কোম্পানির ঠিকে কাজের লোক হয়ে দৈনিক মজুরিতে দিন গুজরান করছেন। লরি বোঝাই থার্মাল অ্যাশ, মানে ছাই ফেলে ফেলে নিজেদের হাতে তৈরি জমি নিজেরাই বন্ধ্যা করে দিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত সেই ঘেরা জমিতে শিল্প গড়ে ওঠার কোনও চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। ওখানকার মানুষও জানেন না, সালিমদের সস্তার মোটর সাইকেল ‘অর্জুন’ আদৌ আলোর মুখ দেখবে কি না। তাঁদের কারও চাকরি ওখানে হবে কি না। অথচ ওই জমিটি ঘেরার ফলে সেচের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাশের খালটি একেবারে অকেজো হয়ে গেছে। তাই যে সব জমি অধিগ্রহণ হয়নি, সেখানকার চাষিরাও সেচের জল না পাওয়ার জন্য এই ক’দিন আগেও যেখানে তাঁরা সোনা ফলাতেন, সেখানে তাঁরা চাষই করতে পারছেন না। কী করবেন তাঁরা?
সল্টলেকের কথাই ধরা যাক। সেখানে যাঁরা কৃষিজীবী ছিলেন, তাঁরা বছরে প্রায় দু’লক্ষ বত্রিশ হাজার মন ধান ফলাতেন। ওখানে যাঁরা মৎস্যজীবী ছিলেন, তাঁরা মূলত রাজবংশী সম্প্রদায়ের। তাঁরা বছরে প্রায় এক লক্ষ ঊনষাট হাজার মন মাছ ধরতেন। ওঁদের মধ্যে যাঁরা এখনও বেঁচে আছেন, তাঁদের মধ্যে হাতে গোনা মাত্র কয়েক জন লোক সরকারি ভেড়িতে কাজ পেয়েছেন। বেশির ভাগ লোকই, হয় রাজমিস্ত্রির কাজ করছেন, না হলে রিকশা টানছেন। কেউ কেউ আবার বেঁচে থাকার জন্য ওখানকার বড়লোকদের বাড়িতে ‘ঝি’, ‘চাকর’-এর কাজ করছেন। কেউ কেউ রাস্তার ধারে ছোটখাটো চায়ের দোকান কিংবা পান-বিড়ির দোকান খুলে বসেছেন। আর একচল্লিশ শতাংশ মানুষই পেটের দায়ে, সংসার চালানোর জন্য নানা ধরনের বেআইনি ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছেন। আর তাঁদের সন্তানেরা বাবা-মায়েদের দুর্দশা দেখে অনেক ক্ষেত্রেই দুটো কাঁচা পয়সার মুখ দেখার জন্য অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।
সবাই জানেন, কোনও কারণে কৃষিজমি একবার শিল্পস্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হলে, সেই জমি আর চাষযোগ্য থাকে না। হয়তো অভিমান করে জমি নিজেই নিজেকে বন্ধ্যা করে দেয়। তাই আইনে আছে, উন্নত কৃষিজমিকে কোনও ভাবেই অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এমনকী, চাষের জমিতে বসতি গড়ে তোলাটাও বেআইনি। কিন্তু কে শুনছে কার কথা! আসলে ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর টাকা। সেটা তারা এমনি এমনি ফেলে রাখতে চায় না। কারণ, টাকা ফেলে রাখলে টাকা কখনও ডিম পাড়ে না। তাই তারা সেই টাকা যতটা পারা যায় লগ্নি করতে চায়। তারা চায় এমন জায়গায় লগ্নি করতে, যেটা থেকে মুনাফা হবেই। যেমন– ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, এক্সপ্রেসওয়ে, ফ্লাইওভার, মাল্টিপ্লেক্স, শপিং মল, সিনেমা বা টিভির ধারাবাহিক নির্মাণ, নার্সিংহোম, বেসরকারি বিলাসবহুল চিকিৎসাকেন্দ্র। সব সুযোগ-সুবিধে সমেত বড় বড় হোটেল, রিসর্ট, চা বাগান। আর অবশ্যই বড়লোক আর গরিবদের কথা মাথায় রেখে পৃথক পৃথক মাপ, কাঁচামাল এবং জায়গা অনুযায়ী তৈরি আবাসন।
যাদের হাতে অফুরন্ত টাকা আছে, তাদের কথা ভেবেই সরকার বলছে, কারখানা তৈরি হলে কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু একবারও ভেবে দেখছে না, কারখানায় যা উৎপাদন হবে, সেটা কিনবে কে? যেখানে এ রাজ্যে ৫৬ হাজার কলকারখানা বন্ধ। ১৭ লক্ষ লোক ছাঁটাই হয়ে গেছে। ৭০ লক্ষ শিক্ষিত ছেলে একেবারে বেকার হয়ে বসে আছে। কারখানায়-কারখানায় চলছে লে-অফ, লক আউট। সুযোগ পেলেই শ্রমিক অসন্তোষের ছুতো দিয়ে কারখানার গেটে তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে মালিকপক্ষ। ফলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কর্মচারীদের রোজগার। সুতরাং লোকজন যেখানে দু’বেলা খাবারের টাকাই জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছেন, সেখানে বিভিন্ন কোম্পানির উৎপাদিত জিনিস তাঁরা কিনবেন কী করে? তবু সরকার বলছে, আমরা কারখানা গড়ব। কিন্তু কারখানা করতে গেলে তো জমি দরকার। জমি তো আর আকাশ থেকে পড়ে না। পাতাল থেকেও উঠে আসে না। আর একলপ্তে অতখানি জমি পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। ফলে কারখানা গড়তে গেলে কৃষিজমি নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কে তাদের বলবে, শিল্প যেমন আকাশে হয় না, চাষও আকাশে হয় না। তার জন্য দরকার শুধু জমি নয়– উর্বর জমি। আপনারা ওই জমি নিচ্ছেন। কেন?
যতই বিতর্ক উঠুক, হইচই হোক, সরকারের এই নতুন নতুন কারখানা গড়ার পদক্ষেপে পুঁজিপতিরা কিন্তু খুশিতে একেবারে ডগমগ। তাঁরা জানেন, জমিই সব। এই জমির জন্যই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল। এই জমির জন্যই নিজের বাবা সাজাহানকে নজরবন্দি করেছিলেন ঔরঙ্গজেব। এই জমির জন্যই বারবার অন্ধকার নেমে আসে মানব সভ্যতায়। ঘটে পরমাণু বিস্ফোরণ। আজ এত বছর পরেও তা এতটুকুও পালটায়নি। তবে এখন আর কেউ দেশ দখল করতে যান না। যান বাজার দখল করতে। যে যে-পণ্য তৈরি করেন, তিনি চান গোটা দুনিয়া জুড়ে তাঁর সেই পণ্য বিক্রি হোক। তার জন্য যা যা করণীয়, তা করতে তাঁরা এতটুকুও পিছ-পা হন না।
কিন্তু যে কোনও পণ্য তৈরি করার জন্যই লাগে কারখানা। আর কারখানা গড়ার জন্য লাগে জমি। ফলে কারখানার জন্য যতটা দরকার, বুঝিয়ে-সুজিয়ে, ভুজুংভাজুং দিয়ে, সরকারি কর্তাদের নানা উপঢৌকন দিয়ে, তার থেকে অনেক অনেক বেশি জমি সরকারের কাছ থেকে নিয়ে এক-একটা বৃহৎ পুঁজিপতি সংস্থা ভবিষ্যতে কারখানা বাড়ানোর কথা মাথায় রেখে আপাতত ফেলে রাখছে।
আর যাঁদের জমি নিয়ে এই ভাঁওতাবাজি চলছে, তাঁদের শেষ পরিণতি কি শুধুই মৃত্যু? পিছু হটতে হটতে একদম কিনারে গিয়ে খাদে পড়ে যাওয়া? এঁদের পাশে গিয়ে কি সে বা নবীন মাস্টারের মতো আর একজনও গিয়ে দাঁড়াবে না! এই সরকারের প্রধান শরিক দলের সবাই কি একই রকম? দলের নির্দেশে প্রতিটি ইঞ্চি মেপে মেপে পা ফেলেন?
না, সবাই যে একই রকম নয়, তাদের মধ্যে কারও কারও বুকের গভীরে এখনও যে মনুষত্ব উঁকি মারছে, তারই জলজ্যান্ত প্রমাণ– সি পি এমেরই এক সাংসদ, শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়। রাজ্য সরকার যখন জমি নেওয়ার জন্য মরিয়া, তখন তিনি তাঁর দলবল নিয়ে ২০০৬ সালের ১৪ জুন হুগলির জেলাশাসকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে এলেন একটা স্মারকলিপি। তাতে বলা হল, হিন্দমোটর কারখানা যতটা জমির ওপর রয়েছে, তার দু’গুণেরও বেশি, মানে প্রায় সাতশো পঞ্চাশ একর জমি সরকারের কাছ থেকে, বলতে গেলে প্রায় বিনে পয়সায় নিয়ে পঞ্চান্ন বছরেরও বেশি সময় ধরে ফেলে রেখেছে। এবং তার সঙ্গে এও জানানো হল, ওই জেলায় প্রায় কয়েকশো কারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। সেই সব কারখানার জমি হিসেব করলে কয়েক হাজার একর হয়ে যাবে।
যাঁরা সত্যি সত্যিই কারখানা বা কোনও ফ্যাক্টরি করতে চান, যদি বোঝা যায় সেখানে শুধু খাতায়-কলমে নয়, বাস্তবে সত্যি সত্যিই আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থান হবে, তা হলে তাঁদের কারখানা করার জন্য নতুন করে কৃষিজমি অধিগ্রহণ না করে, ওই সব বন্ধ কলকারখানা কিংবা চালু কারখানার সংলগ্ন অব্যবহৃত জমিগুলো ফিরিয়ে নিয়ে, সেগুলো কি তাঁদের দিয়ে দেওয়া যায় না? এ জন্য যদি আইন সংশোধন করার দরকার হয়, তো তার জন্য চেষ্টাচরিত্র করা হোক। আমরা তার পাশে থাকব। শুধু শুধু কৃষিজমিগুলো নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।
কথাগুলো খুব মনে ধরেছিল তেরো নম্বর, নবীন মাস্টার আর তত দিনে ওরা যাঁদের পুরো ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছিল, তাদের সংগ্রামের সঙ্গী করে তুলতে পেরেছিল, তাঁদেরও। ওঁরা ঠিক করেছিলেন, একদিন শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গিয়ে সরাসরি কথা বলবেন। কিন্তু তার আগেই ২০০৭ সালের ৩ জানুয়ারি নন্দীগ্রামে গুলি চলল।
তার প্রতিবাদে পরের দিন ৪ জানুয়ারি গড়চক্রবেড়িয়া আর সোনাচূড়ায় হল জনসভা। সম্ভবত তারই প্রেক্ষিতে ৬ জানুয়ারির মধ্যরাতে ফের গুলি বৃষ্টি হল নন্দীগ্রামে। শহিদ হলেন চার জন কৃষক।
৭ জানুয়ারি ডাকা হল জরুরি সভা। কুলপি বন্দরের জন্য প্রস্তাবিত কৃষি ও বাস্তুজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতির উদ্যোগে কলকাতায় শুরু হল বিক্ষোভ।
৮ জানুয়ারি বারো ঘণ্টার বাংলা বন্ধ সফল করলেন এই রাজ্যের মানুষ। নন্দীগ্রাম যে এত দ্রুত জেগে উঠবে, তেরো নম্বর কেন, তার সঙ্গীসাথী, এমনকী নবীন মাস্টারও আন্দাজ করতে পারেননি। কিন্তু নন্দীগ্রামের মানুষদের এই জেগে ওঠাটাকে জিইয়ে রাখার জন্যই তাঁরা এত ছোটাছুটি করছিলেন যে, শান্তশ্রীর কাছে আর যাওয়ারই সময় পাননি। তারই মধ্যে ঘটে গেল ২০০৭ সালের ১৪ মার্চের সেই ভয়ানক ঘটনা।