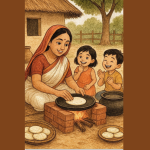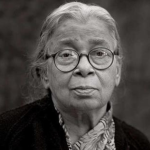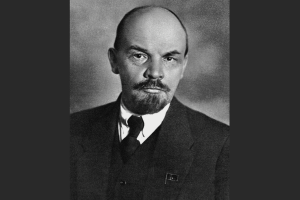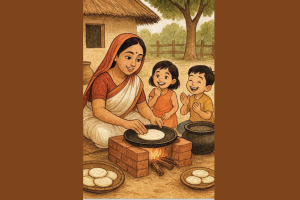ইউরোপীয়রা যখন প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পন করেছিলেন তখনও ভারতের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা কিন্তু ঠিকমতোই চলছিল; এমনকি খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসিত বাংলায় যখন নবীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল, তখনও আগের সেই সুপ্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়নি; বরং তখনও এদেশের সর্বত্রই বহু টোল ও চতুষ্পাঠী এবং মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। তখনও বাংলার গ্রামে গ্রামে গুরুমশাইরা পাঠশালায় এদেশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাচ্ছিলেন, এবং টোলে অধ্যাপকরা শাস্ত্রচর্চায় রত ছিলেন। এই টোল ও মক্তব-মাদ্রাসাগুলিই তখন এদেশের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র, আর পাঠশালাগুলি প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র ছিল।
আর সেকালের বাংলার পাঠশালাগুলির ব্যবস্থা খুবই সাদাসিধে ধরণের ছিল। সেযুগের সব পাঠশালারই যে নিজস্ব গৃহ ছিল—সেটা নয়; বরং তখন অধিকাংশক্ষেত্রেই গ্রামের কোনো সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বা বারোয়ারিতলার পূজামণ্ডপে এই পাঠশালাগুলি বসত। আর যেখানে নিদেনপক্ষে এরকম কিছুও জুটত না, সেখানে গুরুমশাইরা বড় কোন গাছতলার নিচে আশ্রয় নিতেন, সেই আম-বটের ছায়াতেই গ্রাম্য পাঠশালা বসত, সেখানেই গ্রামের ছেলেরা পাততাড়ি বগলদাবা করে নিয়ে এসে জুটতেন এবং গুরুমশাইরা বেতহাতে সেখানেই তাঁদের বিদ্যবিতরণ করিতেন।
তখনকার এই পাঠশালাগুলির কাজ শুরু হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না, বরং তখন গুরুমশাইয়ের সুবিধামত এসব পাঠশালাগুলি বসত ও ছুটি হত। এছাড়া সেযুগে প্রচলিত থাকা বিভিন্ন গ্রাম্য উৎসবে ও পূজাপার্বণের সময়ে এই পাঠশালাগুলি বন্ধ থাকত; প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এখনকার মত সেকালের এসব পাঠশালাগুলিতে সাপ্তাহিক বা বাৎসরিক নির্দিষ্ট কোনো ছুটির ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু তা বলে এগুলিতে অনধ্যায়ের ব্যবস্থা অপ্রতুল ছিল, একথা মনে করলে ভুল করা হবে।
তখনকার পাঠশালাগুলির পাঠ্য সংকীর্ণ বা সংক্ষিপ্ত ছিল; এগুলিতে পাঠ্য বলতে সামান্য লেখাপড়া ও জমাখরচের হিসাব—এটুকুই চালু ছিল। এখনকার মত এগুলিতে যেমন ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি পড়ানো হত না, তেমনি ধর্মশিক্ষা স্বাস্থ্যতত্ত্ব হাতের কাজ বা ব্যায়াম গোছের কিছুও ছাত্রদের শেখানো হত না। সেযুগের গ্রামের ছেলেরা চার-পাঁচ বছর ধরে পাঠশালায় কোনোমতে সময় কাটিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়তে, চিঠিপত্র লিখতে, বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ তৈরি করিতে এবং কোনমতে জমিদারি ও মহাজনী হিসাব রাখতে শিখলেই তাঁর পাঠশালার শিক্ষা যথাযথভাবে শেষ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হত। যেহেতু তখনও পর্যন্ত ছাপা পুস্তকের চল হয়নি, সেহেতু পাঠশালাগুলিতেও এসবের কোন ব্যবহার চালু ছিল না।
তখনকার এই পাঠশালাগুলিতে গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের ছেলেরাই পড়তেন, এবং সেকালে সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত বলতে যাঁদের বোঝানো হত, তাঁদের ঘরের ছেলেরাই এখানে লেখাপড়া শিখতে যেতেন। আর যেহেতু সেযুগে এধরণের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখে তাঁরা কোন জমিদারি সেরেস্তায় বা মহাজনের গদিতে মুহুরীগিরি করতেন, সেহেতু এদিক থেকে সেকালের পাঠশালার শিক্ষাকে বর্ত্তমানের বৃত্তিমূলক শিক্ষার পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব বিবরণের সণ্ধান পাওয়া যায়, সেগুলিতে দেখা যায় যে, তখন পাঠশালার ছাত্রদের মধ্যে তথাকথিত উচ্চবর্ণের ছাত্রের সংখ্যা বেশী হলেও তাঁদের মধ্যে তথাকথিত নিম্নবর্ণের ছাত্রও যে এক-আধজন ছিলেন না—এমনটা কিন্তু নয়; এমনকি তখনকার এসব বিবরণীতে হাড়ি, বাগদি, মুচি, বাউরি, জেলে, মাল, কলু, কামার প্রভৃতি জাতির ছাত্রের কথাও পাওয়া যায়। তবে সেকালে মেয়েরা সাধারণতঃ পাঠশালায় যেতেন না; তাঁরা যেটুকু লেখাপড়া শিখতেন, সেটা বাড়িতেই শিখতেন। অবশ্য সেযুগের এক-আধজন মেয়ে যে পাঠশালায় পড়তেন না—তেমনটাও আবার নয়; কিন্তু সে তাঁদের খুবই অল্প বয়সে। কারণ, এরপরে একটু বড় হলেই তাঁদের গৃহকর্মের শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হত বলে এরপরে তাঁদের আর পাঠশালায় যাওয়ার কোন অবসর থাকত না।
টোল, মক্তব ও মাদ্রাসাগুলি সেকালের বাংলা তথা ভারতের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল। তৎকালীন দেশের বিভিন্ন জায়গায় এগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর মধ্যে নবদ্বীপ, মিথিলা, বিক্রমপুর প্রভৃতি জায়গাগুলি তখন সংস্কৃতশিক্ষার বড় কেন্দ্র ছিল। এসব জায়গায় তখন বহু টোল অবস্থিত ছিল, যেগুলিতে দূর দূর দেশ থেকে ছাত্ররা লেখাপড়া করবার জন্য উপস্থিত হতেন। অন্যদিকে পাটনা, মুর্শিদাবাদ, দিল্লি প্রভৃতি জায়গায় তখন আরবি-ফারসি চর্চার জন্য প্রচুর মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। তখনকার ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলেরা টোলে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি নিয়ে পড়াশোনা করলেও তাঁদের সবাই যে, যাজন বা অধ্যাপনা করবার জন্যই পড়াশোনা করতেন—সেটা নয়। বরং, তাঁদের মধ্যে অনেকেই তখন শুধুমাত্র জ্ঞানলাভ করবার আগ্রহেই বিদ্যাচর্চায় লিপ্ত থাকতেন। সমকালে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ছেলেরা নিজেদের ঘরে আখনজী রেখে ফারসি শিক্ষা করতেন ও কোরান পড়তে শিখতেন; এরপরে তাঁদের মধ্যে যাঁরা উচ্চতর শিক্ষালাভ করতে চাইতেন, তাঁরা মক্তব-মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হতেন। সেগুলিও তখন টোলগুলির মতোই ছিল। সেখানেও ছাত্ররা বিনা ব্যয়ে লেখাপড়া শিখতেন, এমনকি তাঁদের থাকবার ও খাওয়ার খরচ পর্যন্ত দিতে হত না। আর ফারসি যেহেতু সেকালের রাজভাষা ছিল, সেহেতু বহু হিন্দুঘরের সন্তানও রাজসরকারে চাকরির জন্য ফারসি শিক্ষা করতেন। এমনকি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার শুধু জ্ঞান-অর্জনের জন্যই আরবি ফারসি পড়তেন। এটাই তখনকার দিনের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।
প্রসঙ্গতঃ একথাও স্মরণীয় যে, সেযুগের উচ্চশিক্ষা পুরোপুরি অবৈতনিক ছিল। এর কারণ ছিল যে, সেকালের টোল মক্তব মাদ্রাসাগুলি রাজসরকারের বা ধনীদের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সাহায্য পেত। সেযুগের ব্রাহ্মণ অধ্যাপকরা যেমন ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ভোগ করতেন, তেমনি আবার হিন্দুদের বিভিন্ন পূজাপার্বণে বৃত্তি ও বিদায়ীও পেতেন, এবং তাতেই সন্তুষ্ট থেকে তাঁরা নিজেদের কুটিরে বসে বিদ্যাদান ও শাস্ত্রচর্চায় মগ্ন থাকতেন। এখনকার মত তাঁরা বিদ্যা বিক্রি করবার কথা ভাবতেও পারতেন না।
তবে সেযুগের টোলে সুনির্দিষ্ট কোন বেতনের ব্যবস্থা না থাকলেও পাঠশালায় কিন্তু লেখাপড়া শেখবার জন্য বেতন দিতে হত। কিন্তু সেটা কোন নির্দিষ্ট বেতন ছিল না। বরং ছাত্রদের মধ্যে যাঁর যেরকম সাধ্য হত, সে সেটাই পাঠশালার বেতন হিসেবে দিত। যেমন—কেউ হয়ত কিছু চাল দিলেন, কেউ আবার তেল দিলেন; আবার যাঁর আর্থিক ক্ষমতা থাকত, তিনি নগদ অর্থই দিতেন। কোম্পানি আমলের বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, তখনকার দিনের পাঠশালার গুরুমশাইদের আর্থিক অবস্থা পরবর্তী সময়ের শিক্ষকদের তুলনায় কিন্তু বেশ সচ্ছলই ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের একটা রিপোর্টে দেখা যায় যে, তখনকার বাংলার পাঠশালার একজন গুরুমশাই প্রতি মাসে গড়ে নগদ প্রায় পাঁচ-ছ’টাকা উপার্জন করতেন। এখানে মনে রাখতে হবে যে, এখন থেকে একশো-দেড়শো বছর আগে পাঁচ-ছ’টাকা দিয়ে বাড়িতে রীতিমত দুর্গাপূজা সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল। এর উপরে বিভিন্ন সময়ে ছাত্রদের কাছ থেকে লাউ-কুমড়ো, পূজাপার্বণে বিদায়ী, বিভিন্ন উৎসবে একটা ধুতি বা গামছা—এসব তো গুরুমশাইরা পেতেনই। সুতরাং পরবর্তী সময়ের তুলনায় তখনকার গুরুমশাইরা আর্থিক দিক থেকে বেশ ভালোই স্বচ্ছল ছিলেন।
যদিও আধুনিক সুময়ের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে হয়ত তখনকার দিনের পাঠশালার এই শিক্ষাকে পর্যাপ্ত বলে মনে হবে না; কিন্তু তবুও সেযুগের সমাজব্যবস্থা ও প্রয়োজনের তুলনায় সেই শিক্ষা যে অকিঞ্চিৎকর ছিল—একথা বলাও কিন্তু সম্ভব নয়। আর একারণেই সেযুগের একজন মিশনারি তাঁর নিজের দেশ স্কটল্যান্ডের পাঠশালাগুলির সঙ্গে তুলনা করে তৎকালীন বাংলার গ্রাম্য পাঠশালাগুলিকে ভালো বলেছিলেন এবং এসব পাঠশালার গুরুমশাইদের কাজের প্রশংসাও করেছিলেন।
প্রসঙ্গতঃ এখানে তখনকার শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষত্ব নিয়েও কিছু মন্তব্য করবার দরকার রয়েছে।
প্রথমতঃ, বর্তমান সময়ে যেমন শিক্ষাকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা—এধরণের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, সেকালে তেমন কিছু কিন্তু ছিল না। বরং এযুগের হিসেবে তখন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক ও উচ্চ—শুধুমাত্র এই দুটি স্তরই বর্তমান ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে সেকালে কিছুই ছিল না।
দ্বিতীয়তঃ, তখন প্রায় সব গ্রামেই পাঠশালা ছিল; কারণ, প্রাচীন গ্রাম্যদেবতার মতোই পাঠশালাগুলিও তখনকার বাংলার পল্লীসমাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। তবে সেকালের প্রতি গ্রামেই অবশ্য টোল, অর্থাৎ—উচ্চশিক্ষার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। কিন্তু সাধারণতঃ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সেযুগের গ্রামের ছেলেদের গ্রামের বাইরে যেতে হত না; এমনকি সেকালের বড় বড় গ্রামগুলিতে তো পাঁচ-ছ’টি পাঠশালা পর্যন্ত ছিল। আর একারণেই, খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কোম্পানি সরকারের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তৎকালীন দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার সম্বন্ধে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল, তাতে দেখা যায় যে, তখন শুধু বাংলাতেই (সে সময়ে বিহার ও ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যার কটক জেলাও বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল) একলক্ষ পাঠশালা ছিল।
কিন্তু যেহেতু ওই যুগটা প্রাচীন সবধরণের ব্যবস্থারই পড়তির সময় ছিল, সেহেতু তখন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হস্তান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষাব্যবস্থাও ধীরে ধীরে শক্তিহীন ও প্রাণহীন হয়ে পড়েছিল। এর ফলস্বরূপ এদেশের বহু প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তখন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং যাচ্ছিল। অনেকের মতে, তৎকালীন দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যই এর পিছনে প্রধান কারণ ছিল। একথার উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, ১৮২২ সালে মাদ্রাজের একজন ইংরেজ কালেক্টর ভারতের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার ধ্বংসের কারণস্বরূপ দেশের সর্বত্র সৈন্যদের চলাচল, বিদেশী বস্ত্রশিল্পের প্রসার ও প্রাচীন কুটিরশিল্পগুলির ধ্বংসকে দায়ী করেছিলেন। সুতরাং প্রাচীন সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেযুগে কত গ্রাম্য পাঠশালা যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, ইতিহাস সেসবের কোন হিসেব রাখেনি। আর একারণেই খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে যেসব তথ্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে সংগ্রহ করা হয়েছিল, সেসবের উপরে আদৌ নির্ভর করা যায় কিনা—এবিষয়ে ঐতিহাসিকেরা আজও যথেষ্ট সন্দিহান রয়েছেন। তবে তখনকার তথ্যের হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষার যতটা প্রসার হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে, বাস্তবে সেযুগের মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার যে এর থেকে অনেক বেশি ছিল—একথা অনুমান করলে কিন্তু ভুল কিছু করা হয় না।#