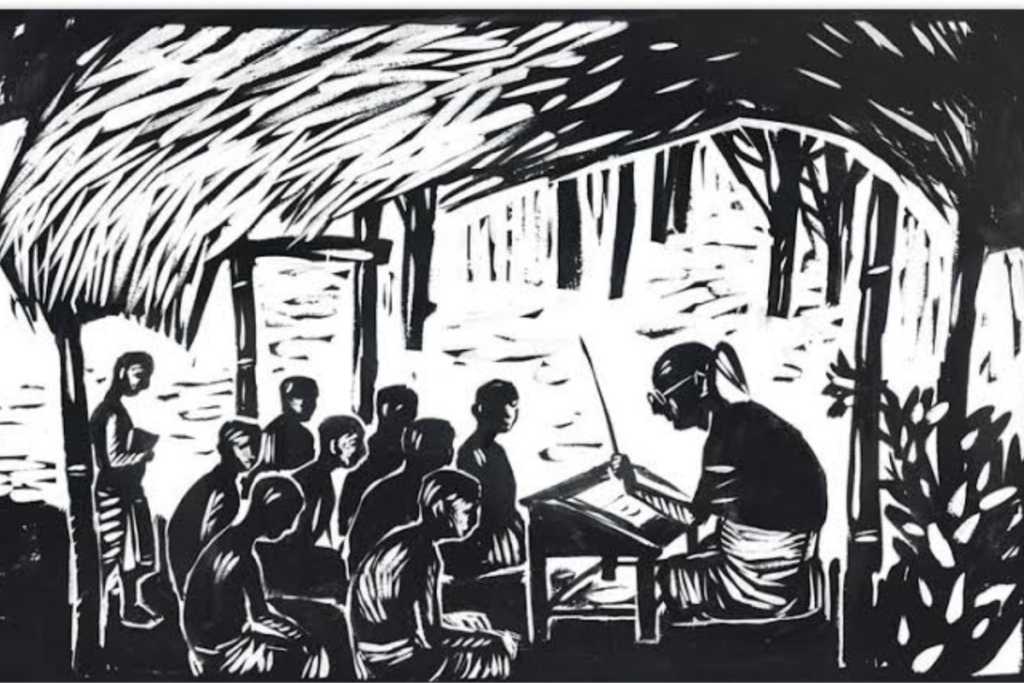এখনও পর্যন্ত ঐতিহাসিকেরা বাংলায় রচিত নব্যস্মৃতির যেসব গ্রন্থগুলির সন্ধান পেয়েছেন, সেগুলির মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থেই এদেশের নব্যস্মৃতির প্রায় মধ্যাহ্নকালের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং বাংলায় ঠিক কোন সময়ে নব্যস্মৃতি রচনা শুরু হয়েছিল, সেবিষয়ে ইতিহাস আজও অন্ধকারে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাংলায় নব্যস্মৃতির যেসব গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে ভবদেব ভট্টের গ্রন্থগুলি সবথেকে বেশি প্রাচীন। তাঁর জীবনকাল খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের মধ্যে ছিল বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। ভবদেব ভট্ট তাঁর ‘প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ’ গ্রন্থে বালক ও জিকন প্রমুখ স্মৃতিকারের মত সযত্নে উদ্ধৃত করেছিলেন এবং অনেক জায়গায় নিজের যুক্তি দিয়ে তাঁদের মত খণ্ডনও করেছিলেন। কিন্তু এসব স্মৃতিকারদের নাম বা মতের উল্লেখ যেহেতু কোন অবাঙালি স্মৃতিকার করেননি, সেহেতু ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, এঁরা আসলে ভবদেব ভট্টের আগেকার সময়ের বাংলার মানুষ ছিলেন। এছাড়া ভবদেব নিজের গ্রন্থে তাঁদের মত খণ্ডন করবার বিষয়ে যে ধরণের ব্যগ্রতা প্রকাশ করেছিলেন বলে দেখা যায়, সেটা থেকে একথাই মনে হয় যে, এঁরা ভবদেবের আগেকার ও সমকালীন পণ্ডিতসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সুতরাং, এই তথ্য থেকে সহজেই একথা অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, বাংলায় নব্যস্মৃতি গ্রন্থগুলি অন্ততঃ খৃষ্টীয় দশম শতক থেকেই রচিত হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল।
এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হওয়া বাংলার স্মৃতিগ্রন্থগুলির রচনাকাল মোটামুটিভাবে খৃষ্টীয় একাদশ শতক থেকে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক পর্যন্ত ব্যাপ্ত রয়েছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। ইতিহাস বলে যে, এই পাঁচশো বছরের মধ্যে বাংলা নানা রাজনৈতিক বিপর্যয় ও দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছিল। বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী পালরাজবংশের পতনের পরে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুসারী সেনরাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। তাঁদের পোষকতায় তখন ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির চরম উন্নতি দেখা দিয়েছিল; এবং স্মৃতি, কাব্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সেনরাজ বল্লালসেন স্বয়ং কতগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; অনেক পণ্ডিতের মতে কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তন ইত্যাদি সমাজসংস্কারও তাঁরই কীর্তি ছিল। বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য-সংস্কৃতির একজন বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কথিত রয়েছে যে—জয়দেব, উমাপতিধর, ধোয়ী, শরণ ও গোবর্ধনাচার্য তাঁর সভাকবি ছিলেন। তৎকালীন হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধ্বজাস্বরূপ হলায়ুধ একাধারে লক্ষ্মণসেনের প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। হলায়ুধের ‘ব্রাহ্মণসর্বস্ব’ গ্রন্থটি ইতিহাসে বিখ্যাত। কিন্তু এই বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী রাজার বৃদ্ধবয়সে তাঁর রাজ্যে তুমুল বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দরা তখন নিজেরাই প্রধান হয়ে উঠে রাজার আনুগত্য অস্বীকার করতে শুরু করেছিলেন। এরপরে বখতিয়ার খলজির বাংলা আক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল, এবং বৃদ্ধ সেনরাজ প্রাণভয়ে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেছিলেন; সেখানেই সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দশকে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। লক্ষ্মণসেনের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় শুধু যে হিন্দু রাজত্বেরই অবসান ঘটেছিল—সেটাই নয়; একইসাথে ক্ষমতার লড়াইয়ের ফলে বাংলায় দীর্ঘকালব্যাপী অন্ধকার যুগের সূচনা ঘটেছিল। লক্ষণ সেনের আগেকার সেনরাজাদের শাসনে সমগ্র বাংলা একটি সুসংহত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। তাছাড়া, পালযুগে বৌদ্ধধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম যখন সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছিল, তখন সেনরাজাদের চেষ্টাতেই বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রবাহ স্তিমিত হয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গ থেকে লক্ষণের পলায়নের পরে বখতিয়ার খলজি পশ্চিমবঙ্গের সুলতানি মসনদে আসীন হয়েছিলেন। এর কিছুকাল পরেই আলি মর্দান নামের একজন ব্যক্তি বখতিয়ারকে হত্যা করে সুলতানি মসনদ অধিকার করে নিয়েছিলেন। তারপর থেকে মসনদের অধিকার নিয়ে বাংলায় দীর্ঘকালব্যাপী লড়াইয়ের সূত্রপাত ঘটেছিল, এবং অন্তর্দ্রোহ, হত্যাকাণ্ড ও বলপূর্বক মসনদ অধিকার প্রভৃতি রাজনৈতিক ব্যাপার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর ফলস্বরূপ ১২২৭ থেকে ১২৮৭ খৃষ্টাব্দ—এই ষাট বছরের মধ্যে পনেরো জন বাংলার শাসক হয়েছিলেন এবং বাংলার উপরে দিল্লীর আধিপত্য তখন শুধু নামেই পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। শেষে তুঘ্রাল খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের আনুগত্য অস্বীকার করলে সুলতান তাঁকে পদচ্যুত করে নিজের পুত্র বুঘরা খাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। বলবন-আমলের বাংলার সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল যে, সেই সময় থেকেই বাংলায় ইসলামধর্মের ব্যাপক প্রচার আরম্ভ হয়েছিল, এবং তৎকালীন সমাজের উচ্চস্তরের নিষ্পেষণে জর্জরিত নিম্নশ্রেণীর বহুসংখ্যক মানুষ ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ও হিন্দু বৌদ্ধ দেবালয়ের জায়গায় বাংলায় প্রচুর দরগা-খানকা ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছিল। কালক্রমে বাংলায় মামলুক সুলতান বংশের অভ্যুত্থান ও পতন ঘটেছিল। এরপরে সুলতান মহম্মদ তুঘলক বাংলাকে নিজের অধিকারভুক্ত করেছিলেন এবং অবশেষে বাংলায় তুঘলকি শাসনেরও অবসান ঘটেছিল। এরপরে চঞ্চলা বঙ্গলক্ষ্মী ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। এই ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকালের পরে অতি অল্পকালের জন্য রাজা গণেশ নামক একজন হিন্দুরাজা কিছুকালের জন্য বাংলার সিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র জিৎমল বা জয়মল—যদু বা যদুসেন নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। এই যদু ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়ে জালালউদ্দিন নাম নিয়ে পিতার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। সেই সময়ে তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রগুলির বিশেষ পোষকতা করেছিলেন। মধ্যযুগের বাংলার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৃহস্পতি রায়মুকুট তাঁর সভা অলংকৃত করেছিলেন। এরপরে বাংলায় পুনরায় ইলিয়াস শাহী বংশের উত্থান ঘটেছিল এবং খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষেরদিকে এই বংশের অবসান হয়েছিল। তারপরে হুসেন শাহী বংশ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা শাসন করেছিল ও এই আমলে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশেষ উন্নতিলাভ করেছিল। এই বংশের পরে আফগানরা বাংলার শাসনপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের শাসন ষোড়শ শতকের শেষপর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। আফগানদের পরে বাংলা মোঘল শাসনাধীনে এসেছিল। বাংলার হিন্দুসমাজে নব্যস্মৃতিশাস্ত্রের যুগ, অর্থাৎ—একাদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত মোটামুটিভাবে এটাই রাজনৈতিক চিত্র ছিল।
আরও পড়ুন: চর্যাপদের দার্শনিকতা
উক্ত পাঁচ শতাব্দীর বাংলার সমাজ এবং ধর্মজীবনের ইতিহাসও যে বৈচিত্র্যময় ছিল,—এসময়ের মধ্যে রচিত বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ এবং শূন্যপুরাণ, ময়নামতীর গান, মনসামঙ্গল বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ ও চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি বাংলা গ্রন্থ থেকে তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে এধারণাই পাওয়া যায়। যদিও এসব গ্রন্থে অনেক অতিরঞ্জন অতিশয়োক্তি রয়েছে, তবুও তৎকালীন সমাজের মূল চিত্রটি যে এগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল, সেবিষয়ে ঐতিহাসিকদের কোন সন্দেহ নেই। সমকালীন কুলজী গ্রন্থগুলিতেও সামাজিক অনেক ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত থাকলেও সেগুলির ঐতিহাসিকত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না।
আগেই বলা হয়েছে যে, হয় পালবংশের পতন ও সেনবংশের উত্থান—এই যুগসন্ধিক্ষণে বঙ্গীয় নব্যস্মৃতির উৎপত্তি ঘটেছিল, কিংবা হয়ত নব্যস্মৃতির উৎপত্তি এর কিছু আগে হলেও এযুগেই সর্বপ্রথম এটি সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেই সময়কার বাংলা বৌদ্ধধর্মের প্রবাহে প্লাবিত ছিল, এবং সেই প্রবাহ নব্যস্মৃতির উৎপত্তি থেকে চরম উন্নতির সময় পর্যন্ত ক্ষীণ হলেও বর্তমান ছিল; রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, রূপরাম ও খেলারামের ধর্মমঙ্গল কাব্য ইত্যাদি গ্রন্থ অন্ততঃ এবিষয়েই সাক্ষ্য দেয়। এরপরে সেনযুগের বাংলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ঘটলেও তুর্কী আক্রমণের পরে, ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বিদের মধ্যে অনেকেই মুসলমানদের দ্বারা উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। ওই সময়ে হিন্দুদের ধর্মকার্যে বাধা দেওয়া, ব্রাহ্মণদের যজ্ঞোপবীত-ছেদন, হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করবার অপচেষ্টা এবং কাজীদের কর্তৃক বহুবিধ অত্যাচারের বিবরণ—সমকালের অনেক বাংলা গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু, ব্রাহ্মণ্যধর্মের যে জীবনীশক্তি প্রাচীনতর যুগ থেকে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এই ধর্মকে সজীব রেখে দিয়েছিল, সেটা এযুগেও লুপ্ত হয়ে যায়নি। ফলে, এই ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম যে কখনোই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি, সেকথার প্রমাণ পূর্বোক্ত পুরাণগুলি ও হরিরামের চণ্ডীকাব্য, মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণচণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত সেযুগে প্রচলিত থাকা বর্ণ উপবর্ণের ভাগ বিভাগ থেকেই স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়।
এর মধ্যে চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম সমগ্র বাংলার সমাজ ও ধর্ম-চেতনাকে আলোড়িত করেছিল। তবে চৈতন্য মহাপ্রভুই বাংলায় প্রথম বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তন করেননি। বস্তুতঃ বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তনের কাল আজও নিশ্চিতভাবে নির্ণীত না হলেও একথা অবিসংবাদিত যে, চৈতন্যের আবির্ভাবের দীর্ঘকাল আগে থেকেই বাংলায় এই ধর্মের অস্তিত্ব ছিল। জয়দেব চণ্ডীদাসের কাব্যই একথার ঐতিহাসিক প্রমাণ। যাই হোক, চৈতন্যের ভাবাবেগে বৈষ্ণবধর্মের ফল্গুধারা বলিষ্ঠ প্রবাহে পরিণত হয়ে একটাসময়ে বাংলার জীর্ণ ও বিধ্বস্ত সমাজদেহে রসায়নের প্রয়োগ করে এই দেহকে নবীভূত করেছিল। চৈতন্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংকীর্ণতাকে অস্বীকার করেছিলেন এবং তাঁর প্রচেষ্টাতেই সেকালের বাংলায় শাস্ত্রীয় যুক্তির থেকে হৃদয়ের আবেগ ও ভক্তি উচ্চতর আসন লাভ করেছিল। এরপরে চৈতন্যকে কেন্দ্র করে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল এবং বৈষ্ণবধর্মের অনুপ্রেরণায় অনেক কবি তখন নিজেদের কাব্য রচনা করেছিলেন। যবন হলেও চৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাসকে সাগ্রহে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত করেছিলেন। এর ফলস্বরূপ সেকালের অনেক মুসলমান পর্যন্ত তখন এই ধর্মে মেতে উঠেছিলেন; এবং আলাওল, সৈয়দ মর্তুজা প্রমুখ মুসলমান কবিরাও বাংলাভাষায় বৈষ্ণবকাব্য রচনা করেছিলেন।
তবে এযুগের অন্য যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য না করলে সমকালীন সমাজ-চিত্রটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়, সেটা হল—সেযুগের হিন্দু বাঙালির উপরে তন্ত্র ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব। মণ্ডল, মুদ্রা, যন্ত্র ও রহস্যময় মন্ত্রের সাহায্যে শক্তিপূজাই এই ধর্মের প্রধান অঙ্গ। এযুগে বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত প্রভৃতি তন্ত্র বাংলার হিন্দুসমাজে নিজেদের প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করেছিল, এবং এযুগেই নবদ্বীপে বিখ্যাত তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দের আবির্ভাব ঘটেছিল। উপরিল্লিখিত পটভূমি ও পরিবেশেই তখন বঙ্গীয় স্মৃতির উদ্ভব এবং পরিপুষ্টি ঘটেছিল।
আরও পড়ুন: লালন শাহের ইসলামীকরণ বিতর্ক
বর্তমানে সাধারণভাবে অনেকেই এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, বঙ্গীয় নব্যস্মৃতি বলতে শুধুমাত্র রঘুনন্দনের রচনাবলীকেই বোঝানো হয়ে থাকে। আসলে তাঁদের এই ভ্রান্ত ধারণার মূলে রঘুনন্দনের অসাধারণ প্রতিভা ও তাঁর রচিত বহু ও বিশাল গ্রন্থরাশি রয়েছে। তবে ইতিহাস বলে যে, তাঁর আগে এবং পরে বাংলায় অনেক বাঙালি স্মৃতিকারের আবির্ভাব ঘটেছিল; কিন্তু সূক্ষ্মবিচার, বিশ্লেষণ এবং পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও ব্যাপকতায় তাঁরা কেউই রঘুনন্দনের সমকক্ষ হতে পারেননি। এরফলে পরবর্তীকালের জনসাধারণ বাংলার নব্যস্মৃতি প্রসঙ্গে আজও শুধুমাত্র রঘুনন্দনকেই মনে রেখেছেন। তবে বর্তমানে যেসব বাঙালি স্মৃতিকারের গ্রন্থাদি পাওয়া যায়, তাঁদের সময়কালকে ঐতিহাসিকেরা যে তিনটি যুগে ভাগ করেছেন, সেটা নিম্নরূপ—
(ক) প্রাক-রঘুনন্দন যুগ।
(খ) রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ।
(গ) নব্যস্মৃতির অপ্রসিদ্ধ লেখকরা।
নব্যস্মৃতির বিষয়গুলিকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে; যথা—আচার, প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবহার। যেহেতু প্রাচীন ভারতীয় স্মৃতির আলোচ্য বিষয়গুলিও এই তিনভাগেই বিভক্ত, সেহেতু বাংলার স্মৃতিকারেরাও প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে আলোচিত কোন বিষয়কেই বর্জন করেননি বলেই দেখা যায়। বরং ন্যায়, পূর্বমীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্যে তাঁরা প্রাচীন স্মৃতির বিভিন্ন বিধি-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং আপাতবিরোধী স্মৃতিবচনগুলির মধ্যে একবাক্যতা বা মৌল ঐক্য নির্ধারণ করেছিলেন।
নব্যস্মৃতির আচারাংশে প্রধান আলোচ্য বিষয় হল—বিভিন্ন সংস্কার, পূজাপার্বণ, বিশেষতঃ দুর্গাপূজা, ব্রত ইত্যাদি।
প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বাংলার স্মৃতিকারদের ধারণা শূলপাণির ‘প্রায়শ্চিত্তবিবেক’ গ্রন্থ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। বাংলার নব্যস্মৃতি অনুসারে—“তপো নিশ্চয়সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্থিতম্”—অর্থাৎ, সেই ধরণের ধর্মানুষ্ঠান বা কৃচ্ছ সাধনাই হল প্রায়শ্চিত্ত, যা পাপক্ষয়কর বলে সকলে নিশ্চিত। ‘পাপক্ষয়মাত্রসাধনত্ব’ই এই প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ। পাপের উৎপত্তি দু’ভাবে হতে পারে—বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান ও নিন্দিত কর্মের সেবনের মাধ্যমে। নব্যস্মৃতিতে পাপের দ্বিবিধ শক্তি স্বীকৃত হয়েছে; এগুলির মধ্যে প্রথম শক্তিদ্বারা পাপ পাপীকে নরকগামী করে, এবং দ্বিতীয় শক্তির ফলে পাপী সমাজে অব্যবহার্য হয়ে ওঠে; অর্থাৎ, তাঁর সঙ্গে অন্যদের বিবাহ এবং ভোজন সংক্রান্ত কোন সম্বন্ধ থাকে না। প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গে বাংলার স্মৃতিকারেরা দুইটি উল্লেখযোগ্য নীতি অবলম্বন করেছিলেন—তন্ত্রতা ও প্রসঙ্গ। পঞ্চানন তর্করত্ন জানিয়েছিলেন—
“অনেকমুদ্দিশ্য সকৃৎপ্রবৃত্তিস্তন্ত্রতা—এক জাতীয় অনেক পাপ করিয়া একবার প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপী পাপ-মুক্ত হইতে পারে; এই নীতির নাম তন্ত্রতা। অন্যদ্দেশেন প্রবৃত্তাবন্যস্যাপি সিদ্ধিঃ প্রসঙ্গঃ—এক ব্যক্তি গুরুতর ও লঘুতর পাপ করিয়া গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেই লঘুতর পাপ হইতেও মুক্ত হইবে; এই নীতির নাম প্রসঙ্গ। অতিপাতক, মহাপাতক, উপপাতক ও অনুপাতক—পাপের এই চারিটি শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। বয়স, বর্ণ প্রভৃতি ভেদে প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য করা হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষ ভেদেও লঘু ও গুরু প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা হইয়াছে।”
আরও পড়ুন: পণ্ডিত বিদ্যাসাগর ও শকুন্তলা
তবে বাংলার নব্যস্মৃতির ব্যবহারাংশ সর্বাপেক্ষা বেশি উল্লেখযোগ্য। এতে যে বিচারপদ্ধতির অবতারণা করা হয়েছে, সেটা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ বলে দেখতে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির কোন কোন বিষয় বর্তমান যুগের বিচারালয়ে অনুসৃত রীতির অনুরূপ। যেমন—বাংলার স্মৃতিকারেরা ব্যবস্থা করেছিলেন যে, দুটি স্মৃতিবাক্যের মধ্যে বিরোধ ঘটলে বিচারক নিজের যুক্তির আশ্রয় নিয়ে বিষয়টার মীমাংসা করবেন। এছাড়া ভাষা বা অভিযোগপত্রের মধ্যে যেসব বিবরণের ব্যবস্থা স্মৃতিকারেরা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, বর্তমানযুগেও সে সমস্ত বিষয়ই Plaint বা আর্জিতে লেখা হয়। এছাড়া স্মৃতিকারেরা এই ব্যবস্থাও করেছিলেন যে, বিশেষ কোন বিষয় সম্বন্ধে বিবাদ আগে কোন বিচারালয়ে মীমাংসিত হয়ে থাকলে সেবিষয়ে নতুন করে পুনরায় অভিযোগ করা চলবে না। বর্তমানযুগের ‘Res Judicata’ (Civil Procedure Code, Sec. 11) এই ব্যবস্থারই অনুরূপ।
এসব ছাড়াও দায়ভাগ অংশে ভারতের অন্যান্য নব্যস্মৃতিকারদের সঙ্গে তুলনায় বাংলার স্মৃতিকারদের মৌলিকতা অনেক বেশি পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। এবিষয়ে পঞ্চানন তর্করত্ন জানিয়েছিলেন—
“এই বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির উপর বিজ্ঞানেশ্বরকৃত মিতাক্ষরা টীকাকে সমগ্র ভারত সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু, বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য তাহাকে মিতাক্ষরার আনুগত্য হইতে বিরত করিয়াছিল। জীমূতবাহন দায়ভাগ নামে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাগ্রন্থই রচনা করিয়া ফেলিলেন। মিতাক্ষরা ও দায়ভাগের মধ্যে মৌল পার্থক্য এই যে, পূর্বমতে পুত্রের জন্মমাত্রেই সে পূর্বপুরুষের সম্পত্তিতে পিতার সমান অংশীদার হইয়া থাকে। কিন্তু, দায়ভাগমতে পিতার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বা পিতা স্বেচ্ছায় দান না করা পর্যন্ত ঐ সম্পত্তিতে পুত্রের কোন অধিকারই জন্মে না। ব্যবহারাংশে পৈতৃক সম্পত্তির বিভাগ, বিবিধ প্রকার পুত্র, উত্তরাধিকারক্রম, স্ত্রীধন, অবিভাজ্য সম্পত্তি প্রভৃতি আইনের যাবতীয় জটিল বিষয় আলোচিত হইয়াছে।”#