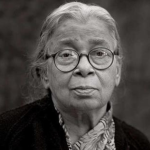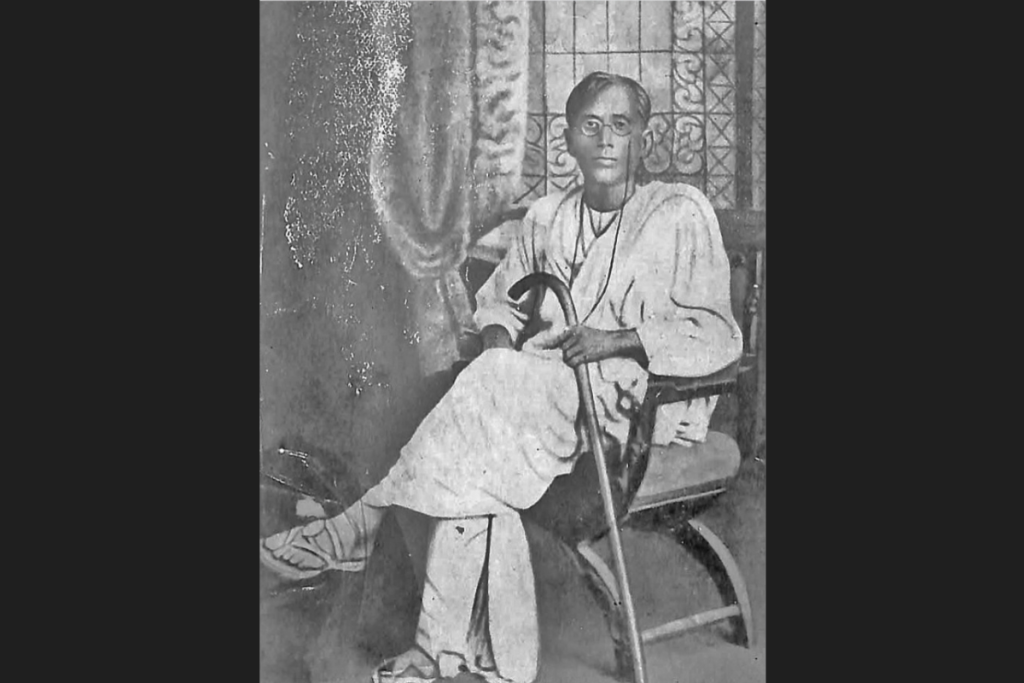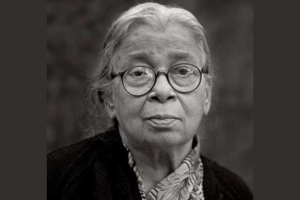অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের এমন এক আশ্চর্য প্রতিভা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর আগে ও পরে— যাঁর কোন দোসর খুঁজে পাওয়া যায় না। একথা সত্যি যে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্যই শরৎচন্দ্রের থেকে অনেক বহুবিস্তারী প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ছিলেন, তাঁরা দু’জনেই রসসৃষ্টিতে যেমন অনন্য ছিলেন, তেমনি আবার মনীষা ও বৈদগ্ধ্যের দিক থেকে বিচিত্রপথসন্ধানী জিজ্ঞাসায় ভরপুর ছিলেন; অন্যদিকে শরৎচন্দ্রের পরেও বাংলা কথাসাহিত্যে এমন কেউ কেউ এসেছিলেন— যাঁরা শরৎচন্দ্রের তুল্য প্রতিভার অধিকারী না হলেও বাংলা সাহিত্যের দিগন্তকে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে সম্প্রসারিত করতে পেরেছিলেন; যেমন— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসে— প্রকৃতিপ্রেম —নামক একটি নতুন আয়তন যোগ করেছিলেন; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রকমারি চরিত্রের স্রষ্টা ছিলেন; আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সমাজ-স্থিতির সবথেকে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক লেখক ও বাস্তবতার সর্বাগ্রগণ্য শিল্পী ছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র যেখানে তুলনারহিত এবং একটু আগে উল্লেখ করা সব দৃষ্টান্তের ঊর্ধ্বে স্থিত, সেটা হল— বাংলা কথাসাহিত্যের মনোহারিত্বের ক্ষেত্র। তাঁর মত করে বাংলা ভাষায় এমন মনোহারী ও লোকপ্রিয় গল্প-উপন্যাস অন্য কেউই সৃষ্টি করতে পারেননি। এই কারণেই শরৎচন্দ্রকে তাঁর জীবদ্দশাতেই বাংলার পাঠক-পাঠিকা সম্প্রদায় ‘অপরাজেয়’ আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। শরৎচন্দ্রকে তাঁদের প্রদত্ত এই অভিধাটি অকারণ ছিল না। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অপরিসীম সৃষ্টিকুশলতার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে রয়েছেন বলে দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তবুও কথাসাহিত্যের সীমিত ক্ষেত্রে এলে দেখতে পাওয়া যায় যে— শরৎচন্দ্র তাঁর লেখার জাদুতে বাংলার পাঠক-পাঠিকার চিত্তকে যেভাবে গভীরভাবে সম্মোহিত করতে পেরেছিলেন এবং আজও করে চলেছেন— তেমন কিছু করা কিন্তু এই দুই অগ্রগামী ও দিপাল লেখকের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। আর তাই মনোজ্ঞতার শিল্পে শরৎচন্দ্রকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা যেতে পারে।
মনোজ্ঞতা তথা লোকপ্রিয়তার শিল্পকে স্বভাবতঃই নিম্নস্তরের শিল্প জ্ঞান করবার একটা সহজ প্রবণতা সকলেরই মধ্যে কম-বেশি রয়েছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লেখকের ক্ষেত্রে একথা সত্যি হলেও শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে একথাটা আদৌ সত্যি বলে দেখা যায় না। বরং লোকপ্রিয়তার নজিরে শরৎচন্দ্রকে খাটো করে দেখবার কোন উপায় নেই, কেননা শরৎচন্দ্র শুধু একজন লোকপ্রিয় শিল্পীই নন, তিনি আরও অনেক কিছু। এই প্রবন্ধে তাঁর সেইসব বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ কিছুটা পরিমাণে করবার চেষ্টা করা হবে, তবে এবিষয়ে গোড়াতেই যে কথাটা বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়া দরকার, সেটা হল যে— তাঁর মত জনপ্রিয় শিল্পী এখনও পর্যন্ত বাংলার কথাসাহিত্যের আসরে দ্বিতীয় কেউ আবির্ভূত হতে পারেননি।
বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকার হৃদয়াসনে নিজের সুদৃঢ় অধিকার স্থাপনা করবার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব অবিসম্বাদী ও সর্বাধিক। কিন্তু নিজের কোন গুণে শরৎচন্দ্র এই অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছেন? সেটা এজন্য যে, তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে শুধুমাত্র মানুষের উপরেই তাঁর সব মনোযোগ সংহত করেছিলেন— মানুষ ছাড়া অন্য কোন অবাস্তব প্রসঙ্গের উত্থাপনায় তিনি নিজের সাহিত্যিক জীবনের সময় ও উদ্যম ব্যয় করেননি। মানুষ ও মানুষের হৃদয়— এই দুটিই তাঁর একান্ত অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ছিল। মানুষ যে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে বাস করে, সেই পারিপার্শ্বিকের উন্মোচনে তাঁর ঠিক ততটা উৎসাহ দেখা যায়নি, এমনকি নিসর্গের রূপ বর্ণনা করবার ক্ষেত্রেও তাঁর মধ্যে সামান্যই অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়; তাছাড়া যে মানুষ বা মানুষী সাহিত্যে তাঁর মুখ্যমনোযোগের বস্তু, বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা অন্য দু’-একজন অগ্রগণ্য লেখকের ধরণে তিনি তাঁদের দৈহিক রূপসৌন্দর্য বর্ণনা করবার জন্য পাতা ভরানোর কোন চেষ্টা করেননি। তাঁর একমাত্র চিত্রিতব্য বিষয় ছিল— মানুষ ও মানুষের মন। চরিত্রসমূহের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ করতে তিনি বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলেন। তবে সেখানেও কিছু কথা রয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত— মানুষের জটিল কুটিল মনের বিশ্লেষণের দিকে তাঁর কোন ঝোঁক ছিল না; সমাজের প্রচলিত অনুশাসন বা সংস্কারের সঙ্গে অন্তরের সহজ প্রবৃত্তির যে সংঘাত, সেই সংঘাতজনিত আলোড়নের ছবি ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই তিনি তাঁর শিল্পীমনের সমধিক স্ফুর্তি পেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর বর্ণিত চরিত্রগুলির আবেগজীবনের রূপায়ণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাঙালি যে অত্যন্ত ভাবাবেগপরায়ণ জাতি, সেকথা শরৎচন্দ্রের লেখা পড়লে যতটা সুনিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করা যায়, তেমন সম্ভবতঃ অন্য কারও লেখা থেকে করা যায় না। অচরিতার্থ প্রেম, সমাজ নিষিদ্ধ অথচ তা সত্ত্বেও অদম্য ভালবাসার আবেগ, বন্ধ্যাত্বের বেদনা তথা মাতৃত্বের ক্ষুধা, সন্তানবাৎসল্য, ভ্রাতৃস্নেহ, নারীর সেবাপরায়ণতা, বিদ্রোহের তেজ —প্রভৃতি কতগুলি বিশেষ বিশেষ ভাবাবেগকে শরৎচন্দ্র তাঁর কলমের মাধ্যমে অতিশয় চমৎকার শিল্পরূপ দান করেছিলেন। তাঁর সময়কার বাংলার সমাজজীবন, বিশেষ করে পল্লী-সমাজজীবনের চিত্ররূপ উপস্থিত করতে গিয়ে তিনি বিধিমতে দুটি কাজ নিষ্পন্ন করেছিলেন।
প্রথমতঃ, তিনি তৎকালীন বাংলার পল্লীবাসী সাধারণ নর-নারীর স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের উদঘাটন করেছিলেন;
দ্বিতীয়তঃ, তৎকালীন বাংলার সমাজে প্রচলিত একাধিক গতানুগতিক মূল্যবোধের উপরে তিনি সজোরে আঘাত হেনেছিলেন।
অর্থাৎ— তাঁর লেখনী, বাস্তবতা ও আদর্শবাদ— এই দুই খাতেই যুগপৎ প্রবাহিত হয়েছিল। বাঙালি চরিত্রের মানসিক গঠন বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবের ধাত বিশ্লেষণ করে তিনি সেসবের কতগুলি অনুচিত সংস্কারকে চূড়ান্ত রকমের সমালোচনা করেছিলেন। বাঙালির অন্তরে তিনি বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিতে পেরেছিলেন। আর এখানেই তাঁর শিল্পসৃষ্টির সার্থকতা দেখতে পাওয়া যায়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে রক্ষণশীলতার অনুকূলেও শরৎচন্দ্র তাঁর অমিত লেখনীর শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি শিল্পী-মনের প্রবণতা অনুযায়ী কখনও প্রগতিশীলতা তো কখনও আবার রক্ষণশীলতা— এই দুই খাতেই তাঁর লেখনীর আবেগ চালিত হয়েছিল
শরৎচন্দ্রের শিল্পের সার্থকতা বিধানে ভাষার চয়ন তাঁর একটি প্রধান সহায় হয়েছিল। বলাই বাহুল্য যে, তাঁর মত এমন মনোমুগ্ধকর ভাষা বাংলার খুব কম লেখকেরই লেখনীমুখ থেকে নিঃসৃত হতে পেরেছে। তবে এক্ষেত্রে শুধু ভাষা বললে কমই বলা হয়, বরং এটাকে তাঁর স্টাইল বলা উচিত। ভাষার মধ্যে দিয়ে যেখানে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ প্রতিফলিত হয়েছিল, —শব্দ সম্পদ, শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য, বাক্যগঠনের রীতি, চিন্তার ছাঁচ, বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গী— সবকিছু জড়িয়ে ছিল, সেখানে তাঁর স্টাইল কিন্তু সেসবকিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই স্টাইলের জাদুতেই শরৎচন্দ্র বাঙালির চিত্ত হরণ করতে পেরেছিলেন এবং আজও করে চলেছেন। কোন একসময়ে শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে লিখিত একটি পত্রে শরৎচন্দ্র অবশ্য বিনয় করে এপ্রসঙ্গে বলেছিলেন—
“ভাষার ওপরে দখল আমার চিরদিনই কম; শব্দসম্পদ যে কত সামান্য এ সংবাদ আর যার কাছেই লুকোনো থাক, তোমাদের কাছে থাকবার কথা নয়।”
কিন্তু তাঁর এই বিবৃতিকে সত্যি বলে গ্রহণ করবার কোন কারণ অন্ততঃ তাঁর সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায় না। আর এটা যদি সত্য বলে গৃহীত হয়ও, সেক্ষেত্রেও যেটা বলবার কথা, সেটা হল যে— নিজের উপরোক্ত মন্তব্যে তিনি শব্দ সম্পদের ‘সামান্যতা’ নিয়ে কুণ্ঠা প্রকাশ করলেও সেটার মধ্যেই তাঁর ভাষার যথার্থ শক্তি নিহিত রয়েছে বলেই দেখতে পাওয়া যায়। নিসর্গবর্ণনা, প্রতিবেশচিত্রণ, বর্ণিত চরিত্রসমূহের দেহ সৌষ্ঠবের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ— এ সমস্ত বিষয়ের বিবরণ দানে তিনি তাঁর মনোযোগ ব্যয় করেননি বলেই তাঁর শব্দসম্পদ স্বতঃই ‘সামান্য’ থেকে গিয়েছিল। শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বের প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদে তিনি তাঁর কবিত্বশক্তির ন্যূনতা নিয়ে যে আক্ষেপোক্তি করেছিলেন, সেটা আসলে কোন আক্ষেপোক্তি ছিল না, বাস্তবে সেটা তাঁর আত্মশক্তিতে বিশ্বাসেরই একধরণের প্রকাশ ছিল। আত্মশক্তিকে এখানে ভাষার শক্তি বলে বুঝতে হবে। সাহিত্য সমালোচকদের মতে— শব্দসম্পদের বিশালতা বা বিস্তারের মধ্যে কখনোই শিল্পীর চাতুর্য নিহিত থাকে না, বরং যে সমস্ত শব্দ নিয়ে শিল্পীর সচরাচর কারবার সেই সমস্ত শব্দ সাজাবার কায়দার মধ্যে এবং কোথায় কোন শব্দের উপরে ঝোঁক আরোপ করতে হবে সেটার ভঙ্গীর মধ্যেই শিল্পীর চাতুর্য নিহিত থাকে। এই মানদণ্ডে বিচার করলে শরৎচন্দ্রের ভাষার কি কোন তুলনা দেখতে পাওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের যে কোন উপন্যাসের যে কোন পরিচ্ছেদের বর্ণনাংশের যে কোন পাঁচ-ছয় লাইন পর পর তুলে আভ্যন্তর পাঠের রীতিতে বিচার করলেই তাঁর শব্দপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্য, শব্দের ওজন ও সংযম, অন্বয়ের রীতি, অভীপ্সিত অর্থের স্পষ্টতা ও লক্ষ্যবেধিতা বুঝতে পারা সম্ভব। এছাড়া এথেকে অন্য যে কথাটা বুঝতে পারা যায়, সেটা হল যে— শরৎচন্দ্র মূলতঃ পল্লীভিত্তিক লেখক হলেও তাঁর ভাষাশিল্প দরবারী গুণযুক্ত, অর্থাৎ— নাগরিক ছিল। নাগরিক বৈদগ্ধ্যের সুবাসে তাঁর স্টাইল ভরপুর ছিল। ভাস্করসুলভ নিপুণযত্নে পাথর কেটে কেটে মাপজোপ করে বসানোর মত করেই তিনি তাঁর লেখার প্রতিটি শব্দকে মেপে মেপে ওজন করে বসাতেন। শুধু তাই নয়, সেই শব্দগুলির উচ্চারণগত ধ্বনি এবং পাঠক-পাঠিকার মনের উপরে সেই ধ্বনির সম্ভাবিত প্রতিক্রিয়া খুঁটিয়ে বিচার করে দেখে তবেই তিনি তাঁর সাহিত্যে শব্দগুলিকে ব্যবহার করতেন। তাঁর এই প্রক্রিয়া ভাষাশিল্পের একান্তই নাগরিক প্রক্রিয়া ছিল। মননশীলতা এর পরতে পরতে বিধৃত ছিল। সাধারণভাবে যেটাকে ‘অশিক্ষিতপটুত্ব’ কিংবা দৈবানুগ্রহপুষ্ট শিল্পশক্তি বলা হয়ে থাকে— সেটার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না; বরং এটা সম্পূর্ণভাবেই তাঁর সচেতন মনের এক শিল্পসৃষ্টি ছিল। অনুশীলন ছাড়া এই শিল্প কখনোই আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, এবং পরিমার্জনা ছাড়া এই শিল্পের সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয় না।
শরৎচন্দ্র যে কতবড় একজন ভাষাশিল্পী ছিলেন— সেটার যথাযথ মূল্যায়ণ এখনও হয়নি বলেই মনে হয়। তবে যদি কোনদিন এরকম কোন মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে— এক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু লেখককেই নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। ভাষার অসাধারণ চিত্তাকর্ষক ক্ষমতাই তাঁর হাতে বাঙালি পাঠক-পাঠিকার অন্তরে প্রবেশ করবার আসল চাবিকাঠিটি তুলে দিয়েছিল। আর বাঙালী পাঠক-পাঠিকাও যে তাঁকে নিজেদের অন্তরে অবিচলিত আসন দান করেছিলেন, সেটা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ এই ভাষার গুণে প্রভাবিত হয়েই। তাঁদের এই প্রভাবক্রিয়াটা কখনও সজাগ স্তরের তো কখনও আবার অজাগ স্তরের; সম্ভবতঃ এর মধ্যে অজাগ অংশই বেশি। বাস্তবে, সমালোচকদের মতে— বাঙালি পাঠক-পাঠিকা তাঁদের অজান্তে অথবা অর্ধজ্ঞাতসারেই শরৎ-সাহিত্যের ঐকান্তিক ভক্তে পরিণত হয়ে গিয়েছেন।
বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সাথে অল্পবিস্তর পরিচিত প্রায় সকলেই এবিষয়ে অবগত রয়েছেন যে, শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে পুরুষচরিত্রর থেকে নারীচরিত্র অঙ্কনে সমধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিলেন। আরো ভালো করে বললে— নারীচরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করতে গিয়ে সেগুলোর মধ্যে তিনি যেন তাঁর অন্তরের সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়েছিলেন। শুধু যে পল্লী বাংলার মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্ত স্তরের সাধারণ সতীসাধ্বী পতিগতপ্রাণা গৃহবধূ, বাল্যবিধবা, অরক্ষণীয়া অনূঢ়া কন্যা, প্রৌঢ়া জননী প্রভৃতি নানাধরণের নারীচিত্রই তাঁর বর্ণিতব্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল— সেটা নয়; সমাজ-পৈঠার বহির্ভূত সাধারণের অবজ্ঞাত তথাকথিত পতিতা ও ভ্রষ্টাদের উপরেও পরম ঔদার্যে তিনি তাঁর শিল্পদৃষ্টির মমত্ব অর্পণ করেছিলেন। তাদের বহিরঙ্গ ক্লেদাক্ত জীবনের অন্তরালস্থিত সহজাত নারীত্বের মহিমাকে একান্তই যত্ন সহকারে তিনি রূপায়িত করেছিলেন। আর সেজন্য সমকালীন সমাজের রক্ষণশীল অংশ থেকে তাঁকে কম নিন্দাবাদ সহ্য করতে হয়নি; কিন্তু সমস্ত কটু সমালোচনার ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে তিনি তাঁর মানবিকতার অবস্থানে অবিচলিত থেকে গিয়েছিলেন। মানুষের স্খলন-পতনকে অতিক্রম করেও যে তাঁর অন্তর্নিহিত মানব-মহিমা অজেয় থাকে— এই ভাবটিকেই তিনি বারবার তাঁর সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকার মনোযোগের সামনে অকম্পিত হস্তে তুলে ধরেছিলেন বলে দেখা যায়। তাঁর সৃষ্ট— সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী, বিজলী —প্রভৃতি চরিত্র একথার স্বপক্ষেই প্রমাণ দেয়। অন্যদিকে— বিরাজ-বৌ (বিরাজ-বৌ), সুরবালা (চরিত্রহীন), সরযূ (চন্দ্রনাথ), অন্নদাদিদি (শ্রীকান্ত), ষোড়শী (দেনা-পাওনা) —প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি পতিপ্রাণা সতী-সাধ্বী নারীর আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন। পণ্ডিতমশাই উপন্যাসের কুসুম চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি শ্বশুরকুল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা আত্মমর্যাদাদৃপ্তা নারীর মহিমাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট পল্লীসমাজের রমা— সেকালের বৈধব্যের অভিশাপদীর্ণা ও কৃত্রিম সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতির নিরন্তর সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত-হৃদয়া নারীর একটি বেদনাকরুণ উদাহরণ। বিন্দুর ছেলের বিন্দু আর রামের সুমতির নারায়ণী, বড়দিদির মাধবী আর মেজদিদির হেমাঙ্গিনীর মধ্যে স্নেহবাৎসল্যের এক অপরূপ স্নিগ্ধতার আলেখ্য প্রকাশ পেয়েছে। অরক্ষণীয়ার পোড়াকাঠ ভামিনীর চরিত্রে কোন কোন নারীর আপাত-রুক্ষতার খোলসের অন্তরালে যে স্নেহের ফল্গুধারা বহমান থাকে— সেটার দ্যুতির ঔজ্জ্বল্য রূপ পেয়েছে। এছাড়া পল্লীসমাজের জ্যেঠাইমা চরিত্রের মাধ্যমে প্রৌঢ়া জননীর বিচক্ষণ সংসারবুদ্ধি ও ন্যায়ের প্রতি পক্ষপাতের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। এসবই কিন্তু বাঙালি সংসারের কমবেশি পরিচিত কাঠামোর চিরাভ্যস্ত নারীরূপের ছবি। তবে শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রের মিছিল এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। এসব ছাড়াও তিনি কতগুলি বিদ্রোহিনী নারী চরিত্রও সৃষ্টি করেছিলেন; যেমন— অভয়া (শ্রীকান্ত ২য় পর্ব), সুনন্দা (শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব), কিরণময়ী (চরিত্রহীন), কমল (শেষ প্রশ্ন) প্রভৃতি। অভয়া তাঁর নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সন্ধানে প্রতিবেশী যুবক রোহিণীকে সঙ্গে নিয়ে বর্মা মুলুকে পৌঁছেছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর স্বামীর খোঁজ পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু একইসাথে তাঁর কদর্য জীবনযাত্রা ও ততোধিক বিকৃত রুচির পরিচয় পেয়ে স্বামীর সঙ্গে একত্রে ঘর করবার ইচ্ছা তাঁর মধ্যে থেকে উবে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে রোহিণী তাঁকে মনে মনে ভালবাসে ফেলেছিলেন। আর তাই রোহিণীর প্রেমকে মর্যাদা দিয়ে অভয়া তাঁরই সঙ্গে সেখানে ঘর বাঁধেছিলেন ও স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করতে শুরু করেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, সেযুগের নিরিখে শরৎচন্দ্র তাঁর অভয়া চরিত্রটিকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সাহসিকভাবে গড়ে তুলেছিলেন। বাস্তবের পুরুষ শাসিত সমাজের পুরুষের স্বার্থানুকূল একতরফা অনুশাসনাদির বিরুদ্ধে অভয়া আজও একজন মূর্তিমতী বিদ্রোহিনী নারী হিসেবেই থেকে গিয়েছেন। পুরুষ দাম্পত্যজীবনের পবিত্রতাকে নষ্ট করে কদাচারী হলেও তাঁর কোন সাজা হয় না, কিন্তু নারী একটু বেচাল হলেই তাঁর উপরে সমাজের রোষ বজ্রাগ্নির মতোই নেমে আসে— শরৎচন্দ্রের অভয়া তাঁর ভয়শূন্য এই আচরণের মধ্যে দিয়েই এই নিতান্ত অন্যায্য সংস্কারটাকেই আঘাত করতে চেয়েছিলেন। সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের বিস্তৃত আয়তনের ভিতরে অভয়ার তুল্য নির্ভীক দ্বিতীয় অন্য কোন চরিত্র কিন্তু পাওয়া যায় না। শরৎচন্দ্র যে প্রয়োজনবোধে কতটা বিপ্লবী হতে পারতেন— সেটার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তাঁর সৃষ্ট অভয়া চরিত্রের মধ্যেই রয়েছে।
শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বের সুনন্দাও শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট আরেকটি বিদ্রোহিনী নারীচরিত্র। তবে তাঁর বিদ্রোহের জাত আলাদা ও কারণও ভিন্ন। বস্তুতঃ জৈব জীবনের সমস্যাদির সঙ্গে তাঁর সেই বিদ্রোহের কোন সম্পর্ক নেই। সুনন্দা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা ছিলেন, বধূ হয়ে শ্বশুরগৃহে আসবার পরে শ্বশুরকুলের সকলের স্নেহ ও আদরে তাঁর দিনগুলি বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু একটি অন্যায়ের প্রতিবিধানে তেজস্বিনী প্রতিবাদিনীর ভূমিকা গ্রহণ করে তিনি এক আশ্চর্য চরিত্র-মহিমার পরিচয় দিয়েছিলেন। কোন একটি ঘটনাক্রমে তিনি যেদিন জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর ভাশুরের অর্জিত সম্পত্তির একটা অংশ আসলে একজন অনাথিনী তাঁতি-বৌ ও তাঁর শিশুপুত্রকে ঠকিয়ে কৌশলে কেনা সম্পত্তি, সেদিন তিনি মুহূর্তমাত্রেরও দ্বিধা না করেই নিজের স্বামী-পুত্রের হাত ধরে শ্বশুরের ভিটা ত্যাগ করে একটি পোড়ো বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং নিজের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার শত উপরোধেও আর কখনো প্রাচুর্যের সংসারে ফিরে যাননি। অন্যায়কে রুখতে গিয়ে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণের এই গৌরবজনক ঘটনা আরও যে কারণে মহিমান্বিত হয়েছে, সেটা হল যে— এক্ষেত্রে অন্যায়-অসহিষ্ণুতা সেকালের একজন গ্রাম্য নারীর কাছ থেকে এসেছিল, যে শ্রেণীর নারীরা তখন জমিজিরাত সংক্রান্ত বৈষয়িক ব্যাপারে পুরুষের প্রশ্নহীন আনুগত্যকে স্বীকার করে নিতেই সচরাচর অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সুনন্দার ভেতরে সেই তেজটুকু যে কোথা থেকে এসেছিল— সেকথা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। তাঁর সেই তেজের উৎস ছিল, তাঁর সন্ন্যাসীকল্প শাস্ত্রজ্ঞ পিতার শিক্ষা, যে শিক্ষায় ধর্মকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছিল। বাংলার অজপাড়াগাঁর অভ্যন্তরেও যে এমন একটি মহীয়সী নারীচরিত্র থাকতে পারে— সেটা একটা শুভলক্ষণ ও সর্ববিধ প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করেও বাঙালি জাতির টিকে থাকবার পক্ষে একটা মস্ত বড় যুক্তি। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যের অনেক চরিত্রকেই বাস্তব জীবন থেকে তুলে এনেছিলেন বলে জানা যায়। সেইমত তাঁর সুনন্দা চরিত্রটিরও কোন বাস্তব ভিত্তি আছে কিনা— সেকথা বলা সম্ভব নয়, তবে এটি যদি তাঁর কল্পিত কোন চরিত্রও হয়— তাহলেও এর মূল্য কিন্তু কোনভাবেই কমে যায় না। বাস্তবে এই চরিত্রটির সম্ভাব্যতা তথা প্রতীতি-যোগ্যতার মধ্যেই এর শক্তি নিহিত রয়েছে বলে দেখা যায়।
শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী এরকমই আরেকটি অত্যাশ্চর্য চরিত্র। এমনকি তাঁর শেষ প্রশ্নের কমলও এমন বুদ্ধিদীপ্ত সপ্রতিভ সর্বসংস্কার-মুক্ত সনাতন শাস্ত্র শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী নারী নন। কমলের সঙ্গে কিরণময়ীর মূলগত পার্থক্য হল যে, কমল মুখে সনাতন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল্যবোধগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও আচরণে ভারতীয় নারীর স্বভাবগত সংযমেই বৃতা ছিলেন। তিনি একাদশী তিথিতে হবিষ্যান্ন করতেন, প্রায়ই আলু-ভাতে ভাত ফুটিয়ে খেতেন, কঠোর নিয়ম-শাসনে তাঁর জীবন বোধ ছিল। কিন্তু কিরণময়ীর সেসবের কোন বালাই ছিল না। তিনি নিজের বিশ্বাস অনুযায়ীই চলতেন। তিনি ঈশ্বর মানতেন না, শাস্ত্রের পবিত্রতায় বিশ্বাস করতেন না, এমনকি ভোগবাসনাবঞ্চিত রিক্ত নারীজীবনে স্বামীর বর্তমানেই তিনি অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে অনুচিত সম্পর্কের সৃষ্টি করেছিলেন। প্রতিহিংসার তাড়নায় পত্নীপ্রেমে মাতোয়ারা এবং তাঁর প্রতি উদাসীন উপেন্দ্রকে জব্দ করবার মতলবে তাঁর অনভিজ্ঞ ভাই দিবাকরকে প্রলুব্ধ করে তিনি বর্মা মুল্লুকে তাঁকে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই স্বৈরাচার একজন অশিক্ষিতা নারীর স্বৈরাচার ছিল না, বাস্তবে এর পিছনে বুদ্ধি দিয়ে আচরণকে সমর্থন করবার প্রখর মননশীলতা ছিল। শাস্ত্র পড়েই তিনি শাস্ত্রকে অস্বীকার করতে শিখেছিলেন। স্বামী বেঁচে থাকতে স্বামীর সাহায্যে শাস্ত্রগ্রন্থগুলি তিনি তন্ন তন্ন করে ঘেঁটেছিলেন, এরফলে শাস্ত্রনির্মাতা পুরুষদের কাপট্য আর ভণ্ডামিটাই শুধু তাঁর চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করবার কোন কারণ তিনি খুঁজে পাননি। কিন্তু এমন যে সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী কিরণময়ী, তিনিও কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি। নিজের বুদ্ধি আর প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হয়ে তিনিও শেষপর্যন্ত পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র শেষপর্যন্ত তাঁকে পাগল বানিয়েছিলেন কেন? তিনি কি কিরণময়ীকে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসে বিজয়িনী রেখে চরিত্রহীন উপন্যাসের অন্য কোন উপসংহার করতে পারতেন না? এখানেই শরৎচন্দ্রকে নিয়ে ধাঁধার সৃষ্টি হয়, আর এই ধাঁধার উন্মোচন প্রচেষ্টার মধ্যেই শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের দ্বৈধতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।
অনেকের মতে— শরৎচন্দ্র একইকালে একজন প্রথম শ্রেণীর বিদ্রোহী লেখক ও রক্ষণশীল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। রাঢ়দেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণের মজ্জাগত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার থেকে তিনি যেখানে তাঁর রক্ষণশীলতা পেয়েছিলেন, সেখানে নিজের বাউন্ডুলে ভ্রাম্যমাণ ভবঘুরে জীবনযাত্রার ছক থেকেই তিনি বিদ্রোহের প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাই কৌলিক সংস্কারে যেখানে তিনি রক্ষণশীল, সেখানে জীবনাচরণে তিনি বিদ্রোহী ও বিপ্লবী ছিলেন। তাঁর এই দুই প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতে কখনও রক্ষণশীল সত্তা জয়ী হয়েছিল, তো কখনও আবার তাঁর বিদ্রোহী সত্তা বিজয়ী হয়েছিল। আলোচ্য ক্ষেত্রে, অর্থাৎ— কিরণময়ীর পরিণাম চিত্রণে, শরৎচন্দ্র বস্তুতঃ রক্ষণশীলতার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন। খুব সম্ভবতঃ নিতান্তই ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েই তিনি এই কাজটি করেছিলেন। তখন এই ব্যাপারে তাঁর সামনে দুটি দৃষ্টান্ত পূর্ব-উদাহরণের কাজ করেছিল; যথা— বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসের শেষে কুন্দনন্দিনীর বিষপানে আত্মহত্যা ও কৃষ্ণকান্তের উইলের শেষে রিভলভারের গুলিতে স্বৈরিণী বিধবা রোহিণীর হত্যা। তবে শরৎচন্দ্র অবশ্য আত্মহত্যা বা হত্যার পথে যাননি, বরং মস্তিষ্কবিকৃতির পথেই তিনি কিরণময়ীর ‘উন্মার্গগামিতার’ শাস্তিবিধান করেছিলেন। তাতে ফল সেই একই হয়েছিল। কারণ— আত্মহত্যা বা হত্যা জনিত মৃত্যুই হোক আর উন্মাদাবস্থাই হোক, —লৌকিক বিচারে দু’ধরণের অবস্থাই কিন্তু মৃত্যুর সামিল। তাছাড়া এক্ষেত্রে পূর্বসূরীর দৃষ্টান্ত ছাড়াও কিছু বস্তুগত কারণও শরৎচন্দ্রকে রক্ষণশীলতার অনুকূলে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। অন্ততঃ এবিষয়ে শরৎচন্দ্রের লেখা চিঠিপত্র থেকে সেটাই খানিকটা আঁচ করা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তাঁর চরিত্রহীন উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে মাসিক ‘ভারতবর্ষ’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার কথা থাকলেও, পত্রিকাটির তৎকালীন পরিচালকবৃন্দ উক্ত উপন্যাসটিকে ‘immoral’ বলে মত প্রকাশ করে শরৎচন্দ্রকে এর পাণ্ডুলিপিটি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। স্বভাবতঃই শরৎচন্দ্র তাতে অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে তখন তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে, যিনি নিজেও তখন ভারতবর্ষ পত্রিকাটি পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি চিঠিতে নিতান্ত আক্ষেপের সুরে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর এই উপন্যাসটিকে ‘immoral’ বলায় ভারতবর্ষ পত্রিকার পরিচালকদের গোঁড়ামিই শুধু প্রকাশ পেয়েছে, এতে তাঁদের সাহিত্যবুদ্ধি প্রকাশ পায়নি। এবং তাঁদের সকলেরই যখন এত আপত্তি, সেজন্য—
“যাতে এটা in strictest sense moral হয় তাই উপসংহার করিব।” (শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ, দ্বাদশ সম্ভার, পত্র-সংকলন, পৃ- ৩৬৩)
এরই ফলে তিনি কিরণময়ী চরিত্রটির এমনতর পরিণতি করেছিলেন। যদিও এই পরিণতিটি তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা প্রসূত ছিল না, বরং তাঁর অভিমান প্রসূত ছিল, তবুও এটিকে অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। বিদ্রোহের আবেশ এবং রক্ষণশীলতার সংকোচনী প্রবৃত্তির মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্বের ফলে কিরণময়ী চরিত্রে যে ‘tension’–এর সৃষ্টি হয়েছিল, সেটার পরিণামে কিরণময়ীর পাগল হয়ে যাওয়াটা কিছুই বেমানান হয়নি; বাস্তবে এমন ক্ষেত্রে এরকম হওয়াই সম্ভব।#