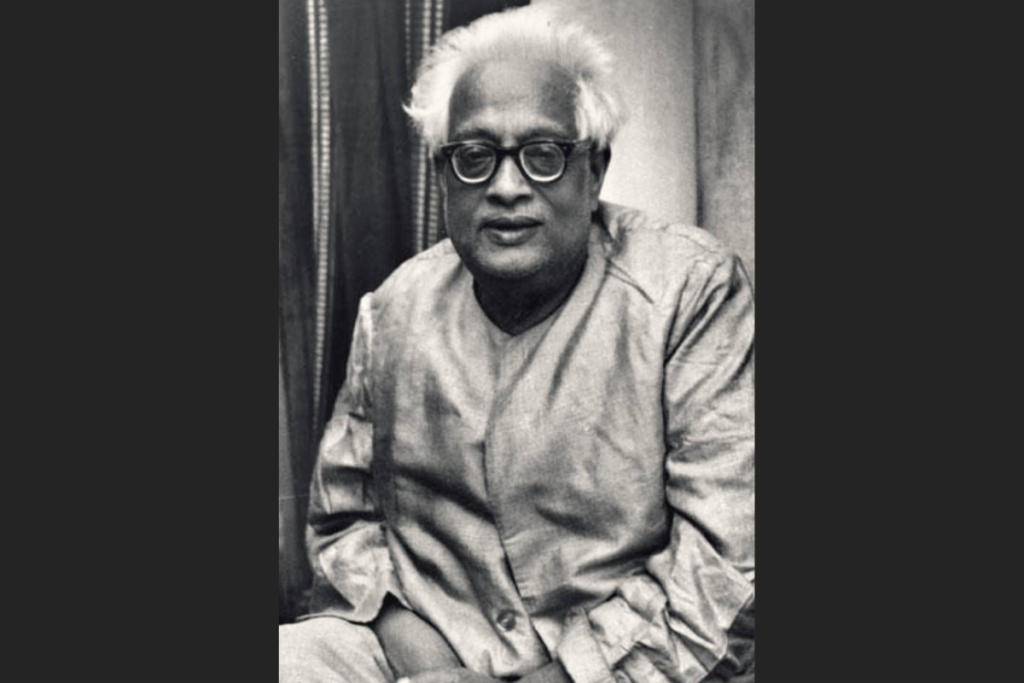বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অন্যতম সুহৃদ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ একবার তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন – “আচার্য বসুর বৈজ্ঞানিক দিকটা যদিও বা বাইরে থেকে কিছুটা বোঝা যায়, কিন্তু মানুষ সত্যেন্দ্রনাথকে বোঝা খুব সোজা নয়।” আর তাঁর ছাত্র রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন – “সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি অনেক পরে – তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসার পর। দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁর সান্নিধ্যে থেকে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রে যে সকল মহান দিকের পরিচয় পেযেছি তাতে মুগ্ধ অভিভূত হয়েছি। এক এক সময় মনে হয়েছে বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি আমাদের মনকে যতখানি টেনেছেন তার চেযেও বোধ হয় বেশি টেনেছেন মানুষ হিসাবে। তবু কতটুকুই বা আমরা তাঁকে মানুষ হিসাবে জানতে পেরেছি আমাদের স্বল্পপরিসর সান্নিধ্যে আসার সুযোগে।” তাই সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অন্তরঙ্গ বন্ধু, সহপাঠী, সহকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতিচারণের সাহায্য নিয়ে মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রচিত্রণ করবার ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।
সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু দিলীপকুমার রায় তাঁর ‘স্মৃতিচারণ’ গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছিলেন – “আজ পর্যন্ত এক সুভাষ (নেতাজী সুভাষচন্দ্র) ছাড়া আর কোনো বন্ধুই আমার চিত্তকে সত্যেনের মতন অধিকার করতে পারে নি। যদিও বন্ধু হিসেবে আমার কাছে সুভাষ হয়ে উঠেছিল হিরো-ই বলব, তবু সত্যেনের কাছেও আমি জীবনে কম পাথেয় পাই নি – বিশেষ করে চিন্তা, সংস্কৃতি ও স্বাধীন চিন্তার রাজ্যে। … আমি ওকে ভালবেসেছিলাম প্রধানতঃ তিনটি কারণে – ওর অসামান্য স্নেহশক্তির জন্যে, ওর দৃঢ়মূল সত্যনিষ্ঠার জন্যে, ওর বহুমুখী অনুসন্ধিৎসার জন্যে।”
সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে যে স্নেহশীল দরদী মনটি একটি নদীর মত নিত্যপ্রবাহিত ছিল, সেটার স্পর্শ যিনি একবার পেয়েছিলেন তিনিই বুঝতে পেরেছিলেন যে – তাঁর সেই স্নেহ ও দরদ – কতটা গভীর ও অন্তরস্পর্শী ছিল। এবং তাঁর সেই স্নেহ-দরদ শুধুমাত্র পরিচিত পরিজন, বন্ধু-বান্ধব বা স্নেহভাজন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই সীমিত ছিল না, অপরিচিতজনের প্রতিও অবারিত ছিল। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই ছিল যে, তিনি ছোট বড় পরিচিত-অপরিচিত সকলকেই নিজের সহজিয়া ছন্দে আপন করে নিতে পারতেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতি-ভালবাসার মূল্য সত্যেন্দ্রনাথের কাছে অপরিসীম ছিল। তাই তিনি একবার বলেছিলেন – “আমার ছাত্রজীবনের সবচেয়ে বড় লাভ বইপত্র অধ্যাপকদের লেকচার নয়, সতীর্থদেব সঙ্গে নিত্য-নতুন প্রীতির সম্বন্ধের মধ্য দিয়েই আমি পথচলার সবচেয়ে বেশি পাথেয় পেয়েছি। যাঁরা শুধু পড়াশোনায় ভালো ছেলে তাঁরা তথ্যের বা জ্ঞানের কোঠায় হয়ত সবই পেতে পারে, কিন্তু পায় না বহুর অমূল্য সংস্পর্শের মনজাগানিয়া দান। আমাদের তরুণ মন সত্যি জেগে ওঠার জন্যে এই সখ্যের অপেক্ষা রাখে, বিশেষ করে কৈশোরে ও যৌবনে।”
সত্যেন্দ্রনাথ এভাবেই তাঁর সহপাঠীদের সঙ্গে মিশেছিলেন, নানাজনকে বন্ধু ভাবে নিজের জীবনে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তাঁর সেই গভীর বন্ধুপ্রীতি ও অনাড়ম্বর অন্তরঙ্গতার কথা বলতে গিয়ে দিলীপকুমার রায় বলেছিলেন – “মেলামেশার মধ্য দিয়ে সে অনেক কিছু আহরণ করত বলেই পারত অনেক কিছু দান করতে। … বন্ধুদের দৈনন্দিন জীবনের হাজারো খুঁটিনাটি ও সমস্যার কথা শুনতে সে কখনো বিরক্ত হত না। তাই অনেকেই দেখতাম তাঁর কাছে এসে ধর্না দিত সমাধান চেয়ে। এঁদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন প্রধান প্রষ্টা – প্রায় নচিকেতার কাছাকাছি: যখনই কোনো প্রশ্ন কি সমস্যা হাজিরি দিত সটান তাঁর কাছে এসে দরবার করতাম। এমন বন্ধুগতপ্রাণ মানুষ পিতৃদেবের পরে আর আমি দেখি নি। যাঁকেই একবার বন্ধু বলবে তাঁরই খোঁজ নেবে যথাসাধ্য। আমার এক ধনী জমিদার বন্ধু পাকীস্তানের ফেরে পড়ে যখন বৃদ্ধ বয়সে দেউলে হয়ে দিল্লীতে চাকরি নেন, সত্যেন খুঁজে খুঁজে তাঁর দীন ডেরায় গিয়ে হাজির। তখন দিল্লীতে সে রাজ্যসভার সভ্য, মস্ত লোক। কিন্তু তাঁর কাছে ধনী-গরিব, বড়-ছোট ছিল না – বন্ধু হলেই হল।”
সাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘ঝিলিমিলি’ নামক রচনায় সত্যেন্দ্রনাথের সেই দরদভরা বন্ধুপ্রীতির আরেকটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন – “সেবার Indian Science Association-এর বাৎসরিক সভায় (Indian Science Congress, দিল্লী অধিবেশন, ১৯৪৪) সত্যেন সভাপতিত্ব করছে। সন্ধ্যায় ভারতবর্ষের লাট ওয়াভেল সাহেব সকলকে খানা দিলেন। সেদিনকার সত্যেনই প্রধান অতিথি, আশা করেছিলেন সে এসে পৌঁছবে। রাত ৯টা পর্যন্ত এলো না – তারপরও নয়। ব্যাপারটা হয়েছিল এই – দুপুর বেলা একজন পুরাতন স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা; তাঁরই সঙ্গে টাঙ্গা চড়ে তাঁর বাড়ি হাজির এবং সেইখানেই সারাদিন সে আর তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করল, রাত্রে খেয়েও এলো। ওয়াভেল সাহেবের সাথে আর দেখা হল। নাপরের দিন লেডি ওয়াভেল জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কি হল Sailor boy! এলে না কেন? আমরা সব তোমার জন্য বসেছিলাম।’ আমতা আমতা করে একটা জবাব খাড়া করলে। সে ক’দিন কলকাতার চাঁদনী থেকে কেনা একটা টুপি সারাদিন মাথায় পরেছিল। জামাকাপড়েরও সেই দশা।”
সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয় উজাড় করা বন্ধুপ্রীতির আরেকটি অনুপম কাহিনী অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীরের স্মৃতিচারণে পাওয়া যায়। তিনি জানিয়েছিলেন – “আমার সমসাময়িক বন্ধু পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (ঢাকার বারোজনার তিনি ছিলেন অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক) ছিলেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। পরে তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে এসেছিলেন। বহুদিন রোগভোগের পর প্রায় তিন বছর হলো তাঁর দেহাবসান হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ পুণ্যেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন, পুণ্যেন্দ্রনাথও সত্যেন্দ্রনাথকে বড় ভাই-এর মতো শ্রদ্ধা করতেন। পুণ্যেন্দ্রনাথের মতো ন্যায়পরায়ণ, ধীমান, সদালাপী ও বন্ধুবৎসল মানুষ খুব কমই দেখা যায়। মাঝে মাঝে হঠাৎ তাঁর মস্তিষ্কের বিকৃতি হত। এই অবস্থায় তাঁকে সামলানো খুবই মুস্কিলের ব্যাপার ছিল। কতবার দেখেছি পুণ্যেন্দ্রনাথের এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় পারিবারিক নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের বাড়িতে এনে শুশ্রুষা করেছেন, নিজের হাতে দাড়ি কামিয়ে দিয়েছেন এবং স্নান করিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছেন। কলকাতায় যখন পুণ্যেন্দ্রনাথ বহুদিন অসুস্থ – রোগশয্যায় তাঁর সেবা ও সাহায্য পুণ্যেন্দ্রনাথের সহধর্মিণীর মনে শক্তি দিয়েছে। পুণ্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময়েও সত্যেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। পরের জন্যে নিজেকে এমনভাবে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে কয়জন পারেন?”
সত্যেন্দ্রনাথের এই দরদভরা বন্ধুপ্রীতির মত তাঁর বন্ধুকৃত্যও গভীর ছিল। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর কয়েক মাস আগে সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু অতুলচন্দ্র গুপ্ত দেহ রেখেছিলেন। অতুলচন্দ্র বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি পদে আসীন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে সেই সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সেই বছরের অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ গ্রহণ করবার প্রস্তাব নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। নিজের পরলোকগত বন্ধুর কথা স্মরণ করে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের সেই প্রস্তাবে সানন্দেই সম্মত হয়েছিলেন। এরপরে সম্মেলনের উদ্বোধনের দিনে উদ্যোক্তারা সত্যেন্দ্রনাথকে সমাদরে অনুষ্ঠানক্ষেত্রে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল যে, অতুলচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্যে তাঁরা যে বিশেষ সভার আয়োজন করেছিলেন, সেই সভার কথা সত্যেন্দ্রনাথকে জানাবার প্রয়োজনবোধ করেন নি। সেবারের সম্মেলন সমাপ্ত হওয়ার পরে আরেকদিন অন্য কোন উপলক্ষ্যে উদ্যোক্তারা যখন সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানাতে এসেছিলেন, সেদিন সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধকণ্ঠে তাঁদের বলেছিলেন – “আমার বন্ধুর নাম করে তোমরা আমাকে সভাপতি হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলে, কিন্তু বন্ধুর স্মৃতি সভার দিন আমাকে একবার খবর পর্যন্ত দিলে না!” উদ্যোক্তারা আমতা আমতা করে উত্তর দিয়েছিলেন – “আমরা ভেবেছিলাম যে, আপনি ওদিন যেতে পারবেন না। তাই আপনাকে আর বলি নি।” তাঁদের কথা শুনে স্মিত হেসে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন – “তোমরা একবার বলে দেখতেও তো পারতে আমি যেতুম কিনা। আমাকে সভাপতি করলে, অথচ আমার বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগই তোমরা আমায় দিলে না!” সেদিন সেখানে উপস্থিত সকলেই – বন্ধুকৃত্য সম্পাদন করতে না পারবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথের দুঃখ ও ক্ষোভের গভীরতা টের পেয়েছিলেন।
সত্যেন্দ্রনাথের সেই দরদী অন্তরের স্পর্শ তাঁর বন্ধুজন ও সহকর্মীরা যেমন পেয়েছিলেন, তেমনি সেকালের বয়োকনিষ্ঠরাও তাঁর হৃদয়ভরা স্নেহে নিত্য অভিষিক্ত হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ – সব ছাত্র-ছাত্রীর কাছেই তিনি ‘মাস্টারমশাই’ বলে পরিচিত ছিলেন। ছাত্রছাত্রীদেব কাছে তিনি শুধুমাত্র একজন শিক্ষাদাতা গুরু ছিলেন না, তাঁদের সুখদুঃখের সমব্যথী অভিভাবকস্বরূপও ছিলেন। তিনি যেমন তাঁদের কাজ-কর্মের খবর নিতেন, তেমনি তাঁদের পারিবারিক খবর নিতেও ভুলতেন না। এই প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর ছাত্র রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন – “তাঁর কাছে কোনো কাজ উপলক্ষে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি, কাজের কথা হবার পর তিনি আপনা থেকেই জিজ্ঞেস করেন – ‘তোর বাবা কেমন আছেন? তোর মা কেমন আছেন? তোর দাদা এখন কোথায়?’ এমন আরও কত স্নেহভরা প্রশ্ন। অনেক সময় দেখেছি তিনি দরকারী কথা বরং ভুলে যান, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক দুঃখ দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার কথা (যা তাঁর মনে না থাকাই স্বাভাবিক) ঠিক মনে রাখেন এবং সেবিষয়ে খবরও নেন। … তাঁর বাড়িতে দেখা করতে গেলে তিনি অধিকাংশ সময়েই এটা ওটা না খাইয়ে ছাড়েন না। আমাদের অনেক সময় খেতে সংকোচ বোধ হয়। কিন্তু তিনি তা দেখে বলতে আরম্ভ করেন – ‘এই তুই খাচ্ছিস না যে! চা খেলি শুধু, মিষ্টিটাও খেয়ে নে।’ …”
ছাত্র বা স্নেহভাজনদের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের মমত্ববোধ ও দরদ যে কত গভীর ছিল, সেটার উদাহরণস্বরূপ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ থেকে আরেকটি অতুলনীয় ঘটনাকে এখানে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। ১৯৫৮ সালে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ জব্বলপুরে আয়োজিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির পদে আসীন ছিলেন। সেবারে তাঁর সঙ্গে রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ও ওই সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসাবে অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। তারপরে রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের ভাষায় – “এক রাত্রি ট্রেনে অতিবাহিত হবার পর দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় বোম্বাই মেল যখন জব্বলপুর স্টেশনে এসে পৌঁছল, তখন প্ল্যাটফরমে অভ্যর্থনা সমিতির কর্মকর্তাদের বিশেষ কাউকে দেখা গেল না। মাস্টার মশাই বললেন, ‘চল, আমরা স্টেশনের বাইরে যাই, সেখানে হয়তো কর্তা-ব্যক্তিদের দেখা পাওয়া যাবে।’ কুলীর মাথায় বিছানাপত্র চাপিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে দেখা গেল, অভ্যর্থনা সমিতির কর্তাব্যক্তি দু’-একজন সেখানে সত্যিই উপস্থিত রয়েছেন। মাস্টার মশাই তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমাদের থাকবার ব্যবস্থা কোথায় হয়েছে?’ স্থানীয় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী এগিয়ে এসে বললেন, ‘আপনি আমার বাসায় চলুন, সেখানে আপনার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।’ উত্তরে মাস্টার মশাই (লেখককে দেখিয়ে) তাঁকে বললেন, ‘আমার সঙ্গে আমার এই ছাত্রটি থাকবে। আপনার ওখানে আমাদের দুজনের জায়গা হবে তো?’ একথা শুনে প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী কোনো উত্তর দিলেন না। মাস্টার মশাই আরও দু’বার পুর্বোক্ত কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী পূর্বের মতোই চুপ করে রইলেন। সামনে দাঁড়িয়েছিলেন স্থানীয় মহাকোশল মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল মুখার্জি। মাস্টার মশাই তাঁকে দেখে বললেন, ‘মুখুজ্জে মশাই, আপনার ওখানে আমাদের দু’জনের জায়গা হবে?’ প্রিন্সিপাল মুখার্জি সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজী হলেন। সেই অনুযায়ী আমরা যখন মুখুজ্জে মশায়ের গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় প্রিন্সিপাল চক্রবর্তীর স্ত্রী শ্রীমতী চক্রবর্তী এসে হাজির হলেন। তিনি মাস্টার মশায়ের পথ রোধ করে বললেন, ‘আমি সকাল থেকে আপনার জন্যে রান্নার আয়োজন করেছি আর আপনি মুখুজ্জে মশায়ের বাড়িতে যাবেন, তা কেমন কবে হবে?’ মাস্টার মশাই তাঁকে সবিনয়ে জানালেন, ‘আমি মুখুজ্জে মশাইকে কথা দিয়ে ফেলেছি, তাঁর ওখানেই এখন যাই। পরে আপনাদের বাড়িতে যাব।’ একথা শুনে শ্রীমতী চক্রবর্তী বেশ ক্ষুব্ধ হলেন মনে হলো। আর কোনো কথা না বলে সটান তাঁর গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। পরে মুখুজ্জে মশায়ের বাড়িতে এসে মাস্টার মশাই বললেন, ‘দ্যাখ, আমি ভদ্রলোককে তিন তিনবার বললুম, আমার সঙ্গে আমার ছাত্রটি না থাকলে অসুবিধে হবে। কিন্তু ভদ্রলোক একবারও হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না। মনে হলো ভদ্রলোক বোধ হয় আমাদের দু’জনকে একসঙ্গে রাখতে চান না। তাই ওঁর ওখানে আর গেলুম না।’ পরের দিন ভোরে উঠেই মাস্টার মশাই বললেন (শ্রীমতী চক্রবর্তীর কথা উল্লেখ করে), ‘ভদ্রমহিলা বড়ো চটে গেছেন রে। ওঁর ওখানে একবার গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসি।’ এবং সত্যিসত্যিই তিনি মুখুজ্জে মশায়ের গাড়িতে করে প্রিন্সিপাল চক্রবর্তীর বাড়িতে দেখা করতে গেলেন। এই হচ্ছেন দরদী মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ যিনি একদিকে যেমন ছাত্রের কথা ভেবে নিজের সমাদর স্বেচ্ছায় পরিহার করতে পারেন, আবার তেমনি তাঁর কথায় কেউ আঘাত পেলে তাঁকে শান্ত করতে নিজেই ছুটে যান।”
আলোচনা প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্রবাৎসল্যের আরেকটি মনোজ্ঞ ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেবারে তাঁর একজন প্রিয় ছাত্র বিদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের গবেষণা বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু তখন তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন, সেখানকার কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছুটি মঞ্জুর করবার বিষয়ে গড়িমসি করতে শুরু করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ সেকথা জানতে পেরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের কাছে সরাসরি একটি চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে ছাত্রটির ছুটি তো মঞ্জুর হয়েছিলই, এবং একইসঙ্গে ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তর থেকে বিদেশে যাওয়ার খরচ বাবদ তিনি অর্থসাহায্যও লাভ করেছিলেন। এরপরে বিদেশযাত্রা করবার আগে সেই ছাত্রটি যখন অধ্যাপক বসুকে প্রণাম করবার জন্য এসেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ তখন তাঁর যাত্রার সময়টি জেনে নিয়ে নিজে বিমানবন্দরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন; এবং বিদেশের অধ্যাপকদের উপহার কোনকিছু উপহার দেওয়ার কথা ওঠায় নিজের কেনা শান্তিনিকেতনের চামড়ার কাজ করা একটি সুদৃশ্য বাক্স সেই ছাত্রটির হাতে দিয়ে তাঁকে বলেছিলেন – “এটা কাউকে উপহার দিস।”
এবারে মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহশীল হৃদয়বত্তার আরেকটি ছোট ঘটনার কথা উল্লেখ করে প্রসঙ্গান্তরে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে তাঁর অধীনস্থ একজন কর্মী মাঝে মধ্যেই তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে অর্থসাহায্য নিতেন। একবার তিনি তাঁর ঘরে বসে কাজ করছিলেন, এমন সময়ে সেই কর্মীটি এসে তাঁর কাছে কিছু অর্থ সাহায্য চেয়েছিলেন। সেদিন তাঁর মনিব্যাগে টাকা-পয়সা বিশেষ ছিল না। তবুও যা কিছু ছিল, সেগুলো সমেত ব্যাগটি উপুড় করে সবকিছু টেবিলের উপরে ঢেলে কর্মীটির হাতে তুলে দিয়ে তিনি তাঁকে বলেছিলেন – “ব্যাগে যা ছিল সবই তোকে দিলুম। আজ এখন যা।”
সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহভালবাসা শুধুমাত্র মানুষের প্রতিই বর্ষিত হয়নি, জীবজন্তুর প্রতিও তাঁব স্নেহ মমতা কম কিছু ছিল না। তাঁর পোষা একটি কুকুর ও দুটি বেড়াল ছিল। একটি বেড়ালের নাম ছিল কেলো এবং অপরটির নাম ছিল গদা। সত্যেন্দ্রনাথ তাদের আদর করতেন, নিজের খাবারের ভাগ দিতেন। অনেক সময়ে সেই বেড়ালগুলি তাঁর বিছানায় উঠে সুখনিদ্রাও দিত। এছাড়া অনেক সময়ে সেগুলি টেবিলের উপরে রাখা তাঁর দরকারি কাগজপত্রের উপরেও শুয়ে বসে ঘুমিয়ে নিজেদের সময় কাটাত।
সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রে নিঃস্বার্থ ভালবাসার পরে তাঁর যে মহৎ দিকটি সকলকে আকৃষ্ট করেছিল, সেটা ছিল তাঁর আত্মউদাসীন নিরহঙ্কার ভাব। বর্তমানযুগে স্বল্পখ্যাত ব্যক্তিরাও যেখানে আত্মপ্রচারে পঞ্চমুখ থাকেন এবং সেটার জন্য তাঁরা অপরিসীম আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন, সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে প্রভূত যশের অধিকারী হয়েও বরাবরই নিজের সম্বন্ধে একেবারে নীবব ও উদাসীন ছিলেন। নিজের বা নিজের কাজগুলি সম্বন্ধে কোনো কথাই তিনি সচরাচর বলতে চাইতেন না এবং তাঁর নাম প্রচার করবার জন্য কোনো আয়োজন করা হলে, তিনি সযত্নেই সেটাকে এড়িয়ে যেতেন। সত্যেন্দ্রনাথের এহেন আত্ম-উদাসীনতার একটি অনুপম ঘটনার চিত্র গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণে পাওয়া যায়। এটি ১৯২৪-২৫ সালের কথা। সত্যেন্দ্রনাথ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের জন্য বিদেশযাত্রা করে প্যারিসে অবস্থান করছিলেন। প্যারিসে – ‘17, Rue du Sommerard’ – ঠিকানায় থাকা ভারতীয় ছাত্রসংসদের একটি আশ্রয়স্থলে সত্যেন্দ্রনাথ, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও গিরিজাপতি একত্রে ছিলেন। সেই ঘটনা প্রসঙ্গে গিরিজাপতি জানিয়েছিলেন – “একদিন সারা রাত বরফ পড়েছে। সকালে উঠে দেখি, পেঁজা তুলোর মত সাদা বরফে চারিদিক রাস্তা বাড়ি ছেয়ে গেছে। কনকনে ঠাণ্ডা। সত্যেন্দ্রনাথের ঘরে এলাম। তিনি শোকোনা (কোকো) আনবার আদেশ দিয়ে আইনষ্টাইনের মন্তব্য সম্বলিত ছাপানো গবেষণার একটি কপি হাতে দিলেন। সেটি নিয়ে আমি যথাসাধ্য বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ব্যাপারটি মোটামুটি বুঝিয়ে দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ মূল ইটালিয়ান ভাষায় লেখা Dante-র ‘The Divina Commedia’-তে মনোনিবেশ করলেন। বইটি সবে সেদিন সকালে পড়তে সুরু করেছিলেন; ছাপানো গবেষণার কপিগুলি সদ্য সেই সময় তাঁর হাতে এসেছিল। আমি গবেষণার বিষয়বস্তু ও আইনষ্টাইনের চিন্তায় নিমগ্ন হলাম। আর সত্যেন্দ্রনাথ একটানা দান্তে পড়ে শেষ করলেন। তাঁর গবেষণা আইনষ্টাইন কর্তৃক সমর্থিত, আদৃত ও প্রকাশিত হয়ে বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চলেছে, এ ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপমাত্র করলেন না। বই পড়া শেষ করে আমাকে নিয়ে একত্রে বরফ পড়ার মধ্যেই ‘লাঞ্চ’ খেতে বেরিয়ে পড়লেন।”
সত্যেন্দ্রনাথের সেই আত্ম-উদাসীনতা শুধুমাত্র তাঁর নিজের নাম বা নিজের কাজের প্রচারের বিমুখতার মধ্যেই সীমিত ছিল না, তাঁর সাংসারিক বা বৈষয়িক উদাসীনতার মাধ্যমেও সেটা বহুবার প্রকাশিত হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীরের স্মৃতিচারণ থেকে তেমনই একটি ঘটনার কথা জানা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ ১৯৪৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হয়ে চলে আসবার কয়েকদিন আগে সেই ঘটনাটি ঘটেছিল। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে তাঁকে অনেকক্ষণের জন্যে দেখা যায় নি। এরপরে একটা সময়ে তিনি যখন তাঁর নিজের ঘরে ফিরে এসেছিলেন, তখন সহকর্মীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন – “এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?” তিনি সরল হাসি হেসে তাঁদের উত্তর দিয়েছিলেন – “আমার ব্যাঙ্কে গিয়ে সব লাল আজ কালো করে এলুম।” এরপরে কারো বুঝতে বাকি থাকেনি যে, নানাজনকে সাহায্য করতে গিয়ে এর আগে তিনি ব্যাঙ্ক থেকে যা কিছু ‘overdraw’ করেছিলেন, নিজের ‘Provident Fund’-এর টাকা থেকে সেই ঋণ শোধ করে দিয়ে তিনি সেদিন লালকে কালো করেছিলেন। সেদিন তাঁর হাসির মধ্যে দিয়ে সেই মর্মান্তিক কথাটাই যেন ফুটে উঠেছিল।
নিজের কথা চিন্তা না করে সারাজীবন ধরে তিনি ওভাবে অনেককেই অকাতরে সাহায্য করেছিলেন। তাই দীর্ঘকাল ধরে ভালো উপার্জন করা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের দিক থেকে তিনি প্রায় নিঃসম্বল ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ নিজে কোনোদিনই খ্যাতি বা প্রতিপত্তির পেছনে ছোটেন নি। এমনকি, তাঁর কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল এম. এস. সি. ডিগ্রীমাত্র নিয়েই তিনি চিরকাল আত্মতুষ্ট থেকে গিয়েছিলেন, ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করবার জন্য কোনোদিন থিসিস পেশ করেন নি, বা সম্মানসূচক কোন ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্যও কারো কাছে তদ্বির করেন নি। একজন সত্যসাধক ঋষির মতোই তাঁর মর্মচেতনায় যেন অনুরণিত হয়েছিল –
“সকল ভুলে যতই দিবারাতি
নামটারে ঐ আকাশ-পানে গাঁথি,
ততই আমার নামের অন্ধকারে
হারাই আমার সত্য আপনারে।”
তাই সত্যসাধক সত্যেন্দ্রনাথ নাম বা যশের প্রতি চির-উদাসীন ছিলেন। তাঁর সেই আত্ম-উদাসীনতার জন্যই হয়ত স্বদেশে বা বিদেশে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি অনেক বিলম্বে পেয়েছিলেন। বর্তমান সময়ে নিজে উদ্যোগী না হলে যেখানে কার্যসিদ্ধি হওয়া প্রায় অসম্ভব, প্রচারসর্বস্ব সেই দুনিয়ায় সত্যেন্দ্রনাথের মত একজন আত্মপ্রচারবিমুখ বিজ্ঞানী যে অবহেলিত হবেন – সে বিষয়ে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সেই কারণেই তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন, এবং যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা ঘটেছিল ও শেষ জীবনে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করে তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন, এবং এরপরেও যে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কর্মস্থল ছিল – সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করতে বিলম্ব করেছিল। নিজের শিক্ষাদাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যখন অত বিলম্বে সত্যেন্দ্রনাথকে সমাদর করা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে সেই কর্তব্যবোধের প্রত্যাশা করা দুরাশামাত্র ছিল। এমনকি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতিপদে সত্যেন্দ্রনাথকে বহু বিলম্বে বরণ করা হয়েছিল। ১৯২৪ সালে তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদান বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে খ্যাতি অর্জন করলেও সেই ঘটনার দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সত্যেন্দ্রনাথের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সেই সম্মান প্রদর্শন করেছিল। স্বদেশের মতো বিদেশেও সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি অনেক বিলম্বে পেয়েছিলেন। নিজের জীবনের প্রায় সায়াহ্নে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে নিজেদের ‘ফেলো’ নির্বাচিত করেছিল, এবং সেকালের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডিরাক সেই বিষয়ে নিজে উদ্যোগী হয়ে চেষ্টা করবার ফলেই সেটা সম্ভব হয়েছিল।#