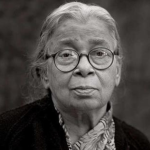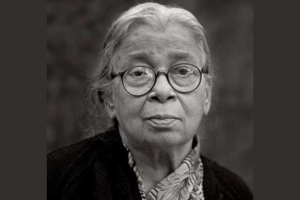বিভূতিভূষণ যখন কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, তখন খুব সম্ভবতঃ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। পাত্রী ছিলেন—তৎকালীন বসিরহাটের মোক্তার পানিতর গ্রামের কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা গৌরী দেবী। এই বিবাহের সময়ে বিভূতিভূষণের বয়স তেইশ-চব্বিশ বছর ছিল বলে এসময়ে তাঁর মধ্যে থাকা রোম্যান্টিক কল্পনা যে নববধূকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল, এবিষয়ে সন্দেহর কোন অবকাশ নেই। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁর প্রথম যৌবনের এই স্বপ্ন খুব নিষ্ঠুরভাবেই ভেঙে গিয়েছিল। কারণ, এই বিবাহের প্রায় বছরখানেক পরেই কার্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে গৌরী দেবী অকালে মারা গিয়েছিলেন। যদিও অতীতে বিভূতিভূষণের শ্যালক চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘বিভূতি বিচিত্রা’ নামক গ্রন্থে গৌরী দেবীর নিউমোনিয়ায় মৃত্যুর কথা বলেছিলেন, কিন্তু তবুও অন্য একটি জনশ্রুতি অনুসারে গৌরী দেবী নাকি হঠাৎই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন বলে জানা যায়; এবং বিভূতিভূষণের দ্বিতীয়া স্ত্রী কল্যাণী দেবীও এই জনশ্রুতির কথা শুনেছিলেন বলে জানিয়েছিলেন। এই জনশ্রুতি অনুসারে, গৌরী দেবী এসময়ে নাকি তাঁর বাপের বাড়িতে ছিলেন; এবং বিভূতিভূষণ হঠাৎই শ্বশুরবাড়ি থেকে একজন বাহক মারফৎ তাঁর অসুস্থতার বিষয়ে একটি পত্র পেয়ে তৎক্ষণাৎ এক বস্ত্রে নৌকা করে শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেও, পথেই শ্মশানে নেমে তিনি গৌরী দেবীর চিতা দেখতে পেয়েছিলেন। এসময়ে গৌরী দেবী ছাড়া হয় তাঁর মা, অথবা অন্য কোন নিকট আত্মীয়ও নাকি কলেরায় মারা গিয়েছিলেন। যাই হোক, গৌরী দেবীর প্রকৃত মৃত্যুর কারণ যেটাই হোক না কেন, মৃত্যুরূপা নিয়তির এই আকস্মিক আঘাতে বিভূতিভূষণ তখন যে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, একথা সহজেই অনুমানযোগ্য। আর এই জনশ্রুতি সত্যি হোক বা না হোক,—গৌরী দেবীর মৃত্যু যে বিভূতিভূষণের জীবনের একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল, এবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ নিজের প্রথম যৌবনের নিকটতম-অন্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একান্ত প্রিয়তমের এই আকস্মিক মৃত্যু তখন তাঁর সমগ্র সত্তাকে আলোড়িত করে তুলেছিল। আর গৌরী দেবীর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য জীবনযাপনের সাধ শুরুতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল বলেই হয়ত অপু-অর্পণার সংসারের ছবিতে সেই সাধ তিনি কল্পনায় পূরণ করেছিলেন। আরো ভালো করে বললে, গৌরী দেবীর মৃত্যুতে তিনি তখন যেন মৃত্যুর নিগূঢ় রহস্য উন্মোচন করতে উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। অন্যদিকে খুব সম্ভবতঃ প্রায় একই সময়েই তাঁর বোন আশালতা নিজের বিবাহের অল্পকাল পরেই হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন। আর আশালতা এবং গৌরী দেবী যেহেতু প্রায় সমবয়সী ছিলেন, সেহেতু তাঁদের পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্ক সখীর মত হওয়াই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। ক্ৰমান্বয়ে এই দুই আপনজনের মৃত্যু তখন বিভূতিভূষণের কল্পনাকে অন্তর্মুখী করে তুলেছিল। এমনকি পরিণত বয়সেও নিজের ‘হে অরণ্য কথা কও’ নামক দিনলিপিতে গৌরী দেবীর কথা স্মরণ করে তিনি লিখেছিলেন—
“গৌরীর কথা—আজ ২১শে নভেম্বর, সেই ২০ নং গোপাল মল্লিক লেনে এই সময়ে প্রথম গিয়েচি, সেই উদ্বেগ, ‘যতবার আলো জ্বালাতে চাই’ সেই গানটার কথা। এই সময়েই সে মারা যায়। জাহ্নবীর কথা—সেও এই সময়, বোধহয় আজই হবে।”
এছাড়া তিনি তাঁর বিভিন্ন দিনলিপির মধ্যে আরো বহুবার গৌরী দেবীকে স্মরণ করেছিলেন। বিভূতিভূষণের জীবনীকাররা বলেন যে, তাঁর ‘অপরাজিত’ উপন্যাসে অপুর আপাত ঔদাসীন্যের অন্তরালে যে গভীর উদ্বেজন ছিল, তা আসলে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিমানসেরই প্রতিফলন ছিল। তাছাড়া এসময় থেকেই তিনি মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মার কি গতি হয়—এবিষয়ে সন্ধান করতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, আর এখান থেকেই তাঁর ‘দেবযান’–এর কল্পনার শুরু হয়েছিল। বস্তুতঃ তাঁর এসময়কার জীবন বা পরলোক সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার এমন অনেক ইতিবৃত্ত এদিকে ওদিকে পাওয়া যায়, জনশ্রুতিতে ঢাকা বুদ্ধিতে যেসবের কোন ব্যাখ্যা করা চলে না। তবে গৌরী দেবীর অকাল মৃত্যুই যে তাঁর বৃহত্তম চেতনার উন্মেষের একটা বড়ো কারণ ছিল—একথা এখন নির্দ্বিধায় বলা চলে।
অন্যদিকে বিভূতিভূষণের সৃষ্টি অপুর জীবনে দেখা যায় যে, অপর্ণার মৃত্যুর পরে সে নিজের পরিচিত সমাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে চাঁপদানীর একটি অখ্যাত স্কুলে চাকরি নিয়েছিল। আর তাঁর এই সময়কার জীবন দ্যুতিহীন হয়ে উঠেছিল, এবং তাঁর কল্পনাময় সজীব অন্তর যেন নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যের পৃষ্ঠায় অপুর এই জীবন কি আসলে বিভূতিভূষণের নিজের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি ছিল? অতীতে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকার সম্পাদক লিখেছিলেন—
“সম্ভবতঃ স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তিনি লেখাপড়ায় ক্ষান্ত দিয়া সামান্য স্কুল মাষ্টারের চাকরী লইয়া হুগলীর জাঙ্গিপাড়া গ্রামে একরূপ অজ্ঞাতবাসে কাটান।” (বিভূতিভূষণের জীবনকথা, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)
কিন্তু বিভূতিভূষণের অন্যান্য জীবনীকারদের মতে, তিনি গৌরী দেবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নিজের লেখাপড়া ছেড়ে দেন নি, বরং এই দুর্ঘটনার বছরখানেক পরে তিনি জাঙ্গিপাড়ায় গিয়েছিলেন। অন্যদিকে বিভূতিভূষণের ‘স্মৃতির রেখা’ নামক দিনলিপিতেও দেখা যায় যে, পরবর্তীসময়ে ভাগলপুরে বসে তিনি জাঙ্গিপাড়ার চাকরির কথা স্মরণ করে ১৯২৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখেছিলেন—
“ভাবতে ভাবতে মনে হোল সাত বৎসর আগে এই দিনটিতে আমি প্রথম চাকরী নিয়েছিলাম। সেই মাইনর স্কুলের খাট, সেই লেপে শোওয়া অন্ধকার আকাশে চেয়ে দেখলাম।”
যাই হোক, গৌরী দেবীর মৃত্যুর প্রায় তেইশ বছর পরে বিভূতিভূষণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন। তবে এরমধ্যে গৌরী দেবীর বাপের বাড়ির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অক্ষুন্ন ছিল। কারণ, নিজের ‘ঊর্মিমুখর’ নামক দিনলিপির একজায়গায় তিনি যে দিদির বাড়ি থেকে ফিরে আসবার কথা লিখেছিলেন, তাঁর জীবনীকারদের মতে, সেটা সম্ভবতঃ গৌরী দেবীরই দিদির বাড়ি ছিল। এপ্রসঙ্গে তিনি তাঁর পূর্বোক্ত দিনলিপিতে লিখেছিলেন—
“ঠাকুর মায়ের শ্রাদ্ধের পর সেই মার্টিন লাইনের গাড়ীতে বসিরহাট থেকে এসেছিলুম, তখন আমি জাঙ্গিপাড়া স্কুলে চাকুরীতে ঢুকেছি। আজ ১৭/১৮ বছর পরে মার্টিনের গাড়ীতে চড়ে বসিরহাট থেকে এলুম।”
তাছাড়া এতে উল্লিখিত এই ঠাকুরমাও বোধহয় গৌরী দেবীর সঙ্গেই সম্পর্কিত ছিলেন। আর একান্তভাবে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিজীবনের কথা হলেও গৌরী দেবীর স্মৃতি প্রসঙ্গে এখানে আরেকটা কথাও অবশ্য উল্লেখ্য। সেটা হল যে, বিভূতিভূষণ তাঁর সমগ্র জীবন ধরেই গৌরী দেবীর কয়েকটি স্মৃতিচিহ্ন নিজের কাছে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন; এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে গৌরী দেবীর লেখা চিঠিতে তিনি নিয়মিতভাবে ফুল দিতেন। এমনকি পরবর্তীসময়ে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী কল্যাণী দেবীও গৌরী দেবীর এসব স্মৃতিচিহ্নের কয়েকটি সযত্নে নিজের কাছে আগলে রেখেছিলেন। আর এই স্মৃতিচিহ্নগুলি যে বিভূতিভূষণের কাছে কতটা মূল্যবান ছিল, একথার আভাস বিভূতিভূষণের দিনলিপি থেকেই পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ—
“তার পর সত্যি সত্যি কত ভাল জিনিসই পেলুম। গৌরী, সেই বনগাঁয়ের গাড়ীতে বসা, সেই বেলেঘাটা ব্রিজ স্টেশনে আমাদের প্রথম ও শেষ ঘরকন্না, সেই আয়না বার করে দেওয়া, সেই চিঠি বুকে করে মাথায় কপালে ঠেকানোর কথা মনে হয়ে পুলক হয়।”
তবে বিভূতিভূষণ কিন্তু জাঙ্গিপাড়ার প্রাইমারি স্কুলে বেশি দিন চাকরি করেন নি। খুব সম্ভবতঃ বছরখানেকের মধ্যেই সেখানকার পালা চুকিয়ে দিয়ে তিনি নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন, এবং এরপরে তিনি সোনারপুরের কাছাকাছি অবস্থিত হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতা করতে শুরু করেছিলেন। আর এই স্কুলে চাকরির জন্য যাওয়ার সময়েই পথে একদিন এই স্কুলেরই তৎকালীন প্রধান শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্র নাথ লাহিড়ীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, এবং তিনি প্রথম কয়েক দিন তাঁর বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই লাহিড়ী মহাশয়ের ভাইঝি অন্নপূর্ণা দেবী বা খুকু বিভূতিভূষণের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন বলে বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে তাঁর উল্লেখও পাওয়া যায়। আর এই হরিনাভি স্কুলের চাকরি পাকা হওয়ার কিছুদিন পরেই বিভূতিভূষণ সেখানে একটি বাসা ঠিক করে তাঁর মা মৃণালিনী দেবী আর ছোটো ভাই নুটবিহারীকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এখানে আসবার কয়েক দিনের মধ্যেই মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়েছিল।
এরপরে হরিনাভিতে বিভূতিভূষণ প্রায় দু’বছর ধরে অবস্থান করেছিলেন; আর এই সময়টা তাঁর সাহিত্যজীবনের ইতিহাসের পক্ষে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, এসময়েই তিনি একজন লেখকরূপে বাংলা সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তাঁর লেখা প্রথম গল্প—‘উপেক্ষিতা’—১৩২৮ বঙ্গাব্দের ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অতীতে এপ্রসঙ্গে ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যার ‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকায় ‘বিভূতিভূষণের জীবন কথা’ শিরোনামের যে রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার একজায়গায় এই পত্রিকার সম্পাদক লিখেছিলেন—
“পাঁচালী প্রিয় বিভূতিভূষণ ছন্দ মিলাইয়া ছড়াও লিখতেন। বনগ্রাম হাই স্কুলে অধ্যয়নকালে বিবাহের প্রীতি উপহার দুই এক খানা লিখিয়াছিলেন। ‘রিপন কলেজ ম্যগাজিনে’ও কবিতা বাহির হইয়াছিল একটা এবং প্রবন্ধও একটা ফাঁদিয়াছিলেন; কিন্তু তখন পর্যন্ত সাহিত্যিক হইবার সাধ পুরাপুরি মনে জাগে নাই। কি করিয়া তাহা জাগিল, সে কাহিনী তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহার ‘নবাগত’ পুস্তকের ‘আমার লেখা’ গল্পে। সেই কাহিনীই তিনি ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন রাত্রে কলকাতা বেতার মারফত ঘোষণা করেন। হরিনাভি স্কুলের শিক্ষকতা করিবার কালে (বিভূতিভূষণ স্বয়ং ভ্রমক্রমে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ লিখিয়াছেন) পাঁচুগোপাল চক্রবর্তীর (সম্ভবত কল্পিত নাম, ছেলেটির আসল নাম যে যতীন্দ্র ভট্টাচার্য, বিভূতিভূষণের উক্তি হইতেই তাহা পাইতেছি) চক্রান্তে তিনি একটি গল্প লেখেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রথম রচনা এইটি। গল্প লিখিয়া তাঁহার নিজেরই ভাল লাগে। তিনি কলিকাতায় আসিয়া একদিন প্রবাসী আপিসে তাহা দাখিল করেন এবং যথারীতি মনোনীত এবং লেখক কর্তৃক পরিবর্তিত (সম্পাদকীয় নির্দেশে) হইয়া তাহা ১৩১৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের প্রবাসীতে বাহির হয়, অর্থাৎ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী তারিখেই বিভূতিভূষণ গল্পলেখকরূপে বঙ্গসাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হন। সুতরাং ইহা যে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দেই লিখিত হইয়াছিল তাহাতে সংশয় নাই। ইতিপূর্বেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তিনি পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধেও চিন্তা করিতেছেন। বিভূতিভূষণের সাহিত্যের যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহার সবগুলিই বীজাকারে তাঁহার এই প্রথম গল্প ‘উপেক্ষিতা’য় পাইতেছি। সেই শুভ্র-সুচিতাবোধ, সেই খাদ্য-লোলুপতা, সেই আদেখলেপনা এবং সেই জন্মান্তর রহস্য, অর্থাৎ ‘পথের পাঁচালী’ ও ‘দেবযান’ দুইই এই গল্পটিতে উঁকি মারিতেছে। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় (‘মেঘমল্লার’) ‘আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম গল্প উপেক্ষিতা—-সুতরাং গল্পটির উপর আমার মায়া থাকা স্বাভাবিক’—-এইরূপ ভূমিকা করিয়া বিভূতিভূষণ কেন যে ‘দেবযান’ অংশ এই গল্পে পরিত্যাগ করিলেন, তাহা গবেষণার বিষয়।
পরিত্যক্ত অংশটি এই,—
‘এ কাকে দেখলুম বলবো?
আমাদের এই পৃথিবীর জীবনের বহু ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত রাজ্যে অনন্তের পথের যাত্রীরা আবার বাসা বাঁধবে, হয়তো যে দেশের আকাশটা রঙে রঙে রঙীন, যার বাতাসে কত সুর, কত গন্ধ, কত সৌন্দর্য, কত মহিমা, ক্ষীণ জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া কত সুন্দরী তরুণীরা যে দেশের পুষ্পসম্ভারসমৃদ্ধ বনে উপবনে ফুলের গায় বসন্তের হাওয়ার মধ্যে তাদের ক্ষীণ দেহের পরশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেই অপার্থিব দিব্য সৌন্দর্যের দেশে গিয়ে আমাদের এই পৃথিবীর মা-বোনেরা যে দেহ ধারণ করে বেড়াবেন,—এ যেন তাঁদের সেই সুদূর ভবিষ্যৎ রূপেরই একটা আভাস আমার বৌদিদিতে দেখতে পেলুম।’
আমরাও বহু সম্ভাবনার আভাস পাইলাম এই রচনাটুকুর মধ্যে। মহাসাধক বিভূতিভূষণের তখন বৃহত্তর কীর্তির জন্য প্রস্তুতির কাল। অনন্তের সঙ্গে সুরসামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা চলিতেছে, তাহার জন্য এই লৌকিক জগতের অসংখ্য বিচিত্রতা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের ব্যাকুল সন্ধান চলিতেছে, তিনি দুই চোখ ভরিয়া দেখিতেছেন চারিদিকে বিজ্ঞান দর্শন হইতে সংগ্রহ করিতেছেন মনের খোরাক, নানা সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী হইতে পৃথিবীর বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জন্মান্তর-রহস্য উদঘাটনেরও প্রয়াস করিতেছেন। কিন্তু যশের এই ক্ষীণ স্পর্শ এই তপস্বী সাধককেও মাতাল করিয়া দিল, তিনি ‘প্রবাসী’তে পর পর গল্প লিখিয়া চলিলেন—‘উমারাণী’ শ্রাবণ, ১৩২৯; ‘মৌরীফুল’ অগ্রহায়ণ, ১৩৩০; ‘অভিশপ্ত’ আষাঢ়, ১৩৩১; ‘নাস্তিক’ পৌষ, ১৩৩১ এবং ‘পুঁইমাচা’ মাঘ, ১৩৩১।”
কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, বিভূতিভূষণ কেন জাঙ্গিপাড়া স্কুল ছেড়েছিলেন—একথা যেমন তাঁর জীবনেতিহাস থেকে জানা যায় না, তেমনি কেন যে তিনি হরিনাভি স্কুল পরিত্যাগ করেছিলেন—একথার হদিসও তাঁর জীবনীকারেরা পাননি। তবে অনেকে অনুমান করেন যে, কোনো কারণে হয়ত হরিনাভিতে তাঁর আর মন বসেনি, কিংবা হয়ত তাঁর অন্তরে তখন ভ্রমণের যে নেশা বাসা বেঁধেছিল—সেটারই তাড়নায় তিনি এরপরে এক আশ্চর্য চাকরি নিয়েছিলেন। তাঁর এসময়কার জীবনেতিহাস থেকে জানা যায় যে, হরিনাভি স্কুল ত্যাগ করবার পরে তিনি কেশোরাম পোদ্দারের গোরক্ষিণী সভার পক্ষ থেকে বাংলার বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ করেছিলেন। আর নিজের এসময়কার ভ্রমণের কথা তিনি তাঁর ‘অভিযাত্রিক’ নামক দিনলিপিতে কিছুটা হলেও সঙ্কলিত করেছিলেন। এছাড়া নিজের ‘স্মৃতির রেখা’ নামক দিনলিপিতে তিনি ভাগলপুরের ইসমাইলপুর কাছারিতে বসে নিজের ভ্রমণ জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে লিখেছিলেন—
“সন্ধ্যার সময় বসে আরাম চেয়ারটায় ঠেস দিয়ে অনেক কথা ভাবছিলুম। এই চেয়ারটা যেদিন থেকে তৈরী হয়েছে—ভ্রমণ সুরু হয়েছে সেদিন থেকে। সেই সত্যবাবুর বাড়ীর দেউড়িতে সন্ধ্যার সময় গিয়ে চেয়ারটা নিয়ে নামলুম—সেই ঢোকে ঢোকে জল খেয়ে তৃপ্ত হলুম—পরদিন থেকে যাত্রা শুরু হোল। মহারাণী স্বর্ণময়ী রোড, ৪৫ মৃজাপুর স্ট্রীট। সেই ফরিদপুরে সত্যবাবুর বাড়ী, চাট-গাঁয়ের স্টীমার, কক্সবাজারের স্টীমারের ডেকে, সীতাকুণ্ডে, নরসিংদিতে জ্যোতির্ময়ের ওখানে, ঢাকায়—আবার ৪৫ মৃজাপুর স্ট্রীটে। বড়বাসায় ইসমাইলপুরে কত জায়গায়। এইতো সেদিন কানিবেনের জঙ্গল হয়ে, জামদহ, জয়পুরের ডাকবাংলোয় শালবনের মধ্যে নির্জন রাত্রি যাপন করে গেলুম দেওঘর। তারপর এই গেলুম রামচন্দ্রপুরে, বেনীবনে, বক্রতোয়ার ধারে ধারে, লক গেটে সূর্যাস্তের সময় কত বেড়ালুম—এই তো গেলুম পাটনা শোনপুরে মেলা দেখলুম—জ্যোৎস্নার রাত্রিতে প্যালেজা ঘাটে স্টীমারে বসে চা খেতে খেতে গঙ্গাপার হয়ে পাটনার বৈকুণ্ঠবাবুর ওখানে ফিরে এলুম। হাসান ইমামের যে নতুন বাড়ীটা উঠচে তারই কাছে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কথা ভাবা, তারপর কালীর সঙ্গে নালান্দা, সেই রাজগির যাওয়া, সেই বাঁশের বন, শোন ভাণ্ডার, সেই চেনো, হরনৌৎ, শো—অদ্ভুত নামের স্টেশন সব—সেই গড়িয়ার জলার জ্যোৎস্না দেখতে দেখতে ৮॥ টার গাড়িতে রাজপুর ফেরা—সেই জাঙ্গিপাড়াকে ভাবতুম কত দূরের দেশটা।
এই অনবরত ভ্রাম্যমান জীবন। ঘুরতেই হবে যে—পথে যে নেমেচি—যাই হোক আমি পথে নেমেচি। আমি কিছুর মধ্যেই নেই, অথচ সবের মধ্যেই আছি—জগতের এই অপূর্ব গতির রূপ আমার চোখে পড়চে। আমি আজন্ম পথিক—পথে বেরিয়েচি, সত্যবাবুর বাড়ী যে দিন থেকে নেই—অনেক কাল আগে সেই ১৯০৮ সালে, এক সন্ধ্যায় বেহারী ঘোষের বাড়ী মাণিকের গান হোল—পরদিন জিনিষপত্র নিয়ে সেই যে বোর্ডিংএ এলুম—কিক্ষণে বাড়ির বাইরে পা দিয়েছিলুম জানি না—সেই বিদেশে বাস সুরু হোল। পরে আর বারাকপুরকে বারমাসের জন্যে একবারও পাইনি—হারিয়ে হারিয়ে পেয়ে আসচি—কত জগদ্ধাত্রী পূজার ছুটিতে, গুডফ্রাইডের ছুটিতে, বড়দিনে, পুজোয়, শনিবারে, পেয়ে এসেছি ছেলেবেলায়, এখনও অন্যভাবে পাই।”
আসলে ব্যারাকপুর আর ইছামতী তাঁর আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকলেও বিভূতিভূষণ বরাবরই অন্তরে অন্তরে একজন ভ্রমণ পাগল ব্যক্তি ছিলেন। তাই কেশোরাম পোদ্দারের গোরক্ষিণী সভার যে কাজ তখন তিনি নিয়েছিলেন, সেটার উপরে তাঁর অন্তরের কোন টান আদৌ ছিল কিনা—একথা বলা কঠিন হলেও, এই উপলক্ষ্যে তিনি যেভাবে গোটা বাংলায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, সেটার মূল্যও কিন্তু কম কিছু ছিল না। বিভূতিভূষণের জীবনীকারদের মতে, প্রথম যৌবনের এই ভ্রমণ তাঁর জীবনে নানাভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছিল।
প্রথমতঃ এই ভ্রমণের নেশা তাঁর মনেপ্রাণে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে তাঁর অন্তরাত্মা পথের ডাক শুনতে পেয়েছিল। আর একারণেই তিনি তাঁর বিভিন্ন দিনলিপিতে বিভিন্ন সময়ে লিখেছিলেন—
(১) “কেন মানুষ ঘরে থাকে তাই ভাবি। আর কেনই বা পয়সা খরচ করে মোটারে কি রেলের গাড়ীতে বেড়ায়। পায়ে হেঁটে পথ চলার মত আনন্দ কিসে আছে?” (উর্মিমুখর)
(২) “… ‘চরন্ বৈ মধু-বিন্দতি’ চলা দ্বারাই অমৃত লাভ হয়, অতএব চলো।” (তৃণাঙ্কুর)
দ্বিতীয়তঃ, এই ভ্রমণের ফলে তাঁর দৃষ্টির প্রসার ঘটবার ফলে কোনো সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে তাঁর চিত্ত আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেনি।
তৃতীয়তঃ, যে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর আশৈশব পরিচয় ছিল, এসময়ে সেটাকে তিনি বিচিত্রভাবে উপভোগ করেছিলেন। এরফলে তাঁর অন্তরে প্রকৃতিপ্রেম গাঢ়তর হয়েছিল, এবং একইসঙ্গে তাঁর অধ্যাত্মচেতনারও উদ্বোধন ঘটেছিল। তাছাড়া সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টা সম্পর্কেও একটা গভীর বিশ্বাস এসময় থেকেই তাঁর অন্তরে জেগে উঠেছিল। আর কারণেই নিজের ‘হে অরণ্য কথা কও’ নামক দিনলিপিতে তিনি লিখেছিলেন—
“ভগবানের সৃষ্টি দেখে বেড়াবো, এই তো চাই।”
সাহিত্য সমালোচকদের মতে, এই অধ্যাত্মদৃষ্টিমণ্ডিত প্রকৃতিপ্রেমই বিভূতিভূষণের কবিপ্রতিভার মূলাশক্তি ছিল।
চতুর্থতঃ, তিনি যখন দেশে দেশে ঘুরে বেরিয়েছিলেন, তখন মানুষের বিচিত্র পরিচয় পেয়েছিলেন; আর সাধারণ মানুষের জীবন গভীর সহানুভূতির চোখে দেখেছিলেন। একারণেই নিজের ‘অভিযাত্রিক’ নামক দিনলিপিতে তিনি বলেছিলেন—
“দেশ বেড়িয়ে যদি মানুষ না দেখলুম তবে কি দেখতে বেরিয়েছি। চিরযৌবনা নিসর্গসুন্দরী সবকালে সব দেশেই মন ভুলায়, মন ভুলায় তার শ্যামল চেলাঞ্চল, বনময় ফুলসজ্জা, মধুমল্লীর সৌরভভরা তার অঙ্গের সুবাস।
তাকে সব স্থানে পাওয়া যায় না সে রূপে, কিন্তু মানুষ সব জায়গাতেই আছে! প্রত্যেকের মধ্যেই একটা অদ্ভুত জগৎ, দেখতে জানলেই সে জগৎটা ধরা দেয়। তাই দেখতেই পথে বার হওয়া। মানুষের বিভিন্ন রূপ দেখবার আমার চিরকাল আগ্রহ, নতুন মানুষ দেখলেই মনে হয় ওর সঙ্গে বসে একটু আলাপ করে চিনি। দেখতে চেয়েছিলুম বলেই বোধ হয় কত রকমের মানুষকেই যে দেখালেন জীবনে।”
তাই গোরক্ষিণী সভার আদর্শ প্রচারে তাঁর সত্যিকারের কোন আগ্রহ ছিল কিনা—এবিষয়ে সন্দেহ থাকলেও, বিভূতিভূষণের সাহিত্য জীবনের পক্ষে চাকরির উপলক্ষ্যে এই ভ্রমণের প্রয়োজন যে ছিল—একথা অনস্বীকার্য। আসলে তখন তাঁর সাহিত্যে কল্পনা সবে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। সূর্যের আলো পড়ে যেমন গাছের পাতায় ক্লোরোফিল সঞ্চারিত হয়ে তার মধ্যে জীবনীশক্তি সঞ্চার করে, ঠিক তেমনি বিচিত্র ভূবনের আলো তাঁর প্রতিভার মধ্যে একটা আশ্চর্য শক্তি সঞ্চার করে এসময়ে তাঁকেও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।
এরপরে বিভূতিভূষণ তাঁর চাকরির ক্ষেত্রে খেলাৎচন্দ্র ঘোষের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। এসময়ে প্রথমে তিনি খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে কিছুদিন গৃহ-শিক্ষকতার কাজ করেছিলেন, আর তারপরে কিছুকাল তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত ছিলেন। এরপরে তিনি ভাগলপুরে খেলাৎ ঘোষ এস্টেটের সার্কেল-সুপারিনটেন্ডেন্টের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর অবশেষে কলকাতায় ফিরে এসে ধর্মতলার খেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলে ১৯৪২ সালের প্রথমদিক পর্যন্ত শিক্ষকতার কাজ করেছিলেন। তবে এসময়ের এসব কাজের মধ্যে ভাগলপুরে খেলাৎ ঘোষ এস্টেটের কাজই তাঁর সাহিত্যজীবনের ইতিহাসের পক্ষে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতীতের ভাগলপুরে বিভূতিভূষণের স্মৃতি সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একদা বলেছিলেন—
“তারিখ মনে নেই, সাল বোধ হয় ১৯২৩ অথবা ২৪ হবে, একদিন সকালে বিভূতিভূষণ আমার ভাগলপুরের গৃহে পরিচিত হলেন। একজন খাঁটি সহিত্যানুরাগীর শিশুর মত সরল মন দেখে মুগ্ধ হলাম। এক বৈঠকেই আলাপ ঘনীভূত হ’ল; আর, তার ফলে অবিলম্বে তাঁকে আমাদের দলে ভর্তি করে নিলাম।”
তৎকালীন কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার রমানাথ ঘোষের ভাগলপুরের বাড়ির নাম ছিল ‘বড় বাসা’। বিভূতিভূষণ এসময়ে খেলাৎচন্দ্র এস্টেটের সার্কেল অফিসার পদে নিযুক্ত হয়ে ভাগলপুরে গিয়েছিলেন, এবং তিনি প্রধানতঃ ভাগলপুরেই থাকলেও মাঝে মাঝেই সেযুগের গঙ্গার উত্তর দিকে অবস্থিত দিরা-ইসলামপুর নামক জঙ্গলমহল পরিদর্শন করবার কাজেও বের হতেন। তখনকার ভাগলপুরের চারপাশের প্রকৃতির অপরূপ শোভা, এখানকার গাছপালা-লতা-পাদপ, ঘননিবদ্ধ তালগাছের কুঞ্জ, এখানকার গঙ্গাবক্ষে উদয়াস্তব্যাপী বিচিত্র লীলা, গঙ্গার উত্তর তীরে ধূসর চক্রবাল পর্যন্ত চরভূমির সুদূর বিস্তৃতি, ইসলামপুরের বন-জঙ্গলের নিবিড় আরণ্য মায়া বিভূতিভূষণের চিত্তকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। (পথের পাঁচালীর বিভূতিভূষণ, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ন, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ) তাছাড়া খেলাৎ ঘোষের এস্টেটের কাজ করবার সময়ে বিভূতিভূষণকে এই অঞ্চলের বনে বনে ঘুরতে হয়েছিল বলেও শৈশব থেকেই তাঁর অন্তরে যে প্রকৃতি প্রেম ছিল, বিহারের গভীর অরণ্যে প্রকৃতির নিবিড় সৌন্দর্যের মধ্যে বাস করবার ফলে এসময়ে তা তাঁর চেতনায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তবে বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে তৎকালীন বিহারের এই অঞ্চলের প্রকৃতির কিছু পার্থক্য ছিল; বস্তুতঃ, বাংলার প্রকৃতি প্রধানতঃ সজলা—নদী খালবিল পুকুরের ধারে এর যে সহজ শোভা দেখতে পাওয়া যায়, তা যেন বাঙালির ঘরোয়া জীবনের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে। আর এর লালন এতটাই সহজ যে বাঙালি আলাদা করে এর কোন অস্তিত্ব বুঝতে পারে না। শুধু এর শ্রী বাঙালির ভালো লাগে—এই পর্যন্ত। কিন্তু বিভূতিভূষণের প্রেম বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে থেকে জননী ভগিনীর স্নেহরসকে আকর্ষণ করতে পেরেছিল। তাঁর স্বভাব বাংলার প্রকৃতির রসে জারিত ছিল। আর তৎকালীন বিহারের অরণ্যভূমির মধ্যেই শ্রীর থেকে রূপ বেশি ছিল। ফলে এই সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতি তখন বিভূতিভূষণের চেতনাকে যেন কান্তা সম্মিত লোভনতা দিয়ে আবিষ্ট করে দিয়েছিল। সুতরাং তাঁর ব্যক্তিপুরুষ যেমন বাংলার প্রকৃতির লালনে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি তাঁর কবিপুরুষ আবার নিসর্গসুন্দরীর আরণ্য প্রেমে উদ্দীপ্ত হয়েছিল। এছাড়া সেযুগের ভাগলপুরের আরণ্যের নিভৃত পরিবেশে বিভূতিভূষণ আত্মসমাহিত হওয়ার অবকাশও পেয়েছিলেন। আর একারণেই নিজের ‘স্মৃতির রেখা’ নামক দিনলিপিতে ১৯২৭ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে রাজগিরিতে বসে তিনি লিখেছিলেন—
“জীবনে বড় আনন্দকে ধ্যানে আগে পেতে হয় এবং ধ্যান ভিন্ন তার সন্ধানই মেলে না।”
সুতরাং এই অরণ্যভূমিই যে তখন তাঁকে এই ধ্যানের অবকাশ দিয়েছিল—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাঁর এই ধ্যান অবশ্য কোন আরণ্যক ঋষির তত্ত্বজিজ্ঞাসা ছিল না, বরং কল্পনার আলোয় জীবনের আনন্দের সন্ধান ছিল। এতে চিন্তা নয় ভাবনা ছিল; আর বুদ্ধির দীপ্তি নয়, হৃদয়ের দ্রুতি ছিল।
তাছাড়া সেযুগের বিহারের নিভৃতনির্জন পরিবেশে বসে তিনি নিজের অতীতকেও রঙে রসে ভরে উপভোগ করতে পেরেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এসময় থেকেই তিনি ‘পথের পাঁচালী’ লিখতে শুরু করেছিলেন; আর এই উপন্যাসে যে তাঁর নিজের শৈশব আর বাল্যের অনেক স্মৃতিও জড়িয়ে ছিল—একথা এখন প্রমাণিত। এতে বাংলার গ্রাম—বিশেষ করে ইছামতী-বারাকপুর থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে তিনি যখন শৈশবের কথা মনে করেছিলেন, তখন তাঁর স্মৃতির সঙ্গে সুখদুঃখের নানা অনুভূতিও জেগে উঠেছিল। এপ্রসঙ্গে ১৯২৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ইসলাইলপুরে বসে নিজের ‘স্মৃতির রেখা’ নামক দিনলিপিতে তিনি বলেছিলেন—
“মনের কোথায় যেন অদৃশ্য খোপে গত জীবনের স্মৃতি সব ঠাসা আছে,—পিয়ানোর চাবিতে হাত পড়ার মত দৈবাৎ কোনো পুরানো খোপে হাত পড়ে যায়—-হঠাৎ সেটা বড় পরিচিত সুরে বেজে ওঠে—অনেক কালের আগের একটা দিন অল্পক্ষণের জন্য বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আবার ফিরে আসে।”
সাহিত্য সমালোচকরা বলেন যে, যে সাহিত্য চিরন্তনী হয়, তা অদ্যাতনীর তাড়না হয় না, এবং তাৎক্ষণিকবার্তার দাবি মেটানোর দায় তার থাকে না। ‘Emotion recalled in tranquility’—-নিরাকুল চিত্তে আবেগের মূর্তিই হল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রস্তুতি। তাই বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে প্রকৃতির উদার পরিবেশে আত্মনিমগ্ন নিভৃত অবকাশে যখন ‘পথের পাঁচালী’ লিখছিলেন, তখন স্মৃতির বন্যা তাঁর কল্পনাকে ভরে ভরে তুলেছিল। আর এই শৈশবকথা স্মরণ তাঁর যে কোন ‘nostalgia’ ছিল না, বরং এ যে স্মৃতিলোকে তাঁর কবিকল্পনার আনন্দ বিচরণ ছিল,—বিভূতিভূষণের জীবনীকারমাত্রেই একথা স্বীকার করে নিয়েছেন। এছাড়া বিভূতিভূষণের সাহিত্যজীবনে এই স্মৃতিচারণ তাঁর একটা বিশিষ্টতাও ছিল। কারণ, তিনি যখন ভাগলপুরে ছিলেন, তখন বারাকপুর-ইছামতীর স্মৃতি যেমন তাঁর মনকে ভরে দিয়েছিল, ঠিক তেমনি আবার এরপরে তিনি যখন কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, তখন অরণ্যের স্মৃতি তাঁর কল্পনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বলেই তিনি ‘আরণ্যক’ লিখেছিলেন। আসলে তাঁর যৌবনের প্রায় সব লেখাই স্মৃতির মধুকোষে সঞ্চিত জীবনের আনন্দরসের পুনরাস্বাদ ছিল।#