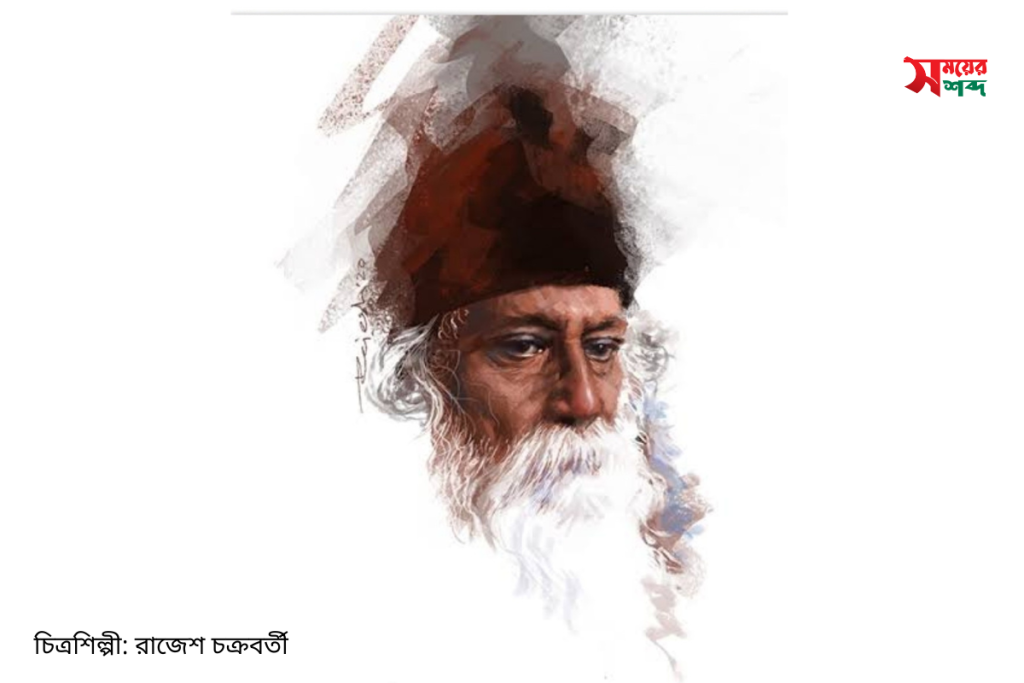বিংশ শতাব্দীতে বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী সংকলনের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন—
“প্রতিভার স্ফুর্তির ন্যায় প্রেমের স্ফুর্তিও একটি মাহেন্দ্রক্ষণ একটি শুভমুহূর্তের উপর নির্ভর করে। হয়ত শতেক যুগ আমি তোমাকে দেখিয়া আসিতেছি, তবুও তোমাকে ভালবাসিবার কথা আমার মনেও আসে নাই—কিন্তু দৈবাৎ একটি নিমিখ আসিল তখন না জানি কোন গ্রহ কোন কক্ষে ছিল—দুইজনে চোখাচোখি হইল, ভালবাসিলাম। সেই এক নিমিখ হয়ত পদ্মার তীরের মত অতীত শত যুগের পাড় ভাঙ্গিয়া দিল ও ভবিষ্যৎ শত যুগের পাড় গড়িয়া দিল।”
রবীন্দ্রজীবনী ও সাহিত্য নিয়ে যাঁরা এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন আলোচনা করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই জানিয়েছেন যে, প্রেমের এই মাহেন্দ্রক্ষণের উপলব্ধিতেই রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিন্তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে মানব প্রেমের স্বরূপ আলোচনা করবার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের পটভূমিতে শুধুমাত্র বৈষ্ণব প্রেমদর্শন নয়, একইসঙ্গে প্লেটো ও শেলীর প্রেমচিন্তাও বর্তমান রয়েছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। এবং রবীন্দ্রনাথের অচলিত রচনার অন্তর্ভুক্ত দুটি গদ্যপুস্তক—‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ (১৮৮০) ও ‘আলোচনা’ (১৮৮৫)—এপ্রসঙ্গে অবশ্যস্মর্তব্য।
রবীন্দ্রজীবনী বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, মানবসংসারের মধ্যে প্রবেশের আগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বোক্ত দুটি গ্রন্থে প্রেমতত্ত্ব ও প্রেমের স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাস বলে যে, ১৮৭৮ সালে ‘কবিকাহিনী’ নামক গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার যাত্রা শুরু হয়েছিল। এরপরে ক্রমান্বয়ে ১৮৮০ সালে ‘বনফুল’; ১৮৮১ সালে ‘বাল্মাকি-প্রতিভা’, ‘ভগ্নহৃদয়’ ও ‘রুদ্রচণ্ড’, ১৮৮২ সালে ‘সন্ধ্যাসংগীত’ ও ‘কালমৃগয়া’; এবং ১৮৮৩ সালে ‘প্রভাতসংগীত’ নামে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাট্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া এসময়ের মধ্যেই ১৮৮০ সালে ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ ও ১৮৮১ সালে তাঁর ‘যুরোপপ্রবাসীর পত্র’ নামে গদ্যরচনা এবং ১৮৮৩ সালে ‘বৌঠাকুরাণীর হাট’ নামের উপন্যাসটিও প্রকাশিত হয়েছিল। এরপরে ক্রমান্বয়ে ১৮৮৪ সালে রবীন্দ্রনাথের ‘ছবি ও গান’, ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’, ‘নলিনী’, ‘শৈশবসঙ্গীত’ ও ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’; ১৮৮৫ সালে ‘রবিচ্ছায়া’ নামক সংগীত সংগ্রহ এবং ১৮৮৬ সালে ‘কড়ি ও কোমল’ প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া এরই মাঝে ১৮৮৫ সালে তাঁর লেখা ‘রামমোহন রায়’ ও ‘আলোচনা’ নামের দুটি গদ্যরচনাও বের হয়েছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচকদের মতে, ‘কবিকাহিনী’ (১৮৭৮) থেকে শুরু করে ‘কড়ি ও কোমল’ (১৮৮৬) পর্যন্ত পর্বের মধ্যে ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ (১৮৮৩) ও ‘আলোচনা’ (১৮৮৫) ছিল তাঁর সাহিত্যিক জীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ গদ্যগ্রন্থ। বস্তুতঃ ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যের আগেই পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলিতে—নাটকে, কাব্যে ও গদ্যালোচনায় রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমের উর্ধ্বায়ন (sublimation) প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আর ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ নামক গ্রন্থে প্রেমের যে বিশিষ্ট রূপটি বাইশ বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথ ধ্যান করেছিলেন, পরবর্তী সুদীর্ঘকালের রবীন্দ্রসাহিত্যে সেটার বিস্তার ঘটেছিল। আর ভালো করে বললে, এই গ্রন্থেই বাইশ বছরের তরুণ কবির কণ্ঠে ভোগাসক্তিমুক্ত প্রেমের যে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল, তাঁর পরবর্তী জীবনে সেটাই বিচিত্র রাগিণীতে বেজে উঠেছিল।
রবীন্দ্র-গবেষকদের মতে, রবীন্দ্রনাথের জীবনে ১৮৮৩-৮৪ সালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে কবির বিবাহ হয়েছিল। এর আগেই কবির ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। আর কবি-বিবাহের মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই, ১৮৮৪ সালের মে মাসে—কবিজীবনে প্রেরণাদাত্রী দেবীসমা বৌঠাকুরাণী কাদম্বিনী দেবীর ‘আত্মখণ্ডন’ বা মৃত্যু ঘটেছিল। এরপরে ১৮৮৫ সালের ভারতী পত্রিকায় ‘পুষ্পাঞ্জলি’ ও ‘আলোচনা’ নামক দুটি রচনায় এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটি নিয়ে কবির প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছিল। তাই একথা বলা সম্ভব নয় যে, এসময়ে রবীন্দ্রনাথ—‘জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে।’ বস্তুতঃ নিজের প্রিয় বৌঠাকুরাণীর মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই কবি তখন সংসার ও জীবনকে নতুন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। কাদম্বিনী দেবীর মৃত্যুতে তিনি প্রেমের অবিনশ্বরতার উপলব্ধি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। এরপরে ‘জীবনস্মৃতি’ নামক গ্রন্থে নিজের এই উপলব্ধিকেই স্বীকৃতি দিতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন—
“জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।”
সমালোচকদের মতে, একারণেই পরবর্তীসময়ে রবীন্দ্রসাহিত্যে মৃত্যুর পটভূমিতে প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছিল। এজন্যই তাঁর ‘কড়ি ও কোমল’ গ্রন্থে প্রিয়বিয়োগের দুঃসহ শোকের মাঝে জীবনের তথা প্রেমের গভীর উপলব্ধির সূচনা ঘটেছিল—
“ধ্বনি খুজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম, শুধিবারে অসীমের ঋণ—
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।”
(চিরদিন)
এর আগে রবীন্দ্রনাথের ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ নামক গ্রন্থে ভালোবাসার অনধিকার তত্ত্ব ও মৃত্যুহীন মোহহীন চিরঞ্জন ভালোবাসার রূপটি ধরা পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মত ছিল যে, ভালোবাসা মূলতঃ গ্রহণ নয়, ত্যাগ; সংগ্রহ নয়, নিজেকে বিতরণ; এবং ভোগাসক্তির বন্ধন নয়, ভোগাসক্তির উর্ধ্বায়ন। আর এরপরে প্রকাশিত ‘আলোচনা’ নামক গ্রন্থে প্রেম নিয়ে কবির বক্তব্য ছিল যে, প্রেমেই মনুষ্যত্বের সার্থকতা হলেও প্রেমের সার্থকতা লোভে নয়, দানে; ক্ষুদ্রতায় নয়, ভূমায়; এবং অধিকারে নয়, অনধিকারে।
সমালোচকদের মতে, এর পরবর্তীসময়ের সুবিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমের যে সব বিচিত্র রূপ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে একথাই নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছিল; এছাড়া সেখানে প্রেম নিয়ে নতুন কোনো কথা ছিল না। তাই ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ ও ‘আলোচনা’–কে রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিন্তার বীজগ্রন্থ বলা যেতে পারে। অতীতে ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন—
“… ‘কড়িও কোমল’ প্রকাশিত হবার আগেই ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ এবং ‘আলোচনা’র লেখাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও সৌন্দর্য্যের অবিচ্ছেদ্য সংযোগের সত্য স্বীকার করেছিলেন এবং প্রেমের সর্বব্যাপকতার প্রেরণায় তাঁর ধর্মবোধের সঙ্গে দেশাত্মবোধ,—দেশাত্মবোধের সঙ্গে বিশ্বানুভূতি,—বিশ্বানুভূতির সঙ্গে শিল্পীচেতনা এবং শিল্পীচেতনার সঙ্গে সমাজচেতনা একই পুটপাকে পাক হয়ে পরস্পর সংশ্লিষ্ট, পরস্পর অবিচ্ছেদ্য, অখণ্ড, অবিভাজ্য এক সত্যবোধে পরিণত হয়েছিল। রবীন্দ্রমানসের এই বিশেষ প্রকৃতিটি পর্যালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবিমিশ্র ‘প্রেমের কবিতা’ বলতে যা বোঝায়, সে পদার্থ রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিরল। তাঁর অনুভূতিতে প্রেম একটি ধাতুসঙ্করের (alloy) মতো। দেশ, সমাজ, বিশ্ব, ঈশ্বর—ইত্যাদি বিষয়ের চিন্তা তাঁর শৃঙ্গার-চেতনার চৌহদ্দীর বাইরে অবান্তরবোধে বহিষ্কৃত হয় নি। ‘কড়ি ও কোমলে’র পূর্বেই প্রেমের ধারণার সঙ্গে এই সব ধারণার পরমাণবিক অন্তরঙ্গতার (affinity) ফলে রবীন্দ্রমানসের শৃঙ্গারচেতনা বিশিষ্ট এক যৌগিক প্রত্যয়ে পর্যবসিত হয়েছিল।” (সাহিত্যপাঠকের ডায়ারি, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র)
প্রসঙ্গতঃ এখানে রবীন্দ্রনাথের ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ ও ‘আলোচনা’ নামক গ্রন্থ দুটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি স্মরণ করা যেতে পারে, যা নিম্নরূপ—
(১) “… ‘ভালবাসা’ অর্থে আত্মসমর্পণ নহে। ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা, হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা নহে, হৃদয়ের যেখানে দেবত্রভূমি, যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।
যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহাকে ফুল দাও, কাঁচা দিও না। তোমার হৃদয়-সরোবরের পদ্ম দাও, পঙ্ক দিও না। হাসির হীরা দাও, অশ্রুর মুক্তা দাও, হাসির বিদ্যুৎ দিও না, অশ্রুর বাদল দিও না।
… প্রেম হৃদয়ের সারভাগ মাত্র। হৃদয়-মন্থন করিয়া যে অমৃতটুকু উঠে তাহাই। ইহা দেবতাদিগের ভোগ্য। অসুরে আসিয়া খায়, কিন্তু তাহাকে দেবতার ছদ্মবেশে খাইতে হয়।
… একে ও যাহাকে ভালবাসি তাহাকে ভাল জিনিস দিতে ইচ্ছা কবে, দ্বিতীয়তঃ তাহাকে মন্দ জিনিস দিলে মন্দ জিনিসের দর অত্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়।
… সত্যকার আদর্শ লোক সংসারে পাওয়া দুঃসাধ্য। ভালবাসার একটি মহান গুণ এই যে, সে প্রত্যেককে নিদেন একজনের নিকটেও আদর্শ করিয়া তুলে। এইরূপে সংসারে আদর্শভাবের চর্চা হইতে থাকে।
… ভালবাসা অর্থে ভাল বাসা অর্থাৎ অন্যকে ভাল বাসস্থান দেওয়া, অন্যকে মনের সর্বাপেক্ষা ভাল জায়গায় স্থাপনা করা।” (মনের বাগান বাড়ি, বিবিধ প্রসঙ্গ)
(২) “প্রকৃত ভালবাসা দাস নহে, সে ভক্ত; সে ভিক্ষুক নহে, সে ক্রেতা। আদর্শ প্রণয়ী প্রকৃত সৌন্দর্যকে ভালবাসেন, মহত্বকে ভালবাসেন। তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে আদর্শভাব জাগিতেছে, তাহারই প্রতিমাকে ভালবাসেন। প্রণয়ের পাত্র যেমনই হউক, অন্ধভাবে তাহার চরণ আশ্রয় করিয়া থাকা তাহার কর্ম নহে। তাহাকে ত ভালবাসা বলে না, তাহাকে কর্দমবৃত্তি বলে। কর্দমে একবার পা জড়াইলে আর ছাড়িতে চায় না, তা সে যাহারই পা হউক না কেন, দেবতারই হউক আর নরাধমেরই হউক! প্রকৃত ভালবাসা যোগ্যপাত্র দেখিলেই আপনাকে তাহার চরণধূলি করিয়া ফেলে। এই নিমিত্ত ধূলিবৃত্তি করাকেই অনেকে ভালবাসা বলিয়া ভুল করেন। তাঁহারা জানেন না যে, দাসের সহিত ভক্তের বাহ্য আচরণে অনেক সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু একটি প্রধান প্রভেদ আছে, ভক্তের দাসত্বের স্বাধীনতা আছে, ভক্তের স্বাধীন দাসত্ব। তেমনি প্রকৃত প্রণয় স্বাধীন প্রণয়। সে দাসত্ব করে কেন না দাসত্ববিশেষের মহত্ম সে বুঝিয়াছে। যেখানে দাসত্ব করিয়া গৌরব আছে, সেইখানেই সে দাস, যেখানে হীনতা স্বীকার করাই মর্যাদা, সেইখানেই সে হীন। ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা নহে, ভাল ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা। তা যদি না হয়, যদি ভালবাসা হীনের কাছে হীন হইতে শিক্ষা দেয়, যদি অসৌন্দর্যের কাছে রুচিকে বন্ধ করিয়া রাখে, তবে ভালবাসা নিপাত যাক।” (আদর্শ প্রেম, বিবিধ প্রসঙ্গ)
(৩) “অনন্ত জ্ঞানের ক্ষুধা লইয়া যে রহস্য দন্তস্ফুট করিতে পারিব না তাহাকেই অনবরত আক্রমণ করা, অনন্য আসঙ্গের ক্ষুধা লইয়া যে সহচর মিলিবে না তাহাকেই অবিরত অন্বেষণ করা, অনন্ত সৌন্দর্যের ক্ষুধা লইয়া যে সৌন্দর্য ধরিয়া রাখিতে পারিব না তাহাকেই চির উপভোগ করিতে চেষ্টা করা, এক কথায় অনন্ত মন অর্থাৎ সমষ্টিবদ্ধ কতকগুলি অনন্ত ক্ষুধা লইয়া জগতের পশ্চাতে অনন্ত ধাবমান হওয়াই মনুষ্য জীবন।” (আত্মসংসর্গ, বিবিধ প্রসঙ্গ)
(৪) “একেবারেই প্রেমের যোগ্য নহে এমন জীব কোথায়! যত বড়ই পাপী অসাধু কুশ্রী সে হউক না কেন, তাহার মা ত তাহাকে ভালবাসে। অতএব দেখিতেছি, তাহাকেও ভালবাসা যায়, তবে আমি ভালবাসিতে না পারি সে আমার অসম্পূর্ণতা।
… জগতের একটি প্রধান ধর্ম পরার্থপরতা। স্বার্থপরতা জগতের ধর্মবিরুদ্ধ।” (ধর্ম, আলোচনা)
(৫) “সৌন্দর্য উদ্রেক করিবার অর্থ আর কিছু নয়—হৃদয়ের অসাড়তা অবচেতনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া।
অতএব কবিদিগকে আর কিছু করিতে হইবে না, তাঁহারা কেবল সৌন্দর্য ফুটাইতে থাকুন—জগতের সর্বত্র যে সৌন্দর্য আছে, তাহা তাঁহাদের হৃদয়ের আলোকে পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখে পড়িতে থাকুক, তবে আমাদের প্রেম জাগিয়া উঠিবে, প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িবে।
… যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ। সে প্রেমের প্রভাবেই সুন্দর হইয়াছে। তাহার আদ্যন্তমধ্য প্রেমের সূত্রে গাঁথা। তাহার কোনখানে বিরোধ বিদ্বেষ নাই।” (সৌন্দর্য ও প্রেম, আলোচনা)
(৬) “প্রকৃত কথা এই যে, প্রেম একটি সাধনা। … স্বদেশের শরীর ক্ষুদ্র, স্বদেশের হৃদয় বৃহৎ। স্বদেশের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছি। স্বদেশের প্রত্যেক গাছপালা আমাদের চোখে ঠেকে না, আমরা একেবারেই তাহার ভিতরকার ভাব, তাহার হৃদয়পূর্ণ মাধুরী দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য এই স্বাধীনতা সফল দেশের সকল লোকেই সমান উপভোগ করিতে পারেন।” (ডুব দেওয়া, আলোচনা)
সমালোচকদের মতে, উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি একথাই প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে ভালবাসার দেবতা স্বভাবসন্ন্যাসী ছিলেন। আসক্তি থেকে অনাসক্তিতে, ক্ষুদ্র থেকে ভূমায়, সংকীর্ণ থেকে বৃহতে এর গতি ছিল। রবীন্দ্রনাথের মত ছিল যে, এই গতি-ই হচ্ছে জীবন, এই গতি-ই হচ্ছে প্রেম। এই গতি সর্বদা ঊর্ধ্বায়নের (sublimation) পথে ঘটে। প্রেমে যেমন সৌন্দর্য রয়েছে, তেমনি প্রেমে ব্যাপ্তি ও সামঞ্জস্যও রয়েছে। প্রেমের অধিকার মানে বৈষয়িক অধিকার নয়,—হৃদয়ের অধিকার, স্বত্ব-স্বামিত্বের অধিকার নয়,—দানের অধিকার। প্রেমের দিব্যাবভায় জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। প্রেমসাধনার গতি যে ঊর্ধ্বগামী, সেটা যে আত্মাবসর্জনোন্মুখ ও মুক্তিকামী, সেটা যে কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত উদ্যাপনেই মুক্তি পায়, পরবর্তীকালের রবীন্দ্রসাহিত্যে একথাই বারবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছিলেন যে, সম্পূর্ণ প্রেমের দ্বারা যা লভ্য, জ্ঞান বা শরীরের দ্বারা যে অংশই লভ্য, সেই প্রেমই হল সর্বসাধ্যসার। আর এই প্রত্যয়ের আলোকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যৌবনে প্রেমের বন্দনা করেছিলেন। এমনকি নিজের ‘আলোচনা’ নামক গ্রন্থের ‘সৌন্দর্য ও প্রেম’ নামক প্রবন্ধে শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং–এর ‘Inclusions’ কবিতাটি উদ্ধৃত করে তিনি তাঁর এই বক্তব্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। উক্ত কবিতাটিতে বলা হয়েছে যে, প্রেমের যে মিলন, সেটা মূলতঃ আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন, অংশের সঙ্গে অংশের মিলন নয়,—বরং সম্পূর্ণের মিলনোপলব্ধি।
“Oh, must thou have my soul, Dear,
Commingled with thy soul,—
Red grows the cheek, and warm the
Hand … the part is in the whole!
Nor hands nor cheeks keep separate,
When soul is joined to soul.”
রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিন্তাও এই আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনের মহৎ ধ্যানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর এজন্যই তিনি বলেছিলেন—
(১) “প্রেম নামক এক অনির্বচনীয় আনন্দময় বেদনাময় ইচ্ছাশক্তি পঙ্কের মধ্য হইতে পঙ্কজীবন জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন।” (পঞ্চভূত)
(২) “ত্যাগের সহিত প্রেমের একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, ত্যাগ ছাড়া প্রেম হয় না, প্রেম না থাকিলে ত্যাগ করাও যায় না।” (প্রেম, শান্তিনিকেতন)
(৩) “ভালবাসায় মার্জনা এবং দুঃখস্বীকারে যে সুখ, ইচ্ছা পূরণ ও আত্মপরিতৃপ্তিতে সে সুখ নেই।” (চিঠিপত্র, ১)
(৪) “প্রেমের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে, রচনা করে, নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান, গন্ধ, নানা আভাস। এমনি করে অন্তরে বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃত লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নিনিত হতে থাকে।” (‘মহুয়া’র কবিকৃত ভূমিকা)
(৫) “প্রকৃতি যখন প্রেমের সারখ্য নেয় তখন সে প্রবৃত্তির জোয়ালে তাকে বাঁধে। কিন্তু ধর্ম যখন তার চালক হয় তখন সে প্রেম মুক্ত রূপে প্রকাশ পায়। নিবৃত্তিশান্ত আত্মত্যাগরত প্রেমের সেই অচঞ্চল মুক্ত স্বরূপই পরম সুন্দর।” (ভারতবর্ষীয় বিবাহ, সমাজ)
সমালোচকদের মতে, রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্যগুলি উপরিধৃত অভিমতকেই সমর্থন করে।
আবার ১৯০৭ সালে প্রকাশিত ‘প্রাচীন সাহিত্য’ নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাসের প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে নিজস্ব বক্তব্যকেই নিপুণভাবে প্রকাশ করেছিলেন। বাসনার আগ্নেয় আতিশয্যকে রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রথম জীবনে কিংবা উত্তর জীবনে—বস্তুতঃ কোন জীবনেই কখনোই সমর্থন করেননি। কারণেই নিজের ‘প্রাচীন সাহিত্য’ নামক গ্রন্থে কালিদাসের কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার আলোচনা করতে গিয়ে কবি লিখেছিলেন—
“দুটিরই কাব্যবিষয় নিগূঢ়ভাবে এক। দুই কাব্যেই মদন যে মিলন সংসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে; সে মিলন অসম্পন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া আপনার বিচিত্র কারুখচিত পরমসুন্দর বাসরশয্যার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে। তাহার পরে কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত দ্বারা যে মিলন সম্পন্ন হইয়াছে তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ, তাহা সৌন্দর্যের সমস্ত বাহ্যাবরণ পরিত্যাগ করিয়া বিরলনির্মল বেশে কল্যাণের শুভ দীপ্তিতে কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।”
লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, এর প্রায় পঁচিশ বছর আগে লেখা ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ গ্রন্থের ‘মনের বাগান বাড়ি’ রচনায় বাইশ বছরের তরুণ যুবক রবীন্দ্রনাথ এই বক্তব্যই উচ্চারণ করেছিলেন। আর পরবর্তীকালে প্রায় পঞ্চাশ বছরের উপান্তে উপনীত প্রত্যয়-অভিজ্ঞতা-খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত ঋষি রবীন্দ্রনাথও এই একই কথা বলেছিলেন। তাছাড়া নারীর মধ্যে প্রেমের প্রবর্তনাকে এই দৃষ্টতেই দেখে কবি তাঁর ‘সমাজ’ (১৯০৮) নামক গ্রন্থে যে কথা বলেছিলেন, সেটাও তাঁর ‘প্রাচীন সাহিত্য’ নামক গ্রন্থের বক্তব্যের পরিপূরক ছিল বলেই দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ নিম্নরূপ—
“নারীর দুটি রূপ, একটি মাতৃরূপ, অন্যটি প্রেয়সীরূপ। মাতৃরূপে নারীর একটি সাধনা আছে … মানব সংসারে তা পাপকে, অভাব অপূর্ণতাকে জয় করে। প্রেয়সীরূপে তার সাধনায় পুরুষের সর্বপ্রকার উৎকর্ষ চেষ্টাকে প্রাণবান করে তোলে।” (ভারতবর্ষীয় বিবাহ, সমাজ)
এরপরে আবার সত্তর বছর বয়সে উপনীত কবি প্রেমের কল্যাণীরূপের, আত্মদান রূপের ও ত্যাগরূপের বন্দনা করে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি’ নামক গ্রন্থের ‘যাত্রী’ নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—
“নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণশক্তিতে জাগ্রত করতে পারে; কিন্তু সে প্রেম যদি শুক্লপক্ষের না হয়ে কৃষ্ণপক্ষের হয় তবে তার মালিন্যের আর তুলনা নেই। পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যায়; নাবীর প্রেমে ত্যাগধর্ম সেবাধর্ম সেহ তপস্যারই সুরে সুর মেলানো; এই দুয়ের যোগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নারীর প্রেমে আর এক সুরও বাজতে পারে, মদনধনুর জ্যায়ের টংকার—সে মুক্তির সুর, না, বন্ধনের সংগীত। তাতে তপস্যা ভাঙে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়।”
রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচকদের মতে, রবীন্দ্রনাথের ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ থেকে ‘যাত্রী’—প্রায় অর্ধশতাব্দী সময়সীমার মধ্যে রচিত বিভিন্ন গদ্যরচনায়—তাঁর প্রেমচিন্তার মূল বক্তব্য একই থেকে গিয়েছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি এসময়ের মধ্যে রচিত রবীন্দ্রকাব্য, উপন্যাস ও নাটকেও এই সত্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। এবং কবির ‘মহুয়া’ নামক কাব্যগ্রন্থের ‘মায়া’ নামক কবিতাটি এই সত্যেরই সংহত রূপ ছিল বলে দেখা যায়।#