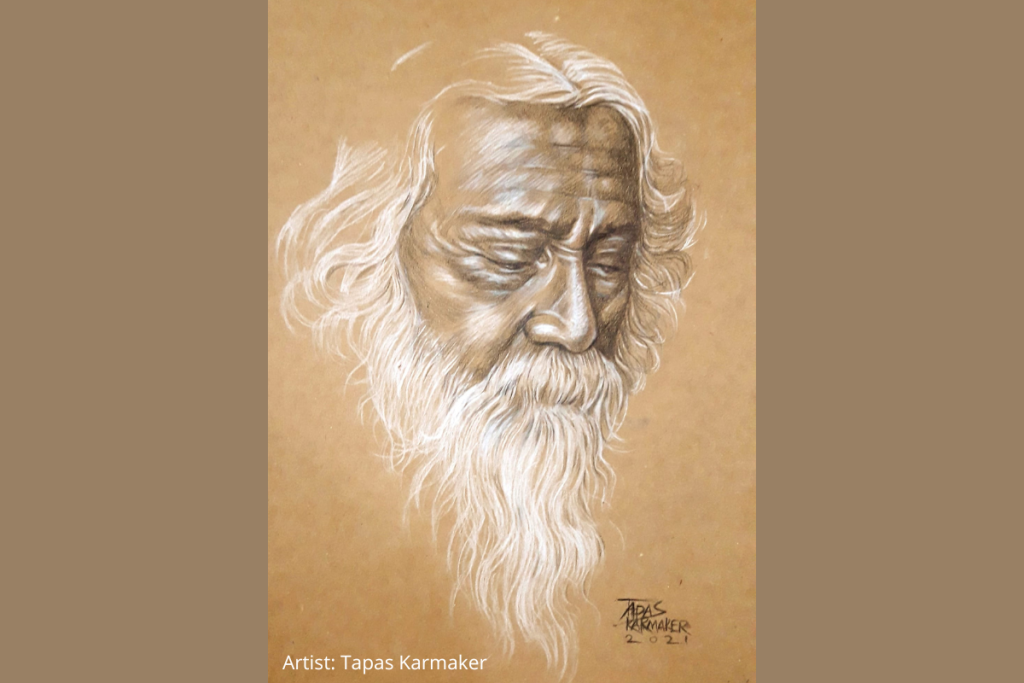১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে অকস্মাৎ মজঃফরপুরে প্রচণ্ড বোমার বিস্ফোরণে সমগ্র ভারতবর্ষ সচকিত হয়ে উঠেছিল। সেই সময়কার কুখ্যাত অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর ছোঁড়া বোমার আঘাতে মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যা নিহত হয়েছিলেন। এরপরেই সুরাট-কংগ্রেসের ঠিক তিনদিন আগে গোয়ালন্দে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেন বিপ্লবীদের হাতে অতর্কিতে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। তারপরে একে একে বিপ্লবীদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হতে শুরু করেছিল। ফলে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, কানাইলাল দত্ত-সহ একঝাঁক তরুণ বিপ্লবী নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। পরাধীন দেশের ধমনীতে অকস্মাৎ যেন প্রাণের প্রবল স্পন্দন শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। আনন্দে, বিস্ময়ে ও আতঙ্কে সমগ্র দেশ শিহরিত হয়ে উঠেছিল। গ্রেপ্তার হয়েই বারীন্দ্র জানিয়েছিলেন — “My mission is over”; এরপরে নিজের মন্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—
“আমাদিগকে প্রকাশ্যে রাজদ্বারে ঘাতকহস্তে স্বেচ্ছায় যাচিয়া জীবন দিতে না দেখিলে, বুঝি এ মরণভীরু জাতি মরিতে শিখে না।” (আত্মকাহিনী, বারীন্দ্র ঘোষ, পৃ: ৫০-৫১)
এসবের মাধ্যমে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটি অভিনব ধারা এসে মিলিত হয়েছিল, যেটার নাম ছিল— সশস্ত্র বিপ্লবীবাদ। অন্যদিকে ইংরেজ গভর্নর থেকে শুরু করে সমকালীন দেশী-বিদেশী পত্রিকাগুলি একবাক্যে সেইসব কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করতে শুরু করেছিল। তৎকালীন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারাও একবাক্যে সেই পথের নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে দেশের যুবকদের বহু উপদেশ দিতে শুরু করেছিলেন। শুধুমাত্র লোকমান্য তিলকই তখন তাঁর ‘কেশরী’ পত্রিকায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনকে পরোক্ষভাবে কিছুটা সমর্থন করেছিলেন। তিলক বৃটিশ সরকারের ক্রিয়াকলাপ ও দমননীতিকেই ওই ধরণের বিপ্লবী কার্যকলাপের উদ্ভবের কারণ বলে সরকারের প্রতি পাল্টা অভিযোগ জানিয়েছিলেন। ফলে তিলকের ছ’বছরের কারাদণ্ডের শাস্তি হয়েছিল। বলাই বাহুল্য যে, সেই সময়কার অমন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হয়নি। সেই কারণে, তিলকের দণ্ডাদেশের কয়েকদিন পরে কলকাতায় উপস্থিত হয়ে চৈতন্য লাইব্রেরিতে তিনি তাঁর ‘পথ ও পাথেয়’ নামক প্রবন্ধটি (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ) পাঠ করেছিলেন (১২ই জ্যৈষ্ঠ)। ওই সময়ে যেসব প্রবীণ কংগ্রেস নেতারা নিজেদের নিরাপদ বিবৃতির অন্তরালে— “আমি ইহার মধ্যে নাই; এ কেবল অমুকদলের কীর্তি, এ কেবল অমুক লোকের অন্যায়; আমি পূর্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি, এসব ভালো হইতেছে না” — ইত্যাদি বলে নিজেদের নির্দোষ বলে প্রমাণ করবার চেষ্টায় অতিমাত্র উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে প্রথমেই তাঁদের তিরস্কার করে বলেছিলেন—
“কোনো আতঙ্কজনক দুর্ঘটনার পর এই প্রকার অশোভন উৎকণ্ঠার সহিত পরের প্রতি অভিযোগ বা নিজের সুবুদ্ধি লইয়া অভিমান আমার কাছে দুর্বলতার পরিচয় সুতরাং লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ আমরা প্রবলের শাসনাধীনে আছি এইজন্য রাজপুরুষদের বিরাগের দিনে অন্যকে গালি দিয়া নিজেকে ভালোমানুষের দলে দাঁড় করাইতে গেলে তাহার মধ্যে কেমন–একটা হীনতা আসিয়া পড়েই। … তাহার পরে, যাঁহারা অপরাধ করিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে, নির্মম রাজদণ্ডযাঁহাদের ’পরে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, আর-কিছু বিচার না করিয়া কেবলমাত্র বিপদ ঘটাইয়াছে বলিয়াই তাঁহাদের প্রতি তীব্রতা প্রকাশ করাও কাপুরুষতা।”
আরও পড়ুন: বাউলের পথেই রবীন্দ্রনাথ
দেশের তৎকালীন অবস্থার পটভূমিতে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লববাদী প্রচেষ্টা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—
“…বস্তুতঃ বহুদিন হইতে বাঙালিজাতি ভীরু অপবাদের দুঃসহ ভার বহন করিয়া নতশির হইয়াছে বলিয়াই বর্তমান ঘটনা সম্বন্ধে ন্যায় অন্যায় ইষ্ট অনিষ্ট বিচার অতিক্রম করিয়াও অপমান-মোচনের উপলক্ষে বাঙালির মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই।”
তবে এতকিছু বলা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের নীতিকে সমর্থন করতে পারেননি। বোয়ার যুদ্ধের সময় থেকেই তিনি পুনঃ পুনঃ শুধু একটি কথাই জোর দিয়ে বলে আসছিলেন যে, ইউরোপের রাষ্ট্রনীতি মানবতা, ন্যায়নীতি ও ধর্মাধর্মবোধকে নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করে চলেছে। কলকাতার চৈতন্য লাইব্রেরিতে দেওয়া ভাষণেও তিনি সেই নীতির বিস্তারিত সমালোচনা করে বলেছিলেন—
“য়ুরোপের এই অবিশ্বাসী রাষ্ট্রনীতি আজ পৃথিবীর সর্বত্রই ধর্মবুদ্ধিকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। এমন অবস্থায় যখন বিশেষ ঘটনায় বিশেষ কারণে কোনো অধীন জাতি সহসা নিজেদের অধীনতার ঐকান্তিক মূর্তি দেখিয়া সর্বান্তঃকরণে পীড়িত হইয়া উঠে, অথচ নিজেদের সর্বপ্রকার নিরুপায়তার অপমানে উত্তপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে একদল অধীর অসহিষ্ণু ব্যক্তি যখন গোপন পন্থা অবলম্বন করিয়া কেবল ধর্মবুদ্ধিকে নহে কর্মবুদ্ধিকেও বিসর্জন দেয় তখন দেশের আন্দোলনকারী বক্তাদিগকেই এইজন্য দায়ী করা বলদর্পে-অন্ধ গায়ের জোরের মূঢ়তা মাত্র। অতএব দেশের যে-সকল লোক গুপ্তপন্থাকেই রাষ্ট্রহিত সাধনের একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাঁহাদিগকে গালি দিয়াও কোনো ফল হইবে না এবং তাঁহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিতে গেলেও তাঁহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। আমরা যে যুগে বর্তমান এযুগে ধর্ম যখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নিকট প্রকাশ্যভাবে কুষ্ঠিত তখন এরূপ ধর্মভ্রংশতার যে দুঃখ তাহা সমস্ত মানুষকেই নানা আকারে বহন করিতেই হইবে; রাজা ও প্রজা, প্রবল ও দুর্বল, ধনী ও শ্রমিক কেহ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। রাজাও প্রয়োজনের জন্য প্রজাকে দুর্নীতির দ্বারা আঘাত করিবে এবং প্রজাও প্রয়োজনের জন্য রাজাকেও দুর্নীতির দ্বারা আঘাত করিতে চেষ্টা করিবে এবং যে সকল তৃতীয়পক্ষের লোক এই-সমস্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত নহে তাঁহাদিগকেও এই অধম সংঘর্ষের অগ্নিদাহ সহ্য করিতে হইবে।”
সেদিন একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মতোই রবীন্দ্রনাথ যেন ঘটনাস্রোতের অনিবার্য অমোঘ পরিণতিটি স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ব্যথা ও মানসিক যন্ত্রণাটি যে কোথায় ছিল, সেকথা বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। সেযুগে যেসব যুক্তি ও ন্যায়-শাস্ত্রের উপরে ভিত্তি করে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, ভারতবর্ষের মত মহান দেশের মুক্তি-আন্দোলন সেইসব নীতির উপরেই ভিত্তি করে গড়ে উঠবে,— রবীন্দ্রনাথ এটা কখনই সহ্য বা সমর্থন করতে পারেননি। তাই তিনি বলেছিলেন—
“… প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয়— কোনো সংকীর্ণ রাস্তা ধরিয়া কাজ সংক্ষেপ করিতে গেলে একদিন দিক হারাইয়া শেষে পথও পাইব না, কাজও নষ্ট হইবে। আমার মনের তাগিদ অত্যন্ত বেশি বলিয়া জগতে কোনোদিন রাস্তাও নিজেকে ছাঁটিয়া দেয় না, সময়ও নিজেকে খাটো করে না। … দুঃখ সহ্য করা তত কঠিন নহে, কিন্তু দুর্মতিকে সংবরণ করা অত্যন্ত দুরূহ। অন্যায়কে অত্যাচারকে একবার যদি কর্মসাধনের সহায় বলিয়া গণ্য করি তবে অন্তঃকরণকে বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি চলিয়া যায়; ন্যায়ধর্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে, কর্মের স্থিরতা থাকে না, তখন বিশ্বব্যাপী ধর্মব্যবস্থার সঙ্গে আবার আমাদের ভ্রষ্ট জীবনের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্ত প্রচণ্ড সংঘাত অনিবার্য হইয়া উঠে।”
আরও পড়ুন: কবিতার সঙ্গে কবি
চৈতন্য লাইব্রেরিতে প্রদত্ত ভাষণে, সংগ্রামের নীতি সম্পর্কে এটাই কবির মূল কথা ছিল। এখানে মনে রাখতে হবে যে, ‘Means’ ও ‘End’–এর বিতর্ক তখনও পর্যন্ত এদেশে আমদানি হয়নি। ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রাম মহোত্তম ন্যায়-নীতি ও ধর্মবুদ্ধির উপরে ভিত্তি করে উত্তরোত্তর ক্রম-পরিণতি লাভ করুক, এটাই কবির মূল বক্তব্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রবিপ্লবকে একেবারে অস্বীকার করেননি; কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবের নেতিমূলক দিকের থেকে ইতিমূলক বা গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির উপরে বেশি গুরুত্ব অরোপ করিতে গিয়ে বলেছিলেন—
“… রাষ্ট্র বা সমাজে অসামঞ্জস্যের বোঝা অনেকদিন হইতে নিঃশব্দে পুঞ্জীভূত হইতে হইতে একদিন একটা আঘাতে হঠাৎ তাহা বিপ্লবে ভাঙিয়া পড়ে। সেই সময় দেশের মধ্যে যদি অনুকূল উপকরণ প্রস্তুত থাকে, পূর্ব হইতেই যদি তাহার ভাণ্ডারে নিগূঢ়ভাবে জ্ঞান ও শক্তির সম্বল সঞ্চিত থাকে, তবেই সেই বিপ্লবের দারুণ আঘাতকে কাটাইয়া সে দেশ আপনার নূতন জীবনকে নবীন সামঞ্জস্য দান করিয়া গড়িয়া তোলে। … গড়িয়া তুলিবার বাঁধিয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাঁহাদের মধ্যে সজীবভাবে বিদ্যমান, ভাঙনের আঘাত তাঁহাদের এই জীবনধর্মকেই তাঁহাদের সৃজনীশক্তিকেই সচেষ্ট সচেতন করিয়া তোলে। এইরূপে সৃষ্টিকেই নূতন বলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা শুদ্ধমাত্র ভাঙন, নির্বিচার বিপ্লব কোনো মতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।”
রবীন্দ্রনাথ সেই সময়কার রাজনৈতিক আন্দোলনে এই গঠনমূলক প্রচেষ্টার একান্তই অভাব লক্ষ্য করেছিলেন বলেই তিনি কোনো পক্ষেরই (অহিংস ও সশস্ত্র) রাজনীতিকে তখন সমর্থন করতে পারেননি। সেযুগের রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি তাঁর অভিযোগ ছিল—
“… যাহার ভিতরে গড়নের শক্তি নাই ভাঙন তাহার পক্ষে মৃত্যু। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশে সেই গঠনতত্ত্বটি কোথায় প্রকাশ পাইতেছে। কোন সৃজনীশক্তি আমাদের মধ্যে ভিতর হইতে কাজ করিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া এক করিয়া তুলিতেছে। ভেদের লক্ষণই তো চারিদিকে। … ভারতবর্ষে এত জাতিবিভাগসত্ত্বেও কেমন করিয়া এক মহাজাতি হইয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিবে এই প্রশ্ন যখন উঠে তখন আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ তরান্বিত তাঁহারা এই বলিয়া কথাটা সংক্ষেপে উড়াইয়া দেন যে, সুইজারল্যাণ্ডেও ভো একাধিক জাতির সমাবেশ হইয়াছে, কিন্তু সেখানে কি তাহাতে স্বরাজের বাধা ঘটিয়াছে।”
এরপরে তিনি বলেছিলেন—
“… সুইজারল্যাণ্ড যদি নানা জাতিকে লইয়াই এক হইয়া থাকে তবে ইহাই বুঝিতে হইবে সেখানে নানাত্বকে অতিক্রম করিয়াও একত্ব কর্তা হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। সেখানকার সমাজে এমন একটি ঐক্যধর্ম আছে। আমাদের দেশে বৈচিত্র্যই আছে, কিন্তু ঐক্যধর্মের অভাবে বিশ্লিষ্টতাই ভাষা জাতি ধর্ম সমাজ ও লোকাচারে নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া এই বৃহৎ দেশকে ছোটো বড়ো বহুতর ভাগে বিভাগে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।”
সেই সময়কার আরেকদল মানুষ বলেছিলেন যে, ইংরেজ সম্রাজ্যবাদ ভারতের সব মানুষেরই সাধারণ শত্রু। কারণ— ইংরেজদের অত্যাচারে তখন ভারতের সব জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়গুলি নিষ্পেষিত হচ্ছিল। সুতরাং তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, তৎকালীন ভারতের সকলেই ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই সাধারণ বিদ্বেষই ভারতীয়দের মধ্যে ‘মহাজাতীয় ঐক্য’ গড়ে তুলবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একথায় বিশ্বাস করতেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—
“একথা যদি সত্য হয় তবে বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনই এ দেশ ত্যাগ কবিবে তখনই কৃত্রিম ঐক্যসূত্রটি তো এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয বিদ্বেষের বিষয় আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইব। তখন আর দূরে খুঁজিতে হইবে না, বাহিরে যাইতে হইবে না, রক্তপিপাসু বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব।”
রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কবাণীর প্রতি উপেক্ষা বর্তমান সময়ে একটা অভিশাপেব মত ভারতবর্ষকে বারবার আঘাত করেছে; ভারতের সাম্প্রতিক ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাষা ও জাতিবিদ্বেষ ভারতের মর্মকেন্দ্রকে পীড়িত ও কলুষিত করে তুলেছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে ভারতের ভাষা ও জাতি-সমস্যাকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দিক থেকে বিচার করেছিলেন, এমনটা কিন্তু নয়। তাঁর মূল কথা ছিল যে, ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের উপরে ভিত্তি করে নয়, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক মিলনের উপরে ভিত্তি করেই ভারতের যথার্থ জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠতে পারে। বহুদিন আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বটি প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করে আসছিলেন যে— ‘ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান ঐতিহ্য মিলনমূলক।’ তাঁর বক্তব্য ছিল যে, ভারতবর্ষের স্বাদেশিক সাধনায় এই মিলনতত্ত্বকেই সচেষ্টভাবে সফল করে তুলতে হবে। এই প্রসঙ্গে কলকাতার চৈতন্য লাইব্রেরিতে প্রদত্ত বক্তৃতার উপসংহারে তিনি আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন—
“… এই ভারতবর্ষে যুগযুগান্তরীয় মানবচিত্তের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাবেগ মিলিত হইয়াছে— এইখানেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের মন্থন হইবে, জাতির সহিত জাতির মিলন ঘটিবে। বৈচিত্র্য এখানে অত্যন্ত জটিল, বিচ্ছেদ এখানে অত্যন্ত প্রবল, বিপরীতের সমাবেশ এখানে অত্যন্ত বিরোধসংকুল— এত বহুত্ব এত বেদনা এত সংঘাত কোনো দেশই এত দীর্ঘকাল বহন করিয়া বাঁচিতে পারিত না— কিন্তু একটি অতিবৃহৎ অভিমহৎ সমন্বয়ের পরম অভিপ্রায়ই এই-সমস্ত একান্ত বিরুদ্ধতাকে ধারণ করিয়া আছে, পরস্পরের আঘাতে কাহাকেও উৎসাদিত হইতে দেয় নাই। … জানিয়া এবং না জানিয়া বিশ্বের মানব এই ভারতক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের যে পরমাশ্চর্য মন্দির নানা ধর্ম, নানা শাস্ত্র, নানা জাতির সম্মিলনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই সাধনাতেই যোগদান করিব, নিজের অন্তরের সমস্ত শক্তিকে একমাত্র সৃষ্টিশক্তিতে পরিণত করিয়া এই রচনাকার্যে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব। তাহা যদি করিতে পারি, যদি জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে ভারতবর্ষের এই অভিপ্রায়ের মধ্যে সমস্ত প্রাণ দিয়া নিযুক্ত হইতে পারি, তবেই মোহমুক্ত পবিত্র দৃষ্টিতে স্বদেশের ইতিহাসের মধ্যে সেই একসত্য, সেই নিত্যসত্যকে দেখিতে পাইব। ঋষিরা যাঁহাকে বলিয়াছেন, ‘স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাম্’— তিনিই সমস্ত লোকের বিধৃতি, তিনিই সমস্ত বিচ্ছেদের সেতু।” (পথ ও পাথেয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৪৪৫-৬৭)
আরও পড়ুন: ভারতীয় দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ
একথা নিঃসন্দেহে একজন অধ্যাত্মবাদী কবির মহৎ ভাবোচ্ছ্বাস ছিল। কিন্তু সেইসঙ্গে আরও যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় সেটা হল যে— এতদিন পর্যন্ত, বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক আন্দোলনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে সমালোচনা করে জনসংযোগ ও পল্লী-উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশের সাংগঠনিক প্রস্তুতির উপরে বেশি পরিমাণে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু আলোচ্য ভাষণে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের আবেগ-উন্মত্ততার মাঝে যেন রাজনীতি কিংবা সমাজ-উন্নয়ের থেকে আধ্যাত্মিক মানবতার উপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। হিংসা, বিরোধ ও অত্যাচারের সমস্ত কালিমা ধুয়ে মুছে ভারতবর্ষই সর্বজাতি-মিলনের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠুক— এটাই কবির কামনা ছিল।
এর কিছুদিন পরে, ১৩১৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যার প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত ‘সমস্যা’ নামক একটি প্রবন্ধে তিনি তাঁর বক্তব্যের বিষয়কে আরো পরিষ্কার করে জানিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের মত একটা বিশাল দেশে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় নিয়ে তখনও পর্যন্ত একটি মহাজাতি বা মহাজাতীয় ঐক্য গড়ে উঠতে পারেনি, এবং রবীন্দ্রনাথের মতে সেটাই ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—
“একথা বলাই বাহুল্য, যে দেশে একটি মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই সে দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না। কারণ স্বাধীনতার ‘স্ব’ জিনিসটা কোথায়? স্বাধীনতা কাহার স্বাধীনতা? ভারতবর্ষে বাঙালি যদি স্বাধীন হয় তবে দাক্ষিণাত্যের নায়ার জাতি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে না এবং পশ্চিমের জাঠ যদি স্বাধীনতা লাভ করে তবে পূর্বপ্রান্তের আসামি তাহার সঙ্গে একই ফল পাইল খলিয়া গৌরব করিবে না। এক বাংলাদেশেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।”
তৎকালীন ভারতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—
“… আমরা হিন্দু ও মুসলমান, আমরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় হিন্দুজাতি এক জায়গায় বাস করিতেছি বটে কিন্তু আমাদের সমস্ত হৃদয়বৃত্তি সমস্ত হিতচেষ্টা পরিবার ও বংশের মধ্যে এবং এক-একটি সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে এতই অতিশয় পরিমাণে নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বীকার করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্বৃত্ত রাখি নাই। সেই কারণে আমরা দ্বীপপুঞ্জের মতোই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মতো ব্যাপ্ত বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই।”
রবীন্দ্রনাথ সেই সময়কার জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের সমস্যাগুলিকে বারেবারে বিভিন্ন দিক থেকে দেখেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন—
“… পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় স্বভাবে আচরণে ধর্মে বিচিত্র-নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট— সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে নির্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে, কিন্তু সর্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি দ্বারা, মানবের প্রতি সর্বসহিষ্ণু পরমপ্রেমের দ্বারা, উচ্চনীচ আত্মীয়পর সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া। আর কিছু নহে, শুভচেষ্টার দ্বারা দেশকে জয় করিযা লও— যাঁহারা তোমাকে সন্দেহ করে তাঁহাদের সন্দেহকে জয় করো, যাঁহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে তাঁহাদের বিদ্বেষকে পরাস্ত করো। রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করো, বারংবার আঘাত করো— কোনো নৈরাশ্যে, কোনো আত্মাভিমানের ক্ষুণ্ণতায় ফিরিয়া যাইয়ো না, মানুষেব হৃদয় মানুষের হৃদয়কে চিরদিন কখনোই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।” (সমস্যা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৪৭৯-৮৩)
আরও পড়ুন: জ ন্ম দি ন
ব্রাহ্মধর্মের ঐতিহ্যসম্পন্ন পারিবারিক ধর্মসাধনার আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ মানুষ হয়েছিলেন। সুতরাং একদিকে তাঁর ঈশ্বর ও ধর্মোপলব্ধি যেমন জাতীয় ও বিশ্ব-সমস্যার ক্ষেত্রে ক্রমশঃই তাঁর চেতনায় একটি অখণ্ড বিশ্ব ঐক্যানুভূতি এনে দিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি স্বদেশ ও স্বজাতির মরণান্তিক দুঃখ ও সমস্যাগুলি এবং সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের জাতি-বিদ্বেষ ও পরজাতিশোষণের নিষ্ঠুর স্বরূপটি ক্রমশঃই তাঁকে বিশ্বমানবতার দিকে আকৃষ্ট করেছিল। এককথায়, জাতীয় সমস্যা ও বিশ্ব-সমস্যার সমাধানে তাঁকে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। এখানে মনে রাখা দরকার যে, তখনও পর্যন্ত ভারতে আধুনিক দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক অর্থনীতি-রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেনি। তাছাড়া একথাও উল্লেখযোগ্য যে, এমনকি বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ সংগ্রামপন্থীরা পর্যন্ত তখন আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে প্যাট্রিয়জমের, অর্থাৎ— ধর্মের সঙ্গে স্বাদেশিকতার মিশ্রণ করে নিজেদের জ্বালাময়ী ভাষায় প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মাধ্যমে দেশের স্বাদেশিকতাবোধকে জাগ্রত করেছিলেন। আরও উল্লেখযোগ্য যে, বিপিনচন্দ্র তখন বক্সা জেলে বসেই তাঁর ‘Study of Hinduism’ নামক পুস্তকটি লিখেছিলেন। অরবিন্দের গীতা ও বৈদান্তিক মায়াবাদ সেযুগের সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রেরণার প্রধান উৎস ছিল। প্রসঙ্গতঃ একথাও স্মরণীয় যে, সেযুগে শুধুমাত্র মডারেটপন্থীরাই শুরু থেকেই ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে যথাসম্ভব রাজনীতি থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টারি রাজনীতির শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁরা রাজনীতিকে শুধু রাজনীতি হিসাবেই বিচার করবার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় তখনও বয়কট আন্দোলন চলছিল। সেই উপলক্ষ্যে তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশ এবং দেশকর্মীরা জায়গায় জায়গায় অশিক্ষিত অনুন্নত শ্রেণীর উপরে কিছুটা যে বল প্রয়োগ করছিলেন না, এমনটা নয়। অন্যদিকে, মুসলমান সম্প্রদায় সেই বয়কট আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। এবং তখন শুধু বয়কট উপলক্ষ্যেই নয়— নানা অজুহাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ক্রমশঃই ব্যাপক আকার ধারণ করছিল। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত সংবাদই পাচ্ছিলেন। তখনকার ওই ডামাডোল অবস্থায় দেশনায়ক ও দেশকর্মীদের লক্ষ্য করে, ১৩১৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যার প্রবাসী পত্রিকায় তিনি ‘সদুপায়’ শিরোনামের প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি বয়কট আন্দোলনের বিস্তারিত পর্যালোচনা করে সেটার বিপদজ্জনক পরিণতিটি স্পষ্ট করে নির্দেশ করেছিলেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই প্রবন্ধে ‘অখণ্ড বাংলা’–র শ্লোগানটি মোহমুক্ত দৃষ্টিতে বিচার করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—
“… বেহারিগণ বাঙালির প্রতিবেশী এবং বাঙালি অনেকদিন হইতেই বেহারিগণের সঙ্গে কারবার করিতেছে, কিন্তু বাঙালির সঙ্গে বেহারির সৌহৃদ্য নাই সে কথা বেহারবাসী বাঙালি মাত্রেই জানেন। শিক্ষিত উড়িয়াগণ বাঙালি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া দাঁড় করাইতে উৎসুক এবং আসামিদেরও সেইরূপ অবস্থা। অতএব উড়িষ্যা আসাম বেহার ও বাংলা জড়াইয়া আমরা যে দেশকে বহুদিন হইতে বাংলাদেশ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি তাহার সমস্ত অধিবাসী আপনাদিগকে বাঙালি বলিয়া কখনও স্বীকার করে নাই এবং বাঙালিও বেহারি উড়িয়া এবং আসামিকে আপন করিয়া লইতে কখনও চেষ্টামাত্র করে নাই, বরঞ্চ তাঁহাদিগকে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া অবজ্ঞা দ্বারা পীড়িত করিয়াছে। … অতএব বাংলাদেশের যে অংশের লোকেরা আপনাদিগকে বাঙালি বলিয়া জানে সে অংশটি খুব বড়ো নহে।”
বাস্তবে ‘বাঙালিয়ানা’–র সেন্টিমেন্টকে এতটা আঘাত করে এমন সত্যি কথা সেযুগের অন্য কেউ বলবার সাহস দেখাননি। এর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন—
“এমন অবস্থায় এই বাঙালির বাংলাটুকুকেও এমন করিয়া যদি ভাগ করা যায় যাহাতে মুসলমান-বাংলা ও হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলাদেশের মতো এমন খণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর একটিও থাকিবে না। … এমনস্থলে বঙ্গবিভাগের জন্য আমরা ইংরেজ-রাজের প্রতি যতই রাগ করি না কেন, এবং সেই ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতি-বর্জন আমাদের পক্ষে যতই একান্ত আবশ্যক হউক-না, তাহার চেয়ে বড়ো আবশ্যক আমাদের পক্ষে কী ছিল। না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের মধ্যে যাহাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা। … সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বযকট-ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইযাছিলাম, যে-কোনো প্রকারেই হোক, বয়কটকে জযী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশিমাত্রায চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিযাছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে সহাযতা করিলাম। … ক্রমশ লোকের সম্মতি জয় করিযা লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না। এই উপলক্ষে আমরা দেশের নিম্ন শ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম, তাহার ফল এই হইয়াছে, বাসনার অত্যুগ্রতার দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছি। আমরা যে সকল স্থানেই মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীব হিন্দুদের অসুবিধা ঘটাইয়া বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছি, একথা সত্য নহে। এমনকি, যাঁহারা বয়কটের কল্যাণে বিশেষ লাভবান হইয়াছে তাঁহারাও যে আমাদের বিরুদ্ধ হইয়াছে এমন প্রমাণও আছে।”
এর পিছনে আসল কারণ কি ছিল? রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, সেই বিভেদ বিদ্বেষ সৃষ্টি করবার পিছনে ইংরেজদের হাত থাকলেও, সেটা কিন্তু গৌণ কারণ ছিল। মুখ্য কারণ ছিল— সেই সময়কার দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, হিন্দু ও মুসলমান, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সত্যিকারের ব্যবধান। ভারতবাসীর নিজেদের মধ্যে থাকা সেই বিভেদ-বিদ্বেষ দূর না করেই সেকালের রাজনীতিজ্ঞরা তাঁদের মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাগুলি দেশের গরিব হিন্দু-মুসলমানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ফলে বয়কট বা স্বদেশী আন্দোলনের কোনো তাৎপর্যই সেইসব দরিদ্র জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারেননি। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—
“আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া ‘মা’ শব্দটাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি। এই শব্দের দ্বারা আমাদের হৃদয়াবেগ এতই জাগিয়া উঠে যে আমরা মনে করিতে পারি না, দেশের মধ্যে মা’কে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই। এইজন্য দেশের সাধারণ গণসমাজ যদি স্বদেশের মধ্যে মা’কে অনুভব না করে তবে আমরা অধৈর্য হইয়া মনে করি, সেটা হয় তাঁহাদের ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ভান, নয় আমাদের শত্রুপক্ষ তাঁহাদিগকে মাতৃবিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু আমরা যে মা’কে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নাই, এই অপরাধটা আমরা কোনোমতেই নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি নহি।”
অর্থাৎ— তিনি জনসংযোগ ও গণচেতনার প্রশ্নের উপরে জোর দিতে চেয়েছিলেন। ‘বয়কট’ আন্দোলনকে কার্যকরী করতে গিয়ে স্বদেশীরা তখন যে জোর জুলুম করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেটার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছিলেন—
“জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতি কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশী কাপড় পরাইয়া ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না। দেশের যে সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশী-প্রচারের ব্রত লইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি এই-সকল লোকের বিদ্বেষকে কি চিরস্থায়ী করা হয় না। … এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না। ‘যাঁহারা কখনও বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আমাদিগকে স্নেহ করে নাই, আমাদিগকে যাঁহারা সামাজিক ব্যবহারে পশুর অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করে, তাঁহারা আজ কাপড়-পরানো বা অন্য যে-কোনো উপলক্ষে আমাদের প্রতি জবরদস্তি প্রকাশ করিবে ইহা আমরা সহ্য করিব না’, দেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং নমঃশূদ্রের মধ্যে এইরূপ অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জোর করিয়া এমনকি ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিলাতী সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে। … তাই বলিতেছি, বিলাতি দ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহ-বিচ্ছেদের মতো এতবড়ো অহিত আর কিছু নাই। … সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না।”
আরও পড়ুন: প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে ভদ্র নারী এবং রবীন্দ্রনাথের ছায়াছবি পরিচালনা
প্রবন্ধটির উপসংহারে, রবীন্দ্রনাথ সেইসব বলপ্রয়োগ এবং গুপ্তহত্যা ও স্বশস্ত্র বিপ্লবী কার্যকলাপের নন্দা করে, রাজনৈতিক সংগ্রামের মূলনীতিটি ঠিক কি হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে বলেছিলেন—
“একটি কথা আমাদের কখনও ভুলিলে চলিবে না যে, অন্যায়ের দ্বারা, অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই, অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। অদ্য বারবার দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে অধ্যবসায়ই শক্তি এবং অধৈর্যই দুর্বলতা; প্রশস্ত ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান; এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা, তাহাই মানবের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা, মানবের মনুষ্য-ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস। প্রেমের কাজে, সৃজনের কাজে, পালনের কাজেই যথার্থভাবে আমাদের সমস্ত শক্তির বিকাশ ঘটে।” (সদুপায়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৫২৩-৩১)
এর কিছুদিন আগে শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারের একটি প্রশ্নের উত্তরে সেযুগের সশস্ত্র বিপ্লবীদের দ্বারা গুপ্তহত্যার নিন্দা করে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২৩শে বৈশাখ তারিখে তিনি লিখেছিলেন—
“মাতঃ, ইহা নিশ্চয় মনে রাখিবে, নিজের বা পরিবারের বা দেশের কাজে ধর্মকে লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করেন না। যদি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে পাপকে আশ্রয় করি তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। দেশের যে দুর্গতিদুঃখ আমরা আজ পর্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি তাহার গভীর কারণ আমাদের জাতির অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে— গুপ্ত চক্রান্তের দ্বারা নরনারী হত্যা করিয়া আমরা সে কারণ দূর করিতে পারিব না, আমাদের পাপের বোঝা কেবল বাড়িয়াই চলিবে। এই ব্যাপারে যে-সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও বিচলিতবুদ্ধি যুবক দণ্ডনীয় হইয়াছে তাঁহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে না— কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই দণ্ড আমাদের সকলের দণ্ড— ঈশ্বর আমাদিগকে এই বেদনা দিলেন— কারণ, বেদনা ব্যতীত পাপ দূর হইতে পারে না— সহিষ্ণুতার সহিত এ সমস্তই আমাদিগকে বহন করিতে হইবে— এবং ধর্মের প্রশস্ততর পথকেই অবলম্বন করিতে হইবে।” (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ- ৬৬২)
সেই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি উগ্র ধর্মবোধ ও কঠোর ন্যায়-নিষ্ঠার ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতনভাবে তৎকালীন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা আরোপ করতে চেয়েছিলেন। সেই সময়ে এদেশের কোনো কোনো ইংরেজি সংবাদপত্রে এমনতর মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল যে, বাংলার সমস্ত স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যেই কেমন যেন একটি আধ্যাত্মিকতা ঘেঁষারূপ রয়েছে। ওই ধরণের মন্তব্যগুলি কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাই তিনি সেই মন্তব্যকে উপলক্ষ্য করে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ‘দেশহিত’ নামক একটি প্রবন্ধে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের লক্ষ্য ও পন্থা সম্পর্কে তাঁর নিজের মতামত জানিয়েছিলেন। সেই প্রবন্ধের শুরুতেই কবি ইংরেজি সংবাদপত্রের ওই মন্তব্যের উল্লেখ করে বলেছিলেন—
“… লেখক বলেন যে, আমাদের দেশের এই স্বাদেশিকতার উৎসাহ গভীরতর আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ; এইজন্য ইহা একটা ধর্মসাধনার আকার ধারণ করিতেছে।”
এরপরে তিনি যেন কিছুটা গর্বের সঙ্গে সেই মন্তব্যটির সাথে নিজের সহমত পোষণ করে বলেছিলেন—
“এ কথা নিশ্চয় মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশের কোনো উদ্যোগ যদি দেশের সর্বসাধারণকে আশ্রয় করিতে চায় তবে তাহা ধর্মকে অবলম্বন না করিলে কোনো মতেই কৃতকার্য হইবে না। কোনো দেশব্যাপী সুবিধা, কোনো রাষ্ট্রীয় স্বার্থসাধনের প্রলোভন কোনোদিন আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে শক্তি সঞ্চার করে নাই। … অতএব আমাদের দেশের বর্তমান উদ্দীপনা যদি ধর্মের উদ্দীপনাই হইয়া দাঁড়ায়, দেশের ধর্মবুদ্ধিকে যদি একটা নূতন চৈতন্যে উদ্বোধিত করিয়া তোলে, তবে তাহা সত্য হইবে, স্থায়ী হইবে, দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।”
আরও পড়ুন: কালিম্পং-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং উপেক্ষিত গৌরিপুর হাউস
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, দেশের সেই ‘যজ্ঞের পবিত্র হুতাশন’–কে তখন শুধু ইংরেজদের যথেচ্ছাচারই নষ্ট করতে চাইছিল না, বরং একদল বিপথগামী স্বদেশী মানুষও সেটাকে পণ্ড ও কলুষিত করবার প্রচেষ্টায় রত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে সেই সময়কার সশস্ত্র বিপ্লবীদের কথাই বলেছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবীবাদ সম্পর্কে শুধু সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হননি, অত্যন্ত কঠোরভাবে সশস্ত্র বিপ্লবীবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার জন্য আহ্বানও জানিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—
“… কিন্তু যেখানে আমাদের স্বদেশের লোক আমাদের যজ্ঞের পবিত্র হুতাশনে পাপ-পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া আমাদের হোমকে নষ্ট করিতেছে, তাঁহাদিগকে আমরা কেন সমস্ত মনের সহিত ভর্ৎসনা করিবার, তিরস্কৃত করিবার শক্তি অনুভব করিতেছি না। তাঁহারাই কি আমাদের সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু নহে। … আজ দস্যুবৃত্তি, তস্করতা, অন্যায় পীড়ন দেশহিতের নাম ধরিয়া চারিদিকে সঞ্চরণ করিতেছে, একি এক মুহূর্তের জন্য তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন যাঁহারা জানেন আত্মহিত, দেশহিত, লোকহিত, যে কোনো হিতসাধনই লক্ষ্য হউক-না কেন, কেবলমাত্র বীর ও ত্যাগী ও তপস্বী তাঁহারা যথার্থ সাধক। … ফল লক্ষ্য নহে, ধর্মই লক্ষ্য। ফললাভ চরমলাভ নহে, ধর্মলাভেই লাভ, একথা যদি কেবল দেশহিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশহিত মানুষের যথার্থ হিত নহে।” (দেশহিত, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৬৩৯-৪২)
সেযুগের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে এতটা কঠোর উক্তি কানে ও হৃদয়ে আঘাত হানলেও, তখন ঠিক কি কারণে রবীন্দ্রনাথকে এতটা কঠোর ভাষা প্রয়োগ করতে হয়েছিল, সমকালীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সেকথা বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। পরাধীন ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ঐতিহাসিক ভূমিকা থাকলেও, সশস্ত্র বিপ্লববাদী নীতির নিজস্ব কোনো সার্বিক মূল্য ও সত্যতা ছিল না; অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের মত একজন ধর্মনিষ্ঠ ভাববাদী কবির কাছে সেটার কোনো মূল্য ও সত্যতা থাকবার কথা ছিল না। প্রয়োজনের জন্য হিংসা ও মিথ্যা দেশের পুণ্যকর্ম ও সত্যপন্থা হতে পারে— এই তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথের মত একজন কবির পক্ষে স্বীকার করে নেওয়া অসম্ভব ছিল। তবে একইসাথে একথাও সত্যি যে, কবির অধ্যাত্মবোধের মধ্যে তাঁর বাস্তবতাবোধ কখনো বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।#