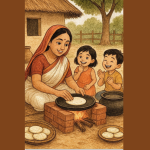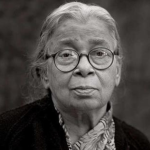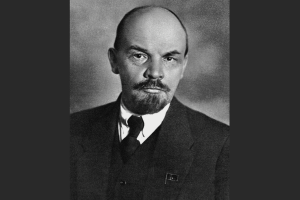শেখ ফয়জুল্লা বাংলা ভাষায় — গোরক্ষবিজয়, গাজীবিজয় ও সত্যপীরের পাঁচালী — রচনা করেছিলেন। এছাড়া অতীতে ঐতিহাসিকেরা ‘মীর ফয়জুল্লা’ ভণিতায় রচিত কতগুলি বৈষ্ণবপদ পেয়েছিলেন, সেগুলিও শেখ ফয়জুল্লার রচনা বলেই মনে হয়। গোরক্ষবিজয় কাব্যটি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একটি বিশিষ্ট রচনা। কিন্তু সেই কাব্যটির রচয়িতা কে এবং সেটির রচনাকাল কি, — অতীতে সেসম্বন্ধে গবেষকরা এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কারণ — কাব্যটির বিভিন্ন পুঁথির ভণিতা একরকমের নয়। সেগুলির মধ্যে ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র, কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস, শ্যামদাস সেন এবং ভীমসেন রায়-সহ নানা লেখকের ভণিতা পাওয়া যায়। কিন্তু গবেষকদের মতে কাব্যটির শতকরা ৮০ ভাগ ভণিতাই শেখ ফয়জুল্লার লেখা। এছাড়া অতীতে ডঃ এনামুল হক ২৪ পরগণা অঞ্চলে কয়েকটি প্রাচীন পুঁথির পাতার মধ্যে নিম্নলিখিত অংশটুকু পেয়েছিলেন —
“গোর্খ বিজএ আদ্যে মুনি সিদ্ধা কত।
কহিলাম সভ কথা শুনিলাম যত॥
খোঁটাদুরের পীর ইসমাইল গাজী।
গাজীর বিজএ সেহ মোক হইল রাজি॥
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন।
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন॥
মুনি রস বেদ শশী শাকে কহি সন।
শেখ ফয়জুল্লা ভণে ভাবি দেখ মন॥”
এই সমস্ত কারণের জন্যই অধিকাংশ গবেষকরা শেখ ফয়জুল্লাকেই বাংলা ভাষায় গোরক্ষবিজয় কাব্যের রচয়িতা বলে মনে করে থাকেন।
উপরে উদ্ধৃত অংশে ফয়জুল্লার সত্যপীর কথার রচনাকাল ১৪৬৭ শকাব্দ বা ১৫৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দ বলা হয়েছিল। কিন্তু সত্যপীরের পাঁচালীর রচনাকাল হিসেবে এই সালটি মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ — খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী, এমনকি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও সত্যপীরের কোন পাঁচালী তো দূরের কথা, সমকালীন বাংলা সাহিত্যে সত্যপীরের কোন উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। সুতরাং, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফয়জুল্লা সত্যপীরের পাঁচালী লিখেছিলেন — একথা রীতিমত অবিশ্বাস্য।
দ্বিতীয়তঃ, গবেষকরা প্রথমে গোরক্ষবিজয় কাব্যের ভাষাকে প্রাচীন বলে ভেবেছিলেন; কিন্তু পরে আরো খুঁটিয়ে দেখে বিশদে বিচার করে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, উক্ত কাব্যের ভাষা কিছুতেই খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর হতে পারেনা। প্রসঙ্গতঃ নিচে তিনটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা হল
(১)
“তবে যদি পৃথিবীতে আইল হরগৌরী।
মীননাথ হাড়িফাএ করএ চাকরী॥”
(২)
“নারী লইয়া যত সবে গৃহবাস করে।
রাধাকানু বঞ্চিলেক পৃথিবী ভিতরে॥”
(৩)
“দিনে দিনে বেশ হইব
সমপতি বাড়িয়া যাইব
তবে যাইব কাথা আর ঝুলি॥”
উপরোক্ত অংশ তিনটির মধ্যে — ‘চাকরী’, ‘রাধাকানু বঞ্চিলেক’ এবং ‘বেশ হইব’ — এই তিনটি শব্দবন্ধে আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। গবেষকদের মতে এই অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত নয়, কারণ শেখ ফয়জুল্লার সমস্ত পুঁথিতেই এগুলি পাওয়া যায়। অতএব ফয়জুল্লার — গোরক্ষবিজয় বা সত্যপীরের পাঁচালী — কোনটিই খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হয়নি। সত্যপীরের পাঁচালীর রচনাকাল — “মুনি রস বেদ শশী” — পাঠকে ডঃ সুকুমার সেন ভ্রান্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে সেটার শুদ্ধ পাঠ হল — “মুনি বেদ রস শশী”; অর্থাৎ — সত্যপীরের পাঁচালীর আসল রচনাকাল হল ১৬৪৭ শকাব্দ বা ১৭২৫-২৬ খৃষ্টাব্দ। পরবর্তী সময়ের অন্যান্য গবেষকরাও ডঃ সেনের মতকে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সত্যপীরের পাঁচালীর আগে গাজীবিজয়, এবং তারও আগে গোরক্ষবিজয় রচিত হয়েছিল। অতএব ১৭০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে ফয়জুল্লার গোরক্ষবিজয় কাব্যটি রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।
আরও পড়ুন: দোলযাত্রা- সমন্বয়ের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য
গবেষকরা এখনও পর্যন্ত গোরক্ষবিজয় কাব্যের যে সমস্ত পুঁথিগুলি পেয়েছেন, সেগুলির কোনটিই ঊনবিংশ শতাব্দীর আগেকার নয়। ডঃ আবদুল করিম সংগৃহীত গোরক্ষবিজয়ের একটি পুঁথির লিপিকাল ছিল ১১৮৪ সাল। ডঃ করিম ‘সাল’ অর্থে বঙ্গাব্দ বলেই ধারণা করেছিলেন, যা ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দের সমান হয়। কিন্তু সেই পুঁথিটি যেহেতু চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল, সেহেতু অন্যান্য গবেষকদের মতে তাতে উল্লেখিত ১১৮৪ সাল মঘী সন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, ওই পুঁথিটি ১৮২২-২৩ খৃষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল। তবে এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত গোরক্ষবিজয়ের বিভিন্ন পুঁথিগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর হলেও সেগুলির ভণিতায় যে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়, সেটা ১০০ বছরের আগে হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। তাই সেদিক থেকেও ১৭০০ খৃষ্টাব্দের মত সময়কে গোরক্ষবিজয়ের রচনাকাল বলে নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়।
অতীতে কেউ কেউ ‘গোরক্ষবিজয়’ কাব্যকে ‘গোর্খবিজয়’ বলে লিখে কিঞ্চিৎ নতুন ধরণের মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁদের যুক্তি ছিল যে, উক্ত কাব্যের কোনও পুঁথিতেই ‘গোরক্ষ’ নামটি পাওয়া যায় না, সেখানে সর্বত্র ‘গোর্খ’ নামটি পাওয়া যায়। কিন্তু মূল শব্দটি যদি ‘গোরক্ষ’ হয়, তাহলে পুঁথিতে কি পাওয়া গেল বা পাওয়া গেল না — সেই প্রশ্ন নিতান্ত অবান্তর বলেই মনে হয়। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দের আগে লেখা বিদ্যাপতির ‘গোরক্ষবিজয়’ নাটকেও যখন ‘গোরক্ষ’ শব্দটি পাওয়া যায়, তখন বুঝতে হবে যে এটিই মূল শব্দ। এছাড়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যত্রও ‘গোরক্ষ’ শব্দটি পাওয়া যায়। যেমন — গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলের এক জায়গায় বলা হয়েছিল—
“গোরক্ষনাথ মহাযোগী মীননাথের শিষ্য।
নানা যত্ন করিলেক গুরুর উদ্দেশ্য॥”
আগেই বলা হয়েছে যে, গোরক্ষবিজয় কাব্যে ফয়জুল্লা ছাড়াও কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস, শ্যামদাস সেন এবং ভীমসেন রায়েরও নাম পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেছিলেন— “ভীমসেন রায় ও ভীমদাস একই ব্যক্তি মনে করা যাইতে পারে। ‘কবীন্দ্রদাস’ ভীমসেনের অথবা শ্যামদাসের নামান্তর হওয়া বিচিত্র নয়।”
পরবর্তী সময়ের গবেষকরাও তাঁর এই মতকে সমর্থন করেছিলেন। এছাড়া অনেকে একথাও জানিয়েছিলেন যে, ভীমদাস বা ভীমসেন রায় এবং শ্যামদাস সেন আসলে একই ব্যক্তি ছিলেন। ডঃ আবদুল করিম সম্পাদিত গোরক্ষবিজয় কাব্যের ভূমিকায় যে সমস্ত ভণিতা উদ্ধৃত করা হয়েছিল, সেগুলি থেকে জানা যায় যে — গোরক্ষবিজয়ের কোন কোন পুঁথিতে — ‘কহে হীন ভীমদাসে’ — ভণিতা ছিল এবং অন্য কয়েকটি পুঁথিতে — ‘কহে সেন শ্যামদাসে’ — ভণিতা ছিল। গবেষকদের মতে লিপিকর-প্রমাদে ‘হীন ভীমদাস’, ‘সেন শ্যামদাস’–এ পরিবর্তিত হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে ‘সাহিত্য প্রকাশিকা’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ‘বাংলার নাথ সাহিত্য’ শীর্ষক আলোচনায় অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন যে, লিপিকর-প্রমাদে ‘হীন ভীমদাস’ থেকে প্রথমে ‘সেন ভীমদাস’ এবং সেটার থেকে ‘সেন শ্যামদাস’ এবং ‘ভীমসেন রায়’ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং, — কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস, শ্যামদাস সেন ও ভীমসেন রায় মূলতঃ একই ব্যক্তি ছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে। ইনি সম্ভবতঃ গোরক্ষবিজয় কাব্যের একজন গায়ন ছিলেন। এঁর বিভিন্ন নামের ভণিতাযুক্ত পুঁথিগুলি খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই পাওয়া যায়। গবেষকদের মতে, প্রথমে ইনি ফয়জুল্লার সমসাময়িক গায়ন ও গোরক্ষবিজয় কাব্যগ্রন্থটি রচনা করবার ব্যাপারে তাঁর সহযোগী ছিলেন, এবং পরে তাঁর দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে নিজের নামে উক্ত গীতিকাটি প্রচার করেছিলেন।#