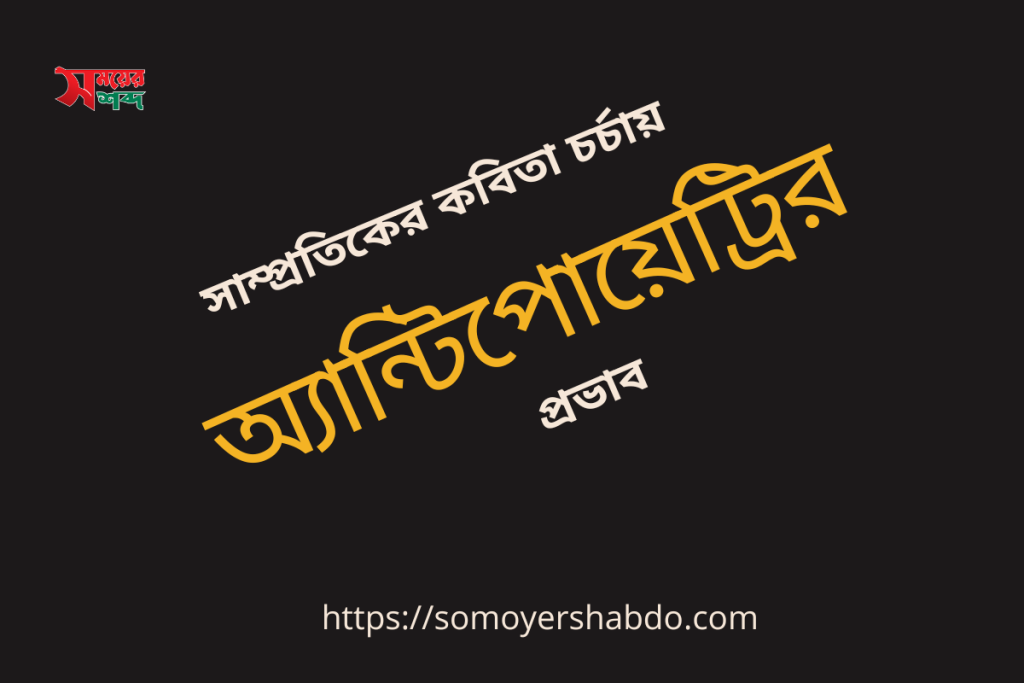কবিতায় যে এত বৈচিত্র্যময়তার সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি দিক হল Anti-poetry বা কবিতা বিরোধী আন্দোলন।
কবিতা লিখতে হলে ছন্দ জানতে হবে, কবিতার যে ফর্ম আছে তাকে মান্যতা দিতে হবে, অলংকার প্রয়োগ করতে হবে ইত্যাদি বহু বিষয় আমরা বলে থাকি। এক কথায় কবিতার প্রকরণ জানা জরুরি বলে মনে করি। কবিতার সমালোচনা করতে গিয়েও এইসব বিষয়কেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। এইসবের খামতি থাকলেই তাকে আমরা কবিতা বলেও মেনে নিতে পারি না। কিন্তু কবিতার বাঁক পরিবর্তনে যে বিরোধী কবিতা বা না-কবিতা বা Anti-poetry সৃষ্টি হয়েছে তার খোঁজ রাখি না। অথচ বিশ্বের তাবড় তাবড় কবিরা এই ধরনের কবিতা লিখেই কবিতাকে একটা নতুন দিশা দেখাতে চেয়েছেন। আর সেই কারণে স্বাভাবিকভাবেই সনাতন পাঠকের কাছে কবিতা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। Anti-poetry বা কবিতা-বিরোধী একটি সাহিত্য আন্দোলন যা কবিতার ঐতিহ্যবাহী ধারণা এবং এর প্রচলিত রীতিনীতিকে সর্বদা চ্যালেঞ্জ করে। এটি বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকা এবং স্পেনে আবির্ভূত হয়েছিল। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও বর্তমানে এর যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে।
অ্যান্টি-পোয়েট্রি বা কবিতা-বিরোধীর মূল বিষয়গুলি অনুধাবন করলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে পড়ে:
১. কবিতার চিরাচরিত বা ঐতিহ্যবাহী রূপের প্রত্যাখ্যান:
অ্যান্টি-পোয়েট্রির কবিরা ছন্দ-প্রকরণ এবং স্তবকের মতো ঐতিহ্যবাহী কাব্যিক কাঠামোকে সর্বদা প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। বাংলা কবিতায় যে প্রধান তিন প্রকার ছন্দ আছে এক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করেন না। সর্বদা কবিরা ছন্দের বিপরীতে হাঁটতে চান। ছন্দের খোলস ত্যাগ করে নতুনভাবে কবিতাকে উপস্থাপন করতে চান। স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে কবিতার পারম্পর্য ভূগোল পাল্টে যায়।
২. দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষার ব্যবহার:
অ্যান্টিপোয়েট্রির কবিরা ঘনিষ্ঠতা এবং সত্যতার অনুভূতি তৈরি করতে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত ভাষাকে তথা কথোপকথনকে কবিতায় তুলে আনেন। তাই এই ধরনের কবিতায় আটপৌরে শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। কোনো কোনো সময় আবার গাণিতিক ভাষারও প্রয়োগ ঘটে।
৩. জাগতিক বিষয়কেই বেশি প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন:
অ্যান্টিপোয়েট্রির কবিরা প্রায়শই মহৎ বা রোমান্টিক বিষয়ের পরিবর্তে জাগতিক, অতিসাধারণ বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকেন। তার ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা দুঃখ ও অন্তরায়গুলি বেশি করে প্রতিফলিত হয়।
কয়েকজন উল্লেখযোগ্য অ্যান্টিপোয়েট্রির কবিরা হলেন:
১. নিকানোর পাররা(১৯১৪-২০১৮): চিলির অ্যান্টিপোয়েট্রির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত, পারার রচনায় দৈনন্দিন ভাষার ব্যবহার এবং জাগতিক বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাঁর “কবিতা এবং প্রতিকবিতা” (১৯৫৪) নামে সংগ্রহটিই অ্যান্টিপোয়েট্রি শৈলীর একটি মূল উদাহরণ, যেখানে তিনি Black Humor and Absurdity বা কালো রসবোধ এবং বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সাধারণ, দৈনন্দিন সমস্যাগুলি অন্বেষণ করেছেন। এছাড়াও তাঁর “ভিজ্যুয়াল আর্টিফ্যাক্টস” নামে পরবর্তী কাজ হাতে আঁকা ছবির অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা কাব্য-বিরোধী রূপকে আরও প্রসারিত করেছিল। অবশ্য পারার কাজ ডাডাবাদ, পপ আর্ট এবং বিট আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত, যা চ্যালেঞ্জিং শৈল্পিক রীতিনীতির একটি বিস্তৃত প্রবণতায় অবদান রাখে। “হোজাস দে প্যারা” (১৯৮৫) নামে এই সংকলনটিও তাঁর কাব্যবিরোধী শৈলীর আরেকটি উদাহরণ, যেখানে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত উপহাসমূলক হাস্যরস এবং প্রচলিত রীতিনীতির বিপর্যয় প্রদর্শন করা হয়েছে।
পারাকে কেন্দ্র করেই “অ্যান্টিপোয়েট্রি” একটি আন্দোলন হিসেবে উঠে আসে। ঐতিহ্যবাহী কবিতার সাধারণ রীতিনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার একটা প্লাটফর্ম হিসেবেই গণ্য করা হয়।
পারাকে “কবিতা-বিরোধী” আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা ঐতিহ্যবাহী কবিতার স্বাভাবিক রীতিনীতি ভেঙে ফেলার পক্ষে একটা শক্তপোক্ত ভিত।
২. জুয়ান গেলম্যান(১৯৩০-২০১৪):
আর্জেন্টিনার গেলম্যানের কবিতায় প্রায়শই রাজনীতি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়বস্তু অন্বেষণ করার জন্য বিদ্রূপ এবং হাস্যরসের মতো বিরোধী কবিতার উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।বিশেষ করে তাঁর “Noises” সংগ্রহে পাওয়া যায় এমন কবিতাগুলি তাদের প্রতিষ্ঠা-বিরোধী, কর্তৃত্ব-বিরোধী এবং প্রতিষ্ঠান-বিরোধী থিম দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। প্রায়শই রাজনৈতিক সক্রিয়তা এবং সামাজিক সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে দুঃখকষ্ট, অবিচার এবং প্রকৃত মানব অবস্থার থিমগুলি অন্বেষণ করে।
গেলম্যানের “কবিতা-বিরোধী” কবিতাগুলির উপর আরও গভীর দৃষ্টিপাত করলে কতগুলি বিষয় জানা যায়। যেহেতু কবি একজন বামপন্থী সাংবাদিক ও সক্রিয় কর্মী, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে রাজনৈতিক সক্রিয়তার উপস্থিতি ঘটে। কবির ব্যক্তিজীবনে কারাবাসের অভিজ্ঞতা এবং নির্বাসিত জীবনের পরিচয়ও ফুটে ওঠে। সামাজিক সমালোচনার বিষয়টিকেও তিনি গুরুত্ব দেন। বিশেষ করে নিপীড়ন,শোষণ ইত্যাদি সামাজিক বাস্তবতা এবং বিপ্লবী আদর্শকে চ্যালেঞ্জ করেন। এছাড়া প্রান্তিক মানুষের জীবন যন্ত্রণা ও দুর্দশার ছবি এবং জীবনের হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাস শোনা যায় তাঁর কবিতায়। তবে কঠোর বাস্তবতার পাশাপাশি গেলম্যান তাঁর কবিতায় প্রেম, স্বপ্ন ও কোমলতার মানবীয় আবেগকেও মান্যতা দিয়েছেন।
গেলম্যান প্রায়শই তাঁর লেখায় ঐতিহ্যবাহী কাব্যিক রূপের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, অপ্রচলিত বিরামচিহ্ন, বাক্য গঠন এবং এমনকি নতুন শব্দেরও উদ্ভাবন করেন।
তাঁর কবিতাগুলিতে একটি সরাসরি এবং কঠোর ভাষা রয়েছে, যার লক্ষ্য তাঁর বার্তাকে স্পষ্টতায় এবং প্রভাবের সাথে পৌঁছে দেওয়া।
Epitaph, Heroes, Noises, Anti-Humanism অর্থাৎ এপিটাফ, নায়ক, গোলমাল,বিরোধী-মানবতাবাদী প্রভৃতি কবিতাগুলিতে যথাক্রমে নিপীড়ক, সামাজিক, বাস্তবতা এবং বিপ্লবী আদর্শের সমালোচনা, কবির ব্যক্তিজীবনের প্রেম এবং মৃত্যুর ধরন, সামাজিক ন্যায়বিচারের শক্তিশালী বার্তা এবং মানবিক অবস্থার অন্বেষণ অনুরণিত হয়েছে।
৩. এনরিক লিন(১৯২৯-১৯৮৮):
চিলির কবি লিন-এর রচনায় অন্যান্য শৈলীর সাথে বিরোধী কবিতার উপাদানগুলিকে মিশ্রিত করা হয়েছে, যা একটি অনন্য এবং উদ্ভাবনী কণ্ঠস্বর তৈরি করে। তিনি “The Dark Room and Other Poems”
লিখেছিলেন, যা ডেভিড উঙ্গার দ্বারা অনুবাদ ও সম্পাদনা করা হয়েছিল এবং ১৯৭৮ সালে নিউ ডাইরেক্টেশনস দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি তাঁর “অ্যান্টি-কবিতা” শৈলীর একটি মূল কাজ হিসাবে বিবেচিত হয়। এনরিক লিন তাঁর অনন্য শৈলী এবং ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্য জগতে অবদানের জন্য পরিচিত ছিলেন। “অন্ধকার ঘর এবং অন্যান্য কবিতা” ডেভিড উঙ্গার কর্তৃক অনুবাদিত এবং সম্পাদিত এই সংগ্রহে ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত লিহনের সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ তুলে ধরা হয়েছে। নিকানোর পারার মতো লিনের কাজও ঐতিহ্যবাহী কাব্যিক রূপকে প্রত্যাখ্যান করে এবং দৈনন্দিন ভাষা ও বিষয়বস্তুর উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্ক ম্যাকশেন ডেভিড উঙ্গার সম্পাদিত “অ্যান্টিপয়েমস: নিউ অ্যান্ড সিলেক্টেড”-এর একটি সমালোচনামূলক ভূমিকাও লিখেছিলেন। লিহনকে “নিঃসন্দেহে আজকের ল্যাটিন আমেরিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং সফল ব্যক্তিদের একজন” হিসেবে মূল্যায়নও করেছিলেন।
প্রভাব এবং উত্তরাধিকার:
অ্যান্টিপোয়েট্রি বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে:
১. মূর্ত কবিতা: অ্যান্টিপোয়েট্রি পরীক্ষা এবং খণ্ডিতকরণের উপর জোর দিয়ে মূর্ত কবিতার বিকাশকে প্রভাবিত করেছে। মূর্ত কবিতা হল ভাষাগত বিষয়বস্তুর একটি বিন্যাস, যেখানে মুদ্রণমূলক প্রভাব মৌখিক তাৎপর্যের চেয়ে অর্থ প্রকাশে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে কখনও কখনও দৃশ্যমান কবিতাও বলা হয়। এটি এমন একটি শব্দ যা এখন একটি স্বতন্ত্র অর্থ তৈরি করেছে। এই কবিতা মৌখিক শিল্পের দৃশ্যমান রূপের সাথেই বেশি সম্পর্কিত। যদিও এটি যে ধরনের পণ্যের সাথে সম্পর্কিত তার মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। তবে ঐতিহাসিকভাবে মূর্ত কবিতা আকৃতি বা প্যাটার্ন যুক্ত কবিতার দীর্ঘ ঐতিহ্য থেকে বিকশিত হয়, যেখানে শব্দ তাদের বিষয়বস্তকে চিত্রিত করার জন্য সাজানো হয়। নানা আকৃতি বা প্যাটার্ন শব্দের দ্বারা অঙ্কন করা হয়।
২. কথ্য শব্দ: অ্যান্টিপোয়েট্রিতে ব্যবহৃত হয় দৈনন্দিনের ভাষা। সাধারণ মানুষের মুখের কথা। যা অভিনয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করতে কথ্য শব্দ আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে।
৩. সমসাময়িক কবিতা: অ্যান্টিপোয়েট্রি ঐতিহ্যবাহী রূপ এবং রীতিনীতির প্রতি চ্যালেঞ্জের ফলে সমসাময়িক কবিতার উদ্ভাবন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর জোর দেওয়াকে প্রভাবিত করেছে। সাহিত্যের বাঁক বদলে তা খুব কার্যকরী প্রয়াস।
৪. বিদ্রূপ এবং হাস্যরস: অ্যান্টিপোয়েট্রির কবিরা প্রায়শই প্রত্যাশা নষ্ট করতে এবং পাঠকদের চ্যালেঞ্জ জানাতে বিদ্রূপ, হাস্যরস এবং ব্যঙ্গের ব্যবহার করে থাকেন।
৫. পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং খণ্ডন: অ্যান্টিপোয়েট্রির কবিরা প্রায়শই রূপ, কাঠামো এবং ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, যার ফলে লেখাগুলি খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।বিচ্যুতি বা প্রসঙ্গবিহীন মনে হতে পারে তখন।
বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিককালের কবিরাও অ্যান্টিপোয়েট্রি বা বিরোধী কবিতার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছেন। সাহিত্যের শিল্পপ্রকরণে তাঁদের কাছে এক ধরনের মুক্তি বইকি! কবিতার আঙ্গিক গঠনেও পরিবর্তন এসেছে। বিষয় বা ভাবের একমুখীনতাও আর কবিরা ধরে থাকেননি। বহুমুখী বহু বিষয়, এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গ, খণ্ডিতকরণ, বিচ্ছিন্নতা এবং প্রচলিত ও অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহারও শুরু হয়ে গিয়েছে বহু আগেই। অ্যান্টিপোয়েট্রির কতগুলি উদাহরণ দিলে আমরা বিষয়টি সহজেই অনুধাবন করতে পারব।
আত্মপ্রকৃতির কবিতা: জহর সেন মজুমদার
(১)
আমি।
আমি।
আমি।
ভাঙা বুকে বজ্রপাতে টিয়া পাখি কাঁদে।
(২)
আমি।
আমি।
আমি।
ডানা নাই। শূন্যে উঠে পুনরায় নীচে পড়লাম সূর্যহীন
চন্দ্রহীন অন্ধকার নীচে পড়লাম।
(৩)
আমি।
আমি।
আমি।
শূন্যের ভেতর সারারাত
নীরব স্বপ্ন আর নিঃশব্দ শিউলি তুললাম।
(৪)
আমি।
আমি।
আমি।
চারিপাশে জন্মদিনে চারিপাশে মৃত্যুদিনে
প্রচুর জং ধরা শিকল দেখলাম। কিন্ত
আজ পর্যন্ত একটাও জং ধরা গোলাপ;
জং ধরা শিউলি কোথাও দেখলাম না।
(৫)
আমি।
আমি।
আমি।
যতবার শিকলে জং ধরবে
ঘষে মেজে বারবার তুলে দেব আমি।
(৬)
আমি।
আমি।
আমি।
শূন্য শুধু শূন্য।
এইবার উড়ে চলে যাবো।”
শম্ভু রক্ষিত: প্রিয় ধ্বনির জন্য কান্না
“প্রত্যহ শীর্ষকোণ ধরে আমি অন্য কতকগুলি জটিল যৌগিক পদার্থ
সৃষ্টি করে করে,গবেষক দেশে,আগের বারের মতই,হো হো
শুধুই ক্ষয়প্রাপ্ত ও স্নেহন
ঐ নিচে পৃথিবী থেকে এগিয়ে উদগীর্ণ গ্রহের পিঠ,পার্থিব প্রাণীর মত জিভ
যেন চিরকাল পূর্ণ,এই সার-সত্যের আভাস দাও
বিশ্রাম ক্যানভাস,বহো বহো,যখন পরমাণুশক্তি ও আধুনিক
রকেটের সাহায্য নিয়ে কোনোরকম না কোনো দুর্ঘটনা
যখন শব্দের চেয়ে সাড়ে দশগুণ বেশি দ্রুতগামী যাত্রিবিমান নির্মাণ
ও সেই অগ্নিসাগরের উর্মিমালা,শুক্র পরীক্ষা করে না এই সাগরের;
উপলদ্ধি জাগে,লম্বা দৌড়ের জন্য হারায় তার দুটি পা
যাকে সহজাত আলোকসম্পন্ন একমাত্র ঘুর্ণমান-নুড়ি বলে অনেকে মনে করে
পায় না গুণগত উৎকর্ষ ও নিরাপত্তা বা স্বর্গের মত শান্তির আবেগ”
গোলাম রসুল: আমার কবিতা
“আমার কবিতার মধ্যে পৃথিবীর সব শোষিত মানুষেরা বসবাস করে
আমি তাদের সূর্য দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করি
মেঘের ভেতর থেকে একটি প্রার্থনা আসে
বৃষ্টি নামে
আমার চোখ ডুবে যায়
আমার কবিতা যখন হয়ে উঠে একটি শক্তিশালী কান্না
তখন সূর্য হয়ে ওঠে আমার মুখ”
গৌতম রায়: অনিয়ন্ত্রিত
“রিলসের অণু পরমাণু এপিসোড দেখতে দেখতে
কিশোরীটি দৃষ্টিপথের কিনারে এসেছে চলে,
প্যারাপিট প্রান্তের পর আর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ নেই
দৃষ্টিপাতে পতন, পতন শ্রবণ যন্ত্রের,
বাড়ে মেটাবলিক রেট
রাত্রি জাগরণে জাগরণে একটি ধোঁয়াশা ভোর
হাইপার টেনশন ইউনিট টেস্ট
ইঁদুর দৌড়ে এক একটি হলুদ অঙ্গে খসে যেতে হয়
এভাবে তারাখসা ভালো নয় জেনেও
পৃথিবী শরীরে কোথাও না কোথাও ক্ষত তৈরি হয়
আমাদের সনাতনী ঘর গেরাস্থলিও এক একটি গ্রহ উপগ্রহ
ঘরে ঘরে বাড়ে উল্কাগহ্বর।”
প্রদীপ চক্রবর্তীর কবিতা: চার.
“একটা আকাশ একটু শ্বাস,
সরল একটি দুর্বোধ্য শব্দ
ছিদ্র বাজুবন্ধ
চাঁদের কেন খুলছেন মৃদুছিট্?
রঙ? বিনোদন?
আত্মনাশা আঁকা নিভৃত বিষ
নৈঋতে আবির খোলা রোদ
দৈর্ঘ্য প্রস্থ কেন্দ্রবিন্দু ক্রমশ শব্দহীন,
ঘুঘু দিতে দিতে যে গাছ শীতল গ্রামে থাকে একা”
অরবিন্দ চক্রবর্তী: সভ্যতা অথবা রাত্রি
“রাত্রির রং বিবাহ। শাড়ি তার কাছে অর্থহীন। তবু মানুষের পাহারা আছে বলে গায়ে মাখে জবরজং। পরিসীমা পেরিয়ে যখন দরজা নাড়ে, হৃদয়ের প্রত্যন্ত জাপটে কোরাসে মালকোষ গায়, দেদার চুমু খায়। তখনই মহিমাখন্ডে নামে তামাটে সোহাগা। যে সাম্রাজ্যের দিকেই যান না কেন সন্ধ্যা তার ক্লাস-বান্ধবী। মিনতি নামে বুটিক বাতিক সত্ত্বেও মালবেরী বন অতি ঘুমপ্রিয়। সহসা শরীরে যার ক্ষুদেবার্তা বহমান। অতসব কা-স্বর শেষে আপনিই বলুন জতুগৃহ, পাজর থেকে কেন উচ্ছেদ হলো না সতীদাহ?”
অংশুমান দে: কবিতা নয়
“স্বপ্ন ফপ্ন আর ভাল্লাগেনা
মনে হয় একটা কালো রঙের পাঁয়তারা#
সেখানে আজকাল সিগারেট নিভে যায়
শব্দের মানে বুঝতে পারিনা
কথা সাজাতে পারিনা
মাথা ফেটে বেরিয়ে আসে থ্রিডি হায়না
সারাবিশ্বের ডট দিয়ে তিন-তিনটের সেট বানিয়ে
ভাবতেই থাকি
অতএব নাকি সুতরাং
ধুর!”
কবিতাকে যেভাবেই বিচার করা হোক না কেন, তা যে অ্যান্টিপোয়েট্রি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। গঠনে ভাবে শব্দে এবং লেখার কৌশলে সর্বদাই তা জানান দিচ্ছে একথা বলাই বাহুল্য। সাম্প্রতিককালে এই কবিতাই যে বেশি লেখা হচ্ছে, কবিরা যে গতানুগতিক পথ পরিহার করে নতুন পথের সন্ধান করছেন এবং এই ধরনের সাহিত্যচর্চার মধ্যেই নিজের সামর্থ্যের ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিচ্ছেন তা পাঠকমাত্রই জানেন।#