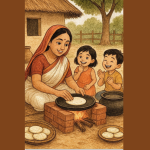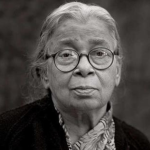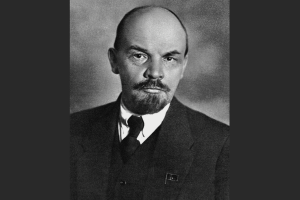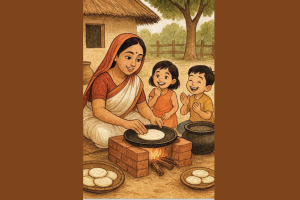সমগ্র ভারতে একই উৎসব প্রচলিত রয়েছে, এমন উদাহরণ মোটামুটিভাবে তিনটির বেশি পাওয়া যায় না। এই উৎসব তিনটি হল—দশেরা, দেওয়ালী এবং হোলি বা দোল। এগুলির মধ্যে সুদূর অতীত থেকেই বসন্তকালে উত্তর ভারতের সর্বত্র হোলি অথবা হোলাকা উৎসবের প্রচলন রয়েছে। অন্যদিকে বাংলায় বসন্তকালের শুক্লা চতুর্দশীতে চাঁচর নামের একটি অনুষ্ঠানের দ্বারা আজও এর সূচনা ঘটে থাকে। বাংলার কোথাও কোথাও এই চাঁচরকে মেড়া পোড়ানো বা বুড়ির ঘর পোড়ানো বলা হয়ে থাকে। এতে খড় ও বাঁশ দিয়ে একটি ছোট্ট ঘরের মত তৈরি করে সেটার মধ্যে স্থানবিশেষে পিটুলির তৈরি একটি মানুষ বা ভেড়ার মূর্তি রাখবার পরে যথারীতি বিষ্ণুপূজা করে সেই ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। তবে কিছুকাল আগেও উড়িষ্যায় কিন্তু মূর্তির পরিবর্তে একটি জীবন্ত ভেড়াকেই এভাবে দগ্ধ করবার রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু অতীতের কেওনঝর রাজ্যে এই প্রথাটি প্রচলিত থাকলেও শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের মন্দিরে তখন ভেড়াটিকে দগ্ধ না করে শুধুমাত্র গায়ে একবার আগুন স্পর্শ করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত। অন্যদিকে বৃটিশ আমলের যুক্তপ্রদেশের (বর্তমান উত্তরপ্রদেশের) মধ্যে মথুরাতে একজন মানুষকে হোলাকা উৎসবের সময়ে আগুনের শিখার ভিতর দিয়ে লাফিয়ে যেতে হত। আবার এই একই প্রদেশের গোরখপুর জেলায় তখন হোলি উপলক্ষ্যে একটি বানরকে সংহার করে সেটিকে গ্রামের সীমানায় রেখে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। এছাড়া যুক্তপ্রদেশের কোন কোন জায়গায় তখন হোলির সময়ে গায়ে ফুল ও গন্ধের প্রলেপ মেখে, পরে সেই বস্তুগুলিকে ঘষে তুলে আগুনে দেওয়ার বিধি চালু ছিল; একইসাথে এসব করা মানুষটি আকারে যত দীর্ঘ হতেন, তত দীর্ঘ একখণ্ড সুতোকে মেপে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হত। অতীতের বিহার প্রদেশে আবার আগুনের সঙ্গে মানুষ বা ভেড়ার মূর্তির কোনও সম্পর্ক ছিল না। সেখানে তখন চতুর্দশীর পরিবর্তে পূর্ণিমার রাত্রে ছেলেরা চুরি-চামারি করে নানা জায়গা থেকে কাঠ সংগ্রহ করে সেগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিতেন; আর সেই আগুনে ছোলাগাছ, তিসি, সুপারি, নারকেল, পিঠা প্রভৃতি নিবেদন করবার রীতি প্রচলিত ছিল। বর্তমানে যুক্তপ্রদেশ বা উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বেশিরভাগ জায়গা থেকে হোলির এসব রীতি উঠে গেলেও আজও কিন্তু এসব জায়গার বিভিন্ন দরিদ্র কিংবা নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে হোলি উপলক্ষ্যে নানাধরণের ভক্তিমূলক গান ও অশ্লীল গান গাওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। বৃটিশ আমলের বিভিন্ন গবেষকদের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, তখন উত্তর ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন জায়গায় হোলির দিন কাঠের তৈরি অশ্লীল মূর্তি অথবা বন্ধকাম নিয়ে সাধারণ মানুষ পথে পথে কোলাহল করে ঘুরে বেড়াতেন; এমনকি এই কিছুকাল আগেও মধ্যভারতের ইন্দোর-রাজ্যে এপ্রথা চালু ছিল। এসব জায়গায় তখন হোলির দিন নারীরা এধরণের মানুষের সামনে পড়লে নানাধরণের কামসূচক অঙ্গভঙ্গিসহকারে তাঁদের ব্যঙ্গ করা হত বলে, ভয়ে হোলির দিন এসব জায়গার নারীরা পারতপক্ষে পথে বের হতেন না। অন্যদিকে অতীত থেকে আজও মধ্যপ্রদেশের বণিক জাতির মধ্যে হোলির সময়ে খেলাচ্ছলে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সংগ্রাম করবার একটা রীতি প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু অতীতে গণ্ডজাতির মধ্যে এটা আরও উগ্র আকারে প্রচলিত ছিল। মথুরায় আবার অতীত থেকেই হোলির দিন জাঠদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব নৃত্যের ছলে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। অতীতের কোন একসময়ের বাংলায় দোল উৎসবের দিন আদিরসাত্মক গান গাওয়ার রীতি প্রচলিত থাকলেও, বর্তমানে কোথাও তেমন কিছু প্রচলিত নেই বলেই দেখতে পাওয়া যায়; শুধু পরিবারের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাসার সম্পর্ক রয়েছে, তাঁদের নিয়ে দোলের সময়ে এখানে একটু বেশি আমোদপ্রমোদ করা হয়ে থাকে।
কিছুকাল আগেও রাজশাহী, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও মেদিনীপুর থেকে শুরু করে দক্ষিণের গঞ্জাম জেলা, পশ্চিমের হাজারিবাগ, এমনকি সুদূর কুমায়ূন পর্যন্ত সর্বত্র হোলির পরে যে ছাই পড়ে থাকত, সেটাকে সাধারণ মানুষ বিশেষ দৈবগুণসম্পন্ন বলে বিবেচনা করতেন। তখন গঞ্জাম জেলার মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই ছাই মাঠে ছড়িয়ে দিলে দ্বিগুণ ফসল ফলবে। এমনকি আজও শস্যে পোকা লাগবে না—এই বিশ্বাসে কোন কোন জায়গার মানুষ এই ছাই গোলার মধ্যে রেখে দেন। অন্যদিকে হাজারিবাগ জেলার কিছু কিছু জায়গার মানুষেরা এখনও বিশ্বাস করেন যে, হোলির পোড়া কাঠ কোনো ফলগাছের উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিলে সে গাছে দ্বিগুণ ফল ধরবে। আবার মধ্যপ্রদেশের গণ্ডজাতির মানুষেরা এখনও হোলির আগুনে তপ্ত লাঙলের ফাল দিয়ে বছরের প্রথম ভূমিকর্ষণের কাজটি করে নেন।
ভারতে এই চাঁচর বা হোলি ঠিক কবে থেকে প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, ইতিহাস থেকে এবিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে জৈমিনি প্রণীত ‘পূর্বমীমাংসা’ নামক গ্রন্থের শবরস্বামীকৃত ভাষ্যে হোলাকার শব্দটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ‘পূর্বমীমাংসা’ গ্রন্থের এই ভাষ্যটি কমপক্ষে হলেও খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর আগেই রচিত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করে থাকেন। আর ‘পূর্বমীমাংসা’ গ্রন্থের শবরস্বামীর ভাষ্য থেকে শুধু এই তথ্যই পাওয়া যায় যে, হোলাকা উৎসবটি প্রাচীনকাল থেকেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এছাড়া ভারতে হোলির উৎপত্তি সম্বন্ধে যেসব অসংলগ্ন কাহিনী বিভিন্ন জায়গায় প্রচলিত রয়েছে, সেগুলির কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই বলেই গবেষকরা মনে করে থাকেন।
তবে এই হোলাকা উৎসবের সঙ্গে ভারতের তথাকথিত হীন জাতির সম্পর্কের একটি প্রমাণ বৃটিশ আমলের বোম্বাই প্রদেশে (বর্তমান মহারাষ্ট্রের মুম্বাই) গবেষকরা পেয়েছিলেন। তখন এই উৎসব উপলক্ষ্যে সেখানে কোঙ্কনি ব্রাহ্মণদের আনুষ্ঠানিকভাবে তথাকথিত হীন জাতীয় কোন ব্যক্তিকে স্পর্শ করতে হত, অথচ সেযুগে অন্য সময়ে তাঁরা একাজ করলে এতে তাঁদের স্পর্শদোষ জন্মাত। সমকালে বিহারে হোলাকায় অগ্নিসংযোগ করবার বিষয়টি সচরাচর ব্রাহ্মণ অথবা গ্রামের কোন বৃদ্ধ ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হলেও, ভাগলপুর জেলায় কিন্তু শুধুমাত্র ডোমজাতীয় মানুষদেরই এই অধিকার ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ডোমেরা তখন সেখানে বাংলার মতোই অস্পৃশ্য জাতি বলে গণ্য হতেন।
অতীতে ভারতবর্ষের অরণ্যচারী জাতিবৃন্দের মধ্যে হোলাকার মত কোনও অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল কিনা, এবিষয়ে বিভিন্ন গবেষক প্রদত্ত তথ্য অনুসন্ধান করলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানতে পারা যায়। অতীতের বিভিন্ন গবেষকদের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে, কোন একসময়ে উড়িষ্যার দক্ষিণভাগে থাকা কন্ধ জাতির মানুষের মধ্যে মেরিয়া নামক নরবলির প্রচলন ছিল। কিন্তু এরপরে বৃটিশ আমলের ভারতে নরবলি আইনতঃ নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পরে কন্ধরা বাধ্য হয়ে মানুষের পরিবর্তে মহিষ বলি দিতে শুরু করেছিলেন। এর আগে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য একজন মানুষকে খণ্ড খণ্ড করে তাঁর মাংস ক্ষেতের মাটিতে পুঁতে দেওয়ার রীতি এঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এছাড়া ভারতের কোনো কোনো গ্রামে তখন আবার এধরণের ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে দগ্ধ করে সেই ছাই মাঠে বা যে নদী থেকে জমিতে সেচের জল দেওয়া হত, সেই নদীর জলে মিশিয়ে দেওয়ার রীতিও প্রচলিত ছিল। অনেক জায়গায় আবার মানুষটিকে বলি দেওয়ার পরদিন তাঁর মাথা এবং দেহের অবশিষ্ট অংশ ও অস্থি যথাসম্ভব সংগ্রহ করে একটি জীবন্ত ভেড়ার সঙ্গে একত্রে দগ্ধ করা হত। এরপরে সেই ছাইকে মাঠে ছড়িয়ে দেওয়া হত অথবা জলে গুলে ঘরে বা শস্যের গোলায় শস্য রক্ষা হবে, এই আশায় লেপে দেওয়া হত।
এসব ছাড়াও অতীতের উড়িষ্যার কন্ধ জাতির মধ্যে তখন এই মেরিয়া-সংহার উপলক্ষ্যে অসম্ভব রকমের মদ্যপান এবং স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যথেচ্ছ সংগমের রীতিও চালু ছিল বলে জানা যায়। কন্ধদের মত ছিল যে, ধরিত্রী দেবী শস্যের মাধ্যমে মানুষকে যে প্রাণশক্তি বিতরণ করেন, তাঁরা নরবলি দিয়ে সেই প্রাণশক্তিকে পুনরায় ধরিত্রীকে প্রত্যর্পণ করে থাকেন। গবেষকদের মতে, ভূমির উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কন্ধরা তখন এধরণের যে অনুষ্ঠানটি করতেন, সে উপলক্ষ্যে তাঁদের সমাজের মধ্যে অবাধ কামচেষ্টা হওয়াও নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এখনও পর্যন্ত সব গবেষকই এবিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন যে, অতীতে কন্ধদের মধ্যে প্রচলিত থাকা এই অনুষ্ঠানটির সঙ্গে হোলির সাদৃশ্য কোনভাবেই আকস্মিক ছিল না। তাঁদের মতে, হয়ত অতীতের কোন একসময়ে সমগ্র উত্তর এবং মধ্য ভারতে ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নরবলির প্রচলন ছিল; যা পরে এসব অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য বা আর্য রীতিনীতির প্রসারের ফলে পরিবর্তিত অথবা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। এবং শুধুমাত্র কন্ধদের মত অরণ্যাশ্রয়ী কিছু জাতির মধ্যেই এটা অপেক্ষাকৃত অবিকৃত অবস্থায় থেকে গিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, আজও হোলি উৎসবে হিন্দুদের মধ্যেও কোথাও কোথাও আগুনের মধ্যে দিয়ে মানুষকে লাফিয়ে যেতে হয়, তো কোথাও আবার পিটুলির মানুষকে দহন করতে হয়। এমনকি কিছুকাল আগেও কিছু কিছু জায়গার হিন্দুদের মধ্যে এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে জীবন্ত ভেড়া পোড়ানোর রীতি প্রচলিত থাকলেও, বর্তমানে কোথাও কোথাও ভেড়ার মূর্তি দাহ করা হয়ে থাকে। এছাড়া এখনও বহু জায়গাতেই এই দাহের পরে ছাই সংগ্রহ করে শস্যের বা শস্যক্ষেত্রের উন্নতিবিধান করবার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। যায়। অর্থাৎ—নরবলির পরিবর্তে বর্তমান সময়ের আদিবাসী সমাজে যেমন এর একটি লঘু সংস্করণ প্রবর্তিত হয়েছে, ঠিক তেমনি হিন্দুধর্মালম্বীদের মধ্যেও আগের অবিমিশ্র কামচেষ্টার পরিবর্তে কামভাবান্বিত ভঙ্গি অথবা গান কিংবা শুধুমাত্র সামান্য ঠাট্টা-তামাসায় আগের রীতির রেশমাত্র অবশিষ্ট থেকে গিয়েছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতির সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির বিশ্লেষণ করলেও এধরণের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন—আজও কোথাও কোথাও প্রাচীন কোনো গ্রাম-দেবতার পূজা এখনও অজলচল জাতির অধিকারে থাকলেও উচ্চবর্ণের সব জাতি সেই দেবতার পূজায় অনার্যের পৌরোহিত্যকে স্বীকার করে থাকেন। একথার উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, কটক জেলায় বাঁকির কাছে অবস্থিত বৈদ্যেশ্বর এবং রামনাথ মহাদেবের মন্দিরের সেবকরা কিন্তু অতীত থেকেই অজলচল মালি জাতির মানুষ। এছাড়া পুরীতে জগন্নাথদেবের মূর্তিসংক্রান্ত যাবতীয় কাজের ব্যাপারে শুধুমাত্র শবর জাতির দৌহিত্র্যবংশজ দইতাপতিদের অধিকার রয়েছে। গবেষকদের মতে, হিন্দুধর্মাবলম্বী বহু জাতির মধ্যে বিবাহের সময়ে প্রচলিত থাকা স্ত্রী-আচারগুলিকে বিশ্লেষণ করলে একথাই মনে হয় যে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের আগে এদেশে বিবাহের যেসব অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, বর্তমান সময়ে সেগুলিই স্ত্রী-আচারের আকারে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছে। এখন এসব সামাজিক রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহার, দেশাচার এবং লোকাচার নামে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কাছে মর্যাদা লাভ করে থাকে। আসলে অতীতে যখন এদেশের নানা জাতিরা ব্রাহ্মণদের অধীনতা স্বীকার করে নিয়ে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের অংশ হয়ে উঠতে শুরু করেছিলেন, তখন কিন্তু তাঁদের কারো আচার-অনুষ্ঠানকে অকারণে নষ্ট করা হয়নি। শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ্যনীতির পরিপন্থী যেসব আচার বা অনুষ্ঠানগুলি ছিল, সেগুলিকে যথাসম্ভব পরিমার্জিত ও সংশোধিত করে নেওয়া হয়েছিল। ইসলাম, খৃষ্ট অথবা ইহুদিদের ধর্ম কিন্তু এবিষয়ে একেবারে স্বতন্ত্র। এসব ধর্মে কোনো মানুষ অন্য কোন ধর্ম থেকে এসে জায়গা পেলে তাঁকে নিজের পূর্বসংস্কার প্রায় সর্বথা বিসর্জন দিয়েই আসতে হয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের ঔদার্যের ফলে অতীতে হিন্দুসমাজের মধ্যে অঙ্গীভূত হতে চাওয়া বা অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়া বিভিন্ন জাতিকে এধরণের কোন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। আর একারণেই ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে জায়গা পাওয়ার পরেও তাঁদের অনেকের মধ্যেই প্রাক্তন নাচ, গান, সামাজিক আচার-বিচার বহুলাংশে অক্ষত অবস্থায় থেকে গিয়েছিল, যেসবের অবশেষে এখনও দেখতে পাওয়া যায়।
অতীতে ব্রাহ্মণ্য সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, যেহেতু সব মানুষের মন সমান স্তরের হয় না, সেহেতু সকলের পক্ষে মানসিক বিকাশের জন্য একই ভাবধারার আশ্রয় করবার প্রয়োজনও হয় না। একটা সমাজে যখন নানা স্তরের মানুষরা বাস করেন, তখন ধর্মের মধ্যেও সকলের সুবিধার জন্য নানা পথ ও নানা মতের জায়গাও অবশ্যই থাকা উচিত। এরফলেই অতীত থেকেই হিন্দুসমাজ যেমন নানা জাতির সংশ্লেষের দ্বারা রচিত হয়েছিল, হিন্দুধর্মও তেমনি নানা মত ও পথের সংশ্লেষের দ্বারা বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর অতীত থেকেই হিন্দু-সমাজের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের ভিতরে দ্বিজাতি এবং দ্বিজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণের জায়গা যেমন সর্বোপরি ছিল, হিন্দুধর্মের মধ্যেও তেমনি নানা জাতির সংস্কৃতি জায়গা পেলেও বৈদিক সংস্কার এবং বৈদিক চিন্তাধারার স্থানও সর্বোপরি নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর তাই সুদূর অতীত থেকেই হিন্দুধর্মের মধ্যে বহু দেবতার স্থান থাকলেও, নদীর গতি যেমন সর্বশেষে সমুদ্রের দিকেই ধাবিত হয়, এক্ষেত্রেও তেমনি সব দেবতার পূজা অবশেষে অবাঙমানসগোচর ব্রহ্মজ্ঞানে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝানোর জন্য এখানে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা যেতে পারে যা নিম্নরূপ—
(১) “যাঁহারা অন্য দেবতার ভক্ত হইয়া শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধিসমন্বিত হইয়া থাকে, হে কৌন্তেয় তাঁহারাও অ-বিধিপূর্বক আমারই উপাসনা করিয়া থাকে। এই স্থানে অ-বিধি শব্দের অর্থ অজ্ঞান, অর্থাৎ—তাঁহারা অজ্ঞানপূর্বক আমারই উপাসনা করিয়া থাকে।” (৯।২৩)
(২) “কেন এই কথা বলা হইল যে তাঁহারা অবুদ্ধিপূর্বক যজ্ঞ করিয়া থাকে? তাহার উত্তর এই যে, যে কারণে আমি বেদবিহিত ও ধর্মশাস্ত্র বিহিত সকল প্রকার যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। আমি দেবতারূপে যজ্ঞের ভোক্তা ‘অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র’ এই শ্লোকে ইহাই বলা হইয়াছে যে, আমিই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা প্রভু। কারণ, আমি যজ্ঞের স্বামী। (অন্য দেবতা ভক্তগণ) আমাকে যথার্থভাবে জানিতে পারে না, এইজন্যই তাঁহারা অবুদ্ধিপূর্বক উপাসনা করিয়াও উপাসনার সম্যক ফল হইতে প্রচ্যুত হইয়া থাকে।” (৯।২৪)
(৩) “যাঁহারা ভক্তিমান অথচ অবিধি পূর্বক অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাঁহাদেরও যাগফল অবশ্যম্ভাবি। কেন? (এরূপ হয়? তাহা বলা যাইতেছে যে)—‘দেবব্রত’ দেবতাগণের প্রীতির উদ্দেশ্যে ব্রতনিয়ম অর্থাৎ দেবতার প্রতি ভক্তি যাঁহারা করে, তাঁহাদিগকে ‘দেবব্রত’ কহা যায়; যাঁহারা দেবব্রত, তাঁহারা (নিজ নিজ ইষ্ট) দেবগণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা ‘পিতৃব্রত’ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণ, তাঁহারা অগ্নিবাত্তাদি নামে প্রসিদ্ধ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হয়। এইরূপ যাঁহারা ভূতগণ (অর্থাৎ) বিনায়ক, মাতৃগণ ও চতুঃষষ্ঠি যোগিনী প্রভৃতিকে উপাসনা করে, তাঁহারাও ভূতগণকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাঁহারা আমার উপাসনা করে, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদিগকেই ‘বৈষ্ণব’ বলে। (অন্য দেবতার পূজার জন্য যে প্রয়াস, আমার পূজাতে সেই প্রকারই প্রয়াস) প্রয়াস সমান হইলেও লোক অজ্ঞানবশতঃ আমাকে ভজনা করে না; সুতরাং তাঁহারা অল্প ফল লাভ করিয়া থাকে।” (৯।২৫)
(৬) “কেবল যে আমার ভক্তগণের নির্বাণ রূপ অনন্ত ফললাভ হয়, তাহাই নহে; আমার উপাসনাও কিন্তু বড় সুলভ (ইহাই বলা যাইতেছে)। পত্র পুষ্প ফল ‘তোয়’ জল (প্রভৃতি যাহা কিছু হউক না কেন) যে আমাকে ভক্তির সহিত অর্পণ করিবে, সেই ‘প্রযতাত্মা’ অর্থাৎ শুদ্ধবুদ্ধির প্রদত্ত (সেই সকল পত্র প্রভৃতি) ‘ভক্ত্যুপহৃত’ ভক্তির সহিত উপহৃত (বস্তুগুলি) আমি ‘ভক্ষণ’—গ্রহণ করিয়া থাকি।” (৯।২৬)
(৭) “যে কারণ এইরূপ, সেই জন্য তুমি যাহা কর (অর্থাৎ) স্বতঃ (গমনাদি) যাহা ভক্ষণ কর, যে শ্রৌত অথবা স্মার্ত হোম কর, যে স্বর্ণঅন্ন ঘৃতাদি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া থাক এবং যাহা কিছু তপস্যাচরণ কর, তাহা (সকলই) আমাতে সমর্পণ কর।” (৯।২৭)
(৮) “এই প্রকার কর্ম করিতে করিতে তোমার কি হইবে, তাহা শুন। শুভ ও অশুভ (অর্থাৎ) ইষ্ট ও অনিষ্ট ফল যাহাদের হয়, তাহাদের নাম ‘শুভাশুভ ফল’। শুভাশুভ ফল বলিলে কর্মই বুঝায়। সেই কর্মই বন্ধনস্বরূপ হইয়া থাকে এবং এই প্রকারে আমাতে কর্ম সমর্পণ করিয়া চলিলে সেই শুভাশুভ ফল কর্মবন্ধন হইতে মোক্ষলাভ করিবে। এই সেই সন্ন্যাসযোগ অর্থাৎ ইহা সন্ন্যাস হইয়াও যোগ; কারণ, আমাকে ফলাপর্ণ করিয়া কর্মানুষ্ঠানই ইহার স্বরূপ। সেই সন্ন্যাসযোগের সহিত যাহার ‘আত্মা’ অন্তঃকরণ যুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে ‘সন্ন্যাসযোগ-যুক্তাত্মা’ কহা যায়; তুমি এইরূপ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা ও কর্মবন্ধন হইতে জীবিতাবস্থাতেই বিমুক্তি লাভ করিয়া, পরে এই দেহ পতিত হইলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে (অর্থাৎ) মদভাবকে লাভ করিবে।” (৯।২৮)
(৯) “স্বধর্ম বিগুণ হইলেও সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম হইতে ‘শ্রেয়ান’ প্রশস্যতর। … যেমন বিষজাত কৃমির পক্ষে বিষ দোষজনক নহে, সেইরূপ স্বভাব-নিয়ত কর্ম করিলে মানব ‘কিল্বিষ’ পাপ প্রাপ্ত হয় না।” (১৮।৪৭)
(১০) “হে কুন্তীনন্দন! স্বভাবজ কর্ম সদোষ হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিবে না; কারণ, ধুমের দ্বারা যেমন অগ্নি আবৃত হয়, সেইরূপ সকল কর্মই দোষের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে।” (১৮।৪৮)
(চিত্র পরিচয়: Holi festival, Murshidabad or Calcutta, c. 1795–1805; ছবি সৌজন্যে: বৃটিশ লাইব্রেরি)