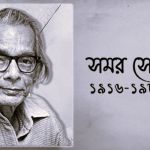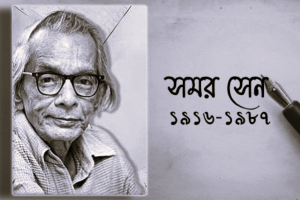নিজের নিজের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য নিয়ে বাংলার হিন্দু-মুসলমানরা একত্রে বৃটিশ আমলে প্রবেশ করেছিলেন; বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাসে সেটাই আধুনিক যুগ নামে পরিচিত। আরবদের মত ইংরেজদেরও বাণিজ্যতরী প্রথমে বাংলার মাটিতে নোঙর ফেলেছিল। ১৬৯০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা ক্রয় করে নিজেদের বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করেছিল। ১৬৯৬ সালে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে কলকাতার ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল। ১৭১৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর মোঘল সম্রাট ফরুখশিয়রের কাছ থেকে একটি ফরমান লাভ করে বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করবার সুবিধা পেয়েছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন ঘটবার পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল। ১৭৬৫ সালে বকসারের যুদ্ধে মীর কাশিমকে পরাভূত করে এবং দিল্লীর মুঘল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে শাহী ফরমানের বলে দেওয়ানী লাভ করে কোম্পানি বাংলার থেকে আদায়কৃত রাজস্বের মালিক হয়েছিল। ১৭৭২ সালে বঙ্গদেশের বুক থেকে দ্বৈতশাসনের অবসান ঘাটিয়ে দিয়ে এবং মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করে কোম্পানি বাংলার সর্বময় প্রভুত্ব লাভ করেছিল।
১৭৮৯ সালে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছিল। তখন সেখানে নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার ও কলকারখানার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছিল। একইসাথে সামন্ততন্ত্রকে বিদায় জানিয়ে ধনতন্ত্রের বিকাশ শুরু হয়েছিল। ব্যক্তির মালিকানা ও ভোগাধিকার হল পুঁজিবাদের সবথেকে বড় কথা। ব্যক্তিত্ববোধ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য চেতনা আসলে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থারই ফল। সামন্ততন্ত্রে ব্যক্তিরা অবহেলিত ও ব্যক্তি সমষ্টির অধীনস্ত ছিলেন। ব্যক্তিত্ববোধে উজ্জীবিত মানুষেরা তখন জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার মাধ্যমে মানসিক উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন এবং মনুষ্যত্বের নতুন মূল্যবোধ রচনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ‘এনসাক্লোপিডিয়া বৃটানিকা’ গ্রন্থে বলা হয়েছে – “It indicates the endeavour of men to reconstitute himself as a free being, not as the thrall of theological despotism.” (Encyclopedia Britannica, Vol. XXIII, P- 83)
ইউরোপের রেনেসাঁসের সেটি একটি প্রধান লক্ষণ ছিল। ইংরেজরা যখন বঙ্গদেশে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন, তখন তাঁরা ওই রেনেসাঁসের মন্ত্রেই দীক্ষিত ছিলেন। যন্ত্র চালাবার জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ এবং শিল্পোৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজার সৃষ্টি অত্যাবশ্যক, তাই ইংরেজদের জন্য ভারতের মত বিরাট উপমহাদেশে তখন নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করাটা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। সমকালীন ভারতের পরস্পর বিবদমান ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশক্তির দুর্বলতাব সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা ছলে বলে কৌশলে নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করতে সফল হয়েছিলেন। অপরিমিত শোষণ চালানোই ভারতের মাটিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লক্ষ্য ছিল। নিজের দেশের পণ্যগুলিকে ভারতে আমদানি করবার জন্য ইংরেজরা ভারতীয় কুটীরশিল্পগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তাঁরাই তখন ছিলেন সুবিশাল রাজ্যের মালিক, রাজস্বের মালিক ও বাণিজ্যের মালিক। ভারতবর্ষের সমস্ত পুঁজি তখন কোম্পানির জাহাজে করে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছেছিল এবং সেখানকার পুঁজিপতিদের উদর স্ফীত করেছিল। কোম্পানির শাসনে বাংলা তথা ভারতের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছিল, জনগণের দুর্দশা চরমে উঠেছিল। যদিও সেই সময়ে ভারতবাসীর বস্তুগত লাভের থেকে ক্ষতিই বেশি হয়েছিল, তবুও যা লাভ হয়েছিল, সেটা ছিল – তাঁদের মন ও মানসের জগৎ, এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগৎ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ। কোম্পানির বাণিজ্যতরীতে বিলেতি পণ্যের সাথে তৎকালীন ইউরোপের রেনেসাঁসের ফসলও ভারতে এসেছিল। পাশ্চাত্য বিদ্যা, শিক্ষা ও সভ্যতা তখন গতিশীল ও বিচিত্রমুখী ছিল। গতানুগতিক আবর্তসঙ্কুল আবহমান ভারতীয় সংস্কৃতির উপরে সেই সময়কার প্রাণচঞ্চল ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী ফল বহন করেছিল। তার অন্তর্জীবনে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়েছিল – যেটার মধ্যে দিয়ে সেই প্রথম ভারতীয় চিত্ত জেগে উঠেছিল, জীবনের পুরোনো মূল্যবোধ ধ্বসে পড়েছিল, এবং নবজাগরণের লক্ষণ বিকশিত হয়েছিল।
ইতিহাস বলে যে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম পঞ্চাশ বছর ক্রান্তিকাল ছিল। সেই সময়টায় কোম্পানি প্রশাসনিক কাঠামো গঠন, নীতি উদ্ভাবন, নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ছিল। এরপরে খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকের গোড়া থেকেই বঙ্গদেশে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রত্যক্ষ ফল ফলতে শুরু করেছিল। ১৮০০ সালে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে দেশীয় মানুষেরা শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি বটে, কিন্তু ইংরেজদের শিক্ষাদান ও গ্রন্থ প্রণয়ন করবার সুযোগ অবশ্যই পেয়েছিলেন। ইংরেজ শিক্ষক ও পণ্ডিতদের সঙ্গে বাঙালী শিক্ষক ও পণ্ডিতরাও তখন বাংলা গদ্যে পুস্তক রচনা করেছিলেন – যা বাঙালীর সাংস্কৃতিক জগতে নব অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। আধুনিক মন ও মনন, বিদ্যা ও বুদ্ধি, চিন্তা ও চেতনা বিকাশের অন্যতম বাহন হল গদ্য। এই গদ্যশিল্পের উদ্ভবকে বাঙালীর জীবনে ইংরেজদের একটা বড় দান বলে স্বীকার করতেই হয়। বাংলা ভাষার জন্মের প্রায় হাজার বছর পরে সেই প্রথম বাংলা গদ্য দলিল-দস্তাবেজের অঙ্গন ছেড়ে সাহিত্য রচনার অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এর অল্পকাল পরে সেই গদ্যশিল্প বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষায়, পাঠ্য পুস্তক ও সাহিত্য রচনায়, ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের বাক-বিতণ্ডায়, পত্র-পত্রিকায় স্বজনশীল ও মননশীল লেখায়, সভা-সমিতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল। সেই গদ্যের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তিকেন্দ্রিক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছিল।
শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজকার্যে এবং বাণিজ্যিক লেনদেনে ও নানাবিধ ব্যবহারিক নিত্যকর্মে ইংরেজি ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যাশিক্ষা তখন অত্যাবশ্যক ছিল। ১৮৩৭ সালে ফারসির জায়গায় ইংরেজি রাজভাষা হওয়ার পরে সেইধরণের শিক্ষার গুরুত্ব আরও বেড়ে গিয়েছিল। তখন কোন কোন ব্যক্তি ও খৃষ্টান মিশনারিদের উদ্যোগে প্রথমে কলকাতা শহর ও শহরতলিতে ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপরে ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হলে বর্ণহিন্দু ঘরের সন্তানেরা সেখানে উচ্চমানের ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করেই বঙ্গদেশে ‘ইয়ংবেঙ্গল’ দলের আবির্ভাব ঘটেছিল। ইংরেজি বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার মাধ্যমে বাংলা তথা ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল, এবং ধর্মের পরিবর্তে মানবিক ও বৈজ্ঞানিক শাখার নানাবিধ জ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৮১৩ সালে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ নতুন সনদ লাভ করবার সময়ে কোম্পানির অধীনস্থ বাংলা সরকার প্রতি বছর একলক্ষ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করবার অনুমতি পেয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৮১৩ সালের সনদের ৪৩নং ধারা মতে আইনটি এরকম ছিল – “It shall be lawful for the Governor General in Council to direct that out of many surplus which may remain of the rents. revenues and profits, a sum of not less than one lakh of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India, and for the introduction and promotion of knowledge of Science among the inhabitants or the British territories in India.” (Selection From Educational Records: 1771-1839, Part I, Edited by H. Sharp, Calcutta, 1920, P- 22)
১৮৩৬ সালে সরকারের উদ্যোগে হুগলী কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। ক্রমে বাংলার বিভিন্ন জেলায় স্কুল ও কলেজ স্থাপন করে শহরের বাইরে আধুনিক শিক্ষার সম্প্রসারণ করা হয়েছিল। এর ফলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এবং সেই ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান শিক্ষার ভেতর দিয়ে বাঙালীর আত্মার জাগরণ, ব্যক্তিচিন্তার উন্মেষ এবং স্বজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। সেযুগের ব্যক্তিত্ববোধের উদ্বোধন, মনুষ্যত্বের উপলদ্ধি, স্বদেশ ও স্বজাতির চিন্তা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা – ঐধরণের বিদ্যাচর্চারই ফল ছিল। ব্যক্তিগতভাবে এবং ক্রমশঃ যৌথভাবে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন তখনই সম্ভব হয়েছিল। মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে এর আগে যেসব কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও অন্যায় আচরণ সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল, এতকাল পরে সেসবের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, এবং সমাজশাস্ত্রের জায়গায় মানবতার জয় ঘোষিত হয়েছিল। গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন ও সতীদাহ প্রথা নিরোধ এবং বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের ভেতর দিয়ে লাঞ্ছিত মানবতার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৎকালীন বাংলা তথা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দান ছিল। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ফলে সেকালের মানুষেরা যুক্তিবিদ্যা ও মুক্তবুদ্ধির অধিকারী হতে পেরেছিলেন।
১৭৭৮ সালে শ্রীরামপুরে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর আগে খড় ও পালকের কলমে তালপাতা ও তুলট কাগজে হাতে লেখা পুঁথিই বিদ্যাচর্চার একমাত্র উপায় ছিল। ক্রমে ছাপাখানার চাহিদা মেটানোর জন্য কাগজের কলও স্থাপিত হয়েছিল। ১৮২৯ সালে কলকাতায় গমপেষার কল, ১৮৫৩ সালে কাপড় সেলাইয়ের কল, ১৮৫৪ সালে শ্রীরামপুরে পাটকল, এবং ১৮৭২ সালে কাপড় তৈরির কল স্থাপিত হয়েছিল। রাণীগঞ্জে কয়লা তোলা শুরু হয়েছিল ১৮২০ সাল থেকে। এসব ছিল বাংলার বুকে যন্ত্রযুগের ও যন্ত্রশিল্পের পদধ্বনি। ঊনিশ শতকের প্রথমভাগ থেকেই ভারতে যন্ত্র আসতে শুরু করেছিল। সেই পর্বে প্রথমে রেল-লাইন বসেছিল এবং তাতে কলের গাড়ি চলেছিল (১৮৫১)। তারপরে বিলেত থেকে ভারতে টেলিগ্রাফ পদ্ধতিও আমদানী করা হয়েছিল (১৮৫৩)। এগুলি ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নততর করবার উপায়। দূর ও নিকটকে একসূত্রে বেঁধে দিয়ে এইসব যন্ত্র সেযুগের মানুষের প্রভুত কল্যাণ সাধন করেছিল। এগুলির ফলে গ্রামের সাথে শহরের সম্পর্ক স্থাপন সহজতর হয়েছিল, দূর-দূরান্ত থেকে মানুষের শহরে আসা এবং শহরের সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ, যন্ত্র তখন মানুষের জীবনকে গতিশীল ও সূচীমুখী কবে তুলেছিল। এটিও ইউরোপীয় সভ্যতার দান ছিল।
ইংরেজ আমলেই কলকাতার মত আধুনিক কসমোপলিটান শহর এবং শহরকেন্দ্রিক আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ সম্পন্ন হয়েছিল। এর আগে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ফলে বাংলার সংস্কৃতি মূলতঃ গ্রামীণ সংস্কৃতি ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গদেশে শহর ও বন্দর থাকলেও সেগুলি মুখ্যতঃ দুর্গকেন্দ্রিক ছিল। তখন রাজা-বাদশাহ, আমীর-ওমরাহরা নিজেদের পারিষদসহ সেইসব দুর্গের অভ্যন্তরে বাস করতেন। দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে তাঁদের সেনাবাহিনী শিবির করে থাকত। রাজপুরুষ ও সেনাবাহিনীর খাদ্য-পানীয় সরবরাহ ও সেবাশুশ্রূষা করবার জন্য কিছু মানুষ সেইসব শহরে বাস করতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দোকানপাট থাকত, এবং সরাইখানা, মুসাফিরখানা, মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি থাকত। মোঘল যুগে ভূমির মালিকানার মত দরবারেও তখন ব্যক্তি-সম্পত্তির কোন মালিকানা ছিল না। সেই কারণে আমীর-উজিরদের মধ্যে কেউ লোকান্তরিত হলেই তখন ‘ফৌৎ আইনে’ তাঁর অর্জিত সম্পত্তির বেশীরভাগই রাজভাণ্ডারে চলে যেত, তাঁর পবিবার-পরিজন সেই সম্পত্তির সামান্য ভাগ পেতেন। (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর, আবদুল মওদুদ, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ- ৪২) তখন সমস্ত ভূমির মালিকানা স্বয়ং সম্রাটের ছিল; জায়গীরদার, মনসবদার, নবাব-নাজিমরা শুধুমাত্র রাজস্ব আদায় ও সেটার অংশবিশেষ ভাগ ও ভোগ করবার অধিকারী ছিলেন। সেযুগের ভূমিবণ্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে শাসকের ইচ্ছাধীন ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন এবং সেই সম্পত্তি বংশধরদের জন্য সঞ্চয় করবার প্রবৃত্তি না থাকবার ফলে মানুষ তখনও পর্যন্ত তেমনভাবে শহরমুখী হয়নি। এই কারণেই মোঘল যুগের মানুষের মধ্যে ভোগ করবার প্রবণতা খুবই বেশি ছিল। কিন্তু ইংরেজদের তৈরি শহরের রীতিনীতি সেটার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। ইংরেজ আমলে ব্যক্তি-সম্পত্তির উপরে ভোগাধিকার ও সঞ্চয়ের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা ছিল বলে ধনবাণ মানুষেরা শহরে উপস্থিত হয়েছিলেন, এবং সেখানে নিজেদের গৃহনির্মাণ করে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্যারিচাঁদ মিত্র মন্তব্য করেছিলেন – “When Fort William was built, the Hindu seem to have looked upon it as a place of refuge and the setts, Gobardhan Mitra, Nabakissen, and other families settled there.” (Notes on Early Commerce in Bengal, Calcutta Review, Vol. LXXII, 1881, P- 116)
উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, পলাশীর যুদ্ধের আগে নবাব সিরাজদ্দৌলা ঢাকার নায়েব-নাজিমের সহকারী রাজদুর্লভের কাছে অর্থ চেয়ে পাঠালে তিনি তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাসকে দিয়ে নিজের সব সম্পত্তি কলকাতায় ইংরাজের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বঙ্গদেশে ইংরেজদের ক্ষমতা লাভের পরে শাসন কাঠামোর পরিবর্তন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার, শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি, কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ফলে কলকাতা শহরের গুরুত্ব অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। এর ফলে রাজধানী শহরে সরকারী বেসরকারী কর্মচারী, কারখানার শ্রমিক ও ছোট বড় ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আগমন ঘটেছিল। সেই শহরবাসীদের সমন্বয়েই তখন একটি শ্রেণী-সচেতন মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছিল। উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী মধ্যযুগেও ছিল, কিন্তু সেটি সংখ্যায় ক্ষীণাঙ্গ এবং নানা জায়গায় বিক্ষিপ্তরূপে ছিল। তাঁরা প্রায় নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় ছিলেন; শ্রেণী-সচেতনতা না থাকবার ফলে তাঁরা সমাজকে নতুন করে কিছুই দিতে পারেননি। পোলার্ড বলেছিলেন যে, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ছাড়া মধ্যশ্রেণীর বিকাশ সম্ভব নয়, আর মধ্যশ্রেণী ছাড়া সমাজে নবজাগরণ আসে না। (বাংলার বিদ্বৎসমাজ, বিনয় ঘোষ, পৃ- ৫৮) ইংরেজ আমলে আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজ একজাগায় কেন্দ্রীভূত হয়ে গতিশীল, কর্মচঞ্চল ও অধিকার-সচেতন হয়ে উঠেছিল। সেই সমাজ মূলতঃ সংকরশ্রেণী হলেও সমস্বার্থে ঐক্যবদ্ধ জীবনব্যবস্থায় বসবাস করতে শুরু করেছিল এবং সমাজের সারবান জাগ্রত অংশ হিসাবে ক্রমশঃ সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিল। ব্যক্তিত্ববোধের উন্মেষ ঘটলে ও ব্যক্তি-অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা জাগলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী জনগণের স্বার্থের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করে এবং ঔপনিবেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। অবশ্য জীবিকার জন্য পরনির্ভরশীল ছিল বলে সেই সমাজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ছিল, কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সেই শ্রেণী সরাসরি দ্বন্দ্বে অবতীর্ন হতে পারেনি। বিভিন্ন আর্থিক কাবণেই তখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব বেড়ে গিয়েছিল এবং মানুষ সামাজিকভাবে স্বার্থপর হয়ে উঠেছিল। সেইসব দোষগুণের সমন্বয়ে গঠিত শহরকেন্দ্রিক শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ঊনিশ শতকের বাংলায় বৃটিশ শাসনের ফল বলেই স্বীকার করতে হয়।
এখন প্রশ্ন হল যে, ইংরেজদের আবির্ভাবের ফলে বাঙালীর অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, সেটা সমকালীন বাঙালী মুসলমান সমাজকে কিভাবে এবং কি পরিমাণে স্পর্শ করেছিল? একথা ঠিক যে, সেইসব পরিবর্তনের সূত্র ধরেই আংশিকভাবে হলেও বঙ্গদেশে নবজাগরণ এসেছিল। খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধেই সেই নবজাগরণের পদধ্বনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আধুনিক ভাষাশিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, পত্রপত্রিকার প্রকাশ, সভাসমিতির গঠন, বাংলা গদ্যের বিকাশ ও সেটার মাধ্যমে আধুনিক সাহিত্যের সৃষ্টি, কলকারখানা স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, নগর সৃষ্টি এবং নগরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, শিক্ষা-ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলন এবং সেসবের মধ্যে দিয়ে মুক্তবুদ্ধির ও মানবতাবোধের বিকাশ – অধুনিকতার এসব লক্ষণ দিয়েই বাংলার বুকে নবজাগরণের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। বৃটিশ শাসনের প্রথমদিক থেকেই সেইসব লক্ষণ হিন্দুসমাজকে যতটা আলোড়িত ও স্পন্দিত করেছিল, মুসলমান সমাজকে কিন্তু ততটা করতে পারেনি। আগে থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়ের লেনদেনে যাঁরা দোভাষী, দালাল, খাজাঞ্চী, ঠিকাদার, মহাজন, বেনিয়ান, গোমস্তা, মুৎসুদ্দী, সরকার, দেওয়ান, মুনশী ও কেরানীর কাজ করতেন – কোম্পানির শাসনকালে তাঁরাই আর্থিক সুবিধাভোগের অধিকারী হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে – নবকৃষ্ণ (লর্ড হেস্টিংসের মুন্সী), কান্তবাবু (মিঃ সাইকসের বেনিয়ান), লক্ষ্মীকান্ত (লর্ড ক্লাইভের বেনিয়ান), দর্পনারায়ণ (মিঃ হুইলারের দেওয়ান), শান্তিরাম সিংহ (টমাস রামবোল্ডের দেওয়ান), রামদুলাল দে (ফেয়ারলি কোম্পানির দেওয়ান), গোকুলচন্দ্র ঘোষাল (ভেরেলস্টের দেওয়ান) – প্রমুখের নাম স্মরণ করা যেতে পারে, যাঁরা তখন প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছিলেন। একই প্রসঙ্গে শেখ ইতিসামুদ্দীন তাঁর ইউরোপ-ভ্ৰমণবৃত্তান্ত – ‘শিগুর্ফনামা-ই-বেলায়েত’ – (১৭৮০) গ্রন্থে নিজের নামসহ সেকালের মোট আটজন মুসলিম মুনশীর নাম উল্লেখ করেছিলেন, যাঁরা তখন কলকাতায় কোম্পানির অধীনে চাকরি করতেন। তাঁরা ছিলেন – (১) মুনশী আমানুল্লাহ, (২) মুনশী ফকরুদ্দীন (তাজউদ্দীনের পুত্র), (৩) মুনশী মোহাম্মদ আসলাব, (৪) মুনশী আবদুল বারী, (৫) মুনশী মোহাম্মদ ফয়েজ (মেজর কর্নলের অধীনস্থ), (৬) মুনশী মীর সদরুদ্দীন (কর্নেল কুটের অধীনস্থ), (৭) মুনশী সলিমুল্লাহ (গভর্নর হেনরী ভ্যান্সিটার্টের অধীনস্থ), এবং (৮) মুনশী শেখ ইতিসামুদ্দীন। (The Vilayetnama, Syed Aulad Hussain, The Dacca Reviews, Feb-Mar., 1917, P- 328) কিন্তু এঁরা কেউ নবকৃষ্ণ-কান্তবাবুর মত প্রভূত বিত্তের মালিক হতে পারেননি। তবে একইসময়ের ইতিহাস থেকে গোলাম হোসেন নামের একজন মুসলমানের নামও পাওয়া যায় যিনি তখন কোম্পানির দালালি করে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন। (সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, ডঃ আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ- ১৩৬)
হিন্দুরাই তখন মূলতঃ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অফিসে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, মিল-কারখানায় চাকরির সুবিধা পেয়েছিলেন। ঐসব কাজের মাধ্যমেই হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে ইংরেজদের প্রথমে যোগাযোগ হয়েছিল। এর আগে মুসলমান শাসনামলে ব্যবসা ও মহাজনী কারবারে হিন্দুরাই বেশি পরিমাণে নিযুক্ত ছিলেন। কলকাতার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে তখন হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা পায়ে হেঁটে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আলোচ্য সময়ে সেইসব জেলাগুলি হিন্দুপ্রধান অঞ্চল ছিল, ফলে তখন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরাই বেশি পরিমাণে কলকাতায় সমবেত হয়েছিলেন। সমকালে বাংলার দূরবর্তী জেলাগুলিতে, বিশেষ করে, পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী ছিল। সেকালে শহরে যাতায়াত ও অবস্থান করবার মত আর্থিক অবস্থা যাঁদের ছিল, তাঁরাই সাধারণতঃ তখন শহরমুখী হয়েছিলেন। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই তখন কৃষিজীবী ছিলেন; তাঁদের মধ্যে চাকরিজীবীদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। এর আগে মুসলমান আমলে চাকরির সুযোগ তেমনভাবে সম্প্রসারিত ছিল না। ফলে ভূমির উপরে স্থায়ী আর্থিক নির্ভরতা ত্যাগ করে মুসলমানরা শহরের অনিশ্চিত আর্থিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারেননি। সেযুগে যাঁরা চাকরি ও অন্যান্য রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, শাসন ক্ষমতা হারানোর পরে তাঁরা কৃষিকার্যে যোগ দিলেও খৃষ্টান শাসকদের অধীনে গোলামি করা পছন্দ করেননি। এই প্রসঙ্গে খোন্দকার ফজলে রাব্বি জানিয়েছিলেন যে, মুসলিম আমলে বাংলার মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর জীবিকার্জনের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক সম্মানজনক উৎস ছিল – তরবারি, কলম পেশা ও ভূসম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয়। সেগুলি ছাড়া তাঁরা অন্যান্য সমস্তধরণের পেশা, হস্তশিল্প, দোকানদারি, ব্যবসা ইত্যাদি কাজকে তাঁদের উচ্চপদ ও মর্যাদার পক্ষে হানিকর বলে মনে করতেন। (The Origin of the Musalmans of Bengal, P- 107) এখানে মনে রাখতে হবে যে, মধ্যযুগের বাংলার মুসলিম সমাজে যাঁরা অভিজাত বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা বহিরাগত মুসলমান ছিলেন। তাঁরা নিজেদের হাতে কৃষিকাজ করাকে উত্তম পেশা বলে মনে না করলেও, শাসনকার্য থেকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে ভূমি ও চাষ করা ছাড়া তাঁদের কাছে অন্য কোন গত্যন্তর ছিল না। তখন রাজকার্যের চাকরি হারিয়ে সেই শ্রেণীর মুসলমানেরা কৃষিকার্য করবার জন্য গ্রামের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন, তাঁরা শহরের নানাবিধ পেশার দিকে কিন্তু যাননি। তবে সেযুগে যাঁরা নিজেদের চাকরি হারাননি, তাঁরা অবশ্য আগেকার পেশাতেই নিযুক্ত ছিলেন, যেমন – বিচার বিভাগে কাজী, মুফতী, মৌলবী, উকিল, মোক্তার, মুহুরী প্রমুখরা। কিন্তু যাঁদের কাছে তখন চাকরি ও ভূমি কিছুই ছিল না, অর্থাৎ দেশজ মুসলমানরা, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সৌভাগ্যের সন্ধানে শহরে ভিড় করেছিলেন। ডঃ এম. কে. এ. সিদ্দিকী ঊনিশ শতকের কলকাতায় মুসলমান বসতির একটি বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছিলেন যে, তখনকার কতগুলি কাজ মুসলমানদের একচেটিয়া ছিল; যেমন – নগর নির্মাণ হওয়ার সময়ে রাজমিস্ত্রির কাজ, বন্দরে খালাসী-সারেঙ্গের কাজ, কাপড় সেলাইয়ের পেশায় দর্জির কাজ, কসাইয়ের কাজ, ফলমূল ও শাকসব্জির ব্যবসায় দোকানদারি ও ফেরিওয়ালার কাজ, গাড়ির সহিস-কোচোওয়ানের কাজ, ভিস্তির কাজ, রান্নার পেশায় খানসামা-বাবুর্চির কাজ, বই-পুস্তক বাঁধাই করবার কাজ, চামড়ার ট্যানারির কাজ, ঘোড়া-গরু-ছাগল কেনাবেচার ব্যাপারীর কাজ ইত্যাদি। এইধরণের কাজগুলিতেই তখনকার বেশীরভাগ বাঙালী মুসলমানরা নিয়োজিত ছিলেন, তবে কোন কোন কাজে বিহার ও অন্য অঞ্চলের মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। (Muslims of Calcutta, M. K. A. Siddiqui, Calcutta, 1974, P: 19-20) তাঁরা প্রধানতঃ শ্রমজীবী শ্রেণী ছিলেন। এছাড়া ডঃ সিদ্দিকী তাঁর গ্রন্থে সেযুগের কলকাতার নানাধরণের দরগাহ, খানকাহ, মাজার, ইমামবাড়া, মসজিদ ও মাদ্রাসার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে দেখিয়েছিলেন যে, ইসলাম ধর্মপ্রচারক পীর-দরবেশ, শিক্ষাদাতা মৌলবী-মোল্লা শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরাও তখন সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের উপরের তলায় ছিলেন নবাব-নাজিম ও অন্যান্য অভিজাত পরিবারের ব্যক্তিরা। অর্থাৎ – কর্মী, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, চাকরিজীবী ও বৃত্তিভাগী অভিজাত পরিবার – এসব শ্রেণীর মানুষদের নিয়েই খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকের কলকাতার মুসলমান সমাজ গড়ে উঠেছিল। (Muslims of Calcutta, M. K. A. Siddiqui, Calcutta, 1974, P- 28)
১৭৮০ সালে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল। তৎকালীন কলকাতার মুসলমানরা লর্ড হেস্টিংসের কাছে সেই মাদ্রাসার জন্য দরবার করেছিলেন। ওই মাদ্রাসা স্থাপন করবার উদ্দেশ্য ছিল –
“… to promote the study of the Arabic and Persian Languages and of Muhammadan Law, with a view more especially to the production of qualified officers for the Courts of Justice.” (Mohammedan Education in Bengal, Abdul Karim, B.A., Metcalfe Press, Calcutta, 1900, P- 1)
১৮২৯ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় প্রথমবারের জন্য ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই ব্যবস্থায় প্রথম বছর ওই মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪২ জন। (British Policy and the Muslims in Bengal, A. R. Mallick, P- 187) ১৮৩৬ সালে হুগলী কলেজ স্থাপিত হয়েছিল; সেখানে ইংরেজি বিভাগে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা ছিল ৩১ জন (হিন্দু ছাত্র ছিলেন ৯৪৮ জন)। (Mohammedan Education in Bengal, Abdul Karim, B.A., Metcalfe Press, Calcutta, 1900, P- 14) ১৮১৭ সালে কলকাতায় স্থাপিত হিন্দু কলেজে মুসলমান ছাত্রদের পড়ার অধিকার ছিল না। তৎকালীন কলকাতা ও শহরতলীতে থাকা খৃষ্টান মিশনারী বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মান্তরের ভয়ে মুসলমান অভিভাবকেরা তাঁদের ঘরের সন্তানদের পাঠাতে চাইতেন না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিক্ষিপ্তভাবে পড়াশুনা করতেন। সুতরাং, ঊনিশ শতকের বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা তেমনভাবে বিস্তারলাভ করতে পারেনি, যেটা হিন্দুদের মধ্যে অনেকাংশে সম্ভব হয়েছিল।
সেযুগের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হিন্দু পণ্ডিতদের সাথে মুসলমান মুনশী-মৌলবীরাও ছিলেন। একটা সময়ে সেখানে তাঁদের সংখ্যা ৩০ জনেরও বেশি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সকলেই উর্দু-ফারসি ভাষার চর্চা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউই বাংলা ভাষায় গদ্য বা পদ্য কিছুই লেখেননি। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ মুসলিমই পাটনাবাসী, লক্ষ্ণৌবাসী ও দিল্লীবাসী ছিলেন। ডক্টর এম. কে. এ. সিদ্দিকী তাঁর গ্রন্থে সেযুগের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে জড়িত ৩০ জন লেখকের কথা বলেছিলেন, এবং তাঁদের মধ্যে ২২ জনের নামোল্লেখ করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন – সৈয়দ বকসিস আলী ফৈজাবাদী, মোহাম্মদ আলী ইবন নিসার আলী, সৈয়দ মনসুর আলী হোসাইন, ফজর আলী ফজলি, মোহাম্মদ বকস, মীর মোহাম্মদ আতা খান তহসীন, মীর আমন, মীর বাহাদুর আলী হোসাইন, মীর শের আলী আফসোস, হায়দার বকস হায়দারী, মজহার আলী খান ওয়েলা, মীর্জা কাজিম আলী জওয়ান, হাফিজুদ্দীন বর্ধমানী, খলিল আলী আশক, মীর মইনুদ্দীন ফয়েজ, বাসিত খান, আমানাতুল্লা সৈয়দ, মীর্জা লুৎফ, মীর্জা জান তাপিস, মৌলভী ইকরাম আলী, মীর্জা মোঘল নিশান, এবং খান নেয়ামত। Muslims of Calcutta, M. K. A. Siddiqui, Calcutta, 1974, P- 23) অন্যদিকে টমাস রোবাক তাঁর গ্রন্থে ১৮১৮ সালের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আরবি-ফারসি ও উর্দু বিভাগে কর্মরত ৩৩ জন মৌলবী-মুনশীর নাম্মোল্লেখ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আরবি-ফারসি বিভাগের সাথে জড়িতরা ছিলেন – করম হোসেন, আবদুর রহিম, জান আলী, শেখ আহম্মদ, বাহাদুর আলী, হোসেন আলী, তেগ আলী, হিসাম-উদ্দীন, মির্জা নূর আলী, মওলা বকস, আব্বাস আলী, কোরবান আলী, নাদির আলী, মির্জা হাসান আলী, সৈয়দ কাজিম আলী, ফরহাত আলী, মহম্মদ আলী, কলব আলী, মীর বকসিস আলী, মহম্মদ ওযাজিদ, মর্তুজা খান, ইউসুফ আলী, আবদুস সামাদ, নজরুল্লাহ, ওয়াজিব-উদ্দীন, মহম্মদ ওয়াসি, বাবউল্লাহ, দলিল উদ্দীন, মাহফুজ আলী, মীর তসাদ্দক হোসেন, বাহাদুর আলী, মীর মনসুর আলী এবং মীর সৈয়দ আলী। (The Annals of the College of Fort William, Edited by Thomas Roebuck, Hindustan Press, Calcutta, 1819, P: 47-48, Appendix.)
১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার ‘স্কুল বুক সোসাইটি’র পরিচালক কমিটিতেও ৪ জন, এবং ১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি’র পরিচালক কমিটিতেও ৪ জন মুসলমান সদস্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যেও কেউ কখনো বাংলা ভাষার চর্চা করেননি, তাঁদের উপরে স্কুলগুলির জন্য উর্দু ও ফারসি ভাষার পুস্তক প্রণয়ন করবার ও পর্যবেক্ষণ করবার দায়িত্ব ছিল।
স্কুল বুক সোসাইটির মুসলিম সদস্যদের নাম ছিল – মৌলবী আমানুল্লা (কোম্পানির উকিল, সদর দেওয়ানী), মৌলবী করম হোসেন (ফারসি ও আরবী পণ্ডিত), মৌলবী আবদুল ওয়াহিদ (সোসাইটির সম্পাদক), এবং মৌলবী আবদুল হামিদ।
ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির মুসলিম সদস্যদের নাম ছিল – মীর্জা কাজিম আলী খান (সরকারী সেক্রেটারী অফিসের ফারসি মুনশী), বেলায়েত হোসেন (মুফতি, কলিকাতা হাইকোর্ট), দরবেশ আলী (বেনারসের রাজার উকিল), নুরুন্নবী (রামপুরের নবাবের উকিল)।
সমকালে মুসলমানদের সম্পাদনায় কয়েকটি উর্দু ও ফারসি ভাষার পত্রিকা প্রকাশিত হলেও বাংলা ভাষায় একটি পত্রিকাও কিন্তু প্রকাশিত হয়নি। ১৮৩১ সালে শেখ আলীমুল্লাহর সম্পাদনায় – ‘সমাচার সভারাজেন্দ্র’ – নামের দ্বিভাষী, এবং ১৮৪৬ সালে রজব আলীর সম্পাদনায় – ‘জগদুদ্দীপক ভাস্কর’ – নামের পঞ্চভাষী একটি পত্রিকায় বাংলার জায়গা হয়েছিল বটে, কিন্তু সেই বাংলা ভাষা উর্দু ও ইংরেজি ভাষার সংবাদগুলির বাংলা তর্জমামাত্র ছিল; এবং সেই তর্জমাও অত্যন্ত দুর্বল ছিল, সেটা বাংলা গদ্যের কোন আদর্শকে বহন করতে পারেনি। (বাংলা সাময়িকপত্র, ১ খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ: ৩৯ ও ৮৮) বাঙালীর আধুনিক মন ও মননের বাহন হিসাবে আলোচ্য যুগে যে বাংলা গদ্যের বিকাশ হয়েছিল, তৎকালীন বাংলার মুসলমানেরা সেটার অংশভাগী ছিলেন না। সভারাজেন্দ্র ও ভাস্করের গদ্যাদর্শ তখনকার কোন বাঙালী মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি, করলে – সেযুগের বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে থেকেও দু’-একজন গদ্য লেখককে অবশ্যই পাওয়া যেত।
ঊনিশ শতকের বঙ্গদেশে আধুনিক যুগের উন্মেষ পর্বে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের গতি ভিন্নমুখী ছিল। বৃটিশ সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করে এবং ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে চাকরি ও ব্যবসার সুযোগ করে নিয়ে হিন্দুরা যখন উন্নতির দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন, বৃটিশ সরকারের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিমুখ থেকে চাকরি ও ব্যবসা করবার সুযোগ হারিয়ে মুসলমানেরা তখন অবনতির দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। বাংলার হিন্দু-মুসলমান সমাজ, বিশেষ করে, বাঙালী মধ্যবিত্তের সেই অসম বিকাশ – ঊনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি বড় রকমের দুর্ঘটনা ছিল। সেই কারণেই বিনয় ঘোষ সেই সময়কার বাংলায় কোন মধ্যবিত্ত মুসলিম বুদ্ধিজীবীর অনুপস্থিতিকে সমকালীন সমগ্র বাঙালী সমাজের জন্য – ‘ট্র্যাজেডি’ – বলে উল্লেখ করেছিলেন। (বাংলার বিদ্বৎসমাজ, বিনয় ঘোষ, পৃ- ২২)#