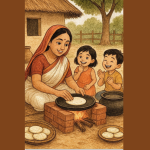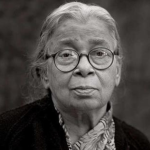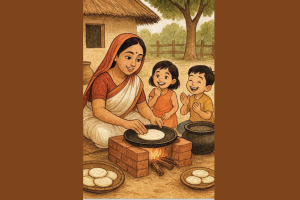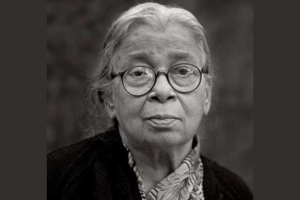নেতাজি, লেনিন, গান্ধিজীর স্ট্যাচুর সামনে দাঁড়িয়ে যতগুলি আন্দোলন হয়েছে, যতগুলি শ্লোগান আমরা খরচ করেছি, সবই যেন এক একটি গড্ডলিকা প্রবাহ। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের শপথ আমরা প্রায় ভুলে গেছি। বরাক উপত্যাকায় ১৯৬১-র ১৯শে মে-র ভাষা-শহিদদের রক্তাক্ত স্মৃতিও ফিকে হয়ে গেছে। আমদের ভবিষ্যৎ রাস্তার বাঁকে বাঁকে বহু ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলে উঠেছে কিন্তু ততদিনে আমরা আর মানুষ থাকিনি, পোকা হয়ে উড়েছি। আলো পিপাসু, না অগ্নি পিপাসু তা অবশ্য আজও বুঝতে পারি না।
এবার সাহিত্য পাঠের হালহকিকত একটু জানা যাক। ধরে নিচ্ছি আমরা ভাষার কদর বুঝি, ভাষা মানে এখানে স্রেফ আলোর ব্যঞ্জনাই। কিন্তু সেই ভাষা আমাদের হৃদয়ের উৎস থেকে উৎসারিত হচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখিনি। হিন্দি আর ইংরাজির চাপে বাণিজ্যিকরণের ভাষা হয়ে উঠেছে বাংলা, যা এক প্রকার মিশ্র ভাষা। উচ্চারণে, শব্দ গঠনে, বাক্য প্রয়োগে কোনো ব্যাকরণের নিয়মের তোয়াক্কা দেখা যায় না। ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার অভাব বলেই বাঙালি আজ কচ্ছপ-খরগোস হয়ে জলে- ডাঙায় বিচরণ করছে। তার কর্মস্থল, বাসস্থল, সমাজক্ষেত্র সবেই ব্যস্ততার দায়সারা তাড়না। মনোযোগ বা নিষ্ঠার যেমন অভাব, তেমনই ভাবনারও প্রশস্ত মাঠটিরও ক্রমশ সংকোচন তার সিরিয়াসনেসকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। রুচিবোধের বাগানটিও পাল্টে যাচ্ছে স্বাভাবিক কারণেই। ফলে সাহিত্যের নিত্য-নতুন ধারায় বিচরণের সাধ্যিও হারিয়ে যাচ্ছে। গুচ্ছের ডিগ্রিধারী সন্তান-সন্ততি রবীন্দ্রনাথকেই পড়তে পারে না। অবশ্য তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথকে না পড়লেও ক্ষতি নেই। এমনই ধারণা। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও একবার সেই রকমই বলেছিলেন। তাই অন্য কবিরা তো তাদের কাছে গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো। সাহিত্যের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারীরাও নির্দ্বিধায় জানাচ্ছে কে মাথা ঘামাবে সাম্প্রতিকের শামুক বোঝাই ভ্রান্ত লেখার পুঁটুলিতে? প্রলাপ বাক্যির মতো সবাই লিখে যাচ্ছে, যার কোনো মাথা মুণ্ডু নেই।
তথাপি ফুরসৎ পেলে কাজের বই পড়া দরকার। রান্নার বই পড়া দরকার। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে যতটুকু দরকার পড়ো, দরকার না থাকলে পড়বে কেন? আর বাংলা বইপত্তর পড়ে হবেই বা কী! না জুটবে চাকরি, না হবে অর্থ উপার্জন। সুতরাং ইংরাজি পড়ো, ইন্টারনেটে পড়ো প্রয়োজন মতো। বাংলা পড়ে সময় তথা মাথা নষ্ট কোরো না। এই উপদেশই কাম্য মনে করে আজকের হিসাবি মাথার পড়ুয়ারা। শিখে নেয় বিভিন্ন প্রযুক্তি বিদ্যার ভাষা সংকেতকে। মেট্রো জীবনের কাঁটা চামচে মাপতে থাকে জীবনের হালচিত্র। সাধারণ ভাবেই শরৎ-বঙ্কিম-তারাশংকররা ফেল। কাকাবাবুরা গোয়েন্দা- গিরির দাপটে কিছুটা প্রশ্রয় পান মাত্র। সেখানে নতুন ব্যান্ড-পার্টির কদর কতখানি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মেট্রো যুগের আলুলায়িত কংক্রিটের হৃদয়বত্তার কারবারিরা প্রায় বিলুপ্তির পথে। সাহিত্য সেখানে পর্নোগ্রাফির লালসায় ঝলসিত। প্রেম কামুক বিলাসের সংবাদে উত্তেজক জারক। সে সবই কিছুটা পাঠযোগ্যতা আদায় করে নেয়।
তবু নতুন খুশির বার্তা, এতদসত্ত্বেও সাহিত্য ভোজের আয়োজনের কমতি নেই। সবাই মেহেন্দি লাগাচ্ছে। ডোলি সাজাচ্ছে। বরবধূরা প্রতিষ্ঠানের মুখে উলু ফোটাচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় গলির মোড়ে রসগোল্লার দোকান। সিগারেট খাওয়া কমিয়েও সেখানে নিজেই মাঝে মাঝে উকি মারছি। দু-একটা রসগোল্লা কিনছি, স্বাদ নিচ্ছি বইকি!
আরে রসগোল্লা কাহারে কইছি বুঝুম না? ধ্যাত্তারি! আজকালকার লিটিল ম্যাগাজিনদেরে রসগোল্লা কইছি! প্রথম প্রথম প্রেমে পইড়্যা দু-চারটা ‘কবতা’ (কবিতা>কবতা) লিইখ্যা ময়রার ঠাঁই (সম্পাদকের কাছে) যাইয়া দিয়া আসি। ময়রা খুশি হইয়া কয়, ‘কবতা তো ছাপাইমু, কিন্তু সহযোগিতা করবেক তো?’ প্রথম বয়েস (কাঁচা ছেলে) ‘ডানাকাটা’ পরিটার জন্য লিইখ্যাছি, তা-না কইরবার কী আছে! ব্যাস অমনি কাজ হইল। সেই থিইক্যা আমুও কবি হইলাম। জীবনে পরিটারে পাই নাই। কিন্তু দাড়ি রাইখ্যা, মদ গিলিয়া মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি পইর্যা ময়রাখানায় হন্যে হইয়্যা ঘুইর্যাছি। এখন তো এহেন ভূরি ভূরি হইতাসে। বড়ো ময়রায় ছোটো ময়রায় পাড়া ভরত্যাসে। ইহারে পাঠক বাড়িল কইব না তো কাহারে কইব? যাই হোক যারা কবিতা লিখতে এল, সাহিত্যচর্চা করতে এল, তারাই তো ম্যাগাজিন বের করল, অনুষ্ঠান করল, রবীন্দ্রসংগীত শুনল, আবৃত্তিকারের ক্যাসেট বাজাল, খুচরো সাহিত্য বাজার প্রতিষ্ঠা করল। তারা আর কিছু না পারুক, সাহিত্যকে দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করল। এরা নোবেল চাইল না। আকাডেমিও চাইল না। ছক্কা মেরে কোটিপতি হবার স্বপ্নও দেখল না। সাহিত্য করে ক’কাপ চা বেশি পান করল মাত্র। ক’খানা বেশি ধূমপান করল মাত্র। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথাবার্তা বলল। তবে পাঠক স্রোতের অনুকূলে আগ্রহের ইচ্ছেগুলি ছেড়ে দিতে লাগল দিকে দিকে। তাই আজ পত্রিকার সংখ্যা বাড়ছে। নিজস্ব মতামত, চেতনা প্রকাশের এক-একটা মাধ্যম হয়ে উঠছে। পাঠক সবটা পড়তে চায় না। তবে যাঁরা লেখেন তাঁরা তো পড়েন। তাঁদের কিছু কিছু ভক্তও তৈরি হয়। সব লেখা কালোত্তীর্ণ নয়। চিরন্তন আবেদন সমৃদ্ধ বা ক্লাসিকও নয়।
তবু আত্মদ্রোহের আত্মসমালোচনার আত্মসচেতনার সাংগীতিক টুকরো টুকরো অশ্রুসিক্ত বেদনার স্বরলিপি সেগুলি কিছু কিছু নির্বাচিত পাঠক তৈরি হতে হতে একসময় কেউই আর ক্ষেত্রের বাইরে থাকতে পারে না। সবাই পাঠের সীমানায় চলে আসেন। এভাবেই একটা যুগের মৌরসিতে সবাই সামিল হয়ে যান। আর একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে লাইব্রেরির সংখ্যা বৃদ্ধিও ঘটে চলেছে। বইগুলি যে নাড়াচাড়া হচ্ছে, পৃষ্ঠাগুলিও পুরানো হচ্ছে আঙুলের ছাপে তা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছি। সাহিত্যের বাঁক বদলের রীতিতে নতুন ও নতুনতরকে জানতে পুরানোদের দ্বারস্থ হতে হয়। পাঠকরা বুঝতে পারছেন। সেই সূত্রেই শুধু ম্যাগাজিন পাঠ নয়, বই পাঠেরও একটা সেতু তৈরি হচ্ছে। সর্বদা মননশীলতায় ও রুচিতে আমরা প্রথম শ্রেণির পাঠকের যে কাঙ্ক্ষা করি তা নয়, পাঠক তো পাঠকই। সব ধরনের বই পড়ার পাঠকের কথাই বলা হচ্ছে। বাৎস্যায়ন থেকে যাজ্ঞবল্ক্য, মধুসূদন থেকে সুকান্ত, শঙ্খ থেকে শ্রীজাত সবাই-ই আছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হুমায়ূন আহমেদ এবং তসলিমার সাহিত্যও পাঠকেরা আগ্রহ নিয়ে এখনও পাঠ করে চলেছে। সাহিত্যের একটা জাগরণ অবশ্যই সাড়া ফেলেছে। ভালো মন্দ বা শ্রেষ্ঠত্বের বিচারের সময় এটা নয়। সেই কারণেই মূল স্রোতের বাইরে থেকেও কোনো কোনো লেখক নিভৃতে তাঁর সৃষ্টি নিয়ে বেঁচে থাকেন। তাঁরও কিছু গোপন পাঠক থাকে। একদিন তিনিও উন্মোচিত হন। সাহিত্য-আন্দোলনের এই প্রবাহকে যতই নঞর্থক মনে হোক, যতই মূল্যহীন ভাবা হোক, বর্তমান সভ্যতায় আত্মক্ষরণের বিমোচন ঘটাতে এই সেতু ক্ষেত্রটির অবদান কম নয়। নিজেকে ভালো রাখার, সমাজকে প্রশ্ন করার এবং নিজের মনন-চিন্তনের প্রকাশ ঘটানোর জন্য এসবের প্রয়োজন ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী, রুচি ও বোধ অনুযায়ী বিষয় ও বিষয়হীনতার নানা শিল্পরূপ নিত্যনতুন পরীক্ষায় উঠে আসে। পাঠক কোনটাকে গ্রহণ করবে দ্রুত, কোনটাকে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিন। তবু সবকিছুরই পাঠক আছে, পাঠক থাকে। এই পাঠকের সংখ্যা বাড়ে বই কমে না।
শেষটুকু না বললেই নয়। যে নেগেটিভ পর্যায় থেকে এই লেখাটির যাত্রা শুরু হয়েছিল, লেখাটির শেষ পর্যায়ে সেই নেগেটিভই পজেটিভ হয়ে উঠল। কারণ সিরিয়াস পাঠকের হিসাবে নয়, কবিতা লিখতে আসা তরুণ-তরুণীর হিসাবে নয়, কিংবা লিটিল ম্যাগাজিন প্রকাশ করার হিসাবেও নয়, পড়াশুনো করতে হয় সামাজিক সিলেবাস অনুযায়ী মান-সম্মান বজায় রাখতে, কারোর সম্পর্কে কিছু বলতে বা লিখতে। প্রতিটি লেখকের একটা ইমেজ বা প্রভাব থাকে বিভিন্ন এলাকায়। এক সময়ে বিবেকের নাড়া খেয়ে তাঁকে নিয়ে ভাবনার অবকাশ হলেও হতে পারে। বিভিন্ন চ্যানেল বা প্রতিষ্ঠান কৌতূহলী করে তোলে। দায়-দায়িত্বের পরাভব থেকে এক প্রকার কর্তব্যও পালনের তাগিদ দেখা দেয়। যার জন্য জন্মদিন বা মৃত্যুদিন পালন। শতবর্ষ বা সার্ধশতবর্ষ পালন এবং বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ ও তাঁর মূল্যায়ন করার রীতিটি চালু হয়েছে। তবু বিস্মৃতি যে নেই, তা নয়। বিস্মৃতির অতলে বহুজনই ডুবে গিয়েছেন। এখনও ডুবে যাচ্ছেন। বহুদিন এই সাহিত্যিক আবহাওয়ায় থাকতে থাকতে আমাদের মনে একপ্রকার ঘর্ষণ সৃষ্টি হয়। তাতেও স্ফুলিঙ্গ ওঠে। আনন্দবাজার পত্রিকার সার্ভে করা পরিসংখ্যানে ২০১২ সালে আমরা বাংলা ভাষার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির অঙ্কটির সহজেই প্রমাণ পেয়ে যাই।
পাঠকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় দেখা যায়: এক, টিভি চ্যানেল দেখার ফাঁকে ফাঁকে সংবাদপত্রের রবিবারের বা সাপ্তাহিকীর পাতাগুলি চোখের দৃষ্টিতে কিছুটা ডিগনিটি ভিক্ষে করে।
দুই, পাড়ার কালচারাল অনুষ্ঠানে গিয়ে কিছু বলার জন্য প্রস্তুতি নেবার তোড়জোড় শুরু করে পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে দেখার প্রয়োজন হয়। সেই সঙ্গে নতুনের তুলনাও।
তিন, সাহিত্যের ছাত্র-শিক্ষক হলে সিলেবাস বা ধারাবাহিক ইতিহাস নিরীক্ষণ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের নানা বাঁকগুলি চিহ্নিতকরণে ও জানতে পাঠের প্রয়োজন হয়।
চার, টিভি সিরিয়ালের একঘেঁয়েমি, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের কর্মবিমুখতাকে বাড়িয়ে দেয়। এই মোহ থেকে বেরিয়ে আসার ভাবনাও শুরু হয়েছে।
পাঁচ, জেলা ভিত্তিক বইমেলা, রাজ্যস্তরে বইমেলা, বই পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষ প্রতিনিয়ত অবহিত হয়ে চলেছে।
ছয়, শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং প্রশাসনিক স্তরে উৎসাহ দানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ কিছুটা হলেও বহুমুখী করার প্রেরণা পাচ্ছে।#