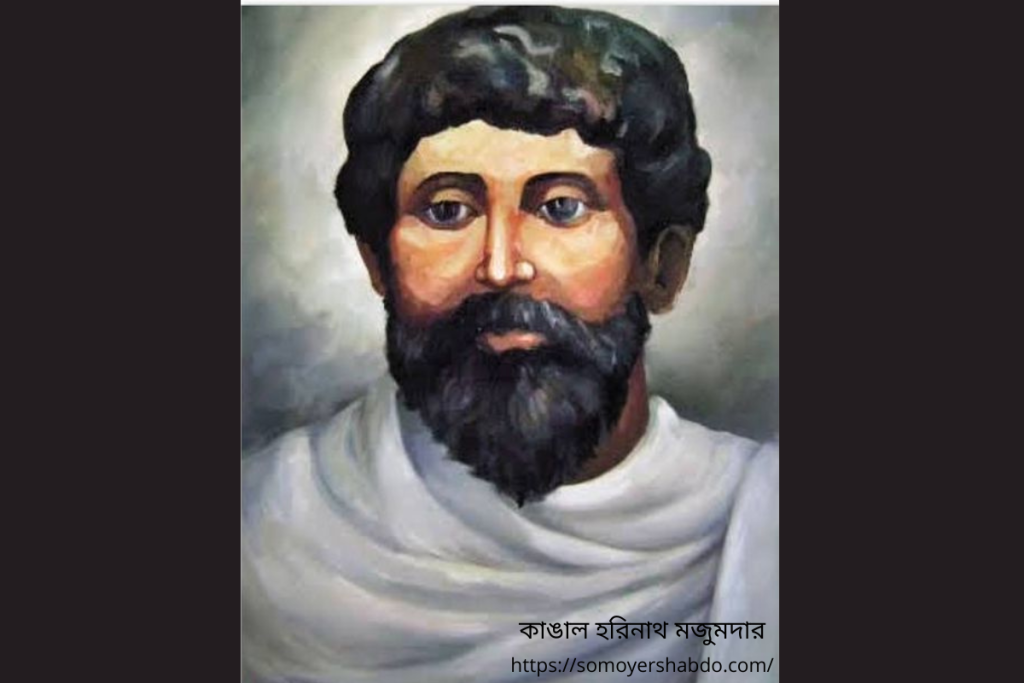নিজে প্রথাগত কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করতে না পারবার ফলে কাঙাল হরিনাথের মনে দুঃখের কোন অন্তঃ ছিল না। আর সেজন্যই অন্যান্য বালক-বালিকাদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে তিনি তাঁর নিজের অতৃপ্ত ইচ্ছাকে পূর্ণ করবার চেষ্টায় সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। গ্রাম বাংলার দরিদ্র বালক-বালিকাদের শিক্ষাদানের কাজকে হরিনাথ তাঁর জীবনের একটি অবশ্য পালনীয় ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তাঁর বয়স যখন একুশ বছর পূর্ণ হয়নি, তেমন সময়েই ১৮৫৪ সালের ১৩ই জানুয়ারি তারিখে তিনি কুমারখালিতে একটা বাঙলা পাঠশালা স্থাপন করে নিজেই সেখানে বিনাবেতনে ছাত্রদের শিক্ষাদান করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। (কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, আবুল আহসান চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮ সাল, পৃ- ১৯)
সেযুগের প্রথাগত শিক্ষার অনধিকারী হরিনাথ শিক্ষাদান করবার স্বার্থে নিজেও শেখবার সক্রিয় ও সজীব প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। অতীতের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র পিতা মথুরানাথ মৈত্রেয় হরিনাথের বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনি তখন পাবনা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ছুটি উপলক্ষে যখনই তিনি বাড়িতে আসতেন, হরিনাথ তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষেত্রতত্ত্ব, অঙ্ক ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করতেন। এরপরে মথুরানাথ যখন কুমারখালি ইংরেজি স্কুলের শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন, তখন হরিনাথের নিজের শেখার এবং ছাত্রদের শেখানোর কাজটি অধিকতর সহজ হয়ে উঠেছিল। (হরিনাথ মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ- ৬) হরিনাথের পরিশ্রম এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে শুরু করেছিল। এর ফলে হরিনাথকে আর অবৈতনিক থাকতে হয়নি। তাঁর বেতন মাসিক এগারো টাকা হয়েছিল। হরিনাথের বিদ্যালয়টির উন্নতি দেখে তৎকালীন সরকার বিদ্যালয়টিকে মাসিক এগারো টাকা সাহায্য দিতে শুরু করেছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা হয়েছিল ৯৫ জন। (হরিনাথ মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ- ৮; Dictionary of National Biography, Vol. III, Edited by S. P. Sen, Institute of Historical Studies, Calcutta. 1974, p: 22-23) তখন সেখানে চারটি শ্রেণী ও তিনজন শিক্ষক কর্মরত ছিলেন। সমসময়ে পূর্ব ভাগের বিদ্যালয়সমূহের তত্ত্বাবধায়ক এচ. উড্রো সাহেব হরিনাথের বিদ্যালয় পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং সরকারের তরফ থেকে বিদ্যালয়টির জন্য মাসিক আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করেছিলেন। বিদ্যালয়টির ক্রমোন্নতির পর্যায়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেখানকার প্রধান শিক্ষক হরিনাথের বেতন কুড়ি টাকা নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সেই কুড়ি টাকা বেতন গ্রহণ করলে যেহেতু অন্যান্য সহশিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিত হয়ে যাচ্ছিল, তাই হরিনাথ তাঁর প্রিয় সহশিক্ষকদের স্বার্থে মাসিক পনেরো টাকা বেতন গ্রহণ করে তাঁদেরও বেতন বৃদ্ধির সুযোগকে অবারিত করেছিলেন। (হরিনাথ মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ- ৮; Dictionary of National Biography, Vol. III, Edited by S. P. Sen, Institute of Historical Studies, Calcutta. 1974, p: 22-23)
আরও পড়ুন: প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তির ইতিবৃত্ত
হরিনাথ বিদ্যাসাগরের মতোই নারীজাতিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তিনি নিজেও স্ত্রীশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োগ-প্রচেষ্টায় তিনি তাঁর নিজের বাড়িতেই নিজের উদ্যোগে — “একটি বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া কয়েকটি বালিকাকে” — শিক্ষাদান করবার কাজ শুরু করেছিলেন। (কাঙাল হরিনাথ, জলধর সেন, ভারতবর্ষ, পৃ- ৭৮১) হরিনাথ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁর নিজের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে সেই বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন। তিনি তাঁর বাঙলা পাঠশালায় ইংরেজি শিক্ষার পদ্ধতি অনুসারে সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। অন্যদিকে নিজের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়েও তিনি যে প্রণালীতে শিক্ষাদান করতেন, সেটা সেযুগের বালিকাদের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর বলে বিবেচিত হয়েছিল। (হরিনাথ মজুমদার, জলধর সেন, দাসী, জুন ১৮৯৬, পৃ- ৩০৮) সেখানে বালিকাদের জন্য ভাল ভাল পুস্তক পাঠের সঙ্গে সামান্য হিসাবরক্ষার পাঠও যেমন যুক্ত হয়েছিল, তেমনই সূচীকার্য্য শিক্ষাকেও যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সমসময়ে কুমারখালিতে হরিনাথের প্রতিষ্ঠিত সেই বালিকা বিদ্যালয়টি স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রসারে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল (কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, আবুল আহসান চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮ সাল, পৃ- ২১)
সেযুগে লেখাপড়া ত্যাগ করে যেসব ছেলেরা গুণ্ডার দলে প্রবেশ করে আধুনিক পরিভাষায় সমাজবিরোধী হয়ে উঠেছিলেন, সেইসব দুর্দান্ত ছেলেদের হিতার্থে মথুরানাথ মৈত্রেয়র সহযোগিতায় হরিনাথ তাঁর নিজের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে পঠন সমিতি ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সেখানে প্রতি শনিবার বেলা চারটের পরে সমিতির কাজ শুরু হত। সেখানে সংবাদ প্রভাকর, এজুকেশান গেজেট প্রভৃতি পত্রিকা রাখা হত এবং সেইসব পত্রিকা থেকে পালাক্রমে সংবাদ পড়াও হত। এইভাবে শিক্ষাদান করবার মাধ্যমে সেইসব গুন্ডাপ্রকৃতির ছেলেদের অনেকেরই মানসিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। “অনেকে গুণ্ডার দল পরিত্যাগপূর্ব্বক কাজের লোক হইয়া পরবর্তীকালে যশঃ ও অর্থোপার্জন করিয়া সুখী হইয়াছিলেন।” হরিনাথের প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয়ের কাজ প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় শুরু হত। সেই নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করবার ব্যাপারে মথুরানাথ মৈত্রেয় এবং গোপালচন্দ্র সান্যাল তাঁর সহযোগী ছিলেন। তাঁরা সেই নৈশ বিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়াতেন, এবং স্বয়ং হরিনাথ বাংলা পড়াতেন। ওই নৈশ বিদ্যালয়ে পড়ে অনেকেই পরবর্তীকালে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন এবং সেখান থেকে — “প্রশংসার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ” — হয়েছিলেন। (কাঙাল হরিনাথ, জলধর সেন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭-৮)
হরিনাথ নিজে যতদিন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, ততদিন তিনি সেযুগের শিক্ষকরূপী যমদূতের সঙ্গে নিজেও পরিচিত হতে পেরেছিলেন। সেকালের শিক্ষকদের মধ্যে তিনি ছাত্র-দরদিভাব দেখতে পাননি। তাঁদের ছাত্রনিগ্রহ করা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। তাই নিজে শিক্ষকতার ব্রতযুক্ত হওয়ার সময়ে হরিনাথ সেসব কথা মনে রেখেছিলেন এবং নিজেকে সেযুগের একজন আদর্শ শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। হরিনাথের বাঙলা বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, পঠন সমিতি ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন এবং শিক্ষাদানপ্রণালী ও সহশিক্ষকদের সঙ্গে আচার-আচরণ তাঁকে একজন ছাত্রদরদি ও আদর্শ শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। হরিনাথের পত্রিকা পরিচালনা, বাউলগানের দল পরিচালনা প্রভৃতি কাজে সেইসব ছাত্ররাই তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন। এখানেই শিক্ষক হরিনাথের শিক্ষাদর্শের সার্থকতা ছিল। হরিনাথের শিক্ষাব্রত সম্পর্কে জলধর সেন লিখেছিলেন—
“আমরা হরিনাথের ছাত্র, শিক্ষকতা কার্য্যে কেশ পরিপক্ক হইয়া আসিল, অনেক স্থানে এ পর্যন্ত অনেক শিক্ষক দেখিয়াছি কিন্তু হরিনাথের ন্যায় শিক্ষাদানে নিপুণ, ক্ষমতাশালী শিক্ষক এ পর্যন্ত একজনও দেখিলাম না। কিরূপভাবে শিক্ষা দিলে একটি নূতন বিষয়ও বালকবালিকাগণের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইতে পারে এবং তাহা সহজে তাঁহাদের আয়ত্ত হয়, তাহা তিনি উত্তম জানিতেন। ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশ হইলে তিনি শিক্ষকশ্রেষ্ঠ স্পেনসারের সমান সম্মান ও খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন।” (হরিনাথ মজুমদার, জলধর সেন, দাসী, জুন, ১৮৯৬, পৃ- ৩০৮)
আরও পড়ুন: সাধু আন্দ্রিয়ের মিশন ও শান্তিধামে আড্ডা
শিক্ষা ছাড়া বালক-বালিকাদের কুপথ থেকে স্বাভাবিক জীবনধারার মূলস্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব নয় বলেই হরিনাথ মনে করতেন। অশিক্ষার অন্ধকারের বিরুদ্ধে শিক্ষার আলোকসংগ্রামে তিনি একজন অক্লান্ত সৈনিক ছিলেন। তিনি কোন রকমের সংকীর্ণ মনোগত চিন্তাভাবনার বাইরে চিন্তাবিন্যাসের বাস্তবায়নের সঙ্গে সক্রিয় অংশগ্রহণের একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন। শিক্ষার উন্মেষের চিন্তার সঙ্গে তিনি সঠিকভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বাস্তব অনুশীলন যুক্ত করেছিলেন। এখানে সংগ্রামের কথা এই কারণেই বলা হল যে, হরিনাথ তাঁর সমসময়ে সেযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের প্রবল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রীতিমতো লড়াই করে নিজের বিদ্যালয়গুলিকে সংস্থাপন করেছিলেন। তখন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সেখানে ছাত্রভর্তির প্রশ্ন তো ছিলই, একইসাথে দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষকতার কাজ পরিচালনা করাও সেটার থেকে বড় প্রশ্ন ছিল। বলাই বাহুল্য যে, এই ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে প্রয়োজননিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবার ক্ষেত্রেও হরিনাথ অনন্য এবং অসাধারণ ছিলেন। বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন ও বালিকাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সমস্ত রকমের প্রতিকূলতাকে তিনি সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। হরিনাথের সময়ে স্ত্রীশিক্ষার নামে সকলেই আতঙ্কিত হতেন। সেযুগের শিক্ষিতপ্রধান রাজধানীসহ পাড়াগাঁয়ের মানুষেরও অমূলক বিশ্বাস ছিল যে — মেয়েরা লেখাপড়া শিখলেই বিধবা হন! বলাই বাহুল্য যে, সেকালের মেয়েদের মা-বাবার মনের ওপরে চাপ সৃষ্টি করবার ক্ষেত্রে এই বাক্যটি যথেষ্ট ছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত ‘মাসিক পত্রিকা’–র ১৮৫৮ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখের সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী হরিহরের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীর, যিনি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন, একটি কল্পিত বার্তালাপ প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে পদ্মাবতীর বক্তব্য নিম্নরূপ ছিল—
“মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখে কি করবে? সে কি চাকরি করে টাকা আনবে? মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে বরং লোকে নিন্দা করবে। রবিবার দিন দিদির বাড়ি গিয়াছিনু সেখানে মাসী পিসী সকলেই এসেছিলেন, তাঁদের কাছে মেয়ের লেখাপড়ার কথা বলিলে তাঁহারা সকলে বললেন মেয়েমানুষের লেখাপড়া শেখায় কাজ কি? আবার কেউ বলে মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখলে রাঁড় হয়। মাগো সে কথাটা শুনে অবধি আমার মনটা ধুক পুক করছে। … আমার মেয়ে অমনি থাকুক। যে কয়দিন পাঠশালে গিয়াছিল তার দোষ কাটাইবার জন্য চূড়ামণিকে দিয়া ঠাকুরের কাছে তুলসী দেওয়াবো।” (বাংলার নবচেতনার ইতিহাস, স্বপন বসু, ১৯৮৫ সাল, পৃ- ৩০৫)
সেযুগের এই ধরণের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও হরিনাথ নিজের ব্রতচ্যুত হয়ে পিছিয়ে আসেনি। কারণ, তাঁর — “অদম্য তেজ ও উৎসাহ কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতে জানিত না।” তাঁর কাছে স্ত্রী ও পুরুষ— উভয়েই সমাজের অঙ্গবিশেষ বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, সমাজের এক অঙ্গকে যদি শিক্ষার দ্বারা উন্নত করা হয়, তাহলে অপর অঙ্গকে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখে সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফলে হরিনাথের দৃঢ় অভিমত ছিল—
“সমাজের মঙ্গলের জন্য যেমন বালক-শিক্ষার প্রয়োজন, তদ্রুপ বালিকা শিক্ষার প্রয়োজন।” (কাঙাল হরিনাথ, জলধর সেন, ১ম খণ্ড, পৃ- ৮)
এই চিন্তাচর্চার জায়গা থেকেই তিনি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও স্ত্রীশিক্ষার প্রচার-প্রসারে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন।
এইভাবে শিক্ষাদানের বাইরেও তিনি তাঁর চিন্তাচর্চাকে প্রসারিত করেছিলেন। শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষা নয়, সেকালের গ্রামের যুবকেরা যাতে নির্দোষ আমোদ উপভোগ করে নিজেদের সময় অতিবাহিত করতে পারেন, সেজন্য হরিনাথ অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক, যাত্রা, পাঁচালি ও কীর্তন রচনা করে স্থানীয় যুবকদের দিয়ে সেসব অভিনয় করিয়েছিলেন। (কাঙাল হরিনাথ, জলধর সেন, ১ম খণ্ড, পৃ- ১৭) তবে সেখানেই তিনি থেমে থাকেননি। সেযুগের সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিবারণ এবং নীলকর-জমিদারদের অত্যাচার-প্রপীড়ন থেকে অসহায় দরিদ্র প্রজাসাধারণকে রক্ষা করবার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুবিচার প্রার্থনা করাকেও হরিনাথ অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন বলে বিবেচনা করেছিলেন। নিজের শরীরী শক্তি প্রয়োগ করে অনেক সময়েই বেশকিছু সংখ্যক অত্যাচারী নীলকরদের এলাকা-ছাড়া করা সত্ত্বেও হরিনাথ এই বোধে উপনীত হতে কোন ধরণের দ্বিধা করেননি যে, নীলকরদের অত্যাচার থেকে প্রজাদুর্দশার কোন স্থায়ী সমাধান সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল না। এসব ছাড়াও তাঁর সময়কার জমিদারদের প্রজাপীড়ন তো ছিলই। তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে, সেক্ষেত্রে একই দাওয়াই কোন কাজে লাগবে না। তাই এই ব্যাপারে তিনি তাঁর সামনে দুটো উন্মুক্ত পথ দেখতে পেয়েছিলেন—
প্রথমতঃ, সংঘশক্তি সংগঠনের মাধ্যমে সেসবের প্রতিকারে জন্য জন-আন্দোলন সংগঠিত করা; এবং
দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে অসহায় প্রজাবর্গের দুঃখ-দুর্দশার বিবরণ সরকারের কাছে তুলে ধরে সেসবের প্রতিকার বিধান করা।
তাছাড়া, হরিনাথ জানতে পেরেছিলেন যে, সেযুগের বাঙলা সংবাদপত্রগুলির মর্ম সম্বন্ধে অবগত হয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবার লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে একটি অনুবাদ কার্য্যালয় খোলা হয়েছিল। (হরিনাথ মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ- ১৩) রবিন্সন সাহেব সেই কার্য্যালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। হরিনাথ সেই সংবাদে এই কারণের আরও বেশি করে উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, তাঁর পরিবেশিত সংবাদ অনুবাদের মাধ্যমে সেসব কথা সহজেই সরকারের কর্ণগোচর হবে। হরিনাথ এই দ্বিতীয় পথটিকেই তখন অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় সেযুগের গ্রামীণ সমস্যার বিভিন্ন বিবরণ পাঠানো সত্ত্বেও তাঁর মন শান্ত হতে পারেনি। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত হরিনাথের গুরু হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে মতের কোন মিল ছিল না। স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্রের রক্ষণশীল মনোভাবকে হরিনাথ কখনোই মেনে নিতে পারেননি। স্ত্রীশিক্ষার প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে হরিনাথের সক্রিয় ভূমিকা, সেই বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর বিরোধকে প্রকটিত করে তুলেছিল। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। হরিনাথ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে দৃঢ় এবং সক্রিয় অবস্থান নেওয়া সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির মাধ্যমে মেয়েরা চাকরি করুন, এমনতর কোন চিন্তাভাবনার বিরোধী ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল—
“আমরা স্ত্রী জাতির উচ্চশিক্ষার দ্বারা অর্থ-উপার্জনের প্রত্যাশা করি না।” (গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ; ৯ই জুন ১৮৭৭ সাল)
এখানে স্পষ্টতঃই লক্ষ্য করা যায় যে, স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রক্ষণশীল মনোভাবের বিরোধিতা করেও তিনি শেষপর্যন্ত আরেক ধরণের রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।
আরও পড়ুন: দশটি হাইকু
এছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে হরিনাথের আরেকটি বিষয় নিয়ে বিরোধ হয়েছিল। সেটা হল যে, তাঁরা সেযুগের নিপীড়িত প্রজার স্বার্থরক্ষার বিষয়ে একমত হতে পারেননি। প্রজাস্বার্থ রক্ষা করবার ব্যাপারে হরিনাথ তাঁর গুরু ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে অনেক সময়েই তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে জানা যায়। প্রজাপীড়নের ক্ষেত্রে হরিনাথ সেযুগের দেশীয় জমিদার ও নীল ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোন ধরণের পার্থক্য রেখা টানতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই ব্যাপারে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর মতভেদ দেখা দিয়েছিল। মধুরানাথ মৈত্রেয় এবং হরিনাথ নীলকরদের অত্যাচার সংক্রান্ত খবরাখবর একইসঙ্গে সংবাদ প্রভাকর এবং হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় পাঠাতেন। হরিনাথের পাঠানো সংবাদগুলি পেট্রিয়ট পত্রিকা ইংরেজিতে তর্জমা করে নিত। কিন্তু— “জমির মাপে ও ফসলের মাপে, চক্রবৃদ্ধি সুদ ও দাদনের ব্যবসায় দেশী বিদেশীদের মধ্যে” হরিনাথ কোন প্রভেদ দেখতে পাননি। সেই প্রশ্নে পেট্রিয়টের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্বে তিনি সম্পর্কছেদ করেছিলেন। (বিবর্ণ যুগের বর্ণঢ্য অতীত, চিত্ত বিশ্বাস, নদীয়া দর্পণ, বিশেষ সংখ্যা, ১৫তম বর্ষ, ১৯৯২ সাল, পৃ- ৬০)
উপরোক্ত ঘটনাবলীই শেষপর্যন্ত হরিনাথকে তাঁর নিজস্ব সংবাদপত্র প্রকাশ করবার সিদ্ধান্তে উপনীত করেছিল। কারণ— তাঁর ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, নিজের পরিচালনাধীনে কোন সংবাদপত্র না থাকলে তাঁর পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। আর তাই সংবাদ প্রভাকর ও হিন্দু পেট্রিয়টে সংবাদ লেখবার এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা পাঠের মাধ্যমে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও যথেষ্ট আর্থিক ঝুঁকি নিয়েই ১২৭০ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ (১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাস) তারিখ থেকে হরিনাথ তাঁর সুবিখ্যাত ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ পত্রিকাটি প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। প্রথমে এই পত্রিকাটি মাসিক সংস্করণ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপরে ১২৭৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ (১৮৬৯ সালের এপ্রিল) মাস থেকে গ্রামবার্তার পাক্ষিক সংস্করণ এবং ১২৭৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ (১৮৭০ সালের এপ্রিল) মাস থেকে গ্রামবার্তার সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। ১২৭০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে শুরু করে ১২৯২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন পর্যন্ত মোট দীর্ঘ সাড়ে বাইশ বছর ধরে নিয়মিতভাবে গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রামবার্তা-পর্যায়ে হরিনাথ তাঁর নিজের সমস্ত সামর্থ্যকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। এই সংবাদপত্রটির কাজ ও দায়দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য হরিনাথ শেষপর্যন্ত শিক্ষকতার চাকরি পর্যন্ত ত্যাগ করে সর্বক্ষণের জন্য সংবাদপত্রের কাজে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। পত্রিকাটির জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করেও তিনি সত্যনিষ্ঠায় অবিচল থেকেছিলেন। গ্রামবার্তায় প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য-নির্ভর সংবাদে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল এবং সেটার পরিণতিতে সেকালের গ্রামের মানুষেরা কিছুটা হলেও সুফল পেয়েছিলেন। তাছাড়া উক্ত পত্রিকাকেই কেন্দ্র করেই হরিনাথ কুমারখালিতে একটি সাহিত্যের পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন, যেটি ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে বেশ কিছু সংখ্যক উজ্জ্বল নক্ষত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছিল।#