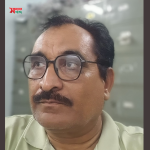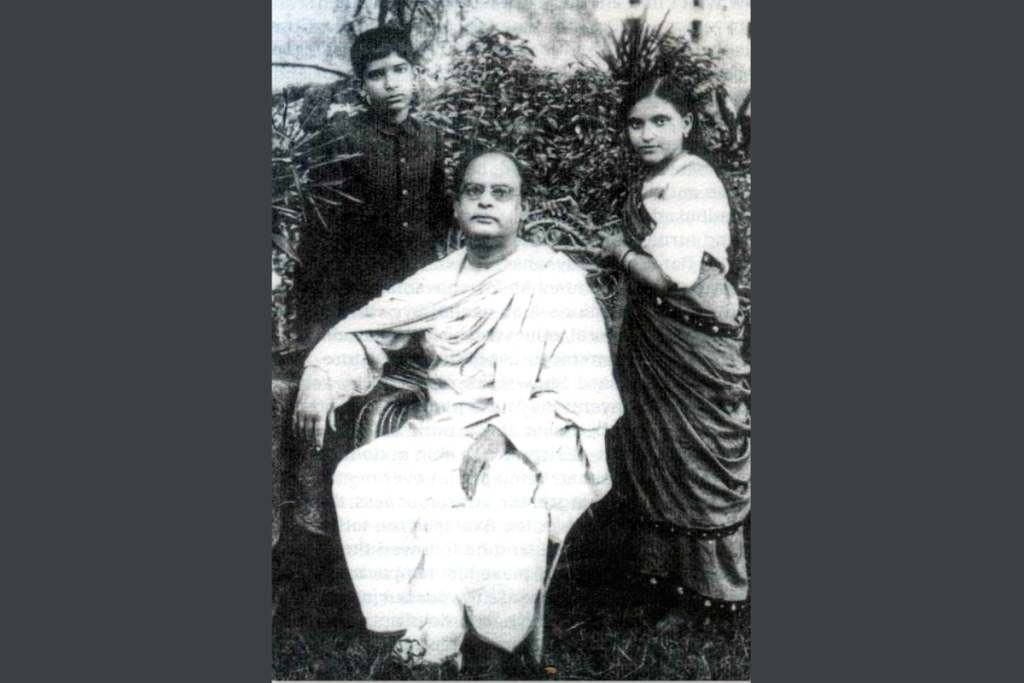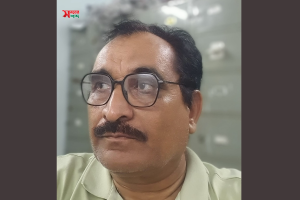অতীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্র কাব্য-গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় সজনীকান্ত দাস লিখেছিলেন— “বাংলাদেশে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রতিভা যে যথাযথ সমাদর লাভ করে নাই তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-প্রতিভার ভাস্বর দীপ্তিতে সকলের চক্ষু এমনই ধাঁধিয়া গিয়াছিল যে, আশেপাশের অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধদীপ্তি জ্যোতিষ্কের সাধারণের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই দলের প্রধান ছিলেন।”
একথা অতিশয় যথার্থ। দ্বিজেন্দ্রলাল আজও তাঁর যথাযোগ্য সন্মান পেয়েছেন বলে মনে হয় না। দ্বিজেন্দ্রলাল মূলতঃ কবি ছিলেন। তাঁর কবিতার ভাব ও বিষয়বস্তু খুব বিচিত্র পথগামী না হলেও যে তিনটি ক্ষেত্রকে অবলম্বন করে সচরাচর কোন কবির কাব্যকৃতি অবলীলায়িত হয়— কবিতা, নাটক ও সঙ্গীত —এই তিনটি বিভাগেই তিনি সমান স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে সঞ্চরণ করেছিলেন বলা যেতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রতিভার সঙ্গে তাঁর নাট্য ও সঙ্গীত-প্রতিভা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই কথাটি বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য। বাংলার আধুনিক পর্বের সমালোচনা-সাহিত্যে এই কথাটা এখনও তেমনভাবে স্বীকৃতি না পেলেও পাশ্চাত্য দেশের সমালোচকদের মধ্যে একথা একপ্রকার অপ্রতিবাদ্য সাহিত্যিক সংস্কারের মত গৃহীত হয়েছে যে, নাটকই হল কাব্যপ্রতিভার উৎকর্মের শ্রেষ্ঠভূমি। সেই কাব্যই হল উৎকৃষ্ট, যেটার মধ্যে কবির আত্মলীন কল্পনা ও বহির্মুখী কল্পনার সমন্বয় সাধিত হয়। শেক্সপিয়ারের নাটকে এই আত্ম-ভাবনা ও বিষয়মুখ ভাবনার সুষ্ঠতম সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে বলেই তিনি ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তারপরেই কাব্যশক্তির সঙ্গে গীতিধর্মী প্রতিভার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের উল্লেখ করতে হয়। কবিতা ধ্বনিনির্ভর, সুতরাং প্রকারান্তরে সুরনির্ভর। সুর ছাড়া কবিতা হয় না। কাব্য এবং সঙ্গীত একই বস্তুর— এপিঠ আর ওপিঠ। এখনও পর্যন্ত যাঁরা প্রথম শ্রেণীর কবিরূপে লোকধন্য হয়েছেন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অনেকেই হয়ত সঙ্গীতকার নন, কিন্তু তাঁদের সকলেরই কবিতার মধ্যে অল্প-বিস্তর সঙ্গীতবোধ অর্থাৎ সুরবোধ অনুসৃত হয়েছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। কারণ— সুরই কবিতার প্রাণ। একথা যদি কোন সাধারণ কবির বেলায় সত্যি হয় তাহলে যে কবির মধ্যে একইকালে কাব্যশক্তি ও সঙ্গীতশক্তির অভিপ্রকাশ ঘটেছিল, তাঁর বেলাতেও একথা আরও কত বেশি যে সত্যি হবে— সেটা না বললেও চলে।
আরও পড়ুন: প্রাচীনকালে বাঙালির বসন
উপরের অনুচ্ছেদে বর্ণিত মানদণ্ড দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বলতে পারা যায় যে, দ্বিজেন্দ্রলাল একজন যথার্থ শক্তিধর কবি ছিলেন। তিনি একাধারে একজন কবি, নাট্যকার ও সুরকার ছিলেন। অর্থাৎ— যুগপৎ তিনটি ক্ষেত্রে তিনি ধ্বনির চর্চা করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর কাব্যশক্তি যে সবিশেষ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়েছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। তবে একথা সত্যি যে, তাঁর কাব্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য নেই; প্রকৃতি, প্রেম ও স্বদেশপ্রীতি— এই তিনটি ভাবকে কেন্দ্র করেই তাঁর কাব্যকল্পনা প্রধানতঃ আবর্তিত হয়েছে; তাঁর জীবনের শেষের দিকে কিছু ভক্তিভাবের কবিতারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একথাও সত্যি যে তাঁর নাটকে বিষয়মুখীনতা অপেক্ষা আবেগোচ্ছ্বাসের প্রকাশ বেশী দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর অকালমৃত্যুর জন্য সুরের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভার যথাযথ বিকাশের অবকাশ ঘটেনি। এসব কথা স্বীকার করে নিয়েও একথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না যে, সব মিলিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টিপ্রতিভা কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ছিল। তিনি মাত্র পঞ্চাশ বছর বেঁচেছিলেন। তিনি যদি আরও আয়ুর আশীর্বাদ পেতেন এবং দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করবার পরে সাহিত্য চর্চায় আরও একান্তভাবে মনোনিবেশ করবার অবসর পেতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি বাংলা সাহিত্যের কাব্য ও নাট্যবিভাগকে আরও অনেক বেশী সমৃদ্ধ করে যেতে পারতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের অকাল প্রয়াণ তাঁর স্বীয় প্রতিভার স্ফূর্তি এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সমৃদ্ধি— সমভাবে দুইয়েরই বিঘাতক হয়েছিল।
দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা বেশী নয়— ‘আর্যগাথা’ ( ১ম ও ২য় খণ্ড), ‘আষাঢ়ে’ (১৮৯৯), ‘হাসির গান’ (১৯০০), ‘মন্দ্র’ (১৯০২), ‘অলেখা’ (১৯০৭) ও ‘ত্রিবেণী’ (১৯১২)। এর মধ্যে আর্যগাথা ১ম ও ২য় খণ্ড তাঁর নিতান্তই প্রথম বয়সের রচনা। কবির আঠাশ থেকে তেত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে এই কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। এই কবিতাগুলিতে ভাবের উচ্ছ্বাস রয়েছে, ভাষার বল্গাহীনতা রয়েছে, ছন্দও তেমন সুপরিণত নয়। তবে ওই কবিতাগুলির মধ্যেই কবির ভবিষ্যৎ কাব্য-ব্যক্তিত্বের প্রবণতা কোন খাত বেয়ে অগ্রসর হবে— সেটার আভাস বিদ্যমান ছিল। সাহিত্য সমালোচকদের মতে— দ্বিজেন্দ্রকাব্যে স্বদেশপ্রীতি ও প্রেম —এই দুটি ভাব বলবৎ রয়েছে বলে দেখা যায়। এই দুই ভাবেরই অঙ্কুর আর্যগাথার কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্র-নাট্যরচনায় স্বদেশানুরাগের আদর্শের প্রকৃষ্ট বিকাশ ঘটেছিল। তাঁর হাসির গানের কবিতাগুলিতে বিজাতীয় রীতিনীতির প্রতি তীব্র ঘৃণা ও জাতীয় মর্যাদার আদর্শে অসংশয় আস্থাশীলতা প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্র-কাব্যে বারে বারেই কাপুরুষতার প্রতি ধিক্কার বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল— তা সেটা হাসির গানেই হোক আর অন্য ধারার কবিতাতেই হোক। এসবেরই আদল তাঁর আর্যগাথার কবিতাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। এর উপরে প্রেমানুভূতির প্রকাশও আর্যগাথার কবিতায় অলক্ষ্যণীয় নয়। আর্যগাথা দ্বিতীয় খণ্ডের রচনায় প্রেম একটি বিশেষ জায়গা জুড়ে রয়েছে। সেখানে প্রেম মানে— দাম্পত্য প্রেম, পারিবারিক শুচিতার সংস্কার দ্বারা মার্জিত স্বামী-স্ত্রীর বৈধ ভালবাসা। পরকীয় বা আধুনিক কালোচিত স্বাধীন প্রেমের আদর্শের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের কখনোই কোন আকর্ষণ ছিল না, এবং সেসবের প্রতি তাঁর কোন সায়ও ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলালের পরিণত জীবনের কাব্য-গ্রন্থাদিতে এই সংসারমুখাশ্রয়ী দাম্পত্য প্রেমের ছবি বারেবারেই প্রকাশমান হয়ে উঠেছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ১৯০৩ সনে স্ত্রী বিয়োগ হওয়ার পরে তাঁর এই বিশেষ হৃদয়ানুভূতিটি যেন আরও বেগবতী হয়ে উঠেছিল। খৃষ্টীয় উনিশ শতকের বাঙালি কবিদের মধ্যে যে বিশিষ্ট প্রবণতাটি দেখতে পাওয়া যায়, সেটা হল যে— তাঁরা প্রায় সকলেই গভীরভাবে গৃহগতপ্রাণ ও দাম্পত্য অভ্যাসের বশীভূত ছিলেন। তাঁদের ভাবনার কেন্দ্র-মধ্যে প্রেমের প্রতীকরূপে সাংসারিক প্রেম সবটুকু জায়গা জুড়ে ছিল বলে দেখা যায়। সেকালের নাগরিক মধ্যবিত্তের সংস্কার অনুযায়ী তাঁদের প্রেম একান্তভাবে গৃহকেই আশ্রয় করেছিল, সেই প্রেম দৃষ্টিগ্রাহ্যের সীমা ছাড়িয়ে বা একান্ত আপনার জনদের আকর্ষণ অতিক্রম করে পরিশোধিত বা বিমূর্তভাবে উদার মানবীয় প্রেমরূপে বিশ্বময় জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তখন ভালবাসা বলতে গৃহের চতুঃসীমার প্রাচীরাবদ্ধ অংশে তাঁদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে শুধুমাত্র মাতৃস্নেহ পত্নীপ্রেম বাৎসল্য স্বজনানুরাগ প্রভৃতি মৌলিক অনুভূতিগুলি প্রতিভাত হয়েছিল বলে দেখা যায়। তাঁদের শুদ্ধতর বা উদারতর রূপের অভিব্যক্তির খুব একটা পরিচয় কিন্তু পাওয়া যায় না। সেকালের কবিদের মধ্যে বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয় বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল, এমনকি প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাথ— সমালোচকদের মতে সকলেই অল্পবিস্তর এই ভাবের ভাবুক ছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যকল্পনার শ্রেষ্ঠত্ব হল যে, তাঁদের কল্পনা অন্যান্য মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বারা আবিষ্ট ঊনিশ শতকীয় বাঙালি কবির মত শুধুমাত্র গৃহচেতনাতেই আবদ্ধ হয়ে থাকেনি; তাঁদের উদার দৃষ্টির কল্পনা নিকটজনদের প্রেমকে ছাড়িয়ে আরও বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েরই পরিণত রচনায় যেটাকে বিশ্বাত্মিকা বুদ্ধি বলে সেটার প্রকাশ ঘটেছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্য কারও তুলনা চলে না, কিন্তু এবিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্বও খুব একটা কম কিছু ছিল না। যে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর মন্দ্র আলেখ্য ও ত্রিবেণী কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় হৃদয়ানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রাবল্যের মুখে দাম্পত্য প্রেমের উচ্ছ্বসিত বন্দনা গান করেছিলেন, সেই দ্বিজেন্দ্রলালই আবার নাটকের ভূমিতে দাঁড়িয়ে বিশ্বপ্রেমকে মানবতার শ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সমালোচকদের মতে— নাটকেই মধ্যবিত্ত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সার্বভৌম উৎকর্ষের লক্ষণমণ্ডিত বিশ্বকবিতে পরিণত হয়ে উঠেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক যতই মেলোড্রামা আর রোম্যান্টিক আবেগাতিরেকের উপাদান দ্বারা ভারাক্রান্ত হোক না কেন, দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ কিন্তু তাঁর নাটকেই ঘটেছিল। তিনি যে একজন যথার্থ কবি ছিলেন, সেটার পরিচয় তাঁর নাটকের মধ্যেই সবথেকে বেশি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। নাট্যরচনার আঙ্গিকগত কলা-প্রকরণের দিক থেকে যেমনই হোক, ভাবের মহিমার দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি নাটককে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের নাট্যসৃষ্টি বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যাই হোক, যেহেতু নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালকে নিয়ে এই আলোচনা নয়, তাই পুনরায় তাঁর কাব্যের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।
আরও পড়ুন: ইতিহাসের বাস্তব এবং লেখকের বাস্তব: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ৪
কবি দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের হৃদয়বত্তার ঐশ্বর্যে বিশ্বাস করতেন। ভাবাবেগের আতিশয্যকে তিনি কাব্যপরিমণ্ডলের মধ্যে অপাংক্তেয় বলে জ্ঞান করতেন না। আন্তরিকতা তাঁর কবিতার সহজ বর্মের মত ছিল। তিনি তাঁর সময়কার একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং— তাঁর ব্যক্তিত্বের গঠনের মধ্যে মননশীলতার কিছু অভাব ছিল না; কিন্তু কাব্যে ও নাটকে তিনি মননশীলতারও বহু ঊর্ধ্বে আন্তরিকতার সম্পদকে জায়গা দিয়েছিলেন। যেকোন আধুনিক কবির রচনায় হৃদয়তাপবর্জিত যে বুদ্ধির জৌলুষ দেখতে পাওয়া যায়, সে রকম একতরফা বুদ্ধির ঝলকানির প্রতি কবির বিশেষ কোন আস্থা ছিল না। এই প্রসঙ্গে কবি নিজেই লিখেছিলেন—
“কাব্য নয়ক’ ছন্দোবন্ধ মিষ্টি শব্দের কথার হার,
কাব্যে কবির হৃদয় নেই যার তাহার কাব্য শব্দসার।
যেথায় ভাস্বর যেথায় মূর্ত ঝঙ্কারিত কবির প্রাণ,
উৎসারিত মহাপ্রীতি— তাহাই কাব্য তাহাই গান।”
(কবি, আলেখ্য)
একটু আগেই কবির নিবিড় দাম্পত্য প্রেম ও সংসার-স্নেহের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর আলেখ্য কাব্যগ্রন্থের— ‘বিপত্নীক’ ও ‘চিরবিচ্ছেদ’; ত্রিবেণী কাব্যগ্রন্থের— ‘প্রথম চুম্বন’, ‘সোনার স্বপ্ন’, ‘স্মৃতি’, ‘আহ্বান’ প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কবির স্ত্রী-প্রেমের নিষ্ঠা ও গভীরতা প্রকাশ পেয়েছিল বলে দেখা যায়। নিজের লোকান্তরিতা স্ত্রীর ভালবাসার স্মৃতি যেন একটা প্রবহমান ধুয়ার মত কবির কাব্যে ও গানে বারে বারেই ফিরে ফিরে আসতে চেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ‘স্মরণ’ কাব্যগ্রন্থে যেমন কবির নিবিড় স্ত্রী-প্রেমের স্মৃতি এক জায়গায় সংহত হয়ে রয়েছে; তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় সেটা নানা জায়গায় নানাভাবে বিক্ষিপ্ত ও বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে বলে দেখা যায়। তাঁর কাব্য শোকের হাহাকারে পূর্ণ। এই প্রসঙ্গে এখানে তাঁর কাব্য থেকে দু’-একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা যেতে পারে—
“সে গেছে, আমার মর্মপটে ছায়ার মত ভেসে,
সে গেছে, আমার হৃদয়-তটে ঢেউয়ের মত এসে,
তারে, নয়ন ভরে দেখেছিলাম
প্রাণের ভিতর রেখেছিলাম
রক্ত দিয়ে ঘিরে—
ঘুমের সিংহাসনে বসিয়েছিলাম
সোনার স্বপ্নটিরে।”
(সোনার স্বপ্ন)
তাঁর ‘প্রথম চুম্বন’ কবিতায় প্রেমিক-প্রেমিকার প্রথম প্রণয়ের যে চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছিল, সমালোচকদের মতে সেটা অপূর্ব—
“প্রণয়ের সেই প্রথম মধুর চুম্বনে,
সে গীতে সর্ব কোলাহল যায় থামিয়া,
মানবের ঘোর দৈন্যে, দুঃখে, দুর্দিনে,
আসে একবার স্বর্গরাজ্য নামিয়া।
জীবনের সার প্রথম মধুর যৌবনে;
যৌবনসার প্রথম মধুর প্রণয়ে;
প্রণয়ের সার প্রথম মধুর চুম্বনে;
—মানবের অতি সুখময়তম ক্ষণ–এ।”
কবি কতভাবে যে নিজের অন্তরের স্ত্রী-বিয়োগজনিত বিরহের আর্তি ও শূন্যতার হাহাকারকে প্রকাশ করেছিলেন— সেসবের কোন ইয়ত্তা নেই। তাঁর ‘মাতৃহারা’ কবিতার একটি স্তবক এরূপ—
“না না, তুইই সইতে পারিস, আমিই সইতে পারি না—
কী জিনিস যে হারিয়েছিস বুঝিস না ক তুই।
এখন রে তোর কাছে,
তুল্যমূল্য স্বর্ণ লোষ্ট্র, দুই।
তাহার উপর শিশুর হাড় ভেঙে গেলে জোড়া লাগে,
আমাদের আর লাগে না ক জোড়া;
তোদের যদি শুকায় গাছটি, শুকায় শুধু গাছের ডগা,
আমাদের যে একেবারে গোড়া।”
তাঁর ‘বিপত্নীক’ কবিতার শেষাংশে রয়েছে—
“চলেছি তো এইরূপেই এ-জীবনপথে শান্তিসুপ্তিহীন;
জানি না তো কখনো কি তাহার সঙ্গে দেখা হবে কোন দিন!
যতখানি দেখা যাচ্ছে, —ধূ ধূ করে শুধু অসীম বারিনিধি।
অহো— কী মনুষ্যজন্মই তোমার বিশ্বে তৈয়ের করেছিলে বিধি!”
এছাড়া তিনি বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসের কবিতাও অনেক লিখেছিলেন। সেই বর্গের কবিতগুলির মধ্যে— ‘ঘুমন্ত শিশু’, ‘পুত্রকন্যার বিবাদ’, ‘নূতন মাতা’, ‘আশীর্বাদ’, ‘জীবন-পথের নবীন পান্থ’ —প্রভৃতি রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। ঘুমন্ত শিশু কবিতাটির শেষাংশ নিম্নরূপ—
“না না, —ঘুমা এমনি করে— আহা মরি, একি
মধুর ছবি! ঘুমা আমি নয়ন ভরে দেখি!
এমন বকুলতলায়, এমন শান্ত বনভূমে,
আরো খানিক থাক রে যাদু, মগ্ন গাঢ় ঘুমে।
চিত্রকরটি হতাম যদি, তোরে এমন দেখে,
রেখে দিতাম যত্ন করে সোনার পটে এঁকে।
ঘুমা এমনি মুগ্ধ হয়ে দেখি আমি খানিক,
ঘুমা আমার সোনার যাদু, ঘুমা আমার মানিক।”
তাঁর ‘জীবন-পথের নবীন পান্থ’ কবিতার অনবদ্য একটি স্তবক নিম্নরূপ—
“দেখেছি সন্ধ্যায়, শান্ত হৈমকরে
রঞ্জিত মেঘের গরিমা দীপ্ত,
দেখেছি উষায়, নীল সরোবরে
অমল কমল শিশিরলিপ্ত
নিদাঘে, নির্মেঘ প্রভাতের ছটা
বসন্তের নব শ্যামল কান্তি,
বর্ষায়, বিদ্যুতে দীর্ণ ঘন-ঘটা;
শরতে, চন্দ্রের স্বপনভ্রান্তি;
এ বিশ্বে সৌন্দর্য যেই দিকে চাই,
রাশি রাশি রাশি হয়েছে সৃষ্ট;
তেমন সৌন্দর্য কিছু দেখি নাই,
শিশুর হাসিটি যেমন মিষ্ট।”
এখানে কিঞ্চিৎ সবিস্তারেই দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহগতপ্রাণ প্রেমিক ও সন্তানস্নেহাসক্ত চিত্তের ছবিটি তুলে ধরবার চেষ্টা করা হল। শুধু যে কবির কাব্য-মানসের পরিচয় দেওয়ার জন্যই এরকম কিছু করা হয়েছে সেটা কিন্তু নয়; এই ধরণের উৎকলনের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ।
প্রথমতঃ, এর মাধ্যমে প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কাব্যের নিজস্ব ক্ষেত্র, অর্থাৎ— কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কবির কল্পনা স্বতঃস্ফূর্ত হয়েও উচ্চ-মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের সীমাবদ্ধ গণ্ডীকে কখনো অতিক্রম করে যেতে পারেনি। তাঁর এই ধরণের কবিতাগুলিতে বড্ড বেশি গার্হস্থ্য লালিত পত্নী পুত্র কন্যা সার জীবনের ছবি আঁকা রয়েছে, এগুলোর মধ্যে বৃহতের ও মহতের কোন আহ্বান দেখতে পাওয়া যায় না। বহির্বিশ্বের কর্মচাঞ্চল্যের অভিমুখে তাঁর দৃষ্টি এখানে প্রসারিত নয়, এবং যে পরিমাণে এই কাব্যে আত্মকেন্দ্রিকতা বেশী ও বহির্মুখীনতা অনুপস্থিত বলে দেখা যায়, সেই পরিমাণেই এই কাব্যগুলি ‘sublime’–এর স্পর্শবর্জিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের গুটিকয় কবিতায় ‘sublimity’–র ছোঁয়া লেগেছেবলে দেখতে পাওয়া যায়; যথা— ‘প্রবাসে’, ‘সত্যযুগ’, ‘সমুদ্রের প্রতি’, ‘তাজমহল’, ‘সমুদ্র’, ‘কলি’ প্রভৃতি কবিতায়। এছাড়া তাঁর একাধিক গানের বাণীতে এই ছোঁয়া দেখতে পাওয়া যায়। গান দ্বিজেন্দ্রলালের একটি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি— বাণীরচনার দিক থেকে হোক, কিংবা সুররচনার দিক থেকে, অথবা গীতিমধুর সঙ্গীতরচনায়, বা স্বদেশভাবাত্মক সঙ্গীত রচনায়, কিংবা একক গানে, অথবা যৌথ বা কোরাস গানে। আর যেকথা আগেই বলা হয়েছে, তাঁর নাটকের মধ্যে সেই সুর পাওয়া যায়— যা মনকে ক্ষুদ্র পরিবারকেন্দ্রিক সংসার সীমানার বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাঁকে মহতের অভিসারের পথে নিয়ে যায় ও মনকে অনুপ্রাণিত করে উন্নীত করে তোলে।
আরও পড়ুন: রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন
দ্বিতীয়তঃ, উপরে উদ্ধৃত কবিতাংশগুলির বাক্য, ছন্দ ও মিলের বাঁধুনি লক্ষ্য করে বিচক্ষণ পাঠক-পাঠিকার স্বতঃই একথা মনে হতে পারে যে— দ্বিজেন্দ্রলাল ধ্বনির একজন ওস্তাদ জাদুকর ছিলেন ও ছন্দ-লয়ে তাঁর হাত অতিশয় কুশলী ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘আধুনিক সাহিত্য’ নামক সমালোচনা গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালের ‘আষাঢ়’ ও ‘মন্দ্র’ কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের বিশদ আলোচনা করেছিলেন। সেখানে তিনি এই দুই কাব্যগ্রন্থের ভাবের স্বতঃস্ফূর্তি, ছন্দের অবলীলায়িত প্রবাহ ও মিলের কারুনৈপুণ্যের অতি উচ্চ প্রশংসা করলেও একটি বিষয়ে তাঁর মনে খটকা থেকে গিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কবিতায় শব্দ-ব্যবহার করতে গিয়ে জায়গায় জায়গায় ইচ্ছাকৃতভাবে যে গদ্যের চাল অবলম্বন করেছিলেন, কবিগুরু সেটার অনুমোদন করতে পারেননি। সেই কারণে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের ‘আষাঢ়’ কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন— “কিন্তু পদ্যকে সমিল গদ্যরূপে চালাইবার কোন হেতু নাই। ইহাতে পদ্যের স্বাধীনতা বাড়ে না, বরঞ্চ কমিয়া যায়। কারণ কবিতা পড়িবার সময়ে পদ্যের নিয়মরক্ষা করিয়া পড়িতে স্বতঃই চেষ্টা জন্মে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যদি স্খলন হইতে থাকে তবে তাহা বাধাজনক ও পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। …আষাঢ়ের অনেকগুলি কবিতা ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতা-বশত আবৃত্তির পক্ষে সুগম হয় নাই বলিয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে।”
দ্বিজেন্দ্রলালের এই অভিনবত্ব প্রয়াস, অর্থাৎ— কাব্যবন্ধের ভিতরে সচেতন গদ্যভঙ্গির আমদানির ফলে তাঁর কাব্যের আবৃত্তিযোগ্যতার যে হানি ঘটেছিল, সে বিষয়ে অন্যান্য সমালোচকদেরও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পরবর্তীকালীন বাংলা কবিতার পৌরুষব্যঞ্জকতা তথা বাস্তবধর্মিতার মূল এখানেই নিহিত রয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মাধ্যমে যে প্রয়াসের বলিষ্ঠ সূচনা ঘটেছিল, আধুনিক কবিতায় সেটারই সার্থক ফলশ্রুতি বহমান রয়েছে। তাই দ্বিজেন্দ্রলালকে নিঃসন্দেহে এদিক থেকে পথিকৃতের মর্য্যাদা দেওয়া যেতে পারে। তিনিই প্রথম সজ্ঞানভাবে পদ্যের চালের ভিতরে গদ্যভঙ্গীর অবতারণা করেছিলেন। তাঁর ‘সত্যযুগ’ কবিতাটি একথার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। সেটির একটি অংশ নিম্নরূপ—
“নির্মেঘ অমাবস্যা রাত্রি, শুয়ে আছি
ঊর্ধ্ব মুখে হাতে মাথা রাখি,
বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেছে,
জেগে আছি বাড়ীর মধ্যে আমিই একাকী
স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে জ্বলন্ত নক্ষত্রপুঞ্জে
চেয়ে দেখি দূরে;
ভাবি এত মহাজ্যোতি কী মহৎ উদ্দেশ্যে
ঊর্ধ্বে মহাশূন্যে ঘুরে?”
এই চালের ছন্দকে অতীতের প্রসিদ্ধ ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন ‘সাক্ষরিক ছন্দ’ আখ্যা দিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন—
“দ্বিজেন্দ্রলালের একটি মস্ত কৃতিত্বই এইখানে যে, তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দে অক্ষরবৃত্তের সমাহিত কদম মিশিয়ে এক নবছন্দের রসসৃষ্টি করেছেন— এমনকি মৌখিক হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদের প্রয়োগ বজায় রেখে। আমরা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আলোচনায় দেখেছি যে, সে ছন্দে হাল আমলে এক হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ ছাড়া আর সব মৌখিক ক্রিয়াপদই পাংক্তেয় হয়েছে (যথা— পেরেছি, ছিলাম, দিয়েছিল)। দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম দেখালেন যাচ্ছি করছি করতে বস্তে বল্লাম জাতীয় হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ এনেও অক্ষরবৃত্তের গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব।”
আরও পড়ুন: বাউলের পথেই রবীন্দ্রনাথ
এসব দৃষ্টান্ত ও মন্তব্য থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দোজ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান নামে হাসির হলেও আসলে সুতীব্র ব্যঙ্গাত্মক রচনা। সমাজ সমালোচনাই এই গানগুলির মূল উপজীব্য। দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক বাঙালি বাবু সমাজের দাস্যতা, পরানুকরণপ্রিয়তা, বিজাতীয় আচার-আচরণের প্রতি তিনি একাধারে কবিতারূপে পাঠ্য ও গানরূপে শ্রাব্য এই বিখ্যাত রচনাগুলিতে মোহ, শাঠ্য ও কাপুরুষতা, আরামপ্রিয়তা, হুজুগেপনা, মদ্যাসক্তি প্রভৃতি বিচিত্র অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্মল বিদ্রূপের চাবুক চালিয়েছিলেন। হাসির গানের মাধ্যমেই দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি প্রথম ছড়িয়ে পড়েছিল। এই হাসির গানগুলিতে যে সমালোচনা প্রকটিত হয়েছিল, সেটা নেহাৎ মিছরির ছুরি ছিল না, সেটা রীতিমত ধারালো ফলাবিশিষ্ট ছুরি ছিল— যা উদ্দিষ্টের মর্মস্থলে কেটে কেটে গিয়ে বসে গিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যায়-অসহিষ্ণু পৌরুষব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বের ছাপ এই রচনাগুলির উপরে বিশেষভাবেই পড়েছিল। মনোরঞ্জনের স্থূল লক্ষ্য ছাড়াও এই রচনাগুলির গূঢ় লক্ষ্যও দেখতে পাওয়া যায়— জাতিকে নানাপ্রকার অবিচার, মূঢ়তা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সজাগ করে তোলাই হল সেই লক্ষ্য। অতীতে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান সম্পর্কে কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছিলেন— “তৎকালীন সমাজে চারিদিকে কাপট্য, অসারল্য, অনাচার, অসংগতি, দাম্ভিকতা, ইতরতা, বাক্যের সহিত আচরণের অসামঞ্জস্য, পরানুচিকীর্ষা, স্বার্থের জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জন ইত্যাদির অজস্র নিদর্শন দেখে তাঁর মনে যেমন বিতৃষ্ণার ভাব জেগেছিল, তেমনি তাঁর দেশভক্ত মনে ক্ষোভ ও আক্ষেপ জন্মেছিল। তিনি সমাজ সংস্কারকের ব্রত গ্রহণ করলে এসব নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন, সভায় সভায় বক্তৃতা করে বেড়াতেন, নানা সংঘ সমিতি গড়তেন। তিনি জন্মসিদ্ধ কবি, তাই কবিতা লিখেছেন। রঙ্গাত্মক মনোভাব তাঁর সহজাত।”
কিন্তু হাসির গানের কবিতায় দ্বিজেন্দ্র-ব্যক্তিত্বের একটি দিকমাত্র প্রকাশিত হয়েছিল বলে দেখা যায়। তাঁর অন্যায় অসহিষ্ণুতা, তাঁর আপোষহীন সমাজ-সমালোচনা, তাঁর রঙ্গব্যঙ্গপ্রিয়তা, তাঁর বৈঠকী মেজাজ, তাঁর ছন্দমিল নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগ্রহ— এসব হাসির গানে কখনও আলাদাভাবে তো কখনও আবার একত্রে উপস্থিত হয়েছিল বলে দেখা যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর মন প্রশান্তি ও গাম্ভীর্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। দুঃখ ও বেদনার অভিষেকে তাঁর মনের নব রূপান্তর লাভ হতে চলেছিল। আঘাতের উল্লাসে তখন তিনি আর আগের মত আনন্দ পাচ্ছিলেন না, বরং তখন তিনি তাঁর হৃদয়ে মানুষের ব্যথায় সমব্যথী হওয়ার একটি অনাস্বাদিতপূর্ব নতুন আকুলতা বোধ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর দীর্ঘবিস্তৃত কবিতা— ‘প্রবাসে’–র এই ক’টি চরণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—
“হাস্য শুধু আমার সখা?
অশ্রু আমার কেহই নয়?
হাস্য করে অর্ধজীবন করেছি তো অপচয়।
চলে যা রে সুখের রাজ্য,
দুখের রাজ্য নেমে আয়।
গলা ধরে কাঁদতে শিখি গভীর সহবেদনায়:
সুখের সঙ্গ ছেড়ে করি
দুখের সঙ্গে সহবাস—
ইহাই আমার ব্রত হৌক,
ইহাই আমার-অভিলাষ।
পরের দুঃখে কাঁদতে শেখা—
তাহাই শুধু চরম নয়।
মহৎ দেখে কাঁদতে জানা—
তবেই কাঁদা ধন্য হয়।”
দুঃখের অভিঘাতে দ্বিজেন্দ্রলালের মন তখন যে ক্রমশঃ নিজের জানাচেনার সংকীর্ণ জগৎকে ছাড়িয়ে উদার মানবপ্রেমের জগতের অভিমুখে প্রধাবিত হচ্ছিল, এসব ভাব সেসবেরই প্রমাণ দেয়। এরপরে নাটকে তাঁর এই উদার ভাব আরও বেশি করে দানা বেঁধে উঠেছিল।#