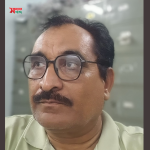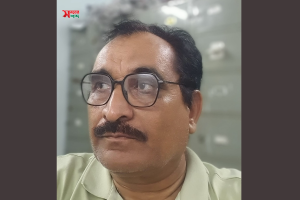হ্যাঁ, পনেরো বছর। আজ থেকে ঠিক পনেরো বছর আগে এমনই এক মে মাসের ২১ তারিখে উত্তর ভারত মহাসাগরে জন্ম নিয়েছিল অত্যন্ত ভয়াবহ দ্বিতীয় ঘূর্ণিঝড়— আয়লা। অবশেষে সমুদ্র উপকূলে সেটা আছড়ে পড়ে।
সেই দিনটা ছিল ২৫ মে, ২০০৯ সাল। তখন মধ্য দুপুর। দিনের বেলাতেই নেমে আসে রাতের চেয়েও নিকষ অন্ধকার। ভয়ঙ্কর সেই দুর্যোগ এতটাই তাণ্ডব শুরু করেছিল যে, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল ভারত সেবাশ্রম সংঘ, বেলুড় মঠ, ইসকন থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।
পর দিনই জানতে পেরেছিলাম, আয়লার তাণ্ডবে অন্তত ১৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এক দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষ ঘরছাড়া। অন্তত ১০০টি নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষয়ক্ষতির শিকার অন্তত সাড়ে তিন লাখ মানুষ। সারা পৃথিবীতে তখন একটাই আলোচনার বিষয়— আয়লা।
কিন্তু মাত্র কয়েক দিন। তার পরেই ঘটে গেল লালগড়-কাণ্ড। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দামামা। ব্যস, মানুষের চোখ সরে গেল সেই দিকে। ফলে আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবনের লোকেরা কে কেমন আছেন, তাঁদের কোনও খবরই আর পাচ্ছিলাম না।
যেহেতু আগেই জেনেছিলাম সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জি-প্লট এবং তার উলটো দিকের রাক্ষসখালি। তাই একদিন সক্কালবেলায় ক্যানিং থেকে একটা ভটভটি ভাড়া করে একা-একাই রওনা হয়ে গেলাম সেখানে।
ভটভটি থেকে নামার আগেই দেখলাম, পাথরপ্রতিমার যে স্থলভূমিতে আমি পা রাখতে যাচ্ছি, সেই রাক্ষসখালি দ্বীপটায় বুঝি সত্যিই কোনও রাক্ষস এসে তছনছ করে দিয়ে গেছে। কিছুটা যেতেই চোখে পড়ল ভাঙাচোরা একটা ডিঙি। ডিঙি তো জলে থাকে! জল থেকে এটা এত দূরে কেন? স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, সে দিন এমন ভয়ংকর তাণ্ডব হয়েছিল যে, হাতানিয়া-দোয়ানিয়ার বুক থেকে জলোচ্ছ্বাস এটাকে তুলে এখানে ছুড়ে ফেলেছে।
এ পাশে ও পাশে দোমড়ানো-মোচড়ানো গাছপালা। ঘরবাড়ি। না, কোনও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়েনি। কারণ, ওই দ্বীপে ওখনও বিদ্যুৎই পৌঁছয়নি। আগামী দশ-কুড়ি বছরেও পৌঁছবে কি না সন্দেহ আছে।
তবে ঝড়ের তাণ্ডবে মুখ থুবড়ে পড়া ছোট্ট একটা মুদিখানা কাম চায়ের দোকানের সামনে দেখলাম, একটা ছেলে মোবাইলে বকবক করে যাচ্ছে। এখানে টাওয়ার আছে!
পকেট থেকে বের করে দেখি, আমার মোবাইলেও পুরো টাওয়ার। অবশ্য চার্জ একদম নেই বললেই চলে। ‘এখানে মোবাইলে কোথায় চার্জ দেওয়া যায় বলতে পারবেন?’ জিজ্ঞেস করতেই ছেলেটি বলল, ‘বাজারে যান। দু’টাকা দিলেই গাড়ির ব্যাটারিতে চার্জ দিয়ে দেবে।’
ইট পাতা রাস্তা। রাস্তার ধারে যে সব গাছপালা ছিল, ঝড়ের দাপটে ধরাশায়ী। প্রকাণ্ড গাছগুলির শিকড়বাকড়ের সঙ্গে উপড়ে গেছে বেশ কিছুটা করে রাস্তাও।
রাস্তার ধারের জমিগুলোর ওপরে লাল পুরু সরের মতো ওগুলো কী? প্রশ্ন করতেই স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তপন মিশ্র বললেন, ‘এখন লালচে দেখছেন, পুরোপুরি শুকোলে দেখবেন সাদা ফটফট করবে। ওগুলো নুন। কয়েক দিন ধরে এই জমিতে আয়লার জল দাঁড়িয়ে ছিল তো। মাটি শুষে নিয়েছে। এই জমিতে আগামী তিন-চার বছর আর কোনও ফসল হবে না।’
স্থানীয় বাসিন্দা মহীতোষ দিন্দা বললেন, ‘এর আগেও তো বহুবার এ রকম হয়েছে। কিন্তু এবারকার মতো এত তীব্র লবণাক্ত জল কখনও জমিতে ঢোকেনি। দেখুন, কোথাও এতটুকু ঘাস দেখতে পাবেন না। সব হলুদ গেছে। গরু-বাছুরগুলো এর পরে যে কী খাবে, কে জানে!’
পাশে দাঁড়ানো ফাতেমা বিবি বললেন, ‘হুহু করে জল ঢুকে পুকুরে পড়তেই মাছগুলো ছটফট করতে লাগল। জল থেকে তিড়িংবিড়িং করে ক’হাত উঁচুতে লাফ মারতে লাগল। মাত্র কয়েক মিনিট। তার পরেই পুকুরের মাছগুলো মরে জলে ভাসতে লাগল। সে মাছ এত নোনতা, ঠিক নোনতা নয়, তেতো, জিভে ঠেকানো যায় না।’
বাজারে গিয়ে মোবাইলে চার্জ দিচ্ছি। দেখি, সামনেই একটা কালীমন্দির। তার পাশেই নামখানা ব্লকের উদয়ন ক্লাব ও জ্ঞানেন্দ্র পাঠাগার। সেখানে প্রচুর ভিড়। শুনলাম, কলকাতার ভবানীপুর থেকে মাতৃসংঘ জনকল্যাণ আশ্রম সাত জনের একটি মেডিকেল টিম নিয়ে এসেছে। সঙ্গে প্রচুর ওষুধ, ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার, শুকনো খাবার আর দুশোখানা মশারি। মশারি? মশারি দিয়ে কী হবে?
দোকানদার বললেন, ‘সাড়ে তিনটে-চারটে বাজুক, রোদের তাপটা একটু কমুক, তখন দেখবেন। কথা বলতে পারবেন না। তাকাতে পারবেন না। চোখে-মুখে মশা ঢুকে যাবে। ওই যে লোকটিকে দেখছেন, উনিই সব ব্যবস্থা করেছেন।’
উনি একষট্টি বছরের তরুণ হরিপদ পাল। একশো দু’খানা দ্বীপ নিয়ে গড়ে ওঠা এই সুন্দরবনটাকে উনি নিজের হাতের তালুর চেয়েও ভাল চেনেন। তিনি সংগঠনের অন্য সদস্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘এখন মশারির বস্তা খোলা যাবে না। তা হলে লুঠপাট শুরু হয়ে যাবে। সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং আমরা দুটো দলে ভাগ হয়ে ব্রজবল্লভপুর আর গোবিন্দপুরে চলে যাই।’ তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘সেখানকার অবস্থা কেমন, দেখতে চাইলে আপনিও আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন।’
গোবিন্দপুরে যে দলটি যাচ্ছে, আমি সেই দলের সঙ্গে ভ্যানরিকশায় চেপে বসলাম। ভ্যানরিকশা যাবে কি! একটু করে যায় আর থমকে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝেই বিশ-তিরিশ হাত করে রাস্তা ভেঙে নিয়ে গেছে জলের তোড়। ভ্যানরিকশা থেকে ওষুধের সমস্ত পেটি, বোঁচকা-টোচকা নামিয়ে সবাই মিলে হাতে-হাতে কোনও রকমে ভ্যানরিকশাটাকে তুলে আবার ভাল রাস্তায় নিয়ে যাই।
হঠাৎ কে যেন দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল, ‘দাদা, আপনারা যে ত্রাণ নিয়ে এসেছেন, সব কিন্তু আপনারাই দিয়ে যাবেন। বিলোবার জন্য এখানকার কারও হাতে দেবেন না। দিলে কিন্তু ওরা নিজেরাই সব নিয়ে নেবে।’
মাতৃসংঘ জনকল্যাণ আশ্রমের প্রশান্ত ঘোষ বললেন, ‘আয়লা আক্রান্তের পর এই নিয়ে আমরা তৃতীয় বার আসছি। এর আগের দু’বারই প্রচুর রোগী ফিরে গেছেন। আজ যাতে কেউ ফিরে না যান, তাই চটপট কাজ শুরু করতে চাই।’
যাওয়ার সময় বাঁ দিকে একটা বাড়ি দেখিয়ে ভ্যানচালক বললেন, ‘এটা আমাদের রাজবল্লভপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ’৮০ না ‘৮২ সালে তৈরি হয়েছিল। এখন পর্যন্ত কোনও ডাক্তার আসেনি। তিন জন নার্স। তাও সব সময় পাওয়া যায় না। ওই দেখুন, গাছটার পাতাগুলো কেমন খ্যার হয়ে গেছে।’
‘খ্যার মানে?’
উনি বললেন, ‘ভাল কইরা দ্যাহেন।’
দেখলাম, সত্যিই গাছটার পাতাগুলো একেবারে গাঢ় খয়েরি রঙের। ভ্যানচালক বললেন, ‘গাছটা মরে গেছে।’
‘মরে গেল কেন?’
উনি বললেন, ‘আইলার জন্য।’
‘পাশের গাছটা তো দিব্যি আছে।’ বলতেই, ভ্যানচালক বললেন, ‘ওটা মেহগিনি গাছ। তাই নোনা জলে কিছু হয়নি।’
রজনীকান্ত বাণী নিকেতন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেখলাম, গিজগিজ করছে লোক। বেশির ভাগই শিশু আর মহিলা। তখন মধ্যদুপুর। একজন স্বেচ্ছাসেবী প্যাকেট খুলে লাইনে দাঁড়ানো বাচ্চাদের হাতে বিস্কুট দেওয়া শুরু করতেই সব যেন হামলে পড়ল। আর একটা ওয়ারেসের জন্য সে কী কাকুতিমিনতি।
হরিপদবাবু বললেন, ‘হেঁটে গেলে পাঁচ মিনিটও লাগবে না। চলুন, আপনাকে বে অফ বেঙ্গলের বাঁধটা দেখিয়ে আনি। তা হলে বুঝতে পারবেন, ঝড়ের তাণ্ডব কী রকম ছিল। খবরের কাগজে যা বেরোয় আর টিভিতে যা দেখায়, ও সব দেখে এর এক শতাংশও আঁচ করতে পারবেন না।’
আমরা যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি পাশের জমিতে একটা গরু মরে পড়ে আছে। অথচ শরীরে কোনও বিকৃতি ঘটেনি। পচনও ধরেনি। উপরে কোনও চিল-শকুনও উড়ছে না। উনি বোধহয় আমার কৌতূহল আঁচ করতে পারলেন। তাই বললেন, ‘আইলার দিন সাগরের জল লবণ-পোড়া হয়ে গিয়েছিল তো, আর সেই লবণ-পোড়া জলে ডুবে এটা মারা গেছে দেখে পচেনি। আর এক টানা এত দিন নোনা জলে ডুবে ছিল বলে বোধহয় ভীষণ তিতকুটে হয়ে আছে। তাই চিল-শকুনও ছুঁচ্ছে না।’
বাঁধের কাছে গিয়ে দেখি, পাশের জমি থেকে মাটি কেটে বস্তায় ভরা হচ্ছে। দশখানা করে বস্তা একসঙ্গে জড়ো করে, জলের তোড়ে ভেঙে যাওয়া জায়গাগুলোতে জোড়াতালি দেওয়া হচ্ছে। কাজ করছে অন্তত শ’দুই লোক।
বিয়াল্লিশখানা করে থান ইট সিমেন্ট-বালি দিয়ে একসঙ্গে গেঁথে, তিন ফুট বাই আড়াই ফুট মাপের এক-একটা চাঁই বানিয়ে, সেগুলো দিয়ে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। ঢেউগুলো এত জোরে জোরে আছড়ে পড়েছিল যে, সেগুলো ভেঙে একদম ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। এক-একটা চাঁইয়ের ওজন প্রায় দেড়শো কিলো। সেগুলোকেও কত দূরে দূরে ছুড়ে ফেলেছে ঢেউ।
হরিপদবাবু বললেন, ‘এর আগে আরও আট-দশটা বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। শেষ বাঁধ ওই যে, ওইখানটায় বলে, আঙুল দিয়ে উনি যেখানটা দেখালেন, সেটার দূরত্ব কমপক্ষে পাঁচশো ফুট।
তিনি বললেন, ‘আমরা যেটায় দাঁড়িয়ে আছি, এটা ছেড়ে নতুন করে আর একটা বাঁধ দিতে গেলে, এই বাঁধ-বরাবর অন্তত পাঁচশো ফুট করে জমি ছেড়ে দিতে হবে। অথচ যাদের জমি, তারা কিন্তু কোনও ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন বা আর্থিক সাহায্য পাবে না। যার গেল তার গেলই।
‘তা হলে সে জমি ছাড়বে কেন?’
‘না ছেড়েই বা কী করবে? ছাড়লে, বাঁধ দেওয়ার জন্য তাও কিছুটা থাকবে। না ছাড়লে তো প্রতি বছর একটু একটু করে পুরোটাই যাবে। এ বার বাঁধ নিয়ে সরকারকে নতুন করে ভাবতে হবে। এমন কিছু দিয়ে, এমন পদ্ধতিতে বাঁধ দিতে হবে, যাতে এর চেয়ে ভয়াবহ দুর্যোগেও এ রকম ক্ষতি আর না হয়। তাতে যদি বেশি টাকা লাগে, তো লাগুক, তাও। ওই যে দেখুন, লুথিয়ান দ্বীপ। আর ওটা হচ্ছে জি-প্লট। আয়লায় সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওই দ্বীপটা। একেবারে লণ্ডভণ্ড। কিছু কিছু রিলিফ অবশ্য যাচ্ছে। যদিও সবার কাছে সব কিছু ঠিক মতো পৌঁছচ্ছে না। এই দ্বীপের মতোই, প্রশাসন থেকে যেগুলো আসছে, সেগুলো তাদের পেয়ারের লোকেরাই ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে নিচ্ছে আর বেসরকারি সংস্থা থেকে যেগুলো আসছে— জলপথে এলে, তারা নৌকো করে পাড়ে নেমেই সামনে যাদের পাচ্ছে, তাদের দিয়ে দিচ্ছে। আর সড়ক পথে এলে, তাদের ইচ্ছে মতো যে কোনও জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে, সামনে যাদের পাচ্ছে, তাদের দিয়ে দিচ্ছে। কেউ আর ভেতর দিকে যাচ্ছে না। ফলে, যারা গ্রামের ভেতর দিকে থাকে, তারা কিছুই পাচ্ছে না। এমনকী, ত্রাণ যে এসেছিল, সে খবরও তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছচ্ছে না। সবাই না পেলেও, কেউ কেউ অবশ্য পাচ্ছে। সদ্য ঘটেছে তো! কিন্তু এর পরে? আগামী তিন-চার বছর তো এখানে কোনও চাষবাসই হবে না। এখানকার মানুষদের কী করে চলবে? কী খাবে ওরা?’
স্থানীয় একজন বললেন, ‘এখন ঠাকুরের কাছে আমাদের একটাই প্রার্থনা, যাতে দু’-তিনটে খুব ভারী বর্ষা হয়। তা হলে হয়তো এই নোনা জলটা ধুয়ে চলে যাবে। না হলে যে কী হবে কে জানে!’
পাড়ে অতগুলো ছেলে বাঁধের কাজ করছে। অথচ বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই বছর বাইশ-তেইশের সানোয়ার বিবির। সে তার কোলের ছেলেটাকে বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে আসছে। একদম উদোম বুক। ‘কী রে, এখানে কী করছিস?’ হরিপদবাবু জিজ্ঞেস করতেই বউটি সাগরের দিকে তাকিয়ে বলল, টোকাটা খুঁজেটি। সাগর নিছে লা!’
তার ভাষা আমি ঠিক মতো বুঝতে না পারায় হরিপদবাবুর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, ‘ও বলছে, ছেলেটাকে খুঁজছি। সাগর নিয়েছে তো…’ একটু থেমে ফের বললেন, ‘ওর তিন বছরের ছেলেটা এ বার আয়লায় ডুবে মারা গেছে। এখানে একটা কথা খুব চালু আছে, সমুদ্র যা নেয়, তা ফিরিয়ে দেয়। ও ভেবেছে, ওর ছেলেকেও সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে। শুধু ফিরিয়ে দেবে না, একেবারে জলজ্যান্ত ফিরিয়ে দেবে। দিয়েছে কি না দেখতে এসেছে… বাচ্চা তো… একা একা বাড়ি চিনে যেতে পারবে না, তাই ও রোজই ছেলের জন্য একবার করে এখানে আসে।’
আমি তখন সাগরের বুকে ডলফিন খুঁজছি। কারণ আয়লা শব্দের অর্থ হল ডলফিন বা শুশুকজাতীয় জলচর প্রাণী। সেই প্রাণীর সঙ্গে নাম মিলিয়ে এই ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করেছেন মালদ্বীপের আবহাওয়াবিদেরা। মানে জাতিসংঘের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের আবহাওয়াবিদদের সংস্থা ‘ইউএন এস্কেপ’-এর বিজ্ঞানীরা। কিন্তু একটা ডলফিনও চোখে পড়ল না।
ফেরার সময় আবার সেই স্কুলবাড়িতে ঢুকলাম একজন বললেন, ‘পাঁচশো তেরো জন রোগী দেখা হয়ে গেছে। ব্রজবল্লভপুরেও রোগীর সংখ্যা চারশো ছুঁই ছুঁই। ডাক্তার অভিজিৎ মজুমদার বললেন, ‘এখানে যত রোগী দেখলাম, ঘুরে-ফিরে সেই একই রোগ। গ্যাস, অম্বল আর মাথা ব্যথা। এই মাথা ব্যথাটা আয়লার কোনও প্রভাব কি না, সেটা এখনই বলা যাবে না।’
হঠাৎ দেখি, স্কুলবাড়ির ওদিককার করিডরে একজন প্রৌঢ় ছটফট করছেন। তাঁকে ঘিরে কয়েক জন স্থানীয় লোক। আমি দেখছি দেখে ডাক্তারবাবু বললেন, ‘আমাদের কাছে যা ওষুধ ছিল, দিয়েছি। কিন্তু ওঁর মাথা ব্যথা কমছে না। অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করছেন।’
যখন ফিরছি চারটে বেজে গেছে। স্কুলবাড়ি ছেড়ে ভ্যানরিকশায় উঠতেই শুনতে পেলাম, অদ্ভুত এক যন্ত্রসংগীত। মাথার উপরে তাকিয়ে দেখি অন্ধকার। না, কালো মেঘ নয়। ঝাঁক ঝাঁক মশা। হঠাৎ শুনি মোবাইল বাজছে। নম্বর দেখেই বুঝতে পারলাম, ও প্রান্তে গ্যারিদা। আমাদের উড়ালপুল পত্রিকার প্রধান সম্পাদক গ্যারিদা, মানে গৌতম দত্ত। আমেরিকার ডালাস থেকে। উনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কোথায়?’
আমি বললাম, আমি এখন সুন্দরবনের একটা দ্বীপে। রাক্ষসখালিতে।
উনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বললেন, ‘কী করছ? রাক্ষস দেখছ?’
আমি বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না— না গ্যারিদা, রাক্ষস নয়, রাক্ষসের তাণ্ডবলীলা দেখছি।#