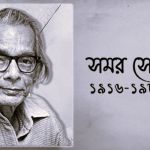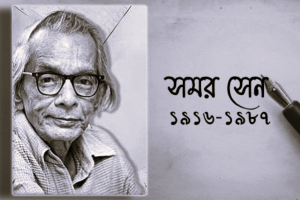একটা আধুনিক শহরের সমস্ত কদর্যতাকে সঙ্গে নিয়েই নগর কলকাতার ক্রমবিকাশ হয়েছিল, আর বৃটিশ শাসনের হাত ধরেই এদেশে বারাঙ্গনাবৃত্তির উদ্ভব ঘটেছিল। ইতিহাস বলে যে, পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই কলকাতার নগরায়ন শুরু হয়েছিল। তখন কোন সংবাদপত্র তো দূরের কথা, ছাপার যন্ত্রের কথাও মানুষের কল্পনায় ছিল না। শৈশবের কলকাতায় লোকসংখ্যাই বা কত ছিল? ১৭১০ সালে কলকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি নামের যে তিনটি গণ্ডগ্রাম নিয়ে কলকাতা নগরী ছিল— সাকুল্যে সেটির লোকসংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। ১৭৪০-৫০ সময়কালে বাংলার গ্রামে গ্রামে মারাঠা বর্গী হামলার ফলে আতঙ্কিত বহু মানুষ নিরাপত্তার জন্য কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। এরপর থেকে ব্যবসা-বানিজ্য ও নানাকারণে কলকাতার লোকসংখ্যা ক্রমে বাড়তে শুরু করেছিল। দেখতে দেখতে কলকাতা নিজের গ্রামীণরূপ থেকে শহরে পরিণত হয়েছিল। ১৭৫২ সালে হলওয়েল সাহেবের হিসেব মত কলকাতার লোকসংখ্যা প্রায় চার লক্ষ ন’হাজারের কাছাকাছি ছিল।
কলকাতায় বিচারালয় স্থাপনের পরে উইলিয়াম হিকি অ্যাটর্নি হয়ে কলকাতা শহরে পদার্পণ করেছিলেন। ১৭৭৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে শুরু করে ১৮০৮ পর্যন্ত তিনি কলকাতায় ছিলেন। এরপরে লণ্ডনে ফিরে যাওয়ার পরে তিনি চারখণ্ডে তাঁর যে স্মৃতিকথা (১৭৪৯-১৮০৯) লিখেছিলেন, সেটি শৈশবের কলকাতার সামাজিক ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল হিসাবে স্বীকৃত। সেই স্মৃতিকথায় হিকি— মিস ডানডাস — নামের তৎকালীন কলকাতা শহরের একজন বহুজন পরিচিতা বারাঙ্গনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। আধুনিকযুগে কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে বারাঙ্গনা বৃত্তির সূচনা যে ইংরেজ আমলেই হয়েছিল, সেবিষয়ে কোনও সংশয় নেই। হিকি তাঁর স্মৃতিকথায় যে সময়কার কলকাতার কথা বলেছিলেন, একটা নগর হিসেবে কলকাতার তখন নিতান্তই শৈশবকাল ছিল। কলকাতার নগরায়ন তখন সবে ক্ষীণ গতিতে শুরু হয়েছিল। সেই সময়ে কোম্পানির কাজকর্ম চালানোর জন্য ইংরেজ ভাগ্যান্বেষীরা তাঁদের নতুন উপনিবেশে আসতে শুরু করেছিলেন। কলকাতার সেই শৈশবে নিজেদের ভাগ্যান্বেষণে যেসব ইংরাজরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই অস্তগামী মধ্যযুগের উচ্ছিষ্টতুল্য প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও উছৃঙ্খল ছিলেন। তৎকালীন ইংরেজ শাসনের প্রসাদলোভী বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দিরা তাঁদের দোসর হয়েছিলেন। পালকি আর গোরুর গাড়ির যুগের সেই কলকাতায় দেশীয় খবরের কাগজ তো দূরের কথা, ছাপার অক্ষরেরও তখনও পর্যন্ত উদ্ভাবন হয়নি। কিন্তু বারবণিতা বৃত্তির প্রসার বেশ ভালোভাবেই হয়ে গিয়েছিল। ১৭৯৫ সালে রুশ যুবক হেরাসিম লেবেদফ যখন কলকাতায় অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে প্রথম বাংলা থিয়েটারের সূচনা করেছিলেন, তখন সেই নাটকের নারী চরিত্রগুলিতে অভিনয় করবার জন্য তিনি বারবণিতা পল্লীর নারীদের নিয়োগ করেছিলেন। অর্থাৎ— ১৭৯৫ সালের অনেক আগে থেকেই কলকাতায় বারাঙ্গনা পল্লীর অস্তিত্ব ছিল। তবে তখন শুধু কলকাতা নয়, তৎকালীন বাংলার অন্যান্য সমৃদ্ধ শহরগুলি, যেখানে ইংরেজরা নিজেদের কোর্ট-কাছারি ও দপ্তর খুলে বসেছিলেন, সেখানেই সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে বারাঙ্গনা পল্লী গড়ে উঠেছিল। অতীতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা) আত্মচরিত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কৃষ্ণনগরের সমকালীন সামাজিক অবস্থার কথা বর্ণনা করেছিলেন। তাতে দেখা যায় যে, এই প্রসঙ্গে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র লিখেছিলেন—
“পূর্বে কৃষ্ণনগরের কেবল আমিনবাজারে পতিতালয় ছিলো, গোয়াড়ীতে গোপ, মালো প্রভৃতি জাতির বাস ছিলো। পরে ইংরেজরা যখন এখানে বিচারালয় ইত্যাদি স্থাপন করেন, তখন গোয়াড়ীর পরিবর্তন হইতে থাকে।”
এরপরে তিনি আরো লিখেছিলেন—
“বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে প্রায় সকল আমলা, উকিল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাঁহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল।”
এই কারণেই আজও উত্তর কলকাতার প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত লোকবসতি কেন্দ্রের আশেপাশেই প্রাচীন গণিকাপল্লীগুলির অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়।
১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার গ্রাম-সমাজের কাঠামোটাকে ভেঙ্গে দিয়েছিল। তখন সূর্যাস্ত আইনের প্যাঁচে পড়ে বাংলার বনেদি জমিদারেরা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন, এবং ইংরেজদের আরও বেশি রাজস্ব দেওয়ার অঙ্গীকার করে নিলামে সেইসব জমিদারিগুলি কিনে নিয়ে ভূমির সাথে সম্পর্কহীন একটি অর্থলোলুপ মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। তখন দুর্নীতিগ্রস্ত ও উছৃঙ্খল ইংরেজ এবং শিকড়হীন সেই নতুন মধ্যশ্রেণীটির পৃষ্ঠপোষকতায় এক কুৎসিত সংস্কৃতি জন্ম নিয়েছিল, যেটাকে ইতিহাসে ‘বাবু কালচার’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। সেই সময়েই ইংরেজদের দালালি করা একটি লোভী, দুর্নীতিপরায়ন ও অলস নাগরিক সমাজ গড়ে উঠেছিল। খৃষ্টীয় আঠেরো শতকের কলকাতা মূলতঃ এদেশীয় দালাল, মুৎসুদ্দি ও বেনিয়াদের কলকাতা আর ঊনিশ শতকের কলকাতা মূলতঃ ‘বাবু সংস্কৃতির’ কলকাতা ছিল। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থে সেই সময়কার কলকাতার সেই বাবুসমাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন—
“ইহাদের বহিরাকৃতি কি কিছু বর্ণনা করিব? মুখে, ভ্রুপার্শ্বে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্ন স্বরূপ কালিমারেখা। শিরে তরঙ্গায়িত বাবরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে কালোপেড়ে ধুতি। অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনোট করা উড়ানী এবং পায়ে পুরু বাগলস সমন্বিত চিনাবাড়ির জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া বুলবুলের লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাফ আখড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত এবং খড়দহের মেলা, মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময় কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিয়া থাকিত।”
ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, সমগ্র ঊনিশ শতকে জুড়ে ইংরেজের শাসন-সহায়ক কদর্য বাবু সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার বারাঙ্গনাপল্লীগুলো ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। সেযুগের কলকাতার নাগরিক সমাজ শুধু রক্ষিতা পোষণ ও বারাঙ্গনাগমনকে অনুমোদনই করেনি, এইসব বেলেল্লাপনা সেই সমাজের মর্যাদার সূচকও হয়ে উঠেছিল।
ইংরেজদের নতুন ভুমিব্যবস্থা বাংলার গ্রাম্য সমাজকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়েছিল। ফলে নিজেদের বংশানুক্রমিক পেশা ও বৃত্তি থেকে উৎখাত হয়ে চোর ডাকাতের দলের যেমন সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাঁরা শহরে আশ্রয় নিয়েছিল, ঠিক তেমনই দারিদ্রের তাড়নায় গ্রামের নারীরা শহরের বারাঙ্গনা পল্লীগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৮৭২ সালের সরকারি নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বারবনিতারা অধিকাংশই— তাঁতি, তেলি, জেলে, কৈবর্ত, ময়রা, চামার, কামার, কুমোর, যুগী, গয়লা, নাপিত, মালি, বেদে —ইত্যাদি জাতির নারী ছিলেন। (অন্য কলকাতা, বিশ্বনাথ জোয়ারদার) সেই সময়ে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বারবনিতাদের সংখ্যা যে কিরকম লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেযুগের সরকারি নথি থেকে এই তথ্য জানতে পারা যায়। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৮৬৭ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের হিসাব মত তিন হাজার নারী তখন এই বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮০ সালের একটি হিসেব অনুযায়ী কলকাতা শহরে বারবনিতার সংখ্যা যেখানে সাত হাজার ছিল, ১৮৯৩ সালে সেই সংখ্যাটা একলাফে বেড়ে ২০,১১৬ জন হয়ে গিয়েছিল। (অন্য কলকাতা, বিশ্বনাথ জোয়ারদার)
বাবু কলকাতার সেই কদর্য বেলেল্লাপনার ছবি এখন কল্পনাতেও আনা সম্ভব নয়। তৎকালীন কলকাতা শহরের যত্রতত্র বারাঙ্গনাপল্লী গজিয়ে উঠেছিল। এমনকি সম্ভ্রান্ত এলাকা বা বিদ্যালয়ের আশেপাশের জায়গাও বাদ পড়েনি। যেহেতু সেযুগের বিত্তশালী বাবুদের প্রশ্রয়েই সেইসব বারাঙ্গনাপল্লী গজিয়ে উঠেছিল, তাই সেগুলোর বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা প্রশাসনের সাধ্যের মধ্যে ছিল না। ইংরেজ রাজকর্মচারীরা সেইসব বাবুদের আদর্শ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীপান্থ তাঁর ‘কলকাতা’ গ্রন্থের ‘রোটি আউর বেটি’ প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন—
“সতীদাহ কলকাতায় তখন প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। সারা ব্ল্যাক টাউন চিতার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, অন্ধকার। সেই অন্ধকারে চলছে বাবু বিলাস, গুরু-প্রসাদী কৌলীন্য রক্ষা। সতীর আর্তনাদে, বিধবার কান্না আর বারবনিতার কাতর আহ্বানে অষ্টাদশ শতকের কলকাতা প্রেতপুরী। পা যেন লজ্জায় জড়িয়ে আসে সেদিকে বাড়াতে।”
তৎকালীন সমাজের শুধু নিম্নবর্গের নারীরাই নন, কুলীন ঘরের বহু নারীও তখন অবস্থার দুর্বিপাকে পড়ে বারাঙ্গনাপল্লীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সমকালীন সরকারি প্রতিবেদনে একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল যে, হিন্দু বিধবাদের বারাঙ্গনাপল্লীতে আশ্রয় নেওয়াই সেই সময়ে বারাঙ্গনাদের সংখ্যা বৃদ্ধির একটা কারণ ছিল। তখনও পর্যন্ত বিধবাবিবাহ প্রথা চালু না হওয়ার ফলে বারাঙ্গনা পল্লীগুলিই পুরুষের লালসার শিকার হওয়া বিধবা তরুণীদের শেষ আশ্রয় হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে সেযুগের একটি সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল—
“হিন্দুর বিবাহ-বিচ্ছেদ নেই, বিধবা হলে হয় পবিত্র হও, নচেৎ বেশ্যা হও।”
সেই সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী, তখনকার কলকাতার বারঙ্গনাপল্লীতে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু বিধবারা মূলতঃ হুগলি, বর্ধমান, হাওড়া, চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা থেকে সেখানে প্রবেশ করতেন। এছাড়া সেযুগের তরুণী বিধবারা বাবুদের লালসার শিকার হয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়লে তাঁরাও শেষপর্যন্ত বেশ্যালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতেন। আবার এমন তথ্যও পাওয়া গিয়েছিল যেখানে দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ, ইত্যাদি কারণে মা ও মেয়ে উভয়েই গণিকাপল্লীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাছাড়া তখন নিজেদের মুহূর্তের ভুলে অন্তঃস্বত্ত্বা নারীরা আত্মহত্যা না করে বেশ্যালয়ে আশ্রয় নিয়ে যেমন নিজেদের বাঁচবার উপায় খুঁজেছিলেন, তেমনি আবার বহুবিবাহের শিকার নারীরা প্রেমিকের হাত ধরে কুলত্যাগিনী হয়ে অবশেষে বারাঙ্গনাপল্লীতে গিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। অতীতে গবেষক অধ্যাপক বিজিতকুমার দত্ত সেকালের সরকারি দস্তাবেজ থেকে এবিষয়ে তথ্য উদ্ধার করে লিখেছিলেন—
“সরকারী মহাফেজখানা থেকে যে রিপোর্ট পেয়েছি তা কৌতূহলোদ্দীপক। দেখা যায় দশ বছরের নিচে বেশ্যাদের বাড়িতে বেশ কিছু মেয়ে রয়েছে। সরকার এঁদের কথা মাঝে মাঝে ভেবেছে। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা এত ব্যাপক যে সরকারের পক্ষে কিছু করে ওঠা কঠিন।”
এই হিসাব মত, ঊনিশ শতকের শেষেরদিকে কলকাতার গণিকাপল্লীগুলিতে বারাঙ্গনা গর্ভজাত কন্যাসন্তানের সংখ্যা ছিল ৪০৮ জন। সেইসব বারাঙ্গনা কন্যাদের পুনর্বাসন বা সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার ব্যাপারে তৎকালীন ইংরেজ সরকার যেমন কিছু করতে পারেনি, তেমনই এবিষয়ে সেযুগের সমাজ সংস্কারকদেরও কোনও হেলদোল ছিল বলে ইতিহাস থেকে তথ্য পাওয়া যায় না। শেষপর্যন্ত তাঁরা নিজেরাই নিজেদের মুক্তির পথ বেছে নিয়েছিলেন। থিয়েটার তাঁদের সেই মুক্তির পথ দেখিয়েছিল, আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বারাঙ্গনা কন্যাদের থিয়েটারে নিযুক্তির পথ খুলে দিয়েছিলেন।
বাংলা থিয়েটারের তখন সবে শৈশবকাল ছিল। ১৮৭২ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে কলকাতায় ন্যাশানাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই সাধারণ মানুষের জন্য রঙ্গালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সেযুগের কলকাতার ধনকুবের আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ ‘বেঙ্গল থিয়েটার’ নাম দিয়ে একটি থিয়েটার খুলেছিলেন এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তকে তাঁদের থিয়েটারের জন্য দুটি নাটক লিখে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। মধুসূদন যে শর্তে সেই কাজটি করতে সম্মত হয়েছিলেন, সেটা ছিল যে, তাঁর নাটকের স্ত্রী চরিত্রের রূপায়ণ মেয়েদের দিয়েই করাতে হবে। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী থিয়েটার সম্পর্কে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তখন ভালোভাবে থিয়েটার পরিচালনা করবার জন্য বেঙ্গল থিয়েটার একটি উপদেষ্টা সমিতি গঠন করেছিল। সেই উপদেষ্টা মণ্ডলীতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিলেন। সেই মণ্ডলীর থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়োগ সংক্রান্ত একটি জরুরি সভায় বিদ্যাসাগর থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়োগের বিরোধিতা করলেও উমেশচন্দ্র দত্ত ও মধুসূদনের সমর্থন পেয়ে বেঙ্গল থিয়েটার কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরের মত মানুষের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করেই কলকাতার বারাঙ্গনাপল্লী থেকে চারজন অভিনেত্রীকে মঞ্চে অভিনয় করবার জন্য নিয়োগ করেছিলেন। এরপরে ১৮৭৩ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখে মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটক দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটার নিজের যাত্রা শুরু করেছিল। তবে মাইকেল অবশ্য সেই দিনটিকে দেখে যেতে পারেননি, কারণ এর আগেই, ১৮৭৩ সালের ২৯শে জুন তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।
তবে মেয়েদের জন্য থিয়েটারের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে অন্ধকার জগতের নারীরা মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকবার একটা অবলম্বন পেয়েছিলেন। এর পিছনে তাঁদের একটা তাগিদ ছিল– মুক্তির তাগিদ। থিয়েটারকে তাই তাঁরা নিজেদের মুক্তিতীর্থ বলে মনে করেছিলেন। এরপরে সেই পথ ধরেই গোলাপসুন্দরী, বিনোদিনী, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, নীহারবালা, কৃষ্ণভামিনী প্রভাদেবীরা থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ নাট্যাভিনয়ে তাঁদের যোগদানের কারণেই বাংলা থিয়েটার নিজের শৈশবকে কাটিয়ে পুরোমাত্রায় পেশাদারী হয়ে ওঠবার দিকে পা বাড়িয়েছিল। ইতিহাস হলে যে, অন্ধকার জগৎ থেকে উঠে আসা সেইসব মহিলারাই পরবর্তী সত্তর/আশি বছর ধরে বাংলা থিয়েটারকে আলোকিত ও সমৃদ্ধ করেছিলেন। থিয়েটারের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিতৃপরিচয়হীনা বারাঙ্গনা কন্যারা ক্লেদাক্ত অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরবার সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। সেদিনের সমাজ যে সেবিষয়ে তাঁদের সঙ্গ দিয়েছিল— তা কিন্তু নয়। বস্তুতঃ সেটা প্রবল শক্তিধর সমাজের সঙ্গে তাঁদের একটা অসম লড়াই ছিল। তবে সেকালের সংবাদপত্র ও সমাজপতিদের লাগাতার বিরোধিতা ও নিন্দাবাদ সত্ত্বেও থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত কিছু মানুষ তাঁদের অলোয় ফেরবার সংগ্রামে সঙ্গ দিয়েছিলেন। তখন যাঁরা সেইসব নষ্টকন্যাদের মঞ্চাভিনয়ের বিরোধিতা করেছিলেন, সেইসব সমাজপতিদের উদ্দেশ্য করে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন—
“এইসব মেয়েদের তো আমি অন্ততঃ রাস্তায় দাঁড়িয়ে খরিদ্দার পাকড়াবার চেষ্টা থেকে সরিয়ে, মঞ্চে তুলে দিয়ে রোজগারের একটা পথ দেখিয়েছি, কিন্তু তোমরা এদের জন্য কি করেছো?”
পঙ্কজা থেকে মহীয়সী হয়ে ওঠা সেইসব বারাঙ্গনাকন্যাদের অনেকেই বাঙালির বিনোদন শিল্পে তো বটেই, সাহিত্যে ও এবং সামাজিক ইতিহাসেও নিজেদের অতুলনীয় কীর্তি রেখে গিয়েছেন। কিন্তু সমাজ কখনও সেইসব নারীদের প্রাপ্য মর্যাদা দেয়নি, এমনকি আজও দিতে চায় না।
কেমন করে তৎকালীন সমাজের গভীর অন্ধকার স্তর থেকে উঠে আসা এক অসহায়া নারী— বিনোদিনী —তাঁর তন্ময় সাধনায় দুরূহ সিদ্ধি আয়ত্ব করেছিলেন, একটি স্থায়ী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং খ্যাতির শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেও শেষে বঞ্চনার শিকার হয়ে মাত্র তেইশ বছর বয়সে নীরবে মঞ্চের অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন— সেসব কথা চিন্তা করলে এখন বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। রঙ্গালয়ের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক ত্যাগের ছাব্বিশ বছর পরে, ৪৯ বছর বয়সে, বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনী— ‘আমার কথা’ —গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন। তবে এর আগে এবং পরেও বিনোদিনীর লেখনিচর্চা অব্যাহত ছিল। এর আগে তিনি— ‘বাসনা’ এবং ‘কনক ও নলিনী’ —নামের দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রথম পতিতা মহিলা আত্মজীবনী লেখিকার মর্যাদা, কিংবা দুটি কাব্যগ্রন্থের লেখিকার মর্যাদা বিনোদিনী পাননি। কারণ তিনি যে বারারাঙ্গনা কুলোদ্ভবা ছিলেন! সেকালের একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষ শিশুকন্যা সহ বিনোদিনীকে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন; কিন্তু তৎকালীন সমাজের মানী লোকেরা, যাঁরা একটাসময়ে তাঁর অভিনয় দেখাবার জন্য রাতের পর রাত প্রেক্ষাগৃহে ছুটে যেতেন, তাঁর অভিনয় দেখে তাঁকে ধন্যধন্য করতেন— সেই তাঁরাই বিনোদিনীর কন্যাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন। ফলে বিনোদিনী তাঁর কন্যা শকুন্তলাকে কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে পারেননি। বিনোদিনী শকুন্তলাকে বাঁচাতে পারেননি, মাত্র তেরো বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।
তবে বিনোদিনী যেটা পারেননি, গোলাপসুন্দরী সেটা করতে পেরেছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের নাট্যপরিচালক উপেন্দ্রনাথ দাস সেই থিয়েটারেরই একজন অভিনেতা— গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে গোলাপের বিবাহ দিয়েছিলেন। বিবাহের পরে তাঁরা একটি ভদ্রপল্লীতে নিজেদের বাসা বেঁধেছিলেন। কিন্তু একটি কন্যার জন্মের পরেই গোলাপ স্বামী পরিত্যক্তা হয়েছিলেন। গোলাপ ততদিনে সুকুমারী দত্ত হয়ে গিয়েছিলেন। মেয়েকে মানুষ করবার জন্য গোলাপ থিয়েটারও ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে স্বামী পরিত্যক্তা হয়েও সুকুমারী কিন্তু থেমে থাকেননি। গোষ্ঠবিহারী তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার ফলে তিনি নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়েছিলেন। এরপরে মেয়েদের নাচ ও অভিনয় শেখাবার জন্য একটা স্কুল খুলে তিনি ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেও সেই স্কুলটি বেশিদিন চালাতে পারেননি। তারপরে ন্যাশনাল ফিমেল থিয়েটারের উদ্যোগে তিনি শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য নাটক লিখেছিলেন। ইতিমধ্যে সেকালের একজন সহৃদয় মানুষ, নবভারত পত্রিকার সম্পাদক বাবু দেবপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সুকুমারীর কন্যার শিক্ষা ও প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তখন নিজের অর্থকষ্ট সামাল দেওয়ার জন্য সুকুমারী নাট্যরচনায় মন দিয়েছিলেন, এবং নিজের ব্যক্তিজীবন ও নাট্যজীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা উজাড় করে দিয়ে ‘অপূর্ব সতী’ নামের একটি নাটক রচনা করেছিলেন। ওই নাটকটি তখন অভিনীতও হয়েছিল। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস সুকুমারীকেই প্রথম মহিলা নাট্যকারের স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়েছে। তিনি নিজের মেয়েকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেযুগের একটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে প্রচুর অর্থব্যয় করে তাঁর বিবাহও দিয়েছিলেন; কিন্তু মেয়েকে দেখাবার জন্য তাঁর শ্বশুরগৃহে প্রবেশের অধিকার তাঁকে চিরকালের মত ত্যাগ করতে হয়েছিল।
অন্যদিকে অভিনেত্রী কৃষ্ণভামিনী নিজের মৃত্যুর আগে তাঁর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ও সম্পত্তি উইল করে শিক্ষাবিস্তারের কাজে ও দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসার কাজে দান করে গিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল যে, কৃষ্ণভামিনীরা ইতিহাস নির্মাণ করলেও ঐতিহাসিকের সম্মান অর্জন করতে পারেন না! বিনোদিনী তাঁর আত্মকথায় লিখেছিলেন— ‘নারীর নিস্তার নাই টলিলে চরণ’। বর্তমানের সমাজ আগের থেকে অনেক আলোকপ্রাপ্ত হলেও মনে এই সংশয়টা কিন্তু থেকে যায় যে, বিনোদিনীর এই কথাটা কি আজও পুরোপুরি মিথ্যা হতে পেরেছে?#