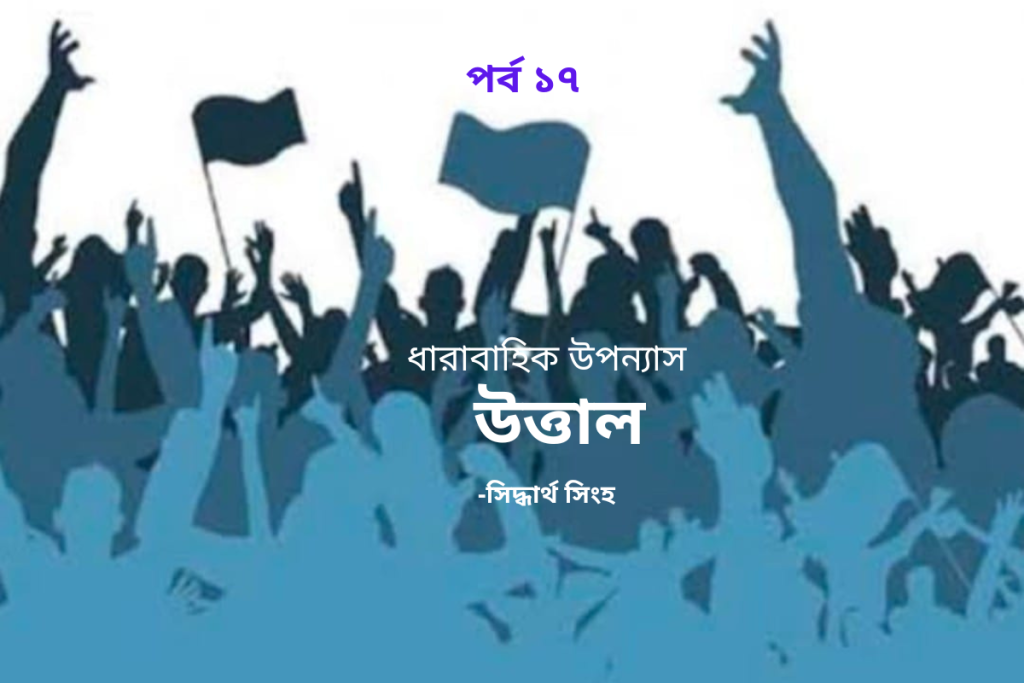।।পর্ব- সতেরো।।
সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসেছিল জ্যোতি বসুর সরকার। আসার কিছু দিন পরেই তারা বলেছিল, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের আমরা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু সত্যিই কি ছেড়ে দিয়েছে? এটা হয়তো কারও কারও মনে হয়েছিল। কারণ, যাঁরা বন্দি ছিলেন, তাঁরা কেউই বাক্ চাতুর্যে এবং জনমোহিনী আকর্ষণে কারও চেয়ে একচুলও কম ছিলেন না। তাঁদের ছাড়লে নিজেদের গদি টালমাটাল হতে পারে, এমন একটা আশঙ্কা ছিলই। ফলে তাঁরা নিশ্চয়ই সাধ করে খাল কেটে কুমির আনবেন না। এটা বুঝতে পেরে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো গোছের কিছু ছেলের কী মনে হয়েছিল কে জানে, তারা খোঁজখবর নিতে শুরু করেছিল। এবং তারা জেনেছিল, নকশাল নেতা আজিজুল হক-সহ বেশ কয়েক জন প্রথম শ্রেণির নেতাকে শর্তসাপেক্ষে বা সমঝোতার মাধ্যমে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ঠিকই, তবে তার সঙ্গে তাঁদের এও বলে দেওয়া হয়েছে যে, কংগ্রেস আমলে তাঁরা যা করেছেন, সেটা যেন ভুল করেও আর কখনও করতে না যান। নকশাল আদর্শে ঘেঁষা আজকাল পত্রিকায় তাঁরা যত খুশি যা-ই লিখুন না কেন, মাথা চাড়া দিয়ে যেন ওঠার চেষ্টা না করেন। ওদের দেওয়া শর্ত যাতে তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন, সে জন্য তাঁদের নানা রকম উপঢৌকন ও টোপও দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে যেমন ছিল সরকারি আবাসান, ছিল মাসিক ভাতা। ছিল টেলিফোনের বিলও।
যখন এই ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, তখন কিন্তু বাজারে মোবাইল আসেনি। এই কলকাতা শহরেই ক’জনের বাড়িতে ফোন ছিল, বলা মুশকিল। সামর্থ্য থাকলেও ফোনের জন্য আবেদন করে বসে থাকতে হত বছরের পর বছর। কত লোক যে চাকরিতে জয়েন করার সঙ্গে সঙ্গে আবেদন করেও তাঁর জীবদ্দশায় ফোন দেখে যেতে পারেননি, তার ইয়ত্তা নেই। আর সেই ফোন একবার ডেথ হয়ে গেলে তো কথাই নেই। চটির সুখতলা ক্ষয়ে যেত সেটা ঠিক করানোর জন্য। ফলে যাঁরা সারাতেন তাঁদের তখন পোয়াবারো। সে সময় তাঁদের সঙ্গে নাকি কেউ কেউ মাসিক চুক্তি পর্যন্ত করে রাখতেন, যাতে তাঁদের ফোনটা সচল থাকে।
একবার টেলিফোন-কর্মীদের নানা রকম দাবিদাওয়া নিয়ে কী একটা আন্দোলনের জেরে টেলিফোন পরিষেবা পুরো ভেঙে পড়েছিল। তখন ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা মিলে একটা সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এবং তাঁরা তিতিবিরক্ত হয়ে টেলিফোন ভবনের কর্তৃপক্ষকে অস্বস্তিতে ফেলার জন্য একবার কালো কুচকুচে একটি ফোনকে খাটিয়ায় শুইয়ে শববাহীর মতো কাঁধে নিয়ে মিছিল করেছিলেন। টেলিফোন ভবনের সামনে দীর্ঘক্ষণ ধরনায় বসেছিলেন। সেখানে টেলিফোনের মৃত্যুতে তাঁরা দু’মিনিট নিরাবতাও পালন করেছিলেন। শেষে রীতিমত পুরুতমশাই এনে শ্রাদ্ধশান্তিও করেন। তার পর গর্ত খুঁড়ে ওই ফোনটাকে কবর দিয়ে তাঁরা একটি স্মৃতিসৌধও বানিয়ে দেন। জানি না, সেটা এখনও আছে কি না।
সেই সময় একটা ফোন বিনে পয়সায় পাওয়া এবং তার সঙ্গে প্রতি মাসে ফোনের বিল, সে তো সাত রাজার ধন মানিক পাওয়ার মতোই। সরকার সেটা দিত। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও।
যাঁরা নতুন কিছু করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, চেষ্টা করেছিলেন এই পচা-গলা সমাজ ব্যবস্থাটাকে আমূল পালটে দেওয়ার, তাঁরা পারুন ছাই না পারুন, দেশের জন্য তো কিছু একটা করতে চেয়েছিলেন। সেটা প্রশাসনের পছন্দ হোক বা না হোক। তাঁরা যখন সেই আদর্শের জন্য রাজনৈতিক শিকার হয়েছিলেন, বছরের পর বছর জেল খেটেছিলেন, ছাড়া পাওয়ার পর তাঁরা যখন সরকারি তত্ত্বাবধানেই কিছু পাচ্ছেন, সেটা তো খুব ভাল কথা। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একই অপরাধে বন্দি হওয়া নিচুতলার অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিদের কী হল?
আরও পড়ুন: মাই নেম ইজ গহরজান
খতিয়ে দেখতেই বোঝা গেল, যাঁরা এখনও বন্দি, তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন কারখানার খেটে খাওয়া শ্রমিক কিংবা দু’পাতা পড়তে শেখা কৃষক। তাঁদের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তাঁদের বাড়ির লোকজনেরা ছেলেদের ছাড়াবার জন্য আদালত আর জেলখানার মধ্যে পিংপং বলের মতো বারবার মার খেতে খেতে, ঘটি-বাটি বেচে, সর্বস্ব খুইয়ে, তত দিনে দেউলিয়া হয়ে গেছেন। আন্দোলন করার পরিণাম যে কত ভয়ানক হতে পারে, তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। তাঁদের শিড়দাঁড়া ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ফলে তাঁদের পাশে যে দাঁড়াবার মতো সে-রকম কেউ নেই, এটা বুঝতে পেরে, সেই সব সহায়-সম্বলহীন অবাঞ্ছিত বন্দির কথা বেমালুম ভুলে গেছেন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিরাও।
ওই সব বন্দিদের যে পরিবারগুলো চাষবাস করে খেতেন, যাঁদের একমাত্র সম্বল ছিল জমি, সেটাও বেচে দিয়ে সেই পরিবারগুলো ইতিমধ্যেই ভূমিহীন হয়ে অন্যের জমিতে জন খাটতে শুরু করে দিয়েছেন। ছেলেকে জেল থেকে ছাড়ানোর জন্য লড়াই করতে করতে অনেক আগেই যাঁদের দাঁত-নখ খসে পড়েছে। খাদের একদম কিনারে ঠেসে ধরলেও, ফুঁসে ওঠা তো কোন ছাড়, চোখে চোখ রেখে যাঁদের তাকাবারও ক্ষমতা নেই, তাঁদের পরিবারের কাউকে মুক্তি দেওয়া তো দূরের কথা, উলটে তাঁদের ঘাড়ে মামলা চাপিয়ে দিয়েছে সরকার। যাতে তাঁদের আমলে ফের আর একটা আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ওঠার সামান্যতম সম্ভাবনাও না থাকে। তাই কারও কারও মনে প্রশ্ন উঁকি দিল, তা হলে কি আজিজুলদের মতো দেওয়া টোপ ওঁরা গেলেনি? নাকি অন্য কিছু?
এই জিজ্ঞাস্য নিয়েই নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে পথে নেমেছিল বিজল্প-র ছেলেরা। বিজল্প একটি ছোট্ট লিটিল ম্যাগাজিন। তাঁরা তখন এই নিয়ে একটি সংখ্যাও প্রকাশ করেছিল। আর সে জন্যই তাঁদের গায়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছিল নকশালের তকমা।
আবার এত দিন পরে সেই বিজল্পের ছেলেরাই আঁধারগ্রামের কথা শুনে প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। কবি জয় গোস্বামী লিখলেন, ‘শাসকের প্রতি’ নামে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি কবিতা। কবিতা, না তাঁর বুকের গভীর থেকে উঠে আসা প্রতিবাদ, কেউ বলতে পারল না। ‘তারা বাংলা’ চ্যানেলের অনুরোধে, সেটা পাঠ করলেন তিনি। বহুল প্রচলিত চ্যানেল না হলেও, যাঁরা শুনলেন, তাঁদের মুখে মুখে সেই কবিতা রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ল জনসাধারণের মধ্যে। এবং সেটাই মানুষের কাছে প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠল।
চুপচাপ বসে রইলেন না কেউই। শাঁওলী মিত্রের পঞ্চম বৈদিক তখন মঞ্চস্থ করছিল অস্কার ওয়াইল্ডের অ্যানিম্যাল ফার্ম-এর বাংলা রূপান্তর ‘পশুখামার’ নাটকটি। জয়ের কবিতাটা তাঁদের এতটাই নাড়া দিয়েছিল যে, তাঁরা ওই কবিতাটির একটি বড় ফ্লেক্স করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন প্রেক্ষাগৃহের সামনে। তাতে সই করতে শুরু করেছিলেন নাট্যকর্মী থেকে শুরু করে নাটক দেখতে আসা দর্শকেরা পর্যন্ত। যেতে যেতে পথচলতি লোকেরাও স্বাক্ষর করেছিলেন কি না এখন আর বলা যাবে না।
সে দিনই বোঝা গেল, টিভি-র বোকাবাক্স মানুষকে এখন গৃহবন্দি করে ফেললেও, যে দেশে বাংলা প্রতিবাদী থিয়েটারের শুরু দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীল দর্পণ’ নাটক দিয়ে, গ্রুপ থিয়েটারের জয়যাত্রা শুরু বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ দিয়ে, সে দেশের নাট্যকর্মীরাই পারেন যে কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদে মানুষকে সংগঠিত করতে। যে কোনও আন্দোলনের বীজকে মহীরুহে পরিণত করতে। পারলেনও তাঁরা।
ওঁরাই তিন ডিসেম্বর মঞ্চস্থ করলেন ‘রাজনৈতিক হত্যা’। আর তার সাত দিনের মাথায় আবার অনুষ্ঠিত হল ‘পশুখামার’। সে দিন আঁধারগ্রাম নিয়ে একটি কোলাজও দেখালেন তাঁরা এবং শো শেষ হয়ে যাওয়ার পরে কয়েকটি প্রশ্ন-সমেত একটি খোলা চিঠি, রাজনৈতিক ভাষায় যাকে লিফলেটও বলা যেতে পারে, সেটা তাঁরা হাতে হাতে বিলি করলেন দর্শকদের মধ্যে। সংগ্রহ করা শুরু করলেন সই। সে দিন এত লোকজনের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পেয়েছিলেন যে, সে দিন রাতেই তাঁরা ঠিক করলেন, সমাজের নামী-দামি বিশিষ্ট লোকজনদের যিনি যাঁকে চেনেন, যাঁর সঙ্গে যাঁর ঘনিষ্ঠতা আছে, আগামী ক’দিন ধরে তাঁরা তাঁর-মারফত তাঁদের কাছে যাবেন। গিয়ে সব জানিয়ে, তাঁদের দিয়েও স্বাক্ষর করাবেন। জনমত গঠন করবেন। সেই মতো কাজও শুরু হল।
আরও পড়ুন: প্রাচীন ভারতে গণিকা ও গণিকাবৃত্তি
দিনের বেলায় সই সংগ্রহ আর রাতের বেলায় সবাই মিলে এক জায়গায় জড়ো হওয়া। এটা রোজকার রুটিন হয়ে দাঁড়াল। এক-একজনের সই যেন তাঁদের আন্দোলনকে এক-একটা বছর এগিয়ে দিতে লাগল। কে সই করলেন না তাতে? অপর্ণা সেন থেকে সুজাত ভদ্র। তরুণ সান্যাল থেকে শুভাপ্রসন্ন। অর্পিতা ঘোষ থেকে দিলীপ চক্রবর্তী। সবাই তাঁদের পাশে এসে কাঁধে কাঁধ মেলালেন।
ওঁরা বুঝতে পারলেন, আর বসে থাকলে হবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জোরদার কিছু একটা করতে হবে। যাতে সরকারের টনক নড়ে। সেটা করার জন্যই তড়িঘড়ি করে মাত্র ক’দিনের মাথায়, উনিশে ডিসেম্বর তাঁরা আঁধারগ্রামের নানান ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং ওখানকার কিছু ভুক্তভোগী লোকজন-সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করলেন। প্রকৃত সত্য কী, তা জানার জন্য।
সেই আলোচনাচক্রে ওঁদের মুখ থেকেই তাঁরা জানতে পারলেন, এই বিংশশতাব্দীতে এসেও এখনও কিছু মানুষ আদিম যুগের জন্তু-জানোয়ারদের মতোই হিংস্র হয়ে উঠেছে। ওরা যা চাইছে, তাই করতে হচ্ছে। ওদের কথা মতো না চললেই নেমে আসছে অকথ্য অত্যাচার। আতঙ্ক আর ভয় ছড়িয়ে বসতভিটে থেকে সবাইকে উৎখাত করতে চাইছে। অতি সন্তর্পণে চারদিক ঢেকে দিতে চাইছে অন্ধকারে।
তাঁদের নির্মম অসহায়তার কথা শুনে আহ্বায়কেরা এতটাই বিচলিত হয়েছিলেন যে, ওঁরা প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিলেন। তাঁদের হয়ে লড়ার জন্য এ দিনই ওঁরা একটি ফোরাম বা মঞ্চ তৈরি করেন। তাতে যোগ দেন অন্যান্য নাট্যদলের কর্মী এবং সাংস্কৃতিক জগতের মানুষেরাও। ঠিক হয়, ওঁরা পথ-নাটক করে, গান বেঁধে, কবিতা লিখে জনগণের কাছে পৌঁছে দেবেন এই নৃশংস অমানবিকতার কথা।
যে ভাবে আজ থেকে বহু বহু বছর আগে এক সৎ মায়ের কীর্তি নিয়ে গান বেঁধেছিলেন তৎকালীন বাউল ফকিরেরা। শোনা যায়, এক সৎমা তার সদ্য জন্মানো শিশুর ভবিষ্যতের কথা ভেবে, স্বামী অফিসে বেরিয়ে যেতেই, তার সন্তানের একমাত্র পথের কাঁটা, চার-পাঁচ বছরের মা-হারা ছোট্ট সৎ ছেলেকে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিল। তার পর তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে রান্না করেছিল। কাছেই স্বামীর অফিস। রোজকার মতো স্বামী যখন দুপুরে খেতে এসেছিলেন, তাঁকে বাটি করে সেটা খেতে দিয়েছিল। প্রথম পক্ষের ছেলেকে ভীষণ ভালবাসতেন তার স্বামী। ছেলেকে দেখভালের জন্যই তাঁর এই বিয়ে করা। খেতে বসে, ছেলে কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করতেই, বউ বলেছিল, আশপাশেই কোথাও আছে। অত চিন্তা কোরো না। সময় হলেই ও ঠিক চলে আসবে। নাও, খাও। তোমাকে তো আবার এক্ষুনি অফিসে ছুটতে হবে।
স্বামীর সঙ্গে কথা বলছিল ও। আর স্বামী খাচ্ছিলেন। মাংস দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে হঠাৎ পাতের মধ্যে একটি কড়ে আঙুল দেখে তিনি লাফিয়ে ওঠেন। বুঝতে পারেন, কী সর্বনাশ হয়ে গেছে তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার-চেঁচামেচি করে লোকজন জড়ো করেন তিনি। থানায় খবর দিয়ে তাঁর সেই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে পুলিশের হাতে তুলে দেন।
এই ঘটনাটা সে সময় তুমুল আলোড়ন ফেলেছিল। এ নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন তখনকার বিখ্যাত কবিরা। নিজের নিজের মতো করে গান বেঁধেছিলেন বাউল ফকিরেরা। হাতে একতারা আর পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে নেচে তাঁরা সেই গান করতেন। কেউ ওই গান গাইতে গাইতে গ্রামের মেঠো পথ ধরে হেঁটে যেতেন। কেউ খেয়াঘাটের সামনে, কেউ বা শহরের প্রাণকেন্দ্রে, অফিস পাড়ার ব্যস্ত সময়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সেই গান গাইতেন। আর যখনই ওই গান কেউ গাইতেন, গলা যেমনই হোক না কেন, তাতে সুর-তাল-লয় না থাকলেও, শোনার জন্য ভিড় উপচে পড়ত।
তখন এত সংবাদপত্র ছিল না। টিভি তো নয়ই। ফলে শুধু গানের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল ওই সৎ মায়ের কুকীর্তির কথা। সবাই ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। শোনা যায়, কোনও উকিলই নাকি ওই মহিলার হয়ে দাঁড়াতে রাজি হননি।
বিচার চলার সময় নিহত বাচ্চাটির বাবা বিচারপতির কাছে বিনীত আবেদন করেছিলেন, তাঁর ওই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে যেন বাঘকে দিয়ে খাওয়ানো হয়। জনগণের চাপে এবং এ রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আর কখনও কোনও দিন না হয়, কেউ এ রকম কিছু ভাবলেও এই শাস্তির কথা ভেবে যাতে পিছিয়ে আসে, সে জন্য শেষ পর্যন্ত ওই আবেদনই বহাল রাখে আদালত।
এ রকম অভিনব শাস্তি এর আগে এ দেশে কখনও কোনও আদালত দেয়নি। তাই বহু লোক এই শাস্তিটাকে চাক্ষুষ করার জন্য আবেদন-নিবেদন করতে থাকেন। বাদ যান না উচ্চশ্রেণির লোকেরাও। তখন ঠিক করা হয়, আলিপুর চিড়িয়াখানায় ক্ষুধার্ত বাঘের খাঁচার ভিতরে ওই মহিলাটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এবং সেই দৃশ্য যাঁরা দেখতে চান, তাঁদের কথা ভেবে টিকিটের ব্যবস্থাও করা হয়। ঠিক হয়, টিকিটের এমন দাম রাখা হবে, যাতে প্রবল ইচ্ছে থাকলেও টিকিটের দাম শুনে লোকেরা পিছিয়ে আসেন।
তখনও ‘ভরি’ সিস্টেম চালু হয়নি। দশ গ্রামের হিসেব তো নয়ই, সোনা বিক্রি হত ‘তোলা’ হিসেবে। যখন সোনার দাম প্রতি তোলা আট টাকা আঠাশ পয়সা, তখন ওই দৃশ্য দেখার জন্য টিকিটের মূল্য ধার্য করা হয়েছিল দশ টাকা। তাতেও টিকিটের জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছিল।
এমনটা যে হতে পারে, তৎকালীন ইংরেজ সরকার ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারেনি, যে-দেশের জমিদারেরা সর্বস্বান্ত হওয়ার মুখেও শুধু নিজেদের ঠাট-বাট বজায় রাখার জন্য কেবল শখ করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পোষা কবুতরের বিয়ে দিতেন, মাঝরাতে হঠাৎ চা খেতে ইচ্ছে হলে, তাড়া তাড়া দশ টাকার বান্ডিল বার করে দিতেন, ওগুলো জ্বালিয়ে চা করে দেওয়ার জন্য, সে দেশের মানুষের পকেটে যতই টান থাকুক না কেন, অন্তত কিছু লোকের মেজাজটা কিন্তু এখনও সেই জমিদারদের মতোই রয়ে গেছে। ফলে ইচ্ছের কাছে দশটা টাকা তাঁদের কাছে কিছুই নয়।
এটা যদি সরকার আগে টের পেত, তা হলে হয়তো দশ টাকা নয়, ওই টিকিটের দাম করত একশো টাকা বা তারও বেশি। সে যাই হোক, ওই দৃশ্য দেখার জন্য যে ক’জন ভাগ্যবান মুষ্টিমেয় দর্শক ওই সীমিত সংখ্যক আসনের টিকিট জোগাড় করতে পেরেছিলেন, তাঁদের মুখেই পরে শোনা গিয়েছিল, মহিলাটিকে ঠেলে বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়ে দিতেই, বাঘটা নাকি তার দিকে জুলজুল করে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। মহিলাটিও দজ্জাল মহিলাদের মতো কোমরে দু’হাত দিয়ে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে ছিল বাঘটার দিকে। বাঘের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তার পা নাকি এতটুকুও কাঁপেনি। লোকেরা ভেবেছিল, এত পাপ করেছে সে, বাঘও বুঝি তাকে ছোঁবে না। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কয়েক মুহূর্ত একে অপরের দিকে ও রকম ভাবে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ঠিকই, তার পরেই বাঘটা আড়মোড়া ভেঙে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মহিলাটির উপরে। ঘাড়ে কামড় বসাতেই চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ দড়ি টেনে পর্দা ফেলে দিয়েছিল।
আরও পড়ুন: ধারাবাহিক উপন্যাস উত্তাল ১৬
যারা আঁধারগ্রামে এই কাণ্ড ঘটাচ্ছে, তাদেরও কি ওই ভাবে বাঘকে দিয়ে খাওয়ানো উচিত নয়? যাঁরা দিনের বেলায় স্বাক্ষর সংগ্রহ করছিলেন এবং রাতেরবেলায় এক জায়গায় জড়ো হচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকে একজন তো ওই ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেই ফেললেন, আগের ঘটে যাওয়া মামলার অনুষঙ্গ টেনেই তো বিচারকেরা সাধারণত যে কোনও মামলার রায় দিয়ে থাকেন। একটা বাচ্চা ছেলেকে কেটে ফেলার জন্য একজন সৎমাকে যদি বাঘের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়, তা হলে এতগুলো লোককে একের পর এক খুন, অপহরণ, সার সার ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, প্রকাশ্য রাস্তায় ফেলে মেয়েদের ধর্ষণ করার জন্য একটা কেন, একশোটা বাঘের সামনে কি তাদের ঠেলে দেওয়া উচিত নয়?
যে বলছিলেন, তাঁকে শান্ত করার জন্যই ও দিক থেকে আর একজন বলে উঠলেন, না না, আমরা কখনওই অমানবিক কিছু করব না। আমরা বদলা চাই না। বদল চাই। যে সরকার এ রকম একটা ঘটনায় মদত দিতে পারে, বলতে গেলে, ব-কলমে এ রকম একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটাতে পারে, সে সরকার আমরা চাই না। এই সরকারের অপসারণ চাই। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন চাই।
সেই পরিবর্তনের ব্রত নিয়ে সে দিনই তাঁরা একটি খোলা চিঠি পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে।
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন, মানে বারোই জানুয়ারি তরুণ সান্যাল, শঙ্খ ঘোষ ও শাঁওলী মিত্রের আহ্বানে একটি মিছিল ও সমাবেশ সংগঠিত হয়। তাতে শুধু কলকাতার নাট্যকর্মী, লেখক-শিল্পীরাই নন, অংশ নেয় মফসসলের অনেকগুলো নাট্যদল। বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদ। চারণিক নাট্য সংস্থার অজন্তা ঘোষও সেখানে এসে যোগ দেন।
বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৌশিক সেন আফসোস করে বলেন, ‘আমাদের আরও আগে একত্রিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখনও সময় আছে। মনে রাখতে হবে, সরকার ”ধীরে চলো” নীতি নিয়েছে। যাতে আমাদের প্রতিবাদ করার কর্মসূচিও কিছুটা শিথিল হতে হতে এক সময় স্তিমিত হয়ে আসে। এই সময় আমাদের বিবেক আর চেতনাকে আরও জাগ্রত রাখা বেশি জরুরি।’
পিছিয়ে রইলেন না কবি-লেখকেরাও। পনেরো মার্চ কবির সুমন, জয় গোস্বামীরা একটি প্রতিবাদ সভা ডাকলেন ধর্মতলায়। ঐতিহাসিক সেই সভা, শুধু সভা নয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ে উঠল একটি মিলন মেলা। কে ছিলেন না সেখানে? ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী থেকে তরুণ কবিরা। ছিল বিজল্পের ছেলেরাও। প্রসূন ভৌমিকেরা সেখানেই ঠিক করলেন, প্রতি শনিবার তাঁরা ওখানে গিয়ে প্রতিবাদ জানাবেন। সে দিনই তাঁরা গড়ে তুললেন, সহনাগরিক মঞ্চ। এর পাশাপাশি গড়ে উঠল বুদ্ধিজীবী মঞ্চ। লেখক-সংস্কৃতিকর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চ। একই ভাবে তৈরি হল শাঁওলী মিত্র, অপর্ণা সেনদের ‘স্বজন’। বাদ গেল না লিটিল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চও।
এঁরা কেউই ময়দানে নেমে সরাসরি লড়াই করতে পারবেন না। চোরাগোপ্তা আক্রমণও করতে পারবেন না। সরকারের পিছনে আড়াল থেকে বড় কোনও বিপর্যয়ের ছকও কষতে পারবেন না। কারণ, তাঁদের সবচেয়ে বড় বাধা, তাঁদের শিক্ষা, তাঁদের রুচি এবং তাঁদের বিচার-বুদ্ধি। তাই যেটা তাঁদের পক্ষে সম্ভব, সেটা দিয়েই তাঁরা চপেটাঘাত করতে লাগলেন সরকারের গালে। এই সরকার যে সব কবি-লেখক-নাট্যশিল্পীদের বিভিন্ন সময়ে নানা পুরস্কারে সম্মানিত করেছিল, তাঁরা সেই পদকগুলো ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। আলোক সরকার, তরুণ সান্যালেরা এই পদক্ষেপ নিতে না নিতেই নাট্য আকাদেমির নানা পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন সুমন মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, কৌশিক সেন, মনোজ মিত্ররা। বাংলা আকাদেমি আয়োজিত বাংলা কবিতা উৎসব যেহেতু সরকারি উদ্যোগে হয়, তাই ওই উৎসবে আমন্ত্রণ পেয়েও, আঁধারগ্রামের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সেই আমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন যশোধরা রায়চৌধুরী, অর্ধেন্দু চক্রবর্তীরা। সরকার থ’। এমনটা যে হতে পারে, তা তারা ভাবতেই পারেনি। নাট্য আকাদেমি, বাংলা আকাদেমি, নজরুল আকাদেমি ভরে যেতে লাগল প্রাপকদের ফিরত দিয়ে যাওয়া ওই সব পদকে।
বিরুদ্ধ-মত পোষণ করতেই তাঁদের বিরুদ্ধে আগেই নানা রকম কু-মন্তব্য করতে শুরু করেছিলেন সরকারের বদান্যতায় বিশিষ্ট হয়ে ওঠা কিছু লোক। সেই নিন্দুকেরা এ বারও তাঁদের পিঠে কালি ছেটাতে ছাড়লেন না। বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা বলে বেড়াতে লাগলেন, এঁরা ফিরিয়ে না দিলে তো আমরা জানতেই পারতাম যে, এই লোকগুলোকে সরকার পুরস্কার দিয়েছে। তা, তাঁরা পুরস্কার ফিরিয়ে দিচ্ছেন খুব ভাল কথা। কিন্তু শুধু পদক ফিরিয়ে দিলেই তো হবে না। পুরস্কারের সঙ্গে যে টাকাটা দেওয়া হয়েছিল, সেটা কোথায়?
নানা রকম কথাবার্তা যখন চালাচালি হচ্ছে। চাপানউতোর চলছে। ঠিক সে সময়ই একটি চিঠি এসে পৌঁছল পঞ্চম বৈদিক-এর দফতরে। সেই চিঠি খুলে শাঁওলী মিত্র দেখলেন, চিঠিটা মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে পাঠানো হয়েছে।
চলবে…