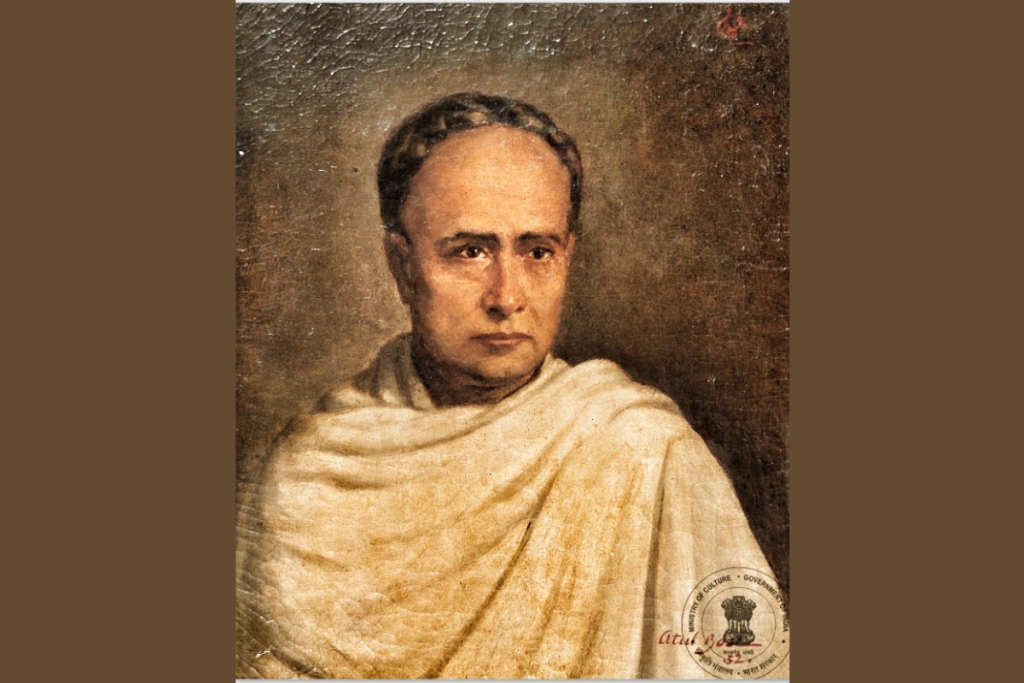রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০২ বঙ্গাব্দে লিখিত তাঁর ‘বিদ্যাসাগর-চরিত’ প্রবন্ধের সূচনাতেই পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ হিসেবে তাঁর— করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের —কথা উল্লেখ করে নির্দ্বিধায় জানিয়েছিলেন যে— ‘তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা’। এরপরে নিজের সেই প্রবন্ধে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের কীর্তি বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছিলেন—
“বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলাগদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।”
বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়েছিল ১৮২০ সালে এবং তিনি ১৮৯১ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বলে যে, তাঁর জন্মের আগে থেকেই বাংলা গদ্যের অনুশীলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮৪৭ সাল থেকে বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর রচনাগুলি একটি একটি করে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। ‘সাহিত্য-সাধক চরিতমালা’ গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের রচনাগুলি নিয়ে আলোচনা করবার আগে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন—
“বিদ্যাসাগরের রচিত, সঙ্কলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা বড় অল্প নহে। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে দুই-চারিখানির কথা বাদ দিলে বাকী সমস্তই অনুবাদ, অনুসৃতি বা পাঠ্যপুস্তক।”
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, কোম্পানি আমলের কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ জি. টি. মার্শাল সাহেবের আদেশে প্রসিদ্ধ হিন্দি পুস্তক অনুসারে লেখা তাঁর ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’ নামক গ্রন্থটি ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই বছরই— ‘কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূল পুস্তক দৃষ্টে সংশোধিত’ —তাঁর সম্পাদিত ‘অন্নদামঙ্গল’ ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এভাবে ১৮৪৭ সাল থেকে শুরু হয়ে তাঁর লেখনীর ধারা তাঁর জীবনের একেবারে শেষ লগ্ন অবধি প্রবাহিত হয়েছিল।
বিদ্যাসাগর যে প্রধানতঃ একজন উদ্যোগী কর্মীপুরুষ ছিলেন, বর্তমানে তাঁর জীবনের সাথে অল্পবিস্তর পরিচিত প্রায় সকলেই এই তথ্যের বিষয়ে অবগত রয়েছেন। অতীতে এপ্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী তাঁর সম্পাদিত ‘বিদ্যাসাগর রচনা-সম্ভার’ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন—
“বিদ্যাসাগরই বোধ করি একমাত্র শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিক বিশুদ্ধ শিল্পপ্রেরণায় যিনি লেখনী ধারণ করেন নাই। তাঁহার রচিত সাহিত্য তাঁহার কর্মজীবনের প্রক্ষেপ মাত্র। কর্মের একটা স্বাভাবিক সীমা আছে, তাহার পরে কর্মের আর যাওয়া সম্ভব নয়। কর্ম যেখানে থামিয়াছে, সাহিত্যের সেখানে সূত্রপাত হইয়াছে। তাঁহার লেখনীর কর্ণধার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ Practical মনোবৃত্তি। কর্মের দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে আদৌ তিনি লেখনী ধারণ করিতেন কি না সন্দেহ। … প্রথমে পাঠ্যপুস্তকের অভাবপূরণের উদ্দেশ্যেই তিনি লেখনী গ্রহণ করেন। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাব; তাঁহার লেখনী বর্ণপরিচয় হইতে যাত্রা শুরু করিয়া নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সীতার বনবাসে গিয়া পৌঁছিল। সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের অভাব; তাঁহার লেখনী আবার যাত্রা শুরু করিল, ঋজুপাঠ উপক্রমণিকা হইয়া সংস্কৃত কাব্যের বিবিধ সংকলনগ্রন্থে গিয়া উপনীত হইল। বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিরোধকল্পে তিনি আন্দোলনে ব্যস্ত, প্রতিপক্ষগণ সমালোচনা করিতেছে, কাজেই বেনামীতে তাঁহাকে ‘কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোগ্য’, ‘কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরণ্য’ প্রভৃতি পুস্তিকা প্রণয়ন করিতে হইল। মহাভারতের বঙ্গানুবাদের সূত্রপাত ও শব্দসংগ্রহের চেষ্টার মূলেও তাঁহার কার্যসম্পাদনী বুদ্ধি। এই নিয়মের ব্যতিক্রমে মাত্র দুইখানি পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একখানি ‘আত্মচরিত’ সম্পূর্ণ করিবার আগ্রহ বোধ করেন নাই। অপরখানি ‘প্রভাবতী-সম্ভাষণ’। এই পুস্তিকাটি তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশুকন্যা প্রভাবতীর মৃত্যুতে রচিত।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস উভয়েই মনে করতেন যে, বিদ্যাসাগরের গদ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেসব প্রশংসার কথা লিখে গেছেন, বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারেরই (১৭৬২-১৮১৯) তা অংশতঃ প্রাপ্য।”
অন্যদিকে প্রমথনাথ বিশীর আগে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করে জানিয়েছিলেন—
“ভাষার ব্যাকরণ-অভিধানও যখন সুষ্ঠুভাবে রচিত ও সংকলিত হয় নাই, মৃত্যুঞ্জয় তখনই কতকগুলি অপ্রচলিত ও পঙ্গু শব্দ পরস্পর যোজনা করিয়া নানা বিচিত্র রস উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টা আংশিক ফলবতী হইয়াছিল। অর্থাৎ শিল্পীর প্রতিভা তাঁহার ছিল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর-সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ উক্তি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।”
আর অধ্যাপক সুকুমার সেন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন—
“বাঙ্গলা গদ্যের জটিলতা ঘুচাইয়া বাক্যে অনেকখানি ভারসমতা ও ব্যবহারযোগ্যতা দিয়াছিলেন অক্ষয়কুমার। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিমিতি ও লালিত্য সঞ্চার করাইয়া বাঙ্গালা গদ্যে প্রাণসঞ্চার করিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় শ্বাসোচ্ছ্বাসতরঙ্গিত ধ্বনিপ্রবাহ অনুধাবন করিয়া বাক্যে স্বাভাবিক শব্দানুবৃত্তির রূপ দিয়া তিনি বাঙ্গালা গদ্যের তাল বাঁধিয়া দিলেন।”
বিদ্যাসাগরের সব জীবনীকারই তাঁর লেখা প্রথম গ্রন্থ হিসেবে ‘বাসুদেবচরিত’ গ্রন্থটির নামোল্লেখ করেছেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থটি সম্পর্কে অধ্যাপক সুকুমার সেন জানিয়েছিলেন —
“এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে পাওয়া একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। সেটি কলেজের এক সিভিলিয়ান ছাত্র হেনরি সারজ্যান্টের লেখা, ‘বাসুদেবচরিত’– জাতীয় কৃষ্ণলীলা বই। আমার মনে হয় এই রচনাটি লিখিবার সময়ে বিদ্যাসাগর— তখন তিনি বোধ করি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক ছিলেন—সারজ্যান্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই হইতেই বোধ হয় ‘বাসুদেবচরিত’ কিংবদন্তীর উৎপত্তি। সারজ্যান্টের লেখায় বিদ্যাসাগরের ছাপ আগাগোড়া নাই। তাহা থাকিবার কথাও নয়। তাঁহার কৃতিত্ব বোধ করি সংশোধনে। রচনা-রীতিতে ফোর্ট-উইলিয়ম-কলেজী ভঙ্গি বেশ আছে, তবে স্টাইল সরল হইয়া আসিয়াছে।”
বিদ্যাসাগরের রচনাবলী প্রধানতঃ পাঠ্যপুস্তক-জাতীয়। ‘বাসুদেবচরিত’ গ্রন্থটিকে যদি তাঁর লেখা প্রথম গ্রন্থ বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে ‘সাহিত্য-সাধক চরিতমালা’ গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের লেখা অন্যান্য গ্রন্থগুলির সালানুসারে যে তালিকা দিয়েছেন, সেটা নিম্নরূপ হয়—
(১) বেতাল পঞ্চবিংশতি। ১৮৪৭। (হিন্দী পুস্তক অনুসারে রচিত।)
(২) বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ। ১৮৪৮।
(৩) জীবনচরিত। সেপ্টেম্বর ১৮৪৯।
(৪) বোধোদয়, (শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাগ)। এপ্রিল ১৮৫১।
(৫) সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, নবেম্বর ১৮৫১।
(৬) ঋজুপাঠ, ১ম ভাগ; নবেম্বর ১৮৫১। ২য় ভাগ; মার্চ ১৮৫২। ৩য় ভাগ; ডিসেম্বর ১৮৫২।
(৭) সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব। ১ মার্চ ১৮৫৩।
(৮) ব্যাকরণ কৌমুদী, ১ম ভাগ; ১৮৫৩। ২য় ভাগ; ১৮৫৩। ৩য় ভাগ; ১৮৫৪। ৪র্থ ভাগ; ১৮৬২।
(৯) শকুন্তলা। ডিসেম্বর ১৮৫৪।
(১০) বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। জানুয়ারি ১৮৫৫।
(১১) বর্ণপরিচয়, ১ম ভাগ; এপ্রিল ১৮৫৫। ২য় ভাগ; জুন ১৮৫৫।
(১২) বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক। অক্টোবর ১৮৫৫।
(১৩) কথামালা। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৫।
(১৪) চরিতাবলী। জুলাই ১৮৫৬।
(১৫) মহাভারত (উপক্রমণিকাভাগ)। জানুয়ারি ১৮৬০।
(১৬) সীতার বনবাস। এপ্রিল ১৮৬০।
(১৭) আখ্যানমঞ্জরী। নবেম্বর ১৮৬৩।
(১৮) শব্দমঞ্জরী (বাঙ্গলা অভিধান)। ১৮৬৪।
(১৯) ভ্রান্তিবিলাস। ১৬ ডিসেম্বর ১৮৬৯। (শেক্সপীয়রের কমেডি অব এররস অবলম্বনে।)
(২০) বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। ১০ অগাস্ট, ১৮৭১।
(২১) বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক। ১ এপ্রিল ১৮৭৩।
(২২) নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস। এপ্রিল ১৮৮৮।
(২৩) পদ্যসংগ্রহ। প্রথম ভাগ; ১৮৮৮ (২ জুলাই)। দ্বিতীয় ভাগ; ১৮৯০।
(২৪) সংস্কৃত রচনা। নবেম্বর ১৮৮৯।
(২৫) শ্লোকমঞ্জরী (উদ্ভট শ্লোক-সংগ্রহ)। মে ১৮৯০।
(২৬) বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)। সেপ্টেম্বর ১৮৯১।
(২৭) ভূগোলখগোলবর্ণনম্। এপ্রিল ১৮৯২।
এছাড়াও তিনি বারোটি বাংলা, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। তাছাড়া বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সম্পর্কে তাঁর লেখা উপরের তালিকার ১০, ১২, ২০ ও ২১ নম্বর গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হওয়ার পরে তৎকালীন পণ্ডিতমহলের অনেকে তাঁর মতের প্রতিবাদ করে কিছু গ্রন্থ রচনা করলে, সেগুলির উত্তরে বিদ্যাসাগর বেমানীতে যে পাঁচটি গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করেছিলেন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তালিকানুসারে সেগুলো নিম্নরূপ ছিল—
(১) অতি অল্প হইল। ৫ মে ১৮৭৩।
(২) আবার অতি অল্প হইল। ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩।
(৩) ব্রজবিলাস। ৩ নবেম্বর ১৮৮৪।
(৪) বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা। ১১ নবেম্বর ১৮৮৪।
(৫) রত্নপরীক্ষা। ১৯ আগস্ট ১৮৮৬।
এই তালিকার প্রথম তিনটি গ্রন্থ তিনি— ‘কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য’, চতুর্থটি— ‘কস্যচিৎ তত্ত্বন্বেষিণঃ’ এবং পঞ্চমটি— ‘কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য’ ছদ্মনামে প্রচার করেছিলেন। অনেকের মতে তাঁর এইধরণের রচনা হয়ত আরো কিছু কিছু ছিল, কিন্তু সেগুলি সবই কালের স্রোতে হারিয়ে গিয়েছে। বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন জীবনচরিত থেকে জানা যায় যে, নিজের ব্যক্তিগত জীবনে উপকারের বদলে অপকার পাওয়াটাই তাঁর কাছে অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। অতীতে অধ্যাপক বিজিতকুমার দত্তের সংগ্রহে থাকা ‘অপূর্ব ইতিহাস’ নামের একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে ডঃ সুকুমার সেন সেটিকেও বিদ্যাসাগরের রচনা বলে চিহ্নিত করেছিলেন, এবং এপ্রসঙ্গে লিখেছিলেন—
“তাঁহার শেষ বয়সে কোনো কোনো বিশ্বাসী ও স্নেহের পাত্রের কাছে এমন আঘাত তিনি পাইয়াছিলেন যাহাতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাঁহাকে সালিশ মানিতে হইয়াছিল। বলিতে পারি পুস্তিকাটি সেই সালিশির রিপোর্ট। বিবাদের বস্তু ও কথাবস্তু এবং পূর্ব-ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় রিপোর্টখানিতে স্বাক্ষর ও তারিখ দিয়াছেন (২১ অগ্রহায়ণ, ১২৯২)। পুস্তিকাটিতে তিন পরিচ্ছেদ। পরিশিষ্টে সালিশ দুইজনের রিপোর্ট (একজনের বাঙ্গালায় আর-একজনের ইংরেজীতে), দুইখানি প্রমাণ চিঠি ও কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক (বিশ্বাসঘাতীর বিরুদ্ধে) ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ আছে। সাহিত্যের দিক দিয়া বিশেষভাবে নজরে পড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ক্রুদ্ধ রচনাভঙ্গি।”
ডঃ সুকুমার সেনের মতে— দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) কলমে বাংলা গদ্য সাহিত্যে ‘বুদ্ধিদীপ্ত গদ্যের পথ’ দেখা দিয়েছিল এবং— “অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরের সমান্তরালে দেবেন্দ্রনাথ অজ্ঞাতসারে বাঙ্গালা গদ্যের একটি নিজস্ব সরল স্টাইল” —তৈরি করে নিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের গদ্যগুলিতে তাঁর সৌন্দর্য আস্বাদনের আনন্দ প্রতিফলিত হয়েছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরের আগে ও পরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮১৩-৮৫) লেখা— ‘উপদেশ কথা’ (১৮৪০), ‘বিদ্যাকল্পদ্রুম’ (১৮৪৬- ৫১) ও ‘ষড়দর্শন-সংবাদ’ (১৮৭৬) —নামক গ্রন্থগুলিতেও বাংলা ভাষার সুষ্ঠু গদ্যরূপের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-৮৬) গদ্য রচনার ভঙ্গি— সহজ সরল পরিমিত এবং প্রকাশক্ষম ছিল বলে দেখা যায়। বাংলা গদ্য সাহিত্যের এই ধারা দেখে ডঃ সুকুমার সেন বিদ্যাসাগরের গদ্য সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, বিদ্যাসাগর কোন স্রষ্টা ছিলেন না, আদতে তিনি বাংলা গদ্যের সংস্কর্তা ছিলেন।
“বিদ্যাসাগর ছিলেন বাঙ্গালীর মানসিক ও সামাজিক জীবনের সংস্কর্তা, এইই ছিল যেন তাঁহার জীবনের মিশন।”
এরপরে তিনি আরও জানিয়েছিলেন—
“উনবিংশ শতকের প্রথম সত্তর বছর বলা যাইতে পারে—বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তকের কল্প। এ কল্পের মনু বিদ্যাসাগর।”
এপ্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীও প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করে জানিয়েছিলেন—
“প্রকৃতপক্ষে নব্য শিক্ষারীতির স্রষ্টা বিদ্যাসাগর, রামমোহন, ডেভিড হেয়ার বা অপর কেহ নহেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষিতসমাজকে ইয়ং বেঙ্গল বলা হইয়া থাকে, বিদ্যাসাগরীয় রীতির শিক্ষিত সমাজকে মডার্ন ম্যান বলা অন্যায় হইবে না। বিংশ শতক বিদ্যাসাগরীয় রীতিতে শিক্ষিত সমাজের উত্তর পুরুষ—বিদ্যাসাগরকে তাহার আত্মীয় মনে না হওয়া অসম্ভব। মায়ের মুখের ভাষা মাতৃভাষা—এখানে বিদ্যাসাগরকে মাতা মনে করিলে অন্যায় হইবে না—তাঁহার মুখের ভাষা পরবর্তী যুগকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে; তাঁহার কলমের গাছে অত্যল্প কালের মধ্যে অপূর্ব নব্য গদ্যের সুফল ফলাইয়াছে।”
অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী তাঁর সম্পাদিত ‘বিদ্যাসাগর-রচনাসম্ভার’ গ্রন্থের ভূমিকায় এইধরণের কিছু মন্তব্য করবার পরে পূর্ববর্তী বাঙালি লেখকদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির প্রভেদ দেখাতে গিয়ে— রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামমোহন রায়ের রচনা থেকে কিছু কিছু নমুনা তুলে ধরেছিলেন। এরপরে সেই দৃষ্টান্তগুলিকে অবলম্বন করে তিনি জানিয়েছিলেন যে—
(১) “… ‘রাজা প্রতাপাদিত্যচরিতে’—নব্য গদ্যের দূরশ্রুত পদধ্বনিটুকুও শোনা যায় না—প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজের রীতির জের টানিয়া চলিয়াছেন রামরাম বসু।”
(২) রামরামের পূর্বোক্ত গ্রন্থটির একবছর পরে লেখা মৃত্যুঞ্জয়ের ‘বত্রিশ সিংহাসন’ (১৮০২) গ্রন্থে—
“গোটাকয়েক পূর্ণচ্ছেদ বসাইয়া—গোটা দুই শব্দের পরিবর্তন করিলে … প্রকৃতপক্ষে আধুনিক গদ্যের দূরশ্রুত পদধ্বনি বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব নয়।”
(৩) আবার মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ‘রাজাবলি’ (১৮০৮) গ্রন্থের ভাষা আরো সরল—
“বাক্যগুলি ছোট করিবার প্রবণতা স্পষ্ট, তবুও ইহাকে নব্যগদ্য বলা চলে না।”
(৪) তাঁর ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’ (১৮৩৩) গ্রন্থের ভাষা আরো সরল—
“যতিস্থাপনে বিচক্ষণতা আরও স্পষ্ট, আর সংস্কৃত শব্দের মধ্যে দেশজ শব্দকে গাঁথিয়া লইবার চেষ্টা প্রত্যক্ষ। প্রায় বিদ্যাসাগরের সময়ে আসিয়া পড়িয়াছি বুঝিতে পারা যায়।”
(৫) কিন্তু সেই তুলনায় রামমোহনের ‘ব্রাহ্মণ সেবহি’ (১৮২১) বা ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ (১৮৩৩) গ্রন্থের ভাষা—
“অনেক বেশি স্থাবর প্রকৃতির, মেদবহুল বিদ্যালঙ্কারের ভাষার তুলনায় তাহাকে প্রাগ্রসর বলা যায় না।”
প্রমথনাথ বিশী বিদ্যাসাগরের আগের লেখকদের এইসব গদ্যরীতির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ‘সীতার বনবাস’, ‘প্রভাবতী-সম্ভাষণ’ ও ‘ব্রজবিলাস’ গ্রন্থের গদ্যের তুলনা করে জানিয়েছিলেন যে—
“বিদ্যাসাগরই প্রথম সজ্ঞানে শিল্পবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া (যতিস্থাপনের) নিয়মটিকে অনুসরণ করিয়াছেন, তাই তাঁহার পক্ষে কমা, সেমি-কোলন প্রভৃতির ব্যবহার অপরিহার্য ছিল; কেবল পূর্ণচ্ছেদে তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। প্রভাবতী-সম্ভাষণের ভাষা হৃদয়াবেগে মন্থর, অশ্রুজলে ভারাক্রান্ত, পদে পদে কমা সেমিকোলনে ঈষৎ থামিয়া থামিয়া চলিয়াছে। ব্রজবিলাস ও তজ্জাতীয় বিতণ্ডা ও বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলিতে ভাষা কেমন টাট্টুঘোড়ার মতো ছুটিয়াছে; চার পায়ের আঘাতে গ্রাম্য শব্দের লোষ্ট্রখণ্ড ছুটিয়া গিয়া প্রতিপক্ষকে আহত করিয়াছে। আর সীতার বনবাসের ভাষায় ঐরাবতের গজেন্দ্রগমন। পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে ঐ ভাষাই অত্যাবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রে পৌঁছিবার আগে ভাষায় এমন বিচিত্র গতিচ্ছন্দ আর পাওয়া যাইবে না। সর্বোপরি বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির ছন্দে নব্য গদ্যরীতির মূল ছন্দ ধ্বনিত। পদ্যে মধুসুদন যাহা করিয়াছেন, গদ্যে তাহা করিয়াছেন বিদ্যাসাগর। তিনি গদ্যছন্দের মধুসুদন।”
অধ্যাপক বিশীর বিদ্যাসাগরের জন্য প্রযোজ্য— ‘গদ্যছন্দ’ —উপমাটি এখানে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এপ্রসঙ্গে অতীতে হরপ্রসাদ মিত্র জানিয়েছিলেন—
“… ‘নব্য গদ্যরীতির মূল ছন্দ’—বলতে কী বোঝায়? পদ্য আর গদ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে, এ কথার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। গদ্যরীতি বা প্রোজ-স্টাইল বললে শব্দসমষ্টিময় বাক্যের একরকম গঠনভঙ্গি বুঝিয়ে থাকে। গদ্য ও পদ্য সম্পূর্ণ পৃথক রূপ। পদ্যের প্রকৃতি নিয়মিত যতিরক্ষা। গদ্য কখনোই সেরকম নয়। পদ্যের চাল আলাদা। আবার কবিত্ব গদ্যেও বাহিত হতে পারে। কিন্তু কবিতার গদ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-প্রয়োজনের গদ্য নয়। কবিতার সঙ্গে গদ্যের পার্থক্য মানসিকতার ভেদে আশ্রিত। গদ্য গঠনধর্মী বা কন্ট্রাক্টিভ; কবিতা সৃষ্টিধর্মী বা ক্রিয়েটিভ—এ মন্তব্যও সম্পূর্ণ স্বীকার্য নয়, কারণ সৃষ্টির মৌলিক সঙ্গীত গদ্যে ধ্বনিত হয়েছে, এরকম দৃষ্টান্তও বিরল নয়।”
বিদ্যাসাগরের ‘সীতার বনবাস’ গ্রন্থের নিম্নলিখিত ছত্রগুলিতে তাঁর ‘গদ্যছন্দ’ রীতির সেই বিশেষ সঙ্গীত দেখতে পাওয়া যায়—
“রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বাণপ্রস্তুধর্ম অবলম্বনপূর্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রাম সুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।”
আবার নিজের ‘প্রভাবতী-সম্ভাষণ’ গ্রন্থে বিদ্যাসাগর তাঁর শেষ বয়সের মর্মবেদনার তাড়নায় নিজের ব্যক্তিগত শোকের কারণে যে অন্যরকমের গদ্য লিখেছিলেন, সেটার নমুনা নিম্নরূপ—
“বোধ হয়, যদি এই পাপিষ্ঠ নৃশংস নরলোকে অধিক দিন থাক, উত্তর কালে বিবিধ যাতনাভোগ একান্ত অপরিহার্য্য, ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলে। এই জন্যই ঈদৃশ স্বল্প সময়ে, যথাসম্ভব, সাংসারিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিয়া, সত্বর অন্তর্হিত হইয়াছ। তুমি, স্বল্পকালে নরলোক হইতে অপসৃত হইয়া, আমার বোধে, অতি সুবোধের কার্য করিয়াছ।”
কিন্তু তাঁর ‘ভ্রান্তিবিলাস’ গ্রন্থে কাহিনী বর্ণনার গদ্যে উপরোক্ত দুটি দৃষ্টান্তের কোনোটির মতোই অনুভূতির ঢেউ পাওয়া যায় না, সেখানে শুধু কথা-বর্ণনার প্রয়োজনবোধ দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ নিম্নরূপ—
“হেমকূট ও জয়স্থল নামে দুই প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজ্য ছিল। দুই রাজ্যের পরস্পর ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে জয়স্থলে এই নৃশংস নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়, হেমকূটের কোনও প্রজা বাণিজ্য বা অন্যবিধ কার্যের অনুরোধে জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিলে, তাঁহার গুরুতর অর্থদণ্ড, অর্থদণ্ড প্রদানে অসমর্থ হইলে প্রাণদণ্ড হইবেক।”
হরপ্রসাদ মিত্র বলেছিলেন—
“কবিতার মতো গদ্যেরও উপাদান শব্দসম্ভার বটে কিন্তু সে হ’লো প্রস্তুত বা ready-made শব্দের প্রয়োগকলা; আর কবিতায় আবেগ-অনুভূতিই শব্দগুলিকে বা শব্দসমষ্টিগুলিকে বাজিয়ে তোলে। হার্বার্ট রীড বলেছেন, কবিতা একটি মাত্র শব্দে বা অক্ষরে ধ্বনিত হতে পারে, গদ্য কিন্তু নিজস্ব বিশেষ সুরের শব্দবন্ধে আশ্রিত থাকে। গদ্য ও কবিতার এই ভেদসূত্র রসিকের অনুভূতিবেদ্য। এই ব্যাপারটি ঠিক ব্যাখ্যাগম্য নয়।”
বিদ্যাসাগর তাঁর রচনায়— সাধু ও চলিত —দুই রীতিই ব্যবহার করেছিলেন বলে দেখা যায়। তবে সকলেই জানিয়েছেন যে— অবশ্য চলিত রীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের চলিত রূপ রক্ষা করা কখনোই তাঁর আদর্শ ছিল না। তাঁর বিদ্রূপাত্মক নিবন্ধগুলিতে পরিহাসের কোন অন্তঃ দেখতে পাওয়া যায় না। সেসব রচনায় বিদ্যাসাগরী চলিত রীতির দুটি নমুনা নিম্নরূপ—
(১) “সংস্কৃতবিদ্যায় খুড়োর পেট ভরা আছে; সে বিষয়ে তাঁহার অপ্রতুল নাই। যে বিষয়ে অপ্রতুল আছে, তাহাতেই সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক।” (আবার অতি অল্প হইল)
(২) “খুড়োর লজ্জা-সরম কম বটে। কিন্তু লোকের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়। দোহাই খুড়ো! তোমার পায়ে পড়ি; এমন করে আর চলিও না, এবং ‘শতং বদ, মা লিখ’ এই অমূল্য উপদেশবাক্য লঙ্ঘন করিয়া, আর কখনও চলিও না।” (অতি অল্প হইল)
পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির সংস্কৃতভাষায় লেখা আক্রমণাত্মক নিবন্ধের উত্তর দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর সহজ বাংলা গদ্যের উপরোক্ত রীতিকে তাঁর লেখায় অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছিলেন। সমালোচকরা জানিয়েছেন যে, বিদ্যাসাগরের এই বিশেষ ধরণের চলিত রীতিতে তৎসম শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম দেখতে পাওয়া যায়, বরং এতে তদ্ভব শব্দ বেশি পরিমাণে উপস্থিত, এমনকি আরবি-ফারসি শব্দও বিদ্যমান রয়েছে বলে দেখা যায়। কিন্তু তাঁর রচনার সাধু-রীতিতে সংস্কৃত শব্দেরই আধিক্য দেখা যায়; নিজের পূর্বগামী লেখক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের মত সেই রীতিতেও তিনি নিজের সাধ্যানুসারে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, এবং সেই ‘লিটারারি’ বা সাধু-রীতিই তাঁর কাছে বেশি প্রিয় ছিল; কারণ— সেই রীতির সঙ্গীতগুণ অনেক বেশি ছিল। অতীতে ডঃ শিশির দাশ এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা করে জানিয়েছিলেন যে, শব্দক্রমে ও বাক্যগঠনে বিদ্যাসাগর তাঁর পূর্বগামী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তকে অনুসরণ করেছিলেন। ডঃ শিশির দাশ জানিয়েছিলেন যে— বিদ্যাসাগর তাঁর ‘বেতাল-পঞ্চবিংশতি’ গ্রন্থে দশ শব্দের কম বাক্য খুব কমই ব্যবহার করেছিলেন, আবার মৃত্যুঞ্জয়ের রীতির মত খুব বেশি শব্দের বাক্যও তিনি কখনো পছন্দ করেননি। তাঁর মতে— বাক্যে ছেদ-যদি চিহ্নের প্রয়োগের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর ঠিক পথপ্রদর্শক ছিলেন না। কারণ— তাঁর আগেই রামমোহন রায়, অক্ষয় দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখরা নিজেদের লেখায় সেসব ব্যবহার করেছিলেন। ডঃ শিশির দাশের এই বক্তব্যগুলি ইতিহাসের ঘটনা হিসেবে অনস্বীকার্য হলেও বিদ্যাসাগরের সৌষম্যবোধ যে তাঁরই নিজস্ব দান ছিল, সেই ঐতিহাসিক সত্যিটি তাঁর গদ্যপ্রবাহের সব ধারাতেই সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বলে দেখা যায়।
১২৮৫ বঙ্গাব্দের ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বাঙ্গালা ভাষা’ নিবন্ধে সেযুগের বাংলার সংস্কৃতপ্রধান— ‘সাধুভাষা’ এবং ‘টেকচাঁদি ভাষা’ —এই দুই শ্রেণীর মধ্যে তুলনা করে অবশেষে টেকচাঁদি ভাষার রঙ্গরসের প্রশংসা করে এবং সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় প্রয়োজনীয় শব্দ ধার নেওয়ার রীতিকে অনুমোদন করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিলেন যে—
“বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষায় উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা।”
এই স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্যগুণের দাবিতেই ভাষার শ্রেয়তা সমালোচকদের কাছে স্বীকার্য। বাংলা গদ্যভাষার বাঞ্ছিত আদর্শের আলোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র— স্পষ্টতা, সৌন্দর্য, ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্য —এই চারটি গুণের ওপরে জোর দিয়েছিলেন বলে দেখা যায়। ‘লুপ্তরত্নোদ্ধার’ গ্রন্থে ‘বাঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ’ নামে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা যে প্রবন্ধটি পাওয়া যায়, সেখানে তিনি লিখেছিলেন যে, বাংলায় সংস্কৃতানুসারিণী গদ্যভাষা প্রথম প্রথম— ‘মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত’ হয়েছিল। এরপরে তিনি নির্দ্বিধায় জানিয়েছিলেন—
“বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে পাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্বজনবোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না।”
বঙ্কিমচন্দ্রের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝতে পারা যায় যে, শুধুমাত্র বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতিতেই বাংলাগদ্যের ধারা আবদ্ধ হয়ে থাকে নি, বস্তুতঃ মানব জীবনের বিচিত্র প্রয়োজনে বিদ্যাসাগরের পরে বাংলা গদ্যের বিচিত্র রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছিল। কিন্তু তাতেও বিদ্যাসাগরের কীর্তি একটুও কমে যায় না, বরং এতে তাঁর প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য আরো বেশি করেই প্রমাণিত হয়। এই কারণেই বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরীয় রীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন—
“গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা-গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।”#