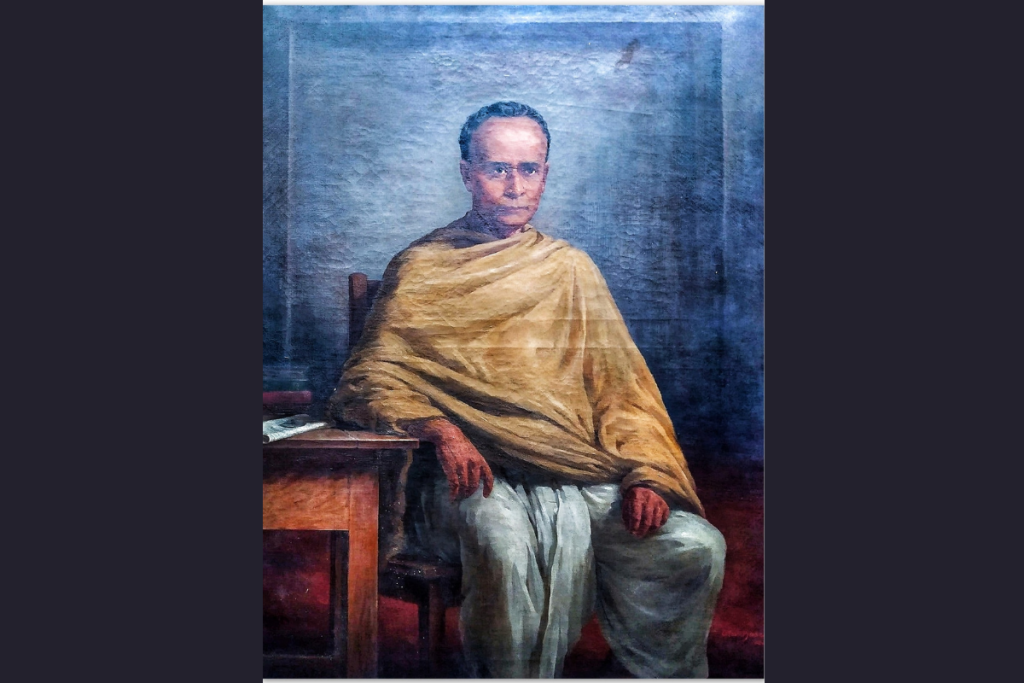পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যদিও সেকেলে সংস্কৃত সাহিত্য পড়েছিলেন, কিন্তু তিনি কোন সেকেলে ধরণের মানুষ ছিলেন না। আর সেই কারণেই সেযুগের অন্য পাঁচজনের মত তিনি বিদ্যা-ব্যবসায়ী টুলো পণ্ডিত না হয়ে বিদ্যাজীবী হিউম্যানিস্ট হতে পেরেছিলেন। এখনো পর্যন্ত প্রায় সকলেই একথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বহমান কালের সঙ্গে চলতে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত প্রত্যয়ে ও সামাজিক মানসে লোক-কল্যাণের আদর্শকে অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। লোকহিতকর বিদ্যাভাবনায় তিনি যেমন বর্ণপরিচয় ও বোধোদয় লিখেছিলেন, তেমনি বাসুদেবচরিত, বেতালপঞ্চবিংশতি, জীবনচরিত, বাঙ্গালার ইতিহাস, শকুন্তলা, কথামালা, চরিতাবলী, সীতার বনবাস, মহাভারত, আখ্যানমঞ্জরী ও ভ্রান্তিবিলাস লিখেছিলেন। তাঁর লেখা বেতালপঞ্চবিংশতি ঊনিশ শতকের বাংলার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের পাঠার্থে রচিত এবং সেযুগের বঙ্গদেশের প্রায় সব বিদ্যালয়েই প্রচলিত হয়েছিল। এমনকি তাঁর লেখা শকুন্তলা ও সীতার বনবাসও অতীতে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ ছিল। তাই সেযুগে সেগুলি তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিল। অথচ তাঁর রচিত মহাভারত ও ভ্রান্তবিলাস ছাত্রদের পাঠার্থে কখনো গৃহীত হয়নি বলে তেমনভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু একইসাথে একথাও উল্লেখ্য যে, তাঁর এই গ্রন্থগুলি কোন স্বাধীন রচনা ছিল না; বরং এগুলি সবই তিনি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের কোনো না কোনো মূল লেখাকে অবলম্বন করে লিখেছিলেন। তাঁর লেখা স্বাধীন রচনাগুলি হল—সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য-শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার, আত্মচরিত, প্রভাবতী সম্ভাষণ ইত্যাদি। সেকালের সামাজিক প্রয়োজনমূলকতাই যেখানে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলির প্রেরণা ছিল, সেখানে শিল্পগত প্রেরণায় তিনি শুধু নিজের আত্মচরিত ও প্রভাবতী সম্ভাষণ লিখেছিলেন।
তবে অতীতের সব সাহিত্য সমালোচকের কাছেই ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত শকুন্তলা গ্রন্থটি বিদ্যাসাগরের সবথেকে সমাদৃত রচনা বলে গৃহীত হয়েছিল। এটির মূল অবলম্বন ছিল—মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাটকটি। এই গ্রন্থটির বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর জানিয়েছিলেন যে, এতে তিনি মূল সংস্কৃত নাটকটির শুধুমাত্র উপাখ্যানভাগ বাংলায় সংকলিত করলেও মূল গ্রন্থের অলৌকিক চমৎকারিত্ব প্রদর্শনের কোনো চেষ্টা করেননি। সমালোচকদের মতে—একটা নাটককে গদ্য-আখ্যায়িকায় রূপায়িত করতে গেলে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত, এই গ্রন্থটির ক্ষেত্রে তিনি সঠিকভাবে সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন। আর সেই কারণেই নিজের গ্রন্থ থেকে তিনি মূল সংস্কৃত রচনার প্রস্তাবনা ভাগ, কাব্যাংশ ও নাটকীয় মুহূর্তগুলিকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি নিজের গ্রন্থের কোথাও কোথাও তিনি বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ ও আভিধানিক শব্দ পর্যন্ত বর্জন করেছিলেন; এছাড়া কোথাও কোথাও তিনি মূল নাটকের যথোচিত পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন এবং সেসবের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও প্রদান করেছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের অবলম্বনে রচিত নিজের গল্পটিকে তিনি তখনকার বাঙালি পাঠক-পাঠিকা, বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের কাছে উপযোগী করবার দিকে লক্ষ্য রেখেই ঢেলে সাজিয়েছিলেন। অথচ এত পরিবর্তন করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর গ্রন্থের কোথাও মূল সংস্কৃত নাটকের বিকৃতি ঘটাননি। এসব তথ্য থেকে স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্নটা উঠে আসে, সেটা হল যে—কালিদাসের ক্ল্যাসিক পর্যায়ের সংস্কৃত নাটকটিকে গদ্য-আখ্যায়িকায় রূপান্তরণের এই আদর্শ তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন? তখন এবিষয়ে তাঁর সামনে যে কোনো ধরণের প্রাচ্য আদর্শ ছিল না,—সেবিষয়ে সব সমালোচকই সুনিশ্চিত বলে দেখা যায়। সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসের সাথে পরিচিত প্রায় সকলেই জানেন যে, ইউরোপে তখন প্রাচীন কাব্য-নাটককে সহজ গদ্যভাষ্যে উপস্থাপিত করবার রীতি প্রচলিত ছিল। এমনকি ইংরেজি ভাষাতেও তখন এই জাতীয় গ্রন্থের কোন অভাব ছিল না। একথার উজ্জ্বল ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসেবে ল্যাম (Lamb) লিখিত ও ১৮০৭ সালে প্রকাশিত ‘Tales from Shakespeare’ গ্রন্থটিকে এখানে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই এখনও পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থটি—‘Children’s classic—বলে পরিচিত হয়ে রয়েছে। উক্ত গ্রন্থটি যেহেতু বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার সাতচল্লিশ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল, সেহেতু যুক্তিসঙ্গতভাবেই একথা অনুমান করা যেতে পারে যে— খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে ল্যামের বইটি বাংলাতেও প্রচলিত ছিল। কারণ—হিন্দু কলেজের আমল, অর্থাৎ—১৮১৭ সাল থেকেই বঙ্গদেশে শেক্সপীয়ার-চর্চা চালু হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন জীবনীমূলক গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় যে, তিনিও শেক্সপীয়ার পড়তেন এবং সেই সাহিত্যের রসগ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর এই কারণেই তিনি উক্ত ইংরেজি নাট্যকারের ‘The Comedy of Errors’ নামক গ্রন্থটির একটি বাংলা ভাষ্য—‘ভ্রান্তিবিলাস’—রচনা করেছিলেন। সুতরাং ল্যামের ‘Tales from Shakespeare’–ই যে বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা রচনার আদর্শ ছিল, এবিষয়ে সব সাহিত্য সমালোচকই নিশ্চিত বলে দেখতে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ একথাও স্মরণীয় যে, ল্যামের মতোই ছাত্রপাঠ্য ও কিশোরপাঠ্য Children’s classic রচনা করাই বিদ্যাসাগরেরও লক্ষ্য ছিল। অতীতের সমালোচকরা উভয় গ্রন্থেরই গল্প বলবার ঢঙ ও বর্ণন-রীতির মধ্যে যথেষ্ট মিল খুঁজে পেয়েছিলেন; এবং তাঁদের মতে— উভয় গ্রন্থকার নাটকেরই গদ্য-রূপান্তর রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন।
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মূল গ্রন্থগুলি অবলম্বনে বিদ্যাসাগর তাঁর যে গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন, সেগুলির বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি নিম্নরূপ—
(১) তিনি তাঁর রচনাকে সমকালীন পাঠক-পাঠিকার কাছে প্রীতিপ্রদ ও গ্রহণযোগ্য করে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন।
(২) সেযুগে প্রচলিত থাকা বাংলা ভাষার দুরূহতা, অসংলগ্নতা ও অশ্লীলতা দূর করবার ব্যাপারে তিনি সচেতন ও সচেষ্ট ছিলেন।
(৩) অর্থবোধ ও তাৎপর্য অনুধাবনে পাঠক-পাঠিকার যাতে সুবিধা হয় সেদিকে তিনি নিজের সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন।
(৪) যদিও মূল রচনার উৎকর্ষ ও চমৎকারিত্ব যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেননি, তবুও সব ক্ষেত্রে সেটা যে সম্ভব নয়—সে বিষয়েও তিনি অবহিত ছিলেন।
(৫) তিনি মূল রচনার সঙ্গে তাঁর রচনার বিষয়গত ঐক্য যথাসম্ভব রক্ষা করতে অভিলাষী ছিলেন; আর এই কারণেই তিনি কখনও মূল রচনার আক্ষরিক অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন, তো কখনও আবার মূল বিষয়টিকে নিজের মত করে বলতে গিয়ে প্রায় নতুন সৃষ্টির স্বাদ দেওয়ার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।
(৬) ক্ষেত্রবিশেষে মূল গ্রন্থের নামধাম পরিহার করে ও সেটার বদলে দেশীয় নামধাম গ্রহণ করে তিনি পাঠক-পাঠিকার মনে সংস্কারানুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করবার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।
বিদ্যাসাগরের সমগ্র রচনাবলী সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রযোজ্য এই কথাগুলি বিশেষভাবে তাঁর শকুন্তলা গ্রন্থটি সম্পর্কেও প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। কারণ—তাঁর এই গ্রন্থটি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাটকের কোন গৌড়ীয় রূপ ছিল না, বরং এটি ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত থাকা এই কাহিনীর রূপ অবলম্বন করেই লেখা হয়েছিল। অতীতে এপ্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনুবাদ-নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলার ভূমিকায় বলেছিলেন—
“পণ্ডিত-চূড়ামণি স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল-প্রচলিত গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াই শকুন্তলার নব-সংস্করণ প্রচার করেন।”
এছাড়া বিভিন্ন অনুবাদের ক্ষেত্রেও ঐ নব-সংস্করণই তাঁর আদর্শ হয়ে উঠেছিল।
মূল রচনার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের রচনা মিলিয়ে নিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, কোথাও যেমন তিনি সেগুলির ভাবানুবাদ করেছিলেন, তেমনি কোথাও আবার সেগুলির আক্ষরিক অনুবাদ করেছিলেন। তবে অনুবাদের ব্যাপারে তিনি কোনো পূর্বপরিকল্পিত সূত্র সুনির্দিষ্টভাবে অনুসরণ করেছিলেন বলে সমালোকরা মনে করেন না। বরং এক্ষেত্রে তিনি যখন যেমন উচিত বলে বিবেচনা করেছিলেন, তেমনিভাবেই এগুলি লিখেছেন। এমনকি রচনার অন্তর্নিহিত ভাব উপস্থাপনার খাতিরে তিনি কখনও কখনও সেগুলির বিস্তার বা বিশ্লেষণের দিকেও ঝোঁক দিয়েছিলেন। যেমন—
“তানলয়বিশুদ্ধ স্বরসংযোগবর্তী গীতি শ্রবণ করিয়া রাজা অকস্মাৎ যৎপরোনাস্তি উন্মনাঃ হইলেন; কিন্তু কি নিমিত্ত উন্মনাঃ হইতেছেন তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই মনোহর গীতি শ্রবণ করিয়া আমার মন এমন আকুল হইতেছে। প্রিয়জনবিরহ ব্যতিরেকে মনের এরূপ আকুলতা হয় না; কিন্তু আমার প্রিয়জনবিরহ উপস্থিত দেখিতেছি না।”
বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা গ্রন্থ থেকে নেওয়া উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশটি যে কালিদাসের শকুন্তলার মূল রচনার নয়, সেটা মূল গ্রন্থটির সংস্কৃত ছত্রটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারা যায়—
“কিং খলু গীতমাকণ্য ইষ্টজন-বিরহাদৃতেহপি বলবদুৎকণ্ঠিতোহস্মি।”
সমালোচকদের মতে, এদিক থেকে বরং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের শকুন্তলার অনুবাদ অনেক বেশি মূলানুসারী। তিনি অবশ্যই বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার অনুবাদ দেখেছিলেন এবং অতিরিক্ত অংশগুলি বর্জন করা শ্রেয় বলেই মনে করেছিলেন; যেমন— “রাজা—(স্বগত) কোনো প্রিয়জনের বিরহে মন যেরূপ উৎকণ্ঠিত হয়, গানটি শুনে আমারও যেন সেইরূপ হয়েছে। কেন এরূপ হ’লো? তার কারণ বোধ হয়—” (পঞ্চম অঙ্ক) সুতরাং এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বিদ্যাসাগর তাঁর রচনায় এই অতিরিক্ত অংশগুলি কেন যোজনা করেছিলেন? সমালোচকদের মতে এর পিছনে সম্ভবতঃ দুটি কারণ ছিল।
প্রথমতঃ, নাটকে উপস্থিত চরিত্রগুলির কথোপকথনের মধ্যে দিয়েই কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও কাহিনীর ধারাবাহিকতার মধ্যে যে ফাঁক থেকে যায়, সেসব মূলতঃ দৃশ্যসজ্জা, অঙ্গভঙ্গি, আবহ-সঙ্গীত ইত্যাদির দ্বারা ভরিয়ে তোলা হয়। কিন্তু গদ্য-আখ্যায়িকার রূপবন্ধ আলাদা হয় বলে সেক্ষেত্রে এমনতর কোন সুযোগ থাকে না, তাই এখানে সংলাপে বা বর্ণণায় অতিরিক্ত অংশ জুড়ে দিয়ে কাহিনীর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয়। নাটকে যা প্রদর্শিত হয়, আখ্যায়িকায় সেটা অন্ততঃ অংশতঃ বর্ণিত হয়। সুতরাং বিদ্যাসাগরের অনুবাদে এই অতিরিক্ত কথাগুলি অনিবার্যভাবেই এসে গিয়েছিল।
দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যাসাগরের স্পর্শকাতর ও করুণাঘন চিত্তবৃত্তি নিজের আভ্যন্তর তাগিদে কাহিনীর মধুর ও দুঃখপূর্ণ অংশে আত্মসংবরণ করতে পারেনি বলে ঈপ্সিত রসসৃষ্টির লোভে অতিরিক্ত ব্যাখ্যামূলক অংশ যোজনা করবার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। এর ফলে তাঁর শকুন্তলার অনুবাদ কোনো কোনো জায়গায় আক্ষরিকতার সীমা ছাড়িয়ে ভাবধর্মী হয়ে গিয়েছিল এবং প্রায় নতুন সৃষ্টিরই আকার ধারণ করেছিল।
অতএব— পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের শকুন্তলাদি গ্রন্থের অনুবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে যে, বিদ্যাসাগর তাঁর অনুবাদমূলক রচনার ক্ষেত্রে তিনটি সূত্র অনুসরণ করেছিলেন; যথা— মূলানুগত্য, রূপ (form)-আনুগত্য ও স্বানুগত্য।
এসব ছাড়াও বিদ্যাসাগরের বিষয়-সমাধি ও তাঁর ভাষাগত পরিণামও এখানে অবশ্য উল্লেখ্য। বিষয়ের সঙ্গে একাত্মকতাই তাঁর সাহিত্যিক সিদ্ধির চাবিকাঠি ছিল। সমালোচকদের মতে তাঁর রচনার ভাষাবিভঙ্গে ভাববস্তুরই অনুক্রম দেখতে পাওয়া যায়। এপ্রসঙ্গে জীবেন্দ্র সিংহ রায় জানিয়েছিলেন—
“শুধু শব্দসজ্জা, অন্বয়শৃঙ্খলা ও বাক্যনির্মাণের খণ্ডাংশে নয়, ভাষার রূপাবয়বের সামগ্রিকতায় বিষয়-শ্রদ্ধা অনুস্যূত বলেই তাঁর লেখার ব্যক্তিনিষ্ঠ স্টাইলের একটা নৈর্ব্যক্তিক রস-পরিণতি ঘটেছে। যে বিষয় যেমনভাবে লেখা উচিত, সেই বিষয় তেমনিভাবে লেখা হলে তা সকলের হয়ে দাঁড়ায়। যে ভাষারীতি সীতার বনবাসে, শকুন্তলার ভাষারীতি তা থেকে পৃথক আত্মচরিতের ভাষারীতি প্রায় যোজন দূরে। এ থেকে শুধু বিদ্যাসাগরের ভাষার ক্রম-পরিণতি বোঝা যায় না, বিষয়ভেদে ভাষাভেদের তাৎপর্যও বোঝা যায়।”
তবে মূল রচনার ভাষাপদ্ধতি যে তাঁর অনুবাদের ক্ষেত্রে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছিল,—যদিও সেবিষয়ে সমালোচকদের কোন সন্দেহ নেই; তবুও এবিষয়েও তাঁরা একমত যে, তাতে বিষয়বোধ ও ভাষাবোধের সাক্ষ্যও কিন্তু পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ এখানে বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার তিনটি অনুচ্ছেদ তুলে ধরা যেতে পারে—
(১) “মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! কোথাকার পত্র, পত্র পড়িয়া এত বিষণ্ণ হইলে কেন? রাজা কহিলেন, বয়স্য! ধনমিত্র নামে এক সাংযাত্রিক সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিত। সমুদ্রে নৌকা মগ্ন হইয়া তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। সে ব্যক্তি নিঃসন্তান। নিঃসন্তানের ধনে রাজার অধিকার। এই নিমিত্ত অমাত্য আমায় তদীয় সমুদয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে লিখিয়াছে। দেখ, বয়স্য! নিঃসন্তান হওয়া কত দুঃখের বিষয়। নামলোপ হইল, বংশলোপ হইল, এবং বহু যত্নে বহু কষ্টে বহু কালে উপার্জিত ধন অন্যের হস্তে গেল। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, আমার লোকান্তর হইলে, আমারও নাম, বংশ ও রাজ্যের এই গতি হইবেক।”
(২) “রাজা, বিরহকৃশা মলিনবেশা শকুন্তলাকে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, নয়নযুগলে প্রবলবেগে জলধারা বহিতে লাগিল; বাক্-শক্তিরহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। শকুন্তলাও, অকস্মাৎ রাজাকে দেখিয়া, স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিয়া, স্থির নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপ্লুত হইয়া আসিল। বালক, শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র, মা মা করিয়া, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসিল, মা! ও কে, ওকে দেখে তুই কাঁদিস কেন? তখন শকুন্তলা গদগদ-বচনে কহিলেন, বাছা, ওকথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।”
(৩) “শকুন্তলা কহিলেন, সখি! যে অবধি আমি সেই রাজর্ষিকে নয়নগোচর করিয়াছি—এইমাত্র কহিয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন, আর বলিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা উভয়ে কহিতে লাগিলেন, সখি! বল, বল, আমাদের লজ্জা কি? শকুন্তলা কহিলেন, সেই অবধি তাহাতে অনুরাগিণী হইয়া, আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। এই বলিয়া, তিনি বিষণ্ণ বদনে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন।”
উপরোক্ত অংশগুলি বিশ্লেষণ করে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন যে— লেখকের হৃদয়-রসে জারিত হয়ে এই তিনটি অনুচ্ছেদেই বেদনাভর অনুভূতির জলতরঙ্গ বেজে উঠেছে। এই মূলগত ঐক্য সত্ত্বেও তিনটি ক্ষেত্রেই সূক্ষ্ম শ্রুতির স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করা সম্ভব। প্রথম উদাহরণে দুষ্মন্ত কর্তৃক সন্তানসম্ভবা শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের ভাবানুষঙ্গে সন্তানহীনের খেদ অনুরণিত হয়েছে বলে দেখা যায়; তেমনি আবার দ্বিতীয় উদাহরণে অপ্রত্যাশিত পুনর্মিলনের ক্ষণে বিস্ময়, অনুতাপ ও আনন্দের বিচিত্র মিশ্র স্বাদ রয়েছে। অন্যদিকে সুরত প্রদীপের কাঞ্চন-শিখার লজ্জারক্তিম শিহরণ তৃতীয় উদাহরণে অভিব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং অনুভূতির নিগূঢ় ছন্দে অনুচ্ছেদত্রয়ের বিভিন্ন রসপরিণাম ঘটেছে। এর মূলে বিদ্যাসাগরের পৃথক পৃথক বিষয়ের মানস-সান্নিধ্যে অনুভবের প্রাতিস্বিকতা এবং প্রত্যেক বিষয়ে গভীর আত্মলীনতা ছিল বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়—
“ধনমিত্রের প্রসঙ্গে দুষ্মন্তের অন্তঃস্পন্দন নানা মাপের বাক্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মধ্যখানের ছোট্ট বাক্যটি যেন বেদনার কেন্দ্রবিন্দু (‘সে ব্যক্তি নিঃসন্তান’); আর তারই চারপাশে দুঃখের আবর্ত ক্রম-দীর্ঘ রূপ নিতে নিতে আত্মশোচনার দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘতম বাক্যবৃত্ত রচনা করেছে। ‘নিঃসন্তান হওয়া কত দুঃখের বিষয়’—এ-বাক্যে শব্দসজ্জার চটক নেই নতুন শব্দ বানিয়ে নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টির প্রয়াস নেই; অথচ এর আবেদন পাঠকের মনে চারিয়ে যায়। সার কথা, বিদ্যাসাগর তাঁর বিষয়ভাবনায় সমাধিস্থ হতেন বলেই তাঁর সিদ্ধি ঘটতো এমন তর্কাতীত।
দ্বিতীয় উদাহরণের প্রথম দুটি বাক্য রুদ্ধশ্বাস ঝড়ের রূপক স্মরণ করিয়ে দেয়। বিরহকৃশা মলিনবেশা শকুন্তলাকে দেখে বিস্ময়াপন্ন দুষ্মন্তের আলোড়ন যেন উত্তুরে হাওয়ার বিপরীত দিগন্তপ্রসারী বিস্তার, আর দুষ্মন্ত-দর্শনে শকুন্তলার প্রতিক্রিয়া দখিনা হাওয়ার আদিগন্ত উত্তরায়ণ। তাই বাক্যগুলিরও অপরিহার্য দীর্ঘতা। তারপর পুত্রের প্রশ্নে শকুন্তলার বিক্ষিপ্ত মনের আকাশ থেকে শুরু হয়েছে ছোট বাক্যের বৃষ্টিফোঁটা। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, নায়ক-নায়িকার আবেগের দিকে লক্ষ্য রেখেই বিদ্যাসাগর বাক্যধারা রচনা করেছেন। এ সিদ্ধি লেখকের বিষয়মগ্নতা থেকে উৎসারিত।
বিদ্যাসাগরের রসিকচিত্তের শিল্প-স্বাক্ষরে তৃতীয় উদাহরণটি উজ্জ্বল। শকুন্তলার উক্তি প্রথম দিকে অসম্পূর্ণ রেখেই তাঁর লজ্জার ব্যঞ্জনাটুকু সম্পূর্ণ করে তুলেছেন লেখক। নায়িকার ব্রীড়াবনত কান্নাসুন্দর মুখখানি নিঃসন্দেহে পাঠকের মন টেনে নেয়। এখানে বিদ্যাসাগরের ‘emotional attitude to his subject’ শকুন্তলার অনুভবের মধ্যে একটা যৌবনবেদনারস সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে।’#