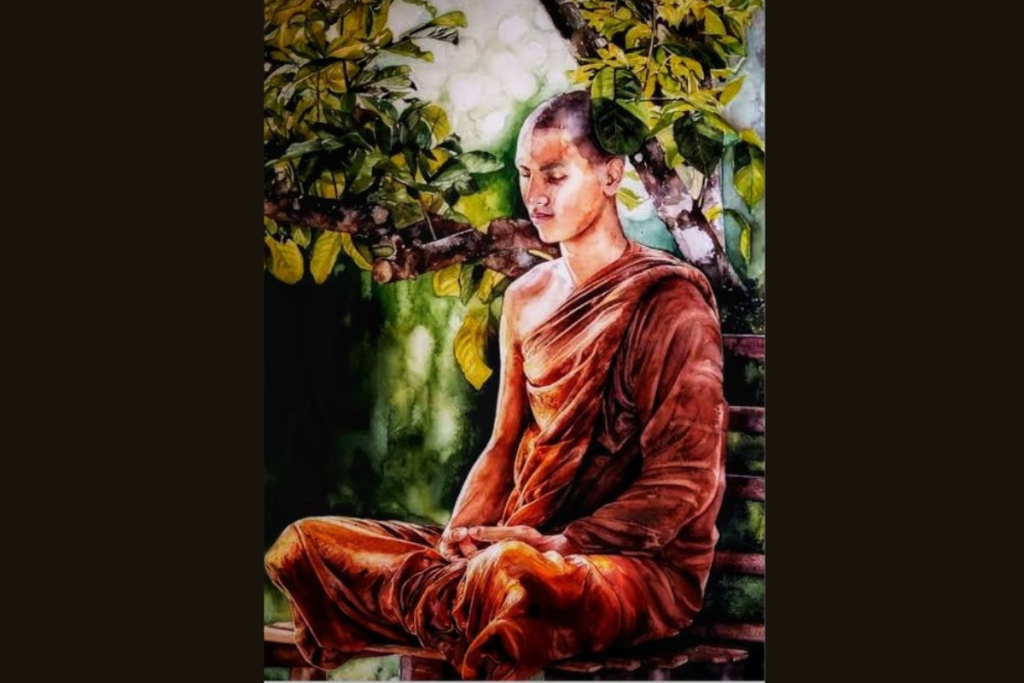প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক-সম্প্রদায়ের ধর্মসাধনার নিগূঢ় সংকেতবাণী বহন করে চর্যাপদগুলি আধুনিকযুগের মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। চর্যাপদে ইশারা ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে অতীতের বাংলার সহজিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মসাধনার গুহ্যতত্ত্বকথা আভাসিত হয়ে উঠেছে। তবে সেই তত্ত্বকথার গহন-গভীরে প্রবেশ করবার আগে বৌদ্ধধর্মের সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ইতিহাসটি জেনে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।
সাধারণভাবে বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্যই হল—ভবজন্ম থেকে মুক্তিলাভ করে নির্বাণপ্রাপ্ত হওয়া। এই নির্বাণলাভ বা ভবচক্র থেকে মুক্তিপ্রাপ্তির উপায়কে কেন্দ্র করেই অতীতে বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই মতবাদ অনুসারে— জীবমাত্রকেই বার বার চক্রক্রমে ভবচক্রের আবর্তনে ঘুরে অসংখ্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। আর এই ব্যাথা-বেদনার ও দুঃখ-দারিদ্রের দাবদাহ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার অর্থই হলো ভবচক্র (whirl of existence) থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নেওয়া। কিন্তু এই ভবচক্র হতে নিজেকে ছিন্ন করবার উপায় কি? অতীতের বৌদ্ধ দার্শনিকেরা বলেছিলেন যে, মানুষের অন্তরে যে অবিদ্যার জন্ম হয়, সেই অবিদ্যাই মানুষকে বারবার ভবচক্রের নির্মম গতিশীলতার মাঝে টেনে নিয়ে আসে। সুতরাং এই ভবচক্র থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে পরমলভ্য নির্বাণ পেতে হলে প্রথমেই নির্বাণ-পথের পরম এবং প্রধান শত্রু অবিদ্যাকে দূর করবার প্রয়োজন রয়েছে। অবিদ্যার প্রতি মানুষের আর কোন আকর্ষণ না থাকলেই তাঁর নির্বাণলাভ সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই অবিদ্যাকে কি দিয়ে দূর করা সম্ভব? প্রাচীন বৌদ্ধ-দার্শনিকদের মতে এই অবিদ্যাকে দূর করবার জন্য শূন্যতা জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধধর্মের দুই প্রধান মতবাদী দল—হীনযান ও মহাযান—উভয়েই এই শূন্যতাবাদকে গ্রহণ করেছিলেন। এগুলির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনতম রূপ নিয়ে হীনযান গঠিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে মতবাদ গড়ে উঠেছিল, সেটা নিয়ে মহাযান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ধর্মমতের দিক থেকে হীনযানী মতবাদ অতীত থেকেই রক্ষণশীল এবং সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ। হীনযানী মতাবলম্বীদের কাছে নিজের ব্যক্তিগত মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই চরম। অতীতে তাঁদের এই মুক্তিলাভের পথও দুর্গম ছিল, আর তাই কঠিন নৈতিক আদর্শ ও দুরূহ সাধনপন্থায় এই মতে নির্বাণলাভ করা প্রায় প্রাণান্ত ব্যাপার ছিল। সেযুগের হীনযানীদের সাধনপন্থায় চারটি স্তর ছিল; যথা—স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎ। শূন্যতা জ্ঞানের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে জগৎ ও জীবনের পিছনে কোন সত্যি নেই জেনে অবিদ্যার ধ্বংসসাধন করে অর্হৎত্ব লাভ করাই এই মতবাদের চরম লক্ষ্য ছিল। কিন্তু এই মতবাদের পিছনে নিয়ম-নীতির প্রচণ্ড শাসন থাকবার ফলে এবং সর্বোপরি এটি সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকবার জন্য জনসাধারণ ক্রমশঃ এই মতবাদের উপর থেকে নিজেদের আস্থা হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছিলেন। এরফলেই পরবর্তী সময়ে মহাযান মতবাদের উদ্ভব ঘটেছিল। মহাযানীদের দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা এবং এক বিশ্বপ্রসারী মনোভাব—এই মতবাদের পরিপুষ্টির অন্তরালে বেগ সঞ্চার করেছিল। শুধুমাত্র নিজেদের ব্যক্তিগত মুক্তিই তাঁদের কাম্য ছিল না, বরং ব্যক্তিগত মুক্তির সাথে তাঁরা নিখিল বিশ্বমানবের দুঃখ-মুক্তিও চেয়েছিলেন। ফলে শূন্যতা জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার ধ্বংসসাধন করে শুধুমাত্র অর্হৎত্ব লাভ করাই তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠেনি, বরং তাঁদের সমগ্র ধ্যান-সাধনা শূন্যতা-জ্ঞানের সাথে করুণার সংমিশ্রণে বোধিচিত্ত লাভ করবার ওপরে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাঁদের এই করুণার স্বরূপ কি ছিল? করুণা হল—ভবচক্রে বেদনা লাঞ্ছিত নিখিল বিশ্বের অসংখ্য মানবের জন্য অপরিসীম বেদনা-বোধ। সুতরাং বোধিচিত্ত হল—শূন্যতা-জ্ঞানের সাথে বিশ্বমানবের জন্য অপরিসীম করুণা বোধে নতুন চেতনায় আলোকোদ্ভাসিত চিত্ত,—যা কিনা শূন্যতা ও করুণার সমান্বিত রূপ। সুতরাং মহাযানী মতবাদের প্রভাবে একটাসময়ে বৌদ্ধধর্ম ও সমাজ থেকে নৈতিক-নৈষ্টিকতার কড়াকড়ি এবং সংকীর্ণতা দূর হয়েছিল, আর হীনযানীদের শূন্যতাময় নেতিবাচক (negative conception) নির্বাণ করুণার সংমিশ্রণে বোধিচিত্তের মধ্যে একটি ইতিবাচক (positive conception) রূপলাভ করেছিল। এই উদার নীতির পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত মহাযান বৌদ্ধধর্ম যখন নিজের মহাযান নিয়ে মানুষের দ্বারপ্রান্তে আবির্ভূত হয়েছিল, তখন সর্বদলের সর্বশ্রেণীর মানুষ মুক্তিলাভের আশায় সেখানে প্রবেশ করেছিলেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যে এই মতবাদ প্রাচীন বাংলার লোকসমাজের কাছে ব্যাপক প্রিয় হয়ে উঠেছিল।
আরও পড়ুন: চর্যাপদের ভাষা বিতর্ক
সেযুগের সর্বশ্রেণীর মানুষ মহাযানের অন্তর্গত হওয়ার ফলে এরপরে একটাসময়ে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লৌকিক মতবাদ এবং আচার অনুষ্ঠানও এই মহাযান মতবাদে অনুপ্রবিষ্ট হতে শুরু করেছিল। এরফলে নিয়ম বন্ধনের শিথিলতার জন্য একদিকে মহাযান যেমন ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে পড়েছিল, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের ক্রমপ্রচলনের ফলে মহাযানের ধর্মমতের বিবর্তনও অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, এবং এই অনিবার্যতার ফলস্বরূপই পরবর্তী সময়ে মূল মহাযান বৌদ্ধধর্ম ভেঙে—মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান ইত্যাদি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত জানিয়েছিলেন যে, সহজযান নামের কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের উল্লেখ প্রাচীন বৌদ্ধ তন্ত্রগুলিতে পাওয়া যায় না। এছাড়া তিনি বলেছিলেন যে, বজ্রযানপন্থী একদল সাধকের কতগুলি মত-বৈশিষ্ট্য ও সাধন-বৈশিষ্ট্য দিয়েই এই নামটি পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছিল। মূলতঃ ‘মন্ত্র’, ‘মুদ্রা’ ও ‘মণ্ডল’—ইত্যাদি নিয়েই তান্ত্রিকাশ্রয়ীরূপে বজ্রযান মতবাদের পত্তন ঘটেছিল। এছাড়াও সেই বজ্রযানে বিবিধ দেবদেবীর পূজার্চনা এবং তান্ত্রিক পদ্ধতির কতগুলি গুহ্য যোগ-সাধনা ছিল। তাই বৌদ্ধ সহজযান মূল মহাযান থেকেই উৎপন্ন হোক কিংবা বজ্রযান থেকেই আসুক—সহজযানের সাধনপদ্ধতি ও ক্রিয়াকলাপের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আর চর্যাপদের প্রতিটি চর্যা এই সহজিয়াদেরই ধ্যান-ধারণার একটি অনুলিখনমাত্র।
কিন্তু সহজযান মতবাদ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে শুরুতেই যে প্রশ্নটা উঠে আসে, সেটা হল যে—এই সহজযান নামের অন্তরালে এই মতবাদের কোন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে কিনা? এপ্রসঙ্গে শশিভূষণ দাশগুপ্ত জানিয়েছিলেন— “এই সম্প্রদায়ের সাধকগণকে সহজিয়া বলিবার দুইদিক হইতে সার্থকতা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ ইহাদের ‘সাধ্য’–ও ছিল সহজ আবার ‘সাধনা’ও ছিল সহজ, প্রত্যেক জীবনের প্রত্যেক বস্তুরই একটি সহজ স্বরূপ আছে—ইহাই তাহার সকল পরিবর্তনশীলতার ভিতরে অপরিবর্তিত স্বরূপ। এই সহজ স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া মহাসুখে মগ্ন হইতে হইবে—ইহাই হইল এই পন্থী সাধকগণের মূল আদর্শ—এই জন্যই ইঁহারা হইলেন সহজিয়া। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা সাধনার জন্য কোনও বক্রপথ অবলম্বন করিতেন না—গ্রহণ করিতেন সরল সোজা পথ, এই জন্যও তাঁহারা সহজিয়া।”
সহজিয়ারা সবসময়েই নিজের সাধন-পদ্ধতিকে সোজা পথ বলেছিলেন। এই কারণেই সিদ্ধাচার্যের একটি চর্যায় পাওয়া যায়—
“উজুরে উজু ছাড়ি মা জাহরে বঙ্ক।
নিয়ড়ি বোহি মা জাহরে লঙ্ক॥”
অর্থাৎ—এপথ সোজা (ঋজু), সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে যেওনা; বোধি কাছেই আছে (দূর) লঙ্কায় যাওয়ার (প্রয়োজন) নেই।
এবারে প্রশ্ন হল যে, সহজিয়ারা বারবার যে বাঁকা পথ ছেড়ে সোজা পথে যেতে বলেছিলেন সেই বাঁকা পথ আসলে কি ছিল এবং সেটা ছাড়ারই বা প্রয়োজন তাঁরা কেন বোধ করেছিলেন? এই প্রশ্ন দুটির উত্তর চর্যাকাররাই দিয়েছিলেন। তাঁদের মত ছিল যে—শাস্ত্র-তর্ক-পাণ্ডিত্যের পথ, ধ্যান-ধারণা সমাধির পথ, বিবিধ তন্ত্র-মন্ত্র আচার পদ্ধতির পথই হল বাঁধা পথ; এবং পাণ্ডিত্যের অভিমান নিয়ে সেই পথে চলে মুক্তি বা সহজানন্দ পাওয়া সম্ভব নয় বলেই সেটা ত্যাজ্য। পাকা বেলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে অলি যেমন শুধু সেটার চারপাশে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু সেটার ভিতরে প্রবেশ করে ফলের সার গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি পাণ্ডিত্যগর্বী মানুষেরা মহাসুখের চারপাশে পাণ্ডিত্যের অভিমানে মত্ত হয়ে শুধু ঘুরে মরেন, মুক্তির স্বাদ পাওয়া তাঁদের পক্ষে কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠে না। ‘সহজানন্দ’ বা মহাসুখ বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, বরং সেটা পুরোপুরি অনুভূতি সাপেক্ষ ব্যাপার। সুতরাং বুদ্ধি-শাসিত পাণ্ডিত্যে সেটাকে পাওয়া অসম্ভব। বাক্য-মনের অগোচরে যে সহজানন্দ থাকে, যেটাকে বোঝা যায় না—শুধুমাত্র আভাস-ইঙ্গিতে একটু অনুভব করা যায় মাত্র, ঠিক তেমনি বাহ্যাড়ম্বরযুক্ত ক্রিয়াকাণ্ড বা বুদ্ধিদীপ্ত পাণ্ডিত্যের দ্বারা সেটাকে কোনমতেই পাওয়া যায় না—সেটাকে পেতে হলে গুরুর উপদেশ গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। আর এই কারণেই চর্যাকারেরা বারবার গুরুর উপদেশ গ্রহণ করবার উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা জানিয়েছিলেন যে, গুরুর নির্দেশিত পথে পদচারণা করলেই নির্বাণ তথা সহজানন্দ তথা মহাসুখলাভ অনিবার্য হয়ে ওঠে।
আরও পড়ুন: চর্যাপদের রচয়িতাদের ধর্মমত
এরপরে তাঁরা বলেছিলেন যে—নির্বাণ, অদ্বয়, সহজানন্দ, মহাসুখ ইত্যাদি শব্দগুলির মধ্যে একটি গভীর যোগসূত্র থাকলেও আসলে সবই কিন্তু এক। হৃদয়ের মধ্যে যে রাগের আগুন রয়েছে, যে দ্বেষের আগুন এবং যে মোহের আগুন রয়েছে, সেই আগুন নির্বাপিত হলেই যথার্থ নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। এবং এই নির্বাণই হল পরম সুখের বা মহাসুখের। ধর্মপদের বহু জায়গায়—‘নির্ব্বাণং পরমং সুখং’—বলা হয়েছে বলে দেখা যায়। অদ্বয় কি? এটি হল মানুষের দেহান্তরালবর্তী আদি-অন্ত-রহিত শাশ্বত সহজ সত্তা। এই সহজ সত্তার সাথে মিলনেই সহজানন্দ বোধ হয় এবং সহজানন্দে মিলনই হল নির্বাণ ও নির্বাণেই মহাসুখ নিহিত রয়েছে। কিন্তু এই সহজানন্দ বা স্বরূপানুভূতির ক্ষেত্রে কোন জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞেয়ত্ব বা গ্রাহকত্ব-গ্রাহ্য়ত্ব থাকে না। তাই গ্রাহ্যত্ব-গ্রাহকত্ব রহিত যে স্বরূপ—সেটাই হল অদ্বয় স্বরূপ; অদ্বয়ই হল সহজ, আর সহজই হল মহাসুখ। সুতরাং সহজিয়াদের কাছে—অদ্বয় লাভ, মহাসুখ প্রাপ্তি, সহজে প্রতিষ্ঠা কিংবা বোধিচিত্ত লাভ— এসবই একই কথা। আগেই বলা হয়েছে যে, সহজিয়াদের কাছে বোধিচিত্তলাভই হল পরম লক্ষ্য, আর এই বোধিচিত্ত শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতার দ্বারাই লাভ হয়। তাই এবারে দেখা যাক যে, এই শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতার অর্থ আসলে কি? এই উভয়ের মধ্যকার তাৎপর্যের দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য রাখলে সহজিয়াদের দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব বা সাধনতত্ত্ব—সবকিছুই পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায়। সুতরাং সহজিয়াদের জটিলতত্ত্বকথা বুঝতে এই শূন্যতা ও করুণার প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।
সহজিয়া ধর্মমতের পক্ষ অবলম্বন করে বলা যায় যে, শূন্যতার দ্বারা নির্বাণ, অর্থাৎ—বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে শুধুমাত্র এককভাবে মুক্তির চেষ্টা না করে করুণার সংমিশ্রণে বিশ্বমানবের মঙ্গলের জন্য বৃহত্তর পথে পদচারণার সাধনাই হল বোধিচিত্ত লাভের সাধনা। এই শূন্যতাকে আবার—প্রজ্ঞা বা জ্ঞাত বা গ্রাহক বা ‘Principle of subjectivity’, এবং করুণাকে—উপায় বা জ্ঞেয় বা গ্রাহ্য বা ‘Principle of objectivity’ বলা হয়ে থাকে। আর এই গ্রাহ্য-গ্রাহকত্ব বা জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃত্বের দুই প্রবহমান ধারা সম্মিলিত হয়ে শেষপর্যন্ত যে অদ্বয়তত্ত্ব লাভ হয়—সেটাই হল বোধিচিত্ত, সেটাই সহজানন্দ, সেটাই মহানন্দ, সেটাই নির্বাণ, বা এগুলো সবকিছু। এটাই হল সহজিয়া ধর্মমতের দিক থেকে শূন্যতা ও করুণার সম্মিলনের তাৎপর্য।#