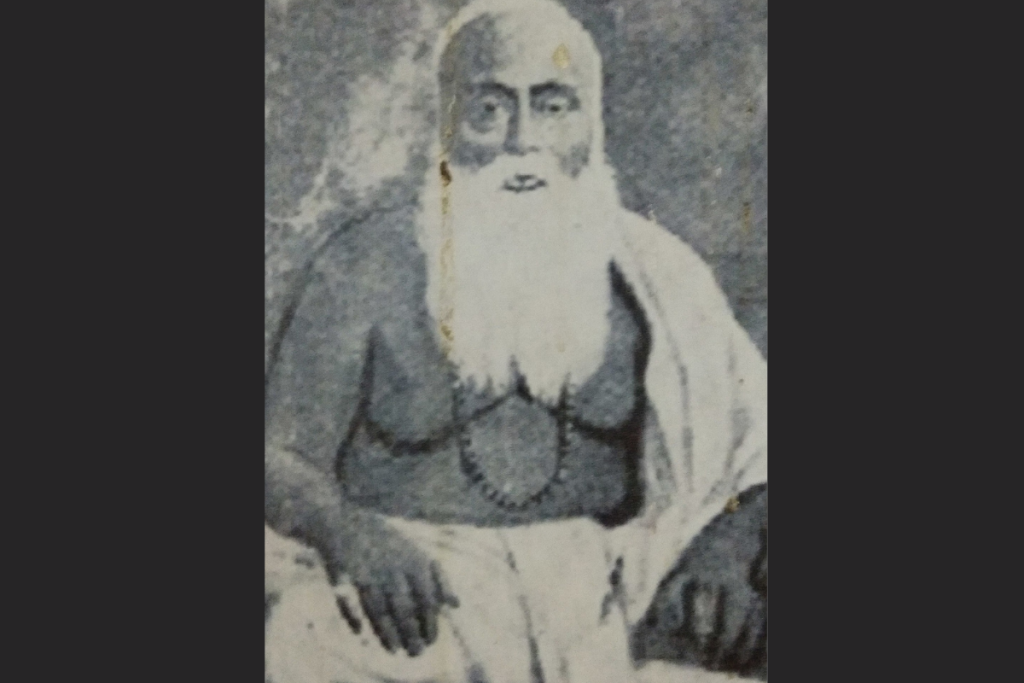খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকের প্রথমদিকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয়চন্দ্র সরকার মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগী ও বঙ্কিম পর্বের বা বঙ্কিম গোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার হলেও পরবর্তী সময়ের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গ সংযোগ ছিল। ১২৮২ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ—১৮৭৫ সালে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিদ্বজ্জন সমাগম’ সভায় আমন্ত্রিত অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে একটি স্বরচিত কবিতা শুনেছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর, এবং কবিতাটির নাম ছিল ‘প্রকৃতির খেদ’। এরপরে কবিতাটির প্রসঙ্গে তিনি ‘সাধারণী’ পত্রিকায় লিখেছিলেন— “গত রবিবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে ‘বিদ্বজ্জন সমাগম’ হইয়াছিল। প্রায় একশত গ্রন্থাকার ও বিদ্বানব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সাহিত্য ও সঙ্গীতের আমোদ এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। সভাগৃহ তরুরাজি, পুষ্পমালা, আলোকাবলি ও সুন্দর আসনে সুশোভিত হইয়াছিল।
প্রথমে বাবু রাজনারাণ বসু বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি এবং বঙ্গকবি ও গ্রন্থকারদিগের সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন, পরে প্রাচীন কবি বিদ্যাপতির গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পঠিত হয়। তাহার পর রাজনারায়ণ বাবু কবি কঙ্কণের চণ্ডী হইতে একটুকু পাঠ করেন। অনন্তর ‘হুতোম প্যাঁচা’ ও ‘নবীন তপস্বিনী’ হইতেও কিছু পাঠ করা হয়। তদনন্তর বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘প্রকৃতির খেদ’ নামে স্বরচিত একটি পদ্য প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ পদ্য অতি মনোহর। পাঠকালে সকলের মনে ভারতভূমির বর্তমান হীনাবস্থা স্মরণ হওয়াতে নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইয়াছিল। রবীন্দ্রবাবুর বয়স ১২।১৩ বৎসর।” (সাধারণী, ১২৮২ বঙ্গাব্দ, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, পৃ- ৫৬)
এছাড়া নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) লেখা ‘আমার জীবন’ গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথ-অক্ষয়চন্দ্র সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ পাওয়া যায়। সেই বিবরণ অনুসারে, ১৮৭৭ সালে হিন্দুমেলার একটি অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ‘দিল্লীর দরবার’ সম্পর্কে একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন এবং একটি গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র তাঁর সেই কবিতা ও গানে যে কতটা অভিভূত হয়েছিলেন, একথার পরিচয় ১৮৭৭ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখের সাধারণী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি প্রতিবেদনে পাওয়া যায়, যেখানে লেখা হয়েছিল—
“আমরা প্রকাণ্ড একটা বৃক্ষচ্ছায়ায় দুর্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া রবীন্দ্রের কবিতা এবং গীতটি শ্রবণ করি। রবীন্দ্র এখনও বালক, তাঁহার বয়স ষোল কি সতেরো বৎসরের অধিক হয় নাই। তথাপি তাঁহার কবিত্বে আমরা বিস্মিত এবং আদ্রিত হইয়াছিলাম, তাঁহার সুকুমার কণ্ঠে আবৃত্তির মাধুর্য্যে আমরা বি-মোহিত হইয়াছিলাম। যখন দেখিলাম যে বঙ্গের একটি সুকুমার শিশু ভারতের জন্য এই রূপ রোদন করিতেছে, যখন দেখিলাম যে তাঁহার কোমল হৃদয় পর্যন্ত ভারতের অধঃপতনে ব্যথিত হইয়াছে তখন আশাতে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তখন ইচ্ছা হইল রবীন্দ্রের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলি ‘আয় ভাই আমরা গাইব অন্য গান’। একজন সুপরিচিত কবিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দ্রবিত হৃদয়ে বলিলেন, যখন এই কবি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবে তখন দুঃখিনীবঙ্গের একটি অমূল্য রত্ন লাভ হইবে।”
এরপরে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ‘নবজীবন’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যাতেই ‘রাজপথ’ এবং ‘ভানুসিংহের জীবনী’ বের হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থে লিখেছিলেন— “এই সময়ে অক্ষয় সরকার মহাশয় নবজীবন মাসিক পত্র বাহির করিয়াছেন—আমিও তাহাতে দুটা-একটা লেখা দিয়াছি।” (জীবনস্মৃতি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১০ম খণ্ড পৃ- ১১৫)
পরবর্তী সময়ে সারদাচরণ মিত্রের সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র ‘প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ’ নামের যে খণ্ডগুলি প্রকাশ করেছিলেন, সেই সংগ্রহ পড়েই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনে প্রবল আকর্ষণের সৃষ্টি হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছিলেন— “শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয়সরকার মহাশয়ের প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড়ো করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি-অনুসারে যথসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।” (রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, জীবনস্মৃতি, ঘরের পড়া, পৃ- ৫৬)
প্রসঙ্গতঃ বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রযুক্ত ‘পহুঁ’ শব্দটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনাও এখানে অবশ্য উল্লেখ্য। এবিষয়ে তিনি লিখেছিলেন— “বৈষ্ণব কবিদের গ্রন্থে সচরাচর পহুঁ শব্দের দুই অর্থ দেখা যায়, প্রভু এবং পুনঃ। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের টীকায় লিখিয়াছেন পহুঁ অর্থে প্রভু এবং পহুঁ অর্থে পুনঃ। কিন্তু উভয়-অর্থেই পহুঁ শব্দের ব্যবহার এত দেখা গিয়াছে যে, নিশ্চয় বলা যায় এ নিয়ম এক্ষণে আর খাটে না।” (রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৪’শ খণ্ড, শব্দতত্ত্ব, পৃ- ৭৩)
রবীন্দ্রনাথের জীবনীগুলি থেকে জানা যায় যে, ১৮৮২ থেকেই একুশ বছর বয়সী যুবক রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যাতায়াত শুরু করেছিলেন। আর তখন থেকেই অনেক উপলক্ষ্যে বঙ্কিমের বৈঠকখানাতেই অক্ষয়চন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের আলাপ আলোচনা জমে উঠেছিল। পরে সেই আলাপ-আলোচনারই পরিণতিতে ‘নবজীবন’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। কারণ, এছাড়া নবজীবনের মূল বক্তব্য, অর্থাৎ—হিন্দু ধর্মালোন্দনের সঙ্গে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ধর্ম-ধারনার কোন ধরণের মিল ছিল না।
প্রসঙ্গতঃ এখানে অক্ষয়চন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ বিরোধের প্রসঙ্গও উল্লেখযোগ্য। একটাসময়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সকলের কাছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করছে দেখে অক্ষয়চন্দ্র তাতে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। এবিষয়ে তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, এই অতিশয় স্তাবকতা রবীন্দ্র-প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে। আর তাই ১২৯১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের ‘নবজীবন’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ভাই হাততালি’ নামক একটি রচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথকেই যেন হাততালির অপকারিতার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, সরস ব্যঙ্গরসাশ্রয়ী এই রচনাটি অক্ষয়চন্দ্রের অপূর্ব গদ্য ভঙ্গীর একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। এই রচনায় তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, রমাবাঈ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের তুলনা দিয়ে বলেছিলেন যে, হাততালিতে আত্মতুষ্টি জন্মায়, এরফলে কৃতি পুরুষের যোগ্যতার লাঘব ঘটে। হাততালির ‘অসার আস্ফালনে উদাসীনতা প্রদর্শনে’র বয়স বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের হলেও— “বয়স-বিগুণে রবীন্দ্রনাথের সে অধিকার এখনও হয় নাই।—তাই হাততালি, তাঁহার জন্য, আমাদের রবীন্দ্রনাথের জন্য, আজি তোমার কাছে আমাদের এই উপাসনা।” (অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার, শেষার্ধ, পৃ- ৪৮৫)
এরপরে তিনি আরও বলেছিলেন— “রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপশিখা; ধীরে ধীরে জ্বলিলে এই শিখা স্বীয় বর্ধমান আলোকে চারি দিক আলোকিত করিবে; প্রাচীন হিন্দুর সুগন্ধ-তৈল-নিষেবিত দীপের ন্যায় সেই অমল আলোকের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধে চারি দিক আমোদিত করিবে। … না, এখনও রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশার স্থল, ভরসার সংবল; তুমি না লাগিলে তিনি এখনও আমাদের দেশের গৌরব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। তুমি না লাগিলে—আর তুমি লাগিলে? তোমার সেই লক্ষ হস্তের দশ লক্ষ চট্চটি একবার প্রতিনিয়ত ধ্বনি করিলে, বীরের বীরাসন টলে, তা কোমল বঙ্গ-সন্তানের কি আর স্থৈর্য থাকিবে? ভাই! স্বীকার করিলাম তুমি বাহাদুর, তুমি মনে করিলে বীরপাত করিতে পার, কিন্তু তোমার হাতে ধরি, বিনয় করি, তুমি দিন কতক ক্ষান্ত থাকিবে না কি?” (অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার, শেষার্ধ, পৃ- ৪৮৫)
বলাই বাহুল্য যে, তরুণ রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতর মনে অক্ষয়চন্দ্রের এহেন বক্তব্যের অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া মোটেও ভাল হয়নি। বরং অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর প্রতি বিরূপ সমালোচনা করেছেন ভেবেই রবীন্দ্রনাথ এরপরে নবজীবন পত্রিকার সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র এরপরেও রবীন্দ্র রচনা বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি পূর্বোক্ত ‘ভাই হাততালি’ রচনাতেও তিনি সুদর্শন রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা দিয়ে লিখেছিলেন— “সেই অমল, কোমল, কমল-শোভা-সমন্বিত মুখশ্রী—সেই উজ্জ্বল, সলজ্জ, ভাসা ভাসা, ভ্রমর-ভরস্পন্দিত পদ্মপলাশ লোচন—সেই ঝামর-চামর-নিন্দিত, গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব-বেণী-বিনায়িত-চিকুর-ঝল-ঝল মুখমণ্ডল—সেই রহস্যে আনন্দে মাখানো হাসি-খুসী-ভরা-অধর-প্রান্ত—সেই সৎচিন্তার প্রসর-ক্ষেত্র, সুন্দর, শুভ্র, পরিষ্কার দর্পণোপম ললাট-ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখন বৃথা হইবার নহে।” (অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার, শেষার্ধ, পৃ- ৪৮৫)
আবার পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তি উপলক্ষে সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন— “রবিবাবুর কবিতা, এটি না-হয় ওটি, সকলকেই কখনও না কখনও মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার সম্মান করিতে তাঁহার দেশবাসী পরাম্মুখ হয় নাই—স্বয়ং সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র নিজ গলদেশে গ্রহণ না করিয়া কুসুমমালারূপিণী যশের মালা রবিবাবুর গলদেশে দিয়াছিলেন; প্রথম সাহিত্য-সম্মিলনে রবিবাবুই সভাপতি হন; সাহিত্য-পরিষৎ এবং এই টাউনহলের সভা তাঁহার উপযুক্ত সংবর্ধনা করিয়াছে। … তাঁহার একটি ক্ষুদ্র কবিতাকণিকা ‘গীতাঞ্জলি’ যাই বিলাতি বাটখারার ওজনে চড়িয়া আপনার গৌরব কাঞ্চনমুদ্রায় স্থির করিল, অমনই মহা শোরগোল পড়িয়া গেল। … কিন্তু বাস্তবিক মনীষিমাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন, রবিবাবু বেশি সার্থকও হন নাই, তাঁহার সর্বনাশও হয় নাই। তিনি আমাদের যে রবিবাবু, সেই রবিবাবুই আছেন; তাঁহার ‘নৈবেদ্য’ প্রকৃতই নৈবেদ্য; তাহার ভিত্তি পৃথিবী—’পরে হইলেও, কাঞ্চনশৃঙ্গের মত উজ্জ্বল শুভ্রকান্তি লইয়া সেই কাব্য নিয়তই রাজরাজেশ্বরের স্বর্গস্থ সিংহাসনাভিমুখে উন্নীত হইয়া আছে। তাঁহার ‘গীতাঞ্জলি’ পরমপিতার পূজার উপকরণ, সাধকের সাধনার সামগ্রী, ধাতুচক্রে তাহার গৌরব বাড়াইতে কমাইতে পারিবেনা।” (অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার, শেষার্ধ, পৃ- ৬৮১)
তবে পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথেরও অবশ্য অক্ষয়চন্দ্র বিষয়ে কোন ধরণের বিরূপ মনোভাব ছিল না। তাই পিতা গঙ্গাচরণ সরকার এবং অক্ষয়চন্দ্রের নিজের জীবনী লেখবার জন্য তিনি অক্ষয়চন্দ্রকেই অনুরোধ করেছিলেন। আর তাঁর এই অনুরোধের ফলেই অক্ষয়চন্দ্র নিজের ‘পিতাপুত্র’ নামক গ্রন্থটি লিখেছিলেন। এপ্রসঙ্গে তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন— “আমার ও পিতৃদেবের জীবনী লিখিতে আমি অনেকদিন হইতে অনুরুদ্ধ ছিলাম; সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি আমাদের সাহিত্য-জীবনের কথা বিশেষ করিয়া লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই সকল অনুরোধ-রক্ষার চেষ্টা করিতেছি।” (বঙ্গভাষার লেখক, ১ম খণ্ড, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, পৃ- ৪৬৫)
এছাড়া রবীন্দ্রনাথের ‘নৈবেদ্য’ প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র উক্তি করেছিলেন— “রবিবাবুর নৈবেদ্য আমি মাথায় করিয়া লইয়া দেবী সরস্বতীর পাদপীঠ-সম্মুখে নৃত্য করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করি।” (অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার, প্রথমার্ধ, পৃ- ২১)
সাহিত্য সমালোচকদের মতে রবীন্দ্রনাথের ‘নৈবদ্য’ প্রসঙ্গে তাঁর এই উক্তি নিঃসন্দেহে গভীর প্রশংসাসূচক ছিল। আবার ‘বিচিত্র প্রসঙ্গ’ গ্রন্থের লেখক বিপিনবিহারী গুপ্ত অক্ষয়চন্দ্রের পূর্বোক্ত উক্তি প্রসঙ্গে বলেছিলেন—
“যে নৈবেদ্য মাথায় করিয়া লইয়া বঙ্কিমবাবুর সমসাময়িক প্রবীণ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার আনন্দে নৃত্য করিতে পারেন, তাহার তুলনা আমাদের সাহিত্যে মেলে কি?” (বিচিত্র প্রসঙ্গ, বিপিনবিহারী গুপ্ত, গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে, পৃ- ২৯৬)
১৩২২ বঙ্গাব্দের ২০শে বৈশাখ তারিখের ‘প্রবাহিনী’ পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র যখন অক্ষয়চন্দ্রের স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তখন সমকালের বাংলা সাহিত্যের অবস্থা, ঐতিহাসিক গবেষণা ও নগেন্দ্রনাথ বসুর ‘বিশ্বকোষ’ প্রসঙ্গের পরে রবীন্দ্রনাথের কথা উঠলে তিনি জানিয়েছিলেন— “তাঁহার সম্বন্ধে অক্ষয়বাবু বলিলেন আমরা সাহিত্য চর্চ্চায় রত হইবার পর, রবীন্দ্রবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য আসরে দেখা দেন। তখন তাঁহার বয়স অল্প। তখনও তাঁহার লেখার আড় ভাঙ্গে নাই। রবীন্দ্রের তখন নবীন উদ্যম, নবীন বয়স, নবীন সাধনা। কিন্তু সাহিত্যে যশস্বী হইবার মত প্রতিভা যে তাঁহার আছে, আমরা তখনই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমরা বলিতে, আমি বঙ্কিমবাবুর কথাই বলিতেছি। তিনি তাঁহার সম্বন্ধে প্রথমে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। আজ তাহা সফল হইয়াছে। এযুগের লোকের উপর তাঁহার অসীম প্রভুত্ব থাকিবার অনেকগুলি কারণ আছে। তিনি আপনার বক্তব্যগুলি বেশ গুছাইয়া বলিতে পারেন। তাঁহার ভাষা মিষ্ট—যেন একটা ঝঙ্কার, সত্যসত্য একটা সঙ্গীত। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইয়া গেলেও তাহার রেশ মাথার মধ্যে অনেকক্ষণ রিশ রিশ করিতে থাকে। তাহার পর, তাঁহার গলা মিষ্ট, তাঁহার ভাষারই উপযোগী। এবং তিনি দেখিতেও সুপুরুষ। যখন তাঁহার স্বভাব সৌন্দর্য্যের সহিত ভাষার সৌন্দর্য্য মিশিয়া, সভার গৃহে তাঁহার বীণানিন্দিত কণ্ঠ বাজিয়া উঠে, তখন সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়, যুক্তি-তর্ক ভাসিয়া যায় একেবারে সকলকে হিপনটাইজ করিয়া ফেলে। এবিষয়ে একটা সুন্দর গল্প আছে। একবার তাঁহার সহিত শ্রদ্ধেয় শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের শব্দের শক্তি আছে কিনা এই লইয়া তর্ক হয়। শব্দের অর্থ লইয়াই কথা, যাহার অর্থের যত গভীরতা, তাহাই তত শ্রোতাকে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রবাবু বলেন শব্দের অর্থ থাক বা না থাক, তাহার একটা নিজস্ব শক্তি আছে। অনেক সামান্য অর্থহীন শব্দও শ্রোতাকে মুগ্ধ করে, এই বলিয়া তিনি উদাহরণস্বরূপ একটা গান গাহিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সেই মধুর কণ্ঠস্বরে সভাগৃহ যে মূর্ছনায় ভরিয়া উঠিল, তাহা ব্রজেন্দ্রবাবুর সমস্ত যুক্তি তর্ককে ভাসাইয়া দিল। শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই রবীন্দ্রনাথের কথাতেই সায় দিলেন, এমন কি ব্রজেন্দ্রবাবু পর্যন্ত। কিন্তু তোমরা জান, যুক্তির নিকট রবীন্দ্রবাবুর একথা খাটে না। রবীন্দ্রনাথের রচনা একটা কুহকের সৃষ্টি করে। বর্তমান সময়ে আমার মনে হয়, আমাদিগের দেশে এরকম সাধনা, অতি কম লোকেরই আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে এ বিদ্যায়, তিনি অদ্বিতীয়।” (প্রবাহিনী, পৃ: ১৮২-৮৩)
১৯১১ সালে ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ার পরে অক্ষয়চন্দ্র ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নামের একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। (মানসী, ফাল্গুন, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ) তাতে তাঁর মূল কথা ছিল যে, বাঙালির স্বদেশভাবনা ভারতকে ছেড়ে বঙ্গকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে এবং সেই পাপেরই ফলস্বরূপ রাজধানী স্থানান্তরের ঘটনাটি ঘটেছে। ‘অয়ি ভুবনমনোমোহিনী’ গানের ভারতচিন্তা ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’–এ সঙ্কুচিত হয়েছে। এরপরে তিনি বলেছিলেন—
“কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বদেশের পরিধি কমাইয়া ভারতপ্রীতিকে বঙ্গপ্রীতিতে পর্যবেশিত করিতে ইদানীং বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। … আমরা পুরাণ’ পাপী, ভারতমাতার ভিখারী সন্তান। আমরা কিন্তু সেই গরীয়সী জগজ্জননী ভারতমাতাকে ভুলিয়া নবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথ ডাকযোগে আমাকে রাখীসূত্র এবং মন্ত্রসূত্র পাঠাইয়াছিলেন। রাখী বাঁধিলাম, কিন্তু মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিলাম না।” (মানসী, ফাল্গুন, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৪৫-৫০)
কিন্তু একথা বলাই বাহুল্য যে, বঙ্গসর্বস্বতা কখনোই রবীন্দ্রনাথের দেশানুরাগের মূল কথা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রাখীবন্ধন আন্দোলন একটি সাময়িক ব্যাপার ও ভারতের জাতীয়-আন্দোলনের একটি সন্ধিপর্ব ছিল। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারত ভাবনাকেই পরে বিশ্বমানবচেতনায় রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র-মানসের এই বিকাশ-বিবর্তন অক্ষয়চন্দ্র সরকার অনুধাবন করবার আর সুযোগ পাননি। কারণ, ১৯১৭ সালেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, আর রবীন্দ্র-প্রতিভা ১৯৪১ সাল পর্যন্ত নিজের সৃষ্টিকর্মে নিরলসভাবে নিয়োজিত ছিল। বঙ্গভঙ্গের সাময়িক মুহূর্তটি বাদ দিলে কবির স্বদেশভাবনা আর কখনই বঙ্গসীমায় সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েনি বলেই গবেষকরা মনে করে থাকেন। আবার, এই বিশেষ সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়ে অক্ষয়চন্দ্র তাঁর যে সমালোচনা করেছিলেন, সেটার দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়াও তাঁর বিচক্ষণতারই পরিচয় দেয়।#