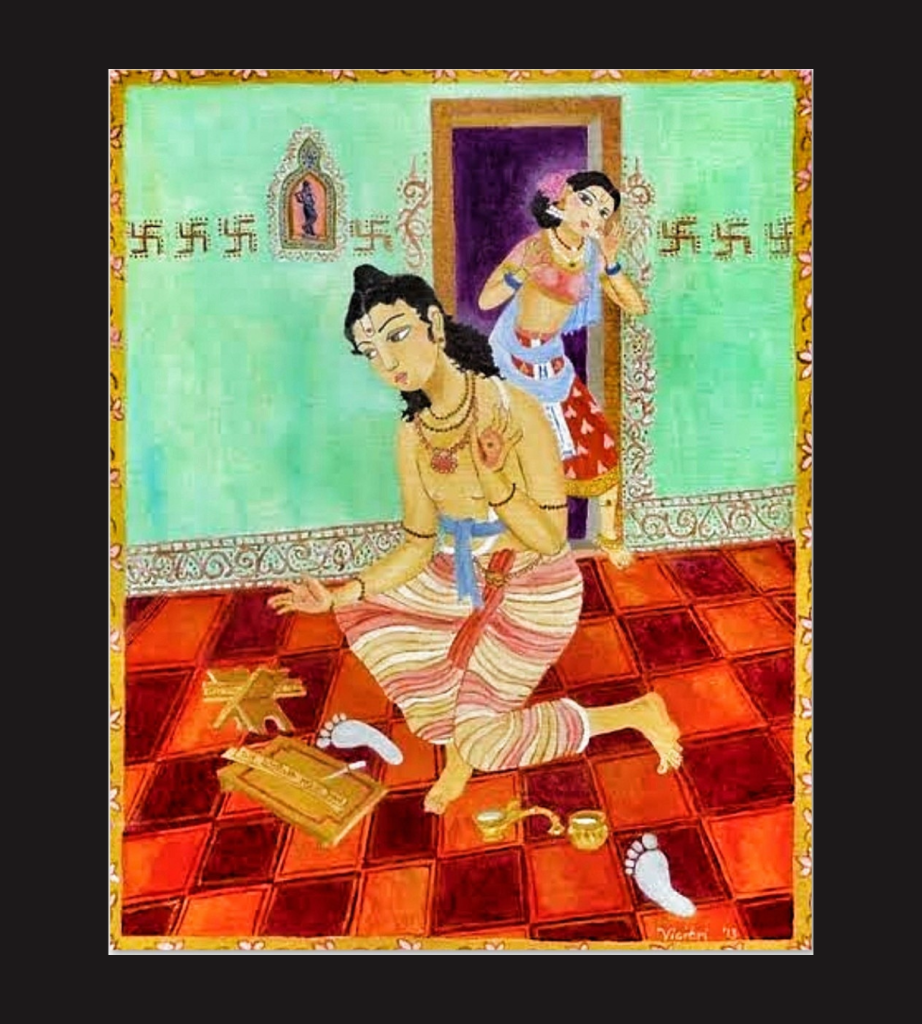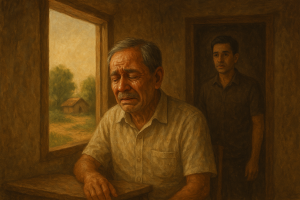বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীর আদি কবিকুলগুরু জয়দেব একজন ধর্মীয় কবিরূপে মধ্যযুগের ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে শুরু করে গোবিন্দদাসের কবিপ্রণাম পদে সমভাবেই শ্রদ্ধা অর্জন করে এসেছিলেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁকে নিয়ে প্রথম গোলমালের সূত্রপাত ঘটেছিল আধুনিকযুগে পৌঁছে। মধ্যযুগের মতোই, খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের ইউরোপীয় সমালোচক ও অনুবাদকরাও প্রথমে জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের লৌকিক বর্ণনায় মুগ্ধ হলেও, পরবর্তীসময়ে সময়ে কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই কাব্যকে অধ্যাত্মতত্ত্বের রূপক বলে অভিহিত করেছিলেন। বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এবিষয়ে সমালোচকদের দৃষ্টির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আর এরপরে আধুনিক বাঙালি সমালোচকরাও জয়দেবের কাব্যের প্রশংসা করেছিলেন বটে, কিন্তু একইসাথে জয়দেবের কাব্য যে বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য—এরকম কোন অলীক কল্পনার বশবর্তী হয়ে নয়, বস্তুতঃ বিশুদ্ধ লৌকিক সাহিত্যের বিচারে জয়দেবের গীতগোবিন্দের যতটুকু প্রশংসা প্রাপ্য ছিল, ঠিক ততটুকু প্রশংসাই তাঁরা করেছিলেন। তাই আধুনিকযুগে পৌঁছে গীতগোবিন্দের সমালোচনা আগের মত আর হরিস্মরণে সরস নয়, বরং বিলাস কলার কৌতূহলে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল বলে দেখা যায়।
এবিষয়ে আধুনিকযুগের বাঙালিদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথম নিজের লেখনী ধারণ করেছিলেন। ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত ‘সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব’ নামক গ্রন্থে তিনি জয়দেবের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছিলেন—
“গীতগোবিন্দ জয়দেব প্রণীত। এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এরূপ ললিত পদবিন্যাস, শ্রবণমনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা, ও প্রসাদগুণ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার রচনা যেরূপ চমৎকারিনী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিণী। জয়দেব রচনা বিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্ব শক্তি তদনুযায়ী হইত, তাহা হইলে তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব কালিদাস ভবভূতি হইতে অনেক ন্যূন বটেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য নয়। বোধ হয় বাংলাদেশে যত সংস্কৃত মহাকবি হইয়াছেন, তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট।”
এভাবেই বিদ্যাসাগরের উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলায় জয়দেব বিষয়ে সর্বপ্রথম কোন অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী ধরা পড়েছিল। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, পণ্ডিত বিদ্যাসাগর কিন্তু জয়দেবের কাব্য সমালোচনা করতে গিয়ে কোন ধরণের ভক্তিবাদী ভাবোচ্ছ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হননি; বরং তিনি মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যকে ধর্মীয় আবহাওয়া থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ শিল্পের আদর্শে বিচার করেছিলেন। আধুনিক সমালোচকদের এই অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই এযুগে যেমন বৈষ্ণব সাহিত্যকে বৈকুণ্ঠের গান হিসেবে না দেখে লৌকিক প্রেমসাহিত্যরূপে দেখবার একটা প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল, ঠিক তেমনি আবার জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসকে বৈষ্ণব সাধনার অস্পষ্ট কুহেলিকার মধ্যে না রেখে ঐতিহাসিক গবেষণার পটভূমিতে অবতীর্ন করে ধর্মসংস্কারবর্জিত বিশুদ্ধ কবিত্বের বিচারে তাঁদের নবমূল্যদান করবার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। এরফলে তখন থেকেই মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের বৈষ্ণব সাহিত্য বিচারের মধ্যে বিপুল পার্থক্য দেখা দিয়েছিল।
কথিত রয়েছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব নাকি জয়দেবের কাব্য শুনে তৃপ্ত হতেন; কিন্তু এই সামান্য তথ্যটুকুতে তৃপ্ত হয়েই সমগ্র মধ্যযুগ জয়দেবের কাব্য বিচার করাকে একটা স্পর্ধা বলে মনে করেছিল, এবং জয়দেবকে একজন আধ্যাত্মিক কবি ও জয়দেবের কাব্যকে আধ্যাত্মিক কাব্য বলে অন্ধভাবে পূজা করে এসেছিল। কিন্তু আধুনিকযুগে পৌঁছানোর পরে পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের কণ্ঠে সর্বপ্রথম জয়দেবের কাব্যের জন্য সংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ কাব্যবিচারের আহ্বান শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, আপাত প্রশংসা সত্ত্বেও জয়দেব সম্পর্কে বিদ্যাসাগর যা কিছু বলেছিলেন, সেটাই হল জয়দেব সম্পর্কে এযুগের আধুনিক বাঙালির মত। এই প্রথম কোন বাঙালি ধর্মীয় সংস্কারের চশমা খুলে একজন কাব্যরসিকের খোলাচোখে জয়দেবকে দেখেছিলেন। আর এরফলে এটাই দেখা গিয়েছিল যে, প্রতিভার ক্ষেত্রে জয়দেবের অবস্থান কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখের থেকে অনেক নীচে, এবং তাঁর রচনারীতি যতটা প্রশংসনীয়,—কবিত্বশক্তি কিন্তু তদনুযায়ী নয়। জয়দেব যতটা কানকে ভোলান, মনকে কিন্তু ততটা নাড়া দিতে পারেন না—ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে এই প্রথম জয়দেবের এই আংশিকতা ধরা পড়েছিল। এরপরে বিদ্যাসাগবের এই মন্তব্যই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের জয়দেব সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে দিয়ে শেষপর্যন্ত বলেন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর তীব্র সমালোচনায় পরিণত হয়েছিল।
সুতরাং সংক্ষেপে বললে একথাই বলতে হয় যে, বিদ্যাসাগরের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যই ছিল জয়দেব সম্পর্কে আধুনিকযুগের প্রথম কোন প্রতিানধিত্বসূচক সমালোচনা। এক্ষেত্রে রীতিবাদী কবি জয়দেবের শ্রবণ সুভগ রচনারীতির যেমন প্রশংসা করা হয়েছিল, ঠিক তেমনি আবার তাঁর কবিত্ব শক্তির ন্যূনতা সম্পর্কেও যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আর এই পথ অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে জয়দেবের সঙ্গে বিদ্যাপতির তুলনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জয়দেবের মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতের সৌন্দর্যকে প্রশংসা করলেও একে বহিরিন্দ্রিয় বলে নিন্দা করেছিলেন বলেও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিত বিদ্যাসাগর কোন ধরণের ব্যাখ্যা না করেই জয়দেবকে কালিদাস ও ভবভূতির থেকে ন্যূন বলে যে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করেছিলেন, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’ গ্রন্থের ‘কেকাধ্বনি’ নামক প্রবন্ধে কালিদাস ও জয়দেবের কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করে চমৎকার ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তকেই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। এছাড়া বিদ্যাসাগর জয়দেবের বর্ণনারীতির প্রশংসা করে যা কিছু বলেছিলেন, পৰৱৰ্তীসময়ে রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর ‘The Literature of Bengal’ নামক গ্রন্থে জয়দেব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সেটাকেই আবার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিলেন। অন্যদিকে ‘নবজীবন’ নামক একটি পত্রিকায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার, এবং নবপর্যায়ের ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় জিতেন্দ্রলাল বসু জয়দেবকে সপ্রশংস সমর্থন করেছিলেন বলে দেখতে দেখতে পাওয়া যায়। আবার বিদ্যাসাগর তাঁর লেখনীতে জয়দেবের যে অক্ষমতার কথা নির্দেশ করেছিলেন, পরবর্তীসময়ে ‘সাধনা’ ও ‘ভারতী’ পত্রিকায় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী এটাকেই আরও তীব্র ও তিক্ত বিরোধী আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছিলেন।
এবারে আধুনিকযুগের বাঙালিদের কলমে জয়দেবের স্বপক্ষ-প্রশংসা এবং বিপক্ষনিন্দা—দুটোকেই অনুধাবন করা যেতে পারে।
এপ্রসঙ্গে প্রথমেই রমেশচন্দ্র দত্তের কথা উল্লেখ্য। তিনি জয়দেবের কাব্যের সঙ্গীতগুণ ও চিত্রগুণ—উভয়েরই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন বলে দেখা যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রচলিত থাকা সংস্কৃত শব্দের কঠিন উপলস্তর ভেদ করে জয়দেব সঙ্গীতের যে স্রোতস্বিনী ধারা প্রবাহিত করেছিলেন, এর প্রশংসা করে রমেশচন্দ্র তাঁর ‘The Literature of Bengal’ গ্রন্থে লিখেছিলেন—
“The first thing that strikes the reader is the exquisite music of the songs. It is a master hand that wakes the lyre and the ear is pleased and ravished with a flood of the sof- test and sweetest melody before one comprehends the sense.”
তবে শুধু সুরসঙ্গীত নয়, জয়দেব রচিত সাহিত্যের অন্য উপাদান—চিত্রধর্মিতা সম্পর্কেও রমেশচন্দ্র উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলে—
“It is no less rich in its soft and voluptuous description. The blue waves of Yamuna, the cool shade of the dark some Tamal tree, the soft whisperings of the Malaya breeze, the voluptuous music of Krisna’s flute, more melodious than the song of the Kokil from the neighbouring Bokul tree, the timid glances of the love-stricken milk-maids that spoke of love, the fond workings of a lover’s heart, the pangs of jealousy, the sorrows of separation, the raptures of reunion, all these are clearly and vividly reflected in the song of the immortal bard of Birbhum.”
লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, রমেশচন্দ্র কৃত এই বিস্তৃত সমালোচনায় জয়দেবের কাব্যের প্রাকৃত প্রেম ও জাগতিক সৌন্দর্যেরই শুধু প্রশংসা করা হয়েছে, এতে তিনি অপ্রাকৃত প্রেমের আধ্যাত্মিকতার কোন উল্লেখ করেননি।
এরপরে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের বা ১৮৮৬ সালের ‘নবজীবন’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘জয়দেব’ নামক প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার গীতগোবিন্দের ভাষা ও ছন্দ এবং কাব্যবৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বাংলায় ও বাংলা সাহিত্যে জয়দেবের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—
“বঙ্গের সাহিত্যজগতে জয়দেব আদিগুরু, তিনি গীতিকাব্যের কল্পতরু। এখনও বঙ্গের গীতিসাহিত্য সেই মহাজনের দ্বারস্থ, তাঁহার নিকট পদানত।”
অন্যদিকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর ‘গীতগোবিন্দ’ নামক প্রবন্ধে জয়দেবের সঙ্গে কালিদাসের তুলনামাত্র করলেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিন্তু বিদ্যাপতির সঙ্গে জয়দেবের তুলনা করে ১২৮০ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘মানস বিকাশ’ নামের প্রবন্ধটিতে যা কিছু বলেছিলেন, সেটাই পরে কিছু পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে ‘জয়দেব ও বিদ্যাপতি’ শিরোনামে তাঁর ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ নামক গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন জয়দেব ও বিদ্যাপতিকে নিয়ে তুলনামূলক সমালোচনা আরম্ভ করেছিলেন, তখন তাঁর দেখাদেখি সেযুগের অনেক সমালোচকই মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিদের নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাঁদের এসমস্ত তুলনামূলক সমালোচনায় চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন, এবং তাঁদের মধ্যেকার এই তুলনাও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ভাললাগা ও মন্দলাগার আলোচনা ছিল। কিন্তু বিদ্যপতিকে জয়দেবের প্রতিযোগী নির্বাচন করে এই উভয় কবির ব্যক্তিগত রুচির সঙ্গে যুগগত কারণ বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিকযুগের বাংলায় বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনার যে উচ্চমান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সমসাময়িক ও পরবর্তীযুগে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ্য যে, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমের ‘মানস বিকাশ’ প্রবন্ধটি পরবর্তীসময়ে তাঁর ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ নামক গ্রন্থে ‘জয়দেব ও বিদ্যাপতি’ শিরোনামে প্রকাশিত হওয়ার সময়ে অনেকটাই পরিবর্জিত ও কিছুটা পরিবর্তিত করা হয়েছিল। একথার উদাহরণস্বরূপ এখানে জয়দেব সম্পর্কিত বঙ্কিমের মন্তব্যের একটি পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্তঃপ্রকৃতির সংস্পর্শশূন্য বহিঃপ্রকৃতিই যদি শুধু কোন কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় হয়, তাহলে সেটাকে ইন্দ্রিয়পরতা দোষ বলে অভিহিত করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘মানস বিকাশ’ প্রবন্ধে লিখেছিলেন—
“এস্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের আনুরক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ কালিদাস ও জয়দেব।”
কিন্তু পরবর্তীকালে নিজের ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ গ্রন্থের ‘জয়দেব ও বিদ্যাপতি’ প্রবন্ধে তিনি যখন অনুরূপ সিদ্ধান্তের উদাহরণ দিয়েছিলেন, তখন কিন্তু লিখেছিলেন—
“ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ জয়দেব।”
অর্থাৎ, এবারে তাঁর চোখে কালিদাস জয়দেবীয় দোষ থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সংশোধন কিন্তু লক্ষ্যণীয়। আসলে জয়দেবের ইন্দ্রিয়াসক্তির দোষ যে কালিদাসের মধ্যে নেই, একথা তিনি স্বভাবতঃই বুঝতে পেরেছিলেন।
এরপরে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত সকলেই কালিদাসের সঙ্গে জয়দেবের তুলনা করে জয়দেবের এই অক্ষমতার দিকটাই বিশেষভাবে তুলে ধরেছিলেন।
এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘কেকাধ্বনি’ নামক প্রবন্ধে জয়দেবের কাব্য সম্পর্কে বঙ্কিমকথিত ইন্দ্রিয়পরতার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন—
“জয়দেবের ললিতলবঙ্গলতা ভালো বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ ভাল নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন মহারাজার কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়।”
আর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘জয়দেব ও বিদ্যাপতি’ প্রবন্ধে কাব্যের ইন্দ্রিয়পরতা ও আধ্যাত্মিকতা দোষ সম্পর্কে যা কিছু বলেছিলেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘জয়দেব’ নামক প্রবন্ধে সেটারই প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন—
“শরীরমাত্রগত সম্ভোগ ও দর্শনস্পর্শনাকাঙ্ক্ষহীন অতি সূক্ষ্ম ধ্যানগত সম্ভোগ-মৃতদেহ ও প্রেতাত্মা-উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে মনুয়্যত্বকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে অক্ষম।”
এছাড়া বিদ্যাপতির সঙ্গে জয়দেবের তুলনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমকথিত জয়দেবের ইন্দ্রিয়পরতা দোষকেই বলেন্দ্রনাথ অন্যভাবে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন—
“গীতগোবিন্দ পাঠান্তে মনে হয় ন্যায়শাস্ত্র বর্ণিত অন্ধের ন্যায় প্রেমের বিপুল বহিরঙ্গেই জয়দেব হাত বুলাইয়া গিয়াছেন।”
এরপরে প্রমথ চৌধুরী তাঁর ‘জয়দেব’ নামক প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে জয়দেবের গীতগোবিন্দের সম্পর্ককে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে বলেছিলেন—
“আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে এ কাব্যে আধ্যাত্মিকতার কোন পরিচয় নাই।”
এক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, এর আগে বঙ্কিমও কিন্তু বলেছিলে—
“যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্মোৎসব।”
আধুনিকযুগের বাংলায় জয়দেবের বিপক্ষবাদীদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১২২৭ বঙ্গাব্দ বা ১৮৯০ সালের ভারতী পত্রিকায় এবং বলেন্দ্রনাথের ‘জয়দেব’ প্রবন্ধটি ১৩০০ বঙ্গাব্দের বা ১৮৯৩ সালের সাধনা পত্রিকায় প্রতিক্ষিত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী কিন্তু গীতগোবিন্দ কাব্যের আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত প্রচলিত মতকে প্রথমেই অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর মত ছিল যে, দেহবর্ণনাই হল গীতগোবিন্দের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া তিনি একথাও জানিয়েছিলেন যে, কালিদাসের তুলনায় জয়দেবের বিরহবর্ণনা প্রাণহীন, সৌন্দর্য বর্ণনা গতানুগতিক, উপমা প্রথানুগত, অর্থহীন ও কবিত্ব বর্জিত, ভাষা ভাবানুযায়ী নয়, কৃত্রিম এবং ছন্দ রিদমহীন ও একান্ত পিচ্ছিল। আসলে প্রমথ চৌধুরী জয়দেবের কাব্যের বিলাসাতিরেক সম্পর্কে যে যুগগত কারণ বিশ্লেষণ করেছিলেন, সেটা বঙ্কিমেরই সমর্থন ছিল। অন্যদিকে বলেন্দ্রনাথের জয়দেব-বিরোধিতার কারণ এটাই যে, প্রেমের ক্ষেত্রে জয়দেবের সম্ভোগান্ধ দেহসর্বস্ব দৃষ্টি যেমন খণ্ডিত, ছন্দপিচ্ছিল কাব্যবর্ণনার ক্ষেত্রেও জয়দেবের কাব্য ইন্দ্রিয়াতিরেকের জন্য ক্লান্তিকর। সর্বোপরি জয়দেবের কাব্যে নগ্নতার জঘন্য ইঙ্গিতকে নির্দেশ করে বলেন্দ্রনাথ গীতগোবিন্দের গোবিন্দগীতিকেও কিন্তু অস্বীকার করেছিলেন।
এভাবেই আধুনিকযুগের বাংলায় জয়দেবের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া যখন প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল, ঠিক তখনই আবার ১৯১৯ সালের নবপর্যায়ের ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় জিতেন্দ্রলাল বসুর ‘জয়দেব ও বিদ্যাপতি’ প্রবন্ধে জয়দেব বিরোধিতার তীব্র প্রতিবাদ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এতে বিদ্যাপতির উপরে জয়দেবের প্রভাব নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক গীতগোবিন্দের কাব্যগৌরব ও অধ্যাত্মমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছিলেন বলে দেখা যায়। তবে এসবের মাঝে এই প্রবন্ধটিতে জয়দেব বিরোধীদের প্রতি কটাক্ষপাতও লক্ষ্যণীয়।
এরপরে ডঃ সুশীলকুমার দেবের ‘জয়দেব ও গীতগোবিন্দ’ প্রবন্ধে এবং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের ‘কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ’ নামক গ্রন্থে জয়দেবের জয়ধ্বনি আবার উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল।
এভাবেই জয়দেবের সপক্ষবাদী এবং বিপক্ষবাদীদের পক্ষপাতপূর্ণ সমালোচনায় ঊনিশ ও বিশ শতকের বাংলা যখন উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল, ঠিক তখনই আবার কোন পক্ষ অবলম্বন না করে জয়দেবের ব্যক্তিপরিচয় ও কাব্যপরিচয় উদঘাটন প্রসঙ্গে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘শ্রীজয়দেব কবি’ নামের যে নিরপেক্ষ গবেষণা ও সমালোচনাটি ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় ১৩৫০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটাই এখনো পর্যন্ত জয়দেব সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ আলোচনা ও পরিণত গবেষণা বলে গণ্য হয়ে রয়েছে।
আর অবশেষে ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর মেঘদূত অনুবাদের ভূমিকায় জয়দেব সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত একটি বিদগ্ধ মন্তব্যে জয়দেব সম্পর্কে আধুনিকযুগের বাঙালির সমস্ত সিদ্ধান্তের যে সারমর্ম পাওয়া গিয়েছিল, সেটা এরকম ছিল—
“জয়দেব এক সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন: ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীনের অস্তরাগ তিনি এবং আধুনিকের পূর্বরাগ।”#